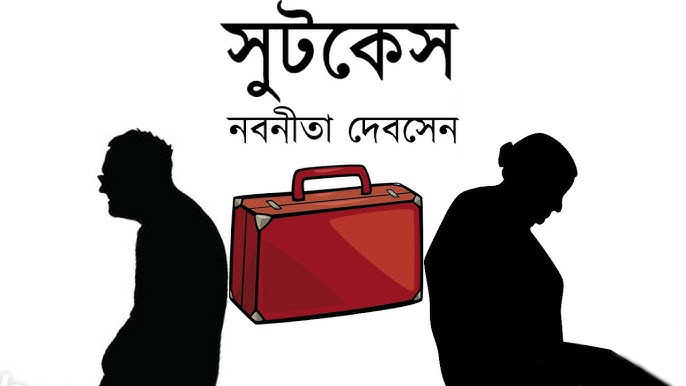চন্দন বাবার জন্যে বিলেত থেকে ঘড়ি আনল, কিন্তু মা’র জন্য কী যে আনবে ভেবে পেল না। শেষে কী ভেবে একটা লাল-টুকটুকে, ছোটো দেখে হালকা ফাইবার গ্লাসের সুটকেস কিনল। বাবা ঘড়ি পেয়ে মহাখুশি, এক স্নানের সময়েই যা ঘড়িটা খুলে রাখতে বাধ্য হন। আর মা গদগদচিত্তে সুটকেসটিকে একটা টুলের ওপরে, ফুল তোলা কাপড় দিয়ে ঢেকে সাজিয়ে রাখলেন।
চন্দনের ছোট ভাই বুচকুন এখনও কলেজে পড়ে, মা-বাবার কাছে শুধু সে-ই থাকে। আর থাকে সেজ বোন ইন্দিরা, ওখানে গার্লস স্কুলে পড়াচ্ছে। ছোট বোনটা ক্লাসফ্রেন্ডকে বিয়ে করে আগেই কলকাতায় চলে গেছে। দিদি মেজদি বহুকাল শ্বশুরবাড়িতে। দিদির ছেলেই বুচকুনের সমান। চন্দনের চার দাদাও বিয়ে-থা করে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন। দশ ছেলে মেয়ের মা হলে কী হবে, সলাজনয়নী এখনও বেশ শক্ত আছেন, রান্নাবান্না নিজেই করেন। ক্ষেত্রবাবুর এই আটাত্তর হল। বাঁ চোখে ছানি পড়েছে, ভাল দেখতে পাচ্ছেন না আজকাল। চন্দন তাই চিঠিতে দরকারি অংশগুলো আন্ডারলাইন করে দেয়।
আপাতত চন্দনের দুটো চাকরি হয়েছে বার্নপুরে। এক: এঞ্জিনিয়ারিং, আর এক: বোনের জন্যে ঘটকালি। বাবা-মায়ের মনে এখন প্রধান উদ্বেগ ইন্দিরা, যার বয়েস সাতাশ পুরেছে। গোটা শিলিগুড়ি শহরে নাকি সাতাশ বছরের অবিবাহিত কন্যা আর একটিও নেই। চিঠিতে চন্দন তাই নিয়ম করে পাত্রের খবর পাঠায়। সাধারণত খাঁটিই, মাঝে মাঝে অবশ্য কল্পিতও। কেন না, চন্দন সার কথাটা বুঝে গেছে, বাবা-মাকে সবচেয়ে খুশি করতে পারে এই একটিই প্রসঙ্গ।
সেদিন চন্দনের চিঠিতে একটা চমৎকার সম্বন্ধ এল। পাত্র এই শিলিগুড়িরই ছেলে, কাজ করে আসানসোলে, মাইনিং এঞ্জিনিয়র। বাবা যদি সম্বন্ধটা পছন্দ করেন, তবে চন্দন কথা বলতে পারে ছেলের সঙ্গে। বাবা যাতে যোগাযোগ করতে পারেন পাত্রের বাবার সঙ্গে তাই শিলিগুড়ির ঠিকানাটাও পাঠিয়েছে চন্দন। ছানি-পড়া চোখে বাবা অধিকাংশ সময়েই আন্দাজে কাজ সারেন। তিনি আন্দাজে পড়লেন যে, চন্দন কথা বলে ফেলেছে পাত্রের সঙ্গে, এখন বাবা যেন কথাটা পাকা করেন পাত্রের বাবার সঙ্গে। বাবা ছাতাটা নিয়ে জুতোতে পা গলাতে গলাতে ডাকলেন—“বড়বউ, আমি একটু বেরুচ্চি। কথাটা পাকা করে আসি, ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা যখন হয়েই গেছে। কাল বিকেলে ওরা মেয়ে দেখে যাক।”
মা (ওরফে বড়বউ) বললেন—“সে কী গো? পাকা কথা কি? চন্দন তো কোনও কথাই পাড়েনি এখনও। তুমি বরং যাও, পাওনা-থোওনা কে কীরকম চায় সব শুনে এসো, ঘরদোর দেখে এসো, মেয়ে দেখানো এক্ষুনি কী? ও পরে হবে। কালই দেখাতে হবে না।”
বাবার কেবল চোখেই ছানি নয়, কানেও একটু কম শোনেন মাঝে মাঝে। তাই রাগটা ইদানীং বেড়েছে। বাবা রেগে বললেন—“মেয়ে দেখানো হবে না? বেশ আমি তাহলে চন্দনকে লিখে দিচ্ছি এ সম্বন্ধ ক্যানসেল, এখানে হবে না।”
—“আহা, আমি কি তাই বলেছি? আগে তুমি অন্য অন্য কথাবার্তা করে নাও, ঘরটা কেমন বুঝেশুনে এসো, চন্দন ওখানে পাত্রের সঙ্গে কথা বলুক, তারপরে তো মেয়ে দেখাবে?”
কেবল আধখানা শুনতে পেয়ে বাবা বললেন— “ও! চন্দন পাত্রের সঙ্গে কথা বলবে, তারপরে হবে। আমি কেউ নই? আমার কথা বলা চলবে না? বেশ, দেখাচ্ছি কেমন আমি কেউ নই। এই চললুম পাত্রপক্ষকে বারণ করে আসতে। দেখি এ বিয়ে কী করে হয়? বিলেত ফেরত বলেই ছেলের কথা বাপের কথার ওপর উঠবে?”
বাবা জুতো পরে ছাতা বগলে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে মাও চেঁচিয়ে উঠলেন—“অ্যাঁ, বিয়ে ভাঙতে গেলেন? এত বড় রাগ? বাপ হয়ে মেয়ের এত বড় সব্বোনাশ করা? বেশ আমিও চললুম তবে মাথাভাঙ্গা!”
চন্দনের মামাবাড়ি মাথাভাঙ্গার কাছাকাছি। রাগ করে কথায় কথায় গত পঞ্চাশ বছর ধরেই সলাজনয়নী বলে আসছেন— “এই চললুম আমি মাথাভাঙ্গা।” কিন্তু তারপরে কার্যটি আর এগোয়নি।
এগোয়নি, তার কারণ একাধিক। প্রথম কথা, শিলিগুড়ি থেকে মাথাভাঙ্গার কাছে ওই পাড়াগাঁয়ে যাওয়াই ছিল এক বিপুল জটিলতা। যেতে হলে জলপাইগুড়ি হয়ে ট্রেন বদলে, অন্য ট্রেন ধরে, তারপরে বাস ধরে, তারও পরে হাতি কিংবা ডুলি চড়ে যেতে হত। যদিও বা কোনও জাদুবলে মা একা-একা এতকাণ্ড করতেনও, মস্ত একটা দ্বিতীয় বাধা ছিল তোরঙ্গ। চন্দনের বাড়িতে কেবল ধেড়ে ধেড়ে স্টিলের ট্রাংক আর কাঠের প্যাঁটরা ছাড়া বাক্সই ছিল না। সুটকেসের চল হয়নি চন্দনের বাড়িতে। তা, রাগ করে কি কেউ একখানা ধুমসো ভারী তোরঙ্গ মাথায় করে বাপের বাড়ি যায়? না কি এককাপড়ে ভিকিরির মতনই কেউ খালি হাতে বাপের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে? এই গূঢ় সমস্যার কারণেই মা এতদিনে ‘চললুম মাথাভাঙ্গা’টাকে কাজে পরিণত করতে পারেননি। পঞ্চাশ বছর পরে এতদিনে সমস্যার সমাধান হয়েছে। মা ফুরফুরে হালকা বিলিতি সুটকেসে ভরে নিলেন ক’খানা ভাল দেখে ধোপ-দোরস্ত শাড়ি-সেমিজ, গুরুদেবের ফটো, জপের মালা, তেল সাবান গামছা, ফিতে চিরুনি আয়না। আর জমানো হাতখরচের টাকাটা। ছোকরা চাকর পরমেশ্বরের হাতে এক টাকা চার আনা দিয়ে বললেন—“একটা সিনেমা দেখে আয়।” দোরে তালা লাগিয়ে দোরের চাবি, ঘরের চাবি প্রতিবেশিনীর আঁচলে বেঁধে দিয়ে এলেন—‘ইন্দু ইস্কুল থেকে এলেই তাকে দিয়ে দিয়ো—’ বলে। বুচকুন তখনও কলেজে।
সোজা একটি রিকশা চড়ে মা গেলেন সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে। গত পুজোয় তাঁর দাদার ছেলেরা এসেছিল—আজকাল দিব্যি টানা বাস হয়ে গেছে শিলিগুড়ি টু মাথাভাঙ্গা। চমৎকার নতুন টারম্যাকের রাস্তা হয়েছে। বদল-টল করতে হয় না কোথাও। ওখানে নেমেও হাতি চড়তে, কি ডুলি নিতে হয় না। রিকশা করেই বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বাড়ি যাওয়া যায়। দাদার ছেলেরা বার বার করে ডিরেকশান দিয়ে গেছে—মা তো প্রায় চোখ বুজেই পৌঁছে গেলেন দাদার বাড়ির দোরগোড়ায়। দাদা বুড়ো হয়েছেন, বউদিও। কিন্তু স্বয়ং সলাজনয়নী দেবীকে সুটকেস হস্তে মজুত দেখে তাঁরা যেন আহ্লাদের চোটে খোকাখুকু হয়ে পড়লেন। ভাইপো-ভাইঝি, নাতিনাতনিদের মধ্যে উল্লাসের সাড়া পড়ে গেল—এ যে রিয়্যাল এ্যাডভেঞ্চার।
এদিকে বুচকুন, ইন্দিরা আর তাদের বাবার চক্ষে ঘুম নেই, অন্নে রুচি নেই। রান্নাবান্না করে ইসকুল করতে ইন্দুর বেশ স্ট্রেন হচ্ছে, বাবা এদিকে পরমেশ্বরের রান্না মোটেই খাবেন না। চিঠির পরে চিঠি যাচ্ছে মাথাভাঙ্গা, জবাব আসে না। শেষে মামাবাবুই লিখলেন—‘নয়ন এখন কিছুদিন এখানে থাকিবেক। উহার দেহ আগে আরও একটু সারিয়া উঠুক।’—শুনে বাবা আর থাকতে পারলেন না, সেইদিনই বুচকুনকে মাথাভাঙ্গায় পাঠালেন। পরের বাসেই। বুচকুন গিয়ে দ্যাখে মা’র শরীর দিব্যি ভালই আছে। বুচকুনকে দেখে মা লজ্জা-লজ্জা হেসে বললেন—‘এসেছিস? চল, যাই। এই দ্যাখ না, এরা কি যেতে দ্যায়?’— বুচকুনকেই কি ছেড়ে দিলেন তাঁরা? মামামামি? কি ভাইবোনেরা? অতএব বুচকুনও রইল।
এবারে ইন্দিরার চিঠি এল—‘মা, আমি আর পারছিনা, বাবার মেজাজ ভীষণ খারাপ, দিনরাত্রি রাগারাগি করছেন। পরমেশ্বরকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার বড্ডই খাটুনি পড়েছে। তোমরা কি ওখানেই থাকবে?’
বাবাই দোর খুললেন। মা লাজুক লাজুক মুখে অল্প হেসে প্রণাম করে বললেন—‘সব ভাল তো?’ বাবা জবাব দিলেন না। মা বললেন—‘ইন্দু কোথায়?’ যদিও জানেন ইন্দু তখন ইসকুলে। বাবা জবাব দিলেন না। মা ডাকলেন—‘পরমেশ্ব-র!’ এবার বাবা কথা বললেন—‘নেই।’ মা এটাও জানতেন।—‘কবে গেল?’ —‘অনেকদিন। এবারে আমিও যাব।’—তুমি কোথায় যাবে?’ —‘তা দিয়ে তোমার দরকার কী? তবে মাথাভাঙ্গাতে নিশ্চয় যাব না।’ মাথাভাঙ্গার পবিত্র নাম এমন অশ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হতে দেখে মা’র তক্ষুনি মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেল। শক্ত গলায় মা বললেন—‘যেখানেই যাও আমার সুটকেসটা নিয়ে যাওয়া হবে না।’ বাবা রহস্যময় হেসে উদাস সুরে বললেন—‘আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে সুটকেস লাগে না।’ এই কথাটিতে মা ঘাবড়ে গেলেন বলে মনে হল। ভিতু-ভিতু অপ্রস্তুত চোখে বাবার কাছে ঘেঁষটে এলেন—‘কোথায় যাবে গা? বলো না?’ বাবা সুরুত করে কিছুটা সরে গিয়ে মা’র নাগাল বাঁচিয়ে বললেন—‘রাস্তার কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে এলে হত না, সব ছোঁয়া-ন্যাপা করবার আগে?’ মা কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি কলঘরে চললেন।
রাত্রে খেতে বসে বাবা বললেন—‘কাল সকাল সকাল পুজোটুজো সেরে তৈরি হয়ে নেবে। আমার সঙ্গে কোর্টে যেতে হবে।’ মা’র হাতের রুটিটা হাতেই রইল, তাওয়ায় আর পড়ল না।
—‘কোর্টে? আমি? আমি কেন কোর্টে যাব? আমি বাপু সাক্ষী-টাক্ষি হতে পারব তোমাদের খুড়ো-ভাইপোর ব্যাপারে।’ জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বাবার কী একটা মামলা চলছিল বহুদিন। জ্যাঠামশাই মারা গেছেন, ছেলের সঙ্গে চলছে। বাবা বললেন—‘সে মামলা নয়। এ অন্য মামলা। ডিভোর্সের মামলা। তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে আর আমি তাই সইব ভেবেছ? আমি তোমাকে ডিভোর্স করব।’ অম্লান বদনে মা বললেন—‘তা করো না। তার জন্যে কোর্টে কেন যেতে হবে? ডিভোর্সটা বাড়িতেই হতে পারে।’
—‘তোমাকে এই সুখবরটি কে দিলেন শুনি? জাননা, ডিভোর্স মানে কী?’
—‘খুব জানি। ওই সই করে সাক্ষী ডেকে বিয়ে-ভাঙা তো? তা এ বাড়িতে কেন হবে না?
—‘বাড়িতে এইজন্যে হবে না যে এটা আইনগত ব্যাপার।’
—‘কেন? আইনের বিয়ে তো বাড়িতেই হয়! সে বুঝি দেখিনি? বদনাকে তো দিব্যি পুরুতমশাই বাড়িয়ে এসে সই করিয়ে বিয়ে দিয়ে গেলেন। ডিভোর্সের পুরুতমশাই ইচ্ছে করলেই বাড়িতে এসে…’
বাবা কাতরে ওঠেন—‘ডিভোর্সের পুরুত! আরে পুরুত নয়, পুরুত নয়, সে লোকটা ছিল গিয়ে রেজিস্ট্রার। কিন্তু ডিভোর্স তো রেজিস্ট্রারে করাতে পারে না, ওটা উকিলের কাজ।’
—‘অ! তা না হয় হল, উকিল বুঝি আর বাড়িতে আসে না? আসুক সে-উকিল বাড়িতে।’
—‘না না, ও হয় না। কোর্টে যেতে হয়। জজের সামনে সওয়াল করতে হবে না?’
—‘সওয়াল করার কী আছে। এ কি চোর দায়ে ধরা পড়েছে কেউ? যত বাজে কথা। বাড়িতেই হোক ডিভোর্স।’
—‘দ্যাখো বড়বউ, বাজে বকবক কোরো না তো মেলা! বলছি ওসব বাড়িতে হয় না।’ মা এবার একটু আদুরে গলায় বললেন—‘হ্যাঁগা, তা বাড়িতে যখন হবেই না, তবে কোর্ট-কাছারিতে কেন, তার চেয়ে বরং কালীবাড়ি গিয়ে ডিভোর্স করলে হয় না? ছোট খুকিরা তো কলকাতায় গিয়ে কালীবাড়িতেই নিজেরা বিয়ে করে নিয়েছে, অমনি কালীবাড়ির ডিভোর্সও নিশ্চয় হয় আজকাল? সে বরং ভাল।’
—‘ও হোঃ। এই গোমুখ্যুকে নিয়ে আমি কী করি, কোথায় যাই? বলি বিয়ে আর ডিভোর্স দুটো জিনিস কি এক হল?’
—‘হল না? গেরো বাঁধা আর গেরো খোলা। একটা হয়েছে ভগবান সাক্ষী রেখে, অন্যটার বেলায় শুধু হাকিম-মুতসুদ্দি হলেই চলবে? ভগবান চাই না? অমনি বললেই হল?’
—‘হা ভগবান! আমি আর কোনও কথা শুনতে চাইনে, কোর্টে কাল তোমায় যেতেই হবে বড়বউ। সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিয়ো, পুজো সারতে তিন ঘণ্টা লাগিয়ে দিয়ো না। ফার্স্ট আওয়ারেই পৌঁছুতে চাই।’
—‘কোর্ট-মোটে যেতে আমার বয়েই গেছে। কেন মরতে কোর্টে যাব? আমি এই পাষ্টাপষ্টি বলে দিলুম, উকিল যদি ঘরে আনতে পারো আমি ভালয় ভালয় ডিভোর্স হব, নইলে তুমি যত ইচ্ছে কোর্টে গিয়ে একা-একাই ডিভোর্স হওগে যাও। হুঁ!’
এবারে বাবা রীতিমতো হুংকার দিয়ে ওঠেন—‘বাঃ! একা-একা ডিভোর্স হওগে যাও! বলি—একা-একা কি বিয়েটা হয়েছিল, যে একা-একা ডিভোর্স হবে?’
—‘কেন তুমিই তো বললে এটা বিয়ের মতন নয়, অন্য ব্যাপার। আবার এখন কেন বলছ বিয়ের মতন?’ বাবা এবার আহতকণ্ঠে খেদোক্তি করলেন—‘আহ্ মেয়েমানুষদের মুখ্যু কি আর সাধে বলেছে? নির্বোধ? বোধ-বুদ্ধি কিস্যু নেই?’ আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে মেঝের ওপর ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—‘বেশ বেশ! মুখ্যু তো মুখ্যু! তা মুখ্যুকে নিয়ে ঘর করতেই বা কে বলেছে, ডিভোর্স করতেই বা কে বলেছে? আমি বলেছি? আমি এই চললুম মাথাভাঙ্গা। ব্যস। ইন্দু আমার সুটকেসটা দে তো মা।’
ঠিক এই সময়ে পড়ার ঘর থেকে বুচকুন চেঁচিয়ে উঠল—‘ব্যাপারটা এখন মুলতুবি থাকুক মা—এসব নতুন আইন তোমরা কেউই ঠিকমতন জানো না—আমার পরীক্ষাটা এ-মাসে হয়ে যাক, তারপর আমিই সব খোঁজখবর এনে দেব তোমাদের। কিচ্ছু ভাববেন না বাবা, আমিই সব বন্দোবস্ত করে দেব। মেজজামাইবাবুর কাছে সব আইনকানুনগুলো জেনে এলেই হবে কলকাতা থেকে। আপনারা কেবল বলে দেবেন সেজদি কোন পক্ষে সাক্ষী দেবে, আর আমি কোন পক্ষে। পরমেশ্বরটাকেও ডেকে আনা দরকার। কে জানে সে ব্যাটা কোন পক্ষে যাবে?’
—‘হুঁ যত্তো সব ইয়ে ছেলে হয়েছে আজকাল। সব কথায় কথা কওয়া চাই। সভ্যতা ভব্যতা কিছুই শেখাওনি তো ছেলেদের—যেমন মা, তেমনি ছেলে—’ বলতে বলতে বাবা উঠে পড়লেন, চটি ফটফটিয়ে কলে গেলেন আঁচাতে। মা বললেন—‘ঠিক আছে, এখনকার মতন থাকলুম। বুচকুনের পরীক্ষাটা আগে হয়ে যাক। কিন্তু এই বলে রাখছি, পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিনই আমি মাথাভাঙায় চলে যাব। সুটকেস আমার গোছানোই রয়েছে। হুঃ।’
বিলেত থেকে ফেরার পরে তিন মাসের মাথায় চন্দনের কাছে বাবার এই চিঠিটি এল—
নিরাপদ্দীর্ঘজীবেযু,
বাবা চন্দন, তোমার মাকে বিলাইতী সুটকেস উপহার দিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার খরচ ও অসুবিধা দুইটাই যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি করাইয়াছ। আর এক ঝামেলা করিয়াছে এই বাসরুট হইয়া। লাভের মধ্যে তোমার মা মাসের মধ্যে তিনবার সুটকেস গুছাইয়া বাসে চড়িয়া মাথাভাঙ্গায় গোসা করিতে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্রীমান বুচকুনকেও কলেজ কামাই করিয়া হপ্তায় হপ্তায় মাথাভাঙ্গায় ছুটিতে হইতেছে। খরচের কথা বাদই দাও। ইহাতে বুচকুনের পড়াশুনার যারপর নাই ক্ষতি হইতেছে। তাল বুঝিয়া পরমেশ্বর হতভাগা বাজারে দোহাত্তা চুরি করিতেছে। ইন্দুমায়ের স্কন্ধে রান্নাবান্না সংসারের পাট এবং চাকুরি, সমস্তই আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে ইন্দুর স্বাস্থ্য বেশ ভাঙিয়া যাইতেছে। এভাবে চলিলে আর কেই বা উহাকে বিবাহ করিবে? আমাদিগের নাওয়া-খাওয়া সকলই মাথায় উঠিয়াছে, প্রাণে স্বস্তি নাই। বাড়িতে অশান্তির সীমা নাই। চূড়ান্ত অনিয়ম সৃষ্টি হইয়াছে। ওই অলক্ষুণে সুটকেস আমদানি করিয়া সংসারে ঘুন ধরাইয়া দিয়াছ। আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, দুর্গাপূজার সময়ে আসিয়া তুমি অই বাহারী বিলাইতী সুটকেস অতি অবশ্যই ফিরাইয়া লইয়া যাইবা। ইহার কোনমতেই নড়চড় না হয়। (এই দু’লাইন লাল পেন্সিলে আনডারলাইন করা।)
আশা করি কর্মস্থলের এবং অন্যান্য সমস্তই কুশল। শ্রীভগবানের নিকটে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। ইতি ৯ই আশ্বিন, ১৩৮২
আঃ
শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ চক্রবর্তী
পুনশ্চ: সুবিধা থাকিলে বরং তোমার মায়ের জন্য একটি ছোট দেখিয়া লোহার আলমারি কিনিয়া দিয়া যাইও।
২৮.১২.১৯৭৫