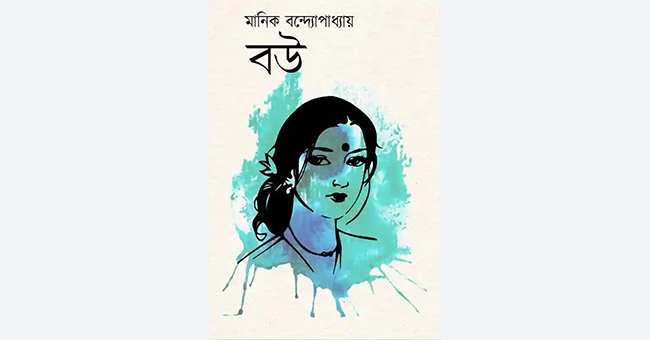১. দোকানির বউ
সরলার পায়ে সব সময় মল থাকে। মল বাজাইয়া হাঁটে সরলা,—ঝমর ঝমর! চুপিচুপি নিঃশব্দে হাঁটিবার দরকার হইলেও মল সরলা খুলিয়া ফেলে না, উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া শক্ত করিয়া পায়ের মাংসপেশিতে আটকাইয়া দেয়—মল আর বাজে না। প্রথম প্রথম শম্ভু এ খবর রাখিত না, ভাবিত বউ আশপাশে আসিয়া পৌঁছানোর আগে আসিবে মলের আওয়াজের সংকেত—পিছন হইতে মোটর আসিবার আগে যেমন হর্নের শব্দ আসে। ক’বার বিপদে পড়িয়া বউয়ের মলের উপর শম্ভুর নির্ভর টুটিয়া গিয়াছে।
ঘোষপাড়ার প্রধানতম পথটার ধারে একখানা বড় টিনের ঘরের সামনের খানিকটা অংশে বাঁশের মাচার উপর শম্ভুর দোকান। মাটির হাঁড়ি, গামলা, কেরোসিন কাঠের তক্তার চৌকো চৌকো খোপ, ছোটবড় বারকোশ, চটের বস্তা ইত্যাদি আধারে রক্ষিত জিনিসপত্রের মাঝখানে শম্ভুর বসিবার ও পয়সা রাখিবার ছোট চৌকি; হাত ও লোহার হাতা বাড়াইয়া এখানে বসিয়াই শম্ভু অধিকাংশ জিনিসের নাগাল পায়। পিছনে প্রায় এক মানুষ উঁচু পাঁচ সারি কাঠের তাক। সাবু, বার্লি ও দানাদার চিনি রাখিবার জন্য এক পাশে কাচ বসানো হলদে রঙের টিন, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি দামি মশলার নানা আকারের পত্র, লণ্ঠনের চিমনি, দেশলাইয়ের প্যাকেট, কাপড় কাচা গায়ে মাখা সাবান, জুতার কালি, লজেনচুস এবং মুদিখানা ও মনিহারি দোকানের আরো অনেক বিক্রেয় পদার্থের সমাবেশে তাকগুলি ঠাসা। তাকের তিন হাত পিছনে শম্ভুর শয়নঘরের মাটিলেপা চাঁচের বেড়ার দেয়াল। তাক আর এই দেয়ালের সমান্তরাল রক্ষণাবেক্ষণে যে সরু আবছা অন্ধকার গলিটুকুর সৃষ্টি হইয়াছে, শম্ভুর সেটা অন্দরে যাতায়াত করার পথ। সরলা বউ মানুষ, অন্দরেই তার থাকার কথা, কিন্তু সরলা মাঝে মাঝে করে কী, পায়ের মল উপরে ঠেলিয়া দিয়া চুপিচুপি তাকের জিনিসের ফাঁকে চোখ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, স্বামীর দোকানদারি দেখে এবং খদ্দেরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শোনে। বাড়িতে শম্ভু খুব নিরীহ শান্ত প্রকৃতির চুপচাপ মানুষ, কিন্তু দোকানে বসিয়া খদ্দেরের সঙ্গে তাকে কথা বলিতে ও হাসি-তামাশা করিতে দেখিয়া সরলা অবাক মানে। মানুষ বুঝিয়া এমন সব হাসির কথা বলে শম্ভু যে তাকের আড়ালে সরলার হাসি চাপিতে প্রাণ বাহির হইয়া যায়। ক্রেতারা যদি পুরুষ হয় তবেই শম্ভুর ব্যবহারে এরকম মজা লাগে সরলার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শম্ভুর দোকানে শুধু পুরুষেরাই জিনিস কিনিতে আসে না।
বেচাকেনা শেষ হওয়া পর্যন্ত সরলা অপেক্ষা করে, তারপর পায়ের মলগুলি আলগা করিয়া দেয় এবং মাটিতে লাথি মারার মতো জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া অন্দরে যায়। শম্ভুও ভিতরে আসে। একটু পরেই। দেখিতে পায় উনান নিবিয়া আছে, ভাত-ডালের হাঁড়ি গড়াগড়ি দিতেছে উঠানে, আর স্বয়ং সরলা গড়াইতেছে রোয়াকে। অন্য দুর্লক্ষণগুলি শম্ভু তেমন গুরুতর মনে করে না; ঘরে তিন পুরুষের পালঙ্কে প্রশস্ত সুখশয্যা থাকিতে রোয়াকে ছেঁড়া মাদুরে কালা, কানা, বোবা ও বিকৃতমুখী সরলাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াই সে কাবু হইয়া যায়। তারপর অনেকক্ষণ তাকে ওজন করিয়া কথা বলিতে ও সোহাগ জানাইতে হয়। একটা মানুষের একটু হাসা ও একটা মানুষকে একটু হাসানোর মধ্যে যে দোষের কিছুই নাই আর একটা মানুষ যে কেন তা বুঝিতে পারে না বলিয়া অনেক আপসোস করিতে হয়, আর অজস্র পরিমাণে খরচ করিতে হয় দোকানে বিক্রির জন্য রাখা লজেনচুস। সরলা একেবারে লজেনচুস খাওয়ার রাক্ষসী, তাও যদি কম দামি লজেনচুস খাইয়া তার সাধ মিটিত পয়সায় যে লজেনচুস শম্ভু দুটির বেশি বিক্রি করে না, কেউ চার পয়সার কিনিলেও একটি ফাউ দেয় না, সেইগুলি সরলার গোগ্রাসে গেলা চাই।
তারপর সরলার কানাত্ব কালাত্ব ও বোবাত্ব ঘোচে এবং রাগের আগুন নিবিয়া যায়। তবে একটা উদাস-উদাস অবহেলার ভাব, কথায় কথায় অভিমান করিয়া কাঁদো কাঁদো হওয়া, এ সমস্তের ওষুধ হিসাবে দরকার হয় একখানা শাড়ি, দামি নয়, সাধারণ একখানা শাড়ি, ডুরে হইলেই ভালো।
এক বছর মোটে দোকান করিয়াছে শম্ভু, এর মধ্যে এমনিভাবে এবং এই ধরনের অন্যভাবে সরলা সাতখানা শাড়ি আদায় করিয়াছে। সাধারণ কম দামি শাড়ি—ডুরে হইলেই ভালো।
.
তবু, বছরের শেষাশেষি চৈত্র মাসের কয়েক তারিখে, অকারণে শম্ভু তাকে আর একখানা ডুরে শাড়ি কিনিয়া দিল। বলিল অবশ্য যে ভালবাসিয়া দিয়াছে, একটু বাড়াবাড়ি রকমের ব্যগ্রতার সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকম স্পষ্ট করিয়াই বলিল, কিন্তু বিনা দোষে সাত বার জরিমানা আদায়কারিণী বউকে এরকম কেউ কি দেয়? যাই হোক, শাড়ি পাইয়া এত খুশি হইল সরলা যে আর এক দণ্ডও স্বামীর বাড়িতে থাকিতে পারিল না, বেড়ার ও পাশে শ্বশুরবাড়িতে গিয়া হাজির হইল। শম্ভুর বাড়িটা আসলে আস্ত একটা বাড়ি নয়, একটা বাড়ির এক টুকরা অংশ মাত্র,—তিন ভাগের এক ভাগ। দোকানঘর ও শয়নঘরে ভাগ করা বড় ঘরখানা, উত্তরের ভিটায় আর একখানা খুব ছোট ঘর, তার পাশে রান্নার একটি চালা আর শয়নঘরের কোণ হইতে রান্নার চালাটার কোণ পর্যন্ত মোটা শক্ত ডবল চাঁচের বেড়া দিয়া ভাগ করা তিনকোনা এক টুকরা উঠান। শম্ভুরা তিন ভাই কিনা, তাই বছরখানেক আগে এই রকমভাবে পৈতৃক বাড়িটা ভাগ করা হইয়াছে, বেড়ার এ পাশে শম্ভুর একভাগ এবং ও পাশে অন্য দু ভায়ের বাকি দু ভাগ। এ পাশে শম্ভু আর সরলা থাকে, ও পাশে একত্রে থাকে শম্ভুর দাদা দীননাথ ও ছোটভাই বৈদ্যনাথ, তাদের বউ আর ছেলেমেয়ে, শম্ভুর বিধবা মা আর মাসি এবং শম্ভুর দুটি বোন। এভাবে শুধু বউটিকে লইয়া বাড়ির উঠানে বেড়া দিয়া ভিন্ন হওয়ার জন্য শম্ভুকে ভয়ানক স্বার্থপর মনে হইলেও আসল কারণটা কিন্তু তা নয়। এক বছর আগে শম্ভু ছিল বেকার, সরলার দোকানদার বাবা বিষ্ণুচরণ তখন অবিকল এই রকমভাবে ভিন্ন হওয়ার শর্তে জামাইকে দোকান করার টাকা দিয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয়, স্বামীকে ভেড়া বানাইয়া নয়, বর্তমান সুখ ও স্বাধীনতাটুকু সরলা তার বাপের টাকাতেই কিনিয়াছে!
কী সুখ সরলার, কী স্বাধীনতা! বেড়ার ও পাশে যাদের কাছে সে ছিল একটা বেকার লোকের বউ, বেড়ার এ পাশে এখন তাদের শোনাইয়া ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া হাঁটিতে তার কী গর্ব, কী গৌরব! দোকানটা ভালোই চলিতেছে শম্ভুর, ওদের টানাটানির সংসারের তুলনায় তার কী সচ্ছলতা! একটু মুখভার করিলে তার ডুরে শাড়ি আসে, না করিলেও আসে।
সরলার পরনে নূতন ডুরে শাড়িখানা দেখিয়া বেড়ার ও পাশের অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করিল। তার মধ্যে সবচেয়ে কড়া হইল ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা বড় জা কালীর মন্তব্য। শীর্ণ মুখে ঈর্ষা বিকীর্ণ করিয়া বলিল, নাচনেউলি সেজে গুরুজনদের সামনে আসতে তোর লজ্জা করে না মেজো বউ? যা যা নাচ দেখিয়ে ভোলাগে যা স্বামীকে।
ছোট জা ক্ষেন্তির মাথায় একটু ছিট আছে কিন্তু ঈর্ষা নাই। সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, ঝমঝম যা মল বাজে সারা দিন, মেজদি নিশ্চয় দিনরাত্তির নাচে, দিদি। পান খাবে মেজদি?
হঠাৎ ভাসুরের আবির্ভাব ঘটায় লম্বা ঘোমটা টানিয়া সরলা একটু মাথা নাড়িল। দীননাথ গম্ভীর গলায় বলিল, মেজোবউ কেন এসেছে পুঁটি?
বিবাহের তিন মাসের মধ্যে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত কাঠির মতো সরু পুঁটি বলিল, এমনি।
এমনি আসবার দরকার!——বলিয়া দীননাথ সরিয়া গেল। সরলা ঘোমটা খুলিল এবং বৈদ্যনাথ আসিয়া পড়ায় ক্ষেন্তি টানিল ঘোমটা। বৈদ্যনাথ একটু রসিক মানুষ, শম্ভু কেবল দোকানে বসিয়া বাছা বাছা খদ্দেরের সঙ্গে রসিকতা করে, বৈদ্যনাথ সময়-অসময় মানুষ-অমানুষ বাছে না। সম্ভবত রাত্রে তার রসিকতায় চাপিয়া চাপিয়া হাসিতে হয় বলিয়া ক্ষেন্তির মাথায় যখন-তখন কারণে অকারণে খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠার ছিট দেখা দিয়াছে। সে আসিয়াই বলিল, মেজো বউঠান যে সেজেগুজে! কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, অ্যাঁ? ও পুঁটি, দে দে বসতে দে, ছুটে একটা দামি আসন নিয়ে আয় গে ছিনাথবাবুর বাড়ি থেকে।
এই রকম করে সকলে সরলার সঙ্গে। কেবল শম্ভুর মা বড় ঘরের দাওয়ার কোণে বসিয়া নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে মালা জপিয়া যায়; সরলা সামনে আসিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিলেও চাহিয়া দেখে না। সরলা পায়ে হাত দিতে গেলে শুধু বলে, নতুন কাপড় পরে ছুঁয়ো না বাছা।
সরলার দাঁতগুলি একটু বড় বড়। সাধারণত কোনো সময়েই সেগুলি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে না। কুড়ি মিনিট শ্বশুরবাড়ি কাটাইয়া বাড়ি ফেরার সময় দেখা গেল তার অধর ও ওষ্ঠে আজ নিবিড় মিলন হইয়াছে।
.
ভিন্ন হওয়ার আগে ওরা সরলাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিত। উঠানে বেড়া ওঠার আগে সরলা ছিল ভারি রোগা ও দুর্বল, কাজ করিত বেশি, খাইত কম, বকুনি শুনিয়া শুনিয়া ঝালাপালা কান দুটিতে শম্ভুও কখনো মিষ্টি কথা ঢালিত না।
এক বছর একা থাকিয়া সরলার শরীরটি হইয়াছে নিটোল, মনটি ভরিয়া উঠিয়াছে সুখ ও শান্তিতে। রানীর মতো আছে সরলা, রান্না ছাড়া কোনো কাজই একরকম তাকে করিতে হয় না, পাড়ার একটি দুঃখী বিধবা কাজগুলি করিয়া দিয়া যায়। দোকান করার জন্য তার বাবা যত টাকা শম্ভুকে দিবে বলিয়াছিল, সব এখনো দেয় নাই, অল্পে অল্পে দিয়া দোকানের উন্নতি করার সাহায্য করিতেছে। মাসে একবার করিয়া আসিয়া দোকানের মজুত মালপত্র ও বেচাকেনার হিসাব দেখিয়া যায়। প্রত্যেকবার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে ইতোমধ্যে শম্ভুর পত্নীপ্রেমে সাময়িক ভাটাও কখনো পড়িয়াছিল কি না। বড় সন্দেহপ্রবণ লোকটা, বড় অবিশ্বাসী, নয় তো মেয়ের আহ্লাদে গদগদ ভাব আর ডুরে শাড়ির বহন দেখিবার পর ও কথাটা আর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার চেষ্টা করিত না।
দুঃখ যদি সরলার কিছু থাকে সেটা তার এই পরম কল্যাণকর একা থাকিবার দুঃখ। বেড়ার ও ধারে অশান্তি-ভরা মস্ত সংসারটির কলরব দিনরাত্রি তার কানে আসে, ছোটবড় ঘটনাগুলির ঘটিয়া চলা এ বাড়িতে বসিয়াই সে অনুসরণ করিতে পারে; ছেলেমেয়েগুলি কখনো কাঁদে ক্ষুধায় আর কখনো কাঁদে মার খাইয়া, বড় জা কখনো কারণে অকারণে চেঁচায়, ছোট জা কখনো খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ধমক শোনে, ছোট দেবর কখনো কাকে খোঁচা দিয়া ঠাট্টা করে, কবে কে আত্মীয়স্বজন আসে যায়। বেড়ার এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সরলা স্থানে স্থানে কয়েক জোড়া ফুটা করিয়াছে, সরিয়া সরিয়া এই ফুটাগুলিতে চোখ পাতিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। ওই আবর্তের মধ্যে কিছুক্ষণ পাক খাইয়া আসিতে বড় ইচ্ছা হয় সরলার।
নিজের বাড়ি আসিয়া সে ডুরে শাড়ি ছাড়িল না, রান্নার আয়োজন করিল না; একবার শম্ভুর দোকানদারি দেখিয়া আসিয়া ছটফট করিতে লাগিল। বিকালে তার বাবা আসিবে, বাপের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে কি না তাই ভাবিতে লাগিল সরলা। কত কথা মনে আসে, আলস্যের প্রশ্রয়ে অবাধ্য মনে। শম্ভু বেকার ছিল তাই আগে সকলে তাকে দিত যন্ত্রণা, ভিন্ন হইয়া আছে বলিয়া এখন সকলে তার সঙ্গে ব্যবহার করে খারাপ। বেড়াটা ভাঙিয়া আবার ভাঙা বাড়ি দুটাকে এক করিয়া দিলে ওরা কি তাকে খাতির করিবে না? তার স্বামী এখন রোজগার করে, ভবিষ্যতে আরো অনেক বেশি করিবে, এই সমস্ত ভাবিয়া? তবে মুশকিল এই, এখন যদি দোকানের আয়ে ওরা ভাগ বসায় দোকানের উন্নতি হইবে না, এমন একদিন কখনো আসিবে না যেদিন লোহার সিন্দুকে টাকা রাখিতে হইবে শম্ভুকে। যত ডুরে শাড়ি সে আদায় করুক আর লজেনচুস খাক, দোকানের আয়ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব তো সরলা জানে। তিন পুরুষের পালঙ্কে গিয়া সে শুইয়া পড়ে। কত দিন পরে ও বাড়ির সকলের ভয় ভালবাসা ও সমীহ কিনিবার মতো অবস্থা তার হইবে হিসাব করিয়া উঠিতে না পারিয়া বড় কষ্ট হয় সরলার।
অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া অভ্যাস মতো সরলা একবার বেড়ার মাঝখানের ফুটায় চোখ পাতিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ও বাড়িতে বড় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া শম্ভু সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে শম্ভুকে সে বেড়ার ওদিকে দেখিতে পায়। এতে সরলা আশ্চর্য হয় না, সে পরের মেয়ে সে যখন যায়, শম্ভুও মাঝে মাঝে যাইবে বইকি! সরলার কাছে বিস্ময়কর মনে হয় শম্ভুর সঙ্গে সকলের ব্যবহার। ভিন্ন হওয়ার জন্য রাগ করা দূরে থাক কেউ যেন একটু বিরক্ত পর্যন্ত হয় নাই শম্ভুর উপর। বেড়া ডিঙানো মাত্র ও পাশের মানুষগুলির সঙ্গে শম্ভু যেন এক হইয়া মিশিয়া যায়, এতটুকু বাধা পায় না। পুঁটি এক গ্লাস জল আনিয়া দিল শম্ভুকে। সকলের সঙ্গে কী আলোচনা শম্ভু করিতেছে সরলা বুঝিতে পারিল না; মন দিয়া সকলে তার কথা শুনিতে লাগিল আর খুশি হইয়া কী যেন বলাবলি করিতে লাগিল নিজেদের মধ্যে। শম্ভু উঠিয়া আসিবার পরেও ওদের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। সরলা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, তার স্বামীর যোগ আছে অথচ তার জানা নাই এমন কী গুরুতর ব্যাপার থাকিতে পারে যে এত পরামর্শ দরকার হয়? জিজ্ঞাসা করিতে শম্ভু বলিল, ও কিছু না। জমিজমা ভাগবাটোয়ারার কথা হচ্ছিল। আমার ভাগটা বেচে ফেলব ভাবছি কি না।
কেন, বেচবে কেন?
শম্ভু মুখভার করিয়া বলিল, তুমি জান না, না? কবে থেকে বলছি তেল নুন বেচে লাভ নেই একদম, বাজারে একটা মনিহারি দোকান করব,—তাতে টাকা লাগবে না? কোথায় পাব টাকা, জমি না বেচলে?
সরলা বলিল, জমির থেকেও আয় তো হচ্ছে?
দোকানে বেশি হবে।
সরলা চিন্তিত হইয়া বলিল, কবে খুলবে বাজারে দোকান?
পয়লা বোশেখ খুলব ভাবছি, এখন আমার অদেষ্ট।
প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া মুখের সামনে তুড়ি দিল শম্ভু, মাথা নাড়িল, বাঁকা হইয়া বসিল। বলিল, তোমার বাবা বলেছিল সবসুদ্ধ ছ শ টাকা দেবে দোকান করতে, দোকান খোলার জন্যে এক শ দিয়ে বাকি টাকা আটকে দিলে। এক বছরে আর মোটে দু শ দিয়েচে তারপর—এমনি করলে দোকান চালাতে পারে মানুষ? দোকান করতেও একসঙ্গে টাকা চাই।
মনে মনে একটা জটিল হিসাব করিয়া সরলা বলিল, বাবা তো আসবে আজ, বাবাকে বলব?
শম্ভু বিষণ্ণ মুখে বলিল, বলে কী হবে? বিশ-ত্রিশ টাকার বেশি একসঙ্গে দেবে না।
আমি বললে নিয্যস দেবে, বলিয়া সরলা একগাল হাসিল।
তারপর বউকে লজেনচুস দিল শম্ভু, কালো গালে অদৃশ্য রঙ আনিল আর ফিসফিস করিয়া নিজের গোপন মতলবের কথা বলিতে লাগিল। মার হাতে কিছু টাকা আছে শম্ভুর, সব ছেলের চেয়ে শম্ভুকেই তার মা বেশি ভালবাসে তা তো জানে সরলা, ওই টাকাটা বাগানোর ফিকিরে আছে শম্ভু, নয়তো এত বেশি ও বাড়িতে যাওয়ার তার কী দরকার! বাজারে মস্ত দোকান খুলিবে শম্ভু, এবার আর দোকানদারি নয়, রীতিমতো ব্যবসাদারি, বাবাকে বাকি টাকাটা একসঙ্গে দিবার কথা বলিতে সরলা যেন না ভোলে। দুর্গা দুর্গা। না, এ বেলা আর রাঁধিবার দরকার নাই। ফলার-টলার করিলেই চলিবে। আহা, গরমে সরলার রাঁধিতে কষ্ট হইবে যে।
.
সরলা জানে হিসাবে ভুল হইতেছে, বাটখারা লাভের দিকে না-ঝুঁকিবার সম্ভাবনা আছে, তবু স্বামীর সঙ্গে আর বেশি দোকানদারি করা ভালো নয়। বাপের টাকায় স্বামীকে কিনিয়া রাখিয়াছে এক বছর, এবার তাকে মুক্তি দেওয়াই ভালো, তাতে যা হয় হইবে। একদিন তো নিজেকে কোনো রকম রক্ষাকবচ ছাড়াই স্বামীর হাতে সমর্পণ করিতে হইবে তার। তা ছাড়া এক বছর ধরিয়া স্বামী তাকে যেরকম ভালবাসিয়াছে সেটা শুধু নিজের মনের খুঁতখুঁতানির জন্য ফাঁকি মনে করা উচিত নয়। অবশ্য, পেটে যে সন্তানটা আসিয়াছে সেটা জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেই সবচেয়ে ভালো হইত, এতদিন একসঙ্গে বাস করিয়া সরলার কি আর জানিতে বাকি আছে নিজের ছেলের মুখ দেখিলে শম্ভুর পাকা শক্ত মনটা কীরকম কাঁচা আর নরম হইয়া যাইবে। তবে ছেলেটার জন্মিতে এখনো অনেক দেরি। তার আগে জমি বেচিয়া বাজারে মনিহারি দোকান খুলিয়া বসিলে শম্ভু ভাবিবে সব কীর্তি তার একার, কারো কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কিছু নাই। আগেকার কথা মনে করিয়া সরলা অবশ্য ভাবিয়া উঠিতে পারে না কৃতজ্ঞতার কতখানি দাম আছে শম্ভুর কাছে। বাজারে মনিহারি দোকান খুলিয়া দু-এক বছরের মধ্যে এমন অবস্থা যদি হয় শম্ভুর যে মাঝখানের বেড়াটা ভাঙিয়া সরলা নির্ভয়ে এবং সুখে-শান্তিতে, একরকম বাড়ির কর্ত্রীর মতোই সকলের সঙ্গে বাস করিতে পারে, হয়তো অকৃতজ্ঞ পাষাণের মতো শম্ভু নিজেই তাকে দাবাইয়া রাখিবে। তবু, ভবিষ্যতেও সে তার বশে থাকিতে পারে এরকম একটু সম্ভাবনা যখন দেখা গিয়াছে এবারে হাল ছাড়িয়া দেখাই ভালো যে কী হয়।
সরলার সন্দেহপ্রবণ অবিশ্বাসী বাবা মেয়ের অনুরোধ শুনিয়া প্রথমটা একটু ভড়কাইয়া গেল। একসঙ্গে তিন শ টাকা! জামাইকে আর একটি পয়সা না দিবার কথাই সে ভাবিতেছিল। দোকান যেমন চলিতেছে শম্ভুর, তাতে দুজন মানুষের খাইয়া পরিয়া থাকা চলে, বড়লোকের মতো না হোক গরিবের মতো চলে। জামাইকে বড়লোক করিয়া দিবার ভার তো সে গ্রহণ করে নাই। মোট ছ শ টাকা অবশ্য সে দিবে বলিয়াছিল, তবে সংসারে কত সময় মানুষ অমন কত কথা বলে, সব কি আর চোখকান বুজিয়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত, না তাই মানুষ পারে? অবস্থা বুঝিয়া করিতে হয় ব্যবস্থা। তা ছাড়া, বাজারে মনিহারি দোকান খোলার মতো দুর্বুদ্ধি যদি শম্ভু করিয়া থাকে—
কাঁদিয়া-কাটিয়া সরলা অনর্থ করিতে থাকে, কত কষ্টে বাপের কাছ হইতে টাকাটা সে আদায় করিয়া দিতেছে, শম্ভুকে তা বোঝানোর জন্য যতটা দরকার ছিল তার চেয়ে বেশি কাঁদাকাটা করে। দেবে বলেছিলে এখন দেবে না বলছ বাবা?—বলিতে বলিতে দুঃখে অভিমানে বুকটাই যেন ফাটিয়া যাইবে সরলার। একসঙ্গে তিন শ টাকা দেওয়া সরলার বাবার পক্ষে সহজ নয়, তবু একবেলা মেয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সে হার মানিল। ছেলে তার আছে তিনটা কিন্তু আর মেয়ে নাই। সরলা তার একমাত্র মা-মরা ছোট মেয়ে। কোথায় দোকান করিবে, কীরকম দোকান খুলিবে, কত টাকার জিনিস রাখিবে দোকানে আর কত টাকা পুঁজি রাখিবে হাতে, শম্ভুকে এসব অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সরলার বাবা গম্ভীর চিন্তিত মুখে বিদায় হইয়া গেল।
সরলা বলিল, দেখলে?
শম্ভু যথোচিতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইল। স্বামীদের যেভাবে স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ঠিক সে ভাবে নয়, নম্রভাবে, সবিনয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে। এই সময় বেড়ার ও পাশে হঠাৎ শোনা গেল, ছোটবউ ক্ষেন্তির খিলখিল হাসি। বেড়ার ফুটায় সে চোখ পাতিয়া ছিল নাকি এতক্ষণ, তাদের আলাপ শুনিতেছিল? রান্নার চালাটার পিছন দিয়া ঘুরিয়া সরলা চোখের নিমেষে ও বাড়িতে গিয়া হাজির হইল। বৈদ্যনাথ ক্ষেন্তি আর বাড়ির কুকুরটা ছাড়া উঠান নির্জন। উঠানের বেড়া আর ধানের মরাইটার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রসিক বৈদ্যনাথ স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা করিতেছিল।
সবাই কোথা গেছে লো ছোটবউ?
কাছে আসিয়া ক্ষেন্তি ফিসফিস করিয়া বলিল, ঘরে।
সেটা অসম্ভব। চৈত্রের দুপুরে ঘরের বাহিরে কড়া রোদ, গরম বাতাস। কিন্তু এদের দু জনের কি ঘর নাই? এখানে এরা কী করিতেছে এসময়? হাসাহাসি? নিজের বাড়িতে ফিরিয়া বারান্দা ছাড়িয়া এবার সরলা ও শম্ভু ঘরে গেল। তিন পুরুষের পুরোনো পালঙ্কে (ভিন্ন হওয়ার সময় ভাইদের কবল হইতে শম্ভু সেটা কী কৌশলে বাগাইয়াছিল আজো সরলা তাহা বুঝিতে পারে না) শুইয়া সরলা চোখ বুজিল, শম্ভু বসিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল তামাক। নিজেই তামাক সাজে কিনা শম্ভু, এত বেশি তামাক দেয় যে তামাক শেষ হইতে হইতে দুপুরে এবং রাত্রে দু বেলাই সরলার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আজ দেখা গেল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয় বাপের সঙ্গে সমস্ত সকালবেলাটা লড়াই করিয়া না হয় বৈদ্যনাথ ও ক্ষেন্তিকে ধানের মরাইয়ের আড়ালে রোদে দাঁড়াইয়া হাসাহাসি করিতে দেখিয়া সরলা বোধ হয় শান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।
.
দিন সাতেক পরে শম্ভু সকালবেলা সরলার বাবার কাছ হইতে টাকা আনিবার জন্য রওনা হইয়া গেল। গেল ও বাড়ি হইয়া। দোকানে নতুন মাল আনা সে কিছুদিন আগেই বন্ধ করিয়াছিল, অনেক জিনিস ফুরাইয়া গিয়াছে, অনেক খদ্দের ফিরিয়া যায়। মনিহারি দোকানে যেসব জিনিস রাখা চলিবে না, চাল ডাল মশলাপাতি, সেসব শেষ হইয়া যাওয়াই ভালো। তাই আজকাল একটা দিনের জন্যও দোকানটা সে বন্ধ রাখিতে চায় না। বৈদ্যনাথ আসিয়া দোকানে বসিবে। বেকার রসিক বৈদ্যনাথ। শম্ভুর যে ছোট ভাই এবং যে দুপুর রোদে উঠানে ধানের মরাইয়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া বউয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে। শম্ভু ও একদিন বেকার ছিল, বউও ছিল শম্ভুর ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার মতো হাড্ডিসার হোক, বউ বউ। ক্ষেন্তিই বা এমন কী রূপসি পরীর মতো? ওর মাথায় বরং ছিট আছে, এক বছর আগেকার সরলার মতো কম খাইয়া বেশি খাটিতে খাটিতেও কারণের চেয়ে অকারণেও বেশি খিলখিল করিয়া হাসে। বেকার অবস্থায় একবারও নয়, দোকানদার হওয়ার পর শম্ভুকে কয়েকবার হাসাহাসি করিতে দেখিয়াছে সরলা, কিন্তু সে অন্য একজনের সঙ্গে। তারপর শম্ভু বউকে কিনিয়া দিয়াছে ডুরে শাড়ি। অন্য অনেকের সঙ্গেই বৈদ্যনাথ হাসাহাসি করে, ক্ষেন্তিকে কিন্তু কখনো কিছু কিনিয়া দেয় না। কী করিয়া দিবে? পয়সা নাই যে! দু ভায়ের মধ্যে প্রভেদটা কী আশ্চর্যজনক! নামে নামে পর্যন্ত শুধু ‘নাথ’-এর মিল, ওটা বাদ দিলে একজন শম্ভু অন্যজন বৈদ্য!
মল না বাজাইয়া দোকানে তাকের আড়ালে দাঁড়াইয়া সরলা বৈদ্যনাথের অনভ্যস্ত দোকানদারি দেখে। মালপত্রের অভাবে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লক্ষ্মীছাড়া মনে হয় দোকানটা।
ক’দিন হইতে মনটা ভালো ছিল না সরলার, উঁচু দাঁত দুটি অনেক সময় ঢাকা পড়িয়া যাইতেছিল। পাকা দোকানির মেয়ে সে, কাঁচা দোকানির বউ, তার কেবল মনে হইতেছিল ভুল হইয়াছে, ভুল হইয়াছে, শুধু লোকসান নয়, একেবারে সে দেউলিয়া হইয়া যাইবে এবার। কিছুদিন হইতে কী রকম যেন হইয়া উঠিয়াছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার; সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তবু চোখকান বুজিয়া এই সব না-বোঝা অবস্থা ও ঘটনাগুলিকে পরিণতির দিকে চলিতে সাহায্য করিতেছে। আজকাল শম্ভু ঘন ঘন ও বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করিয়াছে, ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে, সেটা না হয় জমিজমার ভাগবাটোয়ারার জন্যই হইল, শম্ভুর সঙ্গে ও বাড়ির সকলের ব্যবহার? ও বাড়িতে কি শুধু দেবদেবী বাস করে যে, এক বছর ধরিয়া এমনভাবে ভিন্ন হইয়া থাকিয়া জমিজমার ভাগবাটোয়ারা করিতে গেলেও শম্ভুর সঙ্গে ওরা সকলে পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিবে? তা ছাড়া এখানকার দোকান তুলিয়া দিয়া বাজারে দোকান খুলিতেছে শম্ভু, সেজন্য ও বাড়িতে একটা উত্তেজনার প্রবাহ আসিবে কেন? ওদের কী আসিয়া যায়? বেড়ার ফুটায় চোখ রাখিয়া সরলা স্পষ্ট বুঝিতে পারে ও বাড়ির বয়স্ক মানুষগুলির কী যেন হইয়াছে, অদূরভবিষ্যতে বিবাহ উপনয়নের মতো বড় রকম একটা ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে বাড়ির লোকগুলি যেমন করে, ওরাও করিতেছে অবিকল তেমনই। হইতে পারে শম্ভুর বাজারে দোকান খোলার একই সময়ে ওদের সংসারেও একটা বড়ো ব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, তবে সেটা যে কী ব্যাপার তা সরলা জানিতে পারিতেছে না কেন? বেড়ার ও পাশে যা ঘটিবে, সকলে গোপন না করিলে সরলার কাছে তা তো গোপন থাকার কথা নয়। আর, সরলার কাছে সকলে যা গোপন করিবে, তার পক্ষে সেটা কি কখনো শুভকর হইতে পারে?
শুধু টাকা আদায়ের চেষ্টা করার বদলে বাপের সঙ্গে এসব বিষয়ে পরামর্শ না করার জন্য সরলার দুঃখ হয়। মেয়েমানুষ সে, এত লোকের ষড়যন্ত্র সে কি সামলাইয়া চলিতে পারে? চক্রান্তটা বুঝিতে পারিলেও বরং আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া দেখিত, একটা বুদ্ধি খাটানো চলিত। সে যে অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছে, স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। সে যে ঠিক করিয়াছে এবার হাল ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো। মেয়েমানুষ সে, বউ মানুষ সে, তার কি উচিত এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখা যাহাতে তার বিরুদ্ধে সকলের চুপিচুপি চক্রান্ত করিতে হয়?
দোকানে খদ্দের নাই দেখিয়া একসময় সে বৈদ্যনাথকে ভিতরে ডাকিল।
আচ্ছা ঠাকুরপো, ও তোমাদের বাড়ি গিয়ে কী সব বলত বল তো?
রসিক বৈদ্যনাথ বলিল, তা জান না মেজোবউঠান? তোমার নিন্দে করত—তুমি নাকি দাদার এক কান ধরে ওঠাও, আর এক কান ধরে বসাও। কানের ব্যথায়—
সরলা রাগিয়া বলিল, চাষার মতোন কথাবার্তা হয়েছে তোমার বাপু, এদিকে এক পয়সা রোজগার নাই, কথা শুনলে গা জ্বলে মানুষের। বিক্রির পয়সা থেকে আজ কত গাপ করবে তুমিই জান!
ক’দিন আগে ধানের মরাইয়ের আড়ালে বউয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করার পুরস্কার পাইয়া বৈদ্যনাথ দোকানে গিয়া বসিল। সরলা গালে হাত দিয়া রোয়াকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল ভবিষ্যতের কথা। বড় ভাই উকিলের মুহুরি, পাত্র নিজে একটা পাস দিবার দু ক্লাস নিচে পর্যন্ত পড়িয়া একটা আড়তে হিসাব লেখার কাজ করে, এত সব দেখিয়া তার বাবা শম্ভুর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়াছিল, তার দাঁত-উঁচু কালো মেয়েকে। নাই বা দিত? পাশের গাঁয়ের জগৎ নামে যে লোকটি জমি চাষ করিয়া খায় তার সঙ্গে দিলেই হইত? সে লোকটা এমনিই বশে থাকিত সরলার, আর অদৃষ্টে থাকিলে তাহাকে দিয়া আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি করিয়া এমন দিন হয়তো সে আনিতে পারিত যখন ডুরে শাড়িটি পরিয়া মল বাজাইয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইত, না করিত সংসারের কাজ, না শুনিত কারো বকুনি। দোকানদারের দাঁত-উঁচু কালো মেয়ের মুখ্যু চাষা স্বামীই ভালো। লেখাপড়া শিখিয়া পরের আড়তে যে কাজ করে আর পরের টাকায় দোকানি হয়, তার মতো পাজি বজ্জাত লোক
পরদিন অনেক বেলায় শম্ভু ফিরিয়া আসা মাত্র সরলা টের পাইল, যে লোকটা কাল বাড়ি ছাড়িয়া গিয়াছিল অবিকল সেই লোকটাই ফিরিয়া আসে নাই। গিয়াছিল দম আটকানো অবস্থায়, ফিরিয়া আসিয়াছে হাঁফ ছাড়িয়া। শম্ভু একবার একটা মামলায় পড়িয়াছিল, রায় প্রকাশের দিন সে যেমন অবস্থায় কোর্টে গিয়াছিল আর স্বপক্ষে রায় শুনিয়া যেমন অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া-আসা তার সঙ্গে মেলে।
টাকা পেলে? সরলা জিজ্ঞাসা করিল।
শম্ভু একগাল হাসিয়া বলিল, হাঁ পেয়েছি।
সব?
সব। পাখাটা কই? বাতাস কর না একটু।
সরলা হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, ওই যে পাখা বেড়ার গায়ে। হ্যাঁগো, দাদা কিছু বলল না এই টাকার ব্যাপার নিয়ে? বিয়ের সময় তোমাকে চার শ টাকা পণ দেওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে যে কাণ্ডটা বেধেছিল দাদার!
শম্ভুর মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল, কড়াদৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, ঘেমে-টেমে এলাম এই রোদে, পাখাটা পর্যন্ত এনে দিতে পার না তুমি হাতে? অন্য কেউ হলে বাতাস করত নিজে থেকে, বলতেও হত না।
সরলা হাসিয়া বলিল, ছোটবউ করে, ঠাকুরপো ওকে খুব হাসায় কিনা সেই জন্যে।
পাখাটা আনিয়া সরলা স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল বটে, বাতাসে শম্ভু কিন্তু ঠাণ্ডা হইল না। ভিতরে ভিতরে সে যে গরম হইয়াই আছে সেটা বুঝা যাইতে লাগিল তার মুখের ভাবে ও তাকানোর রকমে। সরলা আনমনে বলিতে লাগিল, আহা, আমার মাথার যত চুল তত বচ্ছর পরমায়ু হোক ছোটবউয়ের!
কেন?
কাল রাত্তিরে দুঃস্বপন দেখলাম যে। হাসতে হাসতে ছোটবউটা যেন মরে গেছে বুক ফেটে। আগুন লাগুক আমার পোড়া স্বপন দেখায়!
শম্ভু রাগিয়া বলিল, ইয়ার্কি জুড়েছ নাকি আমার সঙ্গে, অ্যাঁ? ভালো হবে না বলছি। ঘেমে-টেমে এলাম আমি—
বকুনি শুনিয়া সরলা অভিমান করিয়া পাখা ফেলিয়া বোয়াকে গিয়া ছেঁড়া মাদুরে শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া তেল মাখিতে মাখিতে শম্ভু বলিল, রাগ হল নাকি? রাগবার মতো কী তোমাকে বলেছি শুনি?
সরলা জবাব না দেওয়ায় গামছা কাঁধে সে স্নান করিতে চলিয়া গেল পুকুরে। চলন্ত স্বামীকে দেখিতে দেখিতে চৈত্রের রোদে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল সরলার! ডুরে শাড়ি নয়, লজেনচুস নয়, সোহাগ নয়, মিষ্টি কথা নয়, শুধু সে রাগ করিয়াছে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়া স্নান করিতে চলিয়া যাওয়া! একদিনে এমন অধঃপতন হইয়াছে শম্ভুর? কে জানে স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়া ডাল পোড়া-লাগার জন্য সরলাকে হয়তো আজ সে গালাগালি পর্যন্ত দিয়া বসিবে! সব কথা খুলিয়া বলিয়া বাবার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কী ভুলই সে করিয়াছে।
ডাল পোড়া-লাগার জন্য শম্ভু কিছু বলিল না, বরং মুখভার করিয়া না থাকার জন্য একবার অনুরোধই করিল সরলাকে। সরলা সজল সুরে বলিল, বকলে কেন? শম্ভু বলিল, না বকি নি। ঘেমে—টেমে এলাম কিনা—
খাওয়ার পর সরলাই আজ তাকে তামাক সাজিয়া দিল। সাজিয়া দিল, ফুঁ দিয়া তামাক ধরাইয়া দিল না। আয়নার সামনে সে অভিনয় করিয়া দেখিয়াছে যে ফুঁ দিবার সময় বড় বিশ্রী দেখায় তার মুখখানা। শম্ভু নিজেই তামাক ধরাইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত টানিতে আরম্ভ করিল। সরলা বলিল, ঠাকুরপো যা বিক্রি-সিক্রি করেছে, হিসাব নিয়ো।
শম্ভু বলিল, নেব।
সরলা বলিল, রাখালবাবুর বাড়ি আধমন চাল নিয়েছে, ছিনাথ উকিলের বাড়ি আড়াই সের মুগের ডাল, আড়াই পো মিছরি আর গায়ে মাখা একটা সাবান, তা ছাড়া খুচরো জিনিস অনেক বিক্রি হয়েছে। ভাঁড়ে করে ঠাকুরপো অনেকটা তেল বাড়ি নিয়ে গেছে কাল, আর আজ নিয়ে গেছে কতগুলো লেবেঞ্চুস, আর কীসের যেন একটা কৌটো, অত নামটাম জানি না বাপু আমি, জিজ্ঞেস কোরো।
শম্ভু বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবেখন।
তারপর একসময় সে ঘুমাইয়া পড়িল। সরলা একবার ও বাড়িতে গেল। কেহ তাহাকে আসিতেও বলে না, বসিতেও বলে না, তবে এতদিনে এটা তার সহ্য হইয়া গিয়াছে। বড় জা কালী শুইয়া আছে, ক্ষেন্তি সেলাই করিতেছে কাঁথা, বৈদ্যনাথ ঘুমে অচেতন। শাশুড়ি উবু হইয়া বসিয়া মালা জপিয়া চলিয়াছে, কাছে চুপচাপ বসিয়া আছে পুঁটি। ভাশুর এসময় কাজে যায়, নামমাত্র ঘোমটা দিয়া অনেকটা স্বাধীনভাবেই সরলা খানিকক্ষণ এ ঘরে খানিকক্ষণ ও ঘরে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। ক্ষেন্তির কাছেই সে বসিল বেশিক্ষণ। ফিসফিস করিয়া আবোল-তাবোল কতকগুলি কথা বলিল ক্ষেন্তি, একবার খিলখিল করিয়া হাসিল, আসল কথা একটিও আদায় করা গেল না তার কাছে। বাড়ি আসিয়া পালঙ্কে উঠিয়া সরলা বসিয়া রহিল। টাঙানো বাঁশে সাজানো জামাকাপড়গুলি জোর বাতাসে দুলিতেছে, ওর মধ্যে সরলার ডুরে শাড়ি দু খানাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশি। আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শম্ভুর ঘাড়ের কাছে লোমভরা মস্ত জন্মচিহ্নটি। কাত হইয়া শুইয়া আছে শম্ভু, চওড়া পিঠে শয্যায় বিছানো পাটির ছাপ। সরলা বিছানায় উঠিবার পর সে পাশ ফিরিয়াছে, সরলার দিকে নয়, ওদিকে। কে জানে এটা তার ভাগ্যেরই ইঙ্গিত কি না! এরকম কত ইঙ্গিত ভাগ্য মানুষকে আগেভাগে করিয়া রাখে। শম্ভুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে সোনারপুরে তার জন্য খুব ভালো একটি পাত্র দেখিতে বাহির হওয়ার সময় তার বাবা চৌকাঠে হোঁচট খাইয়াছিল, আগের বারের ছেলেটা তার পেটের মধ্যেই যেদিন মরিয়া গিয়াছিল তার আগের রাত্রে একটা প্যাচা ঘরের পিছনে আমগাছটায় ডাকিয়া ডাকিয়া ভয়ে তাহাকে আধমরা করিয়া দিয়াছিল। সরলা হঠাৎ শক্ত হইয়া যায়, লম্বাটে হইয়া যায় তার মুখখানা। বেড়ার গায়ে ঠিক এমনি সময় একটা টিকটিকিও যে ডাকিয়া উঠিল আজ? মাগো, না জানি কী আছে সরলার কপালে!
বিকালে ঘুম ভাঙিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আগের বারের সাজা তামাক টানার সুখটা মনে করিয়া শম্ভু বলিল, দাও না, এক ছিলিম তামাক সেজে দাও না।
সরলা বলিল, তুমি সেজে নাও।
শম্ভু গভীর উদারতা বোধ করিতেছিল, জেলখানার কয়েদি যেন নিজের বাড়িতে তিন পুরুষের পুরোনো পালঙ্কে প্রথম ঘুম দিয়া উঠিয়াছে। নিজেই তামাক সাজিয়ে সে গিয়া দোকান খুলিল, কাঠের ছোট চৌকিটিতে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল। পাড়ার দুঃখী মেয়েটি আসিয়া বাসন মাজিয়া রান্নাঘর লেপিয়া জল তুলিয়া দিয়া গেল। ও বাড়ির দুপুরের স্তব্ধতা ধীরে ধীরে ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। বেলা পড়িয়া গেল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সরলা গা ধুইল না, রান্নার আয়োজন করিল না, খানিকক্ষণ ছটফট করিতে লাগিল অন্দরে আর খানিকক্ষণ ফাঁকে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিল দোকানে তাকের আড়ালে। সন্ধ্যার পর দীননাথ কাজ হইতে ফিরিয়া বাড়ি ঢোকার আগে আসিল শম্ভুর দোকানে। উপস্থিত খদ্দেরটি চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিল, টাকা পেয়েছিস?
হাঁ, বাড়ি যান আমি যাচ্ছি।
এখানেই বসি না, বসে কথাবার্তা কই?
না, না, এখানে নয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি সব শোনে।
দীননাথ এ বগলের নথিপত্র ও বগলে চালান করিয়া বলিল, বাড়িতে ছেলেপিলেগুলো বড্ড জ্বালায়। বউমা এলে মলের আওয়াজে—?
সরলার মল যে সব সময় বাজে না এ কথা বুঝাইয়া বলিতে সে যে কেমন লোকের মেয়ে এ বিষয়ে একটা মন্তব্য করিয়া দীননাথ বাড়ি গেল। খানিক পরে দোকান বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া শম্ভু গেল অন্দরে। ত্রিকোণ উঠানের এক কোণে এক বছর আগে সরলার স্বহস্তে রোপিত তুলসীগাছটার তলায় শুধু একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে নিবুনিবু অবস্থায়, আর কোথাও আলো নাই। বেড়া ডিঙাইয়া ও বাড়ির আলো খানিকটা শোবার ঘরের চালে আসিয়া পড়িয়াছে! ঘরে গিয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া সরলা যে খাটে শুইয়া আছে শম্ভু তাহাও দেখিয়া লইল, একটা বিড়িও ধরাইয়া লইল। তারপর সরলাকে একবার ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেল ও বাড়িতে।
তখন উঠিয়া বসিল সরলা। এ বাড়িতে এক বছর রানীর মতো যে মল বাজাইয়া সে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে আজ প্রথম সেই মলগুলি খুলিয়া ফেলিল। এমন হালকা মনে হইতে লাগিল পা দুটিকে সরলার! লঘুপদে সে নামিয়া গেল উঠানে। বেড়ার ফুটায় চোখ দিয়া বুঝিতে পারিল ও বাড়ির একমাত্র কালি-পড়া লণ্ঠনটি জ্বলিতেছে বড় ঘরে এবং ও ঘরেই আসর বসিয়াছে তিন ভাইয়ের, দরজার কাছে বসিয়া আছে কালী আর ভিতরে তার শাশুড়ির শরীরটা রহিয়াছে আড়ালে, শুধু দেখা যাইতেছে মালা-জপ-রত হাত। রান্নার চালাটার পিছন দিয়া ঘুরিয়াই বেড়ার ওপাশে ও বাড়ির উঠানের একটা প্রান্ত পাওয়া যায়। সরলা সেদিকে গেল না, একেবারে নামিয়া গেল ও বাড়ির রান্নাঘর ও তার লাগাও ক্ষেন্তির ঘরের পিছনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে। কী অন্ধকার চারদিক। ভয়ে সরলার বুক ঢিপঢিপ করিতেছিল। ছিটাল পার হওয়ার সময়ে পায়ে একটা মাছের কাঁটা ফুটিল। কিন্তু কী করিবে সরলা? ভয় করা আর মাছের কাঁটা ফোটাকে গ্রাহ্য করিলে তার চলিবে কেন? একা মেয়েমানুষ সে, এতগুলি লোক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জুড়িয়াছে, রচনা করিতেছে ফাঁদ। কীসের ভয় এখন, কীসের কাঁটা ফোটা! আর যা হয় হোক, অন্ধকারে এভাবে বনে জঙ্গলে আর ছিটালে হাঁটার জন্য কিছু যেন তার নাগাল না পায়, পেটের ছেলেটা এবারো যেন তার মরিয়া না যায় জন্ম নেওয়ার আগেই। এলোচুলে সে ঘরের বাহির হয় নাই, একটি চুল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখে কামড় দিয়া তবে উঠানে নামিয়াছে, এই যা ভরসা সরলার
বড়ঘরের পিছনে কয়েকটা কলাগাছ আছে, ঘরের দুটো জানালাও আছে এদিকে। উঁচু ভিটার ঘর, জানালাগুলিও বেড়ার অনেক উঁচুতে। এত কষ্টে এখানে আসিয়া জানালার নাগাল না পাইয়া সরলার কান্না আসিতে লাগিল। তবে জানালার পাশে পাতা চৌকিতেই বোধ হয় তিন ভাই বসিয়াছে, ওদের কথাগুলি বেশ শোনা যায়, শুধু বোঝা যায় না পুঁটি কালী শাশুড়ি ওদের মন্তব্য। কান্না এবং ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা দেখিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া সরলা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।
শম্ভুর গলা : ক’বার তো বললাম, এই সোজা হিসেবটা তোর মাথায় ঢোকে না বদ্যি? আমার দোকানে যা মনিহারি জিনিস আছে তার দাম একশর বেশিই হবে, ধরলাম এক শ। মাল না কেনার জন্যে হাতে জমেছে এক শ দু-পাঁচ টাকা, ধরলাম এক শ। আর শ্বশুরমশায় দিয়েছে তিন শ। এই হল পাঁচ শ, আমার ভাগ। তুই আর দাদা পাঁচ শ করে দিলে হবে দেড় হাজার। হাজার টাকায় দোকান হবে; হাতে থাকবে পাঁচ শ।
হাসি চাপিতে ক্ষেন্তির মুখের কাপড় গোঁজার আওয়াজ। দীননাথের গলা : বউমা! বেহায়াপনা কোরো না বউমা।
কী জানিস শম্ভু, বড় বউয়ের সব গয়না বেচে আর কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমি না হয় পাঁচ শ দিলাম, বদ্যি অত টাকা কোথা পাবে? ছোটবউমার গয়না বেচলে তো অত টাকা হবে না।
বৈদ্যনাথের গলা : শ-তিনেক হয়তো ঢের। তবে আমার বিয়ের আংটি বেচলে—
শম্ভুর গলা : থাম বাপু তুই, সব সময় খালি ফাজলামি তোর।
দীননাথের গলা : যেমন স্বভাব হয়েছে তোর তেমনি স্বভাব হয়েছে ছোটবউমার।
শম্ভুর গলা : যাক, যাক। কাজের কথা হোক। বদ্যি তবে আড়াই শ দিক, লাভের আমরা যা ভাগ পাব ও পাবে তার অদ্দেক। ভাগাভাগির কথা বলছি এই জন্যে, আগে থেকে এসব কথা ঠিক করে না রাখলে পরে আবার হয়তো গোল বাধবে। যে যত দেবে তার তত ভাগ, বাস, সোজা কথা; সব গণ্ডগোল মিটে গেল।
একটু স্তব্ধতা। তারপর দীননাথের গলা : তবে আমিও একটা পষ্ট কথা বলি তোকে শম্ভু। তুই যে পাঁচ শ টাকা দিবি-
শম্ভুর গলা : পাঁচ শ নগদ নয়, এক শ টাকার জিনিস, চার শ নগদ।
দীননাথের গলা : বেশ। চার শই আমাদের একবার তুই দেখা। গয়নাগাঁটি বেচে ফেলবার পর শেষে যে তুই বলবি
শম্ভুর গলা (ক্রুব্ধ) : আমাকে বুঝি বিশ্বাস হয় না আপনার? ভাবছেন আমি ভাঁওতা দিয়ে-
চার-পাঁচটি গলার প্রতিবাদ। শম্ভুর গলা (আরো ক্রুদ্ধ) : সকলকে সমান সমান ভাগ দিতে চাচ্ছি কিনা তাই আমাকে অবিশ্বাস! আমি যেন একা গিয়ে দোকান করতে পারি না! পাঁচ শ টাকা নিয়ে যদি দোকান খুলি আমি, এক বছরে হাজার টাকা লাভ করব, না আসতে চাও তোমরা নাই আসবে! চাই না তোমাদের টাকা।
কোলাহল, কলহ, কড়া কথা, মধ্যস্থের গোলমাল থামানোর চেষ্টা খানিকক্ষণ বাজে ব্যক্তিগত কথা। আবার ঝগড়া বাধিবার উপক্রম।
তারপর শম্ভুর গলা : বেশ, কাল সকালে টাকা দেখাব।
দীননাথের গলা : গজেন স্যাকরার সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি, সাড়ে ঊনত্রিশ দর দেবে বলেছে। কাল কাজে না গিয়ে গয়নাগুলোর ব্যবস্থা করব। যা লোকসানটাই হবে! এমনি সোনা হয় আলাদা কথা, তৈরি গয়না বেচার মতো মহাপাপ আর নাই। বউমা বুঝি রাঁধে নি আজ? এখানেই তবে তুই খেয়ে যা শম্ভু। ও পুঁটি, ঠাঁই করে দে তো আমাদের।
.
বাসে টাকাগুলি রাখিয়াছিল শম্ভু, কোথায় যে গেল সে টাকা! টাকার শোকে এবং ও বাড়ির সকলের কাছে লজ্জায় শম্ভু পাগলের মতো চুল ছিঁড়িতে লাগিল।
সরলা সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, কী আর করবে বল? অদেষ্টের ওপর তো হাত নেই মানুষের! আমি ঘুমোচ্ছি, ঘরের দরজা খোলা, আর তুমি ও বাড়িতে গিয়ে বসে রইলে রাত দশটা পর্যন্ত! আর ওই তো বাকো! শাবলের এক চাড়েই হয় তো ভেঙে গেছে। আমারই বা কী ঘুম, একবার টের পেলাম না!
দু চোখে সন্দেহ ভরিয়া চাহিয়া শম্ভু বলিল, টের পেয়েছ কি না পেয়েছ-
সরলা তাড়াতাড়ি বলিল, এমন কোরো না লক্ষ্মী। যেমন দোকান করছিলে তেমনি কর এখন, বাবাকে বলে আর কিছু টাকা—
আর কী টাকা দেবে তোমার বাবা!
সহজে কি দেবে? আমি কাঁদাকাটা করলে—
ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া গিয়া সরলা স্বামীকে এক বাটি মুড়ি ও খানিকটা গুড় আনিয়া দিল। সস্নেহে বলিল, খাও। না খেলে কি টাকা ফিরে পাবে? বাবা টাকা যদি নাই দেয়,—দেবে ঠিক, যদির কথা বলছি—আমি গয়না বেচে তোমায় টাকা দেব।
২. কেরানির বউ
সরসীর মুখখানি তেমন সুশ্রী নয়! বোঁচা নাক, ঢেউ তোলা কপাল, ছোট ছোট কটা চোখ। গায়ের রং তার খুবই ফরসা, কিন্তু কেমন যেন পালিশ নাই। দেখিলে ভিজা স্যাঁতসেঁতে মেঝের কথা মনে পড়িয়া যায়।
সরসীর গড়ন কিন্তু চমৎকার। বাঙালি গৃহস্থ সংসারের মেয়ে, ডাল আর কুমড়ার ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইয়া যারা বড় হয়, একটা বিশেষ বয়সে মাত্র তাদের একটুখানি যৌবনের সঞ্চার হইয়া থাকে, বাকি সবটাই অসামঞ্জস্য। সে হিসাবে সরসী বাস্তবিকই অসাধারণ। তার শরীরের মতো শরীর সচরাচর চোখে পড়ে না। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কবিকে সে অনায়াসে মুগ্ধ করিতে পারে। একটু নিচুদরের ব্রহ্মচারীর মনে ঘোমটা খুলিয়া তার মুখখানি দেখিবার সাধ জাগা আশ্চর্য নয়।
ঘটনাটা নিছক মাতৃমূলক। সরসীর মার অনেক বয়স হইয়াছে, চল্লিশের কম নয়; কিন্তু এখনো তার শরীরের বাঁধুনি দেখিলে আপনার বিস্ময় বোধ হয় এবং তিনি লজ্জা পান।
তের বছর বয়সে সরসী টের পায় যে অহঙ্কার করার মতো গায়ের রং তো তার আছেই, কিন্তু আসল রূপ তার গায়ের রঙে নয়, অস্থিমাংসের বিন্যাসে। টের পাইবার পর সরসীর কাপড় পরার ভঙ্গি দেখিয়া সকলে অবাক!
‘ও কী লো? ও আবার কী ঢং?’
‘ঢং আবার কোথায় দেখলে?’
‘ও কী কাপড় পরার ছিরি তোর? সং সেজেছিস কেন?’
‘বেশ করেছি। তোমার কী?’
‘মুখে আগুন মেয়ের!… যাসনে, সং সেজে ঢং করে পাড়া বেড়াতে তুই যাসনে সরি! মেরে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব।’
পাড়া বেড়ানোর শখ সরসীর আপনা হইতেই গেল।
একদিন বাড়ি ফিরিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া তার কী কান্না!
‘কী হয়েছে লো?’
সরসী বলিতে পারে না। অনেক চেষ্টায় একটু আভাস দিল। বাকিটুকু মা জেরা করিয়া জানিয়া নিলেন।
জানিয়া মাথায় যেন তার বাজ পড়িল। এ কী সর্বনাশ! রাগের মাথায় মেয়ের পিঠেই গুম্ গুম্ করিয়া কয়েকটা কিল বসাইয়া দিলেন। বলিলেন, ‘সেইকালে বারণ করেছিলাম সারা দুপুর টো টো করে ঘুরে বেড়াসনে সরি, বেড়াসনে। হল তো এবার? মুখে চুনকালি না দিয়ে ছাড়বি, তুই কি সেই মেয়ে!’
সরসী খুব কাঁদিল। রাত্রে ভাত খাইল না। কারণ অভিমানে ভাবিতে লাগিল, মা আমাকেই মারল কেন? আমার কী দোষ?
সংসারের অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, কিন্তু এ ব্যাপারটা তার কাছে চূড়ান্ত রকমের রূঢ় ঠেকিল। তার কোনোই অপরাধ নাই, সুবলদার মতলব বুঝিতে পারা মাত্র তার হাতে কামড়াইয়া দিয়া পলাইয়া আসিয়াছে সে এত ভালো মেয়ে। তবু তাকেই মার খাইতে হইল। সকলের ভাব দেখিয়া বোঝা গেল সেই একটা অপকর্ম করিয়াছে, দোষ আগাগোড়া তারই!
সুবলের কী শাস্তি হয় দেখিবার জন্য সরসী ব্যগ্র হইয়া রহিল, কিন্তু সুবলের কিছুই হইল না। সুবলের বাবাকে ব্যাপারটা জানাইয়া দিবার পরামর্শ পর্যন্ত মার যুক্তিতর্কে বাতিল হইয়া গেল। সরসীর প্রতিই শাসনের অবধি রহিল না। আপনজন যে বাড়ি আসিল সকলের কাছে একবার করিয়া ব্যাপারটার ইতিহাস বলিয়া তাকে লজ্জা দেওয়া হইতে লাগিল। এ বাড়িতে দুজনকে চুপি চুপি কথা বলিতে দেখিলেই সরসী বুঝিতে পারে, তার কথাই আলোচিত হইতেছে। নিদারুণ কড়াকড়ির মধ্যে পড়িয়া কয়েক দিনের মধ্যেই সরসী হাঁপাইয়া উঠিল।
সময়ে শাসনও একটু শিথিল হইল, সরসীরও সহ্য হইয়া গেল, কিন্তু মনে মনে সে এমন ভীরু হইয়া পড়িল বলিবার নয়।
ছেলেবেলা হইতে চেনা ছেলেরা বাড়িতে আসিলে একা তাদের সঙ্গে কথা বলিতে সরসী ভয় করিতে লাগিল। লোকে দোষ দিবে, ভাবিবে, কী জানি মনে ওর কী আছে! একা পাশের বাড়ি যাওয়ার সাহস পর্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিল। দুপুরবেলা সে মার কাছে শুইয়া থাকে, ঘুম আসে না, অন্য ঘরে গিয়া একটু একা থাকিতে ইচ্ছা করে, তবু সে শুইয়া থাকে। কোথায় গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি বলে যে বাড়িতেই ছিল, পাশের ঘরে ছিল, কোথাও যায় নাই, মা হয়তো সে কথা বিশ্বাস করিবে না।
সংসারের আর সমস্ত মেয়ের মতো সে নয়, কুমারীধর্ম বজায় রাখার জন্য তার ওদের মতো যথেষ্ট ও প্রাণপণ চেষ্টা নাই; সকলের মনে এমনি একটা ধারণা জন্মিয়াছে জানিয়া সরসী দিবারাত্রি সজ্ঞানে নিজের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।
সকলের চুরি চুরি খেলার মধ্যে চুরি না করিয়াও বেচারা হইয়া রহিল চোর।
উপদেশ শুনিল : মেয়েমানুষের জীবনে আর কাজ কী মা? চাদ্দিকে পুরুষ গুণ্ডা হাঁ করে আছে, পা পিছলে না ওদের খপ্পরে পড়তে হয়,—ব্যস এইটুকু সামলে চলা।
ছড়া শুনিল : পুড়ল মেয়ে উড়ল ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই!
শুনিয়া শুনিয়া সরসীর ভয় বাড়িয়া গেল। সংসারের নারী-সংক্রান্ত নিয়মগুলি এখন সে মোটামুটি বুঝিতে পারে। ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে যে খারাপ হওয়াটাই প্রত্যেক মেয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; মেয়েদের খারাপ না হওয়াটাই আশ্চর্য। এই আশ্চর্য কাজটা করাই নারী-জীবনের একমাত্র তপস্যা।
সাবধানী হইতে হইতে সরসী ক্রমে ক্রমে অতি সাবধানী হইয়া গেল। ভালো হইয়া থাকাটা তার কাছে আর ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বিবেচনার অন্তর্গত হইয়া রহিল না। সকলে চায়, শুধু এই জন্যই নারীধর্ম পালন করিয়া যাওয়ার জন্য নিজেকে সে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া নিল।
তারপর, ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার কয়েক মাস আগে রাসবিহারীর সঙ্গে সরসীর বিবাহ হইয়া গেল।
.
বলা বাহুল্য, রাসবিহারী কেরানি।
বলা বাহুল্য এই জন্য যে সরসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে, বরাবর গাঁয়ে থাকার জন্য খানিকটা গেঁয়ো আর কথামালা পড়া বিদ্যায় লুকাইয়া নভেল পড়ার জন্য একটু শহুরে, অসামান্য অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য তার শুধু স্বাস্থ্য ভালো এবং গায়ের রঙের জন্য সে একটু মূল্যবতী। কেরানি ছাড়া এসব মেয়ের বর হয় না। রাসবিহারীর মাহিনা যে এখন একশর কাছে এবং একদিন দু-শর কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে, সে শুধু সরসীর ওই রংটুকুর কল্যাণে।
রাসবিহারীর সাইজ মাঝারি, চেহারা মাঝারি, বিদ্যা মাঝারি, বুদ্ধি মাঝারি। যাকে বলে মধ্যবর্তী, তাই। সরসীকে সে মাঝারি নিয়মে ভালবাসিল, কখনো মাথায় তুলিল, কখনো বুকে নিল, কখনো পায়ের নিচে চাপিয়া রাখিল। বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে রাগের মাথায় দুই-একবার চড়-চাপড়টা দিতে যেমন কসুর করিল না, ন-ভরি সোনার একছড়া হার এবং মধ্যে মধ্যে ভালো কাপড়ও তেমনি কিনিয়া দিল।
রাসবিহারী আর তার দাদা বনবিহারী এক বাড়িতেই বাস করিতেছিল। মাসের পয়লা তারিখে রাসবিহারী বরাবর মাহিনার চারের তিন অংশ দাদার হাতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে, বিবাহের বৎসর দুই পরে সেটা কমাইয়া কমাইয়া অর্ধেক করিয়া আনায় বনবিহারী তাকে পৃথক করিয়া দিল।
পটলডাঙ্গায় একটা বাড়ির দোতলায় একখানা শয়নঘর, একটি রান্নাঘর ও খানিকটা বারান্দা ভাড়া নিয়া রাসবিহারী উঠিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিল।
সরসীকে বলিল, ‘চালাতে পারবে তো?’
সরসী বলিল, ‘ওমা! তা আর পারব না?’
বলিয়া বিবাহের পর এই প্রথম হাসিমুখে যাচিয়া দুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্বামীকে চুম্বন করিল।
স্বাধীনতার, বেশি নয়, অল্প একটু স্বাধীনতার লোভে সরসীর খুশির সীমা ছিল না। স্বামী তো তাহার আপিস যাইবে? সে বাড়িতে থাকিবে,—একা! একেবারে একা! চাকরের চোখের সামনে কলতলায় স্নান করিলে কেহ তাকে গাল দিবে না, দুই বেলা পাশের বাড়ি গেলে কেহ জানিবে না, খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিলে আর রাস্তার অজানা, অচেনা, ভয়ঙ্কর ও রহস্যময় লোকদের নিজেকে দেখাইলে কেহ কিছু মনে করিতে আসিবে না।
বনবিহারীর স্ত্রী চারটি সন্তান প্রসব করিয়া আর অজস্র পানদোক্তা খাইয়া শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, রাসবিহারীর যাওয়ার দিন সে স্বামীকে বলিল, ‘যাই বল বাবু, বাঁচলাম।
এবং এক সময় রাসবিহারীকে একান্তে ডাকিয়া নিয়া বলিল :
‘তোমার ভালোর জন্যই বলা।’
রাসবিহারী কৌতূহল প্রকাশ করিলে এদিক-ওদিক চাহিয়া নিচু গলায় : ‘বউকে একটু সামলে চলো।’
‘কেন?’
‘কেমন যেন বাড়াবাড়ি। সেদিন রাখাল এসেছিল জান, নিচে আমি খাবার- টাবার করছি, বললাম, ও ছোটবউ, বাড়িতে একটা লোক এসেছে, দুটো কথাবার্তা বল গে, একা একা চুপ করে বসে থাকবে? তা ছোটবউ কী জবাব দিলে শুনবে? বললে, ‘পারব না দিদি, আমার লজ্জা করছে!’ আমার ভাইয়ের,— বয়েস এখনো ওর আঠার পোরে নি, ভগবান সাক্ষী, আমার ভাইয়ের কাছে ওর লজ্জা কী বল তো?’
রাসবিহারী বলিল, ‘কী জানি।’
‘অথচ আড়াল থেকে নুকিয়ে নুকিয়ে দেখার কামাই নেই! কী তাকানি, যেন গিলে খাবে!’
রাসবিহারী বলিল, ‘তা তোমার ভাইকে দেখলে দোষ কী?’
বনবিহারীর স্ত্রী একটু হাসিল। অনেক পানদোক্তা খাওয়ার জন্য মুখের হাসি পর্যন্ত তার ঝাঁজালো।
বলিল, ‘তারপর শোনো। এদিকে ছাতে কাপড়টি মেলে দিয়ে আসতে বললে যায় না, বলে, ‘চাদ্দিক থেকে তাকায় দিদি, আমি যাব না।’ আমি মরি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে, ভাবি, আহা ছেলেমানুষ, না যায় না যাক, পাড়ার লোকগুলোও তো পোড়ারমুখো নয় কম। ওমা, এদিকে দুপুরবেলা চোখ বুজিছি কি বুজি নি, অমনি তুডুক করে ছাতে গিয়ে হাজির!’
রাসবিহারী বলিল, ‘ছাতে গিয়ে কী করে?’
‘কে জানে বাবু কী করে। কে খোঁজ নিতে যায়? একদিন মাত্র দেখেছি, মাথার কাপড় ফেলে, চুল এলো করে মহারানী ঘুরে বেড়াচ্ছেন।’
‘চুল শুকোচ্ছিল হয়তো।’
‘হবে। কিন্তু নুকিয়ে যাবার দরকার! যাব না বলে শরমের কাঁদুনি গাইবার দরকার!’
সরসীর কৌতূহল প্রচণ্ড। বাড়ির কোথাও গোপনে কিছু ঘটিবার জো নাই। রাত্রে বনবিহারী কতক্ষণ হুঁকা টানে, বড়বউ তাকে কী বলে না বলে, কী নিয়া মধ্যে মধ্যে তাদের বচসা হয়, এসব খবরও সরসী অনেক রাখে। আড়ালে দাঁড়াইয়া বড়বউয়ের কথাগুলি শুনিতে সে বাকি রাখিল না। তখনকার মতো সরসী চুপ করিয়া রহিল। বড়বউ চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিলে বিনা আপত্তিতে চুল বাঁধিল, সিঁদুর পরানোর পর যথানিয়মে তাকে প্রণামও করিল। জিনিসপত্র অধিকাংশই সকালে সরানো হইয়াছিল, বিকালে গাড়ি ডাকিয়া বাকি জিনিস উঠাইয়া রাসবিহারী যখন শেষবারের মতো নিচে গিয়া তার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর করিয়া সরসী বড়বউকে বলিল, ‘সকালবেলা ওঁকে কী বলেছিলে দিদি?’
‘কাকে? ঠাকুরপোকে? কই, কিছু বলি নি তো!’
‘তোমার মুখে কুঠু হবে।’
‘কী বললি?’
‘বললাম তোমার মুখে কুঠ হবে। কুঠ কাকে বলে জান না? কুষ্ঠব্যাধি।’কার মুখে কুঠ হবে ভগবান দেখছেন। আমি তোর গুরুজন, আমাকে তুই—’
‘আ মরি মরি, কী গুরুজন। মুখে আগুন তোমার মতো গুরুজনের! বানিয়ে বানিয়ে কথা শুনিয়ে স্বামীর মন ভারি করে দিতে একটু বাধে না, তুমি আবার গুরুজন কিসের? পাবে পাবে, এর ফল তুমি পাবে। যে মুখে আমার নামে মিথ্যে করে লাগিয়েছ সে মুখে যদি পোকা না পড়ে তো চন্দ্র সূর্য আর উঠবে না দিদি, ভগবানের সৃষ্টি লোপ পেয়ে যাবে। আমি যদি সতী হই তো—’ ভাবাবেগে সরসী কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু বলিতে ছাড়িল না,— ‘আমি যদি সতী হই তো আমার যতটুকু অনিষ্ট তুমি করলে ভগবান তোমাকে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবেন। অঙ্গ তোমার খসে খসে পড়বে দিদি, পচে যাবে, গলে যাবে—ভাসুরঠাকুর দূর দূর করে তোমাকে বাড়ি থেকে দেবেন খেদিয়ে!’
সরসী যে এমন করিয়া বলিতে জানে বড়বউয়ের তা জানা ছিল না। হেলে সাপকে কেউটের মতো ফোঁস ফোঁস করিতে দেখিয়া সে এমন অবাক হইয়া গেল যে ভালোমতো একটা জবাবও দিতে পারিল না। চোখ মুছিয়া গাড়ি চাপিয়া সরসী বিজয়-গর্বে চলিয়া গেল। মুখ দিয়া উপরোক্ত কথাগুলি স্রোতের মতো অবাধে বাহির করিয়া দিতে পারিয়া নিজেকে তার খুব উচ্চশ্রেণীর আদর্শ স্ত্রী বলিয়া মনে হইতেছিল।
.
নূতন বাড়িতে আসিয়া সরসী সংসার গুছাইয়া বসিল। শোবার ঘরখানা রাস্তার ঠিক উপরে। রাস্তার ওপাশে সামনের বাড়ি হইতে ঘরের ভিতরটা সব দেখা যায়। জানালার আগাগোড়া সরসী পরদা টাঙাইয়া দিল। রাসবিহারীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল—’পরদা সরিয়ো না বাবু, ও বাড়ি থেকে দেখা যায়। ঘরটা একটু অন্ধকার হল, কী করব!’
রাসবিহারী ভাবিল, বড়বউয়ের কথাটা মিথ্যা নয়। সরসীর একটু বাড়াবাড়ি আছে।
কাল তারা হোটেলের ভাত আনিয়া খাইয়াছিল। ঘর গোছানো ও জানালায় পরদা টাঙানোর হিড়িকে এবেলাও সরসী রাঁধিতে পারে নাই। রাসবিহারীর আপিসের বেলা হইলে সরসী বলিল, হোটেলে খেয়ে তুমি আপিস চলে যাও, আমি এক ফাঁকে দুটি ভাতে ভাত ফুটিয়ে নেব।
রাসবিহারী মনে মনে বিরক্ত হইয়া জামা গায়ে দিল। ঘরের দেয়ালে একটু ফুটা থাকার আশঙ্কার কাছে স্বামীর খাওয়া চুলোয় যায়, সব সময় এ গভীর ভালবাসা হজম করা শক্ত।
তবু, বাহিরে যাওয়ার আগে রাসবিহারী বলিয়া গেল, ‘ছাতে উঠো না।’
সরসী বলিল, ‘না।’
বলিয়া তৎক্ষণাৎ আবার জিজ্ঞাসা করিল, ‘কিন্তু কাপড় শুকোতে দেব কোথায়?’
‘দিও, ছাতেই দিও। দিয়ে চট্ করে নেমে আসবে।’
‘আচ্ছা।’
এসব অপমান সরসীর গায়ে লাগে না। অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। খোলা ছাতের চারিদিকে প্রলোভন, চারিদিকে বিস্ময়, চারিদিকে রহস্য। স্বামী তো বারণ করিবেই। কিছু মন্দ ভাবিয়া নয়, তার মঙ্গলের জন্যই বারণ করা।
রাসবিহারী বাহির হইয়া যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে সরসী ছাতে উঠিল। ভাবিল, এক মিনিট, এক মিনিট শুধু চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আসব।
কিন্তু এক মিনিটে চোখ বুলানো যায় না।
ইটের স্তূপ জড়ো করিয়া মানুষ এই শহর গড়িয়াছে, চারিদিকে সীমাহীন সংখ্যাহীন মানুষের আস্তানা, কোনোদিকে শেষ নাই, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই, নীড়ে নীড়ে একটা বিস্ময়কর জমজমাট আলিঙ্গন, ছাতে ছাতে আলিসায় কার্নিশে একটা অবিশ্বাস্য মিলন। এই বিপুলতার বিস্ময় অনুভব করিতেই সরসীর আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, কোনো একটি বিশেষ বাড়িকে বিশেষভাবে দেখিবার অবসর এই সময়ের মধ্যে সে পাইল না, এ তো তার চেনা শহর, সে বাড়ির ছাত হইতে সকলকে লুকাইয়া,—না, সকলকে লুকাইয়া নয়, অত সাবধানতা সত্ত্বেও বড়বউ টের পাইয়াছিল, এই শহরকে সে দেখিয়াছে, কিন্তু নতুন বাড়ির নতুন ছাতে মাথার কাপড় পায়ের নিচের শুকনো শ্যাওলায় লুটাইয়া মলিন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নির্ভয় নিশ্চিন্ত পর্যবেক্ষণের সবটুকুই আজ অভিনব।
মাথার উপরে সূর্য আগুন ঢালিতেছে, ছাতের কোথায় এক টুকরা ভাঙা কাচ পড়িয়াছিল সরসীর পা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, কোমরে কোনোমতে কাপড় আঁটা আছে কিন্তু দেহের ঊর্ধ্বাংশ একেবারে অনাবৃত, সরসীর খেয়াল নাই। আকাশে একটা চিলের সকাতর চিৎকারে সরসী শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ে আজ তার আনন্দের উত্তেজনার বান ডাকিয়াছে, সে উন্মাদিনী। তার বহুদিনের দেয়াল- চাপা দুর্বল প্রাণে খোলা ছাতের এই সকরুণ দুঃসাহস, মানুষকে ভয় না-করার এই প্ৰথম সংক্ষিপ্ত উপলব্ধি বুকের চামড়ায় পিঠের চামড়ায় পৃথিবীর গরম বাতাস আর আকাশের রূঢ় রৌদ্র লাগানোর উগ্র ব্যাকুল উল্লাস তার সহ্য হইতেছে না। তার ইচ্ছা হইতেছে, অর্ধাঙ্গের কার্পাস তুলার বাঁধনটা টানিয়া খুলিয়া দূরে ছড়িয়া ফেলিয়া দেয়, দিয়া পাগলের মতো সমস্ত ছাতে খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করে।
আর চেঁচায়। গলা ফাটাইয়া প্রাণপণে চেঁচায়। সে যে ঘরের বউ, সে যে বোবা অসহায় ভীরু স্ত্রীলোক সব ভুলিয়া বুকে যত শব্দ সঞ্চিত হইয়া আছে সমস্ত বাহিরে ছড়াইয়া দেয়। অথবা আলিসা ডিঙাইয়া নিচে লাফাইয়া পড়ে।
হ্যাঁ, শূন্যে পড়িবার সময়টুকু উন্মত্ত উল্লাসে হাতপা ছুড়িতে ছুড়িতে প্রকাশ্য রাস্তার ধারে ওই শক্ত রোয়াকটিতে আছড়াইয়া পড়িলে ভালো হল। মাথাটা গুঁড়া হইয়া যাইবে কিন্তু শরীরের তার কিছু হইবে না। তার এই কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙে স্থানে স্থানে রক্ত লাগিবে। রাস্তার লোক ভিড় করিয়া তার অপরূপ দেহের অপূর্ব অপমৃত্যু চাহিয়া দেখিবে।
কোথায় লজ্জা, কোথায় সঙ্কোচ! কে জানিবে এই দেহের মধ্যে যে বাস করিতেছিল নিজেকে লুকাইয়া লুকাইয়া সে দিন কাটাইয়াছে, আঠার বছরের বালকের ভয়ে অবশ হইয়া গিয়াছে, স্বামী ভিন্ন জগতের আর একটি পুরুষের দিকে চোখ তুলিয়াও চাহিতে সাহস পায় নাই? কে অনুমান করিতে পারিবে সকলের সামনে আত্মোন্মোচনের তার আর দ্বিতীয় পথ ছিল না বলিয়া, আঘাতের ভয়, অপমৃত্যুর ভয়ের চেয়ে সকলের সামনে মরিবার ভয় প্রবলতর ছিল বলিয়া, সে এ কাজ করিতে পারিয়াছে? নিজের অনন্ত দুর্বলতার বিরুদ্ধে এ শুধু তার একটা তীব্র প্রতিবাদ, আপনার প্রতি তার এই শেষ প্রতিশোধ।
স্বামীর সাহায্য ছাড়া, সমাজের চাবুকের সাহায্য ছাড়া কোনোমতেই সে খাঁটি থাকিতে পারিত না, নিজেকে এমনি একটা কদর্য জীব বলিয়া চিনিয়াছিল, তাই সে নিজেকে এমন ভয়ানক মার মারিয়াছে, এ কথাটাও কি কারো একবার মনে হইবে না?
দুই হাত শক্ত করিয়া মুঠা করিয়া সরসী এখন আপন মনে বিড়বিড় করিতেছে, তার মুখের দুই কোণে সূক্ষ্ম ফেনা দেখা দিয়াছে। হঠাৎ একসময় হাঁটু ভাঙিয়া সে ছাতের উপর বসিয়া পড়িল। দুই করতল সজোরে ছাতে ঘষিতে ঘষিতে সে জোরে জোরে বলতে লাগিল—
‘বেশ, বেশ, বেশ! আমার খুশি! আমার খুশি আ-মা-র খু-শি!’
তারপর শূন্যের উপর ঝাঁজিয়া উঠিয়া শূন্যকেই সম্বোধন করিয়া আবার বলিল, ‘হল তো?’
তাকে ঘিরিয়া সমস্ত জগৎ কলরব করিতেছে, সমস্ত জগৎ একবাক্যে তাকে ছি ছি করিতেছে, তার কথা কেহ শুনিবে না, তার কোনো মুহূর্তের আত্মজয়ের দাম দিবে না, তাকে ঠাসিয়া চাপিয়া ধরিয়া থাকিয়া তারই ক’টা চামড়ার স্বেদে তারই যৌবনের উত্তাপে তাকে সিদ্ধ করিবে।
সরসীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। লুটানো আঁচল তুলিয়া নিজেকে সে আবৃত করিয়া নিল। ঘষিয়া ঘষিয়া চোখ শুষ্ক করিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া আলিসায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হিস্টিরিয়ার ফিটের পর যেমন সমস্ত জগৎ একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায়, মুখে একটা ধাতব স্বাদ লাগিয়া থাকে, সরসীর কানের কাছে তার নিজের রক্তের কোলাহল তেমনিভাবে অকস্মাৎ থামিয়া গিয়াছে, জিভে একটা কটু স্বাদ লাগিয়া আছে।
এখন আর তার কোনো উত্তেজনা নাই। সে একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তার মনে হইতেছে, এমন একটা কাজ সে করিয়া বসিয়াছে সাধারণ কোনো মেয়ে যা করে না। কাজটা তার ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।
রাসবিহারীর আদেশ অমান্য করিয়া ছাতে বেড়ানোর জন্য সরসীর কোনো আফসোস নাই, স্বামীর ছোটবড় অনেক আদেশই অমান্য করিতে হয়, নহিলে টেকা অসম্ভব, কিন্তু তারও অতিরিক্ত কিছু সে কি করিয়া বসে নাই? নিজেকে তবে কলুষিত অপবিত্র মনে হইতেছে কেন?
ভাবিতে ভাবিতে সরসী নিচে নামিয়া গেল। ছাতের নিচেকার ছায়ায় গিয়া দাঁড়ানো মাত্র তার যেন অর্ধেক গ্লানি কাটিয়া গেল। জানালার পরদা টাঙানোর জন্য ঘরের আলো স্তিমিত হইয়া আছে, বাতাসের মৃদু স্যাঁতসেঁতে ভাব এখনো শুকাইয়া যায় নাই, সরসীর চোখেমুখে আর সর্বাঙ্গে অল্প অল্প স্নিগ্ধতা সিঞ্চিত হইতে লাগিল।
ঘরের অসমাপ্ত কাজগুলি ঠিক যেন তারই প্রতীক্ষায় উন্মুক্ত হইয়া আছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সরসী চারিদিকে সস্নেহে দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল। কত কাজ তার, কত অফুরন্ত কর্তব্য! তার কি নিশ্বাস ফেলিবার সময় আছে? সংসারে কী হয় আর কী হয় না, তাই নিয়া মাথা ঘামানোর অবসর সে পাইবে কোথায়? স্বামী হোটেলে খাইয়া আপিসে গিয়াছে, এবেলার মধ্যে সমস্ত কাজ তার সারিয়া রাখিতে হইবে, ওবেলা দুটি রাঁধিয়া না দিলে চলিবে কেন? হোটেলের ভাতে পেট ভরানোর জন্য সে তো তাকে ভাত কাপড় দিয়া পুষিতেছে না।
সরসী অবিলম্বে কাজে ব্যাপৃত হইয়া গেল। নোড়া আনিয়া দেয়ালে পেরেক ঠুকিয়া কোনাকুনি একটা দড়ি টাঙাইয়া দিল, জড়ো করা পরনের কাপড়গুলি একটি একটি করিয়া কুঁচাইয়া রাখিল; তাকে খবরের কাগজ বিছাইয়া তেলের শিশি, জুতার বুরুশ, রাসবিহারীর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, তার নিজের মুখে মাখার পাউডার, পায়ে দেওয়ার আলতা, সিঁথিতে দেওয়ার সিঁদুর সমস্ত টুকিটাকি জিনিস গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল।
চুল বাঁধার যন্ত্রপাতিগুলি সাজাইয়া রাখার সময় একটু হাসিয়া ভাবিল, ও ফিরে আসার আগে চুল বাঁধার সময় পাব তো? খাবারটা করেই চট করে একটু সাবান মেখে গা ধুয়ে নিয়ে বেঁধে ফেলব চুলটা, যে নোংরাই দেখে গেছে।
চুলগুলি মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, দুই হাতে চুলের গোছা ধরিয়া খালি ঘরে একটা অনাবশ্যক অপচয়িত মনোরম ভঙ্গির সঙ্গে সরসী এলো-খোঁপা বাঁধিয়া নিল।
এবার কোন কাজটা আগে করিবে?
বাক্সগুলি ও-কোণে রাখা চলিবে না, এদিকে সরাইয়া আনিতে হইবে, জলের কুঁজোটা যেখানে আছে সেইখানে।
জলের কুঁজো! সরসীর দুচোখ চকচক করিয়া উঠিল। কী তৃষ্ণাই তার পাইয়াছে!
হাতের কাছে গেলাস ছিল, দেখিতে পাইল না। উবু হইয়া বসিয়া দুই হাতে কুঁজোটা তুলিয়া ধরিয়া সে গলায় জল ঢালিতে লাগিল। খানিক পেটে গেল, বাকিটাতে তার বুকের কাপড় ভিজিয়া গেল।
কী তৃষ্ণাই সরসীর পাইয়াছিল!
৩. সাহিত্যিকের বউ
সাহিত্যিক? শেষ পর্যন্ত একজন দেশপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সঙ্গেই তার বিবাহ হইবে নাকি?—এই বিস্ময় বিবাহের আগে কতদিন অমলাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে; মোটামুটি তিন মাস। কারণ, স্বনামধন্য সাহিত্যিক সূর্যকান্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হওয়ার মাস তিনেক পরেই শুভবিবাহটি সম্পন্ন হইয়াছিল।
ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত স্কুলে পড়িয়া তারপর বাড়িতে লেখাপড়া, গানবাজনা, সেলাই-ফোঁড়াই, সংসারের কাজকর্ম, ঝগড়াঝাঁটির কৌশল ইত্যাদি শিখিতে শিখিতে যেসব মেয়ে আত্মীয়স্বজনের সতর্ক পাহারা ও অসতর্ক রক্ষণাবেক্ষণে বড় হয়, অমলা তাদের একজন। অতএব বলাই বাহুল্য যে লাইব্রেরি মারফত বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে অমলার ভালোরকম পরিচয়ই ছিল। প্ৰথমে লুকাইয়া আরম্ভ করিয়া তারপর ঘরের কোণ আশ্রয় করার মতো বয়স হওয়ার পর হইতে প্রকাশ্যভাবেই সে সপ্তাহে চার-পাঁচখানা গল্প-উপন্যাসের বই ও মাসে তিন- চারখানা মাসিকপত্র নিয়মিতভাবে পড়িয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে, স্কুল ছাড়িবার পর বাড়িতে তার পড়াটা দাড়াইয়াছে এই এবং লেখাটা দাঁড়াইয়াছে চিঠি লেখা। সূর্যকান্তের লেখা পাঁচখানা উপন্যাস, তিনখানা গল্প সঞ্চয়ন ও একখানা নাটক সে তার সঙ্গে ভদ্রলোকের বিবাহের প্রস্তাব হওয়ার অনেক আগেই পড়িয়া ফেলিয়াছিল। তখন কী সে জানিত হৃদয়ের ভাবপ্রবণতাগুলিকে পরম উপভোগ্যভাবে উদবেলিত করিয়া রাখা, কখনো কাঁদানো কখনো- হাসানো এই কাহিনীগুলির জন্মদাতা একদিন স্বয়ং তিনটি বন্ধুর সঙ্গে তাকে দেখিতে আসিবে এবং দেখিয়া পছন্দ করিয়া যাইবে!
বড় খাপছাড়া মনে হইয়াছিল ব্যাপারটা অমলার। সাহিত্যিকরা, বিশেষত সূর্যকান্তের মতো সাহিত্যিকরা, কী রকম রামশ্যামের মতো জীবনসঙ্গিনী খুঁজিয়া নেয়? তার মতো পর্দানশিন সাধারণ মেয়েকে (সাধারণ মেয়ে অবশ্য সে নয় কিন্তু একদিন খানিকক্ষণ শুধু চোখে দেখিয়া, কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া, সেলাইয়ের কাজের একটু নমুনা দেখিয়া, আর একখানা গানের সিকি অংশ শুনিয়া তার কী পরিচয় ওরা পাইয়াছিল শুনি?) পছন্দ করে? এ জগতে পুরুষ ও নারীর প্রেম তো একরকম ওরাই ঘটায় এবং শেষ পর্যন্ত মিলন হোক আর বিচ্ছেদ হোক—ওদের ঘটানো প্রেমের অগ্রগতির কাহিনী পড়িতে পড়িতেই তো যতটুকু মন কেমন করা সম্ভব ততটুকু মন কেমন করে মানুষের? কয়েকটি ছোটগল্প ছাড়া সূর্যকান্তের কোন লেখাটি সে পড়িতে পারিয়াছিল যার মধ্যে দু-এক জোড়া নরনারীর জটিল সম্পর্ক তাকে দুশ্চিন্তা, আবেগ ও সহানুভূতিতে পরবর্তী বইখানা পড়িতে আরম্ভ করা পর্যন্ত অন্যমনা ও চঞ্চলা করিয়া রাখে নাই? সেই সূর্যকান্ত এ কী করিতে চলিয়াছে? একটা শ্বাসরোধী অসাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়া প্রথম পরিচয় এবং কতগুলি জটিল ও বিস্ময়কর অবস্থার মধ্যস্থতায় প্রেমের জন্ম হইয়া না হোক অন্ততপক্ষে জানাশোনা মেয়েদের মধ্যে একজনকে খুব সাধারণভাবেই একটু ভালবাসিয়া তারপর তাকে বিবাহ করা তো উচিত ছিল সূর্যকান্তের? তার বদলে একটা অজানা-অচেনা মেয়েকে সে গ্রহণ করিতেছে কোন যুক্তিতে? জীবনে এ অসামঞ্জস্য সে বরদাস্ত করিবে কী করিয়া। ওর বইগুলিতে কত স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসিতে পারে নাই, জীবনটা তাদের ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নিজের বেলাও সেরকম কিছু ঘটিতে পারে—এ ভয় সূর্যকান্তের নাই?
এসব গভীর সমস্যার কথা ভাবিবার সময় অমলা পাইয়াছিল তিন মাস। তিন মাসে উনিশ বছরের একটি মেয়ে যে কত চিন্তা আর কল্পনায় মনটা ঠাসিয়া ফেলিতে পারে, কত রোমাঞ্চকর রোমান্স অনুভব করিতে পারে, উনিশ বছরের মেয়েরাই তা জানে। একটা কথা অমলা বেশি করিয়া ভাবিত : প্রেম-সংক্রান্ত বিরাট ব্যাপার কিছু একটা যদি সূর্যকান্তের জীবনে নাই ঘটিয়া থাকে— সব বিষয়ে এমন গভীর ও নিখুঁত জ্ঞান সে পাইল কোথায়, আর ওরকম কিছু ঘটিয়া থাকিলে বিবাহে তার রুচি আসিল কোথা হইতে? কোনো সময় অমলার মনে হইত নিজের বুক ভাঙিবার রোমাঞ্চকর অপূর্ব ইতিহাস যদি সূর্যকান্ত ভুলিয়া গিয়া থাকে, এত দুর্বল যদি তার হৃদয়ের একনিষ্ঠতা হয় যে ইতোমধ্যে ভাঙা বুকটা আবার লাগিয়া গিয়া থাকে জোড়া, মানুষ হিসাবে লোকটা তবে কী অশ্রদ্ধেয়! ছি ছি, শেষ পর্যন্ত এমন একটা স্বামী তার অদৃষ্টে ছিল যে ভালবাসে, কিন্তু ভুলিয়া যায়? আবার অন্য সময় অমলার মনে হইত, সূর্যকান্তের হৃদয়ে হয়তো কখনো ভালবাসার ছাপ পড়ে নাই, আসলে লোকটা খুব জ্ঞানী আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া অন্য লোকের জীবনের ঘটনা ও মানসিক বিপর্যয় দেখিয়া শুনিয়া অনুমান ও কল্পনা করিয়া নরনারীর হৃদয়-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলি সে আহরণ করিয়াছে। ভালবাসিলে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি অনিবার্য, এ কথা জানে বলিয়াই বোধ হয় ভালো না বাসিয়া বিবাহ করাটা সে মনে করিয়াছে ভালো? তা যদি হয়, অমলা ভাবিত, তাতেও ওকে শ্রদ্ধা সে করিতে পারিবে না। দুঃখ পাইবে বলিয়া যে ভালবাসে না, সে আবার মানুষ না কি! একেবারে অপদার্থ জীব! আবার সময় সময় অমলার মনে হইত, নিজের ভালবাসার নির্মম পরিণতির স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছে না বলিয়া অসহ্য মনোবেদনার তাড়নাতেই সূর্যকান্ত এই খাপছাড়া কাণ্ডটা করিতেছে! অমলা কি জানে না ও রকম অবস্থায় কত লোকে কত কী অদ্ভুত কাণ্ড করে? কেউ মদ খাইয়া গোল্লায় যায় (সূর্যকান্তের ‘দিবাস্বপ্ন’, ‘ঘরের বাহিরে পথ’ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), কেউ সন্ন্যাসী হয়, কেউ হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ করিয়া যশ ও টাকা করে (নাম মনে নাই), কেউ আত্মহত্যা করে (মাগো!)। সূর্যকান্ত একটা বিবাহ করিবে তা আর বেশি কী? এই কথাগুলি ভাবিবার সময় ভাবী স্বামীর জন্য বড় মমতা হইত অমলার। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সে বলিত, আহা, আমি কি ওকে এতটুকু শান্তি দিতে পারব?
যত পরিবর্তনশীল এলোমেলো কল্পনাই মনে আসুক এ কথা কিন্তু অমলা কখনো ভুলিত না যে সাধারণ উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, চাকরে, ব্যবসাদার বা ওই ধরনের কারো সঙ্গে তার বিবাহ হইবে না, স্বামী সে পাইবে অসামান্য; দেশসুদ্ধ লোক যার নাম জানে, দেশসুদ্ধ লোক যার লেখা পড়িয়া হাসে কাঁদে।
প্রায় ত্রিশ বছর বয়স সূর্যকান্তের। ঠিক সুপুরুষ তাকে বলা যায় না, তবে চেহারায় একটা দুর্বোধ্য ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, একটা আশ্চর্য আকর্ষণ আছে। কথাবার্তা-চলাফেরায় সে খুব ধীর ও শান্ত—অনেকটা বৃহৎ সংসারের আকণ্ঠ- সংসারী বড়কর্তাদের মতো। কারো সঙ্গে কথা বলিবার সময় সে এমনভাবে নিরপেক্ষ নিরুত্তেজ হাসি হাসে যে মনে হয় আলাপি লোকটির মতো অসংখ্য লোকের সঙ্গে ইতোপূর্বেই তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে এবং যে কথাগুলি লোকটি বলিতেছে কতবার যে এসব কথা সে শুনিয়াছে তার সংখ্যা হয় না। কেবল মানুষ নয়, জগতে কিছুই যেন সূর্যকান্তের কাছে মৌলিক নয়, কিছুই তাকে আশ্চর্য করিতে পারে না, পুরোনো জুতার মতো হইয়া গিয়াছে— মানুষ, ঘটনা, বস্তু, বাস্তবতা, কল্পনা ও জীবনের খুঁটিনাটি; তার অভিজ্ঞতায় এমন বেমালুম খাপ খায় যে ফোসকা পড়া দূরে থাক অস্পষ্ট একটু মচমচ শব্দ পর্যন্ত যেন করে না। যা কিছু আছে জীবনে সমস্তের সমালোচনা করিয়া দাম কষা হইয়া গিয়েছে—আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যথা-বেদনা আনন্দ-উচ্ছ্বাস আবেগ-কল্পনা সমস্ত হইয়া আসিয়াছে নিয়ন্ত্রিত : নালিশও নাই, কৃতজ্ঞতাও নাই। বাহুল্যবর্জিত একটা আরাম বোধ করা ছাড়া বাঁচিয়া থাকার আর কোনো অর্থ সে যেন খুঁজিয়া পায় না। পাকা সাঁতারুর মতো সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সে সাঁতার কাটে জীবনসমুদ্রে, প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়িয়া ফেনিল আবর্ত সৃষ্টি করে না।
জীবনসমুদ্র? অমলা তো একেবারে থতোমতো খাইয়া গেল। এ যে গুমোটের দিঘি! এ কী শান্ত, ঠাণ্ডা মানুষ! ভাব কই, তীব্রতা কই, উচ্ছ্বাস কই? অন্যমনস্কতা, ছেলেমানুষি, খাপছাড়া চালচলন, রহস্যময় প্রকৃতির ছোটবড় অভিব্যক্তি—এসব কোথায় গেল? মানুষের মধ্যে সে যে একজন অত্যাশ্চর্য মানুষ—দিনে-রাত্রে কখনো একটিবারও এ পরিচয় সে দেয় না। সাধারণত মানুষের মধ্যেও বরং যতটুকু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, চরিত্রগত মৌলিকতা থাকে, তাও যেন তার নাই। তার অসাধারণত্ব যেন এই যে সাধারণ মানুষের চেয়েও সে সাধারণ। গম্ভীর নয়, বেশি কথাও বলে না। বেশভূষার দিকে বাড়াবাড়ি নজর নাই, অবহেলাও করে না। সুখসুবিধা যতখানি পাওয়ার কথা না পাইলে কারণ জানিতে চায়, বেশি পাইলে খুশি হয়, অতিরিক্ত উদারতাও দেখায় না, স্বার্থপরের মতো ব্যবহারও করে না। ক্ষুধা পাইলে খায়, ঘুম পাইলে ঘুমায়, রাগ হইলে রাগে, হাসি পাইলে হাসে, ব্যথা পাইলে ব্যথিত হয়, এই কী অমলার কল্পনার সেই আত্মভোলা রহস্যময় মানুষ? এসব সাধারণ ব্যাপারে শুধু নয়, বউয়ের সঙ্গে পর্যন্ত সে হাসে, গল্প করে, বউকে রাগাইয়া মজা দেখে, বউকে আদর করে, স্নেহ জানায়—একেবারে সহজ স্বাভাবিকভাবে, আর দশজন বাজে লোকের মতো, একটা অপূর্ব ও অসাধারণ সম্পর্ক তাদের মধ্যে যেন সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে না : আঙুলে আঙুলে ঠেকিলে দুজনের যাতে রোমাঞ্চ হয়, চোখে চোখে চাহিয়া মুহূর্তে তারা যাতে আবিষ্কার করিতে পারে পরস্পরের নব নব পরিচয়, যাতে শুধু অফুরন্ত শিহরন।
গোড়ার একদিনের কথা— যখন পর্যন্ত স্বামীর প্রকৃতির এরকম স্পষ্ট পরিচয় অমলা পায় নাই—অমলার মনে গাঁথা হইয়া আছে। বিকালে কোনো কাগজের বিপন্ন সম্পাদক জরুরি তাগিদ দিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার পর শোবার ঘরে সূর্যকান্ত লিখিতে বসিয়াছিল গল্প। বাড়িতে অনেক লোক : বিবাহ উপলক্ষে আসিয়া অনেক আত্মীয়স্বজন তখনো ফিরিয়া যায় নাই! কত যে বাধা পড়িতে লাগিল লেখায় বলা যায় না। এ অকারণে ডাকে, সে কী দরকারি কথা জিজ্ঞাসা করে, ছেলেরা হট্টগোল করে ঘরের সামনে বারান্দায়, রান্নাঘরে ডাল সম্ভার দিবার সময় হাঁচিতে হাঁচিতে বেদম হইয়া আসে সূর্যকান্ত। ঘরে আসিয়া দেখিয়া যাইতে না পারিলেও অমলা টের পাইয়াছিল স্বামী তার লিখিতে বসিয়াছে। ঘরে গিয়া স্বনামধন্য লেখক সূর্যকান্তকে প্রথমবার লিখনরত অবস্থায় দেখিবার জন্য মনটা ছটফট করিতেছিল অমলার এবং এ কথা ভাবিয়া মনটা তার ক্ষোভে ভরিয়া গিয়াছিল যে এই হাঁকাহাঁকি গণ্ডগোলের মধ্যে এক লাইনও সে কি লিখিতে পারিতেছে? বাড়ির লোকের কি এটুকু কাণ্ডজ্ঞান নাই? তার যদি অধিকার থাকিত, সকলকে ধমকাইয়া সে আর কিছু রাখিত না। সূর্যকান্ত লিখিতে বসিলে সমস্ত বাড়িটা তো হইয়া যাইবে স্তব্ধ—পা টিপিয়া হাঁটিবে সকলে, কথা বলিবে ফিসফিস করিয়া, ডালে সম্ভার পর্যন্ত দেওয়া হইবে না। তা নয়, আজই যেন গোলমাল বাড়িয়া গিয়াছে বাড়িতে-এ কী অবিবেচনা সকলের, ছি!
রাত সাড়ে দশটার সময় সে যখন ঘরে গেল, সূর্যকান্ত তখনো লিখিতেছে। টেবিলে সাত-আটখানা লেখা কাগজ দেখিয়া অমলা অবাক হইয়া গিয়াছিল। অত বাধা ও গোলমালের মধ্যেও সূর্যকান্ত তবে লিখিতে পারে? তা ছাড়া, কত সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া সে ঘরে আসিয়াছে, লিখিতে লিখিতে তবু তো সে টের পাইল! এবার সূর্যকান্তের বিরুদ্ধেই অমলার মনটা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।
বাস্, আজ এই পর্যন্ত, বলিয়া কলম রাখিয়া দু হাত উঁচু করিয়া বিশ্রী ভঙ্গিতে তুলিয়াছিল হাই। তারপর হাসিমুখে কাছে ডাকিয়াছিল অমলাকে। বিষণ্নমুখে অমলা গিয়া টেবিল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিয়াছিল, আচ্ছা আপনি কী করে লেখেন?
গলার আওয়াজে তার কৌতূহল ছিল এত কম, আর বলার ভঙ্গিতে ছিল এত বেশি অবহেলা—যে মনে হইয়াছিল সে বুঝি জিজ্ঞাসা করিতেছে সূর্যকান্তের মতো লোক যে লিখিতে পারে এটা সম্ভব হইল কী করিয়া? সূর্যকান্ত বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা বলা যায় না, চেয়ার ঘুরাইয়া বসিয়া সে ধরিয়াছিল অমলার একখানা হাত, তারপর তাকেও বসাইয়াছিল নিজের চেয়ারে। সাহিত্যিক বলিয়া অবশ্য নয়, নতুন বউ টেবিল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ওরকম একটা প্রশ্ন করিলে প্রথম নিঃশব্দ জবাবটা এভাবে না দিয়া কোনো স্বামী পারে? তারপর একটু হাসিয়াছিল সূর্যকান্ত, বলিয়াছিল, তুমি যেমন করে লেখ ঠিক তেমনি করে, কাগজের ওপর কলম দিয়ে। কিন্তু অমলারানী, আর কতদিন আমায় আপনি বলবে?
অমলা অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিল, বারণ তো করো নি আগে।
কেন করি নি জান? তুমি নিজে থেকে বল কিনা দেখছিলাম। কেন বল নি বল তো?
লজ্জা করে না বুঝি? অভিমান হয় না বুঝি?
যে অধিকার হইতে স্বামী তাকে এক সপ্তাহ বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, অধিকার পাওয়ামাত্র লজ্জাও থাকে নাই অমলার, অভিমানও থাকে নাই। সে ভাবিতেছিল, ঠিক দিয়েছি তো জবাবটা? এমন অবস্থায় এরকম জবাব তো দিতে হয়? না, আর কিছু বললে ভালো হত? আচ্ছা, এ কথা বলব, তুমি কী বুঝবে তোমাকে তুমি বলতে বল নি বলে কী গভীর ব্যথা লেগেছিল আমার মনে? মুখের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে! আর কিছু না বলে মুখ নিচু করাই বোধ হয় ভালো এবার।
সূর্যকান্ত সত্যসত্যই কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অমলার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, মুখের মৃদু লালিমার মধ্যে সে যেন পরিমাণ করিতে চাহিয়াছিল তার লজ্জা ও অভিমানের। বই লিখিবার সময় যত বড় মনস্তত্ত্ববিদ হোক সূর্যকান্ত, অমলাকে সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। স্বামীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি ভাব জমানোর জন্য অমলার ঔৎসুক্য তার কাছে অল্পে অল্পে ধরা পড়িতেছিল বটে, কিন্তু ভাব জমানোটাই যে তার অধীরতার কারণ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নয়—তাও বেশ বোঝা যাইতেছিল। ঠিক ভাবপ্রবণতা যেন নয়, কী যেন অমলা জানিতে ও বুঝিতে চায় তার সম্বন্ধে, সব সময়ে কী যেন একটা বিস্ময়কর কিছু সে প্রত্যাশা করে তার কাছে। এমন নাটকীয় ধরনে কথা বলে অমলা! কথার পিছনে প্রকৃত নাটত থাকে না অথচ একেবারেই। হৃদয়াবেগ ও মস্তিষ্ক মিশিয়া যেন তৈরি হয় তার ব্যবহার ও মুখের শব্দগুলি। কাঁচাপাকা আমের মতো নতুন বউকে সূর্যকান্তের লাগিতেছে মিষ্টি আর টক। তার দোষ ছিল না, ওইরকম ব্যবহারই করিতেছিল অমলা! তিন মাস ধরিয়া তপস্যার মতো সে যে ভাবিয়াছে কী, কী কারণে সূর্যকান্তের মতো লোক তার মতো মেয়েকে এমন সাধারণভাবে বিবাহ করে, এখন বিবাহের পর সে জানিবার চেষ্টা করিবে না সেই কারণগুলির মধ্যে কোনটা তার স্বামীর বেলা প্রযোজ্য? তিন মাসের গভীর গবেষণা তার বিফলে যাইবে?
তবে ও বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের ইচ্ছাটা তার ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছিল। তার মনে হইতেছিল, অতীত জীবনে যত বিপর্যয় সূর্যকান্তের হৃদয়ে ঘটিয়া থাক, সে কথা আজ না ভাবাই ভালো। তাকে লইয়া একটা নতুন অধ্যায় আরম্ভ হোক সূর্যকান্তের জীবনে। আপনা হইতে সে তুমি বলিতে আরম্ভ করে কিনা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল সূর্যকান্ত! হয়তো আপনা হইতে সে তাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে কিনা দেখিবার জন্যও সে অপেক্ষা করিয়া আছে? হায় অমলার অবোধ স্বামী! এত বড় সাহিত্যিক তুমি, তোমাকে ভালো না বাসিয়া কি অমলা পারে? এইসব ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে অমলা নিজেকে ও স্বামীকে মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল সূর্যকান্তেরই একখানা বইয়ের এক জোড়া নবদম্পতির মতো। যদিও বইয়ের ওরা দুজনে, শঙ্কর ও সরযূ, প্রায় তিন বছর ধরিয়া অনেক ভুল-বোঝা, কলহ-বিবাদ ও বাধা-বিপত্তির পর একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে নবদম্পতি হইয়াছিল, কিন্তু তাতে কী আসিয়া যায়? তেমন বৈচিত্র্যময় তিনটা বছর কাটাইবার পর তাদেরও মিলন হইয়াছে এটা কল্পনা করা এমন কী কঠিন? অন্তত সূর্যকান্তের পক্ষে একটুও কঠিন নয়—সেই তো লিখিয়াছে বইটা।
অমলা (এখন সরযূ) তাই ধীরে ধীরে গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল সূর্যকান্তের (এখন শঙ্কর), ‘স্মৃতির কাতরতা মেশানো অবর্ণনীয় পুলকের স্বপ্ন’ ঘনাইয়া আসিয়াছিল তার দুটি অর্ধনিমীলিত চোখে, ‘তিন বছর যে কণ্ঠস্বরে লুকানো ছিল গোপন অশ্রুর সজল সুর তাতে প্রথম মোহকরী আনন্দের আভাস মিশিলে যেমন শোনায়’ তেমনই কণ্ঠস্বরে সে বলিয়াছিল – হ্যাঁ গো, তুমি কি কখনো ভাবতে পেরেছিলে তুমি আর আমি কোনোদিন এত কাছাকাছি আসতে পারব?
যেসব গহনা দাবি করা হইয়াছিল বিবাহের সময়, আজ অমলার হাতে তার অতিরিক্ত একজোড়া ব্রেসলেট ছিল। সূর্যকান্ত জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল ও গহনাটি কে দিয়েছে। অবাক হইয়া সে বলিয়াছিল, তার মানে?
অমলা বলিয়াছিল, আমার মনে হচ্ছে কতকাল যেন ভাগ্য আমাদের জোর করে তফাত করে রেখেছিল। আরো দু-এক বছর দেরি করে যদি আমাদের বিয়ে হত, তা হলে হয়তো আমি—
সূর্যকান্তের মুখ দেখিয়া অমলা থামিয়া গিয়াছিল। এ তো অভিমান নয়, সত্যই বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতেছিল তার, আবেগে সে নিশ্বাস ফেলিতেছিল ছোট ছোট। মধ্যবিত্ত সংসারের অনভিজ্ঞ, কোমলমনা, ছেলেমানুষ মেয়ে, জীবনে প্রথমবার একজনের সঙ্গে পাকা প্রেমিকের মতো ব্যবহার করিতে গেলে বইপড়া বিদ্যায় কুলাইবে কেন! আবেগ, উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস ও হঠাৎ একেবারে জন্মের মতো কথা বন্ধ করিয়া সূর্যকান্তের বুকে মুখ লুকাইয়া ফেলিতে যাওয়ার মতো যে গভীর লজ্জা এখন অমলার আসিয়াছিল, তার কোনোটাই বানানো নয়।
সূর্যকান্ত ভ্রু-কঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিল, তোমার বয়স কত বল তো?
উনিশ বছর।
বিয়ের আগে শুনেছিলাম ষোল চলছে। তোমার নাকি বাড়ন্ত গড়ন।
এ কী অচিন্তিত আঘাত! আশ্বিনের রাত্রি, আকাশে হয়তো জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি—পরশু সন্ধ্যায় সূর্যকান্তের এক বন্ধুর বউ যে একরাশি ফুল দিয়াছিল, ঘর ভরিয়া সেই বাসিফুলের গন্ধ। শুধু তাই নয়। প্যাডে সূর্যকান্তের অসমাপ্ত গল্পটির শেষ কয়েকটা লাইন অমলা আড়চোখে পড়িয়া ফেলিয়াছিল, অবনী নামে কে যেন অনুপমা নামে কার ছদ্মবেশ-পরানো গোপন ভালবাসা জানিতে পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, বিবর্ণ পাংশু হইয়া আসিয়াছে তার মুখ, আর অনুপমার অনুপম চোখ দুটিতে দীপশিখার মতো দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে বিদ্রোহ—প্রথার বিরুদ্ধে, দুর্বলতার বিরুদ্ধে, কে জানে আরো কীসের বিরুদ্ধে! এমন সময়, অবনী ও অনুপমার ওরকম উত্তেজনাময় মুহূর্তগুলোর কথা লিখিতে লিখিতে, বউকে বুকে লইয়া এ কী রূঢ় বাস্তব মন্তব্য সূর্যকান্তের! সম্বন্ধ করার সময় দু বছর কী আড়াই বছর বয়স ভাঁড়াইয়াছিল তার বাপ-মা, এই কি সে কথা তুলিবার সময়?
অবনী ও অনুপমার গল্পটা পরে অমলা অনেকবার পড়িয়াছে। সেদিন যেখানে সূর্যকান্ত লেখা বন্ধ করিয়াছিল, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া প্রত্যেকবার অমলার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর ও পর্যন্ত লিখিয়া সেদিন রাত্রে সূর্যকান্ত অমন নিরুত্তেজ আবেগহীন অবস্থায় কী করিয়াছিল? কী প্রবঞ্চক সূর্যকান্ত!
.
আজকাল স্বামীর প্রবঞ্চনাকে অমলা মাঝে মাঝে আত্মসংযম বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছে। এটাও সে জানিয়াছে যে সূর্যকান্ত সবদিক দিয়া যতই সাধারণ হোক— বাস্তব জীবনে, কী যেন আছে লোকটার মধ্যে, অপূর্ব ও অদ্ভুত, যার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না, প্রমাণ করা যায় না, গ্রহণও করা যায় না। সাফল্যলাভ করিবার আগে প্রতিভাবানের প্রতিভা যেমন থাকিয়াও থাকে না, সেই রকম একটা অস্তিত্বহীন বিপুল ব্যক্তিত্ব যেন সূর্যকান্তের থাকিয়াও নাই—অন্তত অমলার কাছে। তাই, মাঝে মাঝে বিনয়ে তার হৃদয়টা কেন এতখানি ভরিয়া আসে যে সূর্যকান্তের কাছে মাথা নত করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, সে ভালো বুঝিতে পারে না। বশ মানিতে সাধ হয় অমলার। স্বামী তার স্বপ্ন ভাঙিয়া দেয়, কল্পনাস্রোত রুদ্ধ করে, আশা অপূর্ণ রাখে, নিজেও যথোচিতভাবে ভালবাসে না, তাকেও বাসিতে দেয় না—তবু!
আজকাল মানে বিবাহের মাস আষ্টেক পরে-বসন্তের শেষে যখন গ্রীষ্ম শুরু হইয়াছে—গরমে অমলার ঘনঘন পিপাসা পায়—সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্যকান্তের অবাস্তব কবিত্বময় ভালবাসার জন্য তার যে পিপাসা সব সময় জাগিয়া থাকে, গ্রীষ্ম তার কারণ নয়, সেটা স্বাভাবিকও নয়। একদিন, একটা দিনের জন্যও সূর্যকান্ত যদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত! যদি আবোলতাবোল কথা বলিত অমলাকে, আবেগে অদ্ভুত ব্যবহার করিত, পাগলের মতো, মাতালের মতো এমন ভালবাসিত তাকে—যে বাস্তব জগৎটা আড়াল হইয়া যাইত প্রেমের রঙিন পর্দায়! কিন্তু সূর্যকান্ত এক মিনিটের জন্যও আত্মবিস্মৃত হইতে জানে না। এমনকি অমলা নিজেই যদি একটু বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাস আরম্ভ করিয়া দেয়, সৃষ্টি করিয়া লইতে চায় একটি মোহকরী কাব্যময় পরিবেষ্টনী, সূর্যকান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, এসব ছ্যাবলামি শিখলে কোথায়?
রাগের মাথায় অমলা বলে, তোমার কাছ থেকে শিখেছি, তোমার বই থাকে।
সূর্যকান্ত বলে, তোমাকে যখন দেখতে গিয়েছিলাম, বিয়ের আগে, মনে হয়েছিল তুমি বুঝি খুব সাদাসিধে সরল—এসব পাকামি জান না। তুমি যা শিখেছ অমল, আমার কোনো বইয়ে তা নেই। যদি কখনো লিখে থাকি, ঠাট্টা করে খোঁচা দিয়ে লিখেছি; এরকম কবিত্ব যারা করে তাদের যে মাথার ব্যারাম থাকে তাই দেখাবার জন্য।
সূর্যকান্তের লেখার সমালোচকরা এ কথা শুনিলে তাকে মিথ্যাবাদী বলিত, অমলা রুদ্ধশ্বাসে শুধু বলে, ভালবাসা বুঝি মাথার ব্যারাম?
ভালবাসার তুমি কী বোঝ শুনি?
অমলা স্তব্ধ হইয়া যায়। রাগে অভিমানে প্রথমে তার মনে হয় এর চেয়ে মরিয়া যাওয়াও ভালো। ভালবাসার কিছু বোঝে না সে? বেশ, চুলোয় যাক ভালবাসা! সে বুঝিতে চায় না। সে কী চায় তা তো সূর্যকান্ত বোঝে? হোক এসব তার ছ্যাবলামি, কী দোষ আছে এতে, কী ক্ষতি আছে? তার সঙ্গে এই ছ্যাবলামিতে সূর্যকান্ত একটু যোগ দিলে কি বাড়ির ছাদটা ধসিয়া পড়িবে, না পুলিশে ধরিয়া তাদের জেলে পুরিবে? ক্ষতি তো কিছু নাইই, বরং লাভ আছে অনেকে—এইসব মনান্তর ও মনঃকষ্টগুল ঘটিবে না। অকারণে কেন এরকম করে সূর্যকান্ত তার সঙ্গে? কী সুখটা তার হয়, বউকে এত কষ্ট দিয়া? অমলার কান্না আসে। কুঁজোটা হাতখানেক সরাইয়া রাখা, টেবিল গুছানো, বই ও কাগজপত্রগুলো একটু ভিন্নভাবে সাজানো, এই ধরনের খুঁটিনাটি কাজ করিতে করিতে সে চোখের জল ফেলিতে থাকে। সূর্যকান্ত যে দেখিতে পাইতেছে যে সে কাঁদিতেছে, তাতে অমলার সন্দেহ থাকে না।
সূর্যকান্ত বলে, এক গ্লাস জল দাও তো।
অমলা কাচের গ্লাসে জল দিলে এক চুমুক পান করিয়া হাসিয়া বলে, তুমি জল দিলে আমার মনে হওয়া উচিত—জল খাচ্ছি না, সুধা পান করছি, না অমলা?
ঠাট্টা! সে কাঁদিতেছে দেখিয়াও এমন রূঢ় পরিহাস! বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া এবার অমলা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে। আছড়াইয়া পড়ার ধাক্কায় সূর্যকান্তের হাত হইতে গ্লাসটা পড়িয়া গিয়া বিছানা ভাসিয়া যায়। গ্লাসটা তুলিয়া সরাইয়া রাখিবার পর মনে হয় অমলার চোখের জলেই বিছানাটা এমনভাবে ভিজিয়াছে।
সূর্যকান্ত বিব্রত হইয়া বলে, তোমার সঙ্গে পেরে উঠলাম না অমল, সোজা সহজ জীবনে তুমি খালি বিকার টেনে আনছ। এই বয়সে এরকম হল কেন তোমার? অনর্থক দুঃখ তৈরি কর কেন? কী হয়েছে তোমার, ছেলে মরেছে, না স্বামী তোমায় ত্যাগ করেছে? খেতে পরতে পাচ্ছ না তুমি? সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সইছে না তোমার? দিব্যি হেসে খেলে মনের আনন্দে দিন কাটাবে তুমি, তা নয়, সব সময় একটা কৃত্রিম ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আছ। বিয়ের আগে আর কারো সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে থাকলেও বরং ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম। তাও তো নয়। তোমার যত ব্যথা বেদনা সব আমাকে নিয়েই। কেন বল তো? তোমাকে আমি অবহেলা করি, আদর-যত্ন করি না? আজ তোমাকে হাসাবার কত চেষ্টা করলাম তুমি হাসলে না, রাগাবার চেষ্টা করলাম রাগলে না, বললাম এস দুজনে একটু ব্যাগাটেলি খেলি, তার বদলে তুমি-
উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে অমলা উঠিয়া বসে, অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা গুঁজিয়া দেয় স্বামীর পায়ের মধ্যে, বলে, আমায় মাপ কর, মাপ কর। আমি তোমার উপযুক্ত নই।
সূর্যকান্ত বলে, এই তো! এই দ্যাখো আবার কী আরম্ভ করলে!
.
এই ধরনের দাম্পত্যালাপের যখন ইতি হয় এবং উত্তেজনা কিছু জুড়াইয়া আসে, অমলার মনের মধ্যে তখন যে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া গজরায় ও গুমরায় তার মধ্যে প্রধান হইয়া থাকে অভিমান। দুরন্ত অভিমানকে জয় করিয়া তাকে ঘুম পাড়াইতে একেবারে হয়রান হইয়া যায় ঘুমের পরীরা। সকালে থাকে বিষাদ। সংসারের কাজ করিতে করিতে সে অন্যমনা হইয়া যায়। বড় জা, বিধবা ননদ, দুটি দেবর এবং আরো যারা বাড়িতে থাকে পরীক্ষকের দৃষ্টিতে সকলে মুখের দিকে তাকায় অমলার, মেয়েরা ফিসফিস করিয়া নিজেদের মধ্যে তার কথা আলোচনা করে। তারপর সূর্যকান্ত আপিসে চলিয়া গেলে নিজের অজ্ঞাতেই এমন ব্যবহার করে অমলা, বাড়িতে যেন আর মানুষ নাই, বাড়ি খালি হইয়া গিয়াছে।
দেবর চন্দ্রকান্ত বলে, মাথা ধরেছে মেজোবউদি?
কই না।
তবে দয়া করে শুয়ে না থেকে একবার শুনে এস দিকি দিদি ডাকছে কেন? এমন সময় মানুষ শোয়!
তখন অমলার মনে পড়ে আজ তার রান্নার পালা ছিল, কিন্তু রান্না সে করে নাই। তার জন্য হয়তো হেঁসেল আগলাইয়া একজন বসিয়া আছে। হায়, যে স্বামী পদে পদে অপমান করে, আপিস যাওয়ার সময় যার জামার বোতাম লাগাইতে কাঁপা গলায় ‘কী করে সারা দুপুর কাটাব?’ বলার জন্য যার পরিহাসের আঘাতে আজই তাকে বিছানা আশ্রয় করিতে হইয়াছে, দশটা হইতে বেলা একটা পর্যন্ত সেই স্বামীর কথাই ভাবিয়াছে বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া। —কী করা যায় এখন? সকলের কাছে কী কৈফিয়ত দেওয়া যায় শুইয়া থাকার?
অমলা হঠাৎ কাতরকণ্ঠে বলে, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, আমি আজ খাব না।
উপবাসী হৃদয়ের কাণ্ডকারখানায় দিনটা অমলার উপবাসে কাটে। বিকালের দিকে ক্রমবর্ধনশীল উত্তেজনায় সে হইয়া থাকে বোমার মতো উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরক। সূর্যকান্ত বাড়ি আসিলেই বলে, শোন, ওগো শোন, কাছে এস না? এইখানে এসে শোন! এক মাসের ছুটি নেবে? কোথাও নিয়ে যাবে আমাকে? যেখানে হোক, যেদিকে দু চোখ যায় চল আমরা বেরিয়ে পড়ি। শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়। যাবে? বল না, যাবে? তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে অপর্ণার মতো আমি তোমাকে শেষবার জিজ্ঞেস করব—
আপিস ফেরত ঘর্মাক্ত সূর্যকান্ত গলা হইতে অমলার হাতের বাঁধন ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয়। তারপর খোলে জামা।
জিজ্ঞাসা করে, অপর্ণা কে?
ওমা, ভুলে গেছ? তোমার অপর্ণা গো!
আমার অপর্ণা?
তোমার রামধনু বইয়ের। যে বলেছে, মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত একজনকে ভালবাসা, সে রাজা হোক, পথের ভিখারি হোক—
ও, সেই অপর্ণা? জুতা জামা খুলিয়া সূর্যকান্ত তফাতে চেয়ারে বসে। গম্ভীর চিন্তিত মুখে অমলার মুখের ভাব দেখিতে দেখিতে বলে, সামনের শনিবার ছুটি নিয়ে তোমাকে বাপের বাড়ি রেখে আসব কিছুদিনের জন্য।
স্তম্ভিত অমলা বলে, কেন?
এখানে থাকলে তুমি খেপে যাবে।
এ আঘাতে অমলার উচ্ছ্বাসের বোমা ফাটিয়া যায়, কান্নার বিস্ফোরণে। সূর্যকান্ত নিষ্ঠুর নয়, মিনিটখানেকের মধ্যে তার ঘামে ভেজা বুকখানা অমলার চোখের জল আরো ভিজাইয়া দিতে থাকে। বড় ম্লান দেখায় সূর্যকান্তের মুখখানা।
.
স্ত্রীকে নার্ভ টনিক খাওয়ানোর বদলে কিছু দিনের জন্য বাপের বাড়ি পাঠানোই সূর্যকান্ত ভালো মনে করিল। এখানে থাকিয়াই সে নার্ভ টনিক খাইতে পারিবে শুধু এই ভয়ে নয়। অমলা অনেক দিন বাপ মাকে দেখে নাই। কুমারী জীবনের আবহাওয়ায় কিছু দিন বাস করিয়া আসিলে হয়তো বিবাহিত জীবন যাপনের কৌশলগুলো সে কিছু কিছু আয়ত্ত করিতে পারিবে। উনিশটা বছর অমলা সেখানে ছিল, সবগুলো বছর বোধ হয় সঙ্গে আনিতে পারে নাই, তাই এরকম ছেলেমানুষি করে। তা ছাড়া একটু বিচ্ছেদ ভালো। বিরহের তাপে ওর প্রেমের অস্বাভাবিকতার বীজাণুগুলো একটু নিস্তেজ হইতেও পারে।
যাইতে রাজি হইল বটে অমলা, সে জন্য কাণ্ড করিল কম নয়। রাজি হওয়ার রাত্রে অনেকক্ষণ গুম খাইয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে সইতে পারছ না বলে পাঠিয়ে দিচ্ছ না তো?
না গো, না।
আমার জন্য তোমার মন কেমন করবে?
করবে না? তুমি বুঝি ভাব তোমাকে আমি ভালবাসি না? একা একা বিশ্রী লাগবে অমল।
শুধু বিশ্রী লাগিবে! অমলা জোর দিয়া বলিল, একা একা আমি মরে যাব। এক মাস বাপের বাড়িতে থাকিয়া অমলা ফিরিয়া আসিল। মরিয়া যাইতে অবশ্য সে পারিত, কারণ সেখানে দিন সাতেক সে খুব জ্বরে ভুগিয়াছিল। আশ্চর্য জ্বর। এক শ এক ডিগ্রিতে পৌঁছিলেই অমলা বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতে শুরু করিত (সজ্ঞানে) এবং তার চারটি বউদির মধ্যে ছোটজনকে চুপিচুপি জানাইয়া দিত যে জীবনটা তার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ছোটবউদি বলিত ছোটদাদাকে এবং দুই ননদকে। জ্বরের সাত দিনে বাড়ির বিশেষ আদরের ছোট মেয়েটির জীবনের ব্যর্থতার সাত রকম দুর্বোধ্য কাহিনী শুনিয়া বাড়ি সুদ্ধ লোক এমন দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছিল বলিবার নয়। জ্বর সারিবার পর সকলের প্রতিনিধি হিসেবে বাড়ির বড়বউ কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল অমলাকে। লোক ভালো নয় অমলার শ্বশুরবাড়ির সকলে? কী করে অমলাকে তারা? বকে? গঞ্জনা দেয়? খাইতে দেয় না? খাটাইয়া মারে? এমনি মারে? তা যদি না হয় তবে সূর্যকান্ত বুঝি—
প্রশ্নগুলোর জবাব শুনিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের দুশ্চিন্তা পরিণত হইয়াছিল অবাক হওয়ায়। কী জন্য তবে জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে তার? কত খুঁজিয়া সূর্যকান্তের মতো জামাই তারা সংগ্রহ করিয়াছে অমলার জন্য! পণই যে দিয়াছে ষোল শ টাকা! বাড়িসুদ্ধ লোক যদি বাড়িরই একটি মেয়ের জীবন ব্যর্থ হওয়ার মতো বৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে ধাঁধায় পড়িয়া যায়, মেয়েটির বিপদের সীমা থাকে না। সকলের ব্যবহার চিন্তায় ফেলিয়া দেয় তাকে। তার মনে হয়, তবে কি সেই ভুল করিয়াছে? সত্যই কি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনাগুলো অকথ্য রকমের উদ্ভট মানসিক রোগ?
অমলার প্রতিহত উন্মাদনা, পৃথিবীতে আকাশকুসুমের বাগান করার অপূর্ণ কামনা ও বিবাহিত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা—সূর্যকান্তের কাছ হইতে সরিয়া আসিবার কয়েক দিন পর হইতেই তার মনে কাজ করিতেছিল। তা ছাড়া, বইয়ের যদি প্রভাব থাকে বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবঞ্চিত কল্পনাপ্রবণ মনে, বই যারা লেখে তাদের কি প্রভাব নাই? কাছে থাকিবার সময় স্বামীকে তার সাধারণ মানুষের মতো মনে হইত বলিয়া, স্বনামধন্য সাহিত্যিক বলিয়া চেনা যাইত না বলিয়া, যে আপসোস ছিল অমলার মনে, সাত দিন জ্বরে ভুগিবার সময় ছাড়া এখানে যেন সে আপসোস ধীরে ধীরে উপিয়া যাইতেছিল। মনে হইতেছিল, ওরকম সাধারণত্ব কি মানুষ মাত্রেরই থাকে না? ভুল দিকে সে স্বামীর অসাধারণত্ব খুঁজিয়া মরিয়াছিল। অনেক বিষয়ে অসামান্য ছিল বইকি সূর্যকান্ত! তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসীম জ্ঞান, উদ্দেশ্য বুঝিয়া মানুষের ভালোমন্দ কাজের বিচার করা, কোলাহলভরা সংসারের বাস্তবতার মধ্যে থাকিয়াও অমন সুন্দর সব গল্প-উপন্যাস রচনা করা, এসব কি অসাধারণত্ব নয়? সারা দিন আপিস করিয়া রাত্রি দশটা এগারটা পর্যন্ত লেখার পর এক-একদিন কি বড় শান্ত মনে হইত না সূর্যকান্তকে? সেই শ্রান্তিকেই কোনোদিন অবহেলা, কোনোদিন সংসারের চিন্তা, কোনোদিন মানুষটার নির্জীবতা মনে করিয়া সে কি নিজের রাগ দুঃখ অভিমানের পাহাড় সৃষ্টি করিত না, রোমাঞ্চকর ভালবাসার খেলা চাহিয়া শেষে মনোবেদনায় শুরু করিত না কান্না? রামধনুর অপর্ণার মতো লাখ লাখ মেয়েকেও সে সৃষ্টি করে ওরকম শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায়—সেও কি ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে বলিয়া বউয়ের সঙ্গে ছাদে গিয়া মুগ্ধ ও বিহ্বল হইতে পারে? ঘুমানোর সুযোগ দেওয়ার বদলে কথা বলিয়া অভিমান করিয়া কাঁদিয়া রাত দুটো পর্যন্ত সে তাকে জাগাইয়া রাখিত!
এই ধরনের অনেক কথা ভাবিয়াছিল অমলা এক মাস ধরিয়া—সূর্যকান্তের ব্যক্তিত্ব, সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার ও উপদেশগুলো তলে তলে কাজ করিতেছিল এবং জ্বরের টনিক একটু শান্ত করিয়া দিয়াছিল অমলাকে। জ্বরের পর কিছু দিন একটু চুপচাপ শান্তিতে থাকিতে কে না চায়? তাই শুধু রোগা হইয়াই নয়, একটু বদলাইয়া অমলা এবার স্বামীগৃহে ফিরিয়া আসিল।
সূর্যকান্ত বলিল, এমন রোগা হয়ে গেছ!
জ্বরে ভুগলাম যে?
জবাবটা খাপছাড়া যেমন হইল সূর্যকান্তের।’রোগা হব না? এক মাস তোমাকে ছেড়ে—’ এরকম একটা জবাব সে প্রত্যাশা করিতেছিল। যাই হোক, সোজা কথার সোজা জবাব দিতে যদি অমলা শিখিয়া থাকে, ভালোই। তাতে ক্ষুণ্ণ হওয়ার কিছু নাই।
অমলা বলিল, তুমিও রোগা হয়ে গেছ।
সূর্যকান্ত বলিল, হব না? এক মাস তোমাকে ছেড়ে থেকেছি একা একা
এ জবাবটা খাপছাড়া মনে হইল অমলার।’রোগা হয়েছি? ক’দিন যা খাটতে হয়েছে অমলা—’ এই রকম একটা জবাব সে প্রত্যাশা করিতেছিল। যাই হোক, সাধারণ কথার মিষ্টি জবাব দিতে যদি সূর্যকান্ত শিখিয়া থাকে, ভালোই। তাতে পুলকিত হওয়ার কিছু নাই।
এই হইল তাদের প্রথম দেখা, অপরাহ্নে এবং অল্পক্ষণের জন্য। রাত্রে যখন আবার দেখা হইল, চাঁদটা পৃথিবীর অপর পিঠে জ্যোৎস্না ঢালিতেছিল। একটু অস্থির ও উন্মনাভাবে সূর্যকান্ত ঘরে পায়চারি করিতেছিল। আকাশ—ঢাকা মেঘগুলো এমন গুমোট রচনা করিয়াছে যে ফ্যানটা প্রাণপণে ঘুরিয়াও ভালোমতো বাতাস সৃষ্টি করিতে পাারিতেছিল না। শুধু টেবিলে খোলা প্যাডটার পাতাগুলোকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।
অমলা নালিশ করিল, সন্ধে থেকে মেঘ করেছে, এখনো বিষ্টি নামল না, নামলে বাঁচি।
মেঘ করেছে নাকি?
টের পাও নি? ক’বার যে বিদ্যুৎ চমকাল, মেঘ ডাকল?
সূর্যকান্ত এক নতুন দৃষ্টিতে অমলাকে দেখিতেছিল, পরীক্ষার সময় ছেলেদের প্রথম প্রশ্নপত্র দেখার মতো। তারপর একটা প্রশ্নেরও জবাব-না-জানা ছেলের মতো সে বলিল, সন্ধ্যা থেকে গল্প লিখবার চেষ্টা করছিলাম অমল।
সত্যি? নতুন গল্প! দেখি তো কতটা লিখলে?—অমলা তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গেল, কাগজ-চাপাটার তলে একটিও লেখা কাগজ না দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল। প্যাডটার প্রথম পাতায় শুধু হেডিং, সূর্যকান্তের নাম আর পাঁচ-ছ লাইন লেখা।
সন্ধ্যা থেকে শুধু এইটুকু লিখেছ!
সূর্যকান্ত ধপাস করিয়া বিছানায় বসিয়া বলিল, না, অনেক লিখেছি। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটাতে পাবে।
অমলা সবিস্ময়ে বলিল, ওমা, ছেঁড়া কাগজে যে ভর্তি। সব আজকে লিখে লিখে ছিঁড়েছ?
সায় দিয়া সূর্যকান্ত একটা হাই তুলিল। শ্রান্তি? অমলা তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিল, ঘুম পেয়েছে? ঘুমোও তবে। দাঁড়াও বালিশটা ঠিক করে দি।
সূর্যকান্ত বলিল, না, ঘুমোব না। এক মাসের মধ্যে এক লাইন লিখতে পারলাম না—ঘুমোব! শুধু আজ? কতদিন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা এমনিভাবে ভর্তি করেছি তার ঠিক নেই। তুমি আমাকে কী করে দিয়ে গিয়েছ তুমিই জান, লিখতে বসতেও আর ইচ্ছে করে না, বসলেও মন বসে না, জোর করে যা লিখি সব ছিঁড়ে ফেলে দিই! উপন্যাসের ইনস্টলমেন্টটা পর্যন্ত লিখে দিতে পারি নি।
সূর্যকান্তের বিষণ্ন মুখ দেখিলে কষ্ট হয়। অমলার বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতেছিল, দু চোখ বড় বড় করিয়া সে চাহিয়া রহিল। বিবাহিত জীবনের এই পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বাপের বাড়ি হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা সহজ ও শান্ত ভাবটুকু অমলার ঘুচিয়া যাইতেছিল। এ ঘরের আবহাওয়ায় সে একা যত বিদ্যুৎ ঠাসিয়া রাখিয়া গিয়াছিল তার দেহমন যেন আবার তাহা শুষিয়া লইতেছে। তবু এবার হয়তো একটু সংযত থাকিতে পারিত অমলা, হয়তো সূর্যকান্ত যেরকম চাহিয়াছিল সেই রকম হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে পারিত সূর্যকান্ত যদি এমন ভাব না দেখাইত আজ, এমনভাবে কথা না বলিত। তার সুদীর্ঘ কুমারী জীবনের শেষ ক’মাসের কল্পনার মতো হইয়া উঠিয়াছে যে সূর্যকান্ত আজ! আঙুল চালাইয়া চালাইয়া চুল এলোমেলো করিয়া দেওয়ায় কী বন্যই আজ তাকে দেখাইতেছে! চোখের চাহনিতে যেন বিপন্নতার সঙ্গে মিশিয়া আছে বিদ্রোহ, কথা বলিবার ভঙ্গিতে যেন শোনা যাইতেছে পরাজিত ক্ষুব্ধ আত্মার নালিশ, বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে হঠাৎ উঠিয়া ভয়ানক কিছু করিবার এটা ভূমিকা মাত্র। তা ছাড়া, তারই জন্য এক মাস সূর্যকান্ত কিছুই লিখিতে পারে নাই! প্রথম দীর্ঘ বিরহ আসিবামাত্র স্বামী তার বুঝিতে পারিয়াছে, কী ভয়ানক ভালোই সে বাসিয়া ফেলিয়াছে তার বউকে! অমলা শিহরিয়া ওঠে, তার রোমাঞ্চ হয়।
গদগদ কণ্ঠে সে বলিল, আমার জন্য? আমার জন্য এক মাস তুমি লিখতে পার নি?
সূর্যকান্ত তার হাত চাপিয়া ধরিল। এত জোরে ধরিল যে চুড়িগুলো প্রায় কাটিয়া বসিয়া গেল অমলার হাতে। গলা আবেগে কাঁপাইয়া সূর্যকান্ত বলিল, কার জন্য তবে? তুমি আমায় পাগল করে দিয়েছ অমল, আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছ। কতবার ইচ্ছে হয়েছে ছুটে গিয়ে তোমাকে দেখে আসি। কেন যাই নি জান? বিরহের যাতনা কত তীব্র হতে পারে তাই দেখবার জন্য। আমার রামধনু বইয়ের অপর্ণাকে মনে আছে তোমার? ভালবাসা বাড়ানোর জন্য সে থেকে থেকে নিজেই বিরহ সৃষ্টি করে নিত। আমিও ভাবছিলাম—
একটি মুখর হিরো ও প্রায় নির্বাক হিরোইন—শুধু এই দুটি চরিত্র লইয়া নাটকের যেন অভিনয় চলিতে থাকে ঘরে,—রাত দুটা পর্যন্ত। প্ৰথম অঙ্ক শেষ হওয়ার আগেই অমলার সবটুকু উত্তেজনা নিস্তেজ হইয়া আসে, জাগে ভয়, মুখ হয় বিবর্ণ। এ কী ব্যাপার? সত্যসত্যই পাগল হইয়া গিয়াছে নাকি সূর্যকান্ত? এসব সে কী বলিতেছে, কী করিতেছে? ক্রমে ক্রমে শান্তি বোধ করে অমলা, তার ঘুম পায়। কিন্তু ঘুমানোর উপায় নাই। তার আট মাসের প্রতিহত উচ্ছ্বাস স্বামী আজ সুদে-আসলে ফিরাইয়া দিতেছে, গ্রহণ না করিয়া তার উপায় কী? কখনো প্রচণ্ড ও কঠিন, কখনো মৃদু ও কোমল ভালবাসার বন্যা আনিয়া দিতেছে স্বামী, যা সে চাহিয়া আসিয়াছে চিরকাল, আজ এ বন্যায় ভাসিয়া না গেলে কি চলে? মাগো, এমন হইল কেন সূর্যকান্ত, কীসে এমন পরিবর্তন আসিল তার?
রাত দুটোর সময় বোধ হয় তার মুখ দেখিয়া দয়া হইল সূর্যকান্তের। হঠাৎ মোটরের ব্রেক কষার মতো, সে থামিয়া গেল। অমলা মরার মতো জিজ্ঞাসা করিল, আমি এসেছি, এবার তো লিখতে পারবে?
সূর্যকান্ত আনমনে জবাব দিল, আমি ভাবছি অমলা, কথা কোয়ো না। তোমার কথা ভাবছি। পাশে শুয়ে আছ তুমি, তবু তুমি যেন কত দূরে, কত সমুদ্র, কত মরুভূমি পার হয়ে কুয়াশার আড়ালে তুমি যেন লুকিয়ে আছ, মনকে বাহন করে আমি তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। বাধা দিয়ো না, কথা কোয়ো না।
.
বিষের ওষুধ নাকি বিষ। তবু, স্ত্রী প্রকৃতির অস্বাভাবিকতাটুকু স্বাভাবিক করিয়া আনার জন্য সূর্যকান্তের এই অভিনব চিকিৎসাকে সমর্থন করা যায় না। আসলে, দোষ তো তারও কম নয়। প্রথম বয়সে ভাবপ্রবণতা, কবিত্ব ও রোমান্সের পিপাসা, হৃদয়ে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বাহুল্য, অধিকাংশ ছেলেমেয়েরই কমবেশি থাকে। এদিকে সূর্যকান্ত হইয়া গিয়াছে বুড়া। বয়সে না হোক, মনের হিসাবে। শুধু নিজের জীবনে নয়, পরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করিয়া সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে স্তুপাকার, লিখিতে বসিয়া শুধু পুরুষের নয়, মেয়েদেরও অসংখ্য বিভিন্ন অনুভূতি উপভোগ করিয়াছে বহুবার। ধরিতে গেলে ইতোপূর্বেই অনেকবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে সূর্যকান্তের, কখনো সে হইয়াছে বউ, কখনো বর; সে একাই একজোড়া স্বামী-স্ত্রী সাজিয়া নানাভাবে নানারকম সংসার স্থাপন করিয়াছে। অমলা তার কোন পক্ষের বউ বলা যায় না! তবু অমলার কল্পনাকে পর্যন্ত স্তম্ভিত করিয়া দেওয়ার মতো ছেলেমানুষি অবান্তর কল্পনা, জীবনকে কাব্যময় ও নাটকীয় করিয়া তুলিবার পিপাসা—এক কথায়, অনুভূতির জগতে বৈশাখী ঝড় ও বাসন্তী বায়ুর বিপরীত বিপর্যয় ঘটাইবার কামনা আজো সূর্যকান্তের আছে—তবে সেই সঙ্গে আছে ওই পিপাসা বা কামনাকে গোপন করিয়া রাখার অভ্যাস ও কোনো জীবন্ত রক্তমাংসের রমণীর সঙ্গে ও সমস্তের আদান-প্রদানের অক্ষমতা। জীবনটা মানুষের যতখানি গল্প-উপন্যাস হওয়া দরকার, নিজের গল্প-উপন্যাসে সূর্যকান্তের তা বহুগুণ বেশি হয়। লেখার সময় ছাড়া সে তাই হইয়া থাকে ভোঁতা, চায় শান্তি ও সহজ স্বাভাবিক জীবন। প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা এরকম হয় কিনা জানি না, তবে যে সব লেখকের বই পড়িয়া শুধু অমলার মতো মেয়েদের বুকটা ধড়ফড় করে, তারা অবিকল এই রকম বা এই ধরনের অন্যরকম হয়।
বাস্তব জীবনের সাধারণ কাজগুলো সূর্যকান্ত সাধারণভাবেই করে, সাধারণ সমস্যার মীমাংসা করে সাধারণ বুদ্ধি খাটাইয়া, তাতে কাজও হয়, সমস্যাও মেটে। অমলার জ্বর হইলে সে ডাক্তার ডাকিত সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্বর সাধারণ অসুখ। অমলার হৃদয়-মনের অস্বাভাবিক উত্তাপ তো জ্বর নয়। এই অসুখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সূর্যকান্তের সাধারণ বুদ্ধি গুলাইয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল যে বিষে যদিও বিষ ক্ষয় হয়, হিস্টিরিয়া হিস্টিরিয়ায় সারে না—কারণ হিস্টিরিয়া বিষ নয়।
কয়েক দিনের মধ্যে অমলা শুকাইয়া গেল। এ তো আর বই পড়া নয়, কল্পনা করা নয়, স্বপ্ন দেখা নয়, নিজের হৃদয়োচ্ছ্বাসকে কোনো রকমে বাহির করিয়া দেওয়া নয়! অন্য একজনের হৃদয়কে বহিয়া বেড়ানো—প্রত্যেক দিন উত্তেজনার মদ খাইয়া নেশায় জ্ঞান হারানো। স্বামীর আক্রমণের আকস্মিকতায় প্রথম রাত্রে অমলা ভয় পাইয়া গিয়াছিল, এখন আর ভয় হয় না, বুকটা ফাটিয়া যাইতে চায়, মাথার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল আবর্তনের সৃষ্টি হয়, চোখের সামনে সমস্ত ঝাপসা হইয়া আসে। এক-একসময় চিৎকার করিয়া হাসিয়া অথবা কাঁদিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। এক-একসময় ঘরের জিনিসপত্র ভাঙিয়া ছারখার করিয়া দিবার অথবা সূর্যকান্তের বুকটা আঁচড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিবার অদম্য প্রেরণা জাগে। সূর্যকান্তের আদরে তার দম আটকাইয়া আসে, কথা শুনিতে শুনিতে দুই কানের মাঝে ঝমঝম আওয়াজ হয়, হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া সে চুপ করিলে চারদিকের স্তব্ধতা মনের মধ্যে আছড়াইতে থাকে।
ফিসফিস করিয়া বলে, আলো নিভিয়ে দাও, আলো নিভিয়ে দাও!
সূর্যকান্ত বলে, আলো? কোথায় আলো অমলা? জ্যোৎস্নাকে আলো বোলো না।
একটু ঝিমায় অমলা।
লিখবে না আজ?
লেখা? একটু হাসে সূর্যকান্ত, কার জন্য লিখব? মনের পাতায় লিখছি, মুখে তোমাকে শোনাচ্ছি। আর কী দরকার লিখে?
মাথাটা কেমন ঘুরছে, কী রকম একটা কষ্ট হচ্ছে।
এবার হঠাৎ যেন সূর্যকান্ত চোখের পলকে আগেকার সূর্যকান্ত হইয়া যায়। এক গ্লাস জল গড়াইয়া সে অমলাকে দেয়, ভিজা হাত বুলাইয়া দেয় তার কপালে ও ঘাড়ে। শুধু বলে শোও। তারপর আলো নিভাইয়া সেও আসিয়া শুইয়া পড়ে! বলে, কী কষ্ট হচ্ছে অমলা?
কী জানি, বুঝতে পারছি না।
কেবল কষ্ট নয়, অনেক কিছুই সে বুঝিতে পারে না! বারুদ-ফুরানো তুবড়ির মতো হঠাৎ সূর্যকান্ত নিভিয়া গেল কেন? রামধনুর মোহিতের মতো বিপুল দুর্বোধ্য প্রেম একমুহূর্তে কী করিয়া হইয়া গেল এমন মৃদু কোমল স্নেহ? গভীর বিষাদ ও অবসাদ বোধ করে অমলা, তার ঘুম আসে না। একসময় মৃদুস্বরে সূর্যকান্ত তাকে ডাকে। ঘুমের ভান করিয়া সে জবাব দেয় না। তামাশা? সূর্যকান্ত কি তামাশা জুড়িয়াছে তার সঙ্গে? এতদিন ধরিয়া এরকম তামাশা করিবার মানুষ তো সে নয়! তা ছাড়া, কারো তামাশা কি এমন উতলা করিয়া তুলিতে পারে একজনকে? প্রথম দু-এক দিন কেমন খাপছাড়া মনে হইয়াছিল স্বামীর এই অভিনব পরিবর্তন, এখনো মাঝে মাঝে সব যেন কেমন বেসুরো কৃত্রিম মনে হয়—কিন্তু বাকি সময়? তখন যে আশ্চর্য ব্যাকুলতা সে দেখায়, যে অভূতপূর্ব ভাব ফুটিয়া থাকে তার মুখে চোখে, তা কি কখনো বানানো হইতে পারে? কথা বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া সে যখন শুধু চাহিয়া থাকে; শুধু ভাবে, আর মোহগ্রস্ত বিহ্বল মানুষের মতো দুটি হাত বাড়াইয়া তাকে স্পর্শ করামাত্র চমকাইয়া ওঠে এবং ভীরু শিশুর মতো তাকে জড়াইয়া ধরে, তখনো সে অভিনয় করিতেছে এ কী ভাবা যায়! অথচ এদিকে তার একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা অমলার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সূর্যকান্ত তাকে বলিয়াছিল সে বাপের বাড়ি যাওয়ার পর মাসিকের উপন্যাসটির ইনস্টলমেন্ট পর্যন্ত সে লিখিয়া দিতে পারে নাই। ক’দিন আগে, সে আপিস চলিয়া গেল বারোটার ডাকে মাসিকপত্রটি আসিয়াছিল; তাতে ছিল উপন্যাসটির দশ পাতা ইনস্টলমেন্ট! কৈফিয়ত অবশ্য সে একটা দিয়াছিল, সে নাকি এ মাসের কথা বলে নাই, বলিয়াছিল আগামী মাসের কথা। এ সংখ্যার লেখা তো সে কবে লিখিয়া দিয়াছে, অমলার বাপের বাড়ি যাওয়ার অনেক আগে।
অন্তত দু মাস আগে লেখা দিতে হয় অমল, নইলে ওরা সময় পাবে কেন ছাপবার?
তবু অমলার মনের খটকা যায় নাই। দু মাস আগে হোক চার মাস আগে হোক, পাঠাইয়া দেওয়ার আগে সূর্যকান্তের কোন লেখাটা সে পড়িয়া ফ্যালে নাই? এ লেখা সে লিখিল কখন?
আপিসে লিখেছিলাম। দশ-বারো দিন একদম কাজ ছিল না, সেই সময় এডিটর তাগিদ দিচ্ছিল তাই আর তোমাকে পড়তে দিই নি
তবু মিথ্যাটা এসব কৈফিয়তের খোলসে সম্পূর্ণ ঢাকা যায় নাই। অমলার মনের প্রতিবাদ এসব না মানিয়া একটা বিস্বাদ ব্যথায় পরিণত হইয়া আজো তার মনে বাসা বাঁধিয়া আছে। আছে গোপনে। সূর্যকান্তের এখনকার নতুন ধরনের ভালবাসারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই!
লেখা সূর্যকান্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। বাড়িতেও লেখে না, আপিসেও লেখে না। বাপের বাড়ি গিয়া নয়, এখানে আসিয়া অমলা তার লেখার ক্ষমতা হরণ করিয়াছে। অমলাকে অজস্র পরিমাণে দেওয়ার জন্য নিজের মধ্যে সে যে উচ্ছ্বাসের কারখানা বসাইয়াছে এবং কারখানা চালানোর জন্য মজুর ভাড়া করিয়াছে—বই লেখার
লেখার কৃত্রিম খাদ্যে পরিতুষ্ট মনের চাপ পড়া পাগলামিগুলোকে, সেই কারখানাতে এখন সব সময় সে কর্তৃত্ব খাটাইতে পারে না। অমলাকে দেওয়ার জন্য ছাড়া অন্য কাজে খাটাইতে গেলে মজুররা ধর্মঘট করে, কারখানা বন্ধ করার কথা ভাবিলে আরম্ভ করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে একটু একটু মদ খাইতে আরম্ভ করিয়া যারা নেশার দাস হইয়া পড়ে, তাদের মতো অবস্থা হইয়াছে সূর্যকান্তের। অমলার সঙ্গ ছাড়া আর কিছু তার ভালো লাগে না—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কর্তব্যপালন। শয়নঘরের বাহিরে সে আগের চেয়েও গম্ভীর হইয়া থাকে, মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারকে সে আরো সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিয়া রাখে—মনে হয় সে যেন সব সময় প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া চলিতেছে আর বোধ করিতেছে দারুণ অস্বস্তি। সাহিত্যিক বন্ধুরা জানিতে চায় সে তার এক নম্বর এপিকটা লিখিতেছে কি না, সম্পাদকরা প্রকারান্তরে জানাইয়া দেয় এরকম অন্যায় ব্যবহার সহ্য করা কঠিন, সাধারণ বন্ধুরা উপদেশ দেয় চেঞ্জে যাওয়ার, বাড়ির লোকে চেষ্টা করে আদর যত্ন স্নেহ মমতা সহানুভূতি প্রভৃতির পরিমাণটা বাড়াইবার। বাইশ বছর বয়সে যা করা চলিত, ত্রিশ বছর বয়সে তাই করিতে চাহিয়া চারদিকে সূর্যকান্ত বিশৃঙ্খলা আনিয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে তার মনে হয় অমলার চিকিৎসার জন্য নয়—ওই ছুতা করিয়া নিজের দাবাইয়া রাখা মানসিক বিকারগুলোকে সে সতেজে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছে। অমলার পাগলামি সারানো নয়, এ তার নিজেরই পাগল হওয়ার ইচ্ছা মেটানো। তা না হইলে, এসব অমলার সহ্য হইতেছে না দেখিয়াও সে কি থামিয়া যাইত না? সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া আনিত না তাদের সঙ্গ? এভাবে সে তো ওকে নির্যাতন করিতে চায় নাই! ওকে শুধু সে বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, ও যে নাটকীয় প্রেম চাহিত সেটা কত তুচ্ছ, কত হালকা, কতদূর হাস্যকর! সে তো শুধু থিয়েটার করিতে চাহিয়াছিল ক’দিন, তার নিজের গৃহের সিমেন্টের রঙ্গমঞ্চে সাধারণ বাস্তব জীবনের বিরুদ্ধে দৃশ্যপটের আবেষ্টনীতে অমলার উদ্ভ্রান্ত কল্পনা লইয়া রচিত একটা শিক্ষাপ্রদ নাটকের অভিনয়; এখন তার কাছেই সে অভিনয় এত বড় সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে কোনোমতেই যবনিকা সে আর ফেলিতে পারিতেছে না।
দিন কাটে। এক মাসের ছুটি নেয় সূর্যকান্ত, আপিস বিরক্তিকর। অমলার চোখের নিচেকার কালিমার ছাপ গাঢ় হইতে থাকে, কোনো কারণে কোনো দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিলে মনে হয় চোখে যেন তার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সংসারের কাজ আছে, সকলের সঙ্গে মেলামেশা আছে, সংসারের দৈনন্দিন সুখদুঃখ হাসিকান্নার ভাগ নেওয়া আছে। শ্রান্ত, বিষণ্ণ ও অন্যমনস্কভাবে এসব সে করিয়া যায়। রান্নাঘরে রাঁধিবার সময়ও সে যেন থাকে তার নিজের ঘরে, কল চালাইয়া সেজো ননদের ছেলের জামা সেলাই করিবার সময় সে যেন কণ্ঠলগ্না হইয়া থাকে সূর্যকান্তের। শান্ত ও স্নিগ্ধ একটু রূপ ছিল অমলার আর ছিল তেলমাখা পাথরের বাটির মতো একটু ভোঁতা লাবণ্য, এখন তার রূপ হইয়াছে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা মুখভঙ্গির তীক্ষ্ণ তেজি মৌলিকতা, লাবণ্য হইয়াছে সদ্য শাণ দেওয়া সিসার ছুরির পালিশ। মেজাজ, বুদ্ধিবিবেচনা, আত্মসংযম, চিন্তা ও কল্পনা, সুনিদ্রা এসব বড় অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে অমলার। হঠাৎ সামান্য কারণে সে এত রাগিয়া যায় যে অন্তত আরো একটা বছরের পুরোনো বউ যদি সে হইত, না খাইয়া শুইয়া থাকার বদলে বাড়িঘর মাথায় না তুলিয়া কখনই ছাড়িত না। ভাবনাগুলো তার এমন এলোমেলো হইয়াছে যে সব সময় কী ভাবিতেছে তাও সে বুঝিতে পারে না; স্টিমারে চাপিয়া কবে সে একবার ঢাকা গিয়াছিল, আর কাল সেজো ননদ যে বড় জার ছেলের দুধটুকু নিজের ছেলেকে খাওয়াইয়া দিয়াছিল, আর পরশু রাত্রে সূর্যকান্ত যে তার উনিশ বছর বয়সের একটা ভুলের কাহিনী শোনাইয়াছিল, আর..! তবু এ সমস্ত খিচুড়ি পাকানো চিন্তার মধ্যে আসল চিন্তার খেইটা না হয় নাই খুঁজিয়া পাওয়া গেল, বাড়ির সে দাসীটা আঁচল পাতিয়া ঘুমাইয়া আছে ওর মাথায় এক ঘটি জল ঢালিয়া দিবার সাধটা কোন দেশী সাধ? আর আজ রাত্রে বিধবা বড় ননদের সঙ্গে শোয়ার সাধ? চুপিচুপি সদর দরজা খুলিয়া পালাইয়া যাওয়ার সাধ? কলের ছুঁচটার নিচে একটা আঙুল দিয়া নিজেকে কেন্দ্র করিয়া বাড়িতে একটা হইচই গণ্ডগোল সৃষ্টি করার সাধ? আচ্ছা, কাল যখন সিঁড়ি দিয়া নামার সময় পা পিছলাইয়া গিয়াছিল, রেলিং ধরিয়া সামলাইয়া না নিলে কী হইত? খুব কী লাগিত গড়াইয়া গড়াইয়া নিচে পড়িয়া গেলে, হাত ভাঙিত, মাথা ফাটিত, একেবারে সে অজ্ঞান হইয়া যাইত? কী করিত সকলে? সূর্যকান্ত কী করিত?—দ্যাখো! সেজো ননদের ছেলের জামার কোনখানটা সে সেলাই করিয়া ফেলিয়াছে। মরেও না সেজো ননদটা।
এক মাস ছুটি নিয়াছে সূর্যকান্ত। কিন্তু দুপুরে অমলা ঘরে যায় না। সূর্যকান্তও তাকে ডাকে না। আপিস না করার আলস্য সে অমলা কাছে না থাকার মুক্তির সঙ্গে মিশাইয়া উপভোগ করে। বেশি বেলায় বেশি খাওয়ার জন্য একটু অম্বলের জ্বালাও সে ভোগ করে। চোখ দিয়া দ্যাখে কড়িকাঠ, কান দিয়া শোনে ওদিকের ঘরে অমলার কল চালানোর ক্ষীণ শব্দ, হৃদয় দিয়া অনুভব করে ভোঁতা একটা গ্লানি, আর মন দিয়া ভাবে আজই পোস্ট অফিস হইতে শ-তিনেক টাকা তুলিয়া বিকালের কোনো একটা গাড়িতে কোথাও বেড়াইতে গেলে কেমন হয়। বিকালের গাড়িতে, অন্তত রাত্রি ন’টার আগের কোনো গাড়িতে। অমলা ঘরে আসার আগেই যে গাড়িটা ছাড়িয়া যায়। কোন অমলা? তার মনের, না ও ঘরে কল চালাইয়া যে সেজো ননদের ছেলের জামা সেলাই করিতেছে, যে ঘরে আসিলে এতটুকু ঘরে কোটি বসন্ত আর কোটি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন মুহূর্তগুলো ঘনাইয়া আসিবে? ঠিক বুঝিতে পারে না সূর্যকান্ত। মনের অমলাকে সাথী করিয়া বিকালের গাড়িতে পালানো যায়, কিন্তু তাতে কি ও ঘরের অমলার জন্য মন কেমন করা কমিবে?
ছুটি নেওয়ার চার-পাঁচ দিন পরে বিকাল বেলা সূর্যকান্ত একখানা চিঠি লিখিতেছিল, অর্ধেক লিখিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কার উপরে রাগ করিয়াই সে যেন উঠিয়া পড়িল। সহজ ভাষায় পরিষ্কার করিয়া কেবল দরকারি কথাগুলো লিখিয়া একখানা চিঠি লেখার ক্ষমতাও যদি তার লোপ পাইয়া থাকে, এবার তবে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। জামা গায়ে দিতে দিতে সূর্যকান্তের রাগ কমিয়া আসিল। কার উপরে রাগ করিবে? চিঠি লিখিতে বসিয়া সে যদি ভাবিতে আরম্ভ করে যে আজ রাত্রে অমলার সঙ্গে প্রথমেই কীভাবে একটা নতুন ধরনের মধুর কলহ আরম্ভ করা সম্ভব, গুরুতর বিষয়ের বৈষয়িক চিঠি সে লিখিবে কী করিয়া? জুতা পায়ে দিয়া, কাপড় বদলাইয়া সূর্যকান্ত ঘরের বাহিরে আসিল। বারান্দায় স্টোভ জ্বালিয়া বৈকালিক চা-জলখাবারের আয়োজন হইতেছে। মেঘলা রঙের শাড়ি পরিয়া অমলা বেলিতেছে লুচি। শুধু বাড়ির মেয়েদের ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে অমলার স্বাভাবিক তুচ্ছ অসংযমটুকু কী রহস্যময়! একটু দাঁড়াইল সূর্যকান্ত। অমলার সেজো ননদ বলিল, বেরিয়ে যাচ্ছ নাকি দাদা? খেয়ে যাও, আগে চা করে দিচ্ছি তোমাকে। কেটলিতে জল আনো দিকি মেজো বউদি? যা লুচি ভাজা হয়েছে ওতেই দাদার হয়ে যাবে।
সূর্যকান্ত বলিল, এখন কিছু খাব না। খিদে নেই। সময় নেই।
তখন উঠিয়া আসিয়া অমলা ঘরে ঢুকিল। বক্তব্য আছে। এ বাড়িতে আধ- পুরোনো বউদের প্রথমে নিজে সকলের চোখের আড়ালে গিয়া—তারপর স্বামীকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া কথা বলা নিয়ম। এখন ইশারার দরকার ছিল না। সূর্যকান্তও ঘরে গেল।
অমলা বলিল, বাইরে থেকে চা খেয়ে এস না কিন্তু। আমিও এখন চা খাব না, তুমি ফিরে এলে নিজে চা করে দেব, তারপর এক পেয়ালা থেকে দুজনে একসঙ্গে চা খাব, কেমন? এমনি করে খাব
এ মন্দ পরামর্শ নয়। গালে গাল ঠেকাইয়া একসঙ্গে দুজনে চায়ের কাপে চুমুক হয়তো তারা দিতে পারিবে। কিন্তু কেন? গালে গাল ঠেকানো আর চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ব্যাপার দুটো পৃথক করিয়া রাখিলে দোষ কী?
আজ আমি ফিরব না অমল।
ফিরিবে না! রাত্রে বাড়ি ফিরিবে না! কোথায় থাকিবে সূর্যকান্ত সমস্ত রাত? কেন? বন্ধুর বাড়িতে রাত্রে থাকিবে কেন? নিমন্ত্রণ আছে, খাওয়া শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে, তাই? হোক রাত্রি, ট্যাক্সি করিয়া যেন সে ফিরিয়া আসে। একদিন না হয় ট্যাক্সি ভাড়া বাবদ দেড় টাকা—দু টাকা খরচই হইবে! অমলার অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি চোখে বিধিতে থাকে সূর্যকান্তের, মাথাটা যেন ঘুরিয়া ওঠে।
তবে যাব না অমল।
সেই ভালো। কী হবে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে?
তাই তো বটে! তার চেয়ে অমলার সঙ্গে এক কাপে চা খাওয়া ঢের বেশি উপভোগ্য। কিন্তু কীভাবে ওর সঙ্গে আজ সে মধুর কলহটা আরম্ভ করিবে? কীভাবে আজ সে নতুন একটা বৈচিত্র্য আনিবে তাদের প্রেমাভিনয়ে? বেশি জটিল হইলে, বেশি আর্টিস্টিক হইলে অমলা আবার বুঝিতে পারে না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে সে তার উপযুক্ত বউ নয়, তার মরাই ভালো। ফেনা ভালবাসে অমলা, শুধু ফেনা। তার মতো সাধারণ অল্পশিক্ষিতা ঘরের কোনায় বাড়িয়া ওঠা মেয়ে যা কিছু বুঝিতে, অনুভব করিতে ও উপভোগ করিতে পারে তারই ফেনা। ওর জন্য জলকে সোডা ওয়াটারের মতো, সিদ্ধির শরবতকে মদের মতো ফেনিল করিয়া তুলিতে হয় তাকে। নতুবা তাদের নাটক জমে না। নাটক না জমিলে অমলার মতো তারও মনে হয় জীবনটা বৃথা হইয়া গেল, বাঁচিয়া থাকার কোনো মানে রহিল না।
.
বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে নয়, পরদিন থিয়েটার দেখিতে গেল সূর্যকান্ত। অমলা ও বাড়ির অন্য মেয়েরাও অবশ্য সঙ্গে গেল। থিয়েটারে তাই দুজনের মধ্যে দু-একবার দৃষ্টি বিনিময় ছাড়া কথাবার্তা কিছুই হইল না। রাত তিনটায় বাড়ি ফিরিয়া নিদ্রাতুর দুজনে দু-একটি কথা বলিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সূর্যকান্ত বাড়িতেই রহিল বটে কিন্তু আগের রাত্রে বাহিরের আসল নাটক দেখিয়া আসার জন্যই সম্ভবত সেদিন রাত্রে ঘরোয়া নাটক তাদের তেমন জমিল না, দারুণ অস্বস্তি মনে লইয়া দুজনে সে রাত্রে ঘুমাইল। পরদিন অমলার সেজো ননদকে স্বামীর কাছে রাখিয়া আসিতে সূর্যকান্ত চলিয়া গেল পাটনা। কাজটা অমলার দেবর করিতে পারিত—তাই ঠিক ছিল আগে, শুধু দিন তিনেক তার কলেজ কামাই হইত। তিন দিন তাকে ছাড়িয়া থাকার চেয়ে ভাইয়ের তিন দিন কলেজ কামাই হওয়াকে সূর্যকান্ত যে বড় মনে করিল এতে কী মর্মান্তিক আঘাতই অমলার মনে লাগিল! তাও, ভাগনের সঙ্গে যখন সেজো ননদকে পাঠানো চলিত, সেজো ননদের স্বামীকেও যখন লেখা চলিত যে, আসিয়া লইয়া যাও। ভাগনে অবশ্য খুব ছেলেমানুষ, সেজো ননদের স্বামী অবশ্য অনেক চেষ্টা করিয়াও ছুটি পায় নাই—তবু মনে আঘাত লাগা তো এসব যুক্তি মানে না! তারপর তিন দিন পরে যখন অমলার বদলে অমলার দেবরের নামে একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি আসিল সূর্যকান্তের যে, এখানে ওখানে, সে একটু বেড়াইবে এবং ফিরিতে তার দেরি হইবে, অমলার চোখে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল স্বামী তাকে ত্যাগ করিয়াছে। হঠাৎ তাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া একবার যেমন ত্যাগ করিয়াছিল, এবার নিজে বোনের শ্বশুরবাড়ি গিয়া আবার তেমনই ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সেবার এখানে ফেরামাত্র স্বামীকে সে ফিরিয়া পাইয়াছিল, এবার স্বামী তার ফিরিয়া আসিলেও তাকে আর সে ফিরিয়া পাইবে না। অনুপযুক্তা বউটাকে জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য না থাকিলে এত লোক থাকিতে সে কেন যাচিয়া পাটনা যাইতে চাহিবে, তার সজল চোখের বারণ মানিবে না? হায়, একখানা চিঠিও যে সে লিখিল না অমলাকে!
তিন-চার দিন পরেই আগ্রা হইতে চিঠি আসিল বটে, বেশ বড় চিঠি, ফুলস্ক্যাপ কাগজের প্রায় একপাতা। কাগজ দেখিয়া আর ‘কল্যাণীয়াসু’ সম্বোধন দেখিয়াই অমলা বুঝিতে পারিল এ চিঠি চিঠিই নয়, পরিত্যক্তা স্ত্রীর সঙ্গে এ শুধু সূর্যকান্তের ভদ্রতা। কী লিখিয়াছে সূর্যকান্ত? কিছুই নয়! অমলাকে সে একটা ভ্রমণ-কাহিনী পাঠাইয়া দিয়াছে। শুধু গোড়ায় একটা অর্থহীন কৈফিয়ত দিয়াছে হঠাৎ তার বেড়ানোর শখ জাগিল কেন এবং শেষে লিখিয়াছে অমলাকে সাবধানে থাকিতে, সময়মতো খাওয়া-দাওয়া করিতে, শরীরের দিকে নজর রাখিতে, বাড়ি ফিরিয়া সে যদি অমলাকে বেশ মোটাসোটা দ্যাখে তবে তার কত আনন্দ হইবে–এই কথা। তারপর ভালবাসা জানাইয়াই ইতি এবং সে যে শুধু অমলারই এই মিথ্যা ঘোষণা।
ঘরে খিল দিয়া চিঠি পড়িয়াছিল অমলা, পাঁচ ঘণ্টা পরে সে খিল খুলিল। পাংশু বিবর্ণ তার মুখ, চোখ দুটি লাল। অসুখের কথা সকলে বিশ্বাস করিল, কেবল অমলার ছোট ননদ, যার বিবাহের বয়স হইয়াছে এবং সূর্যকান্তের মতো সাহিত্যিকদের উপন্যাস পড়িয়া যার আজকাল বুক ধরফড় করে, সে শুধু বলিল—বিরহ নাকি বউদি? চিঠি তো এল আজ। দাও না চিঠিখানা লক্ষ্মী বউদি ভাই, দেখি দাদা কী লিখেছে। সারা দিন ধরে পড়লে চিঠি, খেলে না দেলে না-
বিরহ? ওসব তুচ্ছ মৃদু বেদনা বোধ করিবার শক্তি অমলার আর ছিল না। আর কী তার সন্দেহ আছে যে সূর্যকান্তের হঠাৎ পাটনা যাওয়া ও এত দেরি করিয়া বাড়ি ফেরা তাকে ত্যাগ করারই ভূমিকা? রামধনুর অপর্ণাকে তার সাধারণ অনুপযুক্ত স্বামী যে কারণে ত্যাগ করিয়াছিল, তার ঠিক উলটা কারণে। নিজের বিবাহিত জীবনকে ও বিবাহিত জীবনের বাছা বাছা ছোটবড় ঘটনাকে অমলা তার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সূর্যকান্ত তাকে বিবাহ করিয়াছিল, তাই গতবার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া পর্যন্ত তাকে সে ভালবাসে নাই, তার বুকে ভালবাসা জাগাইবার চেষ্টাও করে নাই, বরং বাধাই দিয়াছে। অমলার ভালবাসা তখন সে চাহিত না, আর একজনের স্মৃতি (উনিশ বছর বয়সে একটা ছেলেমানুষি ভুল করার কাহিনীতে সে যার নাম করিয়াছিল তারই স্মৃতি কি না কে জানে!) বুকে পুষিয়া রাখিয়াছিল, নিজেকে ধরা দেয় নাই। অথবা সে অপেক্ষা করিতেছিল যে তাকে জয় করিয়া অমলা নিজের উপযুক্ততার প্রমাণ দিবে : মাঝে মাঝে দেখা হইয়া নয়, দিবারাত্রি একসঙ্গে বাস করিয়াও যদি তার বুকে ভালবাসা না জাগাইতে পারে, কোন গুণে তবে সে তার মতো দেশবিখ্যাত সাহিত্যিকের বউ হইয়া থাকিবে? তারপর তাকে বাপের বাড়ি পাঠানোর নামে ত্যাগ করিয়া বুঝি একটু মায়া হইয়াছিল সূর্যকান্তের, ভাবিয়াছিল সবদিক দিয়া নিজেকে অমলার কাছে সঁপিয়া দিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে অমলা তাকে বাঁধিতে পারে কি না। তাও যখন সে পারিল না, তখন আর পাটনা যাওয়ার ছলে তাকে ত্যাগ করা ছাড়া কী উপায় ছিল সূর্যকান্তের।
অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিয়া ত্যাগ হয়তো সে করিবে না, এখানে থাকিতে দিবে। আগের মতো থাকিতে দিবে, গাম্ভীর্য ও সহজ ব্যবহারের ব্যবধান রচিয়া। মৃদু একটু স্নেহমমতা সে পাইবে, আর কিছুই নয়। এ জীবনে একটি রাত্রিও আর অমলার আসিবে না স্বামীর যখন সে নাগাল পাইবে, স্বামী যখন তাকে ভালবাসিবে।
আগে, বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিবার আগে, অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে এইসব কথা হয়তো অমলার মনে আসিত কিন্তু আসিত কল্পনার রথে। হাজার সে বিচলিত হোক তার নারী- মস্তিষ্কের স্বভাব ও অপরিবর্তনীয় হিসাব করার প্রবৃত্তি, যা বাস্তবতা ও বাস্তব লাভ-লোকসানের হিসাব ছাড়া আর কিছুই মানে না, তাকে কখনো ভুলিতে দিত না যে তার এই সব উদ্ভট বিশ্লেষণ সাংসারিক রীতিনীতির বিরুদ্ধ, এ তার পাগলামি, তার নারীজীবনের প্রকৃত সার্থকতাগুলোর একটাও এইসব কারণে আসিতে বাধা পাইবে না। বরং এই উপলক্ষে একটা নতুন ধরনের মান-অভিমানের পালা গাহিয়া আরো সে নিবিড়ভাবে বাঁধিতে পারিবে তার স্বামীকে। কিন্তু অস্বাভাবিক ও মারাত্মক ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে তার আত্মরক্ষার এই স্বাভাবিক ব্রহ্মাস্ত্রটি সূর্যকান্ত অব্যবহার্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। যা ছিল অমলার শুধু কল্পনা ও হৃদয়োচ্ছ্বাস, কয়েক বছরের মধ্যে সংসারের ঢের বেশি গুরুতর ও ঢের বেশি প্রিয়তর ভাবনাচিন্তার তলে যা কোথায় তলাইয়া যাইত, নিজের অপরিমেয় অস্থায়ী পাগলামি দিয়া সূর্যকান্ত তাকেই অমলার কাছে দিয়া গিয়াছে সত্য ও বাস্তবতার রূপ। জীবনে নভেলি আবহাওয়া থাকে না জানিত বলিয়াই নিজের জীবনকে একটু নভেলি করার জন্য অমলার অদম্য পিপাসা জাগিয়াছিল, বিশেষত সে যখন মনে করিয়াছিল যে সূর্যকান্তের মতো নামকরা সাহিত্যিকের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় জীবনটাকে ওরকম করার একটা দুষ্প্রাপ্য ও বিশিষ্ট সুযোগ পাইয়াছে। জীবনটা কাব্যময় করার সুযোগ, কাব্যকে জীবন করার নয়। অমলা তো সামান্য স্ত্রীলোক, কাব্য ও জীবনের এই পার্থক্য জানা থাকে বলিয়াই কবি পর্যন্ত এ জগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সূর্যকান্ত সব ভণ্ডুল করিয়া দিয়া গিয়াছে। কবিত্ব করিতে গিয়া স্বামীর কাছে প্রশ্রয় না পাইয়া আগে কাঁদিয়াও সে সুখ পাইত, কারণ তাও ছিল এক ধরনের কাব্য। বাহুল্য কল্পনা ব্যাহত হইয়া বাহুল্য ব্যথা আসিয়া জীবনকে অমলার করিয়া তুলিত রসালো। এখন বাহুল্য ঘুচিয়াছে, রস হইয়াছে বিষ। একটা বোঝাপড়া যদি করিয়া যাইত সূর্যকান্ত, ভাবিবার একটা নতুন খোরাক যদি সে দিয়া যাইত অমলাকে! শুধু এইটুকু যদি অমলা কোনো রকমে ভুলিতে পারিত যে ইদানীং সূর্যকান্ত যখন তাকে অজস্র পরিমাণে স্বর্গের সুধা আনিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাকে সে সহ্য করিতে পারিত না, কাছে যাইতে ভয় করিত। হায় ভগবান! সাধে কী স্বামী তার হাল ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে।
সময়ে স্নানাহার হয় না, রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, জীবনের গোড়াটাই যেন আলগা হইয়া গিয়াছে অমলার। কথা বলিতে কষ্ট হয়। মানুষ কাছে থাকিলে বোধ হয় বিরক্তি। হোক। কেউ কিছু বলিতে সাহস পায় না, এ বিরহিনী উন্মাদিনীকে কে ঘাঁটাইবে? নিজের মনে থাকে অমলা, অনেকটা স্বাধীনভাবেই নিজের মনের বিকারকে ব্যবহার করে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন শহর হইতে সূর্যকান্তের চিঠি আসে, কখনো অমলার নামে—কখনো বাড়ির অন্য কারো নামে। প্রত্যেকটি চিঠি অমলাকে আঘাত করে। অমলার বিকৃত জগতে যা কিছু দামি সেসব কোনো কথাই চিঠিতে থাকে না, শুধু বাজে অবান্তর কথা। সূর্যকান্তের কাছে অমলার তুচ্ছতাই শুধু প্রমাণ করে চিঠিগুলো, আত্মগ্লানির আলোড়ন তুলিয়া দেয় মনে। একদিন প্রায় সমস্ত রাত জাগিয়া অমলা একখানা চিঠি লেখে সূর্যকান্তকে, আর একবার সে তাকে সুযোগ দিক, আর একটিবার, এবার যদি অমলা তার উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী হইতে না পারে তবে বিষ খাইয়া হোক, গলায় দড়ি দিয়া হোক ইত্যাদি। দশ দিন পরে মাদ্রাজ হইতে এ চিঠির জবাব আসিল। অমলার চিঠি পাইয়া সূর্যকান্ত নাকি খুব খুশি হইয়াছে, তবে ওসব আবোলতাবোল কথা কী ভাবিতে আছে, ছি! অমলা যে তার উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী নয় এ ধারণা তার কোথা হইতে আসিল ভাবিয়া সেই মাদ্রাজের একটা হোটেলের ঘরে বসিয়া সূর্যকান্ত এমন অবাক হইয়া যাইতেছে যে—
এদিকে আরো এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়াছে সূর্যকান্ত। আরো কিছুদিন বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিবে। অমলা যেন খুব সাবধানে থাকে, কেমন?
.
হাসিতে হাসিতে দম আটকাইয়া আসে অমলার, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়, হাত-পা ছুঁড়িবার ভঙ্গি দেখিয়া ভয় হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো বুঝি খসিয়া চারদিকে ছিটকাইয়া পড়িবে। পালিয়ে পালিয়ে কতকাল বেড়াবে ঠাকুরঝি বলে, আর ধনুকের মতো বাঁকা হইয়া অমলা হাসে। ব্লাউজের বোতামগুলো পটপট করিয়া ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া রাগে অমলা ব্লাউজটাই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, গায়ে আঁচলটুকু পর্যন্ত রাখিতে চায় না। বড় জা চেঁচায়, ছোট ননদ কাঁদে, দেবর মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢালে, ঠাকুর-দেবতার নাম করিয়া পিসি যে কী বলে বোঝা যায় না, বাকি সকলে যা করে অথবা বলে—তার কোনো মানে থাকে না। শেষে সকলে মিলিয়া চাপিয়া ধরে অমলাকে, অমলাও বড় জার হাতে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দেয়। অতি কষ্টে কামড় ছাড়াইয়া দিবার পর এত জোরে তার দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায় যে শরীরের আর কোথাও বোধ হয় একটুও শক্তি অবশিষ্ট থাকে না, সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া যায়।
এই প্রথমবার। দ্বিতীয়বার হয়—জরুরি টেলিগ্রাম পাইয়া সূর্যকান্ত ফিরিয়া আসিবামাত্র। তবে এবার হাসি দিয়া আরম্ভ হয় না, আরম্ভ হয় কলহে। কার হুকুমে সূর্যকান্ত ফিরিয়া আসিল বলিয়া অমলা কলহ আরম্ভ করে, চিৎকার করিয়া গালাগালি দেয়, মুখে ফেনা তোলে, হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ধনুকের মতো বাঁকিয়া যায়, তারপর দাঁতে দাঁত লাগাইয়া হইয়া যায় শিথিল।
এবার সকলে ব্যস্ত হয় কম। এমনকি অমলার মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে তাকে এ বাড়িতে গছানোর জন্য বড় জা তার বাপ-দাদার নিন্দাও করে। সূর্যকান্ত বলে, তিন বছর বয়েস যখন ভাঁড়িয়েছিল, এ রোগের কথা গোপন করবে তা আর বেশি কী। অ্যাদ্দিন হয় নি কেন তাই আশ্চর্য
কথাগুলো অমলা শুনিতে পায় না। রাত্রে সে তাই চুপিচুপি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বলছ তোমার মন কেমন করত? কেন তবে ফেলে পালিয়ে গেলে আমাকে? পাটনা থেকে কেন ফিরে এলে না?
কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কী হইবে? হিস্টিরিয়া ভাবপ্রবণতা নয়, ও একটা রোগ।
৪. বিপত্নীকের বউ
প্রতিমার বাবা নেহাত গরিব নন, প্রতিমাকেও দেখিতে নেহাত খারাপ বলা যায় না। আরো কিছুদিন চেষ্টা করিলে বিবাহের অভিজ্ঞতাবিহীন ভালো একটি কুমার বর তার জন্য অবশ্যই জোগাড় করা যাইত। তবু বিপত্নীক রমেশের হাতে তাকে সমর্পণ করাই বাপ-মা ভালো মনে করিলেন। একবার বিবাহ হইয়াছিল এবং বছর ছয়েক বয়সের একটি ছেলে আছে, এ দুটি খুঁত ছাড়া পাত্র হিসাবে রমেশের তুলনা হয় না। মোটে একত্রিশ বছর বয়স, দেখিতে খুবই সুপুরুষ, তিন শ টাকা মাহিনার সরকারি চাকরি। উচ্চশিক্ষা, নম্রস্বভাব, সংশের গৌরব এ সবের অভাবও রমেশের নাই। এমন পাত্র হাতছাড়া করিবে কে?
রমেশ নিজেই মেয়ে দেখিতে গিয়াছিল, বিবাহের আগে প্রতিমাও সুতরাং তাকে দেখিয়াছিল। দোজবরে শুনিয়া অবধি অদেখা ভাবী বরটির প্রতি প্রতিমার মনে যতখানি বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল, রমেশের সুন্দর চেহারা দেখিয়া তা কমিয়া যাওয়াই ছিল উচিত। তা কিন্তু গেল না। বিরুদ্ধভাবটা যেন বাড়িয়াই গিয়াছিল। এ পর্যন্ত মনের বিরূপভাবটা ছিল একটি কাল্পনিক ব্যক্তির উপর, অতএব সেটা তেমন জোরালো হইয়া উঠিতে পারে নাই। রমেশকে দেখিবার পর, সে অসাধারণ রূপবান পুরুষ বলিয়াই, আর একটি মেয়ে যে চার-পাঁচ বছর ধরিয়া তাকে ভোগ দখল করিয়াছিল, এ ব্যাপারটা প্রতিমার মনে ভয়ানক অশ্লীল হইয়া উঠিল। এর কারণটা জটিল। রমেশের আর কোনো পরিচয় তো সে তখনো পায় নাই, শুধু বাহিরটা দেখিয়াছিল। আগের স্ত্রীর সঙ্গে বাহিরের এইরূপ সংক্রান্ত সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক কল্পনা করা প্রতিমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাবী বরের কথা ভাবিতে গেলেই লোকটা তার মনে উদিত হইত দেদীপ্যমান কামনার মতো ঈষৎ স্থূলাঙ্গী এক রমণীর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়। বিতৃষ্ণায় প্রতিমার পবিত্র কুমারী দেহে কাঁটা দিয়া উঠিত।
স্বামীর সম্বন্ধে প্রতিমার এই অশুচিবোধ অনেকটা কাটিয়া গেল, স্বামীগৃহে মৃতা সতীনের একখানা বড় ফটো দেখিয়া। না, সেরকম মূর্তি বউটার ছিল না যাকে দেখিলেই টের পাওয়া যায় রূপবান স্বামীকে ক্লেদাক্ত বাহুতে দিবারাত্রি বাঁধিয়া রাখা ছাড়া আর কিছু সে জানে না। গোলগাল হাসিহাসি মুখখানা, ভাসাভাসা চোখে সরল শান্ত দৃষ্টি, কোলে বছর দুয়েকের একটি ছেলে, নড়িয়া যাওয়ায় ফটোতে মুখখানা ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। কাপড় পরিবার ভঙ্গি, দাঁড়ানোর ভঙ্গি সব মিলিয়া প্রমাণ করিতেছে বউটি ছিল নেহাত গোবেচারি, ভালোমানুষ। রমেশের বউ বলিয়া যেন ভাবাই যায় না।
ফটোখানা প্রতিমা দেখিল দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে গিয়া প্রথম দিন দুপুরবেলা, রাত্রে রমেশের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই। বিবাহের পর প্রথম দফায় যে ক’দিন তাদের দেখাশোনা হইয়াছিল তার মধ্যে রমেশ একেবারেই স্ত্রীর কাছে ঘেঁষিবার চেষ্টা করে নাই তাই রক্ষা, সুন্দর স্বামীটির উপর যে নিবিড় ঘৃণার ভাব প্রতিমার মনে তখন ছিল, একটা সে কেলেঙ্কারি করিয়া বসিতে পারিত। এবার মানসীর ফটোখানা দেখিয়া মন একটু সুস্থ হওয়ায় রাত্রে রমেশ আলাপ করিবার চেষ্টা করিলে দু-চারটে প্রশ্নের জবাব দিতে প্রতিমা কার্পণ্য করিল না। রমেশের মৃদুকণ্ঠ, শান্তভাব ও উদাসীনের মতো কথা বলিবার ভঙ্গি ভালোই লাগিল প্রতিমার। কে জানে কী ভাবিতেছে লোকটা?—একেবারে অন্যমনস্ক! ভাবিতেও তাহা হইলে জানে? রঙ-করা সঙের মতো চেহারাটাই সর্বস্ব নয়? গালে ওই দাগটা কীসের? আহা, দাড়ি কামাইতে গিয়া গালটা এতখানি কাটিয়া ফেলিয়াছে!
রাত বাড়ে, প্রতিমার ঘুম পায়, শয়নের কথা রমেশ কিছুই বলে না। খাটের এক প্রান্তে সে এবং অপর প্রান্তে প্রতিমা পা-ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে তো বসিয়াই থাকে। কীরকম মানুষ? প্রতিমা যেরকম ভাবিয়াছিল সেরকম তো নয়! একটু যেন রহস্যের আবরণ আছে চারদিকে। রমেশ একসময় বলিল, আগে থেকে এসব বলে নেওয়াই ভালো, কী বল? তুমি তা হলে আমাকে বুঝতে পারবে, আমিও তোমাকে বুঝতে পারব।
কী সব বলিয়া নেওয়া ভালো? কিছুই বুঝিতে পারিল না। তবু ঘাড় কাত করিয়া সে সায় দিল। শোনাই যাক স্বামীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণটা কীরকম হয়!
রমেশ বলিল, কেন আবার বিয়ে করলাম বলি। সহজে করতাম না। পাঁচ বছর একজনের সঙ্গে ঘরকন্না করে আবার আরেক জনের সঙ্গে, তুমি নিশ্চয় আমাকে অশ্রদ্ধা করছ। করছ না?
প্রতিমা ভদ্রতা করিয়া বলিল, না! তা কেন করব?
রমেশ বলিল, করছ বইকি। সব শুনলে কিন্তু তোমার মায়াই হবে। হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে ও যখন মরে গেল, শোকে আমি যেন কীরকম হয়ে গেলাম। বেঁচে থাকতে কখনো ভাবি নি এতখানি আঘাত পাব। সময়ে মনটা সুস্থ হবে ভেবেছিলাম, তাও হল না। কোনো কাজে মন বসে না, মানুষের সঙ্গ ভালো লাগে না, কর্তব্যগুলো না করলে নয় তাই করে যাই, কিন্তু কী যে কষ্ট হয় তা কী বলব। কতদিকে আমার কত রকম দায়িত্ব আছে ক্ৰমে ক্ৰমে বুঝতে পারবে, আর কারো ওপর যে ওসব ভার দেব সে উপায়ও আমার নেই, আমি না দেখলে চারদিকে অনিষ্ট ঘটবে। অথচ আমার মনের অবস্থা এরকম যে হাত-পা ছেড়ে ভেসে যেতে ইচ্ছে করে বেশি। আগে বাড়িতে সকলের ছিল হাসিখুশির ভাব, এখন আমি মনমরা হয়ে থাকি বলে কেউ আর প্রাণ খুলে হাসতে পারে না, বাড়িতে কেমন একটা নিরানন্দের ভাব ঘনিয়ে এসেছে। মেজাজটাও গিয়েছে বিগড়ে, কথায় কথায় ধমকে উঠি, সে জন্যও বাড়িসুদ্ধ লোক কেমন ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। ছেলেটা পর্যন্ত সহজে আমার কাছে ঘেঁষতে চায় না। প্রথমে অত খেয়াল করি নি, তারপর কিছুদিন আগে টের পেলাম আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে সুন্দর জীবনটা গড়ে তুলেছিলাম, আমার অবহেলায় তা ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে। বড় অনুতাপ হল। আমার একার শোক আর দশজনের জীবনে ছায়া ফেলবে এ তো উচিত নয়? এমন যদি হত যে সংসারে আমার কোনো কর্তব্য নেই, মনের অবস্থা আমার যেমন হোক কারো তাতে কিছু আসে যায় না, তা হলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু তা যখন নয়, শোক দুঃখ ভুলে আবার আমাকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। তাই ভেবে চিন্তে আবার তোমাকে—
এমন করিয়া বুঝাইয়া বলিলে শিশুও বুঝিতে পারে। প্রতিমা বুঝিতে পারিল, বিবাহ উপলক্ষে রমেশ যে ফ্যাশন করিয়া চুল ছাঁটিয়াছে, গোঁপ দাড়ি কামাইয়া মুখখানা চকচকে করিয়াছে ওসব কিছু নয়। হাতকাটা ছোট শার্টটি পরায় ওকে যতই কলেজের ছেলের মতো দেখাক, আড়ালের মনটি সংসারি, হিসাবি, সতর্ক, উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতা কল্পনা প্রভৃতির বদলে সুবিবেচনায় ঠাসা। প্রথমা স্ত্রীকে ভুলিবার জন্য নয়, ভোলা প্রয়োজন বলিয়া আবার সে বিবাহ করিয়াছে। পাঁচ বছর যার সঙ্গে ঘরকন্না করিয়াছিল তার জন্য শোক করিতে করিতে জীবনটা কাটাইয়া দিবারই প্রবল বাসনা, কিন্তু কী করিবে, আর দশজনের মুখ চাহিয়া শোকটা কমানো অপরিহার্য একটা কর্তব্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং এ তো জানা কথাই যে রমেশ বিশেষরূপে কর্তব্যপরায়ণ।
কিন্তু তাকে করিতে হইবে কী? ভিজা ন্যাকড়ায় শ্লেটের লেখা মোছার মতো রসালো ভালবাসায় স্বামীর মনের স্মৃতিরেখা মুছিয়া দিতে হইবে? ঘুমের ঘোরটা প্রতিমার কাটিয়া যায়। রমেশের গম্ভীর বিষণ্ণ মুখখানা এক নজর দেখিয়া সে ভাবিতে থাকে যে, এসব কথা তাকে বলিবার কী প্রয়োজন ছিল, এ কোন দেশী বোঝাপড়া! তার যেটুকু রূপযৌবন আর মানুষ ভোলানোর ক্ষমতা আছে তার এককণা কী সে বাপের বাড়ি ফেলিয়া আসিয়াছে? আস্ত মানুষটা সে আসিয়া হাজির, যে দরকারেই লাগাও বাধা দিতে বসিবে না। কে জানে রমেশ ভাবিয়া রাখিয়াছে কিনা যে মেয়েদের একটা গোপন রিজার্ভ ফান্ড থাকে স্নেহ মমতা ও মাধুর্য-রচনা শক্তির, আগে হইতে বলিয়া রাখিলে ওখান হইতে প্রয়োজন মতো আমদানি করিয়া বিশেষ অবস্থায় বিশেষ একটি মানুষের শোকের তপস্যা মেয়েরা ভঙ্গ করিতে পারে।
এও প্রতিমা বুঝিতে পারে না যে দশজনের মুখ চাহিয়া প্রথমা স্ত্রীকে ভুলিবার জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া অশ্রদ্ধার বদলে তার মায়া হওয়া উচিত কেন। আত্মীয়স্বজন, দায়িত্ব, কর্তব্য এইসব যাকে শোক ভুলাইতে পারে নাই, একটি স্ত্রী পাওয়া মাত্র সে আনন্দে ডগমগ হইয়া আবার বাঁচিয়া থাকার স্বাদ পাইতে আরম্ভ করিবে, এ তো শ্রদ্ধা জাগানোর মতো কথা নয়! স্ত্রীর প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করার চেয়ে এ ঢের বেশি মানসিক দুর্বলতার পরিচয়!
আরো অনেক কথা রমেশ সে রাত্রে বলিয়া গেল; রাত তিনটার আগে তারা ঘুমাইল না। বাড়ির লোকে টের পাইয়া ভারি খুশি। এ পর্যন্ত নববধূর সঙ্গে সে ভালো করিয়া কথা পর্যন্ত বলে নাই জানিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল।
.
বাড়িতে অনেক লোক, অনেক কাজ, অনেক বৈচিত্র্য। হৃদয়ে হৃদয়ে রকমারি স্নেহের ফাঁদ পাতা আছে। প্রতিমাকে আটক করিবার চেষ্টার কেহ কসুর করিল না। বউকে যে কোনো বাড়িতে এত খাতির করে প্রতিমার সে ধারণা ছিল না। সকলের কাছেই সে যেন অশেষরূপে মূল্যবান। কাজ তাহাকে করিতে দেওয়া হয় না, সংসারের গোলমাল হইতে তাহাকে তফাতে তফাতে রাখা হয়। রমেশের শৌখিন সেবাটুকু ছাড়া প্রতিমার কোনো কর্তব্য নাই। দিনরাত্রে সব সময় সে যাতে স্বামীসন্দর্শনের সুযোগ পায় বাড়ির ছেলেবুড়ো যেন তারই ষড়যন্ত্র করিয়া মরে। প্রতিমার বুঝিতে বাকি থাকে না সকলে কী চায়। এক বছর আগে মরিয়া যে বউ আজো এ গৃহের জড়বস্তুতে ও বিভিন্ন চেতনায় অক্ষয় অমর হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাড়াতাড়ি তাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। সে যে বিপুল ফাঁকটা রাখিয়া গিয়াছে শীঘ্র ভরাট হইয়া ওঠা চাই। রান্না খাওয়া প্রভৃতি নিত্যকার তুচ্ছ সাংসারিক কাজে নিজেকে একবিন্দু ক্ষয় করিবার প্রয়োজন প্রতিমার নাই, যা কিছু তার আছে একমনে সব সে ব্যয় করুক মৃতা সতীনের শূন্য সিংহাসনে আত্মাভিষেকের আয়োজনে। হাসি-গল্পে-গানে বাজনায় উথলিয়া উঠিয়া রমেশকে সে ভাসাইয়া লইয়া যাক, তার ভাঙা বুক জোড়া লাগিয়া দেখা দিক আনন্দ, উৎসাহ, প্রণয়ের প্রাচুর্য। হাসি চাই, হাসি! অম্লান, অপর্যাপ্ত হাসি!
হাসি প্রতিমার আসে না, মাধুর্য শুকাইয়া ওঠে। এমন ছিল নাকি তার সতীন, এই ক্ষুদ্র পারিবারিক সাম্রাজ্যে এত বড় প্রাতঃস্মরণীয় সম্রাজ্ঞী? রমেশ হইতে বাড়ির দাসীটির মন পর্যন্ত এমনভাবে সে জুড়িয়াছিল? এমন অসহ্য বেদনা সে রাখিয়া গিয়াছে যে মুক্তিলাভের জন্য বাড়িসুদ্ধ লোক এতখানি পাগল? সকলে যত ব্যাকুল হইয়া নীরবে তাহাকে প্রার্থনা জানায়, ভুলাও ভুলাও, সে মায়াবিনীকে ভুলাইয়া দেও, প্রতিমার তত মনে পড়ে সতীনকে। কী মন্ত্র না জানি জানিত সেই গোলগাল মুখওলা বউটি!
ননদ নন্দা বলে, কেন মুখভার করে আছ, বউদি ভাই? বাপের বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে? বল তো আজকে তোমার যাবার ব্যবস্থা করে দিই, দু দিন থেকে মন ভালো করে এস। তোমার শুকনো মুখ দেখলে আমাদের যে তাকে মনে পড়ে বউদি? বাপের অসুখ শুনেও তাকে আমরা পাঠাই নি, দু দিন ধরে চোখের জল ফেলেছিল। তাই না আমাদের এমন শাস্তি দিয়ে চলে গেল!
এ আরেকটা দিক। প্রতিমা মুখভার করিলে তার কথা সকলের মনে পড়িয়া যায়, প্রতিমা হাসিলে সকলে অবাক হইয়া বলে, ওমা এ যে অবিকল সেই আবাগির হাসি গো? নানা লোকে মৃতা সতীনটির সঙ্গে প্রতিমার নানারকম সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। পিছন হইতে দেখিলে প্রতিমার চলন যে তার মতো দেখায় এটা আবিষ্কার করে ছোটবউ বিমলা। তার বালা তার চুড়ি যে আশ্চর্য রকম মানাইয়াছে প্রতিমার হাতে, এটা আবিষ্কার করে আরেক ননদ মন্দা। বিধবা একজন পিসি থাকেন বাড়িতে, তার আবিষ্কারগুলো আরো ব্যাপক ও গুরুতর। প্রখর দৃষ্টিতে তিনি প্রতিমার প্রত্যেকটি অঙ্গ নিরীক্ষণ করেন, বলেন, ও মন্দা, ও নন্দা দ্যাখসে। বউয়ের চিবুক দ্যাখ, গলা দ্যাখ, ছুঁচোলো কনুই দ্যাখ! বাঁকাও দিকি বউ হাতখানা? – দেখলি নন্দা, ও মন্দা দেখলি!
কোমরের বঙ্কিম ভঙ্গি, আলতা-পরা পায়ের গোড়ালি, ভ্রু আর কানের মাঝখানের অংশটা সব প্রতিমা সেই একজনের কাছে ধার করিয়াছে! সমগ্রভাবে দেখিলে প্রতিমা অবশ্য অন্যরকম, সে ছিল দিব্যি মোটাসোটা রাজরানীর মতো জমকালো, প্রতিমা ক্ষীণাঙ্গী। তবু পিসির মতো শ্যেনদৃষ্টিতে প্রতিমার দেহটা নানা অংশে ভাগ করিয়া একবার সকলে মিলাইয়া দ্যাখো তো সেই হতভাগির যে ছবি স্মৃতিপটে আঁকা আছে তার সঙ্গে! রমেশ যে এত মেয়ের মধ্যে প্রতিমাকেই পছন্দ করিয়াছে, সে কী এমনি? এই মিলের জন্য।
এক দিন প্রতিমার হাত হইতে পান লইবার সময় রমেশ বলিল, জান নতুন বউ, তোমার আঙুলগুলো ঠিক তার মতো।
আঙুলগুলো পর্যন্ত তার মতো? রাগে প্রতিমার মন জ্বালা করিয়া উঠিল। রমেশের স্মৃতিময় আবেগকে রূঢ় আঘাত করিবার জন্য না-বোঝার ভান করিয়া বলিল, কার মতো গো? আর কেউ আছে নাকি তোমার, ভালবাসার কেউ?
রমেশ চমক ভাঙিয়া বলিল, কী বলছ? ছি! তোমার দিদির কথা বলছি।
আমার দিদিকে তুমি আবার দেখলে কোথায়? বিয়ের সময় সে তো আসে নি!
সে নয়। —মানসী। তোমার নখগুলো যেমন ডগার দিকে ঢেউ তোলানো, মানসীরও এমনি ছিল।
এবার প্রতিমা মুখের কৌতুকোচ্ছলতার ছাপ মুছিয়া ফেলিল, বলিল, তোমার আগেকার বউ? তাঁর নাম বুঝি মানসী ছিল?
রমেশ যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল।
তুমি জানতে না? অ্যাদ্দিন এসেছ এখানে, তার নামটাও শুনে রাখ নি?
প্রতিমা ম্লানমুখে বলিল, কে বলবে বল? দিদির কথা কেউ আমাকে কিছু বলে না।
রমেশ সাগ্রহে বলিল, শুনবে নতুন বউ? শুনবে তার কথা?
শুনব, বল।
মানসীর কথা বলিতে বলিতে রমেশের গলা ধরিয়া আসে। প্রতিমার অপরিমিত ঈর্ষা হয়। মনে হয়, এ বাড়ির সকলে তার সঙ্গে এক আশ্চর্য পরিহাস জুড়িয়াছে। মানসীকে ভুলিবার ছলে তাকে আনিয়া মানসীকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে তার মধ্যে। তার মৌলিকতা অচল এ বাড়িতে, সে মানসীরই নূতন রূপ,—অচিন্ত্য অব্যক্ত দেবতার প্রতিকৃতির মতো সেও সকলের নিরাকার ব্যাপক শোকের জীবন্ত প্রতিমা! মানসীর সঙ্গে সে সব দিক দিয়াই পৃথক, তবু মিলের তাই অন্ত নাই। ব্যথার পূজা নিবেদন করার জন্য সকলে তাকে মানসীর প্রতিনিধির মতো খাড়া করিয়া দিয়াছে!
.
একদিন প্রতিমা স্বামীকে বলিল, খোকা কোথায় আছে?
রমেশ বলিল, বড়পিসির ওখানে।
আনবে না তাকে?
তুমি বললেই আনব!
প্রতিমা অবাক হইয়া বলিল, আমার বলার জন্যই কি অপেক্ষা করছিলে? তোমাদের ব্যবহারে আমি সত্য থ বনে যাচ্ছি। কাউকে একদিন খোকার কথা বলতে পর্যন্ত শুনলাম না এসে থেকে। কেন তা বুঝিনে কিছু।
রমেশ বলিল, আমি বারণ করে দিয়েছিলাম নতুন বউ। এখানে তোমার মনটন বসলে তারপর—
খোকার দিকে মন দেবার সময় পাব? কী চমৎকার বোঝ তোমরা মানুষের মন!
দু দিন পরেই খোকা আসিল। বেশ মোটাসোটা লম্বাচওড়া ছেলে, কোলে করা কষ্টকর। তবু সকলে উদ্গ্রীব হইয়া আছে দেখিয়া কোনোরকমে প্রতিমা তাকে একবার কোলে করিল। বড় লজ্জা করিতে লাগিল প্রতিমার। প্রসব না করিয়াই সে এত বড় ছেলের মা? খোকাও নতুন লোকের কোলে উঠিয়া কাঠ হইয়া রহিল। পরের বাড়ির ছেলের সঙ্গে ভাব করার মতো করিয়া ছেলেকে যদি প্রতিমা আপন করিবার সুযোগ পাইত, মাতাপুত্রের প্রথম মিলনটা হয়তো এমন নীরস হইত না। কিন্তু সে যে মা এবং নতুন বউ, হাসি আর ছেলেমানুষি কথা দিয়া শুরু করিয়া দূর হইতে ধীরে ধীরে কাছে আগাইবার উপায় তো তার নাই, ছেলে কাছে আসিলে প্রথমেই বুকে জাপটাইয়া ধরিয়া আধঘোমটার ফাঁকে তাকে চমু খাওয়া চাই।
ছেলে তো আসিল, একটু মায়াও ওর দিকে প্রতিমার পড়িল, কিন্তু মৃতা সতীনের ছেলেও কম বিপজ্জনক পদার্থ নয়। একটা কঠিন সমস্যার মতো। আদর যত্ন ভালবাসা সব সতর্কভাবে হিসাব করিয়া দিতে হয়, কম হইলে লোকে ভাবিবে, সতীনের ছেলে বলিয়া অবহেলা করিতেছে; বেশি হইলে ভাবিবে, সব লোক-দেখানো। আঠার বছর বয়সের ভাবপ্রবণ মনে এ ধরনের সতর্কতা বজায় রাখিয়া চলা কঠিন। হিসাবও সব সময় ঠিক হয় না : প্রাত্যহিক জীবনে পদে পদে এমনি অভিনয় করিয়া চলিবার মতো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সে পাইবে কোথায়। ছেলেকে ভাত খাওয়াইতে বসিয়া প্রতিমা যদি একটু সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া যায়, চমক ভাঙিয়া সভয়ে সে চারদিক লক্ষ করে, কেহ তাকে বিমনা দেখিয়াছে কিনা। খোকার অসংখ্য শিশুসুলভ অন্যায় আবদার প্রতিমার অসংখ্য বিপদ। কী করিবে প্রতিমা ভাবিয়া পায় না। আবদার রাখিলে খোকার ক্ষতি, তাতে নিন্দা হয়। না রাখিলে খোকা কাঁদে, তাতেও নিন্দা হয়, ভরা পেটে খোকার হাতে সন্দেশ দিয়া প্রতিমা শুনিতে পায়, শাশুড়ি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, ওর সে বিবেচনা কোত্থেকে হবে নন্দা যে বলছিস? নাড়ির টান তো নেই।
পরদিন ভরা পেটে আবার সন্দেশের জন্য খোকা কাঁদে। প্রতিমা তাকে কাঁদায়, সন্দেশ দেয় না। মুখভার করিয়া পিসিমা আসিয়া খোকাকে কোলে নেন, ভাঁড়ার খুলিয়া খোকাকে সন্দেশ দেন, তারপর করেন স্থানত্যাগ। প্রতিমার মুখ লাল হইয়া যায়।
খোকাকে উপলক্ষ করিয়া প্রতিমা ধীরে ধীরে টের পাইতে থাকে, অতিরিক্ত স্নেহ যত্নের তলে তলে তার প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাবও সকলের আছে। এ বাড়ির মনগুলো যতক্ষণ তাকে টনিকের মতো ব্যবহার করিতে পারে ততক্ষণ কৃতজ্ঞ ও স্নেহশীল হইয়া থাকে কিন্তু যখনই প্রতিমার একটি বিশিষ্ট অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ সচেতন হইয়া ওঠে যাহা এ বাড়িতে কারো কোনো কাজে লাগিবার নয়, প্রতিমাকে তখন সে আঘাত করে। তখন সে প্রতিমার সমালোচক।
দিন কাটে কিন্তু এর ব্যতিক্রম হয় না। প্রতিমার ঘোমটা কমিতে থাকে, চলাফেরার স্বাধীনতা বাড়ে, সুখ-সুবিধার অতিরিক্ত কতগুলো ব্যবস্থা হয়, মানসীর সঙ্গে প্রতিমার মিল খুঁজিবার উৎসাহে সকলের ভাটা পড়ে, তবু না হয় প্রতিমার ব্যবহার কৃত্রিমতাহীন, না দেয় কেহ তাহাকে বাঁচিবার জন্য একটি সহজ স্বাভাবিক জগৎ। আর একজনকে তার আসনে পাঁচ বছর বধূজীবনের বিচিত্র তপস্যায় ব্যাপৃত ছিল প্রতিমার জীবনকে এই সত্য অপ্রতিহতভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। একবার এক মাসের জন্য বাপের বাড়ি ঘুরিয়া আসিল। খোকাকে সঙ্গে না আনা উচিত হইয়াছে কিনা ভাবিয়াই মাসটা কাটিল প্রতিমার। বাপের বাড়িতেও মন খুলিয়া সকলের সঙ্গে সে মিশিতে পারিল না। একটা অদ্ভুত জ্বালাভরা আনন্দ উপভোগের জন্য সত্যমিথ্যা জড়াইয়া প্রাণপণে শ্বশুরবাড়ির নিন্দা করিল এবং সে জন্য বিষণ্ন ও উন্মনা হইয়া রহিল। কে কী ভাবিবে তাই ভাবিয়া ভাবিয়া কাজ করার অভ্যাসটা প্রায় স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল, বাপের বাড়িতেও নিজের তাহার চলাফেরা অনেকটা পরের ভাবনাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল, বিবাহের পর যেমন হয় প্রতিমা তেমনই হইয়াছে,—পর হইয়া গিয়াছে। প্রতিমা আর সে প্রতিমা নাই!
তবু, সব প্রতিমার সহ্য হইত রমেশকে যদি সে ভালবাসিতে পারিত। ঘৃণার ভাব কোন কালে মুছিয়া গিয়াছিল, শ্ৰদ্ধা আসিতেও দেরি হয় নাই। রূপে গুণে মানুষটা অসাধারণ, সরল সহজ ব্যবহার, গাম্ভীর্যের অন্তরালে অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, রাগী কিন্তু সুবিবেচক। এ ধরনের পুরুষের সাহচর্য মেয়েদের কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর, এদেরই তারা স্বেচ্ছাদাসী। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপালনে রমেশ খুব যে বেশি ত্রুটি করে তা নয়, তবু স্বর্গীয়া সতীনের বিরুদ্ধে প্রতিমার অকথ্য ঈর্ষা দাম্পত্য জীবনের সহজলভ্য সুখের পথেও কাঁটা দেয়। মানসীকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়া রমেশের পক্ষে এখনো সম্ভব নয়, আজো সে অন্য মনে তার কথা ভাবে, কণ্ঠলগ্না প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া আজো সে তারই কণ্ঠবেষ্টন করিতে যায়, যে কোথাও নাই। এক-একদিন রমেশের চুম্বন পর্যন্ত অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, প্রতিমা স্পষ্ট অনুভব করে দড়ি ছিঁড়িবার মতো স্বামীর বাহুবন্ধন হঠাৎ শিথিল হইয়া গেল, নিভিয়া গেল চুম্বনের আবেগ। তা যাক, তাও হয়তো প্রতিমা গ্রাহ্য করিত না। হয়তো এই জন্যই সে স্বামীর মন জয় করিবার তপস্যা তীব্রতম করিয়া তুলিল, একটা মৃতা রমণীর কাছে হার মানিবার অপমান এ বয়সে সহ্য হয় না। কিন্তু জয় করিতেই অনেক বাধা, অনেক লজ্জাকর বেদনাদায়ক অন্তরায়। রমেশকে যখন সে মুগ্ধ করে, অতীতের দিক হইতে তার দৃষ্টি যখন সে ফিরাইয়া আনে নিজের দিকে, রমেশের প্রীতিপূর্ণ ভাষা ও মোহস্নিগ্ধ চাহনি আনন্দের বদলে তাকে যেন অকথ্য লজ্জা দেয়। সে যেন অনুভব করে এ ভাষা উচ্চারিত, এ চাহনি পুরাতন। যে কথা মানসীকে বলিত, যে চোখে মানসীকে দেখিত আজ সেই কথা সেই দৃষ্টিই রমেশ তাকে নিবেদন করিতেছে। এসব পুরোনো অভিনয়, অভ্যস্ত প্রণয়। রমেশের জীবনে স্তব্ধ নিশুতি রাত্রে এসব বহুবার ঘটিয়া গিয়াছে। পুনরাবৃত্তি আর প্রতিধ্বনি। আর কিছু নয়।
আর জয় করিবার সাধ থাকে না, রমেশকে ক্ষুব্ধ করিয়া প্রতিমা সরিয়া যায়। ভিতরে কে যেন শরমে মাথা হেঁট করিয়াছে। ক্ষোভে প্রতিমার চোখে জল আসে, ছবিতে দেখা একটি নারীর প্রতিহিংসার অন্ত থাকে না। কত সাধ ছিল প্রতিমার, কত কল্পনা ছিল, সব পর্যবসিত হইয়াছে এক বিপন্ন বিস্বাদ আত্মনিয়োগে—কর্তব্যেও নয়, খেলাতেও নয়, জীবনযাপনের অপরিচ্ছন্ন প্রয়োজনে।
এরকম সময়ে স্বামীর প্রতি প্রতিমার সেই গোড়ার দিকের ঘৃণার ভাবটা পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য ফিরিয়া আসে। এত যদি অবিস্মরণীয় প্রেম তার মানসীর জন্য, এ কী অপদার্থ সে যে প্রতিমাকে সাময়িকভাবেও তার ভালো লাগিল? একজনের স্মৃতিপূজায় আত্মহারা অবস্থাতেও আর একজন যাকে মুগ্ধ করিতে পারে, শ্রদ্ধা করিবার মতো কী আছে তার মধ্যে?
রমেশ জিজ্ঞাসা করে, এখানে তোমার মন টিকছে না কেন প্ৰতিমা?
প্রতিমা পালটা প্রশ্ন করে, আমার মনের খবর তোমাকে কে দিল?
অন্য লোকের দিতে হবে কেন, আমি নিজে টের পাই না? মন খুলে যেন মিশতে পারছ না, কেমন ফুর্তি নেই। কেউ কিছু বলে না তো তোমাকে? আদরযত্ন করে তো সকলে?
প্রতিমা হাসে, মাগো, তা আর করে না! আদরযত্নর চোটে হাঁপিয়ে উঠলাম : আমায় নিয়েই তো মেতে আছে সবাই।
রমেশ বলে, তুমি সবাইকে নিয়ে ওরকম মাততে পারলে বেশ হত! আমি তাই চেয়েছিলাম।
প্রতিমার ইচ্ছা হয় একবার জিজ্ঞাসা করে, আমার মন বসছে না বলছ, আমাকে কেন মনে ধরছে না তোমার? শুধু ভদ্রতা না করে ভালবাসা দিয়ে দ্যাখো না মন বসে কিনা আমার!
সমস্ত বাড়িতে মানসীর স্মৃতিচিহ্ন ছড়ানো, সেগুলো প্রতিমাকে পীড়ন করে। খান তিনেক বাঁধানো ফটোই আছে মানসীর। একখানা তার শয়নঘরে, একখানা রমেশ যে ঘরে কাজ করে সেখানে, আর একখানা শাশুড়ির ঘরে। ফটোর মানসীকে দেখিয়া যদিও মনে হয় না শখ ও শৌখিনতার তার কোনো বিশেষত্ব ছিল, হাতের যে রাশি রাশি শিল্পকর্ম রাখিয়া গিয়াছে সেগুলো অবাক করিয়া দেয়। পাঁচ বছরে নানা কাজের ফাঁকে এত বাজে কাজের সময় সে পাইত কখন? বাড়ির অর্ধেকের বেশি আসবাবও নাকি তারই পছন্দ করিয়া কেনা। গান জানিত না, তবু শখ করিয়া সে অর্গান কিনাইয়াছিল, তাই বাজাইয়া আজ প্রতিমাকে গান গাহিতে হয়। মানসীর ড্রেসিং টেবিলে তার প্রসাধন, মানসীর কয়েকটি বাছা বাছা গহনা তার আভরণ, মানসীর ব্যবহৃত খাটে তার শয়ন। মানসীর জামাকাপড়ে বোঝাই বাসো- প্যাটরায় বাড়ি বোঝাই। আরো কত অসংখ্য খুঁটিনাটি সে যে রাখিয়া গিয়াছে!
বধূত্বের নতুনত্ব কমিয়া আসিলে মানসীর গয়না কখানা প্রতিমা খুলিয়া রাখিল। সকলে তা লক্ষ করিল, শাশুড়ি খুঁতখুঁত করিলেন তবে বিশেষ কেহ কিছু বলিল না। কিন্তু কয়েকটি গহনা খুলিয়া রাখিলে কী হইবে! ব্যবহার্য, অব্যবহার্য পদার্থ যত কিছু মানসী রাখিয়া গিয়াছে চারদিকে, প্রকট হইয়া থাকা নিবারণ করিবে কে? মনের স্মৃতি, বাহিরের স্মৃতিচিহ্ন এ বাড়িতে সে মৃতা রমণীকে অমরত্ব দিয়াছে।
নন্দা বলে, জান বউদি, ওই যে আলমারিটা সাফ করে বাজে জিনিস রাখছ, ওটা ছিল তার শখের সামগ্রী। ওপরের তাকে ঠাকুর-দেবতার মূর্তি সাজিয়ে রাখত, রোজ সকালে উঠে প্রণাম করত।
ঠাকুর-দেবতারা গেল কোথায় ভাই?
কে জানে দাদা কোথায় রেখেছে। মূর্তিগুলোর ওপরে দাদা বড্ড রেগে গিয়েছিল সে স্বর্গে যাবার পর
প্রতিমা বলে, সেই থেকে তোমার দাদার স্বভাবটা রাগী হয়ে গেছে, তাই না ভাই?
নন্দা বলে, কেন, দাদা রাগারাগি করেছে নাকি তোমার সঙ্গে?
প্রতিমা হাসিয়া তার গাল টিপিয়া দেয়, বলে বিয়ে হলে বুঝবে বরের রাগারাগিও কত মিষ্টি শুধু মিষ্টি ব্যবহারের চেয়ে। একদিনও যদি রাগারাগি না হয় তবে বুঝবে বরের মনে কিছু গোলমাল আছে।
মৃতার জন্য স্বামীর মনের গোলমাল চিরস্থায়ী হইবে এ কথা প্রতিমা যে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিল সেটা আশ্চর্য নয়। স্বামী ভিন্ন যে কুলবধূর জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের পদার্পণ ঘটে না, তার সরলতা অনিন্দ্য, সে বিশ্বাসী। বিবাহের পরেই স্বামীর ভালবাসার শুরুকে সে অনায়াসে ভালবাসার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকে। প্রেমের পরবর্তী অগ্রগতি তার জীবনের অফুরন্ত বিস্ময়। মানসীর স্মৃতিতে রমেশকে মশগুল দেখিয়া কোন জ্ঞান আর অভিজ্ঞতায় প্রতিমা ভাবিতে পারিত মৃত্যু মৃত্যুই স্মৃতি কপূরধর্মী, জীবনে জীবিত ও জীবিতাদের আকর্ষণই সবচেয়ে জোরালো, যাকে মনে করিলে কষ্ট হয়, চিরকাল কেহ তাহাকে মনে করে না? ঈর্ষায় প্রতিমা যে মনের দল মেলিয়া ধরিল না তাতে রমেশের কাছে তার একটি রহস্যময় আবরণ রহিয়া গেল, তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছোটবড় প্রকাশ রমেশকে তার সম্বন্ধে যত সচেতন করিয়া তুলিতে লাগিল, এই রহস্যের অনুভূতি তার মনের গোলমালের তত বেশি জোরালো প্ৰতিষেধক হইয়া উঠিতে লাগিল।
বছর ঘুরিয়া আসিতে আসিতে জন্মিয়া গেল কত অভ্যাস, সৃষ্টি হইল কত অভিনব রসাস্বাদ। মানসীর শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য আসিয়া থাক, প্রতিমা তো একটি নিজস্ব জগৎ সঙ্গে আনিয়াছে। মানসীর ফাঁকটাতে খাপে খাপে তাকে বসানো অসম্ভব! কোথাও প্রতিমা আঁটে না, কোথাও সে ছোট হয়। মানসীর সঙ্গে তার যত বিরোধ, যত পার্থক্য সব দিনে দিনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। প্রতিমার দোষগুণ যে বিরক্তি ও ভালো লাগা সৃষ্টি করে তার অভিনবত্ব বিচলিত করিয়া করিয়া সকলকে শেষে আর বিচলিত করে না, প্রতিমার দোষগুণকে প্রতিমার দোষগুণের মতো করিয়াই সকলের মানিতে হয়। তা ছাড়া মানসীর মতো করিয়া পাইতে চাহিলে প্রতিমাকে কেহ পায় না, মানুষকে পাইতে চাহিয়া না পাইলে ভালো লাগিবার কথা নয়। অথচ প্রতিমার স্বকীয় আকর্ষণকে স্বীকার করিয়া কাছে গেলে বড় সুন্দর একটি হৃদয়ের পরিচয় মেলে।
যেভাবে মানসীর সঙ্গে সকলের অচ্ছেদ্য বন্ধনগুলো সৃষ্টি হইয়াছিল, সেইভাবেই প্রতিমাও সকলকে বাঁধিতে ও বাঁধা পড়িতে থাকে। খোকা ‘মা’ বলিয়া ডাকিলে প্রতিমার আর একটা বিশ্রী অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগে না, মোটামুটি ভালোই লাগে, যদিও ছেলেটার জন্য তার যে মায়া তাকে বাৎসল্য বলা যায় না। শাশুড়ি ননদ জা এদের সঙ্গে বাড়ির বউয়ের যে সম্পর্ক আধখানা মন দিয়াই সুষ্ঠুভাবে তা বজায় রাখিতে পারা যায়, প্রতিমা সেটা দিতে পারে।
সবই যেন একরকম সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া আসে, শুধু রমেশকে প্রতিমা নিজের জীবনে মানাইয়া লইতে পারে না। প্রথম যেদিন সে বুঝিতে পারে, শীতের কুয়াশা কাটিবার মতো রমেশের মন হইতে মানসীর শোক কাটিয়া যাইতেছে, তার ঈর্ষাতুর মনে সেদিন আনন্দের পরিবর্তে গভীর বিষাদ ঘনাইয়া আসে। কেমন সে লজ্জা পায়। মনে হয়, নিজের তারুণ্য দিয়া এতকাল একটা অপবিত্র ব্রত পালন করিতেছিল, উদ্যাপনের দিন আসিয়াছে।
তা তো সে করে নাই? কতদিন মানসীর ফটোর সামনে দাঁড়াইয়া হিংসায় জ্বলিতে জ্বলিতে তার সাধ গিয়াছে ফটোখানা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, যেখানে যা কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে সে মায়াবিনীর, ভাঙিয়া সব গুঁড়া করিয়া দেয়, কিন্তু যাচিয়া রমেশের মন হইতে তাকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা সে আর কতটুকু করিয়াছে?
দেবীপক্ষে প্রতিমার বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের রাত্রি একদিন ঘুরিয়া আসিল। গোপনে রমেশ সেদিন ফুল আর সোনার উপহার কিনিয়া আনিল। গম্ভীর চাপা লোটির মধ্যে একটা সুগভীর উত্তেজনা, আজিকার বিশিষ্ট রাত্রিটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার উৎসুক প্রত্যাশা সবই প্রতিমার কাছে ধরা পড়িয়া গেল। খুশি হইতে পারিল না। বোধ করিল মৃদু একটা বিস্ময়, একটা গ্লানিকর অস্বস্তি।
কী ভাবিয়া রমেশের আনা ফুলের মালা একটি প্রতিমা মানসীর ফটো বেষ্টন করিয়া টাঙাইয়া দিল। দীর্ঘকালের তীব্র উত্তপ্ত ঈর্ষায় প্রতিমার মন জুড়িয়া ওর স্থায়ী স্থানলাভ ঘটিয়াছে। ওর কথা ভাবিতে ভাবিতে এমন হইয়াছে প্রতিমার যে, নিজের বিবাহ রাত্রেও ওকে ভুলিবার তার উপায় নাই। এমনই আশ্চর্য যোগাযোগ যে প্রতিমাকে চুম্বন করিয়া মুখ তুলিতেই মানসীর ফটোর দিকে রমেশের চোখ পড়িল। সে বলিল, ওর ফটোতেও মালা দিয়েছ? তুমি তো বড় ভালো প্রতিমা?
প্রতিমা অনুভব করিল, তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলায় দড়ি কাটিবার মতো মানসীর স্মৃতি কমাস আগেও রমেশের যে বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া দিত, জীবন্ত সাপের মতো সেই বাহু দুটি আরো জোরে আজ তাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। রমেশের যে চুম্বন ছিল, শুধু ওষ্ঠের স্পর্শ, আজ তা প্রেমের আবেগে অনির্বচনীয়।
সহসা প্রতিমা কাতর হইয়া বলিল, ছাড়ো ছাড়ো, শিগগির ছাড়ো আমায়!
কী হল?-রমেশ ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল।
দম আটকে গেল আমার। ছাড়ো।
স্বামীকে ঠেলিয়া দিয়া প্রতিমা খাট হইতে নামিয়া গেল। ঘরে পর্যন্ত থাকিল না। বিদ্যুতের আলো মানসীর ফটোর কাচে প্রতিফলিত হইয়া চোখে লাগিতেছিল, প্রতিমার মনে হইয়াছিল সে যেন মানসীর তীব্রোজ্জ্বল ভর্ৎসনার দৃষ্টি।
প্রতিমা ছাদে পালাইয়া গেল। ছাদ ছাড়া বউদের আর তো যাওয়ার স্থান নাই। অপরিবর্তনীয় আকাশ ছাদের উপরে, তারার আলো মেশানো অপরিবর্তনীয় রাত্রির অন্ধকার চারদিকে। দুঃখে প্রতিমার কান্না আসিতে লাগিল। ভুলিয়া গিয়াছে? এমন মন তার স্বামীর যে এর মধ্যে মানসীকে ভুলিয়া গিয়াছে, তার মনোরাজ্যের সেই সর্বময়ী সম্রাজ্ঞীকে?
৫. তেজি বউ
সুমতির একটা মস্ত দোষ ছিল—তেজ। দেখিতে শুনিতে ভালোই মেয়েটা, কাজেকর্মেও কম পটু নয়, দরকার হইলে মুখ বুজিয়া উদয়াস্ত খাটিয়া যাইতে পারে, স্নেহ মমতা করার ক্ষমতাটাও সাধারণ বাঙালি মেয়ের চেয়ে তার কোনো অংশে কম নয়, খারাপ কেবল তার অস্বাভাবিক তেজটা। কারো এতটুকু অন্যায় সে সহিতে পারে না, তুচ্ছ অপরাধ মার্জনা করে অপরাধীকে অপরাধের তুলনায় তিন গুণ শাস্তি দিয়া, কারো কাছে মাথা নিচু করিতে তার মাথা কাটা যায়। হুকুম দিবার অধিকার যার আছে তার কথা সবই সে শোনে—যতক্ষণ কথাগুলো হুকুম না হয়। যত জোর হুকুম, তত বড় অবাধ্য সুমতি।
সবচেয়ে বিপদের কথা, কোনো বিষয়ে কারো বাড়াবাড়ি সুমতি সহ্য করিতে পারে না—গায়ে পড়িয়া তেজ দেখায়। বাঙালি ঘরের বউ, তার গায়ে পড়িয়া তেজ দেখানোর মানেই গুরুজনকে অপমান করা, সমবয়সীদের সঙ্গে ঝগড়া করা আর ছোটদের মারিয়া গাল দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দেওয়া।
দুঃখের বিষয়, সংসারে বাড়াবাড়ি করার বাড়াবাড়িটাই স্বাভাবিক। এমন মানুষ কে আছে যে জীবনে অনেক বিষয়ে বঞ্চিত হয় না? অনেক বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াটা কয়েকটা বিষয়ের বাড়াবাড়ি দিয়া পরিপূরণ করার চেষ্টা না করাটা রীতিমতো সাধনা-সাপেক্ষ। সংসারের লোক সাধনার ধার ধারে বা ইচ্ছা করিলেই ধারিতে পারে এরকম একটা ধারণা সাধু মহাত্মারা পোষণ করেন বটে, কিন্তু কথাটা সত্য নয়।
সুমতির তাই পদে পদে বিপদ। বিবাহের আগে গুরুজনদের মান না রাখিয়া, সমবয়সীদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আর ছোটদের বকিয়া মারিয়া ক্রমাগত হাঙ্গামার সৃষ্টি করা যদি বা চলে, বিবাহের পর শ্বশুরবাড়িতে এসব চলিবে কেন? প্রথম বছর দুই সুমতি প্রাণপণে তেজটা দমন করিয়া রাখিয়াছিল— দু-এক বার সকলকে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করার বেশি ভয়ানক কিছু করে নাই। অবস্থা বিপাকের কৃত্রিম সংযম আর প্রকৃতিগত স্বাভাবিক তেজের লড়াইয়ে সংযমটা ক্ষয় পাইতে পাইতে নিঃশেষ হইয়া আসায় এখন সে পড়িয়াছে মুশকিলে। শাশুড়িকে একদিন বেলুনি নিয়া মারিতে উঠাইয়া ছাড়িয়াছে, প্রথমবার বলিয়া শাশুড়ি মারিতে উঠিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, একেবারে মারিয়া বসেন নাই। কিন্তু কতকাল না মারিয়া থাকিতে পারিবেন? একে মেয়েমানুষ, তায় শাশুড়ি-ধৈর্যের সীমা তার স্বভাবতই সংকীর্ণ।
এতখানি তেজ সুমতি কোথা হইতে পাইল বলা কঠিন। তার বাবা সদানন্দ অতি নিরীহ গোবেচারি মানুষ, —কখন মানুষকে চটাইয়া বসেন এই ভয়েই সর্বদা শশব্যস্ত। মা চিররুগ্ণ রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মেজাজটা তার বিগড়াইয়া গিয়াছে বটে, বলা নাই কওয়া নাই হঠাৎ রাগিয়া কাঁদিয়া মাথা-কপাল কুটিয়া যখন তখন অনর্থ বাধান বটে, কিন্তু সেটা তেজের লক্ষণ নয়। মানুষটা আসলে ভয়ানক ভীরু। বড় ভাই দুজনে কুড়ি-বাইশ বছর বয়স হইতে কেরানি, তাদের তেজ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বোনেরা সব অতিরিক্ত লজ্জাশরম আর ভাবপ্রবণতায় ঠাসা,—চার জনেই অমানুষিক সহিষ্ণুতার বর্মে গা ঢাকা দিয়া স্বামীপুত্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে।
এদের মধ্যে সুমতির আবির্ভাব প্রকৃতির কোন নিয়মে ঘটিল বলা যায় না কোন নিয়মের ব্যতিক্রমে ঘটিল তাও বলা যায় না। আগাগোড়া সবটাই দুর্বোধ্য রহস্যে ঢাকা। লজ্জাশরম ও ভাবপ্রবণতা কিছু কম হওয়া আশ্চর্য নয়, প্রকৃতিতে কিছু অসহিষ্ণুতার আমদানিও বোধগম্য ব্যাপার, কিন্তু স্বামীপুত্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মধ্যে এতখানি তেজ বজায় রাখা যেমন খাপছাড়া তেমনই অবিশ্বাস্য।
পুত্র সুমতির মোটে একটি, এখনো দু বছর পূর্ণ হয় নাই। আর একটি যে কয়েক মাসের মধ্যে আসিয়া পড়িবে, আসিয়া পড়িবার আগে সে পুত্র অথবা কন্যা তা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে সুমতি আশা করে এটিও পুত্রই হইবে, দুটি পুত্রের পর একটি কন্যা হইলে মা হওয়ার আনন্দে একদিন সে কী পরিমাণ গর্বই না মিশাইতে পারিবে!
এসব ভবিষ্যতের কথা, আপাতত প্রথমটির মতো দ্বিতীয়টিকেও বাপের বাড়িতে গিয়া ভূমিষ্ঠ করার সাধটা সুমতির অত্যন্ত প্রবল হইয়া ওঠায় একটা ভারি গোলমালের সৃষ্টি হইল।
শাশুড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, বাপের বাড়ি যেতে হবে না। এই না সেদিন এলে বাপের বাড়ি থেকে?
সুমতি যুক্তি দিয়া বলিল, সে তো গিয়েছিলাম ছোড়দার বিয়েতে তাও তো সাতটা দিনও থাকতে পেলাম না।
মেজাজটা শাশুড়ির ভালো ছিল না। সকালে খোকাকে দুধ খাওয়ানোর সময় খোকা ভয়ানক চিৎকার জুড়িয়া দেওয়ায় শাশুড়ি বিশেষ কোনো অসন্তোষ বা বিরক্তি বোধ না করিয়াও নিছক শাশুড়িত্ব খাটানোর জন্যই একবার বলিয়াছিলেন, না কাঁদিয়ে দুধটুকু পর্যন্ত খাওয়াতে পার না বাছা!
আগে হইলে সুমতি চুপ করিয়া থাকিত, আজকাল সংযম ক্ষয় হইয়া আসায় মুখ তুলিয়া বলিয়া বসিয়াছিল, দুধ খাওয়াবার সময় ছেলেপিলে একটু কাঁদে।
কাঁদে না তোমার মাথা—বড় তো মুখ হয়েছে তোমার বউমা আজকাল?
মুখ হওয়া হওয়ি কী, যা বলেছি মিথ্যে তো বলি নি।
আমি মিথ্যে বলেছি? আমি মিথ্যে বলি? তুমি আমায় মিথ্যেবাদী বললে!
রাগে শাশুড়ির কণ্ঠ ক্ষণকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, আরো জোরালো আওয়াজ বাহির হইবার জন্য। কিন্তু সুমতির অপূর্বদৃষ্ট মুখভঙ্গি, তীব্রদৃষ্টি আর চালচলন দেখিয়া আওয়াজটা আর বাহির হইতে পারে নাই। ছেলেকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করিয়া সুমতি ধীর স্থির শান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ছেলেকে শান্ত করিয়া শাশুড়ির দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিল, আপনাকে মিথ্যেবাদী বলি নি, বলেছি দুধ খাওয়াবার সময় ছেলেপিলে একটু কাঁদে। কান্না থামিয়ে দিলাম, না কাঁদিয়ে খাওয়ান তো দুধ?
প্রথমটা থতমত খাইয়া শাশুড়ি অবশ্য বলিয়াছিলেন, তোমার হুকুমে নাকি? এবং তারপর একটা প্রচণ্ড হইচই বাধাইয়া দিয়াছিলেন যে মোহনলাল সুমতিকে বকিয়া আর কিছু রাখে নাই।
স্বামীর অন্যায় বকুনিতে সুমতি অভিমান করিয়া সারা দিন কিছু খায় নাই, তবু শাশুড়ির মেজাজটা খারাপ হইয়া আছে। মোহনলালের বকুনি শুনিতে শুনিতে সুমতি যদি অন্তত একবারও ফোঁস করিয়া উঠিত, শাশুড়ির হয়তো মেজাজটা এত খারাপ হইয়া থাকিত না। অকারণে শাশুড়িকে তেজ দেখাইয়া স্বামীর বকুনি বউ চুপচাপ হজম করিলে শাশুড়ির সেটা ভালো লাগে না, মেজাজ বিগড়াইয়া থাকে।
ফের মুখের ওপর কথা বলছ? বললাম বাপের বাড়ি যেতে হবে না, বাস্ ফুরিয়া গেল, অত কথা কীসের? মোটে সাত দিনের জন্যে গিয়েছিলাম! সাত দিনের জন্যে যে যেতে দিয়েছিলাম এই তোমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি, তা জেনে রেখ।
সুমতির নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইয়া উঠিল।
গুরুজনের কি চোদ্দোপুরুষ তুলে কথা বলা উচিত মা?
শাশুড়ির মেজাজ আরো খারাপ হইয়া গেল।
গুরুজন। গুরুজন বলে কী মান্যিই কর! আর বকতে পারি না বাছা তোমার সঙ্গে, বলে দিলাম যেতে পাবে না—পাবে না, পাবে না, পাবে না।
রাত্রে সুমতি পেট ভরিয়া খাইয়া ঘরে গেল। মোহনলাল আশা করিতেছিল সে একটু কাঁদিবে। গা ঘেঁষিয়া বসিয়া শাশুড়ির ছেলেমানুষিতে উত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করার ভঙ্গিতে একটু হাসিয়া সুমতি বলিল, কী অন্যায় দ্যাখো তো মার! এসময় বাপের বাড়ি না গেলে চলে? আমায় নেবার জন্য বাবা চিঠি লিখেছেন, মা পষ্ট বলে দিলেন যেতে দেবেন না। কালকেই চিঠির জবাব লেখা হবে—সকালে মাকে তুমি একটু বুঝিয়ে বোলো, কেমন?
সুমতি একটু কাঁদিলে, বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া পায়ে না পড়ুক অন্তত বুকে মুখ লুকাইয়া আত্মসমর্পণ করিলে, মোহনলাল তা করিত। বুঝাইয়া বলা কেন, স্পষ্ট করিয়াই বলিত যে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হোক। সুমতির তেজ দেখিয়া সে রাগ করিয়া বলিল, আমি বলতে টলতে পারব না।
পারবে না? বেশ।
বেশ মানে। তোমার যখন ইচ্ছা হবে তখনই বাপের বাড়ি যেতে দিতে হবে নাকি?
সুমতি সরিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, যখন ইচ্ছা বাপের বাড়ি আবার কবে গেলাম?
সুতরাং মোহনলাল রাগ করিয়া বলিল, বাপের বাড়ি যাওয়া না যাওয়ার মালিক তুমি নাকি? যখন পাঠানো হবে যাবে, যখন পাঠানো হবে না যাবে না। অত মেজাজ দেখাচ্ছ কীসের? বাড়ির বউ না তুমি?
বউ না হলে এমন অদৃষ্ট হয়। যেতে দেবে না?
না।
কেন দেবে না?
আমার খুশি!
এতক্ষণ সুমতি তেজটা চাপিয়া রাখিয়াছিল, আর পারিল না। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইতে লাগিল।
হাড়িমুচিরাও তোমাদের মতো বউয়ের ওপর খুশি খাটায় না, তাদেরও দয়ামায়া আছে। তোমরা ভদ্দরলোক কিনা-
ঘুমন্ত খোকার পাশে আছড়াইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া সে অসমাপ্ত কথাটা শেষ করিল অন্য কথা দিয়া, প্রতিজ্ঞা করার মতো করিয়া।
আমি যাবই এবার।
মোহনলাল রাগে আগুন হইয়া বলিল, মা যদিবা যেতে দেন, আমি দেব না। তোমার মতো বেয়াদব নচ্ছার মাগিকে ধরে চাবকানো উচিত।
সুমতি চোখ মেলিয়া বলিল, এক মাসের মধ্যে যদি আমি বাপের বাড়ি না যাই, চাবুক কেন আমায় ধরে তুমি জুতিয়ো
এত কাণ্ড ঘটিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। শাশুড়ির কাছে একটু নম্র হইয়া থাকিলে আর মাথা নিচু করিয়া আবদার ধরিলে প্রথমটা অরাজি হইলেও শেষ পর্যন্ত শাশুড়ি রাজি হইয়া যাইতেন। মোহনলালের কাছে একটু কাঁদিলেই কাজটা হইয়া যাইত। অপরপক্ষে, শাশুড়ি একটু মিষ্টিমুখে যদি বলিতেন যে এবার সুমতির বাপের বাড়ি না যাওয়াই ভালো, সুমতি ক্ষুণ্ণ হোক, রাগ করুক, বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিত না। এমনকি শাশুড়ির সঙ্গে কলহ করিয়া ঘরে যাওয়ার পর মোহনলাল যদি শুধু বলিত, মা যখন মানা করেছেন, এবার বাপের বাড়ি নাইবা গেলে?—সুমতি হয়তো ফোঁস ফোঁস করিয়া একটু কাঁদিয়া বলিত, আচ্ছা। বাপের বাড়ি যাওয়ার সমস্যার চমৎকার মীমাংসা হইয়া যাইত। সুমতির তেজের জন্য সব গোলমাল হইয়া গেল।
এখান হইতে কর্তৃপক্ষের চিঠি গেল, এবার বউমাকে পাঠানো হইবে না, পাঠানো সম্ভব নয়, অনেক কারণ আছে। সুমতি নিজে বাবার কাছে লিখিয়া দিল, যত শীঘ্র সম্ভব কাহাকেও পাঠাইয়া যেন তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়।
সদানন্দ অনেক বুঝাইয়া মেয়ের কাছে লম্বা চিঠি লিখিলেন। কেউ যখন তাকে পাঠাইতে ইচ্ছুক নন, তাকে নেওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি করা উচিত?
এ চিঠির এমন একটা জবাব সুমতি লিখিয়া দিল যে ভদ্রলোক স্বয়ং তিন দিনের ছুটি নিয়া মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আসিয়া হাজির হইলেন। বুক তখন তার টিপটিপ করিতেছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। মেয়েকে নেওয়ার জন্য প্রায় সজল চোখে কত যে কাকুতিমিনতি করিলেন, অন্ত হয় না। কিন্তু সুমতির শাশুড়ি গোঁ ছাড়িলেন না, ঘাড় নাড়িয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন, না বেয়াই না, এবার বউমাকে পাঠাতে পারব না।
কাকুতিমিনতিতে মন গলার বদলে শেষ পর্যন্ত শাশুড়িকে রাগিয়া উঠিবার উপক্রম করিতে দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সদানন্দ চুপ করিয়া গেলেন। সদানন্দ নিজে আসিয়া এভাবে বলিলে অন্য অবস্থায় শাশুড়ির মন হয়তো গলিয়া যাইত, বাপের বাড়ি যাওয়া নিয়া প্রথমবার সুমতির সঙ্গে যে ঝগড়া হইয়াছিল তাও হয়তো তিনি আর মনে রাখিতেন না, কিন্তু ইতিমধ্যে সুমতি আরো অনেকবার তেজ দেখাইয়া বসিয়াছে। যেমন তেমন তেজ নয়, গা পুড়িয়া জ্বালা করার মতো তেজ।
সুমতি বলিল, আমি তোমার সঙ্গেই চলে যাব বাবা, আমায় নিয়ে চল।
সদানন্দ মেয়েকে বুঝাইলেন। এরকম অবস্থায় যত রকম উপায়ে মেয়েকে বোঝানো সম্ভব, তার একটাও বাদ দিলেন না। কিন্তু এ তো বোঝার কথা নয়, কথাটা তেজের। সুমতির মুখে সেই এককথা, আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমায় নিয়ে চল।
শেষে সদানন্দের মতো নিরীহ গোবেচারি মানুষটা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এরা পাঠাবে না, তবু তুই যাবি কী রকম? আমি নিয়ে যেতে পারব না। এদের বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করতে পারিস, আমায় চিঠি লিখিস, এসে নিয়ে যাব। যাবার জন্য এত পাগলামিই বা কেন তোর? পরে না হয় যাস?
সদানন্দ ফিরিয়া গেলেন। এবার নিজের তেজের আগুনে সুমতি নিজেই পুড়িতে লাগিল। শারীরিক অবস্থাটা তার এতখানি মানসিক তেজ সহ্য করিবার মতো ছিল না, এ অবস্থায় মনটা যত শান্ত আর নিস্তেজ থাকে ততই ভালো। হাত- পাগুলো দেখিতে দেখিতে কাঠির মতো সরু হইয়া গেল, শুষ্ক শীর্ণ মুখে কেবল জ্বলজ্বল করিতে লাগিল দুটি চোখ। কথা কমিয়া গেল, খাওয়া কমিয়া গেল, আলস্য কমিয়া গেল—নিজের মনে নীরবে যতটা পারে কাজে অকাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আর যতটা পারে কোনো কাজ না করিয়া সে ছটফট করিতে লাগিল। তারপর সে এক মাস সময়ের মধ্যে বাপের বাড়ি না যাইতে পারিলে চাবুকের বদলে স্বামীর জুতা খাইতে রাজি হইয়াছিল, সেই সময়টা প্রায় কাবার হইয়া আসায়, একদিন শেষরাত্রে কিছু টাকা আঁচলে বাঁধিয়া একাই বাপের বাড়ি রওনা হইয়া গেল।
এ একটা মফস্বলের শহর। বাপের বাড়িটাও মফস্বলের একটা শহরেই। কিন্তু সোজাসুজি যোগ না থাকায় কলিকাতা হইয়া যাইতে একটু সময় লাগে।
সুমতির আরো অনেক বেশি সময় লাগিল। কারণ কলিকাতায় পৌঁছাইয়া বাপের বাড়ি যাওয়ার বদলে তাকে যাইতে হইল মেয়েদের একটা হাসপাতালে। খবর পাইয়া সদানন্দও আসিলেন, মোহনলালও আসিল এবং মোহনলাল বিনা বাক্যব্যয়ে মেয়েকে বাপের বাড়ি লইয়া যাইবার অনুমতিও সদানন্দকে দিয়া দিল। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার একমাস তাকে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে দিলেন না।
একমাস পরে বাপের বাড়ি গিয়া তিন মাস পরে অনেকটা সুস্থ হইয়া সুমতি স্বামীগৃহে আসিল। আর কোনো পরিবর্তন হোক না হোক, সুমতির একটা পরিবর্তন স্পষ্টভাবেই ধরা পড়িয়া গেল। দেখা গেল, তার সবটুকু তেজ কপূরের মতো উবিয়া গিয়াছে।
৬. কুষ্ঠ-রোগীর বউ
কোনো নৈসর্গিক কারণ থাকে কি না ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে মানুষের কথা আশ্চর্য রকম ফলিয়া যায়। সমবেত ইচ্ছাশক্তির মর্যাদা দিবার জন্যও ভগবান বিনিদ্র রজনী যাপন করেন না, মানুষের মর্মাহত অভিশাপের অর্থও জ্বালাময় অক্ষমতা ঘোষণা করার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। তবু মাঝে মাঝে প্ৰতিফল ফলিয়া যায়, বিষাক্ত এবং ভীষণ
এ কথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া? পকেট হইতে চুপিচুপি হারাইয়া গিয়া যেটি পথের ধারে আবর্জনার তলে আত্মগোপন করিয়া থাকে সেটি ছাড়া নারীর মতো মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই। কম এবং বেশি অর্থোপার্জনের উপায় তাই একেবারে নির্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের শয়তানি। কারো ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালের পাঁচশ ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন করো : সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ করো। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলে বলে কৌশলে যেভাবে পার তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাংকে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে।
ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।
সুতরাং বলিতে হয় যতীনের বাবা অনন্যোপায় হইয়াই অনেকগুলি মানুষের সর্বনাশ করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিল। সকলের উপকার করিয়া টাকা করিবার উপায় থাকিলে এমন কাজ সে কখনো করিত না। তাই, জীবনের আনাচে- কানাচে তাহার যে অভিশাপ ও ঈর্ষার বোঝা জমা হইয়াছিল সেজন্য তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলে না। তবু সংসারে চিরকাল পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন বাপের জমা করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভালো করিয়া ভোগ করিতে পারার আগেই মাত্র আটাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ঘটিল।
লোকে যা বলিয়াছিল অবিকল তাহাই। একেবারে কুষ্ঠব্যাধি।
মহাশ্বেতা একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল : ‘তোমার আঙুলে কী হয়েছে?’
‘কী জানি। একটা ফুসকুড়ির মতো উঠেছিল।’
মহাশ্বেতা আঙুলটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিল : ‘ফুসকুড়ি নয়। চারদিকটা লাল হয়েছে।’
‘আঙুলটা কেমন অসাড় অসাড় লাগছে শ্বেতা।’
‘একটু টিনচার আইডিন লাগিয়ে দেব? নয়তো বলো একটা চুমো খেয়ে দিচ্ছি, এক চুমোতে সেরে যাবে।’
আঙুলটা চুম্বন করিয়া মহাশ্বেতা হাসিল।
‘পুরুষ মানুষের আঙুল তো নয়, উর্বশী মেনকার কাছ থেকে যেন ধার করেছ। বাবা, মানুষের আঙুলের রং পর্যন্ত এমন টুকটুকে হয়! রক্ত যেন ফেটে পড়ছে!’
আঙুলটি যে হাতে লাগানো ছিল স্বামীর সেই হাতটি মহাশ্বেতা নিজের গলায় জড়াইয়া দিল। জীবনে যে-কথা সে বহুবার বলিয়াছে আজ আর একবার সেই কথাই বলিল।
‘এ তোমার ভারি অন্যায় তা জান? তুমি সুন্দর বলেই তো আমার ধাঁধা লাগে! তোমাকে ভালবাসি, না, তোমার চেহারাকে ভালবাসি বুঝতে পারি না। শুধু কি তাই গো? হুঁ, তবে আর ভাবনা কী ছিল! দিনরাত কীরকম ভাবনায়- ভাবনায় থাকি তোমার হলে টের পেতে। ঈর্ষায় জ্বলে মরি যে!’
তারপর আরো কিছুকাল বোঝা গেল না। শুধু আঙুল নয়, যতীনের হাতে দু-তিন জায়গায় তামার পয়সার মতো গোলাকার কয়েকটা তামাটে দাগ যখন দেখা দিল, তখনো নয়। মহাশ্বেতার শুধু মনে হইল যতীনের শরীরটা বুঝি ভালো যাইতেছে না, গায়ের রঙটা তাহার রক্ত খারাপ হওয়ার জন্য কীরকম নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। একটা টনিক খাওয়া দরকার।
‘দ্যাখো, তুমি একটা টনিক খাও।’
‘টনিক খেয়ে কী হবে?’
‘আহা খাও না। শরীরটা যদি একটু সারে।’
যতীন টনিক খাইল। কিন্তু টনিকে এ ব্যাধির কিছু হইবার নয়। ক্রমে আরো কয়েকটা আঙুলে তাহার ফুসকুড়ি দেখা দিল। শরীরের চামড়া আরো কর্কশ, আরো মরা মরা দেখাইতে লাগিল। চোখের কোল এবং ঠোঁট কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর মৃত মাংসের রূপ লইয়া অল্প-অল্প ফুটিয়া উঠিল। স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি তাহার ক্ষীণ হইয়া আসিল। চিমটি কাটিলে তাহার যেন আর তেমন ব্যথা বোধ হয় না। দিবারাত্রি একটা ভোঁতা অস্বাস্থ্যকর অনুভূতি তাহাকে বিষণ্ন ও খিটখিটে করিয়া রাখিল। এবং সকলের আগে যে আঙুলের ছোট একটি ফুসকুড়িকে মহাশ্বেতা চুম্বন করিয়া টিনচার আইডিন লাগাইয়া দিয়াছিল সেই আঙুলেই তাহার পচন ধরিল প্রথম।
ষোল টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : ‘আপনাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি; আপনার কুষ্ঠ হয়েছে।’
বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : ‘টাইপটা খারাপ। একেবারে সেরে উঠতে সময় নেবে।’
‘সেরে তা হলে যাবে ডাক্তারবাবু?’
‘যাবে না? ভয় পান কেন? রোগ যখন হয়েছে সারতেও পারে নিশ্চয়।’
এমন করিয়া ডাক্তার কথাগুলি বলিলেন, আশ্বাস দিবার চেষ্টাটা তাহার এত বেশি সুস্পষ্ট হইয়া রহিল যে কাহারো বুঝিতে বাকি রহিল না যতীনের এ মহাব্যাধি কখনো সারিবে না।
একশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : ‘যতটা সম্ভব লোকালাইজড করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। তার বেশি কিছু করা অসম্ভব। জানেন তো রোগটা ছোঁয়াচে, সাবধানে থাকবেন। আপনাকে তো বলাই বাহুল্য যে ছেলেমেয়ে হওয়াটা বোঝেন না?’
বোঝে না? যতীন বোঝে, মহাশ্বেতা বোঝে। কিন্তু ছ’মাস আগে যদি এই বোঝাটা যাইত!
মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে। অন্যায় অসঙ্গত অপঘাতে যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য-সদ্য মরিয়া গিয়াছে। বিমূঢ় আতঙ্কে বিহ্বলের মতো হইয়া সে বলিল ‘তোমার কুষ্ঠ হয়েছে? ও ভগবান, কুষ্ঠ!’
ব্যতীন তখনো মরে নাই, মরিতেছিল। সাধারণ কথার সুর তাল লয় মান সমস্ত বাদ দিয়া সে বলিল : ‘কী পাপে আমার এমন হল শ্বেতা?’
‘তোমার পাপ কেন হবে গো? আমার কপাল!’
নিজের বাড়িতে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে যতীন হইয়া রহিল অস্পৃশ্য। গৃহের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবার সাধ থাকিলেও বাধা অবশ্য কেহই তাহাকে দিতে পারিত না। কিন্তু সে গোপনতা খুঁজিয়া লইল। বাড়ির একটা অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সেখানে নিজেকে সে নির্বাসিত ও বন্দি করিয়া রাখিল। মহাশ্বেতা ছাড়া আর কাহারো সেদিকে যাইবার হুকুম রহিল না। বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিয়া বাহির হইতে ফিরিয়া গেল, সামনাসামনি মৌখিক সহানুভূতি জানাইবার চেষ্টা করিয়া আত্মীয়স্বজন হইয়া গেল ব্যর্থ। যতীন নিজের পচনধরা দেহকে কারো চোখের সামনে বাহির করিতে রাজি হইল না। নিজের ঘরে সে রেডিও বসাইল, স্তূপাকার বই আনিয়া জমা করিল, ফোন বসাইয়া বাড়ির অন্য অংশ এবং বাহিরের জগতের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চাপা শব্দের সংযোগ স্থাপিত করিয়া লইল। জীবন যাপনের প্রথার আকস্মিক পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না।
পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বর্জন করিলেও মহাশ্বেতাকে সে কিন্তু ছাড়িতে পারিল না। নিকটতম আত্মীয়ের দৃষ্টিকে পর্যন্ত পরিহার করিয়া বাঁচিয়া থাকার মতো মনের জোর সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল বলা যায় না কিন্তু মহাশ্বেতার সম্বন্ধে সে শিশুর মতোই দুর্বলচিত্ত হইয়া রহিল। আপনার সংক্রামক ব্যাধিটিকে আপনার দেহের মধ্যেই সংহত করিয়া রাখিয়া মৃত্যু পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া চিতার আগুনে ভস্ম করিয়া ফেলিবার যে অনমনীয় প্রতিজ্ঞা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিল, মনে হইল, মহাশ্বেতাকে সে বুঝি তাহার সেই আত্মপ্রতিশ্রুতির অন্তর্গত করে নাই। আত্মীয়-পর সকলের জন্য সাবধান হইতে গিয়া মহাশ্বেতার বিপদের কথাটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবনটা এতকাল ভাগাভাগি করিয়া আসিয়াছে বলিয়া দেহের এই কদর্য রোগের ভাগটা ও মহাশ্বেতাকে যদি আজ গ্রহণ করিতে হয়, তাহার যেন কিছুই বলিবার নাই।
স্ত্রীকে সে সর্বদা কাছে ডাকে, সব সময় কাছে রাখিতে চেষ্টা করে। কাছে বসিয়া মহাশ্বেতা তার সঙ্গে কথা বলুক, তাকে বই পড়িয়া শোনাক। রেডিওতে ভালো একটা গান বাজিতেছে, পাশাপাশি বসিয়া গানটা না শুনিলে একা ভালো লাগে না। ফোনে সে কার সঙ্গে কথা বলিবে নম্বরটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া কানেকশন লইয়া রিসিভারটা মহাশ্বেতা তাহার হাতে তুলিয়া দিক। আর তা না হয় তো সে শুধু কাছে বসিয়া থাক, যতীন তাহাকে দেখিবে।
মহাশ্বেতা এসব করে। খানিকটা কল-বনিয়া-যাওয়া মানুষের মতো যতীনের নবজাগ্রত সমস্ত খেয়ালের কাছে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যতীন যা বলে নির্বিকার চিত্তে সে তাহাই পালন করিয়া যায়। যতীনের ইচ্ছাকে কখনো সংশোধিত অথবা পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করে না। তাহার নিরবচ্ছিন্ন স্বামীর কথা শুনিয়া চলিবার রকম দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না তাহার নিজেরও স্নানাহারের প্রয়োজন আছে, সুস্থ মানুষের সঙ্গলাভের প্রয়োজন আছে, কিছুক্ষণ আপন মনে একা থাকিবার প্রয়োজন আছে। যতীন খেয়াল করিয়া ছুটি দিলে সে খাইতে যায়, যতীন মনে করাইয়া দিলে বিকালে তাহার একটু বাগানে বেড়ানো হয়। তা না হইলে নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া যতীনের পরিবর্তনশীল ইচ্ছাকে সে অক্লান্ত তৎপরতার সহিত তৃপ্ত করিয়া চলে।
অথচ যাচিয়া সে কিছুই করে না। যতীনের দরকারি সুখসুবিধাগুলির জন্য ধরাবাঁধা যে সব নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলি যথারীতি পালিত হয় কি না এ বিষয়ে সে নজর রাখে কিন্তু যতীনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য, যতীনকে তাহার নিজের খেয়ালে সৃষ্টি করিয়া লওয়া আনন্দের অতিরিক্ত সবকিছু দিবার জন্য, স্বকপোলকল্পিত কোনো উপায় দিন ও রাত্রির চব্বিশটা ঘণ্টার মধ্যে মহাশ্বেতা একটিও আবিষ্কার করে না।
তাহাদের সহযোগ রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে।
তাহাদের জীবনের একটি সমবেত গতি ছিল। জীবনের পথে পাশাপাশি চলিবার কতগুলি রীতি ছিল। সে গতিও এখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে-সব রীতিও গেছে বদলাইয়া। পুরোনো ভালবাসা, পুরোনো প্রীতি, পুরোনো কৌতুক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইয়াছে। বিবাহের চার বছর পরে পরস্পরের সঙ্গে আবার তাহাদের একটি নবতর সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। পূর্বতন বোঝাপড়াগুলি আগাগোড়া বদলাইয়া ফেলিতে হইয়াছে।
প্রথমদিকে যে মুহ্যমান অবস্থাটি তাহাদের আসিয়াছিল সেটুকু কাটিয়া যাওয়ার আগে আপনা হইতে এমন কতকগুলি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে—যাহা খেয়াল করিবার অবসরও তাহাদের থাকে নাই। চিকিৎসার বিপুল আয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া রোগী ও সুস্থ মানুষের শয্যা গিয়াছে পৃথক হইয়া। কথা বলিবার সময় শুধু হাসিয়া কথা বলিবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ বাতিল হইয়া গিয়াছে। যার নাম দাম্পত্যালাপ এবং যাহা নয়টির মধ্যে প্রায় সবগুলি উপভোগ্য রসেই সমৃদ্ধ, দুটি পৃথক শয্যার মাঝে চিড় খাইয়া তাহা নিঃশব্দে মরিয়া গিয়াছে। দিবারাত্রির মধ্যে একটি চুম্বনও আজ আর পৃথিবীর কোথাও অবশিষ্ট নাই। চোখে-চোখে যে ভাষায় তাহারা কথা বলিত সে ভাষা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সবটুকু নয়। এখন চোখের দৃষ্টিতে একটি বিহ্বল শঙ্কিত প্রশ্ন তাহারা ফুটাইয়া তুলিতে পারে। চোখে-চোখে চাহিয়া এখন তাহারা শুধু দেখিতে পায় একটা অবিশ্বাস্য অপ্রকাশিত বেদনা এই জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়া আছে : এ কী হল?
মহাশ্বেতা দিনরাত বোধ হয় এই কথাটাই ভাবে। তাহার ঠোঁট দুটি পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া অহরহ কঠিন হইয়া থাকে, ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এক-এক সময় সে শুধু বেশি বাতাসের প্রয়োজনে জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়, অদৃষ্টকে অভিশাপ দিবার মতো শোনায়।
যতীন অনুযোগ করিয়া বলে : ‘দিনরাত তুমি অমন কর কেন?’
মহাশ্বেতা ঠোঁট নাড়িয়া উচ্চারণ করে : ‘কেমন করি? কিছু করি না তো?’
যতীন হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলে : ‘এমনিতেই আমি মরে আছি, তারপর তুমিও যদি আমার মনে কষ্ট দাও—’
যতীন ভুলিয়া যায়। ভুলিয়া গিয়া সে মহাশ্বেতার হাত চাপিয়া ধরে। প্রথম দিকে তাহার ঘায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা হইত, আজকাল আলো ও বাতাস লাগাইবা জন্য খুলিয়া রাখা হয়। ডাক্তার দিনে পাঁচ-ছয় বার ধুইয়া যতক্ষণ সম্ভব রোদে ঘাগুলি মেলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যান্ডেজ শুধু রাত্রির জন্য।
মহাশ্বেতা তাহার তিনটি চামড়া তোলা ফাটিয়া যাওয়া আঙুলের দিকে চাহিয়া থাকে। আঙুলগুলি তাহার হাতে লাগিয়া আছে বলিয়া বারেকের জন্যও সে শিহরিয়া ওঠে না। মনে হয় যতীন অনুরোধ করিলে তাহার হাতে কনুইয়ের অল্প নিচে টাকার মতো চওড়া যে ক্ষতটি ছোট ছোট রক্তাভ গোটায় উর্বর হইয়া আছে, মহাশ্বেতা সেখানে চুম্বন করিতে পারে।
যতীন হাত সরাইয়া লয়। রাগ করিয়া বলে : ‘তুমি আমায় ঘেন্না করছ শ্বেতা?’
মহাশ্বেতা এ কথা অনুমোদন করিবার সুরে রাগিয়া বলে : ‘কখন আবার ঘেন্না করলাম?’
‘তবে অমন করে তাকাও কেন?’
‘কেমন করে তাকাই?’
এ রকম অবস্থায় এ ধরনের পালটা প্রশ্ন মানুষের সহ্য হয়? যতীন উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বেলা বারটার কড়া রোদে পাতিয়া-রাখা ইজিচেয়ারটিতে কাত হইয়া এলাইয়া পড়ে। বৈশাখী সূর্যের এ অম্লান কিরণ ভালো মানুষের হয়তো পাঁচ মিনিটের বেশি সহ্য হয় না। কিন্তু যতীনের অনুভব-শক্তি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই রোদে নিজেকে মেলিয়া রাখিয়া পড়িয়া থাকে। রোদ সরিয়া গেলে ইজিচেয়ারটাও সে সরাইয়া লইয়া যায়। ডাক্তারের কাছে সে সূর্যালোকের মধ্যে অদৃশ্য আলোর গুণের কথা শুনিয়াছে। সে আলোককে যতীন প্রাণপণে কাজে লাগায়। অপচয় করিতে পারে না।
খানিক পরে ডাকিয়া বলে : ‘এদিকে শোনো শ্বেতা!’
মহাশ্বেতা আসিলে বলে : ‘এইখানে বোসো।’
মহাশ্বেতা যতীনের কাছে ছায়ায় বসে। নিকটবর্তী রোদের ঝাঁজে তাহার ঘর্মাক্ত দেহ শুকাইয়া উঠিয়া জ্বালা করিতে থাকে। কিন্তু সে উঠিয়া যায় না। জ্যোতির্ময়ী পতিব্রতার মতো স্বামীর কাছে বসিয়া ঝিমায়।
যতীন বলে : ‘আমার তেষ্টা পেয়েছে।’ মহাশ্বেতা তাহাকে জল আনিয়া দেয়।
যতীন বলে : ‘আমার আর-একটা বালিশ চাই।’
মহাশ্বেতা তাহাকে আর-একটা বালিশ আনিয়া দেয়।
যতীন বলে : ‘এনে দিলেই হল বুঝি? মাথার নিচে দিয়ে দাও।’
মহাশ্বেতা বালিশটা তাহার মাথার নিচে দিয়া দেয়।
যতীন রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে : ‘কী ভাবছ শুনি?’
মহাশ্বেতা বলে : ‘কী ভাবব?’
বৈশাখী দুপুরটি গুমোটে জমিয়া ওঠে।
রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া মহাশ্বেতা দেখিতে পায় যতীন তার বিছানায় উঠিয়া আসিয়াছে। দেখিয়া মহাশ্বেতা চোখ বোজে। সারা রাত্রি আর সে চোখ খোলে না।
.
এ জগতে সবই যখন ভঙ্গুর, মনুষ্যত্বের ভঙ্গুরতায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই! মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বভাবও ভাঙে গড়ে। আজ যে রাজা ছিল কাল সে ভিখারি হইলে যদি-বা এটুকু বোঝা যায় যে লোকটা চিরকাল ভিখারি ছিল না, তার বেশি আর কিছুই বোঝা যায় না।
সঙ্কীর্ণ কারাগারে নিজের বিষাক্ত চিন্তার সঙ্গে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকিয়া যতীন দিনের পর দিন অমানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। বীভৎস রোগটা তাহার না কমিয়া বাড়িয়াই চলিল, তার সুশ্রী রমণীয় চেহারা কুৎসিত হইয়া গেল। বাহিরের এই কদর্যতা তাহার ভিতরেও ছাপ মারিয়া দিল। তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকাও মুহ্যমানা মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। মেজাজটা যতীনের একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। মাথায় রক্ত চলাচলের মধ্যে তাহার কী গোল বাধিয়াছে বলা যায় না, চোখ দুটি মেজাজের সঙ্গে মানাইয়া দিবারাত্রি আরক্ত হইয়া আছে। গলার আওয়াজ তাহার চাপা ও কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুলগুলি অর্ধেকের বেশি উঠিয়া গিয়া পাতলা হইয়া আসিয়াছে। নাকের রঙটা তাহার তামাটে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মুখের ও দেহের মাংস দেখিলে মনে হয় কত কালের বাসি হইয়া ভিতর হইতে পচন ধরিয়া গাঁজিয়া উঠিয়াছে। কোণঠাসা হিংস্র জন্তুর মতো উগ্র ভীতিকর ব্যবহারে মহাশ্বেতাকে সে সর্বদার জন্য সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে শুরু করিয়াছে।
মানুষের স্তরে আর যে তাহার স্থান নাই যতীন তাহা বুঝিতে পারে। মানুষের শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসা পাওয়ার আশা এ-জীবনের মতো তাহার ঘুচিয়া গিয়াছে। সে কাছে আসিতে দেয় না বলিয়া কেহ তাহার খোঁজখবর নেয় না। এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে সে রাজি নয়। মহাশ্বেতার নির্বাক ও নির্বিকার আত্মসমর্পণকে সে অসাধারণ ঘৃণার অস্বাভাবিক প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। মানুষকে দিবার যতীনের আর কিছুই নাই। সে তাই মানুষের উপর রাগিয়াছে। সে তাই স্বার্থপর হইতে শিখিয়াছে। ব্যথা পাইয়াছে বলিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে কুণ্ঠিত নয়।
নাগাল সে পায় শুধু মহাশ্বেতার। মহাশ্বেতাকেই তাহার ব্যাধি ও ব্যাধিগ্রস্ত মনের ভার বহন করিতে হয়।
সে শান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তার অবসন্ন শিথিল ভাবটাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। মনে হয়, আত্মরক্ষার ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলি আর তাহার ঘুমাইয়া নাই। এবার সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। চিরটাকাল সহমরণে যাইবে না।
যতীনকে সে বলে : ‘কোথাও যাবে?’
যতীন বলে : ‘না।’
‘সমুদ্রের জল লাগালে হয়তো কমত।’
যতীন কুটিল সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে : ‘কমত? তোমার মাথা হত! ডাক্তার ও কথা বলে নি।’
মহাশ্বেতা রাগ করিয়া বলে : ‘ডাক্তারের কথা শুনে তো সবই হচ্ছে।’
খানিক পরে সে আবার বলে : ‘ঠাকুর দেবতার কাছে একবার হত্যে দিয়ে দেখলে হত। হয়তো প্রত্যাদেশটেশ কিছু পেতে।’
যতীন আরক্ত চোখে মহাশ্বেতার সুস্থ সবল দেহটির দিকে চাহিয়া থাকে।
‘নিজের ছেলে খেয়ে ঠাকুর-দেবতায় অত ভক্তি কেন? প্রত্যাদেশ! তোমার মতো পাপিষ্ঠার স্বামীকে ঠাকুর প্রত্যাদেশ দেন না।’
ব্যাপারটা মাসখানেক পুরোনো। যতীন ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়াছে। কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সে বিশ্বাস করে নাই। মহাশ্বেতাকে সন্দেহ করিয়াছে, সন্দেহটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে নিজের তাহাতে প্রত্যয় জন্মাইয়াছে এবং উগ্র উত্তেজনায় একটা পুরা দিন পাগল হইয়া থাকিয়াছে।
মহাশ্বেতা কিছু প্রকাশ করে না। জেরার জবাবে এমন সব কথা বলে যে যতীন বিশ্বাস করিতে পারে না। জোড়াতালি দিবার চেষ্টাটা তাহার ধরা পড়িয়া যায়। তা ছাড়া মহাশ্বেতা এমন এমন ভাব দেখায় যেন এটা সম্পূর্ণভাবে তাহারই ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। এমনো যদি হয় যে এ ব্যাপারে তাহার হাত ছিল, দৈবের চেয়ে সে-ই বেশি দায়ী, বলিবার অধিকার যতীনের নাই। সে তাহার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা তুলিয়া অনর্থক উদ্বিগ্ন হইতেছে। মহাশ্বেতার কপালে দুঃখ ছিল, সব দিক দিয়া বঞ্চিত হওয়ার বিধিলিপি ছিল, সে দুঃখ পাইয়াছে, বঞ্চিত হইয়াছে। যতীনের কী? সে কেন ব্যস্ত হয়?
তার স্বামী বলিয়া যতীন দেবতার প্রত্যাদেশও পাইবে না। এ কথাটা মহাশ্বেতার সহ্য হয় না। সে বলে : ‘ছেলে-ছেলে করে তো মরছ। গুনে জেনেছ ছেলে?’
যতীনের চোখে প্রত্যাদেশকারীর দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে।
‘ছেলে নয়? ওরা যে বলল ছেলে?’
‘আমার চেয়ে ওরা যে বেশি জানে!’
যতীন তখন আর কিছু বলে না। চুপচাপ ভাবিতে থাকে। পরদিন দুপুরে যতীনের রোদটুকু হরণ করিয়া আকাশ ভরিয়া মেঘ জমিলে মহাশ্বেতাকে কাছে, খুব কাছে আহ্বান করে। বাহিরে ব্যাকুল বর্ষণ শুরু হইলে হঠাৎ সে বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া অভিমানের সুরে বলে : ‘মেয়ের বুঝি দাম নেই?’
মহাশ্বেতা অবাক হইয়া বলে : ‘তুমি এখনো সে কথা ভাবছ?’
যতীন বলে : ‘কী করেছিলে? গলা-টিপে তুমি তাকে মারতে পার নি শ্বেতা? না, তাও পেরেছিলে?’
মহাশ্বেতা বলে : ‘আবোল-তাবোল কথার কত জবাব দেব? যা বোঝ না তাই নিয়ে কেবল বকবক করবে। বেঁচে থাকলে কত দুঃখ পেত ভেবে আমি মন ঠাণ্ডা করেছি। তুমি পার না?—কী বৃষ্টিটাই নাবল! দেখি একটু।’
মহাশ্বেতা উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়ায়। বাহিরে অবিশ্রান্ত জল পড়ে আর যতীন অবিরত গাল দেয়। মহাশ্বেতা চোখ দিয়া বর্ষা দ্যাখে আর কান দিয়া স্বামীর কথা শোনে। যতীন যখন বলিতে থাকে যে এ কাজ যে-মেয়েমানুষ করিতে পারে সে যে আর কোনো অন্যায় করিতে পারে না, এ কথা স্বয়ং ভগবান তাহাকে বলিলেও সে বিশ্বাস করিবে না, তখন মহাশ্বেতা একটু হাসে।
একদিন তাহাদের এই কথোপকথন হইয়াছিল :
‘কী পাপে আমার এমন হল শ্বেতা?’
‘তোমার পাপ কেন হবে? আমার কপাল।’
আজ কথা বলিবার ধারা উলটিয়া গিয়াছে। যতীন আজ প্রাণপণে চেঁচাইয়া বলে : ‘তোমার পাপে আমার এমন দশা হয়েছে, ছেলে-খেকো রাক্ষসী। তুমি মরতে পার নি? না, সাধ-আহ্লাদ এখনো মেটে নি? এখনো বুঝি একজন খুব ভালবাসছে?’
এই সন্দেহটাই এখন যতীনের আক্রমণ করার প্রধান অস্ত্রে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মহাশ্বেতার মুখ দেখিলে কারো এ কথা মনে হওয়া উচিত নয় যে সে সুখে আছে। যতীনের দেখিবার ভঙ্গি ভিন্ন। মহাশ্বেতার মুখের ম্লানিমা তার চোখে রূপৈশ্বর্যের মতো লাগে, ওর চোখের ফাঁকা দৃষ্টি যে আজকাল শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে সেটা তার মনে হয় পরিতৃপ্তি। ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা যতীনের কাছে হইয়া উঠিয়াছে সাজসজ্জা। তার দৃষ্টির আড়ালে ওর নেপথ্য জীবনটির পরিসর বাড়াইয়া তোলা যতীনের কাছে গভীর সন্দেহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাকে একা ফেলিয়া সমস্ত দুপুরটা সে কাটায় কোথায়? অন্য ঘরে বিশ্রাম করে? যতীন বিশ্বাস করে না। বিশ্রামের জন্য অন্য ঘরেরই যদি তার প্রয়োজন, যতীনের পাশের ঘরখানা কী দোষ করিয়াছে? নির্জন দুপুরে নিচের তলায় কোনার একটা ঘর ছাড়া ওর বিশ্রাম করা হয় না, বাহির হইতে যে-ঘরে সকলের অগোচরে মানুষ আসা-যাওয়া করিতে পারে?
‘অত বোকা নই আমি, বুঝলে?’
পালটা প্রশ্ন করার অভ্যাসটা মহাশ্বেতার এখনো একেবারে যায় নাই। সে বলে : ‘তোমাকে বোকা কে বলেছে?’
যতীন গোঁ ধরিয়া বলে : ‘ওসব চলবে না। আমার বাড়িতে বসে ওসব তোমার চলবে না, এই তোমাকে আমি বলে দিলাম। এখনো মরি নি আমি।’
‘কী সব বলছ?’
‘বলছি তোমার মাথা আর মুণ্ডু। ওরে বাপরে, চাদ্দিক দিয়ে আমার একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল যে!’
যতীন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মহাশ্বেতা ছবির মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার বিকৃত ক্রন্দন চাহিয়া দেখে। যতীনের আকুলতা যত তীব্ৰ হইয়া ওঠে সে যেন ততই শান্ত হইয়া যায়। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে তাহার চোখে পলক পড়ে, ঘরের দেয়ালে ঝাপসা ছবিগুলি মন্থরগতিতে তাহার চারিদিকে পাক খায়। বাহিরের শব্দগুলি তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে, সে একটু একটু করিয়া তাহা অনুভব করে। তাহার মনে হয়, কে যে কোথায় কাঁদিতেছে।
পাগলামি মহাশ্বেতারও আসিয়াছে বৈকি। তাহা অপরিহার্য। সাধারণ অবস্থায় মানুষ যাহা করে না সে-সব করার নাম পাগলামি। সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে যাহার জীবন, ওসব তাহাকে করিতে হয়। মস্তিষ্কের কতগুলি অভিনব অভ্যাস জন্মিয়া যায়। বন্ধুকে কারো মনে হয় শত্রু, প্রিয়কে কারো মনে হয় অপ্রিয়, জীবনকে কারো মনে হয় সীমাত্তোলিত কৌতুক। দুঃখ দেখিলে কেহ কাঁদিয়াই মরিয়া যায়, কেহ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবে বিকালে চা পান করা হয় নাই বলিয়া মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছে, আকাশে কী আশ্চর্য একটা পাখি উড়িয়া গেল!
মহাশ্বেতা রাত্রে এ ঘরে থাকে না। পাশের ঘরে সে বিছানা পাতে।
যতীন প্রশ্ন করে, ‘কেন?’ সে মুখে কিছু বলে না, ঘরে ঢুকিয়া খিল তুলিয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি জবাবটা সুস্পষ্ট করিয়া রাখে। যতীন রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলে : ‘রিভলবারে গুলি ভরে রাখলাম। কাল সকালে ঘর থেকে বেরুলেই তোমাকে গুলি করব।’
বলে : ‘এ অপমান সহ্য হয় না শ্বেতা! তুমি আমাকে এমন করে ঘেন্না করবে?’
এ ঘরে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত যতীন জাগিয়া থাকে, ও ঘরে মহাশ্বেতা শূন্য বিছানায় নিস্পন্দ অনুসন্ধানে জীবনের অবলম্বন খোঁজে। কত কথা সে ভাবিবার চেষ্টা করে কিন্তু ভাবিতে পারে না, কত কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারে না; সব গোলমাল হইয়া যায়। কুমারী জীবনের স্মৃতি একটা অচিন্তনীয় অনুভূতির মতো মস্তিষ্কের বাহিরে-বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, বিবাহের পর যে চারটা বছর যতীন সুস্থ ছিল, সুরূপ ছিল, সে সময়ের কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করা মাত্র মহাশ্বেতার চিন্তাশক্তি অসাড় হইয়া যায়। জীবনের সেই আদিম নিষ্পাপ উৎসব হইতে সে একেবারে উপস্থিত হয় যতীনের গলিত দেহ ও বিকৃত জীবনকে কেন্দ্র-করা পচা ভাপসানো জীবনে, সেখানে একটি নবজাত শিশু, একটি পরিপুষ্ট বিস্ময়, জন্মিয়া মরিয়া যায়। বারবার জন্মিয়া বারবার মরিয়া যায়।
.
যতীনের মনে যত আলো ছিল সব নিভিয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারে তাহার মনে এককালীন হাস্যকর কত কুসংস্কারের যে জন্ম হইয়াছে, সংখ্যা হয় না। কয়েক দিন ভাবিয়াই প্রত্যাদেশে তাহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। দেবতা একদিন যার কাছে ছিল অলস কল্পনা, ধর্ম ছিল বার্ধক্যের ক্ষতিপূরণ, জ্ঞান ছিল অনমনীয় যুক্তি, আজ সে আশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেবতার যদি দয়া হয়, হয়তো আবার সুস্থ হইয়া ওঠার পথ দেবতাই তাহাকে বলিয়া দিবেন।
কিন্তু কোন দেবতা? তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কামাখ্যা, কোথায় তাহার প্রত্যাদেশ আসিবে?
যতীন নিজে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। মহাশ্বেতাকে সে পরামর্শ করিতে ডাকে।’কোথায় গিয়ে হত্যে দেওয়া ভালো শ্বেতা?
মহাশ্বেতা সবচেয়ে দূরবর্তী একটি পীঠস্থানের নাম স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলে : ‘কামাখ্যায় যাও।’
‘আমি যাব?’ যতীন স্তম্ভিত হইয়া যায় : ‘এ অবস্থায় আমি কী করে যাব?’
মহাশ্বেতা বলে : ‘কে যাবে তবে?’
‘কেন তুমি যাবে। স্বামীর অসুখ হলে স্ত্রী গিয়েই হত্যে দেয়, প্রত্যাদেশ নিয়ে আসে।’
মহাশ্বেতা বলে : ‘আমি? আমি গেলে প্রত্যাদেশ পাব না। ঠাকুর-দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই।
‘বিশ্বাস নেই?’ মন্তব্যটা যতীনের অবিশ্বাস্য মনে হয়।
‘এক ফোঁটাও নয়। হত্যে দেবার কথা ভাবলে আমার হাসি আসে।’
যতীন রাগিয়া ওঠে।
‘তা পাবে না? হাসি তো পাবেই। হাসি নিয়েই যে মেতে আছ। এদিকে স্বামী মরছে, ওদিকে আর একজনের সঙ্গে হাসির হা চলছে। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ!’
মহাশ্বেতা বলে : ‘কার সঙ্গে হাসির হররা চলছে?’
‘তাই যদি জানব তুমি এখনো এ বাড়িতে আছ কী করে?’ যতীন পচনধরা নাক দিয়া সশব্দে নিশ্বাস গ্রহণ করে, গলিত আঙুলগুলি মহাশ্বেতার চোখের সামনে মেলিয়া আর্তনাদের মতো বলিতে থাকে : ‘ভেবো না, ভেবো না, তোমারও হবে! আমার চেয়ে আরো ভয়ানক হবে! এত পাপ কারো সয় না!’
হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন আঙুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোরে জোরে ঘষিয়া দেয়। আগুন দিয়া আগুন ধরানোর মতো সংক্রামক ব্যাধিটাকে সে যেন মহাশ্বেতার দেহে চালান করিয়া দিয়াছে এমনি একটা উগ্র আনন্দে অভিভূত হইয়া বলে : ‘ধরল বলে, তোমাকেও ধরল বলে! আমাকে ঘেন্না করার শাস্তি তোমার জুটল বলে। আর দেরি নেই।’
এই অভিশাপ দেওয়ার পর মহাশ্বেতা যতীনকে একরকম ত্যাগ করিল। সেবা সে প্রায় বন্ধ করিয়া আনিয়াছিল, এবার কাছে আসাও কমাইয়া দিল। সকালে একবার যদি কিছুক্ষণের জন্য আসিয়া যতীনকে সে দেখিয়া যায়, সারা দিন আর তাহার দেখা মেলে না। রাত্রে শোয়ার আগে একবার শুধু উঁকি দিয়া যায়। মুহূর্তের জন্য। পরিহাসের মতো।
যতীন খেপিয়া উঠিয়া মহাশ্বেতাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ি হইতেই তাড়াইয়া দিত কি না বলা যায় না, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সে নিজেই প্রত্যাদেশ আনিতে কামাখ্যায় চলিয়া গেল। যতীনের পীড়াপীড়িতে ক্রুদ্ধ আদেশ ও সকরুণ মিনতিতে মহাশ্বেতা সঙ্গে যাইতে রাজি হইয়াছিল। কিন্তু যাত্রা করার সময় তাহাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। যতীনের এক পিসি বলেন : ‘মহাশ্বেতা কালীঘাটে গিয়াছে। যতীনের চাকরকে সঙ্গে করিয়া যতীনের মোটরে এই খানিক আগে মহাশ্বেতা কালীঘাটে চলিয়া গিয়াছে।’
.
গোড়াপত্তন কালীঘাটেই হইয়াছিল। মহাশ্বেতা যে যতীনকে বলিয়াছিল, ঠাকুর- দেবতায় সে বিশ্বাস করে না এ কথাটা তাহার সত্য নয়। সত্য হইলে যতীনের কামাখ্যা যাওয়ার দিন অত টাকা খরচ করিয়া সে পূজা দিত না, এক ধামা পয়সা ভিখারিদের বিতরণ করিত না।
এ কাজটা মহাশ্বেতা নিজেই করিয়াছিল। মন্দিরে ঢুকিবার পথে দুদিকে সারি দিয়া ভিখারি বসিয়া ছিল। চাকর আর মোটর চালকের হাতে পয়সার ধামাটা তুলিয়া দিয়া আগে আগে চলিতে চলিতে মহাশ্বেতা দুদিকে মুঠা মুঠা পয়সা বিলাইয়াছিল। সে হইয়াছিল এক মহাসমারোহের ব্যাপার। শুধু ভিখারি নয়, ভিক্ষা দেওয়া দেখিতে রাস্তায় লোক জমা হইয়া গিয়াছিল অনেক।
ভিখারিদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীও ছিল বৈকি! হাতে পায়ে কারো ছিল চট বাঁধা, কারো নাক গলিয়া গিয়া একটা গহ্বরে পরিণত হইয়াছিল, কারোর সমস্ত মুখের ফাঁপানো মাংস বড় বড় গোটায় ভরিয়াছিল, কারো কবজির কাছ হইতে দুটি হাত বহুকাল আগে খসিয়া গিয়া ঘা শুকাইয়া হইয়াছিল মসৃণ। এদের পয়সা দিবার সময় মহাশ্বেতার একটি মুষ্টিতে কুলায় নাই। এদের দিয়া এক ধামা পয়সায় কুলানো যায় নাই।
.
বাড়ি ফিরিয়া সেই দিন বিকালে মহাশ্বেতা কুষ্ঠাশ্ৰম খুলিয়াছে।
চাকর সেদিন পথ হইতে পাঁচ জন ভিখারিকে ধরিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দুজন হাজার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভেও এখানে থাকিতে রাজি হয় নাই। বাকি তিনজন সেই হইতে আরাম করিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। খায়-দায় ঘুমায়, আর মহাশ্বেতাকে ক্ষণে ক্ষণে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করায়, আর তাহাদের কাজ নাই। সাত দিনের মধ্যে মহাশ্বেতার আশ্রমবাসীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে একুশ জন।
আত্মীয়স্বজন সকলকে সে ভিন্ন বাড়িতে স্থানান্তরিত করিয়াছে। মাহিনা করা কয়েকজন চাকর-দাসী—মেথর আর বাড়ি-ভরা কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে সে এখানে বাস করে একা। সকালে-বিকালে এদের দেখিয়া যাওয়ার জন্য সে একজন ডাক্তার ঠিক করিয়াছে। দুজন অভিজ্ঞ নার্সের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।
ডাক্তার বলিয়াছে : ‘এখানে আপনাকে কুষ্ঠাশ্ৰম খুলতে দেবে না।’
‘কেন?’
‘শহরের মাঝখানে এ ধরনের আশ্রম কি খুলতে দেয়?’
মহাশ্বেতা আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছে : ‘ওরা তো শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি বাড়ির মধ্যে ভরে বিপদ আরো কমিয়েছি।’
ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিয়াছে : ‘তবু দেবে না। তবে কি জানেন, এসব হল সৎ কাজ। সহজে কেউ বাধা দিতে চায় না। পাড়ার লোকে নালিশ করবে; সে নালিশের তদ্বির হবে, তারপর আপনার কাছে নোটিশ আসবে। তখনো দুমাস আপনি চুপ করে থাকতে পারবেন। ফের আর একটা নোটিশ এলে তখন ধীরে- সুস্থে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন।’
ডাক্তারের এত কথার জবাবে মহাশ্বেতা বলিয়াছে : ‘কুষ্ঠ কি ভয়ানক রোগ ডাক্তারবাবু!’
ডাক্তার তাহার বিপুল অভিজ্ঞতায় আবার অল্প একটু হাসিয়াছে : ‘এ রকম কত রোগ সংসারে আছে! মানুষকে একেবারে নষ্ট করে দেয়, বংশের রক্তধারার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে মিশে থাকে এমন রোগ একটা নয়, মিসেস দত্ত।’
বংশ! পুরুষানুক্রম! কে জানে ডাক্তার কতখানি টের পাইয়াছিল? যতীন শুধু সন্দেহ করিয়া খেপিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়াছিল তাকেই মহাশ্বেতা বঞ্চনা করিয়াছে। ডাক্তার জানিয়াও নির্বিকার হইয়া আছে। হয়তো মনে মনে ডাক্তার সমর্থনও করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে একটু পার্থক্য থাকিবেই।
নার্স ঠিক হওয়ার আগেই যতীন ফিরিয়া আসিল। সে ঠিক প্রত্যাদেশ পায় নাই, কেমন একটা স্বপ্ন দেখিয়াছে যে কুণ্ড হইতে একটি সাদা ফুল আনিয়া মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে সে নীরোগ হইতে পারে। বাড়ি ফেরার আগেই যতীন মাদুলি ধারণ করিয়াছে।
বাড়ির ব্যাপার দেখিয়া তাহার চমক লাগিয়া গেল।
‘এ সব কী করেছ শ্বেতা?’
মহাশ্বেতার মন অনেকটা শান্ত হইয়া আসায় বুদ্ধিটাও তাহার বেশ পরিষ্কার ছিল। সে বলিল : ‘তোমার কল্যাণের জন্যই করেছি। কালীঘাটে একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম, অমন তেজালো সন্ন্যাসী আমি জীবনে কখনো দেখি নি চোখ যেন আগুনের মতো আলো দিচ্ছে। তিনি বললেন : ‘কুষ্ঠাশ্রম কর, তোর স্বামী ভালো হয়ে যাবে।’
মাদুলি ধারণের প্রভাব তখনো যতীনের মনে প্রবল হইয়া আছে। সে অভিভূত হইয়া বলিল : ‘সত্যি?’
‘তোমার কাছে মিছে বলছি? তুমি সে সন্ন্যাসীকে দ্যাখো নি। দেখলে তোমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত! আমাকে কথাগুলি বলে কোন দিকে যে চলে গেলেন কিছুই বুঝতে পারলাম না।’
যতীন আফসোস করিয়া বলিল : ‘একটা ওষুধ-টষুধ যদি চেয়ে নিতে শ্বেতা!’
বাড়ির যে অংশ যতীনের ছিল সে আবার সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাদুলি আর সন্ন্যাসীর ভরসায় মেজাজটা সে অনেকখানি নরম করিয়াই রাখিল।
কিন্তু মহাশ্বেতা কাছে ভেড়ে না। কামাখ্যা যাওয়ার আগে যেমন ছিল তেমনি দূরে দূরে থাকে। কুষ্ঠাশ্ৰম লইয়া সে মাতিয়া উঠিয়াছে। একুশটি অধিবাসীর সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছিলে তার যেন আনন্দের সীমা থাকে না। দিবারাত্রি সে পথে- কুড়ানো এই বিকৃত গলিত মানুষগুলির সেবা করে। মায়ের মতো তাহার মমতা, মায়ের মতো তাহার সেবা। এই পঁচিশটি অসুস্থ পচা পাঁজর দিয়া যেন তাহার বুক তৈরি হইয়াছে, তার হৃদয়ের সবটুকু উষ্ণতা ওরা পায়।
যতীন একদিন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল : ‘তুমি খালি ওদেরি সেবা কর শ্বেতা। আমার দিকে তাকিয়েও দ্যাখ না।’
মহাশ্বেতা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিতে পারিল না।
সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠ রোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে।
এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ বুদ্ধির অনায়াসবোধ্য কথা।
মহাশ্বেতা দেবী তো নয়? সে শুধু কুষ্ঠ-রোগীর বউ।
৭. পূজারির বউ
বাহিরে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত পৃথিবীকে এত রাত্রে শুধু কয়েকটি রহস্যময় শব্দের সাহায্যে চিনিতে হয়। কাদম্বিনীর চোখে ঘুম নাই। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কান পাতিয়া সে রাত্রির প্রত্যেকটি দুর্বোধ্য ভাষা শুনিতে থাকে।
ঝিঁঝির শব্দ এমনই একটানা বিরামহীন যে থাকিয়া থাকিয়া আপনা হইতে তাহার শুনিবার অনুভূতি বিরাম নেয়। চেষ্টা করিয়াও আর যেন ডাক শোনা যায় না। ঘরের পিছনে নিমগাছটার পাতায় সহসা বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যায়, শুকনো আমপাতাগুলো উঠানের এক পাশ হইতে অন্য পাশে উড়িয়া যাওয়ার সময় যেন তাহারা প্রতিধ্বনি করে। দূরে শিয়াল ডাকিয়া ওঠে। তাদের আর্তকণ্ঠ নীরব হইবার পর বহুক্ষণ অবধি গ্রামের কুকুরগুলোর চিৎকার থামিতে চায় না। কাছেই কোথায় একটা প্যাচা বীভৎস চিৎকারে রাত্রিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য কদর্য করিয়া তোলে। খানিক পরে অদূরে বড় রাস্তায় গোরুর গাড়ির চাকার ক্যাচক্যাচ শব্দ ওঠে, গোরুর গলার বাঁধা ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়।
এবং অতি অকস্মাৎ রাত্রির এইসব নিজস্ব শব্দকে ছাপাইয়া উঠিয়া, কাদম্বিনীর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ তুলিয়া দিয়া, প্রতিবেশী রমেশ হাজরার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া ওঠে।
কাদম্বিনী থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া যায়। রমেশ হাজরার বউ ছেলেমানুষ, তার ঘুম ভাঙিতে দেরি হয়। ছেলেটা অনেকক্ষণ কাঁদে। শুনিতে শুনিতে কাদম্বিনীর মাথার মধ্যে তার চেতনা নির্ভরহীন হইয়া যায়। একটা অদ্ভুত সমতলতার অনুভূতি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়া তাকে একপাশে টলাইয়া ফেলিয়া দিতে চায়। কাদম্বিনী সভয়ে চৌকির প্রান্ত দুই হাতে প্রাণপণে চাপিয়া ধরে।
প্রকৃতপক্ষে রমেশ হাজরার ছেলেটার কান্না শুনিবার আশঙ্কাতেই বাসন্তী অমাবস্যার রাত্রিটি কাদম্বিনীর কাছে বিনিদ্র ও শব্দময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। রমেশের বউ ছেলে হওয়ার সময় এখানে ছিল না। বাপের বাড়ি গিয়াছিল। মাসখানেক আগে চার মাসের ছেলে কোলে সে ফিরিয়া আসিয়াছে। তার কয়েক দিন পরেই তার ছেলের কান্না কাদম্বিনী গভীর রাত্রে প্রথম শুনিতে পায়।
আপনার অসহ্য মনোবেদনা নিয়া কাদম্বিনী সেদিন ঘরের বাহিরে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুপদ অনেক বলিয়াও তাহাকে ঘরের মধ্যে নিতে পারে নাই। শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া খানিকক্ষণ তামাক টানিয়া কাদম্বিনীর পাশে বসিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।
এমন সময় রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে মাটির প্রাচীরের ওপাশে শোনা গিয়াছিল ক্ষীণকণ্ঠের কান্না।
কাদম্বিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আতঙ্কে উত্তেজনায় দিশেহারার মতো স্বামীকে সজোরে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।
ওগো, খোকা কাঁদছে। শুনছ? ওগো তুমি শুনছ!
গুরুপদ বলিয়াছিল, রমেশের ছেলে কাঁদছে কাদু। অমন কোরো না। ভয় কী।
কাদম্বিনী অনেকক্ষণ তার কথা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বিস্ফারিত চোখে দু-বাড়ির মাঝখানে প্রাচীরটার পাশে আনারস গাছের ঝোপের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বারবার শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, ওগো না, আমার খোকা কাঁদছে। আমি স্পষ্ট শুনছি আমার খোকার গলা, ওই ঝোপের মধ্যে কাঁদছে। ওই শোনো, শুনছ? আমার খোকার গলা নয়?
তারপর হঠাৎ উন্মাদিনীর মতো উঠানে নামিয়া গিয়া সে আনারসের ঝোপটার দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। গুরুপদ তাকে ধরিয়া রাখে। সহজে কী তাকে আটকানো গিয়াছিল। নিরুদ্দেশের দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খোকা তার উঠানের পাশে ঝোপের মধ্যে কান্না আরম্ভ করিয়াছে মনে করিয়া শোকাতুরা শীর্ণা মেয়েটির দেহে কোথা হইতে বিস্ময়কর শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল কে জানে।
ছাড়ো, নিয়ে আসি। ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও। নদীর ধার থেকে খোকা আমার এতদূর এগিয়ে এসেছে, এইটুকু ও তো আসতে পারবে না।
ছাড়া পাওয়ার জন্য বেশিক্ষণ স্বামীর সঙ্গে সে যুঝিতে পারে নাই। সহসা মূর্ছিতা হইয়া গুরুপদর বুকে এলাইয়া পড়িয়াছিল। সেই তার প্রথম মূর্ছা। শেষ রাত্রির আগে সে মূর্ছা আর ভাঙে নাই।
রমেশ হাজরার বউকেই ছেলে কোলে উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর সেবা করিতে হইয়াছিল। অচৈতন্য স্ত্রীর শিয়রের কাছে বিছানায় পা গুটাইয়া বসিয়া ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে শোয়াইয়া তাকে হাতের চুড়ি বাজাইয়া পাখা নাড়িতে দেখিয়া গুরুপদর কী মনে হইয়াছিল বলা কঠিন। ঘরের আলোটা যে শুধু তার চোখেই নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল এটা ঠিক।
গ্রামের জমিদার মহীপতি বসাক। গুরুপদ তার পিতার আমলে প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরের পূজারি। মন্দিরে রাধাশ্যামের মূর্তি আছে। মূর্তির সৌন্দর্য অপরূপ নিকষ কালো পাথর কুঁদিয়া এ মিলন মূর্তি কোন শিল্পী গড়িয়াছিল আজ তাহা জানা যায় না। কিন্তু তার প্রতিভা বিগ্রহের মধ্যে আজো বাঁচিয়া আছে। দিনের পর দিন পাথরের দেবতা গুরুপদর চিত্তহরণ করিতেছিল। মন্দিরে যথারীতি পূজা ও আরতি করিয়া, ভোগ দিয়া তার সাধ মিটিত না। মন্দিরের দুয়ার বন্ধ করিয়া যখন তার বাড়ি যাওয়ার অবকাশ, টাকার বিনিময়ে দেবসেবার সাময়িক বিরতি, তখনো অনেক সময় সে বহুক্ষণ ধরিয়া বিগ্রহের সামনে চুপচাপ বসিয়া থাকিত। হৃদয়ানন্দের বিনিময়ে দেবতাকে বিনামন্ত্রে বিনা গন্ধপুষ্পে বিনা ধূপ-চন্দনে পূজা করিত।
পরদিন মন্দিরে যাইতে তার দেরি হইয়া গিয়াছিল। মহীপতির বিধবা বোন ভাবিনী একটু পূজা-পাগলা। জাতিতে তাঁতিনি বলিয়া বিগ্রহের কাছে ঘেঁষিবার অধিকার তার ছিল না। মন্দিরের একটা চাবি কিন্তু সে আঁচলে বাঁধিয়া নিয়া বেড়াইত। বিগ্রহকে সেও বোধ হয় ভালবাসিয়াছিল। কাছে না যাইতে পাক মধ্যে মধ্যে মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া চুরি করিয়া দূর হইতে রাধাশ্যামকে দেখিবার সাধ সে দমন করিতে পারিত না। ভোরে মন্দিরে আসিয়া গুরুপদর প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে সেদিন সে এমনই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে দেরি হওয়ায় কৈফিয়তটা আগাগোড়া শুনিয়াও প্রথমে তার একবিন্দু সহানুভূতি হয় নাই।
পূজা শেষ হইলে কিন্তু বলিয়াছিল, কথাটা ভালো নয় ঠাকুরমশায়, দুটো শোক মনে পুষে রেখেছে, তারপর ভারি মাসে মূর্ছাটা হল। শুনে থেকে মনটা কেমন করছে। আপনি এক কাজ করুন, কাদুদিদির নামে সংকল্প করে দুটো ফুল দেবতার পায়ে ছুঁইয়ে সঙ্গে নে যান। কাদুদিদির কপালে ঠেকিয়ে তুলে রাখবেন।
কাদুর কোল শূন্য হইয়া যাওয়া বন্ধ করার জন্য, কাদুকে শান্তি দিবার জন্য, দেবতার সাহায্য গুরুপদ অনেকবারই চাহিয়াছিল। দেবতা তাহার কামনা পূর্ণ করেন নাই। তবু, ভাবিনীর কথায় গুরুপদ ব্যাকুল আগ্রহে পুনরায় মনের কামনা নিবেদন করিয়া দেবতার পায়ে ফুল ছোঁয়াইয়া নিয়া গিয়াছিল।
মনে মনে কোনো দেবতাকেই কাদম্বিনী আর ভালবাসিত না। ঘর-খালি- করা, কোল-খালি-করা, বুক-খালি-করা শোক যাঁরা দেন তাদের কাদম্বিনী ভালবাসিবে কেমন করিয়া? তবু, ফুল পাইয়া তাহার উপকার কম হয় নাই। বিকালের দিকে উঠিয়া সে গুরুপদকে খাইতে দিয়াছিল, ও পাড়ার কানুর মার সঙ্গে আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ গল্প করিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় গা ধুইয়া কিছুক্ষণ আহ্নিক করিতেও বসিয়াছিল। রাত্রে সকাল সকাল শুইয়া সেই যে ঘুমাইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি একবারও তার ঘুম ভাঙে নাই।
তারপর কয়েক দিন তার নিস্তেজ শান্ত ভাবটি বজায় ছিল। পাশের গ্রামে গুরুপদর এক মাসি থাকিত, গুরুপদ নিজে গিয়া মাসিকে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিল। দু-বেলা রান্নার কাজকর্ম মাসিই করিত, কিন্তু গো-সেবা, স্বামী- সেবা আর ঘর দুয়ার সাফ করার কাজে কাদম্বিনী তাকে হাত দিতে দিত না। মাঝে মাঝে পুকুরঘাটে গিয়া সে বাসন মাজিত। কলসি ভরিয়া জলও আনিত। বাগান দিয়া যাওয়া আসার সময় চকিত সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দু পাশে চাহিয়া দেখিত। তার যেন মনে হইত বাড়ির আনাচেকানাচে, বাগানের গাছের আড়ালে তার হারানো ছেলে দুটিকে সে হঠাৎ একসময় দেখিতে পাইবে।
মাসি বলিত—ভারী কাজ নাই বা করলে বউমা? পোড়া গতর নিয়ে আমি তবে রয়েছি কী জন্যে! টুকিটাকি কাজ করতে চাও করো আর নয় বসে বসে কাঁথা সেলাই করে যাও। কম কাঁথা চাই কি! শেষে দেখ কাঁথার জন্যে কত ভুগতে হয়। ক্ষেমির মেয়ে হবার আগে ওকে কত বললাম, বললাম, ও ক্ষেমি, শুয়ে বসে দিন কাটাসনে মা, এই বেলা যখানা পারিস সেলাই করে নে। তা মেয়ে কথা শুনলে না,—ওমা অমন হু হু করে কেঁদে উঠলে কেন বউমা? কেঁদো না বাছা, কেঁদো না, কাঁদতে নেই। অমঙ্গল হয়।
কাদম্বিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, কাঁথা দিয়ে কী হবে মাসিমা? কাঁথায় কে শোবে? কাঁথা যে আমার একবারও পুরোনো হতে পেল না মাসিমা?
মাসি অবশ্য তাঁকে যথারীতি আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়াছিল, কিন্তু কাদম্বিনীর আশ্বাস পাওয়ার অবস্থা নয়। চোখের সামনে সূর্য ওঠে, চোখের সামনে অস্ত যায়। জগতের সর্বোত্তম বিষয় সূর্যের উদয়াস্তে মানুষ বিশ্বাস করে। দু-দুবার কাদম্বিনীর জীবনের সমস্ত অবলম্বন তারই মধ্যে কেন্দ্ৰীভূত হইয়া আসিয়াছে, আসিবার সম্ভাবনা পার হইয়া যাইবার পর, অনেক তৃষ্ণাতুর দিবারাত্রি যাপনের শেষে, অকালে। দুবারই তার চোখের সামনে জীবনের আনন্দ তার চোখের পলকে অস্ত গিয়াছে। উদয়াস্তের এই একত্র সমাবেশেই কাদম্বিনী বিশ্বাস করে। সে বুঝিয়াছে ছেলে তার বাঁচিবে না। ছেলের জন্যে তপস্যা করিয়া অসময়ে সে মাতৃত্বের বর পাইয়াছে। তার মাতৃত্ব আসিবে, সন্তান থাকিবে না, এ কী আর কাদম্বিনীর বুঝিতে বাকি আছে।
তারপর একসময় রমেশের ছেলের একটানা কান্নার মাঝে মাঝে বিরাম পড়িতে লাগিল। খানিক পরে কান্না একেবারেই থামিয়া গেল। এতক্ষণে তার মায়ের ঘুম ভাঙিয়াছে।
কাদম্বিনীর জগতে আর লেশমাত্র শব্দ রহিল না। আপনার চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ার স্তব্ধতা তার চারদিকে ঘেরিয়া আসিল। মধ্যে মধ্যে কেবল গুরুপদর নিশ্বাস ফেলিবার শব্দ তাকে ক্ষণিকের জন্য সচেতন করিয়া দিতে লাগিল।
বসন্তকালের জোরালো বাতাস এক জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া অন্য জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। কাদম্বিনীর মনে হইল, অনেকক্ষণ ধরিয়া তার শীত করিতেছিল। আঁচিলটা সে ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া নিল। রমেশ হাজরার ছেলে আজ রাত্রে আবার কখন কাঁদিয়া উঠিবে ঠিক নাই। কয়েক দিন আগে প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও ছেলেটাকে কাদম্বিনী মধ্যরাত্রে একবারের বেশি কাঁদিতে শোনে নাই। তবু প্রতি মুহূর্তেই কাদম্বিনী তার কান্না শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।
ঘুমের ঘোরে গুরুপদ পাশ ফিরিয়া শুইল। বাহিরে নিমগাছের ডালে প্যাঁচাটা আবার কর্কশ স্বরে ডাকিয়া উঠিল। হঠাৎ স্বামীর উপর কাদম্বিনীর অভিমানের সীমা রহিল না। দুটি সন্তানকে বিসর্জন দিয়া প্রতিরাত্রে মানুষ কেমন করিয়া এমন শান্তভাবে ঘুমাইতে পারে সে ভাবিয়া পাইল না। তার মনে হইল, গুরুপদ হয়তো কোনো দিন দুঃস্বপ্নও দেখে না। হয়তো ওর ঘুমের দেশেও তার খোকারা আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যও উঁকি দিয়া যায় নাই। হয়তো সোনার জ্যোতি ভরা সুখের স্বপ্ন ওর চোখে মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিয়াছে।
কাদম্বিনীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। এতকাল স্বামীকে সে দেবতার মতোই পূজা করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি সজ্ঞান মুহূর্তে স্বামীর সুখসুবিধার চিন্তায় ব্যয় করিয়াছে। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াই তার দুর্বিষহ মর্মবেদনা যেন নিমেষে লঘু হইয়া আসিয়াছে। ধার্মিক সংযত দেবপূজক স্বামীর ভালবাসা পাইয়া চিরদিন সে নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছে। তার বারো বৎসরব্যাপী বিবাহিত জীবনে একদিনের জন্য স্বামীর প্রতি সমালোচনার ভাব তার মনে জাগে নাই। তবু আজ কাদম্বিনী সহসা তার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করিল। তার কণ্টকশয্যার সুখনিদ্রায় নিদ্রিত মানুষটার উপর অশুদ্ধায় তার মন পূৰ্ণ হইয়া গেল।
তার এই সংস্কার-বিরুদ্ধ অভূতপূর্ব মানসিক বিদ্রোহকে বাধা দিবার কোনো চেষ্টাই সে করিল না। দিনের আলোয় সুস্থ মনে যে চিন্তার ছায়াপাত হইলে সে শিহরিয়া উঠিত, এখন রাত্রির অন্ধকারে সেই চিন্তাকেই তার উদ্বেগমথিত মন সযত্নে পোষণ করিয়া রাখিল। গুরুপদকে তার মনে হইল নির্মম, স্বার্থপর। মনে হইল, যে দুঃখ ভগবানের দান বলিয়া এতদিন সে জানিয়া রাখিয়াছিল ভগবান তাহা দেন নাই, গুরুপদই তার জীবনে বারবার এই সর্বনাশ আনিয়া দিয়াছে। দু বার তাকে শেলাঘাত করিয়াও গুরুপদর সাধ মিটে নাই, পুনরায় সেই একই অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছে।
শয্যা ছাড়িয়া কাদম্বিনী মেঝেতে নামিয়া গেল। দু হাতের কনুই মেঝেতে স্থাপন করিয়া করতলে মুখ রাখিয়া সে যেন একটা শারীরিক যন্ত্রণাই সহ্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইখানে, এই কঠিন মেঝের উপরে বিছানা পাতিয়া তার ছেলে দুটিকে সে শোয়াইয়া রাখিত, চৌকিতে গুরুপদ করিত শাস্ত্রপাঠ। কাজে তার মন বসিত না, দশ মিনিট পরপর ঘুমন্ত ছেলেকে না দেখিয়া গিয়া সে স্থির থাকিতে পারিত না, ঘুম ভাঙিয়া কখন ছেলে তার কাঁদিয়া ওঠে শুনিবার জন্য সারাক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। শাস্ত্র পাঠান্তে গুরুপদ যাইত মন্দিরে। মন্দির হইতে ফিরিয়া রমেশ হাজরার সঙ্গে বসিত দাবা খেলিতে। অনেক রাত অবধি হয় মন্দিরে বসিয়া থাকিয়া নয় কারো বাড়ি আড্ডা দিয়া বাড়ি আসিত। তার ছেলের প্রাপ্য সময় ব্যয় করিয়া যে খাদ্য সে প্রস্তুত করিয়া রাখিত তাই আহার করিয়া এমনই নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় রাত কাটাইয়া দিত।
তার ছেলে মরিয়া গেলে তাকে সান্ত্বনা দিত গুরুপদ। নিজের দু-ফোঁটা লোক-দেখানো চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া তাকে বুঝাইত, উপদেশ দিত, তার চোখের জলও মুছিয়া দিবার চেষ্টা করিত। ছেলের মরণে এতটুকু দুঃখ হইলে এ কি গুরুপদ পারিত?
এই স্মৃতিই কাদম্বিনীর চিত্তকে দহন করিতে লাগিল সবচেয়ে বেশি। তার মতো তার স্বামীও যদি পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত, আজ যদি সে স্বামীর শোকাতুর মূর্তি কল্পনায় আনিতে পারিত, মনের জ্বালা বোধ হয় তার অনেকখানি জুড়াইয়া যাইত। কিন্তু সন্তানকে নদীতীরে বিসর্জন দিয়া আসিবার পরেও গুরুপদকে বারেকের তরে আত্মহারা হইতে দেখিয়াছিল বলিয়া কাদম্বিনী স্মরণ করিতে পারিল না। তার মনের মধ্যে গুরুপদ মায়ামমতাহীন অত্যাচারীর রূপ গ্রহণ করিয়া রহিল।
কাদম্বিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। গুরুপদর ঘুমন্ত মুখখানি একবার দেখিবার ইচ্ছা সে দমন করিতে পারিতেছিল না। কুলুঙ্গির উপর দিয়াশলাই ছিল। কাদম্বিনী প্রদীপ জ্বালিল।
আলো প্রথমে তার চোখে সহিল না। দু চোখ টনটন করিয়া উঠিল। সে চোখ বন্ধ করিয়া দিল। বাতাসে প্রদীপ নিভিয়া যাওয়ার উপক্রম করিতেছিল। কাদম্বিনীর রুদ্ধ চোখের পাতায় আলোর রক্তিম সংবাদ এমনই একটা বিরক্তিকর চাঞ্চল্য হইয়া রহিল যে, তার মনের জ্বালা আরো বাড়িয়া গেল। চোখ মেলিয়া স্বামীর বারো বছরের দেখা মুখে এই আলোতে যে কী দেখিতে কী দেখিবে ভাবিয়া তার একটু ভয়ও যেন করিতে লাগিল।
চোখ মেলিয়া চাহিবার পরেও কিছুক্ষণ কাদম্বিনীর এ ভয় কাটিয়া গেল না। ঘরের চারদিকে সে তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু যার মুখ দেখিবার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়াছিল তার দিকে সহসা দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। ঘরের কোণে কাঠের সিন্দুকটার উপর কাদম্বিনী ছেলেকে দুধ খাওয়াইবার পিতলের ঝিনুকটি তুলিয়া রাখিয়াছিল। ব্যবহারের অভাবে ঝিনুকটি মলিন হইয়া গিয়াছে। শোকাচ্ছন্ন এই জড় বস্তুটিকে আজ যেন কাদম্বিনী প্রথম আবিষ্কার করিল এমনিভাবে অনেকক্ষণ সে ঝিনুকটির দিকে চাহিয়া রহিল। তার বুকের মধ্যে স্বামীর বিরুদ্ধে মর্মাহত অভিযোগ আবার যেন নতুন করিয়া উথলিয়া উঠিল। গুরুপদ এমনই পাষাণ যে ওই ঝিনুকটি ছাড়া তার খোকাদের একটি জিনিস ঘরে রাখিতে দেয় নাই। সে পাগলামি করে বলিয়া, খোকার কাঁথা, খোকার বিছানা-বালিশ বুকে চাপিয়া ভগবানের কাছে তারস্বরে মৃত্যু প্রার্থনা করে বলিয়া, সব গুরুপদ নদীতে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছে।
দুটি আরক্ত চোখে একটা অশুভ জ্যোতি নিয়া প্রদীপ উঁচু করিয়া ধরিয়া কাদম্বিনী সমালোচক শত্রুর মতো গুরুপদর মুখের দিকে চাহিয়া স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীর মুখ সে দেখিল না, দেখিল শুধু আপনার দৃষ্টির বিকার। তার মনে হইল, ঘুমন্ত মানুষটার মুখে রেখায় রেখায় তার স্বার্থপর অত্যাচারী প্রকৃতি রূপ নিয়াছে। তাকে নিয়া খেলা করিবার কৌতুককর সাধ মুখের ভাবে সুস্পষ্ট ফুটিয়া আছে।
কাদম্বিনীর হাত হইতে প্রদীপটা পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। প্রদীপের তেল চলকাইয়া তার হাত বাহিয়া বাহুমূল পর্যন্ত গড়াইয়া আসিল। স্বামীর মুখে আপনার বিভ্রান্ত চিত্তের আবিষ্কার তাহাকে মরণাধিক যন্ত্রণা দিতেছিল, তবু সে তেমনইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পৃথিবীতে তার বাঁচিয়া থাকার একমাত্র অবলম্বনকে অন্ধ আবেগের সঙ্গে ভাঙিয়া দিতে লাগিল।
বুঝিতে তাহার আর বাকি রহিল না যে, বাকি জীবনটা তাহার এমনিভাবে কাটিবে। এক মাসের মধ্যে শূন্য কোল তাহার আবার ভরিয়া উঠিবে, ছয় মাসের মধ্যে কোল খালি করিয়া ছেলেকে তাহার গুরুপদ নদীতীরে রাখিয়া আসিবে। মেঝেতে লুটাইয়া মনের সাধে ধুলা মাখিয়া কাঁদিবার অবসরও সে পাইবে না। তার চোখ মুছাইয়া তার গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া গুরুপদ তাকে এই শয্যায় তুলিয়া লইবে। নদীতীরে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য তার খোকাদের প্রত্যাবর্তন সে রহিত করিতে পারিবে না।
কাদম্বিনীর মনে তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের এই ভয়ংকর ছবি ক্ৰমে ক্ৰমে এমনই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে গুরুপদর মুখ তার চোখের সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল। নিজেকে সে দেখিতে পাইল এই ঘরের মৃত্যুশীতল আবহাওয়ায় স্বামীর বক্ষলগ্না পুত্রহন্ত্রী রাক্ষসীর রূপে। শিশুর ক্রন্দনে মুখরিত রাত্রিতে সে এক একটি শিশুকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে আর গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতেছে।
জীবনে আর তার কাজ নাই, উদ্দেশ্য নাই। কাদম্বিনী সরিয়া আসিয়া পিলসুজের উপর প্রদীপ নামাইয়া রাখিল। রমেশের ছেলের কান্নাকে উপলক্ষ করিয়া পরপর অনেকগুলো রাত্রি সে আপনার মৃত সন্তান দুটির সাহচর্যে কাটাইয়াছে, তবু বাঁচিবার একটা ক্ষীণ সাধ গতরাত্রিতেও তার মধ্যে ছিল। এবার ছেলেটি তার বাঁচিতেও পারে এ আশা সে একেবারে ছাড়িতে পারে নাই। আজ আর আশা করিবারও তার সাহস রহিল না। ছেলে হয়তো তার বাঁচিতেও পারে। ভগবানের রাজ্যে অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আর ভাগ্য পরীক্ষার শক্তি কাদম্বিনী নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যদি না বাঁচে? পলকে পলকে হারানোর ভয় বুকে পুষিয়া ছ-মাস এক বছর মানুষ করার পর যদি মরিয়া যায়? বাঁচিয়া থাকিয়া কাদম্বিনী তাহা সহ্য করিবে কেমন করিয়া?
সিন্দুকের উপর পিতলের ঝিনুকটির দিকে শেষবারের মতো তাকাইয়া লইয়া কাদম্বিনী ফুঁ দিয়া প্ৰদীপ নিভাইয়া দিল। গুরুপদর দিকে চাহিবার সাধ আর তাহার ছিল না। স্বামীর সান্নিধ্য তার কাছে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। তার বারো বছরের ঘরকন্না, তার বারো বছরের স্বামী-পূজা আর তার বারো বছরের সুখ-দুঃখের স্মৃতি-ভরা এই নীড় অতিক্রম করিয়া সে যেন কোনো সুদূরতম অর্ধচেতনার দেশে চলিয়া গিয়াছিল, যেখানে আপনার অসহায় একাকিত্বের অনুভূতি ছাড়া মানুষের আর কোনো জ্ঞানই থাকে না। পূর্ণ চেতনার বাস্তব জগতে বহুবার পরিত্যক্ত ইচ্ছায় মানুষ যেখানে চালিত হয়।
মন্দিরের চাবি গুরুপদ কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিত। চাবিটি হাতে নিয়া দুয়ার খুলিয়া কাদম্বিনী বাহিরে চলিয়া গেল। উঠানে দাঁড়াইয়া একবার শুধু সে ক্ষণিকের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর আগাইয়া গিয়া সদরের দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিয়া গেল।
এ পাড়ায় মানুষ ভিড় করিয়া নীড় বাঁধিয়াছে। রাস্তার দু পাশে স্তব্ধ নিঝুম গৃহগুলো একটির পর একটি অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সময় কাদম্বিনীর কান্না আসিতে লাগিল। এই সব গৃহের অধিবাসী প্রত্যেকটি পরিবারকে সে চেনে। কোনো বাড়িতে তার মতো অভিশপ্ত একটি নারীকে খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে না। পুত্রশোক এ পাড়ায় অজ্ঞাত নয়, হয়তো কোনো বাড়ির অন্ধকার কক্ষে পুত্রশোকাতুরা জননী এখন অশ্রুপাত করিতেছে। কিন্তু তার ছেলের মতো অজ্ঞাত কারণে, ঈশ্বরের দুর্বোধ্য অভিশাপে কার ছেলে আজ পর্যন্ত মরিয়া গিয়াছে? গর্ভে সন্তান আসিলে ওদের মধ্যে তার মতো কোন অভাগিনী জানিতে পারিয়াছে, সুস্থ সবল সন্তান তাহার একদিন তারই কোলে সহসা শুকাইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিনের মধ্যে ধনুকের মতো বাঁকিয়া মরিয়া যাইবে?
মন্দিরের সামনে প্রকাণ্ড দিঘি। দিঘির জলে অমাবস্যা রাত্রির উজ্জ্বলতর তারাগুলো ঝিকঝিক করিতেছে। মন্দিরের সোপানে দাঁড়াইয়া কাদম্বিনী কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো দিঘির বিস্তারিত শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তার মনে হইল, মরিবার মতো প্রয়োজন ছাড়া এ দিঘিকে যেন ব্যবহার করিতে নাই। অপরাধ হয়।
মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া কাদম্বিনী ভিতরে প্রবেশ করিল। মন্দিরের কোথায় কোন বস্তু রাখা হয় কিছুই তার অজানা ছিল না। অন্ধকারে অল্প একটু হাতড়াইয়াই পিতলের সবচেয়ে বড় কলসিটি কাদম্বিনী আবিষ্কার করিতে পারিল।
কলসিতে জল ভরা ছিল। কাত করিয়া কাদম্বিনী জল ঢালিয়া ফেলিল। কলসি কাঁখে তুলিয়া আন্দাজে রাধাশ্যামের মূর্তির দিকে মুখ করিয়া সে মনে মনে বলিল, তুমি আমার দুটি ছেলে চুরি করেছ। আমি শুধু তোমার একটি কলসি নিলাম। তোমার ক্ষমা চাই না।
৮. রাজার বউ
কুড়ি বছর বয়স হইতে যামিনী রানী I
যামিনীর স্বামী ভূপতির রাজ্য কিন্তু একটা বড় জমিদারি মাত্র। বছরে লাখ দেড়েক টাকার বেশি আয় হয় না। ভূপতি রাজা শুধু উপাধির জোরে। যামিনীও সুতরাং অভিধান সম্মত আসল রাজার রানী নয়। উপাধির রানী। রাজার বউ।
ভূপতিরা মোটে তিন পুরুষের রাজা।
কলিকাতায় অনেকগুলো অপ্রশস্ত গলি আছে। তাদের একটার মধ্যে মাঝারি সাইজের দোতলা একটি লাল বাড়িতে ভবশঙ্কর রায় নামক এক ব্যক্তি মাসিক আড়াই শত টাকা উপার্জনে বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ করিয়া বাস করে। সন্ধ্যার পর বন্ধুদের তাসের মজলিশে তার মুখে তার পূর্ব পুরুষদের প্রায় ভারতবর্ষেরই সমান একটি জমিদারির কথা শোনা যায়। গল্পের এই তাল জমিদারির তিলটি ভূপতির বর্তমান সাম্রাজ্য।
ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল ভূপতির প্রপিতামহ মহীপতির আমলে। মহীপতি ছিল ভবশঙ্করের শেষ জমিদার পূর্বপুরুষের প্রধান নায়েব। নিজেকে সে বলিত দেওয়ান কিন্তু কর্তা ডাকিতেন নায়েব মশাই বলিয়া! সেই রাগেই কিনা বলা যায় না তলে তলে কী ষড়যন্ত্রই যে মহীপতি করিল, জমিদারি অর্ধেক গেল বিক্রি হইয়া আর অর্ধেক আসিল তাহার কবলে। ভূপতির পিতামহ যদুপতির আমলে বিক্রীত অর্ধেকটা আবার ফিরিয়া আসিল, জমিদারির প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি হইল এবং মরিবার তিন বছর আগে সে হইয়া গেল রাজা যদুপতি রায় চৌধুরি (সরকার), অবন্তীপুর রাজ-এস্টেট।
তার ছেলে গণপতির শেষ বয়সে একটা সাধ জাগিল যে শুধু রাজা নয়, সে মহারাজ হইবে। বংশানুক্রমে অগ্রগতি প্রয়োজন এমনই একটা কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা বোধ হয় তাহার আসিয়াছিল। জমিদারি হইতে তখন বেশ আয় হইত।
মহারাজা হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় গণপতি এত টাকা ঢালিয়া দিয়া গেল যে তাহাতে জমিদারি কিনিলে ছেলেকে হয়তো সে রাজার উপযুক্ত একটা ছোটখাটো রাজ্য দিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু বাড়ানোর পরিবর্তে রাজ্যকে সে ছোটই করিয়া দিয়া গেল।
তার ফলে মুশকিল হইয়াছে ভূপতির। জমিদারির আয়ে রাজা সাজিয়া থাকা সহজ ব্যাপার নয়। আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে বত্রিশ বছর বয়সেই ভূপতির মাথায় একটু টাক দেখা দিয়াছে।
যামিনীর বিবাহের সময় টাকটা অবশ্য ছিল গণপতির মাথায়। ভূপতি তখন তেইশ বছরের যুবক। মাথা ভরা নিকষ কালো চুলে সে তখন চাকরের সাহায্যে সযত্নে সিঁথিই কাটিত।
যামিনী রূপসী। রাজার বউ বলিয়া সে রূপসী নয়, রূপসী বলিয়া রাজার বউ।
সকল রূপের মতো যামিনীর রূপও ঐতিহাসিক। রূপের ইতিহাস ব্যাপারটা এই রকম। চারপুরুষ আগে যে দরিদ্র বংশের প্রত্যেকটি নরনারীর গায়ের রঙ ছিল সাঁওতালদের মতো কালো এবং চেহারা ছিল চীনাদের মতো কুৎসিত, চারপুরুষ ধরিয়া সে বংশের সিন্দুক যদি টাকায় ভরা থাকে তবে দেখা যায় চার পুরুষেই বংশের কালিমা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া রূপ ও শ্রীর স্তূপ জমিয়া গিয়াছে। যামিনী রাজার মেয়ে নয় কিন্তু বনেদি ঘরের মেয়ে, অনেক পুরুষ ধরিয়া তাদের লোহার সিন্দুকে অনেক টাকা। অনেক পুরুষের জমা করা রূপ তাই যামিনীকে রূপকথার রাজকুমারীর বাস্তব প্রতিনিধির মতো সুন্দরী করিয়াছে। পার্থিব তিলোত্তমার মতো বহুকাল ধরিয়া বহু বিভিন্ন রূপসীর রূপ তার মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছে। তার বঙ্কিম ভ্রু হইতে পায়ের গোলাপি নখর পর্যন্ত বিচিত্র রূপরেখা ও বিমিশ্র বর্ণ-লালিত্যের সমাবেশ।
বিবাহের পূর্বে রানী হওয়ার আশীর্বাদ যামিনী অনেক শুনিয়াছিল। কিন্তু রানিত্ব মানুষের ঠিক কী ধরনের অস্তিত্ব সে বিষয়ে কোনো জ্ঞান না থাকায় রানী হওয়ার স্বপ্নও সে দেখিত না, একদিন যে তাকে সত্যসত্যই রানী হইতে হইবে এ ধারণাও রাখিত না। রাজবধূ হইয়া প্রথম বছরটা তার তাই একটু বিহ্বলতা ও ভয়ের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছিল।
ধরনধারণ চালচলন কিছুই তার শিখিতে বাকি ছিল না। বনেদি মুনশিয়ানার সঙ্গে জটিল জীবনকে ঠিকমতো বুনিয়া চলিবার শিক্ষা তাহার জন্মগত। কিন্তু হাজার বনেদি ঘরের মেয়ে হোক, রাজরাজড়ার বাড়িতে ঠিক রক্তমাংসের মানুষই থাকে কি না এ বিষয়ে তার মনে একটা সংশয় বরাবর থাকিয়া গিয়াছিল। তার কুমারী জীবনের রাজারা সকলেই ছিল উপকথা রামায়ণ মহাভারত ও ইতিহাসের অন্তর্গত। অবন্তীপুর রাজ এস্টেটের রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে এ কথা যেদিন সে শুনিয়াছিল সেদিন তার কল্পনায় ভাসিয়া আসিয়াছিল রহস্যস্তব্ধ মর্মর প্রাসাদ, ময়ূর ও হরিণভরা পুষ্পবন, চামর-সেবিত স্বর্ণ সিংহাসন, এবং একদল বিচিত্র উজ্জ্বল বেশধারী গম্ভীর সমুন্নত নরনারী।
আর কোমরে তরোয়াল-ঝোলানো উষ্ণীষধারী অশ্বারোহী একজন রাজকুমার!
অবন্তীপুরে পা দিয়া এক কল্পনাকে সে আবার তাহার মনের কল্পলোকে গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল বটে, অল্প অল্প ভয় তবু তার মনে রহিয়া গেল। বউরানীর পদমর্যাদা কী, তাকে কী বলিতে ও কী করিতে হয়, কোথায় সরলতার সীমা টানিয়া তাকে কতখানি অভিনয় করিয়া চলিতে হয়—এসব জানা না থাকায় প্রথম বছরটা তার দুর্ভাবনার মধ্যে কাটিয়া গিয়াছিল।
স্বামীকে সে বারবার জিজ্ঞাসা করিত,— দোষ করছি না তো? ভুল হচ্ছে না তো আমার?
ভূপতি বলিত—না গো না, দোষও তোমার হচ্ছে না ভুলও তুমি করছ না। সবাই শতমুখে তোমার প্রশংসা করছে।
ত্রুটি হলে বোলো। শুধরে দিয়ো। শিখিয়ে নিয়ো।
তোমার কিছুই শেখাবার নেই, মিনি।
যামিনী ভাবিত, তাই হবে। এ কথা হয়তো মিথ্যা নয়; আমি অনর্থক বিচলিত হই, ভাবি। রাত্রিটা সে বেশ আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়া কাটাইয়া দিত। কিন্তু পরদিন চারদিকে জীবনের অরাজক সমারোহে আবার সে অস্বস্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিত।
তার এই অস্বস্তিকর ভীরুতার কিন্তু কোনোরকম কটু অভিব্যক্তি ছিল না। তার প্রকৃতির একটি অপরূপ নম্রতার মতোই ইহা প্রকাশ পাইত। পাড়ার এমনই একটি অ-বনেদি মেয়েদের আবেষ্টনীর মধ্যে যামিনীকে মানুষ হইতে হইয়াছিল যে নিজের অজ্ঞাতেই তার মধ্যে একটা অহংকার প্রশ্রয় পাইয়াছিল। না বুঝিয়া সে তার চেয়ে ছোটঘরের মেয়েদের মনে ব্যথা দিয়া বসিত। তাদের অভিমান আন্দাজ করিতে পারিলে মনে মনে হাসিয়া ভাবিত, ছোট মনে ছোট মানেটাই এসেছে আগে। আমি হলে এই নিয়ে রাগ করে নিজেকে ছোট করে ফেলতে লজ্জায় মরে যেতাম। তার কথার ব্যবহারে এই অহংকারটুকু বাড়ির লোক ছাড়া আর সকলেরই চোখে পড়িত। অবন্তীপুরে আসিয়া নববধূসুলভ লজ্জা ও সংকোচের তলে এটুকু চাপা পড়িয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু গর্ব লয় পাইলেই স্বভাবের একটি মসৃণ ও মার্জিত মাধুর্য মানুষের সঞ্চিত হইয়া যায় না। কেবল এই সংস্কারটুকু হইলে তার রূপে সকলে অবাক হইয়া যাইত, তার গুণের প্রশংসা করিত এবং তার প্রাপ্য ভালবাসাও সে পাইত। তবে যেরকম পাইয়াছে সেরকম পাইত না। কিন্তু আপনার মৃদু ভীরুতায় সে এমনই মিষ্টি হইয়া উঠিল যে বিনা চেষ্টাতেই সে সকলের চিত্তকে সাধারণ জয় করার একস্তর ঊর্ধ্বে যে জয় করা আছে তাহাই করিয়া ফেলিল। তাদের চেয়ে সামান্য একটু বড় বাড়িতে তাদের চেয়ে সামান্য একটু বেশি বড়লোক পরিবারে আসিয়া শুধু একটি রাজা শব্দকে সমীহ করিয়াই নিজের জন্য পরের বুকে অনির্বচনীয় প্রীতি জাগাইবার দুর্লভ রমণীয়তা যামিনীর অভ্যাস হইয়া গেল।
বিজিত চিত্তগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অপরাজেয় ছিল গণপতির স্ত্রী নগেন্দ্রবালার চিত্ত। সে ছিল মোটা আর ঝাঁজালো, কুইন এলিজাবেথের মতো দুর্ধর্ষ। স্বামী পুত্রকে বশে রাখিতে সে ভালবাসিত। দাসদাসী ও আশ্রিত পরিজনের প্রতি শাসনের তাহার অন্ত ছিল না। নিজেকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত সংসারটাকে পাক খাওয়াইতে না পারিলে তাহার সুখ হইত না। অধিকারের সীমার মধ্যে নিজেকে সে এত বড় করিয়া রাখিত যে তার পায়ে তেল দিয়া দিয়া কোনোরকমে তাহার অনুমতি সংগ্রহ করিতে পারিলে বাড়ির যে কেহ যে কোনো অন্যায় করিতে পারিত।
বউয়ের রূপ দেখিয়া নগেন্দ্রবালা প্রথমে একটু চটিয়াছিল। তাহার এই ঈর্ষাতুর রাগ প্রথম দিকে কিছু কিছু প্রকাশ করিতেও তাহার বাকি থাকে নাই। গোল বাধিত দেবপূজা উপলক্ষে। চিরদিন সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া একটি বৃহত্তর মহত্তর শক্তির কাছে মাথা নত করার জন্য নগেন্দ্রবালার নারী-হৃদয়ের চিরন্তন দুর্বলতা অতৃপ্ত থাকিয়া গিয়াছিল। বেশি বয়সে গৃহদেবতার প্রতি ভক্তি তার তাই উথলিয়া উঠিয়াছিল। দেবতার ভোগ ও আরতি তাহার জীবনে একটা মহা সমারোহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বাড়ির বউকেও সে এইদিকে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। যামিনীর ইহাতে মুশকিলের সীমা থাকে নাই। তার বাপের বাড়িতেও দোল দুর্গোৎসব হয়, কিন্তু নিত্যপূজার ব্যবস্থা সেখানে নাই। পূজাপার্বণের উৎসবের দিকটার সঙ্গেই তাহার পরিচয় ছিল বেশি, ঠাকুরপূজায় ফুল বেলপাতা কোশাকুশি আর নৈবেদ্য লাগে এবং কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া মন্ত্র পড়িতে হয় এর বেশি জ্ঞান তাহার ছিল না। কিন্তু নগেন্দ্রবালার দাবি নিষ্করুণ। এ বাড়ির যে বধূ, ভবিষ্যতের রাজরানী, ঠাকুরপূজা যদি সে না শিখিয়া থাকে আর সব শিক্ষাই জীবনে তার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। না, অবন্তীপুরের রাজপরিবারে নাস্তিকতা চলিবে না।
সে কী বউমা, সে কী কথা? ঠাকুরসেবা না শিখলে মেয়েমানুষ স্বামীসেবার কী জানবে? আসনের কোনদিকে কোশাকুশি রাখতে হয় তাও কি তুমি শেখো নি বাছা? আর আতপচালের নৈবিদ্যি কি অমনি চ্যাপটা করে করতে হয়?
নগেন্দ্রবালা এমনই করিয়া বলিত, আঘাত ও লজ্জা দিয়া।
সে আরো বলিত, না, ভাড়া করা লোকের কাজ এসব নয়। দেবতার কাছে বড়লোকি চলবে না। পরকে দিয়ে স্বামীসেবা হয় না, ঠাকুরের সেবা হবে পরকে দিয়ে! সব করতে হবে নিজেকে। মেঝে ধোয়ার কাজ পর্যন্ত।
যামিনীর হইত ভয়, চোখে আসিত জল। নগেন্দ্ৰবালা পাইত তৃপ্তি।
কিন্তু রূপেগুণে যে বড়, তার নিরীহ আনুগত্য যদি আন্তরিক হয়, বকিয়া যদি তার চোখে জল আনিয়া দেওয়া যায়, নিজস্ব একটা দামি সম্পত্তির মতো ক্রমে ক্রমে তার প্রতি মায়া জন্মে। দেবসেবায় অনভিজ্ঞতা নগেন্দ্রবালার কাছে গুরুতর অপরাধ। কিন্তু নিজেকে শাশুড়ির ভীরু ও উৎসুক শিষ্যা করিয়া নিজের এ অপরাধকেও যামিনী লঘু করিয়া দিল।
তাহাকে বকিবার ক্ষমতা নগেন্দ্রবালার আর রহিল না। বউকে সে ভালবাসিয়া ফেলিল।
.
স্বামীর সঙ্গে যামিনীর যে সম্পর্কটি স্থাপিত হইল তাহা অতুলনীয়। যামিনীকে ভূপতি তাহার সুস্থ মনের নিবিড় কামনা দিয়া জড়াইয়া ধরিল। নারীকে ভালবাসিবার জন্য মানুষের দেহমনে যতগুলো ধর্ম আছে তার সবগুলো দিয়া অপ্রমেয় আবেগের সঙ্গে যামিনীকে সে ভালবাসিল। সে পড়া ছাড়িয়া দিল। মাসে এক বোতল মাত্র শ্যামপেন খাওয়াও সে ছাড়িয়াছে দেখিয়া গণপতি কিছু বলিল না। নগেন্দ্রবালা একটু ঈর্ষা বোধ করিয়াছিল, কিন্তু সেও বউয়ের জন্য ছেলের পড়া ছাড়িয়া দেওয়ায় বাধা দিল না। ভাবিল, তাই হোক, বউ নিয়ে মেতে এ বয়সটা ভালোয় ভালোয় পার হয়ে যাক।
যামিনী প্রথম যেবার বেশিদিনের জন্য অবন্তীপুর আসিল তখন শরৎকাল। শুক্লপক্ষের কয়েকটা রাত্রিতে আকাশের ওই পুরোনো চাঁদটির কাছ হইতে এমন জ্যোৎস্নাই পৃথিবীতে ভাসিয়া আসে যে দেখিলে মানুষের মন কেমন করে। এমনই জ্যোৎস্না উঠিলে অনেক রাত্রে নিদ্রিত রাজপুরীর নিশীথ রহস্যকে অতিক্রম করিয়া ভূপতি আর যামিনী উঠিত ছাদে। আলিসা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তাহারা পৃথিবীকে দেখিত। এদিকে আধাশহর আধাগ্রামখানি নিঃসাড়ে ঘুমাইয়া আছে। হয়তো শুধুই দেখা যায় একটি আধভেজানো জানালায় নিঃসঙ্গ একটি আলো। যামিনী ভাবিত, ওখানে হয়তো তাদেরই মতো ভালবাসার জাগরণ এখনো আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছে। ওদিকে দিঘির জলে থাকিত সোনালি রঙের চমকিত চাঞ্চল্য। দিঘির ওই তীর দিয়া দু পাশে গাছের সারি বসানো নির্জন পথটি কোথায় কতদূরে চলিয়া গিয়াছে।
যামিনী স্বামীর বুক ঘেঁষিয়া আসিত। ওই স্তব্ধ পথটি ধরিয়া পৃথিবী ছাড়িয়া গ্রহতারার কোনো একটা জগতে চলিয়া যাওয়া যায় এমনই একটা কথা ভাবিয়াই সে বোধ হয় ভূপতির দুটি হাত দিয়া নিজেকে বাঁধিয়া ফেলিত।
বলিত—পৃথিবী কতকাল আগে সৃষ্টি হয়েছিল বল না।
পৃথিবী কতকাল ধরিয়া এমন সুন্দর এমন অপার্থিব হইয়া আছে এই ছিল যামিনীর জিজ্ঞাসা। এমনই স্তিমিত জ্যোতির্ময়ী রাত্রে ভূপতির উদাত্ত প্রেমকে অনুভব করিতে করিতে সে প্রায়ই এই ধরনের প্রশ্ন করিত। ভূপতি ইহার জবাব দিত তাহার কানে কানে। বলিত—অনেক দিন আগে গো, অনেক দিন আগে। কোটি বছর আগে। প্রথমে সব অন্ধকার ছিল, তারপর ভগবান বললেন, আলো হোক, অমনই আলো হল। তিনি তারপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন। শুনিয়া নিজেকে যামিনীর এত বেশি ছেলেমানুষ মনে হইত যে সে অসহায়ের মতো প্রশ্ন করিত, আচ্ছা সত্যি ভগবান আছেন?
বিকালে চাকর গালিচা রাখিয়া গিয়াছে। বিছাইয়া ভূপতি তাহাতে বসিত তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইত যামিনী। যামিনীর মুখে পড়িত জ্যোৎস্না আর ভূপতির মুখের পিছনে থাকিত আকাশের পটভূমিকা। ব্যাকুল অন্বেষণের দৃষ্টিতে তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। পরস্পরের মুখের সঙ্গে তাহাদের পরিচয়ের যেন শেষ নাই, কোনো দিন এ রহস্য তারা যেন বুঝিবে না। যামিনী পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিত, ভূপতি চুল সরাইয়া তাহার কপোলে আবৃত অংশটুকু আবিষ্কার করিত। যামিনী চিবুক ধরিয়া স্বামীর মুখ উঁচু করিয়া সে মুখে ফেলিত জ্যোৎস্না। যামিনীর ঘুম আসিলে তাহার অর্ধনিমীলিত চোখের গাঢ় অতল রহস্যকে ভূপতি চুম্বন করিত, যামিনী তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিত বুকে!
আঠার বছরের কচি মেয়ে সে, সে বলিত—জান আমি এখন মরে যেতে পারি। হালকা হাসি তামাশা তাদের বিশেষ ছিল না। তারা খেলা করিত কম। অতর্কিতে যামিনীর খোঁপা যে ভূপতি কখনো খুলিয়া দিত না এমন নয়, নিদ্রিত স্বামীর কপালে বড় করিয়া সিন্দূরের ফোঁটাও যে যামিনী আঁকিত না তাও নয়, কিন্তু ভূপতির টেরি নষ্ট না করিয়া খোঁপা খোলার প্রতিশোধ যামিনীর লওয়া হইত না। ঘুম ভাঙিয়া যামিনীর আঁচলে কপালের সিন্দূর ভূপতির মোছা হইত না। তাদের সহিত অকালমরণ ঘটিত। তারা বুঝিতেও পারিত না কখন তারা গভীর অলৌকিক ভাবাবেগে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া গিয়াছে। যে বয়সে প্রেম বহির্বস্তুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে বেশি, প্রেমকে লইয়া দু জন মানুষ যে বয়সে শিশুর মতো অর্থহীন খেলা খেলে, ধরা দেওয়ার চেয়ে পলাইয়া বেড়ানোই যখন বেশি মজার ব্যাপার, পূর্ণপরিণত বয়স্ক মানুষের মতো তখন তারা সাগরের মতো অতল উদ্বেলিত ভালবাসার বিপজ্জনক বস্তুর অভিনয় করিয়া চলিত।
বিপজ্জনক এই জন্য। মনের পরিণতি তাদের কারো হয় নাই। মনেপ্রাণে ছেলেমানুষ ছাড়া তারা আর কিছুই ছিল না। যে অভিজ্ঞতার স্তূপ সারের মতো মানুষের মনকে উর্বরা করে, বৃহৎ আবেগকে ধারণক্ষম করে, সে অভিজ্ঞতা তাদের জোটে নাই। বেদনাদায়ক মর্মান্তিক প্রেমের আতিশয্যকে সহ্য করিবার জন্য মনের শক্ত হওয়া দরকার, শক্তি থাকা দরকার। এদের মন সেভাবে শক্ত হইবার সুযোগও পায় নাই, সেরকম শক্তিও তাদের ছিল না। অথচ তাদের একজন রাজার ছেলে আর একজন বনেদি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। ওই বয়সেই তারা গম্ভীর হইতে জানিত, জীবনকে একটা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া মনে করিত, পাকা সাজিতে পারিত।
খোলা ছাদে জ্যোৎস্নালোকে তাদের প্রেম যত অলৌলিক হোক সেটাও বয়সের নয়। কিন্তু তাদের উপায় ছিল না! জীবন তাদের হালকা হইতে শেখায় নাই, অথচ জীবনের কোনো গুরুভার আনন্দ ও বেদনাকে বহন করিবার উপযুক্তও করে নাই। পরস্পরের মুখে যখন তাদের হাসি ফুটাইয়া রাখা উচিত ছিল তখন তারা তাই স্তব্ধ বিস্ময়ে পরস্পরের ওষ্ঠে অনুচ্চারিত ভাষা শুনিত, যখন তাদের লুকোচুরি খেলার কথা তারা তখন আত্মহারা পুলকবেদনায় পরস্পরের আরো কাছে ঘেঁষিয়া আসিত।
দুটি লিরিক কবিতা পরস্পরের আশ্রয়ে হইয়া উঠিত মহাকাব্য। জীবনকাব্যের ধরাবাঁধা ছন্দ ও নিয়মাধীন কাব্যরূপের হিসাবে যাহা অসঙ্গতি, যাহা অনিয়ম।
.
যামিনীর বিবাহের তিন বছর পরে অবন্তীপুর রাজবাড়িতে দুটি বিশেষ ঘটনা ঘটিল, গণপতির মৃত্যু ও ভূপতির পুত্রলাভ। এক মাসের মধ্যে নগেন্দ্রবালা হইল রাজমাতা, ভূপতি হইল রাজা আর যামিনী হইল রানী ও ছেলের মা।
রানিত্ব যামিনী এমনিই পাইল, কিন্তু ছেলে তত সহজে মিলিল না। ব্যাপার এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে তার এবং তার ছেলের বাঁচিবার কথা নয়। কলিকাতার তিন জন বড় বড় ডাক্তার কী এক অদ্ভুত উপায়ে তাদের দুজনকে বাঁচাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে কানের কাছে এ কথাও বলিয়া গেলেন যে এই প্রথম এবং এই শেষ। যামিনীর আর ছেলেমেয়ে হইবে না।
না হোক রাজবংশটি রক্ষা পাইয়াছে। ছেলেটা শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে ভূপতির আর একবার বিবাহ না করিলেও চলিবে।
বংশরক্ষা পাওয়ার সান্ত্বনাটি নগেন্দ্রবালার এবং অন্যান্য সকলের, ভূপতির আবার বিবাহ করিতে হইবে না এ আশ্বাস যামিনীর নিজস্ব, আর কারো নয়।
ভূপতির মনোভাব সঠিক জানিবার উপায় ছিল না। রাজা হওয়ার আগেই সে একটু একটু করিয়া বদলাইয়া যাইতেছিল। রাজা হইয়া সে আরো বদলাইয়া গেল।
না, শ্যামপেন অথবা নারী নয়। রাজা হইলেই যে ওসব আপদ আসিয়া জুটিবে এমন কোনো কথা নাই। ভূপতির পরিবর্তন কাব্যের প্রতিশোধ।
কেবল অন্তরের আশ্রয় করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। যামিনীর সঙ্গে সীমাত্তোলিত ভালবাসার খেলা খেলিতে খেলিতে ভূপতি শান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বাহিরে আশ্রয় খুঁজিতেছিল। আশ্রয়ের অভাবও ছিল না তার, যামিনীর জন্য এতদিন বরং সে ইহাকে চলিতেছিল এড়াইয়া। যামিনীর মতো বউ পাইলে হৃদয়ের অনেক প্রয়োজন মিটিয়া যায়, কিন্তু জীবনের দাবি থামে না। ভূপতির কাছে সংসারের দাবি ছিল বিপুল। তার জন্ম মুহূর্তে রাজবাড়ির শতাধিক নরনারী ও দেড় লাখ টাকা আয়ের জমিদারির ভবিষ্যৎ ভার তাহাকেই বাহক বলিয়া দাবি করিয়াছিল। শৈশব হইতে জীবন তাহার বাহিরের সমারোহে ভারাক্রান্ত। তার কাব্যের কোনো দিন শেষ থাকে নাই।
সন্তানের আবির্ভাবে যামিনী ও তাহার মধ্যে যে সাময়িক ছেদ পড়িল সেই সুযোগে ভূপতি তার নিজস্ব জগৎটি তৈরি করিয়া লইল। গণপতির মৃত্যুতে জমিদারির সমস্ত ভার লইতে হওয়ায় অপরিহার্য কর্তব্যের খাতিরে এই জগৎ তার কায়েমি হইয়া গেল। যামিনীর কাছে কোনো কৈফিয়ত দেওয়ারও প্রয়োজন রহিল না।
অনাবশ্যক উৎসাহের সঙ্গে সে তার জমিদারি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। আজ এই বন্ধুর সঙ্গে শিকারে গেল, কাল অমুক গ্রামে বসাইল মেলা, পরশু এক বড় রাজকর্মচারীর সম্মানে মস্ত একটা ভোজ দিল। গণপতির সে পরের যুগের মানুষ, ঘরে-বাহিরে অনেকগুলো সংস্কার সাধনেও তার খুব উৎসাহ দেখা গেল।
মরিতে মরিতে বাঁচিয়া ওঠার ধাক্কায় আর এক ছেলে পাওয়ার আহ্লাদে যামিনী প্রথমটা বেশ ভুলিয়া রহিল। ভূপতির তখন কিছুকালের জন্য—তার প্রয়োজনও ছিল না, সুতরাং সে অভাবও বোধ করিল না। কাঁচা বুকে পাকা ভালবাসা পুষিয়া রাখিতে রাখিতে সেও হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, সেও অন্য আশ্রয় খুঁজিতেছিল।
কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়। ছয় মাসের মধ্যেই তার শরীর সুস্থ হইয়া উঠিল। মাতৃত্ব লাভের অভিনবত্বও আসিল কমিয়া। ছেলে একরকম সেই আঁতুর হইতেই তার ছিল না। সে রাজার ছেলে রাজপুত্র। তার সুস্থ ও সবল দুধমা ও ঘুমপাড়ানো মাসিপিসি ভাড়া করা হইয়াছে। শখ করিয়া ছেলেকে কখনো যদি যামিনী কোলে নেয়, সেটা বাহুল্য মাত্র। প্রয়োজন নয়।
.
তা হোক সে জন্য যামিনীর বিশেষ কোনো আপসোস ছিল না। সে কলম-পেষা কেরানির বউ নয় যে ছেলে মানুষ করার ঝামেলা তাহাকে সহিতে হইবে এবং সেই বিরক্তি দিয়াই আপনার স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া লইবে। বড়লোকের ছেলেরা এমনিভাবেই মানুষ হয়। এ প্রথাকে যামিনী অনুমোদন করে। তা ছাড়া ছেলেকে লইয়া সারা দিন মাতিয়া থাকিলে তার যদি চলিত, এ যদি তার কাম্য হইত যে সন্তানের পিছনে নিজেকে সে ঢালিয়া দিবে, বাধা দিবার কেহ ছিল না। নগেন্দ্রবালা হয়তো একটু খুঁতখুঁত করিত, ভূপতি হয়তো একটু বিরক্ত হইত, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিবার উপায়ের মতো ছেলেকে আঁকড়াইয়া ধরিবার প্রয়োজন হইলে এই সামান্য বাধা যামিনীকে ঠেকাইতে পারিত না। ছেলেকে সে অমন করিয়া চাহিল না। চাহিল ভূপতিকে।
তার দিনগুলোকে একেবারে অচল করিয়া দিবার মতো দূরেই যে ভূপতি বসিয়া গিয়াছে এটা বুঝিতে যামিনীর সময় লাগিল। কিন্তু বুঝিল সে ভালো করিয়াই। কারণ যে অসহ্য প্রেমকে এড়াইয়া ভূপতি কাজ আর অকাজ দিয়া জীবনটা ভরিয়া রাখিতে পারিল, সেই প্রেম ছাড়া যামিনীর আর কোনো অবলম্বন ছিল না।
ব্যাকুল উন্মাদনাময় ভালবাসা বহিয়া বহিয়া তার হৃদয় শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া যাক, ভূপতির সান্নিধ্য সহিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে তার ছুটিয়া পালাইতে ইচ্ছা হোক, কবিতা লিখিবার পর কবি যেমন মরিয়া যায় রাত্রি প্রভাতের পর সারা দিন সে তেমনিভাবে মরিয়া থাকে, ভূপতিকে সে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না। সে নারী, সে বন্দিনী, তার মুক্তি নাই; তার কামনার বিবর্তন চিরদিনের জন্য অসম্ভব হইয়া গিয়াছে।
সে একবার ভালবাসিয়াছে, প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়া পর্যন্ত মুহূর্তের বিরাম না দিয়া সে ভালবাসিবে।
অথচ সাধারণ হিসাবে ধরিলে ভূপতি যে তাকে বিশেষ অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তা বলা যায় না। প্রাথমিক মিলনোচ্ছ্বাস কমিয়া আসিলে যে কোনো সুখী দম্পতির পরস্পরের প্রতি যে পরিমাণ স্বাভাবিক উদাসীনতা আসে, ভূপতির তার বেশি আসে নাই। বাড়ি থাকিলে এবং কাজ না থাকিলে যামিনীর সঙ্গই সে খুঁজিয়া লইত। বিদায় নেওয়ার সময় যামিনী তাকে আরো একটু থাকিতে বলিলে খুশি হইয়াই সে আর একটু তার কাছে থাকিত। যামিনী অনুরোধ করিলে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় কর্তব্যকে অবহেলা করিতেও তাহার বাধিত না। বিনিদ্র যামিনীর সঙ্গে সমানে সে রাত জাগিত না বটে, কিন্তু রাত্রি দশটার মধ্যেই ঘরে আসিত, যামিনীর সঙ্গে গল্প করিত, তাকে আদর করিত, ভালবাসিত। শান্তিপ্রিয় সুখী দম্পতির শান্ত স্বামীর চেয়ে হয়তো এসব সে বেশিই করিত।
কিন্তু গোড়াতে তাদের কিনা সুখী দম্পতির সম্পর্ক ছিল না, ভূপতিকে তাই যামিনীর আগাগোড়া স্তিমিত, অন্যমনস্ক, সুদূর মনে হইত। তার বুক করিত জ্বালা। তার চোখে আসিত জল। স্বামীর নিশ্বাসের শব্দটি কান পাতিয়া শুনিয়া শিহরিয়া সে নিজের মৃত্যু কামনা করিত।
এবং এমনই অপরিবর্তনীয় এই পৃথিবী আর আকাশের গ্রহতারার বিবর্তন যে প্রতি পূর্ণিমা ও পূর্ণিমার আগে-পিছে কতগুলো রাত্রি জ্যোৎস্নায় আলো হইয়া থাকিত। অবন্তীপুর রাজ-এস্টেটের রাজার বউ তখন বিছানায় উঠিয়া বসিত। ব্যাকুল হইয়া ভাবিত, আমার সবই আছে, কিন্তু কী নাই?
স্তরে স্তরে সাজানো তার জীবন, তার রাজ্য আছে, রাজা আছে, প্রেমিক আছে, ছেলে আছে, শতাধিক হৃদয়ের প্রীতি আছে, অতীত ভবিষ্যৎ সবই আছে, পরকাল পর্যন্ত। তবু কী চায় সে? স্বামীর ঘুম ভাঙাইয়া একবার ছাদে যাইতে চায়? শুধু এই কামনা তার? এইটুকু পাইলেই সে পরিতৃপ্ত হইয়া যাইবে।
যামিনী স্বামীর গায়ে হাত রাখিত। কিন্তু তাকে ঠেলিয়া তুলিতে পারিত না। তার কান্না আসিত। তার সীমাহীন দুঃসহ প্রেমের মতো ক্রন্দনবেগে সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত।
সকালে বলিত—কাল এমন সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছিল।
ভূপতি বলিত—দেখেছি। রাত্রে একবার উঠেছিলাম।
যামিনী তখন হাই তুলিয়া বলিত—জানো গো, কাল রাতে আমার ভালো ঘুম হয় নি।
ভূপতি বলিত—আমায় ডাকলে না কেন? গল্প করে তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিতাম।
গল্প? হায় ভগবান, রাত জাগিয়া গল্প! যামিনীর মনের ভাবটা হইত এই রকম।
সংসারে রাজার বউকে কম কর্তব্য পালন করিতে হয় না। যামিনীরও অনেক কাজ ছিল। গণপতির মৃত্যুর পর নগেন্দ্রবালা অল্পে অল্পে রানিত্বের বোঝা বউয়ের কাঁধে নামাইয়া দিতেছিল। ইহলোকে কর্তৃত্ব করিবার সাধ বোধ হয় তার মিটিয়াছিল, এবার পরলোককে আয়ত্ত না করিলেই নয়। এই চেষ্টা করিতে করিতে বছর দুই পরে সে ওইখানে চলিয়া গেল। যামিনীর কাজের আর অন্ত রহিল না।
বিচিত্র সে কাজ। ঠাকুরের নৈবেদ্য সাজানো ছাড়া নিজের হাতে কিছুই করিবার নাই, চারদিকে শুধু নজর রাখা, হুকুম দেওয়া, আর এর নালিশ, ওর তোষামোদ, তার প্রার্থনা শোনা। রাজ সিংহাসনের যেমন একদিনের জন্যও রাজহীন হওয়া চলে না, রাজ-অন্তঃপুরেরও তেমনই অহরহ কেন্দ্র চাই। যামিনীর কিছুই ভালো লাগিত না, কিন্তু সে ছিল নিরুপায়। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে চাহিয়া নয়, নিজের প্রয়োজনেই রাজ-সংসার তাকে ঘিরিয়া পাক খাইতে লাগিল।
তারপর ছিল প্রসাধন। দুজন দাসীর সাহায্যেও প্রত্যেক দিন প্রসাধনে যামিনীর অনেক সময় লাগিয়া যাইত। গন্ধতেলে খোঁপা বাঁধিলেই শুধু চলিত না, চুলে তেল বেশি না পড়ে আবার কমও না হয় এটা খেয়াল রাখিয়া একটু একটু করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তেল মাখিতে হইত। চোখে অদৃশ্য কাজল পরানোর কাজটা এমন সূক্ষ্ম যে বিস্তারিত ভূমিকা না করিয়া দাসী তুলি তুলিতে সাহস পাইত না। দুধের সর-ভিজানো জলে চার-পাঁচ বার মুখ ভিজাইতে, বাহুতে চন্দন মাখাইয়া মুছিয়া তুলিতে, পায়ে আলতা পরিতে এবং এমনই সব আরো অনেক কিছু করিতে আকাশের কত উঁচুর সূর্যটি গাছের শিয়রে নামিয়া যাইত!
এত পদ্ধতি নিয়ম, অভ্যাসও যামিনীর ছিল। কিন্তু এখন তার বিরক্তির সীমা থাকিত না। ভিতরে ভিতরে মানুষ যখন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইতেছে, বাহিরে তখন এত ঢং কেন?
খোকা এখন একটু বড় হইয়াছিল। দুধমা ও মাসিপিসির ব্যূহ অনেকটা ভাঙিয়া গিয়াছিল। যামিনীর ছেলে আবার ক্রমে ক্রমে সরিয়া আসিতেছিল যামিনীরই কাছে। তার হাসিকান্নার মাকে তার প্রয়োজন হইতেছিল। রাশি রাশি পুতুল লইয়া একা সে খেলিবে না, যামিনীর যোগ দেওয়া চাই। খেলায় শান্তি আসিলে যামিনীর কোলে বসিয়াই সে গম্ভীর মুখে উদাসীন চোখে ছড়ানো পুতুলগুলোর দিকে চাহিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়িবে। মা চাহিয়া না দেখিলে বাগানে সে ছুটাছুটি করিবে না। মার পিঠ ছাড়া আর কারো পিঠে সে আচমকা ঝাঁপাইয়া পড়িবে না, মা তোষামোদ না করিলে দুধ তাকে কেহ খাওয়াইতে পারিবে না। দুপুর রাতে ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে যামিনী উঠিয়া তার কাছে না গেলে কান্না তার থামিবে না। শিশুর চেয়ে স্বার্থপর জীবন জগতে নাই। ওদের মানুষের মূল্য যাচাই নির্ভুল। এই বৃহৎ সংসারে কোন মানুষটার দাম সকলের চেয়ে বেশি কারো বলিয়া দিবার অপেক্ষা না রাখিয়া খোকা নিজেই তাহা স্থির করিয়া লইয়াছিল।
যমিনীর মন্দ লাগিত না। আরো বেশি ভালো যাতে লাগে সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টাও সে করিত। কিন্তু অনেক দেরি হইয়া গিয়াছে। স্বামীর উত্তাল ভালবাসার জন্য তীব্র অপূরণীয় ক্ষুধা তার অস্তিত্বের স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন ধর্মে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখন আর তাকে বদলানো যায় না, বিকৃত করা চলে না। স্বামীর অনায়ত্ত স্পর্শকে শুধু কল্পনায় অনুভব করিয়া তার চলিতে পারে কিন্তু তার বদলে খোকাকে বুকে চাপিয়া সাধ মেটানো যায় না।
কল্পনাকে যামিনী বিস্ময়কর পটুতার সঙ্গে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নিজেকে সে যেন দুটি ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিল। এক ভাগ দিয়া সে তাহার সাধারণ জীবনটা যাপন করিয়া যাইত, রানী সাজিয়া থাকিত, স্ত্রী ও মাতার কর্তব্য পালন করিত, দৈনন্দিন জীবনের ছোটবড় সুখ-দুঃখের নিজস্ব অংশটি গ্রহণ করিত। অন্য ভাগ দিয়া সে করিত কল্পনা। নিয়মে বাঁধা সচল জীবনের আড়ালে অবসর রচনা করিয়া লইয়া আপনার অচল জীবনকে মনে মনে সে গতি দিত। তার সর্বাঙ্গ উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, চোখে ফুটিয়া উঠিত উজ্জ্বল অপার্থিব জ্যোতি, একটা উত্তেজিত উল্লাসে তার রক্তের গতি চঞ্চল হইয়া উঠিত। কোথায় পড়িয়া থাকিত এই রাজবাড়ি আর রাজা আর রাজপুত্র, দিনের পর দিন ধরিয়া নিঃসঙ্গ বিরহী মুহূর্তগুলোতে তিল তিল করিয়া সৃজিত বাস্তবধর্মী কল্পলোকে যামিনীর বিবাহের প্রথম বৎসরটি বারংবার আবর্তন চলিত।
জ্যোৎস্নারাতে যামিনী একাই উঠিত গিয়া ছাদে।
প্রথমে আলিসা ঘেঁষিয়া সে নিঝুম হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। হয়তো বা কোনো দিন প্রথমদিকে তার দু-চোখ জলে ভরিয়া আসিত। ঘুমন্ত স্বামীকে, নিস্তেজ বাস্তব জীবনকে সদ্য সদ্য পিছনে ফেলিয়া আসিয়া সহসা সে কল্পনাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিতে পারিত না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আকাশপাতাল ভাবিত। তার বিরহবিধুর জগতে জাগিয়া থাকিত শুধু কাছের একটি নিঃসঙ্গ বটগাছ, দূরের একটি আলো, আকাশের একক চাঁদ। আজো দু-সারি গাছের মাঝখানে সেই জনহীন পথটি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোনো কোনো দিন ওই পথটির সংকেতও যামিনীর কাছে ভাষার মতো সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। পথের গোড়া হইতে শুরু করিয়া ধীরে ধীরে সে দৃষ্টিকে লইয়া যাইত দূরের অস্পষ্টতায়, থামিত সেইখানে। শঙ্কিত সন্দেহে ওইখানে সে অনেকক্ষণ থামিয়া থাকিত।
তারপর একসময় শুরু হইত তার কল্পনা। ভূপতির একটি অবিচ্ছিন্ন নিবিড় আলিঙ্গন তাকে ঘিরিয়া নামিয়া আসিত, তার শ্বাসরোধী প্রেমকে অনুভব করিয়া যামিনীর হৃদয় অধীর আগ্রহে স্পন্দিত হইতে থাকিত।
এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বত্রিশ বছর বয়সে ভূপতির মাথায় একটু টাক দেখা দিয়াছিল। শুধু তাই নয়। মাথার মধ্যেও এই সময় তার অল্প অল্প যন্ত্রণা বোধ আরম্ভ হইল। ডাক্তার ছয় মাস দার্জিলিংয়ে বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন।
ভূপতি ঠাণ্ডা দেশ পছন্দ করে না। বাহির হইতে মৃদু উত্তাপ পাইতেই তার ভালো লাগে। দার্জিলিংয়ের বদলে সে বোম্বে যাওয়া ঠিক করিল। বোম্বে অনেক দূর। ভূপতি দূরেও যাইতে চায়।
যামিনীকে তার সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না।
ওকে সে এখনো ভয় করে। ওকে উপলক্ষ করিয়া তার সেই আদিম উন্মত্ততা ভূপতি এখনো ভোলো নাই।
কিন্তু যামিনী বলিল—আমিও যাব।
ভূপতি আপত্তি করিয়া বলিল-তুমি গিয়ে কী করবে?
যামিনী সজল চোখে বলিল-তোমার কাছে থাকব। আমায় না নিয়ে গেলে আমি মরে যাব।
শুনিয়া ভূপতি অবাক হইয়া গেল। জীবনের কী একটা বিস্তৃত রহস্য প্রভাতের কুয়াশা হইতে মধ্যাহ্নের আকাশে দেখা দিয়াছে।
বোম্বে গিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ভূপতির ভারী মাথা হালকা হইয়া গেল। দিনগুলো এখানে অলস, বৈচিত্র্যহীন। এখানে উকিল-মোক্তার নাই, রাজ্য বিস্তার নাই, প্রজাশাসন নাই। প্রভুত্ব হ্রস্ব, বিরক্তি স্বল্প, বৈচিত্র্য অপ্রতুল। সে আর যামিনীর মধ্যে এখানে আড়াল কম। খোকা যতদিন রহিল তাকে একরকম মাঝখানে খাড়া করিয়া রাখা গেল। কিন্তু সে এখন বড় হইয়াছে। নামকুমের স্কুলে সে বোর্ডিংয়ে থাকিয়া পড়ে। নিজেদের প্রয়োজনে শিক্ষায় ব্যাঘাত দিয়া তাকেও বেশিদিন আটকাইয়া রাখা গেল না।
ভূপতি নিরাশ্রয় অসহায় হইয়া পড়িল।
তাই একদিন সে যামিনীকে বলিল। তুমি এখনো তেমনই আছ মিনি, প্রায় তেমনই আছ।
যামিনী বলিল-তাই কি কেউ থাকে? আমি কত বদলে গিয়েছি।
তারা পরস্পরের চোখের দিকে চাহিল। কিন্তু পরস্পরকে তারা আর খুঁজিয়া পায় না।
না শীত, না গ্রীষ্ম। বোম্বের আবহাওয়া ধর্মহীন, নিরপেক্ষ। বোম্বের পথ দিয়া জগতের যাবতীয় ধর্মের লোক চলাচল করে। বোম্বে শহর ঘুমায় এবং জাগে, বোম্বের আকাশে চাঁদ উঠিতে ছাড়ে না। অবন্তীপুরের রাজা জীবনের যে স্তরগুলো দেশে নামাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে তার তলাকার স্তরগুলো ধীরে ধীরে প্রাণসঞ্চার করে, ইটের সমাধিমুক্ত মুমূর্ষু সাদা ঘাসের মতো।
ভূপতির ভয় করে, ইচ্ছাশক্তির নিচে আবার সে এই প্ৰাণকামী কামনাগুলোকে চাপা দিতে চায়, অবন্তীপুরে ফিরিয়া যাওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বড় যার দাবি তাকে ঠেকানো যায় না। জাগরণকে একদিন হয়তো ঘুমের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু ঘুম যখন ভাঙিতে থাকে জাগিয়া ওঠাকে তখন আর কিছুতেই এড়ানো যায় না।
প্রথমে ভূপতি বুঝি ভাবিয়াছিল, যামিনী আজো তেমনই আছে। ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতে শিখিয়া এ ভুল তার ভাঙিয়া যায়। যামিনীকে এখনো চাহিলেই পাওয়া যায় সেই সঙ্গে কী যেন পাওয়া যায় না। স্বামীর বাহুবেষ্টনের মধ্যেও যামিনীর একদিন যেমন তাকে স্তিমিত, সুদূর অন্যমনস্ক মনে হইত এবং এখনো খেয়াল করিলে হয়, আজ যামিনীকেও ভূপতির তেমনই নিস্তেজ তেমনই ঘুমন্ত মনে হইতে থাকে।
স্বামীর নবজাগ্রত প্রেমকে যামিনী গ্রহণ করিতে পারে না। সে তার কল্পনাকে লইয়া দিন কাটায়। তার অর্ধনিমীলিত চোখে ভূপতি যখন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার পূর্বপরিচিত অতল রহস্যকে সন্ধান করে যামিনী তখন অন্য একজন ভূপতির স্বপ্ন দ্যাখে, অন্য একজন ভূপতির দু চোখ ভরা ব্যগ্র উৎসুক প্রেমকে যাচিয়া লয়।
নিশীথ রাত্রে ভূপতি বিনিদ্র চোখে বসিয়া থাকে বিছানায়। যামিনী মৃদু মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া ঘুমায়।
সকালে ভূপতি বলে—-কাল ভালো ঘুম হয় নি মিনি।
যামিনী বলে মাথা ধরেছিল? আমায় ডাক নি কেন? আজ আবার ওষুধটা তা হলে খাও।
একদিন অপরাহ্ণে তারা ভেহার লেকে বেড়াইতে গিয়াছিল। এই লেক হইতে বোম্বে শহরের জলার্থীদের জল সরবরাহ করা হয়। দৃশ্য ভারি সুন্দর! অনেকে লেকের ধারে পিকনিক করিতে যায়।
ভূপতির পাশে বসিয়া তাকে যামিনী ভুলিয়া গিয়াছিল। চারদিকে চাহিয়া দেখিতেই তার ভালো লাগিতেছে, ভূপতির সান্নিধ্য অনুভব করিবার তার অবসর ছিল না। চারদিকে কত গাছপালা, সবগুলির নামও সে জানে না। কাছের কতকগুলি পামগাছের গোড়া হইতে ডগা পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু খানিক দূরে জলের কাছাকাছি এক স্তূপ সবুজ রহস্যের মধ্যে আট-দশটা গাছ প্রোথিত হইয়া আছে। ওই গাছগুলি আর তার মাঝখানে লেকের তীর নিচু, লেকের জল ভিতরের দিকে ঠেলিয়া আসিয়াছে। চার-পাঁচটি বোবা পশু ওখানে জল খাইতে নামিল। ওপারে এলায়িত পাহাড়। জল গোড়া ছুঁইয়া আছে।
হঠাৎ ভূপতি যামিনীর একখানি হাত দু হাতের মুঠায় শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। এত জোরে ধরিল যে যামিনীর তাতে ব্যথা পাওয়ার কথা।
যামিনী মুখ ফিরাইয়া অবাক হইয়া গেল।
কী হয়েছে? হাতে লাগে যে আমার?
কিন্তু সেদিন লাগিত না।
ভূপতি তার হাত ছাড়িয়া দিল। তার মুখ দেখিয়া যামিনীর সবই বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই সে বুঝিল না। একটা সন্দেহ করিয়া পরম স্নেহে আবার জিজ্ঞাসা করিল—কী হয়েছে? অসুখ বোধ করছ?
ভূপতি বলিল—না। অসুখ নয়।
যামিনী তার দিকে আর একটু সরিয়া গিয়া নিজের ব্যথিত হাতখানা তার লজ্জিত হাতের উপর রাখিয়া ওপারের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিল। ভূপতি যাহা চায় তার মধ্যে তাহা আছে, তাহাদের সেই অনির্বচনীয় অতৃপ্ত প্রেম। কিন্তু তার নাগাল পাইতেছে না। একদিন হয়তো যামিনীর কল্পনা থামিয়া যাইবে, হয়তো আকুল হইয়া আজ রাত্রেই অন্ধকারে সে এই বাস্তব ভূপতিকে খুঁজিবে, কিন্তু ভূপতি তখন হয়তো জাগিয়া নাই। আবার কাল রাত্রে ভূপতি যখন আলো জ্বালিয়া অপলক চোখে তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে, সে হয়তো তখন ঘুমাইয়া আছে। একসঙ্গে তারা যে আজ পরস্পরকে দাবি করিবে তার বাধা অনেক।
৯. উদারচরিতানামের বউ
যতীনের মতো মজলিশি মিশুক মানুষ দেখা যায় না। বেঁটে গোলগাল মানুষটা, চিকন চামড়া ঢাকা একটু চ্যাপটা ধরনের মুখখানিতে হাসিখুশি ভাবটাই বেশি সময় বজায় থাকে, তবে সময়বিশেষে সমবেদনাভরা গাম্ভীর্য, সংশয়ভরা জিজ্ঞাসু আশঙ্কা, বিচারহীন নির্বিকার ক্ষমা, দুঃখ, ক্ষোভ, মায়ামোহ এসব ভাবও এমন পরিষ্কার ফুটিয়া থাকে যে পটের ছবিও তার চেয়ে স্পষ্ট নয়। গলার আওয়াজটা একটু মোটা। কিন্তু কথা শুনিয়া মনে হয় মিষ্টত্ব একটু বেশিরকম ঘন হইয়া পড়ার জন্যই বুঝি এটা হইয়াছে। কথা সে যে খুব বেশি বলে তা নয়, যা বলে তাতেই সকলের প্রাণ জুড়াইয়া যায়। ভালো, মন্দ, ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত, বোকা, বুদ্ধিমান সকলেই ভাবে কী, উঁহু, লোকটা আমার চেয়ে একটুখানি অধম যদিবা হয় উত্তম একেবারেই নয়, সমানই বরং বলা চলে সব বিষয়ে, আমার আপনজনের মতো।
যতীনের কয়েকটা দোষ সকলে অনুমোদন করে না, তার মধ্যে প্রধান মেলামেশা আর খাতির করায় বাছবিচারের অভাব। সমজ্ঞানী অবশ্য যতীন নয়। প্রতিবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামদাসকে মাঝে মাঝে অকারণেই ভক্তিভরে প্রণাম করে বলিয়া বাড়ির সামনে ফুটপাতে যে মুচিটি বসিয়া থাকে তাকে দিয়া জুতা সারাই করাইয়া নেওয়ার পরে যে পায়ের ধুলা মাথায় নেয় তা নয়, তবে যতক্ষণ সে জুতাটা সারাই করে হয়তো সামনে উবু হইয়া বসিয়া সুখদুঃখের গল্প জুড়িয়া দেয়। ব্যাঙ্কের টাকার পরিমাণে যে বড়লোক যতটা সম্মান চায় যতীন তাকে হয়তো বেশিই দেয় তার চেয়ে, আর যে গরিব মানুষটি উপযুক্ত পরিমাণে অবহেলা না পাইলে দারুণ অস্বস্তি বোধ করে তাকে, তাকেও যথেষ্ট পরিমাণে অবহেলা দিতেও তার বাধে না। তবু বড়লোক আর গরিব দুজনেরই মনে হয়, দুজনকেই যেন সে সমানভাবে আপন করিয়াছে : বাপ আর ছেলের সঙ্গে দু রকম ব্যবহার করিয়াও কুটুম্ব যেমন দুজনের সঙ্গেই সমান কুটুম্বিতা বজায় রাখে। এটা সকলের ভালো লাগে না, মৃদু ঈর্ষার জ্বালায় মনটা খুঁতখুঁত করে।
বাড়িতে হরদম লোক আসে, বাপের আমলের মাঝারি আকারের বাড়িটিতে। ছুটির দিন হয়তো এত লোক আসিয়া হাজির হয় যে ছোটখাটো বসিবার ঘরটিতে জায়গা হয় না।
যতীন বলে, চলুন দাদা, ওপরে যাই সবাই মিলে।
কেউ কেউ আপত্তি করে, না না, থাক গে। মেয়েদের অসুবিধে হবে।
অসুবিধে হবে? আহত বিস্ময়ে যতীন এমন করিয়া বক্তার মুখের দিকে তাকায় যে মনে হয় গালে চড় মারিয়াই যেন তাকে আহত আর বিস্মিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তার বন্ধুরা বাড়ির ভিতরে গেলে মেয়েদের অসুবিধা হইবে!
বিনা খবরে সদলবলে যতীন অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়ে। মেয়েরা চটপট রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, শোয়ার ঘরে আর আনাচেকানাচে আশ্রয় নেয়। যতীনের বউ শতদলবাসিনী ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া জলের ডেকচি উনানে চাপাইয়া দেয়—এখনই সকলকে চা দিতে হইবে।
যতীন এক ফাঁকে চট করিয়া রান্নাঘরে আসে। —চা হল? শতদলবাসিনী বলে, জল চাপিয়েছি। আন্দাজ কত কাপ? এই ধর কাপ চল্লিশেক?—পান পাঠিয়ো কিন্তু
ছুটির দিনের পান সাজার দায়িত্ব সেজো ননদ কৃষ্ণার, বিবাহ হইয়া যতদিন না পরের বাড়ি যায়। জল গরম হইতে হইতে পানের খবরটা আনিতে গিয়া শতদলবাসিনী দ্যাখে কী, পান সাজা হইয়াছে মোট পাঁচ-সাতটি, পান সাজার সরঞ্জাম সামনে নিয়া কৃষ্ণা মশগুল হইয়া পড়িতেছে চিঠি। হাতের লেখা চেনা, কার চিঠি তাও জানা।
ঠাকুরঝি!
কৃষ্ণা চমকায়, থতমত খায়, চিঠিখানা ব্লাউজের আড়ালে চালান করিয়া দেয়, ঢোক গেলে।—এই হয়ে গেল বউদি, এক্ষুনি সেজে দিচ্ছি।
চুলোয় যাক তোমার সাজা, ফের আরম্ভ করেছ? দু দিন বাদে তোর বিয়ে, আর তুই—
লিখলে আমি কী করব? আমি তো লিখি না।
লেখো না কীসের, জবাব না পেয়েও সে চিঠির পর চিঠি দিয়ে যাচ্ছে। এবার কিন্তু ওঁকে সব বলব আমি, আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। একটা কিছু ঘটুক, আর সবাই আমায় দুষুক, জেনেও চুপ করে ছিলাম।
টুকটুকে রাঙা রঙ শতদলবাসিনীর, রূপের আর সব খুঁত তাতে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, চোখ দুটি যে একটু ছোটবড় প্রায় সে খুঁতটা পর্যন্ত। মুখ ভার করিয়া ট্যারা চোখে সে তাকায় তার সেজো ননদের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে, আর মুখ নিচু করিয়া কৃষ্ণা নীরবে পান সাজে।
দেখি কী লিখেছে আবার।
কৃষ্ণা কাতরভাবে বলে, দেখে আর কী করবে বউদি? বলেই যখন দেবে—
শতদলবাসিনী বলে, আচ্ছা, এবারকার মতো আর বলব না। কিন্তু ফের যদি তোমরা চিঠি লেখালেখি কর—তুই বুঝিস না ভাই দু দিন পরে তোর বিয়ে-
গভীর আগ্রহে শতদলবাসিনী চিঠি পড়ে, কৃষ্ণার ঠোঁটে দেখা দেয় মুচকি হাসি আর এদিকে রান্নাঘরে উনানে চাপানো চায়ের জলের ডেকচি টগবগ শব্দে বাষ্প ছাড়িতে থাকে। চা দিতেও দেরি হয়, পান দিতেও দেরি হয়।
রাগে আগুন হইয়া যতীন আবার আসিয়া প্রায় দাঁত কড়মড় করিতে করিতে বলে, তোমরা সবাই হনুমান—এক নম্বরের জাম্বুবান তোমরা সব। একটু চা আর দুটো পান দিতে কি বেলা কাবার করবে। চাউনি দ্যাখো একবার, মারবে নাকি? সলজ্জ হাসি হাসিয়া শতদলবাসিনী বলে, ওমা, ছি কী যে বল তুমি! মারব কী গো! গরম জলে হাতটা পুড়ে গেল কিনা-
পুড়বে না, যা কাজের ছিরি। নাও নাও, চটপট বানাও চা।
উপরে মজলিশে ফিরিয়া গিয়া যতীন প্রায় তার বউয়ের লজ্জা পাওয়া হাসিটাই নকল করিয়া বলে, দুধ ছিল না কিনা, একটু দেরি হয়ে গেল চায়ের। যাক, এইবার এসে পড়ছে। চা না হলে কি আলাপ জমে!
আলাপ প্রচণ্ডভাবেই জমিয়াছিল, বর্ষাকালে মেঘের গলিয়া গলিয়া অবিরাম ধারাবর্ষণের মতো, যার ঝমঝম গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে শুনিতে মনে হয় বিশ্বব্যাপীই বুঝি হইবে। ঘরখানা মস্ত, আগে যতীনের বাবার শয়ন ঘর ছিল, আসবাবে বোঝাই হইয়া থাকিত। এখন যতীন এ ঘরে শোয় বটে, ঘরে আসবাবপত্র একরকম কিছুই নাই। মেঝের প্রায় সবটা জুড়িয়াই শতরঞ্চি পাতা, এক কোণে দেয়াল ঘেঁষিয়া বিছানার তোশকপত্র গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। বসিবার ঘরে সবদিন সকলের স্থান সংকুলান হয় না দেখিয়া যতীন এ ঘরখানা খালি করিয়া নিয়াছে। বসিবার জন্য দেয়াল দরকার হয় না তাই দেয়ালে অনেকগুলি ছবি আর ক্যালেন্ডার লটকানো। দক্ষিণের দেয়ালের মাঝামাঝি প্রকাণ্ড তৈলচিত্র—যে জানে না দেখিলেই তার মনে হইবে নিশ্চয় যতীনের পরলোকগত পিতার ছবি। জিজ্ঞাসা করিলে যতীন মাথা নাড়িয়া বলে, ওটা হল গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাবার ছবি। বছর তিনেক আগে পাশের বাড়িতে এক ভাড়াটে আসিয়াছিল, বাপের একটি তৈলচিত্রের জন্য তার জোরালো সাধ ছিল। যতীন ‘ছবিটি আঁকাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাসখানেকের জন্য দেশে গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া দ্যাখে, পাশের বাড়ির নতুন বন্ধুটি কোথায় যে গিয়াছে কেউ জানে না। ছেলের চিকিৎসার জন্য বাড়িটি যে তারা মোটে দু মাসের জন্য ভাড়া নিয়াছে তা কি যতীন জানিত!
কারণ যাই হোক, পুবের দেয়ালে কয়েকজন বিভিন্ন মানুষের সাধারণ কয়েকটি ফটোর মধ্যে নিজের বাবার একটি ফটো টাঙাইয়া রাখিয়া কয়েকদিনের পরিচিত একজনের বাবার তৈলচিত্রকে এতখানি প্রাধান্য দিতে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া যায়, ভাবে, যতীনের মনটা সত্যই উদার বটে।
এদিকে, যতীনের মা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মালা জপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করে, ছেলে কী বলে গেল বউমা?
যতীনের মা কানে একটু কম শোনে। শতদলবাসিনী এতখানি গলা চড়াইয়া তার প্রশ্নের জবাব দেয় যে উপরের ঘরে যতীন আর সমবেত সকলেই প্রত্যেকটি কথা শুনিতে পায় : কী আর বলবে, বলে গেল চায়ে দুধ-চিনি কম দিতে, চা খাইয়েই ফতুর হবে।
এ ধরনের অপরাধের জন্য শতদলবাসিনী শাস্তি পায়। দিনের বেলা যতীন সময় পায় না, বাড়িতে অনেক লোক আসে, নিজেকে অনেক লোকের বাড়িতে যাইতে হয়। রাত্রে,–হয়তো অনেক রাত্রেই, কারণ বিপদ রোগ আর শোক যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ঘাড়ে সব সময় চাপিয়া থাকিতে ভালবাসে এবং তাদের মধ্যে দু-চার জনকে সাহায্য পরামর্শ সেবা আর সান্ত্বনা দিতেই যে কত সময় লাগে বলিবার নয়–বাড়ি ফিরিয়া যতীন বউকে ডাকিয়া তোলে। পাঁচ বছরের ছেলে আর দু বছরের মেয়েকে নিয়া শতদলবাসিনী এ ঘরের লাগাও ছোট ঘরটিতে শোয়, ছেলেমেয়ের কান্না আর নোংরামি যতীনের সহ্য হয় না। দুটি ঘরের মাঝে দরজা আছে, দরকার হইলে কখনো যতীন নিজেই ও ঘরে যায়, কখনো বউকে এ ঘরে ডাকিয়া আনে।
শাস্তির রাত্রেও ডাক শুনিয়া প্রথমটা শতদলবাসিনী বুঝিতে পারে না শাস্তির জন্য তাকে ডাকা হইয়াছে, ঘুম ভাঙার বিরক্তি আর অজানা একটা অস্বস্তির মধ্যেও হঠাৎ উগ্র প্রত্যাশায় সর্বাঙ্গে তার বৈদ্যুতিক রোমাঞ্চ হয়। তারপর এ ঘরে আসিয়া যতীনের পাতা বিছানা তুলিয়া ঘর জোড়া শতরঞ্চি উঠাইয়া বাহিরে নিয়া গিয়া তাকে ঝাড়িতে হয়। ঘর ঝাঁট দিয়া আবার শতরঞ্চি বিছাইয়া পাতিতে হয় বিছানা। সমস্তক্ষণ যতীন নীরবে চুরুট টানিয়া যায়।
বিছানা পাতা হইলে চিত হইয়া শুইয়া বলে, এক গ্লাস জল দাও তো। জল দেওয়া হইলে বলে, হেঁটে হেঁটে পা দুটো কেমন ব্যথা করছে। একটু টিপে দাও না? না, অপমান হবে?
ওমা, অপমান হবে কী গো! কী যে বল তুমি!
যতীন চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে, ঘুমে ঢুলুঢুলু ট্যারা চোখ প্রাণপণে মেলিয়া রাখিয়া দু হাতে শতদলবাসিনী তার পা টিপিয়া দেয়, সে হাত দুটির রঙ তার হাতের সোনার চুড়ির রঙের সঙ্গে প্রায় মিশ খায়।
কৃষ্ণার গোপন চিঠির অদ্ভুত খাপছাড়া লাইনগুলি হয়তো তার মনে পড়িয়া যায়, স্বামীর পা টেপার সময় ওসব লাইন কি মনে না পড়িয়া পারে, যে মেয়ের এখনো স্বামী হয় নাই তার কাছে একটা মাথা পাগলা ছেলের লেখা কাকুতিমিনতি হা-হুতাশ ভরা লাইন? মনে পড়িতে পড়িতে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া ওঠার মতো হঠাৎ তার ঘুম টুটিয়া যায় : পা টেপা শেষ হইলে? পা টেপার পুরস্কার স্বরূপ–?
সন্তর্পণে গায়ে নাড়া দিয়া সে আধো-ঘুমন্ত যতীনকে চোখ চাওয়ায়, সলজ্জ একটু মৃদু হাসি মুখে আনিয়া বলে, এবার থাক? পরে আবার দেবখন, অ্যাঁ?
দু মিনিট দিয়েই হয়ে গেল? বলছি ভয়ানক পা কামড়াচ্ছে।
ঘরে আলো আছে, রাস্তার একটা আলোও জানালা দিয়া দেখা যায়—অসমান চোখ দুটি যতক্ষণ জলে ভরিয়া থাকে ততক্ষণ মুখ উঁচু করিয়া সে ঘরের আলোটা দ্যাখে, তারপর জল শুকাইয়া চোখ ঢুলুঢুলু হইয়া আসিলে তাকায় রাস্তার আলোর দিকে। ঘড়িতে সময় চলার টিকটিক আর যতীনের নিশ্বাস ফেলার স্ স্ শব্দের সঙ্গে মাঝরাত্রির আরো কত শব্দ সে শোনে, সব শব্দ হয়তো শব্দই নয়।
তারপর একসময় মেয়েটা কান্না শুরু করে, তার কান্নায় জাগিয়া গিয়া ছেলেটাও সে কান্নায় যোগ দেয়। পা টেপা বন্ধ করিয়া শতদলবাসিনী বলে, ওগো শুনছ, ওরা জেগেছে, আমি গেলাম।
না, এখন যেতে হবে না।
ওরা যে কাঁদছে?
কাঁদুক।
আর পা টেপায় না, এবার যতীন তার আদরের বউকে আদর করিয়া করিয়া আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলে। ছেলেমেয়ের চিৎকার যত সপ্তমে ওঠে তার বাহুর বাঁধনও তত জোরালো। শাস্তিই বটে। এতক্ষণ এত করিয়াও যাকে শাস্তি পাওয়ানো যায় নাই এতক্ষণে যে তার শাস্তি শুরু হইয়াছে দুজনেই তা বুঝিতে পারে, যে শাস্তি দিতেছে সেও যে শাস্তি গ্রহণ করিতেছে সেও।
গোড়া হইতেই শতদলবাসিনী সব জানে, সব বোঝে। তবু সে কিছুই জানিতে চায় না, কিছুই বুঝিতে চায় না, এখনো চেষ্টা করে জয়ের।
এতক্ষণে রাগ পড়ল?
রাগ আবার করলাম কখন?
কথা বল নি কিনা এতক্ষণ, তাই মনে হচ্ছিল রাগ করেছ। আচ্ছা, আজ দাড়ি কামালে কখন বল তো? সারা দিন তো এক মিনিট সময় পাও নি। কী খাটতেই তুমি পার, বাব্বা!—অত খেটো না, লক্ষ্মীটি, শরীর ভেঙে পড়বে। মধুর হাসি হাসে শতদলবাসিনী, যতীন দাড়ি কামাইয়াছে কিনা গালে আঙুল বুলাইয়া বুলাইয়া তাই পরীক্ষা করে। হঠাৎ ভয়ানক বিরক্ত হইয়া বলে, আঃ, কী চিল্লানিটাই শুরু করেছে দুটোতে, জ্বালিয়ে মারল। মেঝেতে আছড়ে ফেলতে সাধ যায়। ছাড়ো তো দুটোকে শান্ত করে আসি, এখুনি আসব, দু মিনিটের মধ্যে।
কাঁদুক না। ছেলেপিলের কাঁদা ভালো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসছি, দাঁড়াও।
যতীন দু ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে উঠিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে গিয়া শতদলবাসিনী পাশ কাটাইয়া চট করিয়া ও ঘরে চলিয়া যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু স্বামীর বাহুর বন্ধনের সঙ্গে বউ কেন পারিয়া উঠিবে?
দরজাটা বন্ধ করা হয়, কিন্তু ছেলেমেয়ের চিৎকারের শব্দ আটকানো যায় না। একটু পরেই ও ঘরের বারান্দার দিকের দরজায় দুমদুম করাঘাতের শব্দ পাওয়া যায়, কৃষ্ণার গলা শোনা যায়, বউদি, ও বউদি? কী ঘুম বাবা তোমার?—বউদি, ও বউদি?
.
কৃষ্ণার বিবাহের মাস দুয়েক দেরি আছে। পাত্রটি তেমন সুবিধার নয়। বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়, নিজের উপার্জনও বেশি নয়, বয়সটাও কম নয়। কৃষ্ণার পছন্দ-অপছন্দের অবশ্য প্রশ্নই ওঠে না, বাড়ির অন্য কারো পছন্দ হয় নাই। মা দিনরাত খুঁতখুঁত করে, বিবাহিতা বড় বোন দুটি আপসোস ভরা চিঠি লেখে, আত্মীয়স্বজনেরা জিজ্ঞাসা করে, এমন মেয়ের এমন পাত্র ঠিক করা কেন, বাজারে কি আর ছেলে নাই?
যতীন বলে, কত লোক বোনের বিয়েই দিতে পারছে না, কানাখোঁড়ার হাতে দিতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত। আমার বোন বলে কি তার জন্য রাজপুত্তুর আনতে হবে? মন্দই বা কী ছেলেটি? স্বাস্থ্য ভালো, রোজগারপাতি করছে—আবার কী চাই?
তা ছাড়া পাত্রটি সস্তা।
এটাই যে একটা মস্ত বড় কারণ, শতদলবাসিনীর কাছেই সে কেবল তা স্বীকার করে। টাকাপয়সার টানাটানিটা তার সব সময় লাগিয়াই আছে। বাপের অবস্থা তার ভালোই ছিল, দেশে কিছু সম্পত্তি আছে, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ছিল, নিজেও মাসে মাসে বেতন পায় প্রায় তিন শ টাকা। তবু ধার দিয়া আর দান করিয়া টাকায় তার কুলায় না। ব্যাঙ্কের টাকাগুলি যতদিন ছিল ততদিন চেক কাটিয়া কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে, এখন অসুবিধার সীমা নাই। দেশের সম্পত্তির আয়টা বছরে হাজার দুয়ের কাছাকাছি ওঠে নামে। এই আয়টা আছে বলিয়া রক্ষা, নয়তো কী যে হইত!
বউয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে যতীন এ বিষয়ে আলোচনা করে। স্বামীর মুখে দুর্ভাবনার ছাপ দেখিয়া শতদলবাসিনী বলে, এমন করে টাকাগুলো যদি নষ্ট না কর
নষ্ট মানে?—
আহা, যাদের ধার দাও, তারা কেউ একটি পয়সা কখনো ফেরত দিয়েছে, না দেবে? যাদের এমনি টাকা দাও, তাদের আদ্দেকের বেশি মিথ্যে কাঁদুনি গেয়ে তোমায় ভোলায়।
মিথ্যে কাঁদুনি গেয়ে ভোলায়? নাম কর তো একজনের কে ভুলিয়েছে?
শতদলবাসিনী আর যতীনের বন্ধু ক’জনের নাম জানে, কাকে কী উপলক্ষে কখন ধার দিয়েছে বা দান করিয়াছে তাই বা সে কী জানে। সে সময় তো যতীন তার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসে না। অনেক ভাবিয়া একটি দৃষ্টান্তই কেবল তার মনে পড়ে। তিন-চার বছর আগের ঘটনা, যখন হইতে যতীনের দান করা রোগটা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।
কেন, সেই যে সেবার শান্তির বিয়েতে সাতাশ শ টাকা দিলে? ওর বাবার মাইনে কম হোক, ওর দাদা তো সাত-আট শ টাকা মাইনে পায়।
যতীন অসহিষ্ণু হইয়া বলে, সব দাদাই কি বেশি মাইনে পেলে বোনের বিয়েতে টাকা ঢালে? টাকা কম পড়ল, শান্তির দাদা দিতে চাইল না, তাই তো আমি দিলাম। আমি শেষ মুহূর্তে পাত্র বদলে দিলাম, বেশি টাকার দরকার হল, আমি না দিলে কে দেবে? আমার একটা দায়িত্ব নেই?
শতদলবাসিনী জিজ্ঞাসা করে না যে পরের মেয়ের কোন পাত্রের সঙ্গে বিবাহ, সাতাশ শ টাকার খেসারত দিবার দায়িত্ব নিয়া সে বিষয়ে মাথা ঘামাইতে যাওয়ার কী দরকার পড়িয়াছিল, যতীনকে ও কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। মৃদুস্বরে সে শুধু বলে, নাইবা বদল করতে পাত্র? বেশি ভালো পাত্ৰ এনে লাভ তো হয়েছে ভারি, মেয়ের চোখের জল শুকুচ্ছে না। তার চেয়ে আগের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলে হয়তো-
যতীন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কী করে জানলে শান্তি দুঃখ পাচ্ছে?
ওমা, তা জানব না? সেজদি যে ভাগলপুরে থাকে। ননদ সেজদি নয়, আমার সেজদি—সেই যে বিয়ের সময় যে তোমার টিকি কেটে নিয়েছিল না?—সে।
টাকার আলোচনা বেশিক্ষণ তাদের মধ্যে চলে না, অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্যক্তিগত সমালোচনায় দাঁড়াইয়া যায়। একতরফা সমালোচনা, যতীন বলিয়া যায় আর শতদলবাসিনী চুপ করিয়া শোনে। টাকা সম্বন্ধে শতদলবাসিনীর সংকীর্ণতা কত যে পীড়ন করে যতীনকে বলিবার নয়। ভালো কাজেই যদি না লাগে, টাকার তবে আর মূল্য কী? মানুষের চেয়ে টাকা কি বড়? এতই যদি টাকা ভালবাসে শতদলবাসিনী, বাপকে বলিয়া রক্তমাংসের একটা মানুষের বদলে টাকার একটা বস্তাকে বিবাহ করিলেই পারিত!
আমি মরলেই হাজার বিশেক টাকা পাবে। একদিন বিষ-টিস খাইয়ে দিয়ো বরং।
ওমা, বিষ খাওয়াব কী গো? কী যে বল তুমি!
আলোচনাটা হইয়াছিল বর্ষাকালের এক সন্ধ্যাবেলায়। তিন দিন পরে অবিশ্রাম বর্ষণের মধ্যে যতীন ভাগলপুর চলিয়া গেল।
শান্তির জন্য যাচ্ছ?
হ্যাঁ।
কী আশ্চর্য, সেজদি আন্দাজে কী লিখেছে না লিখেছে—
দেখেই আসি কেমন আছে।
পাঁচ দিন পরে সে ফিরিয়া আসিল এবং আসিয়াই শান্তির শ্বশুরের নামে পাঠাইয়া দিল পুরা একটি হাজার টাকা। শতদলবাসিনী ব্যাপারটা জানিতে পারিল আরো দিন সাতেক পরে।
টাকা পাঠালে কেন?
যতীন হাই তুলিয়া বলিল, পণের সব টাকা দেওয়া হয় নি বলে ওরা শান্তিকে কষ্ট দিচ্ছিল কিনা, তাই পাঠিয়ে দিলাম।
সহজ কৈফিয়ত, কিন্তু শতদলবাসিনীর ট্যারা চোখের সঙ্গে ভ্রু দুটি পর্যন্ত কুঁচকাইয়া গেল। টাকা পেলে কোথায়?
তা দিয়ে তোমার দরকার কী?
শতদলবাসিনী উদাসভাবে বলিল, না আমার আর দরকার কী। ধার করেছ কিনা তাই জিজ্ঞেস করছিলাম?
তাই বা জিজ্ঞেস করবে কেন?
যতীনের মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে বুঝিয়া শাস্তির ভয়ে শতদলবাসিনী আর কথাটি বলে না। টাকা সম্বন্ধে নিজের হীনতার চেয়ে স্বামীর উদারতাই তাকে বেশি কাবু করিয়া ফেলে এবং সেজন্য ক্ষণিকের গ্লানি বা অনুতাপ বোধ করিবার মতো উদারও সে নয়। নিজের বোনের বিবাহের বেলায় যার টাকা থাকে না, পরের মেয়ের জন্য সে হাজার হাজার টাকা খরচ করিতে পারে, নিজের না থাকিলে ধার করিয়া যোগাড় করে, এরকম পরোপকার আজ যেন হঠাৎ তার বড় বেশি রকমের খাপছাড়া মনে হয়। এবং দু-একটা দিন কাটিতে মনে হয়, শুধু খাপছাড়া নয়, এটা অন্যায়ও বটে।
কৃষ্ণার জন্য সস্তায় অপাত্র কেনা হইতেছে বলিয়া শতদলবাসিনীর এতদিন বিশেষ আপসোস ছিল না। যে মেয়ে গোপনে পরের ছেলের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেমনতেমন একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হইয়া যাওয়াই ভালো। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের রোগা লম্বা গোঁয়ার-গোবিন্দ এক ছোঁড়া যাকে ওরকম আবোলতাবোল কথা-ভরা চিঠি পাঠায়, একটু বেশি বয়সের মোটাসোটা একজনের সঙ্গেই তার বিবাহ হওয়া উচিত—শাসনে থাকিবে। কেন যতীনও তো তাকে বেশি বয়সেই বিবাহ করিয়াছে, বিবাহের সময় যতীনও তো কম গোলগাল ছিল না, কিন্তু তাতে কী আসিয়া গিয়াছে? স্বামীকে অপছন্দ করিয়া সে কি কোনো দিন গোপনে কারো সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করিয়াছে? তার যদি এতেই মন উঠিয়া থাকে, কৃষ্ণার উঠিবে না কেন? রূপে বল, গুণে বল, কোন দিক দিয়া তার সঙ্গে কৃষ্ণার তুলনা চলে? এমন রঙ আছে কৃষ্ণার, এমন গড়ন, এমন মধুর স্বভাব? এইসব ভাবিতে আর অপাত্রটিকেই কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তার বিশ্বাস জন্মিয়া যাইত। এবার কিন্তু তার মনে হয়, রূপে গুণে যতই তুচ্ছ আর খারাপ মেয়ে হোক কৃষ্ণা, সে তো শান্তির চেয়ে তুচ্ছ নয়, খারাপ নয়? শান্তির জন্য যদি দফে দফে এত টাকা খরচ করা যাইতে পারে, কৃষ্ণার জন্য কেন যাইবে না? পরের মেয়ের জন্য যতটা করা হইয়াছে, ঘরের মেয়ের জন্য অন্তত ততটুকু করা উচিত!
কিন্তু করিবে কে? যতীনের বড় টাকার টানাটানি।
ভাবিতে ভাবিতে শতদলবাসিনীর সোনার মতো মুখের রঙ একটু বিবর্ণ হইয়া আসে, উনানের আঁচেও আর যেন তেমন রঙ খোলে না। সামনে দাঁড়াইয়া সে কৃষ্ণার কণ্ঠার হাড়ের কাছে জমানো ময়লা চাহিয়া দ্যাখে, পিছন হইতে দ্যাখে তার দোলনময় চলন। মমতায় কাতর হইয়া ভাবে, আহা, এই মেয়েকে টাকার জন্যে একটা ধেড়ে হনুমানের কাছে বলি দেওয়া হইবে, একটা পিপের মতো মোটা জাম্বুবান হইবে এই কচি মেয়েটার বর?
মুখ তোমার শুকনো দেখাচ্ছে কেন ঠাকুরঝি?
কী জানি, জানি না তো?
না ঠাকুরঝি, অত ভেব না তুমি। আমি সব ঠিক করে দেব। আর চিঠি লিখেছে?
কৃষ্ণা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করে কিনা সেই জানে, বলে, কে চিঠি লিখবে?
আহা, তোমার সে গো—সে। রোজ পাঁচ-দশটা চিঠি লেখালেখি করছ, জান না কে?
ও, সে? কৃষ্ণা হঠাৎ রাগিয়া যায়, তুমি কেমন ধারা ইয়ে বউদি, বলছি আজ পর্যন্ত আমি একটা চিঠির জবাব দিই নি, বিশ্বাস হয় না কেন তোমার?
শতদলবাসিনীও রাগিয়া যায়, কেন দাও নি জবাব? কী এমন মহাপুরুষটা তুমি যে একটা চিঠির জবাব দিতে বেধেছে? মিছিমিছি মানুষের মনে কষ্ট দিতে বড্ড ভালো লাগে, না? মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি।
কৃষ্ণা যেন মেয়েমানুষ জাতটার সম্মান বাঁচানোর জন্যই বলে, একটা জবাব দিয়েছি। লিখে দিয়েছি, ফের আমার কাছে চিঠি লিখলে পুলিশে ধরিয়ে দেব।
ওমা, পুলিশে ধরিয়ে দেবে কী গো? কী যে বল তুমি!
সে বিব্রত হইয়া থাকে, অশান্তি বোধ করে। ভাদ্রের গরমটা যখনই অসহ্যবোধ হয় তখনই মনে পড়ে আশ্বিনের বেশি দেরি নাই। আশ্বিনের গোড়ায় কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া যাইবে। তার নিজেরই যেন একটা বড় রকমের বিপদের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। চিঠি লিখিলে পুলিশে ধরাইয়া দিবে লিখিয়া দিয়াছে? তার আগে একখানা চিঠিরও জবাব দেয় নাই? এ আবার কী ব্যাপার! অমন আগ্রহের সঙ্গে কেন তবে সে চিঠিগুলি পড়িত, পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া যাইত? ব্লাউজের আড়ালে চিঠি লুকাইয়া সারা দিন ঘুরিয়া বেড়াইত? বড় প্যাচালো কাণ্ড-কারখানা সংসারে, বড় গোলমেলে মানুষের চালচলন।
তার এত দুর্ভাবনা কেন শতদলবাসিনী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শান্তির সঙ্গে কৃষ্ণার যেন একটা নেপথ্য সংগ্রাম চলিতেছে, কৃষ্ণার পরাজয়ের কথাটা সে ভাবিতেও পারে না। তাই যদি ঘটে, বাঁচিয়া থাকিয়া সুখ কী? কীসের ছেলেমেয়ে, কীসের স্বামী, কীসের সংসার, কীসের রাঁধাবাড়া!
খাইতে বসিয়া যতীন চিৎকার করে, ডালে নুন পড়ে নি, মাছের ঝোল নুনকাটা, দিন দিন কী হচ্ছে শুনি? দূর করে দেব বাড়ি থেকে সব কটাকে লক্ষ্মীছাড়া বজ্জাত এসে জুটেছে কোথা থেকে, জ্বালিয়ে মারলে।
মা যদিবা কানে কম শোনে, এ কথাগুলি শুনিতে পায়। ডাকিয়া বলে, বউমা, খারাপ শরীর নিয়ে কেন রাঁধতে গেলে বাছা? ভালো মানুষের এ গরম সয় না, খারাপ শরীরে—
যতীন ধমকাইয়া ওঠে, তুমি থামো, খারাপ শরীর না তোমার মাথা।
পাশের বাড়ির দোতলায় ছাদের একদিকের খানিকটা আলিসায় ঝুঁকিলে এ বাড়ির বারান্দা দেখা যায়। নাতির কাঁথা মেলিয়া দিতে দিতে পাশের বাড়ির গিন্নি আলিসায় ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে বাবা
মুখ তুলিয়া চাহিয়া যতীন হাসিমুখে বলে, কিছু হয় নি পিসিমা। নন্দর চিঠি পেয়েছেন?
যতীনের পাতানো পিসি সরিয়া গেলে শতদলবাসিনী একবাটি দুধ আনিয়া দেয়। আজ দুধ দিয়েই খাও। ক’দিন শান্তির রান্না খেয়ে এসে আমার রান্না মুখে রুচছে না, না?
মুখের উপর ছুড়িয়া মারার জন্য ডালের বাটিটা তুলিয়া নিয়া দেখিতে পায় ও বাড়ির পাতানো পিসিমা আড়ালে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু চলিয়া যায় নাই। আলিসার আড়ালে লুকাইয়া একটা ফাঁক দিয়া এদিকেই চাহিয়া আছে। ডালের বাটিটা যতীন নামাইয়া রাখে।
শতদলবাসিনী বুঝিতে পারে, শাস্তিটা রাত্রির জন্য তুলিয়া রাখা হইল। তা হোক, শাস্তির ভয় কে করে? সব শাস্তির শেষ আছে কিন্তু কতগুলি ব্যাপার যেন কিছুতেই শেষ হইতে চায় না।
ননদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া সে বলে, একখানা চিঠি লেখো না ঠাকুরঝি?
কাকে চিঠি লিখব?
তোমার সেই তাকে?
ও, তাকে? তুমিই লেখো না?
শতদলবাসিনী মুখভার করিয়া নুনকাটা মাছের ঝোলমাখা ভাত খাইতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলে, তুমি বড় বোকা ঠাকুরঝি, বড্ড বোকা। আমি হলে কী করতাম জান, পালিয়ে যেতাম।
পালিয়ে গিয়ে কী খেতে?
সেও একটা সমস্যা বটে। মেয়েমানুষ হইয়া এ সমস্যাটা না বুঝিয়া উপায় নাই। কৃষ্ণা তবে অনেক ভাবিয়াই পুলিশে ধরানোর ভয় দেখাইয়া চিঠি লিখিয়াছে।
কৃষ্ণা খাওয়া বন্ধ করিয়াছিল। মুখের ভাবটা তার কাঁদো কাঁদো।
তুমি যে বলেছিলে সব ঠিক করে দেবে, দাও না? দু-চার দিনের মধ্যে বিয়েটা ঘটিয়ে দাও না।
দু-চার দিনের মধ্যে বিয়ে! কার সঙ্গে?
যার সঙ্গে ঠিক হয়েছে, আবার কার সঙ্গে।
এই ভাদ্র মাসে?
হোক ভাদ্র মাস।
কথা শুনিলে মনে হয় তামাশা করিতেছে, মুখ দেখিলে বিশ্বাস হয় না। শতদলবাসিনী তাই মাখা ভাত নাড়াচাড়া করিতে করিতে চুপ করিয়া থাকে। কৃষ্ণা অধীর হইয়া বলে, চোখ নেই তোমার? আমায় দেখে বুঝতে পার না?
একটু একটু যেন বুঝতে পারি পারি করছিলাম ঠাকুরঝি, ভরসা পাই নি। চিঠির জবাব দিতে না বললে, অথচ—দেখা হত, না?
হত।
তারপর দুজনেই চুপচাপ। আর খাওয়া গেল না, মাছ-তরকারিও আজ অখাদ্য হইয়াছে।
অনেকক্ষণ পরে বলিল, ভাদ্র মাসে তো বিয়ে হয় না ঠাকুরঝি, একটা মাস দেরি করতেই হবে।
রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িতে দেরি করিতে থাকে, একজন ঘুমায় তো আরেক জন জাগিয়া ওঠে। যতীন দশটা বাজার আগেই শুইয়া পড়িয়াছিল, ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে শতদলবাসিনী আহ্বানের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া থাকে। আজ সে শাস্তি গ্রহণ করিবে না—যাই বলুক যাই করুক যতীন আজ সে বিদ্রোহ করিবেই। একবার এখন ডাকিলেই হয়। আজ যেন তার সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, সমাজ সংস্কার নীতি ধর্ম সবকিছুর বিরুদ্ধে যাইতে কৃষ্ণার যত সাহস দরকার হইয়াছিল তার চেয়ে বেশি। যতীন ডাকিয়া যেই বলিবে, পা টেপো, মাথা উঁচু করিয়া জবাব দিবে পারব না, আমি তোমার পা টেপা দাসী?
তারপর? তারপর যা হয় হইবে। কৃষ্ণা চোখ মেলিয়া ভবিষ্যতের কত গাঢ় অন্ধকারকে বরণ করিয়াছে, সে চোখ বুজিয়া গালে একটা চড় খাইতে পারিবে না?
মনের মধ্যে সদিচ্ছার চিতা জ্বলিতে থাকে, বীরত্বের দীপ্তিতে আত্মসম্মান উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। নিজেকে শতদলবাসিনীর মনে হইতে থাকে অতি উত্তম, অতি মহৎএকেবারে অসাধারণ কিছু। কিন্তু হায়, ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়ে, রাস্তার ওপাশের বাড়ি দুটির সব আলো নিভিয়া যায়, পাড়া নিঝুম হইয়া আসে কিন্তু বিদ্রোহ করার সুযোগ দিতে কেউ তো ডাকে না।
তারপর যতীনের নাক ডাকার শব্দ কানে আসিলে মনটা খারাপ হইয়া যায়। শাস্তি দিতেঁ না ডাকিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? নিজেকে বড় অসহায়, বড় নিরুপায় মনে হইতে থাকে।
কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া শতদলবাসিনী ঘুমন্ত স্বামীর পা টিপিতে আরম্ভ করে।
১০. প্রৌঢ়ের বউ
রসিকের প্রৌঢ়ত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই মৃত্যুভয়। মরণের অবিরাম গুঞ্জন, আমি আসিতেছি, আমি আসিতেছি, শুনিয়াও না শুনিবার সতেজ ঔদ্ধত্য ঝিমাইয়া পড়ায় এই বয়সে মানুষের প্রথম খেয়াল হয়, দূর হইতে মরণ আশ্বাস দিয়া বলিতেছে, এখনো সময় হয় নাই, একটু অপেক্ষা কর। মরণের স্বাদ পাইতে পাইতে বৃদ্ধ ভাবে, দেরি আছে, এখনো দেরি আছে : জীবন বিস্বাদ হওয়ায় প্রৌঢ় ভাবে, হায়, দিন যে আমার ফুরাইয়া আসিল।
তাই, রসিক ভাবিত, দু দিনের জন্য কচি একটা মেয়েকে বউ করিয়া বাড়িতে আনা উচিত হইবে না। কেবল তাই নয়, ছেলেমানুষ বউ নিজে কত ছেলেমানুষি করিবে আর তার কাছে কত ছেলেমানুষি আশা করিবে ভাবিলেও রসিকের বড় অস্বস্তি বোধ হইত। আর কি তার সে বয়স আছে? প্রতিদান দেওয়া দূরে থাক, অল্পবয়সী বউয়ের অন্তহীন ন্যাকামি হাসিমুখে সহ্য করিয়া চলাও কি তার পক্ষে সম্ভব হইবে? যে চলিয়া গিয়াছে সে ছিল জননী ও গৃহিণী, আসিবে একটি চঞ্চলা বালিকা। তার সঙ্গে কি বনিবে রসিকের?
প্রয়োজন ছিল না, ইচ্ছা ছিল না, তবু একদিন রসিকের বিবাহ হইয়া গেল।
একদিন অসময়ে তাকে অন্দরে ডাকিয়া সুলোচনা বলিল, এই মেয়েটিকে দ্যাখো তো ঠাকুরপো। ওর নাম সুধারানী।
রসিক থতমত খাইয়া বলিল, তাই নাকি? তা, বেশ তো।
কচি খুকি নয়, বেশ বড়সড়ো মেয়েটি। মুখখানা গম্ভীর। মেঝেতে জাঁকিয়া বসিবার ভঙ্গিতে কেমন একটু গিনি গিন্নি ভাব আছে। রসিক তো জানিত না সুলোচনাই সুধারানীকে চওড়া কালোপাড় শাড়িখানি পরাইয়াছে, কানের দুল খুলিয়া ফেলিয়া বালা আর অনন্ত পরাইয়াছে, চুলের জটিল বিন্যাস নষ্ট করিয়া মাঝখানে সিঁথি কাটিয়া পিছন দিকে টানিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে আর ধমক দিয়া বলিয়াছে : মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকো বাছা, একটু যদি লজ্জা করবে আমার দেওরকে দেখে, একটু যদি চঞ্চল হবে…,। সুধারানীকে রসিকের তাই মন্দ লাগিল না।
তারপর সুলোচনার কাছেই শোনা গেল, মেয়েটার নাকি বয়স হইয়াছে অনেক। গরিব বাপ নাকি বিবাহ দিতে পারে না, কুড়ি পার হইয়া মেয়ে তাই হইয়া গিয়াছে বুড়ি। সময়মতো বিবাহ হলে অ্যাদ্দিনে তিন ছেলের মা হত, ঠাকুরপো।
বিবাহ করার জন্য এতদিন সকলের অনুরোধ উপরোধ যথারীতি চলিতেছিল, সুলোচনার ব্যবস্থাতেই বোধ হয় এবার সেটা দাঁড়াইয়া গেল রীতিমতো আক্রমণে। রসিক হার মানিয়া বলিল, তবে তাই হোক
সুধারানীকে দেখার জন্য হার মানার ইচ্ছা তার কতটুকু জাগিয়াছিল বলা কঠিন।
.
এমনই কপাল সুধারানীর, প্রথমবারের আলাপে প্রথম শব্দটিকেই সে রসিকের মন বিগড়াইয়া দিল। রসিকের মনে অনুতাপ, আত্মসমর্থন, দ্বিধা সংকোচ ঔৎসুক্যের আলোড়ন চলিতেছিল, কখনো জাগিতেছিল বিষাদ, কখনো প্রত্যাশার আনন্দ। নিজেকে নিয়াই সে বড় ব্যস্ত হইয়াছিল।
একদিন রাত প্রায় এগারটার সময় বাহিরের ঘরে কাজ করার নামে সে আকাশপাতাল ভাবিতেছে, ধীরে ধীরে সুলোচনা ঘরে আসিয়া বলিল, ঠাকুরপো, একটিও নাকি কথা কও নি বউয়ের সঙ্গে? একটা দুটো পর্যন্ত নাকি কাজ কর এখেনে? ছি ঠাকুরপো, ছি, এমন করে কি কষ্ট দিতে আছে ছেলেমানুষের মনে? ঘরে লুকিয়ে চুপিচুপি আজ কাঁদছিল।
ভালো উদ্দেশ্যেই সুলোচনা বানানো কথাটা বলিয়াছিল, কিন্তু ফলটা হইল বিপরীত। রসিক ভাবিল, ছেলেমানুষ? কাঁদিতেছিল? কী সর্বনাশ! এতটুকু যার ধৈর্য নাই তার কাছে তবে আর কী আশা করা চলিবে?
তবু বিবাহ যখন করিয়াছে, মেয়েটির মনে কষ্ট না দেওয়াই কর্তব্য বিবেচনা করিয়া রসিক আজ প্রথম রাত একটার আগে, সুধারানীকে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িবার সুযোগ না দিয়াই ঘরে গেল। ভাবিল, সুধারানীকে বুঝাইয়া দিবে, এসব অবহেলা নয়, আদরযত্ন স্নেহমমতার অভাব তার হইবে না। তবে রসিক বুড়া হইয়া পড়িয়াছে কিনা, মানাইয়া চলিতে হইলে সুধারানীর একটু ধীর স্থির শান্ত না হইলে চলিবে কেন?
খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলাইয়া সুধারানী বসিয়াছিল, আস্তে আস্তে দুলাইতেছিল দুটি পা। হয়তো আনমনে, নয়তো অভ্যাসের বশে। একে তো তাকে দেখিলেই মনে হয় কার যেন সে প্রতীক্ষা করিতেছে, তার উপর ঠিক তার বড় মেয়েটির মতো দু পাশে হাত রাখিয়া বসিয়া পা দুলাইতে দেখিয়া রসিক হতাশ হইয়া গেল। হয়তো সুলোচনা জানাইয়া দিয়া গিয়াছে এখনই স্বামী ঘরে আসিবে, কিন্তু এমন বেশে প্রেমিকের পথ চাওয়া এমন অধীর প্রতীক্ষা কেন? হরিণীর মতো চঞ্চলা যে দশ বছরের মেয়ে, তার অনুকরণে পা দোলানো কেন?
রসিককে দেখিয়া সুধারানী একটু জড়সড় হইয়া বসিল সামান্য একটু। বেশি লজ্জা করিতে সুলোচনা বারণ করিয়া দিয়াছে। রসিক গম্ভীর মুখে হাত দুই তফাতে বসিল, সভায় আসন গ্রহণ করার মতো আড়ম্বরের সঙ্গে।
কী বলিয়া কথা আরম্ভ করা যায়? এত জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা রসিকের, এত ধীর স্থির শান্ত তার প্রকৃতি, একটি তরুণীর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিতে গিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম কি দেখা দিল রসিকের কপালে? হায় রে কপাল, সতের বছর আগে বিবাহের রাত্রেই প্রমীলার সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া তার তো কথা খুঁজিতে হয় নাই, ঘর খালি হওয়া মাত্র চাপা গলায় মহাকাব্যের ছন্দে আদরের সুরে আপনা হইতেই যেন উচ্চারিত হইয়াছিল, কেমন লাগছে? এখন থেকে তুমি আমার হয়ে গেলে।
অনিশ্চয়তায় বিপন্ন মানুষের মতো চিবুকে আঙুল ঘষিতে ঘষিতে শেষে রসিক বলিল, তোমায় ক’টা কথা বলব সুধা
সুধা কিছুই বলিল না।
আমার বয়েস হয়েছে, তোমার হয়তো আমাকে ঠিক পছন্দ হয় নি
শুনিয়া চেষ্টা করা গম্ভীর মুখে কী দুষ্টামিভরা হাসিই যে দেখা দিল সুধারানীর; কানের দুলে আলোর ঝলক তুলিয়া মাথা নিচু করার পলকটির মধ্যে মানুষকে মর্মাহত করা কী তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টিতেই একবার সে চাহিয়া নিল রসিকের চোখের দিকে। অস্ফুটস্বরে সে বলিল, ধেৎ।
রসিক নীরবে তার কাজের ঘরে চলিয়া গেল, যখন মনে হইল এতক্ষণ সুধার পক্ষে জাগিয়া থাকা অসম্ভব, তখনো ফিরিয়া গেল না। কাজের ঘরেই শুইয়া রহিল। প্রমীলার আমলেও এ ঘরে তার জন্য একটি বিছানা প্রস্তুত থাকিত, যদিও তখন এ বিছানায় সে ঘুমাইত কদাচিৎ।
এ ঘরে রাত কাটানোর ব্যবস্থা অবশ্য স্থায়ী করা গেল না, লোকে বলিবে কী? কাজের নামে এখানে অনেক রাত পর্যন্ত কাটানো চলে, বিশেষ কাজের নামে মাঝে মাঝে দু-একটা রাত কাবার করাও চলে, কিন্তু ফাজিল একটা মেয়ে বউ হইয়া অন্দরে প্রমীলার শয়ন ঘরটি দখল করিয়াছে বলিয়াই সে ঘরটিকে তো জীবন হইতে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলা যায় না। প্রৌঢ় রসিকের পক্ষে ওরকম ছেলেমানুষি করা অসম্ভব।
ফাজিল বউটাকেও একেবারে বাদ দিয়া দিন কাটানো যায় না। বিশেষত সুলোচনা যখন আছে এবং কোমর বাঁধিয়া রসিকের পিছনে লাগিয়াছে। নানা ছুতায় সুলোচনা সুধারানীকে রসিকের কাছে পাঠায়, এমন অবস্থাই সৃষ্টি করে যে রসিকের দৈনন্দিন জীবনের অনেকগুলি খুঁটিনাটি প্রয়োজন সুধারানীকে ছাড়া মিটিবার কোনো উপায় থাকে না। তার ফলে সুধারানীর অস্তিত্ব রসিকের কাছে খানিকটা অভ্যস্ত হইয়া যায়, টুকরা টুকরা সান্নিধ্যে বাহিরের একটা সহজ সম্পর্ক তাদের মধ্যে গড়িয়া ওঠে, ছোটবড় অনেক উপলক্ষে প্রশ্ন আর জবাবের ধাঁচের আলাপ আলোচনাও চলে, কিন্তু আর কিছুই হয় না। মধ্যস্থের চেষ্টায় কবে কোন স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল ঘটিয়াছিল, চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ, ফাল্গুনের হাওয়া, রাতজাগা বাজেকথার কাব্য, এইসব চিরকালের মধ্যস্থ ছাড়া?
সুলোচনা বলে, ব্যাপার কী বল তো ঠাকুরপো? সুধাকে তোমার পছন্দ হয় নি?
রসিক বলে, বুড়ো বয়সে আবার পছন্দ অপছন্দ।
তবু ব্যাপারটা কী শুনি না? না হয় বললেই আমায়?
সুধা বড় ফাজিল বউঠান। ফাজিল মেয়ের সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার বয়স কি আমার আছে, আজ বাদে কাল চোখ বুজব আমি?
সুলোচনা এবার রাগ করিয়া বলে, ফাজিল! সুধা ফাজিল! একটা সাত ছেলের মা বুড়িকে এনে দিলে তুমি সুখী হতে, না? সাত ছেলের মাও কিন্তু একটু আধটু ফাজলামি করে ঠাকুরপো, আর দশটা মানুষের মতো। তোমার মতো গণেশ ঠাকুর সবাই নয়।
সুলোচনার রাগ দেখিয়া রসিকের মনের অশান্তি বাড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছা তো করে তার সুধারানীকে বউয়ের মতো আদর করিতে, কিন্তু অনেক দিন আগে প্রমীলার সঙ্গে যে ছেলেমানুষি খেলার আবছা স্মৃতিটুকু শুধু মনে আছে, আজ সে খেলার পুনরভিনয় আরম্ভ করার কথা ভাবিলেই তার যে ভয় হয়, বিতৃষ্ণা জাগে। মনে হয়, দূরে বসিয়া থাকিলে যার মুখখানি বিষণ্ন হইয়া থাকে, গম্ভীরভাবে তাদের সম্পর্কের গভীর সমস্যার কথা তুলিলে যে দুষ্টামির হাসি হাসে, কাছে গিয়া বসিলেই যার লজ্জা সংকোচ ভীরুতার অসহ্য ন্যাকামি দেখা দেয়, অপটু একটু সেবাযত্নের চেয়ে সর্বাঙ্গের লাবণ্য, মুখের কথা আর চোখের চাহনি দিয়া যে দিবারাত্রি মন ভুলানোর চেষ্টা করে, তাকে আপন করিতে গেলে সং সাজিতে হইবে, অভিনয় করিতে হইবে হাস্যকর। অন্য কিছুতে সুধারানীর মন উঠিবে না, আর কোনো খেলা সে বুঝিবে না। প্রমীলার সঙ্গে যে খেলা তার চলিত শেষের দিকে, তার গাম্ভীর্য গভীরতা আর মাধুর্যের খবর তো সুধারানী জানে না। সাংসারিক সমস্যার আলোচনা যে চটুল প্রেমের কাকলির চেয়ে প্রীতিকর হইতে পারে, বুঝাইয়া বলিতে গেলে সুধারানী মুচকি মুচকি হাসে। প্রমীলার প্রথম বয়সের সেই গা-জ্বালানো হাসি, চুম্বন ছাড়া আর কিছু দিয়াই সে হাসি মুছিয়া নেওয়া যাইত না।
সুলোচনা যতই চেষ্টা করুক, রসিক তাই মনের বিরাগ জয় করিয়া কোনোমতেই নতুন বউকে কাছে টানিতে পারে না এবং এমনিভাবে দিন কাটিতে থাকে। সুধারানীর মুখের বিস্ময় ও বিষাদের ভাব ঢাকিয়া ক্ৰমে ক্ৰমে এক দুর্বোধ্য অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে থাকে।
.
কাজের ঘরে প্রতিদিন রাত্রি একটা পর্যন্ত জাগিয়া থাকিতে প্রথম প্রথম রসিকের কষ্ট হইত, মাঝে মাঝে বিছানায় শুইয়া কাজ করিতে গিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িত খেয়ালও থাকিত না। তারপর কীভাবে তার সে স্বাভাবিক ঘুমের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর ঘুম আসে না, ঘুমাইতে চাহিলেও নয়। জাগিয়া থাকার জন্য তাকে আর কোনো চেষ্টাই করিতে হয় না। একসময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়, বাড়ি আর পাড়াটা ধীরে ধীরে নিঝুম হইয়া আসে, এই ঘরে শুধু জাগিয়া থাকে রসিক একা। মাথার মধ্যে মৃদু যন্ত্রণা বোধ হয়, দু চোখ জ্বালা করিতে থাকে কিন্তু ঘুম আসে না। সমস্ত জগৎ চারদিকে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িতেছে অনুভব করিতে করিতে নিজের চিন্তা আর কল্পনার জগৎ যেন স্পষ্ট আর উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে।
প্রমীলার জন্য তখন রসিকের বড় কষ্ট হয়, অবুঝ শিশুর মতো তার মন ফিরিয়া চায় প্রমীলাকে। সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে একটা যুক্তিহীন ক্রুদ্ধ অভিযোগ জাগিয়া ওঠার সঙ্গে তার মনে হয়, প্রমীলা থাকিলে এত রাত পর্যন্ত জাগিতে দিত না, জোর করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিত, শুধু কপালে হাত বুলাইয়া ঘুম আনিয়া দিত তার চোখে।
অন্দরের ঘরে গিয়া সুধারানীকে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিয়া রসিকের সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরিয়া যায়। ইচ্ছা হয়, লাথি মারিয়া ঘুম ভাঙাইয়া তাকে ঘরের বাহির করিয়া দেয়। স্বামীর আগে যে ঘুমাইয়া পড়ে, স্বামীকে যে ঘুম পাড়াইতে জানে না, সে কি মেয়েমানুষ, সে কি বউ?
.
সেদিন রাত্রি সবে দশটা বাজিয়াছে। পাড়ার একজন গল্প করিতে আসিয়াছিল। হাতের আড়ালে তাকে হাই তুলিতে দেখিয়া রসিক আশ্চর্য হইয়া বলিল, শরীর খারাপ নাকি হে?
না, দুপুরে ঘুমোই নি, ঘুম পাচ্ছে।
একটু পরে আরেকবার হাই তুলিয়া সে চলিয়া গেল। রসিক ভাবিল, কোনো ছুতায় মানুষটাকে অনেক রাত পর্যন্ত আটকাইয়া রাখিতে পারিলে ঘুমের সঙ্গে তার লড়াইটা দেখা যাইত। মাঝরাত্রে নিদ্রাহীন চোখে তার জাগিয়া থাকার কসরত দেখিয়া একটু কি আমোদ পাওয়া যাইত না? তা ছাড়া, ঘুম হয়তো সংক্রামক। চোখের সামনে ঘুমে একজনের দেহ অবশ আর চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তার চোখেও হয়তো একটু আবেশ আসিত ঘুমের
না, তা আসিত না। সুধারানীকে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াও কি একদিন তার ঘুম আসিয়াছে?
কাজে আর মন বসিল না, উৎসাহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চেয়ারটা একটু পিছনে ঠেলিয়া দিয়া হেলান দিয়া বসিয়া টেবিলে পা তুলিয়া দিল। ঠিক সামনেই দেয়ালের গায়ে বড় একটি ফটো টাঙানো, দামি ফ্রেমের মধ্যে সাধারণ ঘরোয়া সাজে প্রমীলা দাঁড়াইয়া আছে, মুখে দুষ্টামিভরা তৃপ্তির হাসি। ফটোখানা ছাড়া এদিকের দেয়ালটি একেবারে ফাঁকা, এখানে ওখানে কতকগুলি পেরেকের দাগ শুধু আছে। বুঝা যায়, আরো দু-চার খানা ফটো বা ছবি এ দেয়ালে টাঙানো ছিল, সরাইয়া ফেলা হইয়াছে।
গড়গড়ার নল মুখে দিয়া টানিতে গিয়া রসিকের খেয়াল হইল, প্রমীলার ফটো ঘিরিয়া একটা নূতনত্বের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কালও যার অস্তিত্ব ছিল না— টাটকা ফুলের একটি মালা। তাই বটে, সন্ধ্যার পর ঘরে ঢুকিয়া মৃদু একটু ফুলের গন্ধ সে পাইয়াছিল।
তারপর তামাকের ধোঁয়ায় কখন সে গন্ধ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, ফ্যানের বাতাসে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, খেয়ালও থাকে নাই।
কিন্তু প্রমীলার ফটোতে হঠাৎ টাটকা ফুলের মালা জড়াইল কে? এ বুদ্ধি জাগিল কার? প্রথম কয়েক মাস সে নিজেই বিকালে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় মোড়ের দোকান হইতে মালা কিনিয়া আনিয়া ফটোতে পরাইয়া দিত, একদিন বাসি মালাটি খুলিয়া নতুন মালা পরাইয়া দিবার সময় হঠাৎ তার মনে হইয়াছিল, ফুলের মালা ঘুষ দিয়া স্মৃতির মর্যাদা বজায় রাখিতে চেষ্টা করার মতো ছেলেমানুষি আর হয় না। এ কথা কেন মনে হইয়াছিল কে জানে, সেদিন হইতে আর সে মালা কেনে নাই। এতদিন পরে আবার ফুলের মালা দিয়া প্রমীলার স্মৃতিকে পূজা করিল কে?
অন্দরের দরজা একটু ফাঁক করিয়া বাড়ির চাকর নিখিল ঘরের মধ্যে একবার উঁকি দিয়া চলিয়া গেল। রোজ এই সময় এমনিভাবে সে একবার উঁকি দিয়ে যায়। দু-চার মিনেটের মধ্যে সুধারানী সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, মৃদুস্বরে অনুরোধ জানায়, খেতে চলো। আজো সে আসিল, রসিকের টেবিলে তোলা পায়ের কাছেই টেবিলে হাত রাখিয়া সহজভাবে মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টায় চিবুক পর্যন্ত চোখ তুলিয়া বলিল, খেতে যাবে না?
পা নামাইয়া রসিক সোজা হইয়া বসিল।
রসিক জানে, এসব সুলোচনার ব্যবস্থা। খাইতে বসিবার সময় হইলে সুলোচনার হুকুমে নিখিল আসিয়া দেখিয়া যায় ঘরে বাহিরের লোক কেউ আছে কি না, তারপর সুলোচনার হুকুমেই সুধারানী তাকে ডাকিতে আসে। অল্পদিন আগে তার যে বিবাহ হইয়াছে এ কথা ভুলিয়া গিয়া অনেক দিনের পুরোনো বউয়ের মতো একটু গিনি গিন্নি ভাব দেখানোর করুণ চেষ্টার মধ্যেও রসিক সুলোচনার শিক্ষা ও পরামর্শ স্পষ্টই দেখিতে পায়। কোনো দিন সে আমোদ পায়, কোনো দিন মমতা বোধ করে। আজ কিন্তু মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছিল।
তুমি মালা দিয়েছ?
প্রশ্নে নয়, গলার আওয়াজে সুধারানীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। চিরদিন সে বড় ভীরু, তার উপর কুমারী জীবনের অন্তে এই প্রৌঢ় বিপত্নীকের বউ হইয়া খাপছাড়া অস্বাভাবিক অবস্থায় তার দিন কাটিতেছে।
এসব ঢং শিখলে কোথায়? যেখানেই শিখে থাক, আমি ওসব পছন্দ করি না। বুঝলে?
নির্বাক সুধারানীর আঙুলে আঁচলের কোণটা জড়াইয়া যাইতে থাকে আর রসিক নিজের ওপর বিরক্ত হইয়া ভাবে যে রাগ না করিয়াও এমন কড়া কথা সে বেচারিকে বলিল কেন? এসব কিছু বলার ইচ্ছাও তো তার ছিল না। প্রমীলার ফটোতে মালা-টালা সে যেন আর না দেয়, শুধু এই কথাটা সে সুধারানীকে বলিবে ভাবিয়াছিল। সুধারানী যদি এখন কাঁদিয়া ফেলে সে কী করিবে?
সুধারানী কিন্তু কাঁদাকাটা করিল না, একটু কাঁদো কাঁদোও মনে হইল না তার মুখখানা। একটু রাগের ভঙ্গিতেই যেন দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থামিয়া সে ফিরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিল। তখন একটা সন্দেহ মনে জাগায় রসিক বলিল, যেয়ো না, শোনো। বউঠান তোমাকে মালা দিতে বলেছে নাকি?
জানি না। আমিই যদি দিয়ে থাকি, কী করবে তুমি? মারবে?
জবাব, জবাব দেওয়ার ভঙ্গি, গলার সুর সমস্তই অপ্রত্যাশিত। রসিক আশ্চর্য হইয়া গেল। সুধারানীও যে এতখানি অভিমান করিয়া অন্যায় ভর্ৎসনার এমন ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানাইতে পারে এ যেন একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আজ পর্যন্ত একবারও সুধারানীকে সে এমনভাবে কথা বলিতে শোনে নাই। হয়তো সুযোগ দেয় নাই বলিয়া, সুযোগ পাইলে আগেই হয়তো সে এমনিভাবে ফোঁস করিয়া উঠিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারিত নতুন বউ হইলেও সে কাপড়মোড়া তের বছরের ছিঁচকাঁদুনে খুকি নয়। রসিকের মনে হয়, আজো এইমাত্র সে যেন সুধারানীর অস্তিত্ব প্রথম অনুভব করিয়াছে, এতদিন সে যেন থাকিয়াও ছিল না।
তাই, কয়েক মুহূর্তের জন্য সে যেন ভুলিয়াই গেল যে সুধারানী প্রমীলা নয়। প্রমীলা রাগ করিলে যেভাবে তার রাগ ভাঙানো একরকম অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল রসিকের, আজো তেমনইভাবে বড় রকম ভূমিকা করিয়া সে রাগ দূর করিতে গেল সুধারানীর। কিন্তু বেশি দূর এগোনো গেল না, হাত ধরিয়া প্রাথমিক আদরের ভোঁতা কয়েকটা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই সে চাহিয়া দেখিল, সুধারানীর গাল বাহিয়া টসটস করিয়া জল পড়িতেছে।
প্রমীলা হইলে কাঁদিত না। আগে হইতে কাঁদিতে থাকিলেও কান্না বন্ধ করিয়া দিত। মুখের মেঘ কাটিয়া হাসি ফুটিতে হয়তো সময় লাগিত অনেকক্ষণ, কিন্তু চোখের জল ফেলিয়া সে ন্যাকামি করিত না।
সুধারানীর ছেলেমানুষি কান্না সচেতন করিয়া দেওয়ায় রসিক অপ্রস্তুত হইয়া থামিয়া গেল। সোহাগের কথা বন্ধ করিয়া ভদ্রতা করিয়া বলিল, খিদে পেয়েছে, চলো খেয়ে আসি। রান্না হয় নি?
সুধারানী চোখ মুছিয়া বলিল, হয়েছে। রাগ করলে?
রসিক জবাব দিল না। ক’দিন আগে তার ক্রন্দনশীলা দশ বছরের মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে দিতে হঠাৎ থামিয়া যাওয়ায় সেও এমনিভাবে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাগ করেছ বাবা? বলিয়া বাপের রাগের ভয়ে নিজের কান্না সে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।
১১. সর্ববিদ্যাবিশারদের বউ
বিবাহের রাত্রেই নিবারণ ডান দিকের স্ত্রীকে বাঁ দিকে চালান করিয়া দিয়াছিল।
তুমি এ পাশে এসে শোও, কেমন?
এই তার প্রথম প্রেমালাপ। সুকুমারী একটু ভীরু আর ভাবপ্রবণ মেয়ে, তার আশঙ্কা আর আশা দুইই ছিল অন্যরকমের। ব্যাপারটা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু কারণ জানিবার চেষ্টাও করে নাই। কে জানে, ডান দিকের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হয়তো ব্যথাট্যাথা হইয়াছে মানুষটার, ডান দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে কষ্ট হইবে। এই রকম একটা অনুমান করিয়া সে নীরবে স্বামীর সঙ্গে শয্যায় স্থান পরিবর্তন করিয়াছিল।
সুকুমারী কোনো প্রশ্ন করিল না দেখিয়া নিবারণ নিজেই কারণটা ব্যাখ্যা করিয়া তাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল : স্ত্রীকে বাঁ দিকে শুতে হয়—তাই নিয়ম। পরে এ নিয়ম মেনে চল বা না চল তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না, কিন্তু বিয়ের রাতে—
রাত্রি তখন প্রায় তিনটা বাজে। এত রাত্রে এরকম একটা তামাশার মধ্যে কি কেউ বউয়ের সঙ্গে প্রথম আলাপ আরম্ভ করে? যারা আড়ি পাতিয়াছে তারা শুনিলে কী ভাবিবে! সুকুমারী ভীরু বটে, কিন্তু ভাবপ্রবণতার জোরে ভীরুতাকে জয় করিয়া একটু রাগিয়াই গিয়াছিল। আর কিছু মাথায় না আসুক, সোজাসুজি নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কথা আরম্ভ করিলেই হইত।
নিবারণের বোধ হয় ধারণা হইয়াছিল, কথা আরম্ভ করা মাত্র বউয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া অন্তরঙ্গ স্বামীর মতো সে বলিয়াছিল, কত যে ভুল হয়েছে বিয়েতে বলবার নয়। মন্ত্রতন্ত্র থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী-আচার পর্যন্ত। নতুন জামাই বলে চুপ করে ছিলাম, কিন্তু এমন অস্বস্তি লাগছিল মাঝে মাঝে–
শুনিতে শুনিতে সুকুমারীর সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিয়াছিল। কী সর্বনাশ, শেষ পর্যন্ত তবে কি একটা পাগলের সঙ্গে তার বিবাহ হইয়াছে? একটু পরেই অবশ্য জানা গিয়াছিল ঠিক পাগল নিবারণ নয়, সম্ভবত তামাশাই করিতেছিল।
তুমি যে কথা বলছ না? ও, সাধাসাধি করি নি বলে? বলিয়া এতক্ষণ পরে নিবারণ আবার গোড়া হইতে বউয়ের সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল, সুকুমারীর বন্ধুদের কাছে শোনা বিবরণের সঙ্গে যার অনেক মিল। বেশ মিষ্টি লাগিয়াছিল নিবারণকে সুকুমারীর তখন, ভোর পর্যন্ত সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই অনেকবার রোমাঞ্চ হইয়া সর্বাঙ্গ তার অবশ হইয়া আসিয়াছিল প্রথমবারের চেয়ে ভিন্ন কারণে।
কয়েকটা দিন কাটিতে না কাটিতে সুকুমারী বুঝিতে পারিল, বিবাহের রাত্রে বাঁ দিকে তাকে শোয়াইয়া আর মন্ত্রতন্ত্র এবং স্ত্রী-আচারের ভুল দেখাইয়া দিয়া নিবারণ তার সঙ্গে তামাশা করে নাই। তামাশা যে নিবারণ করে না তা নয়, রসকষ মানুষটার মধ্যে যথেষ্টই আছে, কিন্তু নিয়ম পালনের সময় আর ভুলত্রুটি দেখাইয়া দেওয়ার সময় তামাশা করার পাত্র সে নয়।
বিবাহ হইয়াছে শীতকালে, মুখে তাই সুকুমারী একটু ক্রিম মাখে। নয় তো এমন টুকটুকে রঙ তার, স্নো ক্রিম পাউডার মাখিবার তার দরকার? ক্রিমের কৌটাটা দেখিয়া নিবারণ একদিন বলে কী, এই ক্রিম মাখো তুমি? ছি! আর মেখো না।
সুকুমারী অবাক। –কেন?
এই ক্রিমটা ভালো নয়, চামড়া উঠে যায়। তোমায় অন্য ক্রিম এনে দেব।
সুকুমারীর দুই বউদিদি এই ক্রিম মাখিয়া মাখিয়া চামড়া ফাটা ঠেকাইয়া রাখে—দুজনের চামড়াই বড় ফাটল-প্রবণ। সুকুমারী নিজেও আজ কত বছর এই ক্রিম মাখিতেছে ঠিক নাই। সে একটু হাসিয়া বলে, তুমি কী করে জানলে চামড়া ফাটে?
নিবারণ রীতিমতো বিরক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সুকুমারীর হাসি পরক্ষণেই মিলিইয়া যায়। নিবারণ গম্ভীর মুখে বলে, আমি জানি। আর মেখো না।
এরকম হুকুম কোনো নতুন বউ মানিতে পারে? অন্য একটা ক্ৰিম আনিয়া দিলেও বরং কথা ছিল। বিকালবেলা সুকুমারী মুখে একটু ক্রিম মাখিয়াছে, তারপর কতবার যে আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়াছে হিসাব হয় না, রাত্রি আটটার সময় বাড়ি ফিরিয়া নিবারণ যে কী করিয়া টের পাইয়া গেল!
ক্রিম মেখেছ যে?
নিবারণের মুখ দেখিয়া সুকুমারীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। ঢোক গিলিয়া সে বলে, এমন চড়চড় করছিল—
চড়চড় করবে বলেই তো মাখতে বারণ করেছি। এবার থেকে এই ক্রিম মেখো।
পকেট হইতে নিবারণ নতুন ক্রিমটি বাহির করে দেয়। হাতে নিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া সুকুমারী হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। এই ক্রিম মাখব? এ কি মেয়েরা মাখে? এ তো ব্যাটাছেলের দাড়ি কামিয়ে মাখবার ক্রিম।
নিবারণ জাঁকিয়া বসিয়া বলে, তাই তো এটা আনলাম। দাড়ি কামিয়ে লোকে ক্রিম মাখে কেন, চামড়া চড়চড় করবে না বলে তো? কামানোর পর যে ক্রিমে চড়চড় করে না, এমনি লাগালে তো তোমার আরো বেশি কম চড়চড় করবে।
সেদিন হইতে সুকুমারীর ক্রিম মাখা বন্ধ হইয়াছে।
কেবল মেয়েদের প্রসাধনের একটি বিষয় নয়, নিবারণ জানে না এমন বিষয় নাই। বিবাহের রাত্রে চারদিকে সমস্ত ব্যাপারে ভুলত্রুটি আবিষ্কার করিয়া নিবারণের অস্বস্তি বোধ করিবার অর্থটা ধীরে ধীরে সুকুমারী বুঝিতে পারে। চোখের সামনে মানুষকে ভুল করিতে দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে যাওয়াটা নিবারণের পক্ষে অস্বস্তির ব্যাপারই বটে। এখনো মাঝে মাঝে ওরকম অস্বস্তি তাকে বোধ করিতে হয়। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের কথা, নিজের বাড়িতে চুপ করিয়া থাকিবার প্রয়োজন বেশি হয় না বলিয়া অস্বস্তিটাও তাকে বেশি ভোগ করিতে হয় না। বাড়ির বাহিরে পথেঘাটে, আত্মীয়বন্ধুর বাড়িতে আর আপিসে সে কী করে সুকুমারী জানে না।
সমস্ত বিষয়েই নিবারণ ব্যবস্থা দেয়, সমস্ত ব্যবস্থার সমালোচনা করে। ব্যাখ্যা তার মুখে লাগিয়াই আছে, পিঁপড়ার লাইন বাঁধিয়া চলার কারণ হইতে সেজো পিসির ছেলেটা অপদার্থ কেন পর্যন্ত। তার অনেকগুলো নিয়ম এখন এ বাড়িতে চালু হইয়াছে, তার প্রায় সবগুলো নিষেধই বাড়ির মানুষেরা তার সামনে মানিয়া চলে। আগে যে তার মতামতের একটা মর্যাদা ছিল না, বাড়ির কর্তা হওয়ার পর হইয়াছে, এটুকু সুকুমারী সহজেই অনুমান করিতে পারে। তবে কর্তা হইয়া নিবারণ যে নিয়ম কানুনের বহর আর অবিচার অনাচারে বাড়িটাকে গারদখানা বানাইয়া তুলিয়াছে তা নয়। মত মানানোর জন্য তার কোনোরকম জোর জবরদস্তি নাই, তার মতের বিরুদ্ধে গেলেও সে রাগ করে না বা তার মটা মানিয়া চলিলেও খুশিও হয় না। মত প্রকাশ করিতে পাইলেই তার হইল। কঠোর সে শুধু তার অমতের বেলা। তার নিষেধ কেউ না মানিলে সে রাগিয়া আগুন হইয়া ওঠে—তা সে যত তুচ্ছ বিষয়েই নিষেধ হোক। কাঁচা টমেটো খাওয়া যে কত উপকারী আর কেন উপকারী সে কথা সে প্রায়ই বলে, কিন্তু সে ছাড়া বাড়ির কেউ কাঁচা টমেটো খায় না। খায় কি না খায় এটা সে খেয়াল করিয়াও দ্যাখে না। কিন্তু একবার যদি তার নজরে পড়ে যে কেউ একতলায় খালি পায়ে হাঁটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়। চটি বা স্যান্ডেল পায়ে সকলের হাঁটার ব্যবস্থা সে দেয় নাই, দিলে হয়তো সকলে মিলিয়া একসঙ্গে স্যাঁতসেঁতে উঠানে খালি পায়ে সারা দিন হাঁটিলেও সে চাহিয়া দেখিত না! কিন্তু খালি পায়ে একতলায় হাঁটা সে নিষেধ করিয়া দিয়াছে কিনা, তাই বিধবা পিসিকে পর্যন্ত খালি পায়ে হাঁটিতে দেখিলে সে গজগজ করে আর কাঠের সোল দেওয়া নানা প্যাটার্নের কাপড়ের জুতা কিনিয়া আনিয়া জুতা পরানোর জন্য দু বেলা পিসির সঙ্গে ঝগড়া করে।
পিসি বলে, নে থাম। জুতো পরিয়ে আমায় চিতায় তুলিস।
নিবারণ বলে, ছেলে কী তোমার সাধে বিগড়েছে পিসিমা? তোমার স্বভাবের জন্য।
পিসি তখন কাঁদিতে আরম্ভ করে। দুটি অন্ন দেয় বলিয়া এমনভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান করা নিবারণের উচিত, যতই হোক সে তো তার বাপের বোন? বলিতে বলিতে ভাইয়ের জন্য পিসির শোক উথলাইয়া ওঠে, নিবারণ কিছু বলিলেই পিসির এরকম হয়। বাড়িতে একমাত্র পিসির সঙ্গেই নিবারণ আঁটিয়া উঠিতে পারে না।
পিসির ছেলের নাম নিখিল। যেমন রোগা তেমনই লম্বা চেহারা। ছেলেটা সত্যই এক নম্বরের শয়তান। এদিকে মা হয়তো তার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে আর যুদ্ধে হার মানিয়া নিবারণ গজর গজর করিতেছে, ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া চোখ মিটমিট করিতে করিতে নিখিল প্রশ্ন করে, কাঁদলে মানুষের চোখ দিয়ে জল পড়ে কেন দাদা?
সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার উপক্রম করিতে করিতে সুকুমারী মুখ লাল করিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। ভাবে, উদ্ধত গোঁয়ার ছেলেটার এমন একটা খোঁচা দেওয়া ফাজলামিতে কী রাগটাই না জানি নিবারণ করিবে। হয়তো দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে বাড়ি হইতে। কিন্তু পরক্ষণে নিবারণের ব্যাখ্যা তার কানে আসে—বাপের বাড়ির জন্য মন কেমন করিয়া কাঁদায় একদিন তাকে যে ব্যাখ্যা শুনিতে হইয়াছিল। চাহিয়া দেখিতে পায়, দু হাত পিছনে দিয়া একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া নিবারণ পায়চারি আরম্ভ করিয়াছে।
কিছুক্ষণ পরে উপরে গিয়া নিবারণ নিজেই বলে, বড় বজ্জাত হয়েছে নিখিলটা। কী রকম অপমান করল আমায় দেখলে?
অপমানজ্ঞান আছে তোমার? – সুকুমারীর বড় রাগ হইয়াছিল।
কী বললে? বলিয়া রাগ করিয়া কাছে আসিয়া নিবারণ অন্যমনা হইয়া যায়। এতক্ষণ সুকুমারী মাথা নিচু করিয়া ছিল, মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্র নিবারণ ব্যস্ত হইয়া বলে, তোমার জ্বর হয়েছে।
না, জ্বর হতে যাবে কেন?
উঁহু, তোমার নিশ্চয়ই জ্বর হয়েছে। এ বেলা ভাত খেয়ো না।
স্নেহ করিয়াই নিবারণ তাকে ভাত খাইতে বারণ করে, চিন্তিত মুখে সহানুভূতিভরা কোমল গলায়। অন্য সময় হয়তো সুকুমারী গলিয়া যাইত, এখন ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, কী করে জানলে আমার জ্বর হয়েছে? মুখ দেখে?
নিবারণ গম্ভীর হইয়া যায়।—আমি জানি।
ছাই জান তুমি। রাগটাগ হলে আমার মুখ এরকম লাল দেখায়—সবারই দেখায়। থার্মোমিটার দিয়া দ্যাখো, এক ফোঁটা জ্বর যদি ওঠে—
সব জ্বর থার্মোমিটারে ওঠে না। যাই হোক, এ বেলা ভাত খেয়ো না।
.
ছুটির দিন সকালবেলার ঘটনা, সবে চা-টা খাওয়া হইয়াছে, ভাত খাইতে তখনো অনেক দেরি। তবু সুকুমারীর মনে হয়, সে কতকাল খায় নাই, তখন তখন খুব ঝাল কোনো একটা তরকারি দিয়া দুটি ভাত খাইতে পাইলে বড় ভালো হইত। এখনো দেহেমনে স্বামীর গতরাত্রের আদরের স্বাদ লাগিয়া আছে, এর মধ্যে স্বামীর নিষেধ ভাঙার স্বাদ পাওয়ার জন্য এরকম ছটফটানি জাগার মতো রাগ হওয়া কি তার উচিত? ঠিক রাগ কি না সুকুমারী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেমন একটা ঝাঁজালো বিষাদ! দিন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে অন্য দিনও তো এটা সে অনুভব করিয়াছে, আজ তো নয় কেবল?
এ বেলা তাকে ভাত খাইতে বারণ করিয়া নিবারণ বাজারে গিয়াছে, সমস্ত বাজারটাই কিনিয়া আনিবে। কিন্তু একটি বেহিসাবি জিনিস কি থাকিবে তাতে? যা খাইলে মানুষের ভিটামিন বাড়ে না, রক্তমাংস হাড়ের পুষ্টি হয় না, তাপের উৎপাদন হয় না? খাওয়ার কথা ভাবিলে নিছক জিভে জল আসে মাত্র এমন কোনো বাজে জিনিস?
সকালবেলা এখন সংসারের কত কাজ, ঘরে বসিয়া থাকা তার উচিত নয় জানে, তবু ভাত খাইতে বারণ করার রাগে ঘরেই সুকুমারী বসিয়া থাকে। বাজার আসার পাঁচ মিনিট পরে আসে ছোট ননদ পলটু। বিবাহের এক বছরের মধ্যে পলটুর সন্তান সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। পলটুর ধারণা, এ জগতে এমন কেলেঙ্কারি আর কোনো মেয়ের অদৃষ্টে জোটে নাই।
দাদা যেন কী, ছি! বলিয়া লজ্জায় প্রায় মূর্ছা গিয়া সে বউদিদির গায়ের উপর ঢলিয়া পড়ার উপক্রম করে, একগাদা কত কী সব কিনে এনে বলছে আমার জন্য এনেছে, আমার খেতে ভালো লাগবে। এ অবস্থায় আমাদের নাকি অরুচি হয়!
চোখ বুজিয়া থাকিয়াই পলটু একবার শিহরিয়া ওঠে!
সুকুমারী ভাবে, তবু তো আনিয়াছে? তাই বা কম কী! কাজের ছলে বাজার দেখিতে নিচে গিয়া বাহিরের ঘর হইতে নিবারণের গলা তার কানে ভাসিয়া আসে। খবরের কাগজকে কেন্দ্র করিয়া পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোকের কাছে রাজনীতির বক্তৃতা হইতেছে। কথা শুনিলে মনে হয়, সব যেন তার কাছে অপোগণ্ড শিশু। ভিতরের দিকের জানলার পরদা একটু ফাঁক করিয়া সুকুমারী একবার উঁকি মারে, মুচকি হাসি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সকলের মুখের দিকে তাকায়। সকলেই চা পানে ব্যস্ত। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও তাদের নির্বিবাদে চলিতেছে। এক বছরের মধ্যে ইউরোপের অবস্থা কী দাঁড়াইবে ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিবারণ যেন কেমন করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে চলিয়া গিয়াছিল, কার একটা কথা কানে যাওয়ায় মুখের কথাটা শেষ না করিয়াই বলে, আপনি ভুল করেছেন সতীশবাবু, ও শেয়ার কি কিনতে আছে! এক মাসের মধ্যে অর্ধেক নেমে যাবে। তার চেয়ে যদি—
এখন নয়, এসব বিষয়ে নিবারণের সঙ্গে কেউ বিশেষ তর্ক করে না, ঝগড়া বাধিবে খেলার সময়। আজ ছুটির দিন, তাস আর দাবার আড্ডা বসিবেই, নিবারণ হয়তো তাস হাতে করিয়া দাবার চাল বলিয়া দিতে থাকিবে। ঝগড়া শুনিয়া মাঝে মাঝে ভয় হইবে এই বুঝি মারামারি বাধিয়া গেল। কেন যে ওরা এখানে খেলিতে আসে!
কী ঠাকুর?
এবার মাংস চড়াব।
বাহিরের ঘরের ভেজানো দরজার কাছে ঠাকুর ইতস্ত করে।
নাই বা ডাকলে? নিজেই চড়িয়ে দাও আজকে চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।
সে সাহস ঠাকুরের নাই, মাংস চড়ানোর সময় নিবারণ তাকে ডাকিবার হুকুম দিয়া রাখিয়াছে, না ডাকিলে কী রক্ষা রাখিবে!
শুনিয়া সুকুমারীর মনে হয়, তবে তো বারণ না মানিয়া এ বেলা মাংস দিয়া সে দুটি ভাত খাইলেও নিবারণ রক্ষা রাখিবে না! এতক্ষণ পরে গভীর অভিমানে সুকুমারীর চোখে হঠাৎ জল আসিয়া পড়ে।
নতুন কিছুই আজ বাড়িতে ঘটে নাই, তবু যেন সব সুকুমারীর কেমন খাপছাড়া অর্থহীন মনে হয়, বাড়ির সকলের কাজকর্ম চলাফেরা গল্পগুজব। নিবারণের ভাগনি অর্গান বাজাইয়া গান ধরিয়াছে, নিবারণ নিজেই তাকে গান শেখায়। সুকুমারী নিজেও ভালো গান জানে, ভাগনির ভুল সুর শুনিতে শুনিতে তার হতাশা মেশানো এমন একটা উৎকট কষ্ট হয়! রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিবারণের মা একটি নাতিকে দুধ খাওয়াইতেছিল, ভাঁড়ার ঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে বাড়ির অন্য মেয়েরা চানাচুর খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে, ছেলেমেয়েরা হইচই করিয়া খেলা করিতেছে সারা বাড়িতে। এর মধ্যে কী খাপছাড়া, কী অর্থহীন? এতবড় একটা সংসারের দায়িত্ব যার ঘাড়ে সেই লোকটা একটু খাপছাড়া বলিয়া কি তার এরকম মনে হয়? সঙ্গ ভালো না লাগায়, করার মতো একটা বাজে কাজও হাতের কাছে না থাকায় সুকুমারী ঘরে গিয়া ব্লাউজ সেলাই করিতে বসে। ব্লাউজ দুটি নিবারণ ছাঁটিয়া দিয়াছে। গলার ছাঁট দেখিতে দেখিতে সুকুমারী ভাবে, এ ব্লাউজ পরিলে লোকে হাসিবে না তো?
.
বেলা প্রায় তিনটার সময় সুকুমারীর দাদা পরমেশ আসিল। এই দাদাটির জন্য সুকুমারীর মনে কত যে গর্ব আছে বলিবার নয়। পরমেশ খ্যাতনামা অধ্যাপক, এই বয়সেই কলেজের ছেলেদের জন্য দু খানা বই পর্যন্ত লিখিয়া ফেলিয়াছে। তার ডিগ্রিগুলো উচ্চারণ করিবার সময় আহ্লাদে সুকুমারীর জিভ জড়াইয়া আসে।
খানিকটা দুধবার্লি গিলিয়া সুকুমারী বিছানায় পড়িয়াছিল। ততক্ষণে তার নিজের মনেই সন্দেহ জন্মিয়া গিয়াছে, থার্মোমিটারে ধরা পড়ে না এমন জ্বর হয়তো সত্যসত্যই তার হইয়াছে। ঘরের পাশে একতলার মস্ত খোলা ছাদ, তারই এক প্রান্তে এদিকের ঘরগুলোর সঙ্গে কোনাকুনিভাবে আরেকটি ঘর তোলা হইতেছে। নিবারণ গিয়া মিস্ত্রিদের কাজ দেখাইয়া দিতেছিল আর শুইয়া শুইয়া জানালা দিয়া সুকুমারী তাই দেখিতেছিল। পরমেশ সাড়া দিয়া ঘরে ঢুকিতে সে খুশি হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, এস দাদা।
তোর নাকি জ্বর হয়েছে!
হুঁ।
পরমেশ বসিয়া বলিল, নিবারণ কই?
সুকুমারী আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল। একজন মিস্ত্রি তখন কাজ বন্ধ করিয়া নিবারণের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয় সর্দার মিস্ত্রি। ঘরের মধ্যে ভাইবোন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, আর ওদিকে সর্দার মিস্ত্রি বলে, আপনি যদি সব জানেন বাবু তবে আর আমাদের কাজ করতে ডেকেছেন কেন?
সুকুমারী চাপা গলায় বলে, শিগগির ডাক দাদা—এখুনি হয়তো মেরে বসবে।
নিবারণ কী করিত বলা যায় না, পরমেশের ডাক শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তারপর মিস্ত্রিকে বলিল, তোমাদের আর কাজ করতে হবে না। নিচে যাও, তোমাদের পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। বলিয়া গটগট করিয়া ঘরে চলিয়া আসিল।
তারপর সাধারণ কুশল প্রশ্নের অবসরও তাদের হয় না, শালা-ভগ্নিপতিতে তর্ক শুরু হইয়া যায়। পরমেশ বলে, ওরা সব ছোটলোক, ওদের সঙ্গে কি ঝগড়া মারামারি করতে আছে হে!
নিবারণ আশ্চর্য হইয়া বলে, ছোটলোক? ছোটলোক হবে কেন ওরা? ওই তো দোষ আপনাদের, যারা খেটে খায় তাদেরই ছোটলোক ধরে নেন।
অকারণে খোঁচা খাইয়া পরমেশ একটু চটিয়া বলে, ও, তোমার বুঝি ওসব মতবাদ আছে? কিন্তু তুমিও তো বাবু সামান্য একটা কথা সইতে না পেরে বেচারাদের তাড়িয়ে দিলে?
নিবারণ একটু অবহেলার হাসি হাসিয়া বলে, তাড়িয়ে দিলাম কি ওরা ছোটলোক বলে? ওইখানে তো মুশকিল আপনাদের নিয়ে, বই পড়ে পড়ে সহজ বিচারবুদ্ধিও আপনাদের লোপ পেয়ে গেছে। ঘর তুলব আমি, আমি যেরকম বলব সেরকমভাবে ওরা যদি কাজ না করে তা হলে চলবে কেন? তাই ওদের বিদেয় করে দিলাম—ওরা ছোটলোক বলে নয়।
আজ প্রথম নয়, আগেও কয়েকবার দুজনে তুমুল তর্ক হইয়া গিয়াছে, শেষ পর্যন্ত যা গড়াইয়াছে প্রায় রাগরাগিতে। তর্কটা অবশ্য আরম্ভ করে নিবারণ, বিজ্ঞানের কোনো একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা অভিমত প্রশ্ন বা সন্দেহের মধ্যে ব্যক্ত করিয়া পরমেশের মুখ খুলিয়া দেয়। প্রথমে পরমেশ পরম ধৈর্যের সঙ্গে তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে, তারপর ধৈর্যহারা হইয়া চেষ্টা করে আত্মপক্ষ সমর্থনের, তারও পরে চটিয়া গিয়া আরম্ভ করে আক্রমণ। আজ নিবারণের খোঁচায় প্রথমেই তাকে চটিয়া উঠিতে দেখিয়া সুকুমারী চট করিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া ডাকে, দাদা, একবার শোন। শিগগির শুনে যাও আগে।
পরমেশ কাছে গেলে ফিসফিস করিয়া বলে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, ওর সঙ্গে তর্ক কর কেন? যাই বলুক হেসে উড়িয়ে দিতে পার না?
শুনিয়া আজ পরমেশের হঠাৎ প্রথম খেয়াল হয় যে, তাই তো বটে, নিবারণের সঙ্গে সে তর্ক করে কেন? নিবারণ ছেলেমানুষি করে বলিয়া সেও ছেলেমানুষ হইতে যায় কেন? তারপর দুজনে ঘরে ফিরিয়া যায়, এ কথায় সে কথায় কিছুক্ষণ কাটিয়া যায়, কোথা হইতে এক টুকরো মেঘ আসিয়া বাহিরের রোদটুকু মুছিয়া নিয়া যায়। ভাসা আলগা মেঘ, একটু পরেই সরিয়া যাইবে।
তখন নিবারণ বলে, আচ্ছা আপনারা যে বলেন লাইটের চেয়ে বেশি স্পিড আর কোনো কিছুর হতে পারে না, তার কী প্রমাণ আছে?
পরমেশ তাকায় সুকুমারীর মুখের দিকে, ঠোটের কোণে মৃদু একটা হাসি দেখা দেয়। উদাসভাবে বলে, কে জানে।
জবাব শুনিয়া একটু থতমত খাইয়া নিবারণ খানিক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। তারপর বলে, আমি বলছিলাম, মানুষের স্পিড তো আরো বেশি হতে পারে। যাকগে ও কথা। আচ্ছা, গ্রহণের সময় দেখা গেছে তারার আলো সূর্যের পাশ দিয়ে আসবার সময় সূর্যের আকর্ষণে বেঁকে যায়
তাও আমি জানি না।
ও! বলিয়া নিবারণ এবার গম্ভীর হইয়া যায়। গাম্ভীর্য তার বজায় থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণে সুকুমারীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে এবং পরমেশ দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিয়া ভাবিতেছে, তার রাগটা কমানোর জন্য কী বলা যায়। কিন্তু গাম্ভীর্য নিবারণের আপনা হইতেই উবিয়া যায়। সহজভাবেই আবার সে কথাবার্তা আরম্ভ করে। আলগা মেঘটা উড়িয়া গিয়া আবার চারদিক রোদে ভরিয়া যায়, সুকুমারীর মুখের বিষাদের ছায়াটা কিন্তু সরিয়া যায় না। গম্ভীর হইয়া থাকাটা বেশি অপমানকর জানিয়াই কি নিবারণ গাম্ভীর্য ত্যাগ করিল? আর সমস্ত বিষয়ে যেমন, রাগ-দুঃখে মান-অভিমানের বেলাতেও কি তেমনই জানাটা নিবারণের কাছে বড়? এত যে ভালবাসে তাকে নিবারণ, তার মধ্যেও জানাজানির প্রাধান্য কতখানি কে জানে?
.
সন্ধ্যার সময় পরমেশের সঙ্গে নিবারণও বাহির হইয়া যায়। পরমেশ যায় বাড়ি ফিরিয়া, নিবারণ যায় বেড়াইতে। বেড়াইতে গেলে নিবারণ ফিরিয়া আসে এক ঘণ্টার মধ্যে, আজ নটার সময়ও তাকে ফিরিতে না দেখিয়া মনের ক্ষোভে সুকুমারীর মুখে জ্বালাভরা হাসি দেখা দেয়। ক্ষুধায় পেটটা বড় বেশি জ্বলিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় ক্ষোভটাও তার বেশি হয়। বাড়ির সকলে অনেকবার খবর নিয়া গিয়াছে, দুধ আনিয়া খাইতে সাধিয়াছে, সুকুমারী খায় নাই। পলটু বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়া গিয়াছে নটা পর্যন্ত। একা হওয়ামাত্র ক্ষোভটা যেন একলাফে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে।
আর কী সুকুমারীর জানিতে বাকি আছে, এতকাল তাকে ভালবাসার মধ্যে এত বৈচিত্র্য নিবারণ কী করিয়া আনিয়াছে? আর সব সে যেমন জানে বলিয়া করে, ভালবাসিবার নিয়ম-কানুনও জানে বলিয়া মানিয়া চলে! পলটুর মতো অবস্থায় মেয়েদের অরুচি হয় জানে বলিয়া সে যেমন বিশেষ বিশেষ খাবার জিনিস আনিয়া দিয়াছে, ওর মধ্যে দয়া-মায়া স্নেহ-মমতার প্রশ্ন কিছু নাই, স্ত্রীর সঙ্গে কী করিয়া ভাব করিতে, স্ত্রীকে কী করিয়া আদরযত্ন করিতে হয় তাও তেমনই জানে বলিয়াই তার সঙ্গে এমনভাবে ভাব করিয়াছে, তাকে এত আদরযত্ন করিয়াছে নয়তো নিবারণের মতো মানুষের কাছে ওরকম রোমাঞ্চকর মধুর কথা ও ব্যবহার কে কল্পনা করিতে পারে, প্রতিদিন রাত্রে ঘরে আসিবার পর এতকাল তার যা জুটিয়াছে?
নিজের মনের জানাজানি প্রক্রিয়াকে সেও যে নিবারণের চেয়ে অনেক বেশি খাপছাড়াভাবে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিতেছে এটা অবশ্য তার খেলায় হয় না, বেশ জোরের সঙ্গেই অনেক কিছু জানিয়া চলিতে থাকে। একবারে নিঃসন্দেহে হইয়া মানে, রাত্রে নিবারণকে একেবারে নতুন মানুষ মনে হইত কেন, তার কারণটা। বাপের বাড়িতে যে রাত্রিগুলো নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে সেগুলো ছাড়া প্রত্যেকটি রাত্রি আজ দুপুরেও তার কাছে রোমাঞ্চ ও শিহরনে ভরা ছিল, এখন সব ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। সব ফাঁকি নিবারণের, শুধু নিয়ম পালন।
আজ একটু রাগ হইয়াছে তাই নিয়মমাফিক স্ত্রীকে স্নেহ করিবার ইচ্ছাটাও উবিয়া গিয়াছে। পরমেশের উপর রাগটা চলিয়া গেল দু-চার মিনিটের মধ্যেই, কিন্তু অসুস্থা উপবাসী বউকে আর ক্ষমা করিতে পারিল না। কী করিয়া করিবে? যেখানে দরদ আন্তরিক নয়, সেখানে সুবিচারের প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে?
বিবাহের আগে এরকম বিশ্লেষণের ক্ষমতা সুকুমারীর ছিল না, কোনো মানুষের মাথার মধ্যে যে নিজের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত দাঁড় করানোর জন্য দৈনন্দিন জীবনের রাশি রাশি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আবর্জনা হইতে যুক্তিরূপী প্রয়োজনীয় টুকরাগুলোকে শুধু বাছিয়া নেওয়ার এমন একটা প্রক্রিয়া চলিতে পারে এ কথা কল্পনা করার ক্ষমতাও ছিল না। এখন সে যেন খানিক খানিক বুঝিতে পারে, এ ধরনের চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া তার পক্ষে ঠিক উচিত হইতেছে না, এসব ছেলেমানুষি কল্পনামাত্র, এরকম জ্বালাভরা দুঃখ ভোগ করার কোনো কারণ ঘটে নাই। তবু অন্ধকার ঘটে ছটফট করিতে করিতে না ভাবিয়া সে পারে না যে, হায়, যে স্বামী উঠিতে বসিতে চলিতে-ফিরিতে বলে এই করা উচিত আর ওই করা উচিত নয়, যে ক্রিম মাখিতে দেয় না, অকারণে উপোস করাইয়া রাখে আর একরকম বিনা দোষে রাগ করিয়া বাড়ি ফিরিতে দেরি করে, তার সঙ্গে জীবন কাটাইবে কী করিয়া?
দশটার পরে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া নিবারণ আলো জ্বালে। সুকুমারী চোখ বুজিয়া ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া থাকে আর চোখের পাতা একটু ফাঁক করিয়া চুপিচুপি নিবারণ কী করে দেখিবার চেষ্টা করিয়া রামধনুর রঙ দেখিয়া বসে। চোখে একটু জল জমিয়াছে। চোখ মেলিয়া হয়তো সব স্পষ্ট দেখা যাইবে, চোখের পাতা একটুখানি ফাঁক করিয়া কিছু দেখা সম্ভব নয়,— অন্তত চোখ না মুছিয়া।
জামাকাপড় ছাড়িয়া নিবারণ মুখহাত ধুইতে বাহির হইয়া যায়। সুকুমারী তাড়াতাড়ি চোখ দুটি মুছিয়া ফেলে বটে, কিন্তু এবার আরো বেশি জল আসিয়া পড়ে। জানে জানে, নিবারণের মতো সব না জানুক, এটুকু সে জানে যে নিবারণ আর কোনো দিন তার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা বলিবে না।
নিবারণ ঘরে ফিরিয়া আসে। খানিকক্ষণ তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। তারপর প্রায় কানের কাছে অতি মৃদুস্বরে তার প্রশ্ন শুনিতে পায়, কাঁদছ কেন?
সুকুমারীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে, এক মুহূর্তে তার এতক্ষণের সমস্ত জানা যেন বাতিল হইয়া যায়। চোখে একটু জল দেখিবামাত্র রাগ কমিয়া গিয়াছে! দাদাকে পরামর্শ দিয়া অপমান করানোর মতো অমার্জনীয় অপরাধের জন্য যে রাগ হইয়াছিল। এমন গভীর মায়া তার জন্য তার স্বামীর, আর সে এতক্ষণ সন্দেহ করিয়া মরিতেছিল কিছুই তার আন্তরিক নয়!
চোখের পলকে উঠিয়া সুকুমারী নিবারণের পা চাপিয়া ধরে।—আমায় মাপ কর আমি বড্ড অন্যায় করেছি।
নিবারণ অবশ্য তখন তাকে বুকে তুলিয়া নেয়।—তোমার জ্বর তো বেড়েছে দেখছি।
জ্বর বেড়েছে? গা গরম হয়েছে আমার?
বেশ গরম হয়েছে। দাঁড়াও, একবার থার্মোমিটার দিয়ে দেখি।
থার্মোমিটারে দেখা যায়, সত্যই সুকুমারীর জ্বর হইয়াছে, প্রায় একশর কাছাকাছি। থার্মোমিটারটি রাখিয়া আসিয়া নিবারণ সুকুমারীর গায়ে আদর করিয়া হাত বুলাইয়া দেয়। সুকুমারী আরামে চোখ বোজে।
নিবারণ বলে, আমার সত্যি রাগ হয়েছিল। রাগ করে থাকতে পারলাম না কেন জান?
সুকুমারী নীরবে মাথাটা একটু কাত করে। মনে মনে বলে, জানি, আমায় ভালবাস বলে।
আবার প্রায় কানের সঙ্গে মুখ লাগাইয়া অতি মৃদুস্বরে নিবারণ বলে, আজ জানতে পারলাম কিনা তোমার খোকা হবে, জানা মাত্র সব রাগ কেমন জল হয়ে গেল।
ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া সুকুমারী বিস্ফারিত চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, জানা মাত্র সব রাগ জল হয়ে গেল! এই তবে নিবারণের ক্ষমা করিবার কারণ। যে খোকার মা হইবে তার গুরুতর অপরাধও ক্ষমা করিতে হয়! গায়ের চামড়া বড় চড়চড় করিতে থাকে সুকুমারীর, যেখানে যেখানে নিবারণের হাত বুলানোয় এতক্ষণ আরামের সীমা ছিল না। পেটটা জ্বালা করিতে থাকে। মুখটা তিতো লাগে। মাথাটা ঘুরিতে থাকে।
হঠাৎ সে করে কী, নিবারণকে দু হাতে ঠেলিয়া দিয়া ছুটিয়া খোলা ছাদে চলিয়া যায়। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় মিস্ত্রিরা ঘরের যে গাঁথনি আরম্ভ করিয়াছিল অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। তবু সেই হাতখানেক উঁচু গাঁথনিতে হোঁচট খাইয়া সুকুমারী দড়াম করিয়া পড়িয়া যায়।
১২. অন্ধের বউ
বিবাহের এক বছর পরে ধীরাজ অন্ধ হইয়া গেল। চোখের একটা অসুখ আছে, বড় বিপজ্জনক অসুখ, চোখের ভিতরের চাপ যাতে বাড়িয়া যায়। অবস্থাবিশেষে এক দিনের মধ্যেই মানুষের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।
আগের দিনটা ছিল বিবাহের বার্ষিক তিথি। রাত্রিটা দুজনে জাগিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল! সারা রাত কয়েক মিনিটের জন্যও চোখ না বুজিয়া প্রতিদিন সকালে একেবারে সূর্যের মুখ না দেখিলেও রাতজাগাটা তাদের অবশ্য বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। বিবাহের প্রথম বছরে রাত দুটোর আগে ফিসফিসানি শেষ হওয়াটা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর পক্ষেও স্বাভাবিক নয়।
ধীরাজ চোখে একটু যন্ত্রণা বোধ করিতেছিল, একটু ঝাপসা দেখিতেছিল। চোখ দুটি বেশ লাল দেখাইতেছিল। কিন্তু বিবাহের তিথিকে যথাযোগ্য সম্মান করার উৎসাহে ওসব সামান্য বিষয়কে তারা গ্রাহ্যও করে নাই। সুনয়না বলিয়াছিল, তাই বলে আজ রাতে ঘুমোতে পাবে না। কাল সারা দিন ঘুমিয়ো, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমারও তো চোখ জ্বালা করছে।
তবে একটু সেই রকম নাচ দেখাও?
চোখ বোজো?
.
পরদিন বিকালের দিকে ডাক্তার ডাকা হইল। তারপর তাড়াহুড়া ছুটাছুটি করিয়া অনেক কিছুই করা হইল। কিন্তু তখন বড় বেশি দেরি হইয়া গিয়াছে। ভোরে সুনয়নার হাত ধরিয়া ছাদে দাঁড়াইয়া নূতন সূর্যকেও ধীরাজ যখন ঝাপসা দেখিতেছিল তখন সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করিলেও হয়তো কিছু হইতে পারিত। কিন্তু তখন কে ভাবিয়াছিল টকটকে লাল চোখ, যন্ত্রণা, ঝাপসা দেখা চোখের মধ্যে আলোর ঝলকমারা, এসব অন্ধ হওয়ার ভূমিকা! ওসব তারা রাতজাগার ফল বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে।
বিশেষজ্ঞ অনেক রকম পরীক্ষা করিলেন কিন্তু অপারেশন করিতে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন, আর কিছুই করিবার নাই।
পরদিন সকালে জগতের আলোর উৎস যথাসময়ে আকাশে দেখা দিলেন কিন্তু ধীরাজ সেটা টেরও পাইল না। তার চোখের আলো চিরদিনের জন্য নিভিয়া গিয়াছে।
চোখের ডাক্তার স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, রাতজাগা ধীরাজের অন্ধ হওয়ার আসল কারণ নয়। রাত না জাগিলেই অবশ্য ভালো ছিল, কিন্তু তাতেও যে ধীরাজের চোখ বাঁচিত তাই বা জোর করিয়া কে বলিতে পারে? এ বড় সাংঘাতিক অসুখ, কত লোকের চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষের মন কি সহজে এসব যুক্তি মানিতে চায়? সুনয়নার কেবলই মনে হয়, ওভাবে জোর করিয়া স্বামীকে রাত না জাগাইলে চোখের অসুখটা কখনো এত তাড়াতাড়ি এরকম বাড়িয়া যাইত না। অন্তত রোগের লক্ষণগুলোকে রাতজাগার ফল ভাবিয়া নিশ্চয় তারা অবেহলা করিত না, সকালবেলাই চোখের অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত। ভাবে আর চোখের জলে সকালবেলার আলো এমন ঝাপসা দেখায় যেন সেও আধাআধি অন্ধ হইয়া গিয়াছে।
সেই ঝাপসা দৃষ্টিতে স্বামীর বিকৃত মুখখানা দেখিতে দেখিতে সে হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, ওগো, আমার জন্যেই আমাদের এ সর্বনাশ ঘটল।
ধীরাজ মরার মতো বলিল, তোমার কী দোষ?
সুনয়না সজোরে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, কার দোষ তবে? কে তোমার টকটকে লাল চোখ দেখেও তোমায় ঘুমোতে দেয় নি? সকালে কে তোমায় বলেছে, একটু ঘুমোলেই সব সেরে যাবে? আমি তোমার চোখ নষ্ট করেছি….স্বামীর চোখখাগি হতভাগি আমি, আমার মরণ নেই। আমিও অন্ধ হয়ে যাব—নিজের চোখ উপড়ে ফেলব। যদি না উপড়ে ফেলি, মা কালীর দিব্যি করে বলছি—
চুপ, ওসব বলতে নেই।
ধীরাজ ব্যস্ত হইয়া সুনয়নার একখানা হাত হাতড়াইয়া খুঁজিতে আরম্ভ করায় সুনয়না হঠাৎ শিহরিয়া অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল। ধীরাজের কাকা অন্ধ, প্রথম এ বাড়িতে আসিয়া তাকে প্রণাম করার পর এমনিভাবে আন্দাজে তার গায়ে মাথায় শীর্ণ হাত বুলাইয়া কাকা তাকে অভ্যর্থনা আর আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন।
কী খুঁজছ? কী খুঁজছ তুমি?
তোমার হাত কই?
এই যে—
তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া ধীরাজ সান্ত্বনার সুরে বলিতে লাগিল, ওসব কথা মনেও এনো না। তোমার চোখ গেলে আমি বাঁচব কী করে? এখন থেকে তোমার চোখ দিয়েই তো দেখব। তুমি আমার সেবা করবে, কাজ করে দেবে, বইটই পড়ে শোনাবে—
সুনয়নার হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরাজ তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে থাকে। সুনয়নার মাথাটা হঠাৎ এমন জোরে তার বুকে আসিয়া পড়িয়াছে যেন সে তার বুকেই মাথা কুটিয়া মরিতে চায়। সে অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সান্ত্বনা আর সাহস পাওয়ার বদলে সে নিজেই অপরজনকে বুঝাইয়া আদর করিয়া শান্ত করিতেছে, এটা দুজনের কারো কাছে খাপছাড়া মনে হইল না। ভালবাসার এই অন্ধ ব্যাকুলতার মতো দুর্ভাগ্যের ভালো ওষুধ জগতে আর কী আছে?
ধীরাজ বেশি ব্যাকুল হয় নাই। কতকটা বজ্রাহত মানুষের মতো সে বিছানায় পড়িয়া আছে, মুখে বেশি কথা নাই, অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া নাই, কী পাপে তার এমন শাস্তি জুটিল ঈশ্বরের কাছে সে কৈফিয়ত দাবি করা নাই, লোভী শিশুর মতো সকলের সহানুভূতি গিলিবার অধীর আগ্রহও নাই। এখনো সে যেন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই, চিরদিনের জন্য সে অন্ধ হইয়া গিয়াছে। মনের তলে এখনো যেন তার একটা যুক্তিহীন অন্ধ আশা জাগিয়া আছে, হয়তো সব ঠিক হইয়া যাইতে পারে। ইতোমধ্যেই সুনয়নাকে সে বলিয়াছে- তা ছাড়া কী জান, কিছুদিন পরে হয়তো একটু একটু দেখতে পাব। ভালো দেখতে পাব না বটে, চশমা-টশমা নিয়ে হয়তো ধোঁয়াটে ঝাপসা মতো কাছের জিনিস শুধু দেখতে পাব, তবু দেখতে পাব তো। খুব বড় একজন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হবে।
ধীরাজের মনে যতখানি হতাশা জাগা উচিত ছিল, ধীরাজের কাছে আমল না পাইয়া তার সবখানি যেন সুনয়নাকে আশ্রয় করিয়া তাকে আত্মহারা করিয়া দিয়াছে। ধীরাজের আপসোস আর হাহুতাশ যেন মুক্তি পাইতেছে তার মুখে।
পরপর দুটি রাত্রি সে ঘুমায় নাই। একটি রাত্রি জাগিয়াছে স্বামীর সোহাগ ভোগ করিয়া, আর একটি রাত্রি জাগিয়াছে অন্ধ স্বামীর স্ত্রী হইয়া জীবন কাটানোর বীভৎস অসুবিধাগুলোর কথা কল্পনা করিয়া। সারা রাত সে আলো নিভায় নাই। প্রথম রাত্রে তারা আলো নিভায় নাই, দুজনে দুজনকে দেখিবে বলিয়া। পরের রাত্রে সে আলো নিভায় নাই অন্ধকারের ভয়ে। হাসপাতাল হইতে ধীরাজ বাড়ি ফিরিয়াছিল রাত্রি প্রায় এগারটার সময়, শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন, অন্ধ ধীরাজ। একবাটি দুধ চুমুক দিয়া খাইয়াই সে শুইয়া পড়িয়াছিল। শুইয়া পড়িতে তাকে সাহায্য করিয়াছিল বাড়ির প্রায় সকলে, মা বাবা ভাই বোন পিসি খুড়ি ভাইপো ভাইঝি ভাগনে ভাগনির দল। বাড়ির ঠাকুর চাকর পর্যন্ত দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুধু আসে নাই ধীরাজের অন্ধ কাকা। ধীরাজের মার মৃদু কান্নার শব্দ শুনিতে শুনিতে তখন সুনয়নার কানের মধ্যে হঠাৎ ভাঙা কাঁসির বেতালা আওয়াজের মতো কী যেন ঝমঝম করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল, বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল ঘরখানা পাক খাইয়া অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল।
মূর্ছা নয়, মূর্ছা গেলে সুনয়না পড়িয়া যাইত, জ্ঞান থাকিত না। একটু টলিতে থাকিলেও সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে প্রায় মিনিটখানেক চোখ দিয়াই যেন সেই গাঢ় স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার দেখিয়াছিল। কানের মধ্যে তখন শব্দ থামিয়া গিয়াছে। বাহিরেও কোনো শব্দ নাই। সেই স্তব্ধতাকেও সুনয়নার মনে হইয়াছিল সাময়িক অন্ধকারের অঙ্গ।
তারপর সেই নিবিড় কালো অন্ধকার পরিণত হইয়াছিল গাঢ় কুয়াশায় এবং ক্রমে ক্রমে কুয়াশাও কাটিয়া গিয়াছিল। সকলের কথার গুঞ্জনধ্বনি হঠাৎ স্পষ্ট ও বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এক অজানা আতঙ্কে তখন সুনয়নার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছে। সে আতঙ্ক ধীরাজের চোখের জন্য নয়—চোখ যে তার নষ্ট হইয়া গিয়াছে সুনয়না আগেই সে খবর পাইয়াছিল। অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ কানের কাছে জোরে শব্দ হইলে কিছুক্ষণের জন্য মানুষ যেমন বেহিসাবি আতঙ্কে অভিভূত হইয়া যায়, কী জন্য আতঙ্ক তাও বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না, চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিবার পরেও সুনয়না অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই রকম একটা আতঙ্ক অনুভব করিয়াছিল।
তাকে চমক দিয়া বাস্তবে টানিয়া আনিয়াছিল ঘর খালি হওয়ার পর ধীরাজের অস্ফুট প্রশ্ন: আলো নিভালে না?
এ প্রশ্ন সুনয়না অনেকবার শুনিয়াছে। শোয়ার আগে আলো নিভাইতে তার প্রায়ই খেয়াল থাকে না, ধীরাজ মনে পড়াইয়া দেয়। কাল এই পরিচিত সাধারণ প্রশ্নটি শুনিয়া আকস্মিক উত্তেজনায় তার দম যেন আটকাইয়া আসিয়াছিল। ধীরাজ কী তবে ঘরের আলো দেখিতে পাইতেছে!
ধীরাজ সাড়া দেয় নাই। তখন সুনয়না বুঝিতে পারিয়াছিল, ঘুমের অভ্যাস বশে ধীরাজ ওকথা বলিয়াছে। ঘরে আলো জ্বালানো থাক বা নিভানো হোক, ধীরাজের তাতে সব সমান।
বুকের অস্বাভাবিক ঢিপঢিপানি কমিয়া তখন স্বাভাবিক কান্না বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু ধীরাজের ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ার ভয়ে প্রাণ খুলিয়া সে কাঁদিতেও পারে নাই।
তারপর কখনো সন্তর্পণে বিছানায় উঠিয়া কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া আবার নামিয়া আসিয়া, কখনো একদৃষ্টিতে ঘুমন্ত স্বামীর মুখ দেখিয়া, কখনো জানালার শিক ধরিয়া পাশের বাড়ির উঠানে আবছা চাঁদের আলোয় চেনা জিনিসগুলোকে নূতন করিয়া চিনিবার চেষ্টা করিয়া আর সমস্তক্ষণ আকাশপাতাল ভাবিয়া সে রাত কাটাইয়াছে। ঘরের আলো নিভানোর কথা একবারও তার মনে পড়ে নাই।
.
বেলা বাড়িলে কয়েকজন প্রতিবেশী দেখা করিতে এবং দুঃখ জানাইতে আসিলেন। আগে সুনয়না ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, আজ সে উদ্ধতভাবে বিছানার কাছ হইতে শুধু একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়ায়। এই সামান্য ব্যাপারে তার এমন বিরক্তি বোধ হয় বলিবার নয়। সকলের সমবেদনার গাম্ভীর্যে বিকৃত মুখ দেখিয়া আর অর্থহীন ভদ্রতার মিঠা মিঠা কথা শুনিয়া গায়ে যেন তার আগুন ধরিয়া যাইতে থাকে। একজন অকালবৃদ্ধ সবজান্তা ভদ্রলোক যখন অদ্ভুত একটা আপসোসের শব্দ করিয়া বলেন যে অ্যালোপ্যাথি না করিয়া হোমিয়োপ্যাথি করিলে হয়তো উপকার হইত, তখন বাঘিনীর মতো তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাকে ঘরের বাহির করিয়া দেওয়ার ইচ্ছাটা দমন করা কাল রাত্রে কান্না চাপিয়া রাখার চেয়েও সুনয়নার কঠিন মনে হয়।
হঠাৎ সে শুনিতে পাইল তার গলার আওয়াজে তারই মনের কথা কে যেন উচ্চারণ করিতেছে : আপনারা এখন আসুন, উনি একটু বিশ্রাম করবেন।
সকলে আহত বিস্ময়ে তার এলোমেলো চুল, ক্লিষ্ট মুখ আর বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকায়। ধীরাজ ভদ্রতার খাতিরে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বিনয়ের হাসি হাসিবার চেষ্টা করিতেছিল, তার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়।
সকলের আগে কথা বলেন অকালবৃদ্ধ ভদ্রলোকটি : চল হে চল, আপিসের বেলা হল।
ধীরাজের ছোট ভাই বিরাজ সকলকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আনিয়াছিল, সকলে চলিয়া গেলে সে বলিল, তুমি সকলকে তাড়িয়ে দিলে বউদি!
ধীরাজ ভর্ৎসনার সুরে বলিল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?
সুনয়না উদ্ভ্রান্তভাবে বাঁ হাতের বুড়া আঙুল দিয়া নিজের কপালটা ঘষিতে থাকে, কথা বলে না। বিরাজ বছর তিনেক ডাক্তারি পড়িতেছে, সুনয়নার মূর্তি দেখিয়া এতক্ষণে তার খেয়াল হয়, হয়তো তার অসুখ করিয়াছে।
তোমার অসুখ করেছে নাকি বউদি!
সুনয়না মাথা নাড়িয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরেই বিরাজ গিয়া খবর দিল, দাদা ডাকছে বউদি।
ঘরে ফিরিয়া গিয়া ধীরাজের পরিবর্তন দেখিয়া সুনয়না স্তম্ভিত হইয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে, ডান হাতে সে নিজের চুলগুলো সজোরে মুঠা করিয়া ধরিয়া আছে।
সুনয়না সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে?
ধীরাজ অস্বাভাবিক চাপা গলায় বলিল, তোমার অসুখ করেছে তো? আমি টের পাই নি! বিরাজ না বললে জানতেও পারতাম না। এবার থেকে তোমার অসুখ করবে আর আমি না জেনে তোমায় খাটিয়ে মারব, বকব
ধীরাজ হঠাৎ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ঠকাও, ঠকাও, তুমিও আমায় ঠকাও। চোখে তো দেখতে পাই না, যা ইচ্ছা তাই বলে কচি ছেলের মতো ভোলাও। বলিয়া ধীরাজ কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।
আগের মতো শান্তভাবে ধীরাজ কথাগুলো বলিলে সুনয়না হয়তো তার পাশে বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদাকাটা আরম্ভ করিয়া দিত। স্বামীর ব্যাকুলতা আর কান্না দেখিয়া নিজেকে সে সংযত করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে পাশে বসিয়া স্বামীর মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া কয়েক ঘণ্টা আগে ধীরাজ যেভাবে তার মাথায় হাত বুলাইয়া তাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল তেমনিভাবে এখন তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, ওরকম কোরো না। পাগল হয়েছ, তোমায় ঠকাব? ঠাকুরপোর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে? ভাবনায় চিন্তায় রাত জেগে মুখ একটু শুকনো দেখাচ্ছে, ওমনি ঠাকুরপো ধরে নিল আমার অসুখ হয়েছে। অসুখ হলে তোমায় বলব না?
কিন্তু বিরাজ যে বলল তোমার নার্ভাস ব্রেকডাউনের উপক্রম হয়েছে।
ঠাকুরপো তো মস্ত ডাক্তার!
এমন সময় আসিলেন পিসিমা। সুনয়নার দিকে কেউ নজর দিতেছে না বলিয়া বিরাজ বোধ হয় বাড়ির লোককে একটু খোঁচাইয়া দিয়াছিল, ঘরে ঢুকিয়াই পিসিমা বলিতে আরম্ভ করিলেন, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, তুমি কী আরম্ভ করে দিয়েছ বউমা? কাল থেকে উপোস দিচ্ছ এয়োস্ত্রী মানুষ
পিসিমার পিছনে পিছনে কাকিমাও আসিয়াছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, আহা, থাক, থাক। এস বউমা, একটু কিছু খেয়ে নেবে এস।
কাকিমা একটু গম্ভীর চুপচাপ মানুষ, কারো সঙ্গে বেশি মেলামেশা করেন না। এতদিন মানুষটাকে দেখিলেই সুনয়নার বড় মায়া হইত, মনে হইত, আহা, দশ-বারো বছর বেচারি অন্ধ স্বামীকে নিয়া ঘর করিতেছে। আজ কাকিমার শান্ত কোমাল মুখখানা দেখিয়া তার গভীর বিতৃষ্ণা বোধ হইতে লাগিল, আন্তরিক মমতাভরা কথাগুলো শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, সুযোগ পাইয়া তাকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছেন, পিসিমার মৃদু ভর্ৎসনার প্রতিবাদ করিয়া যেন ইঙ্গিতে বলিতেছেন, আহা থাক থাক, ওকে বকবেন না, ও এখন আমার দলের।
একটু আগে সুনয়না হয়তো নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের মতো গুরুজন দুজনকেও অপমান করিয়া বসিত। কিন্তু ধীরাজের আকস্মিক উদ্ভ্রান্তভাব তার সমস্ত সংগত ও অসংগত উচ্ছ্বাসের বাহির হওয়ার পথ তখনো বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া সে নীরবে কাকিমার সঙ্গে চলিয়া গেল।
.
একবার ভাঙিয়া পড়িয়াই ধীরাজের ধৈর্য আর সংযম যেন নষ্ট হইয়া গেল। এতক্ষণে সে যেন টের পাইয়াছে তার চারদিকে যে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে সেটা রাত্রির সাময়িক অন্ধকার নয়, ভাগ্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কখনো দুঃখে সে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িতে লাগিল, কখনো অধীর হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। মা একবার ছেলেকে দেখিতে আসিয়া ছেলের অবস্থা দেখিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, চোখে আঁচল দিয়া পালাইয়া গেলেন। বাড়ির সকলে আসিয়া নানাভাবে তাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাতে সে যেন আরো অশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।
সব কথার জবাবে গুমরাইয়া গুমরাইয়া কেবলই বলিতে লাগিল, অন্ধ হয়ে বেঁচে থেকে কী হবে, এর চেয়ে মরাই ভালো।
ধৈর্য আর সংযম দেখা দিল সুনয়নার মধ্যে। মনের সমস্ত অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাকে সে যেন জোর করিয়া মনের জেলে পুরিয়া ফেলিল, বাহিরে আর তাদের অস্তিত্বের কোনো চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। দুজনের দ্রুত পরিবর্তন দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তারা যেন পরামর্শ করিয়া পরস্পরের মানসিক অবস্থাকে অদল-বদল করিয়া নিয়াছে। ধীরাজ যতক্ষণ শান্ত ছিল ততক্ষণ পাগলামি করিয়াছে সুনয়না, এবার ধীরাজকে পাগল হওয়ার সুযোগ দিয়া সুনয়না আত্মসংবরণ করিয়াছে।
১৩. জুয়াড়ির বউ
ধরিতে গেলে জুয়ার দিকে মাখনের ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা হইতেই। তার অল্প বয়সের খেয়াল আর খেলাগুলির মধ্যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের এমন জোরালো মানসিক বিকারের সূচনা অবশ্য কেউ কল্পনা করিতে পারিত না। বাজি ধরে না কে, লটারির টিকিট কেনে না কে, মেলায় গেলে নম্বর লেখা টেবিলে দু-চারটা পয়সা দিয়া ঘূর্ণমান চাকায় লেখা নম্বরের দিকে তীর ছোড়ে না কে? এসব তো খেলা—নিছক খেলা। তবে মাখনের একটু বাড়াবাড়ি ছিল। কথায় কথায় সকলের সঙ্গে বাজি ধরিত, লটারির টিকিট কেনার পয়সার জন্য বিরক্ত করিয়া করিয়া গুরুজনের মার খাইত, মেলায় গিয়া অন্য জিনিস কেনার পয়সা তীর ছুড়িবার খেলায় হারিয়া আসিত। এই তুচ্ছ ছেলেমানুষি পাগলামি যে একদিন একটা মারাত্মক নেশায় দাঁড়াইয়া যাইবে এ কথা কারো মনে আসে নাই।
প্রকৃত জুয়া আরম্ভ হয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে। মাখন তখন কলেজে গোটা দুই পরীক্ষা পাস করিয়াছে। নলিনীর দাদা সুরেশ ছিল তার প্রাণের বন্ধু, একদিন সে-ই ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিয়া গেল।
‘আজ একটু রেস খেলি চ’ মাখন।’
‘রেস? আমার কাছে মোটে দশটা টাকা আছে।’
‘আবার কত চাই? লাগে তো আমি দেবখন- আয়।’
সাত টাকা জিতিয়া দুজনের সেদিন কী ফুর্তি! সায়েবি হোটেলে সাতগুণ দাম দিয়া চিংড়ি মাছের মাথা আর মুরগির ঠ্যাং গিলিয়া বায়স্কোপ দেখিয়া সুরেশ বাড়ি গেল আর মাখন ফিরিল তার মেসে। তারপর আর দু-একবার রেস খেলিতে গিয়া কয়েকটা টাকা হারিয়াই সুরেশ যদি-বা বিরক্ত হইয়া মাঠে যাওয়া একরকম বন্ধ করিয়া দিল, একটা দিন যাইতে না পারিলে মাখনের মন করিতে লাগিল কেমন কেমন। সুরেশের কাছে প্রায়ই সে টাকা ধার করিতে লাগিল।
আরেকটা পরীক্ষা কোনোরকমে পাস করিবার পর একদিন হিসাব করিয়া দেখা গেল সুরেশের কাছে মাখন অনেক টাকা ধারে। বন্ধুকে টাকা ধার দিতে দিতে সুরেশের নামে পোস্টাফিসে জমা টাকাগুলি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।
‘এবার বাড়ি গিয়ে তোর টাকা এনে দেব।’
ছেলেকে একেবারে এতগুলি টাকা দেওয়া মাখনের বাবার পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না, তবু তিন-তিনটা পরীক্ষা পাস করা ছেলে চাকরির চেষ্টা করার আগে একজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেখিতে চায়, সুযোগ না পাইলে ভয়ানক কিছু করিয়া বসিবার মতো প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে চায়, টাকাটা তাকে না দিলেই বা চলে কেমন করিয়া?
বন্ধুকে দেওয়ার জন্য টাকাগুলি সঙ্গে নিয়া মাখন কলিকাতায় পৌঁছিল শনিবার সকাল দশটার সময়। সমস্ত পথ সে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এতদিন অল্প টাকা নিয়া খেলার জন্য সে হারিয়াছে। বেশি টাকা নিয়া খেলিলে জিতিবার সম্ভাবনা বেশি। বন্ধুর সমস্ত ঋণ একেবারে শোধ করার কি দরকার আছে? আজ যদি কিছু বেশি টাকা টাইগার জাম্পের উপর ধরে—টাইগার জাম্প আজ নিশ্চয় জিতিবে, ঘোড়াটা ফেবারিট হইলেও তিনগুণ নিশ্চয় পাওয়া যাইবে! সুরেশকে দিয়া দেওয়ার আগে টাকাটা খাটাইয়া কিছু লাভ করিয়া নিলে দোষ কি আছে? সব টাকা নয়—অর্ধেক। হারুক বা জিতুক অর্ধেক টাকা সে স্পর্শ করিবে না, ঋণ পরিশোধের জন্য থাকিবে।
সন্ধ্যার আগে শেষ ঘোড়দৌড়ের শেষে খালি পকেটে মাখন এনক্লোজারের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।
পরদিন অনেক বেলায় সে ম্লানমুখে সুরেশদের বাড়ি গেল। দরজা খুলিয়া দিল নলিনী। আগে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিত, আজ কিন্তু মুখখানা তার বড়ই গম্ভীর দেখাইতে লাগিল।
‘ছাতে চুল শুকোচ্ছিলাম, আপনাকে আসতে দেখে নেমে এলাম।’
নলিনীর হাসির অভাবটা পূরণ করার জন্য মাখন নিজেই একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ‘বেশ করেছ। সুরেশ কই?’
‘দাদা আসছে। টাকা এনেছেন দাদার?’
মাখন থতমত খাইয়া বলিল, ‘টাকা? ও, টাকা। তুমি জানলে কী করে টাকার কথা?’
‘আমি কেন, সবাই জানে। বাবা রেগে আগুন হয়ে আছে। আনেন নি তো? তা আনবেন কেন!’—গম্ভীর মুখ অন্ধকার করিয়া নলিনী ভিতরে চলিয়া গেল।
সুরেশ আসিলে টাকার কথাটা উঠিল বড়ই খাপছাড়া ভাবে। মাখন বলিল, ‘তোর টাকাটা দিতে পারব না সুরেশ। এক কাজ কর, ওই টাকাটা আমায় পণ দে, আমি নলিনীকে বিয়ে করব।’
.
কথা ছিল কথাটা গোপন থাকিবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা থাকিল না। বিনা পণে বন্ধুর বোনকে বিবাহ করার জন্য মনে মনে বাড়ির সকলেই একটু চটিয়াছিল— নলিনী তেমন রূপসীও নয়। কথাটার সমালোচনা হইত নানাভাবে—একটু কটুভাবেই। নলিনী যে কী করিয়া মাখনকে ভুলাইল ভাবিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইত। আজকালকার মেয়ে, ফন্দিবাজ বাপের মেয়ে, ওদের পক্ষে সবই হয়তো সম্ভব। আচ্ছা, পয়সাকড়ি যখন দিল না, গয়না কিছু বেশি দেওয়া কি উচিত ছিল না নলিনীর বাপের?
শুনিতে শুনিতে একদিন রাগে নলিনী দিশেহারা হইয়া গেল। বড় গুরুজন কেউ মন্তব্য করিলে রাগে দিশেহারা হইয়াও হয়তো সে চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু সেদিন মন্তব্যটা করিয়াছিল ননদ বিধু। তার সঙ্গে ইতোমধ্যে কতকটা ভাব হইয়া যাওয়ায় সে বলিয়া ফেলিল, ‘পণ দেওয়া হয় নি মানে? পণ তো ওঁকে আগেই দেওয়া হয়েছে।’
তারপর সব জানাজানি হইয়া গেল। প্রথমটা কেউ বিশ্বাস করিতেই চায় না, কিন্তু সত্য কথায় বিশ্বাস না করিয়া উপায় কী! মাখনকে জিজ্ঞাসা করায় সেও স্বীকার করিয়া ফেলিল।
রাত্রে মাখন বলিল, ‘টাকার ব্যাপারটা বলতে না তোমায় বারণ করেছিলাম? বললে কেন?’
নলিনী বলিল, ‘ব্যবসার নাম করে দাদাকে দেবার জন্য টাকা নিয়ে গিয়েছিলে আমায় বল নি কেন? আমার রাগ হয় না বুঝি?’
‘হুঁ, রাগ হলে তুমি বুঝি দশজনের কাছে আমার বদনাম করে শোধ তুলবে? তুমি তো কম শয়তান নও!’
বিশ্রী একটা কলহ হইয়া গেল, কথা বন্ধ রহিল তিন দিন। আবার কথা আরম্ভ হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, ‘আচ্ছা অতগুলো টাকা কী করলে? দাদার কাছ থেকে নিয়েছ, বাবার কাছ থেকে নিয়েছ, টাকা তো কম নয়!’
প্রথমে কৈফিয়তটা ভালো করিয়া নলিনীর মাথায় ঢুকিল না। চুপি চুপি কার সঙ্গে মাখন ব্যবসা করিতেছিল, সব টাকা লোকসান গিয়াছে। তারপর সে টের পাইল মাখন মিথ্যা বলিতেছে। মনটা তার খারাপ হইয়া গেল। স্বামীর মন তো তার ছোট নয়, টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে বরং অতিমাত্রায় উদার। টাকা- পয়সার ব্যাপারেই তার কেন মিথ্যা বলার প্রয়োজন হইল?
বাপ আর শ্বশুরের চেষ্টায় মাখনের একটা চাকরি জুটিয়া গেল ভালোই। বছর পাঁচেকের মধ্যে বেতন বাড়িয়া দাঁড়াইয়া গেল প্রায় তিন শ টাকায়। এতদিনে নলিনীর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইয়াছে এবং কতকটা স্বামীর চাকরির জন্যই অতি দ্রুত প্রমোশন পাইয়া পাইয়া স্বামীর সংসারে প্রায় গিন্নির পদ পাইয়াছে। সংসারে বিশেষ অশান্তি নাই, রোগশোক নাই, অনটন নাই— নলিনীর মনেও জোরালো দুঃখ কিছু নাই। কেবল সেই যে তিন দিন কথা বন্ধ থাকার পর মাখনের মিথ্যা বলার জন্য মনটা তার খারাপ হইয়া গিয়াছিল, মৃদু আশঙ্কার মতো একটা স্থায়ী অস্বস্তির মধ্যে সেই মন খারাপ হওয়ারই কেমন যেন একটা অদ্ভুত খাপছাড়া জের চলিতেছে। কোনো পাপ করে নাই নলিনী তবু ভয়ে রূপান্তরিত পুরোনো পাপের মতোই কী যেন একটা দুর্বোধ্য ভার সব সময়েই তার মনকে বহন করিতে হইতেছে।
মাখনের জুয়ার নেশা কাটিয়া যায় নাই, ভালবাসার নেশার মতোই প্রথম বয়সের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আর অসহ্য অধীরতার যুগটা পার হইয়া ধীরস্থির হিসাব করা নেশায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পাকা প্রেমিকের অভ্যস্ত প্রেম করার মতো তার জুয়া খেলাটাও দাঁড়াইয়া গিয়াছে অনেকটা নিয়মিত। টাকা অবশ্য জমে না, অনেক সাধ অবশ্য মেটে না, মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনের সময় টাকার জন্য সাময়িকভাবে রীতিমতো বিপদে পড়িতে হয়, তবু মোটামুটি সংসার চলিয়া যায়। মাখনের শ-খানেক টাকা বেতন হইলে যেমন চলিত তেমনিভাবে চলিয়া যায়। মাখনের বেতন শ-খানেক টাকা ধরিয়া নিলে অবশ্য অনেক হাঙ্গামাই মিটিয়া যাইত, এর চেয়ে অনেক কম বেতনেও জগতে অনেক লোক চাকরি করে, কিন্তু মুশকিল এই যে তিন শ টাকা যে বেতন পায় তার বেতনের দু শ টাকা কোনো কাজে না আসিলেও বেতন তার শ-খানেক টাকার বেশি নয় এটা ধরিয়া নেওয়া তার নিজের পক্ষেও অসম্ভব, আত্মীয় বন্ধুর পক্ষেও অসম্ভব।
আত্মীয় বন্ধুর রাগ অভিমান বিরক্তি আর উপদেশ উপরোধ সমালোচনা এখনো চলিতে থাকিলেও নলিনী একরকম আর কিছুই বলে না। সে জানে এ রোগের ওষুধ নাই। এ কথাটাও সে জানে যে প্রয়োজন হইলে জুয়ার খরচটা মাখন কমাইয়া দিবে, কিন্তু সত্য সত্যই প্রয়োজন হওয়া চাই। পেট ভরানোর মতো, গা ঢাকা দেওয়ার মতো, রোগের সময় ডাক্তার টাকা ওষুধ কেনার মতো খাঁটি প্রয়োজন। এ রকম আসল প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ববোধের কাছেই কেবল তার জুয়ার নেশা হার মানে।
কত কৃত্রিম প্রয়োজনই নলিনী দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছে! কতবার কতভাবে স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সংসারে এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই। মাখন শুধু বলিয়াছে, আচ্ছা আচ্ছা, হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় কিছুই হয় নাই।
বাড়ি বদলানোর জন্য নলিনী অনেকবার ঝগড়া করিয়াছে। বলিয়াছে, ‘এ বাড়িতে আমি থাকব না, একটা ভালো বাড়িতে চল।’ বলিয়া রাগ করিয়া বাপের বাড়িতে চলিয়াছে। তখন অবশ্য মাখন বেশি ভাড়ার একটা ভালো বাড়িতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তার ফলটা নলিনীর পক্ষেই হইয়াছে মারাত্মক। কারণ, জুয়ার খরচ মাখন এক পয়সা কমায় নাই, টান পড়িয়াছে সংসারের খরচেই। আবার উঠিয়া যাইতে হইয়াছে কম ভাড়ার বাড়িতে।
নলিনী বলিয়াছে, ‘আমি দুগাছা করে নতুন চুড়ি গড়াব।’
মাখন বলিয়াছে, ‘আচ্ছা।’
কিন্তু তারপর দুবছরের মধ্যে সস্তা একজোড়া দুলও নলিনীর গড়ানো হয় নাই। কারণ, চুড়িও নলিনীর আছে, দুলও আছে।
.
কিন্তু নলিনী যেদিন বলিয়াছে, ‘একটা লাইফ ইনসিওর পর্যন্ত করবে না তুমি?’ তার এক মাসের মধ্যে মাখন দশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স করিয়াছে এবং এখন পর্যন্ত নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়া আসিলেও বেশি ভাড়ার বাড়িতে উঠিয়া যাওয়ার ফলটা নলিনীকে ভোগ করিতে হয় নাই।
ধরিতে গেলে টাকা-পয়সার ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়াই হইয়া গিয়াছে। তবু সেই রহস্যময় মৃদু আতঙ্কের পীড়ন একটু শিথিল হয় নাই। কী যেন একটা বিপদ ঘটিবে—অল্পদিনের মধ্যেই ঘটিবে। কিন্তু কী ঘটিবে? মাখন একদিন জুয়ায় সর্বস্ব হারিয়া সর্বনাশ করিবে? কিন্তু মাখনের সর্বস্ব তো তার তিন শ টাকার চাকরি, উপার্জনের টাকা জুয়ার নেশায় নষ্ট করা সম্বন্ধে সে যতই অবিবেচক হোক, চাকরি নষ্ট করার মানুষ সে নয়। সে বিশ্বাস নলিনীর আছে। তবে? আরো অনেক বেশি আরামে ও সুখে বাঁচিয়া থাকার সুযোগ পাইয়াও স্বামীর দোষে কোনোরকমে খাইয়া পরিয়া অতি গরিবের মতো বাঁচিয়া থাকিতে হওয়ার যে জ্বালাভরা অভিযোগ, এটা কি তারই প্রতিক্রিয়া?
কিন্তু কোথায় জ্বালাভরা অভিযোগ? রাজপ্রাসাদে রাজরানীর মতো সুখে ও আরামে থাকিবার ব্যবস্থা মাখন করিয়া দিক এটা সে চায়, মাখনের ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে চায়, কিন্তু না-পাওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষোভ তো তার নাই।
নলিনী তাই কিছু বলে না। সব বিষয়েই সে একরকম হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, মাখনের সহজ সাধারণ ভালবাসার মধ্যে একটু রোমাঞ্চ আনিবার চেষ্টায় পর্যন্ত। চেনা মানুষ স্বামী হইয়াছে, তার কাছে কি অচেনা মানুষের নাটকীয় ভালবাসা আশা করা যায়? এতদিন ছেলেমানুষ ছিল তাই চেষ্টা করিয়াছে, বিবাহের আগে বুদ্ধি কম ছিল তাই তখন ভাবিয়াছে, বিবাহ হইলে হয়তো মাখন বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু জুয়ার নেশায় উত্তেজনা আর অবসাদের মধ্যে যার মনের জোয়ার ভাঁটা, বউয়ের কথা কি তার মনে পড়ে, বউয়ের জন্য একবার একটু পাগল হওয়ার সময় কি তার থাকে!
ভাবিতে ভাবিতে নলিনীর সাধারণ ছোট ছোট চোখ দুটিতে অস্পষ্ট স্বপ্নের স্পষ্ট ছায়া এমন অদ্ভুত ভাবালুতার আবরণে ঘনাইয়া আসে যে জগতের সব ডাগর ডাগর চোখগুলিতেও তা সম্ভব মনে হয় না। হয়তো তখন দুপুরবেলায় আঁচল পাতিয়া মেঝেতে গড়ানোর অবসরটা পাওয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়ের একজন খেলায় মত্ত, একজন ঘুমে অচেতন। চোখ বুজিলে কষ্ট বাড়িয়া যায়, নলিনী তাই চোখ মেলিয়া স্বপ্ন দেখে—তার কুমারী জীবনের স্বপ্ন : আত্মহারা আবেগের সঙ্গে তাকে ভালবাসিলে মাখন কী করিত। সম্ভব অসম্ভব কত কথাই নলিনী ভাবে।
তারপর অল্প অল্প অস্বস্তির মধ্যে মৃদু ভয়ের পীড়নে স্বপ্ন শেষ হইয়া চোখ দুটি তার বড় সাধারণ দেখাইতে থাকে। দুটি সন্তান যার তার কেন আর এসব স্বপ্ন দেখা, আর কি এ স্বপ্ন সফল হয়! যদি-বা হয়, কোনো এক আশ্চর্য উপায়ে আংশিকভাবে সফল হয়, দুদিন পরে সেটুকু সম্ভাবনাও আর থাকিবে না। আবার ছেলে বা মেয়ে কোলে আসিবে নলিনীর, তারপর সব শেষ। উদাসীন মাখনের মধ্যে প্রেমের উদ্দীপনা জাগানোর কথা ভাবিতে তার নিজেরই কি লজ্জা করিবে না? কী দিয়াই বা সে উদ্দীপনা জাগাইবে?
এখনো কেউ জানে না! দুদিন পরেই জানিবে। মাখন হয়তো খুশি হইয়া আদর-যত্ন বাড়াইয়া দিবে, বলিবে : ‘একটু দুধ খেয়ো। এ সময় দুধটুধ খেতে হয়।’ কিন্তু তারপর? আরো শান্ত হইয়া পড়িবে মাখন, আরো ঝিমাইয়া পড়িবে। মাথা কপাল খুঁড়িয়া মরিয়া গেলেও আর নলিনী তাকে জাগাইয়া তুলিতে পারিবে না। নলিনীর ভ্রূ কুঁচকাইয়া যায়, সঙ্কুচিত চোখ দুটিতে মরণের চেয়ে গভীর আতঙ্কের ছাপ পড়ে, শীতের দুপুরে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়।
কোনো উপায় কি নাই? যে-কোনো একটা উপায়? ব্যর্থ হইলে যদি সৰ্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, তবু সার্থকতার যেটুকু সম্ভাবনা থাকিবে তারই লোভে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত। কিন্তু সেরকম উপায়ই বা কোথায় যাতে সমস্ত শেষ হইয়া যায়, নয় মাখনের ভালবাসা মেলে?
ঠিক সেই সময় দুরুদুরু বুকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে মাঠে রেলিং ঘেঁষিয়া এগারটি ঘোড়ার মধ্যে একটির অগ্রগতি লক্ষ করিতে করিতে ভাবিতেছিল, এবারো না জিতলে বিপদে পড়িবে বটে, কিন্তু যদি জেতে—
সন্ধ্যার পর ঘোড়দৌড়ের মাঠ হইতে বন্ধু অবনীর সঙ্গে শ্রান্ত ক্লান্ত মাখন ফিরিয়া আসে। সুরেশের মতো অবনী এখন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মানুষটা সে একটু বেঁটে, রোগা, লাজুক আর ভীরু। কথার জবাবে পারিলে কথা বলার বদলে মৃদু একটু হাসিয়াই কাজ সারে। কখনো কেউ তাকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। ঘোড়া ছুটিবার সময় মাখন যখন আগ্রহ উত্তেজনায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কামড়াইতে থাকে, অবনী নির্বিকারভাবে বিড়ি টানিয়া যায়। জিতিলে মাখন ‘হুররে’ বলিয়া প্রচণ্ড একটা চিৎকার করিয়া লাফাইয়া ওঠে, হারিলে ঝিমাইয়া পড়ে। অবনী জিতিলেও মৃদু একটু হাসে, হারিলেও হাসে।
.
নলিনীর সাজপোশাক দেখিয়া দুজনেই একটু অবাক হইয়া যায়। ফ্যাশন করিয়া শাড়ি পরিয়াছে, রঙিন ব্লাউজ গায়ে দিয়াছে, শুধু ঘষামাজায় খুশি না হইয়া গালে বোধ হয় একটু রঙের আর চোখে একটু কাজলের ছোঁয়াচ দিয়াছে।
মাখন বলে, ‘কোথায় যাবে?’
নলিনী একগাল হাসিয়া বলে, ‘কোথায় আবার যাব?’
‘সেজেছ যে?’
সেজেছি? কী জ্বালা, কোথাও না গেলে বাড়িতে বুঝি ভূত সেজে থাকতে হবে?’ তারপর অবনীর কাছে গিয়া বলে, ‘সইকে বুঝি তালা বন্ধ করে রাখেন, আসে না কেন?’
অবনী নীরবে মৃদু একটু হাসে।
‘চলুন সইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।’
বলিয়া স্বামীর যে-বন্ধুর সঙ্গে তিন হাত তফাতে দাঁড়াইয়া নলিনী সংক্ষেপে কথা বলিত, রীতিমতো তার হাত ধরিয়া তাকে টানিয়া তোলে এবং মাখনের দিকে একনজর না চাহিয়াই বাহির হইয়া যায়।
প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও নলিনী ভিতরের উত্তেজনা গোপন করিতে পারে না। অবনীর বউ বলে, ‘কী হয়েছে সই?’
‘কিছু না।’
কোমরে আঁচল জড়াইয়া অবনীর বউ রান্না করিতেছিল। নলিনীর চেয়ে সে বয়সে বড়, কিন্তু বড়ই তাকে ছেলেমানুষ দেখায়। মানুষটা সে সব সময়েই হাসিখুশি, কাজ করিতে করিতে গুনগুন করিয়া এখনো গান করে। তাকে দেখিলেই নলিনীর বড় হিংসা হয়, মনটা কেমন করিতে থাকে। ওর স্বামীও তো জুয়া খেলে, তার চেয়ে অনেক কষ্টেই ওকে সংসার চালাইতে হয়, দুটি ছেলের মধ্যে একটি ওর মরিয়া গিয়াছে, তবু সব সময় এমন ভাব দেখায় কেন, দুদিন আগে বিবাহ হইয়া আসিয়া স্বামীর আদরে মাটিতে যেন পা পড়িতেছে না!
অবনীর বউ বলে, ‘এমন সেজেগুজে হঠাৎ? ‘
নলিনী বলে, ‘এমনি এলাম তোমায় দেখতে।’
‘কী ভাগ্যি আমার!’ ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপাইয়া হাসিতে হাসিতে অবনীর বউ কাছে আসিয়া বসে।
কথা আজ জমে না। রাত্রির সঙ্গে নলিনীর ভয় বাড়ে, ক্রমেই বেশি অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তবু উঠিবার নাম করে না। যত রাত হইবে মাখন তত বেশি রাগ করিবে—তত বেশি নাড়া খাইবে মাখনের মন। একটুও কি পরিবর্তন আসিবে না? রাগটা যখন পড়িয়া যাইবে তখন?
রান্না শেষ হয়, অবনীর খাওয়া হইয়া যায়, তখনো নলিনীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অবনীর বউ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। হাসিখুশি ভাব মিলাইয়া গিয়া তারও মুখে যেন ভয়ের ছাপ পড়ে।
‘আমায় কিছু বলবে সই?’
নলিনী মাথা নাড়িয়া বলে, ‘কী বলব? না, না, কিছু বলব না।’
‘তোমায় নিতে আসছে না যে।’
‘কে জানে। ওর কথা বাদ দাও।’
খানিক পরে অবনীর বউ বলে, ‘ওই তবে তোমায় দিয়ে আসুক আর রাত করে কাজ নেই। পুঁইচচ্চড়ি রেঁধেছি, মুখে দিয়ে যাবে সই?’
হোক আরেকটু রাত, মাখনের রাগ আরেকটু বাড়িবে। আরম্ভ যখন করিয়াছে, শেষ না দেখিয়া ছাড়িবে না। মরিয়া হইয়া নলিনী সখীর রান্না পুঁইচচ্চড়ি মুখে দিবার জন্য সখীর সঙ্গে একথালায় খাইতে বসে। দুজনে বেশ পেট ভরিয়া খায়, সকালের জন্য পান্তা না রাখাতেই ভাতে কম পড়ে না, আর ডাল ভাজা মাছ তরকারি যতটুকুই থাক, ভাগাভাগি করিয়া খাওয়ার সময় তো মেয়েদের কখনো কম পড়েই না।
খাওয়ার পরে পান মুখে দিয়া অবনীর বউ স্বামীকে ডাকিয়া বলে, ‘ওগো শুনছ, একটু বেরিয়ে এসো ঘর থেকে। সইকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। বাবা, এগারটা বাজে!’
নলিনীর বুক কাঁপিয়া ওঠে। যেভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এতরাত্রে আবার অবনীর সঙ্গে একা ফিরিতে দেখিলে কী রাগটাই না জানি মাখন করিবে! করুক রাগ, রাগাইবার জন্যই তো সাজিয়া গুজিয়া এভাবে সে বাহির হইয়াছে, এখন সেজন্য ভয় পাইলে চলিবে কেন? নিজেকে নলিনী অনেক বুঝায় কিন্তু বুকের টিপ্ঢিপানি কিছুতেই কমে না।
দু-বন্ধুর বাড়ি বেশি দূরে নয়। রিকশায় মিনিট দশেক লাগে। অবনীর বাড়ির কাছেই গলির মোড়ে রিকশা পাওয়া যায়। অবনী দুটি রিকশা ভাড়া করিতেছিল, নলিনী বারণ করিল, ‘মিছিমিছি কেন বেশি পয়সা দেবেন? একটাতেই হবে।’
‘না না, দুটোই নিই-’
নলিনীর গলার আওয়াজ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, এসব খাপছাড়া উত্তেজনা কী তার সহ্য হয়! তবু মরিয়া হইয়া সে বলিল, ‘আসুন না, একটাতে বসে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।’
গল্প কিছুই হয় না, সমস্ত পথ দুজনেই যতটা সম্ভব পাশের দিকে হেলিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। বাড়ির দরজার সামনে রিকশা থামামাত্র নলিনী তড়াক করিয়া নামিয়া যায়। অবনীকে বলে, ‘ওঁকে ডেকে দিয়ে আপনি এই রিকশাটা নিয়ে ফিরে যান।’
দরজা খুলিয়া দিতে আসিয়া মাখন দেখিতে পাইবে এতরাত্রে বউ তার এক রিকশায় অবনীর সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে, নলিনীর এই আশা বা আশঙ্কা পূর্ণ হইল না। দরজা খুলিয়া দিল চাকর।
ঘরে গিয়া নলিনী দেখে কী, মেয়েটাকে কোলে নিয়া আনাড়ির মতো থাপড়াইয়া থাপড়াইয়া মাখন তাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করিতেছে। বউয়ের সাড়া পাইয়া মাখন ক্ষুণ্নকণ্ঠে বলিল, ‘কী আশ্চর্য বিবেচনা তোমার! দুজনকে ফেলে রেখে এত রাত পর্যন্ত বাইরে কাটিয়ে এলে? খুকিকে তো অন্তত নিয়ে যেতে পারতে সঙ্গে।’
মেয়েকে নামাইয়া দিয়া মাখন নিজের বিছানায় উঠিয়া শান্তভাবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। খুব যে রাগ করিয়াছে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।
‘তুমি কাউকে পাঠালে না কেন? অবনীবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে—’
‘কাকে পাঠাব? শম্ভু এতক্ষণ খুকিকে রাখছিল।’
দুমিনিট আগে দরজা খুলতে যাওয়ার সময় শম্ভু তবে মেয়েকে মাখনের কোলে দিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে মাখনকে মেয়ে রাখিতে হয় নাই! নলিনী জিজ্ঞাসা করিল না, মাখন নিজে কেন তাকে আনিতে যায় নাই। আর জিজ্ঞাসা করিয়া কী হইবে? নিজের চোখে বউ আর বন্ধুকে জড়াজড়ি করিতে দেখিলেও বোধ হয় তার রাগ হইবে না। এমন বদমেজাজি মানুষ, এক গ্লাস জল দিতে দেরি হওয়ায় আজ সকালেই শম্ভুকে মারিতে উঠিয়াছিল, শুধু বউকে তার এত অনুগ্রহ কেন? একদিন কি সে রাগের মাথায় বউয়ের গালে একটা চড় বসাইয়া দিতে পারে না, যাতে খানিক পরে ভালবাসার জন্য না হোক অন্তত অনুতাপের জন্যও অনেকগুলি চুমু দিয়া চড়ের দাগটা মুছিবার চেষ্টা করা চলে?
বাহিরটা একবার তদারক করিয়া আসিয়া নলিনী ঘুমন্ত মেয়ের পাশে শুইয়া পড়ে। মাখন বলে, ‘খেলে না?’
নলিনী বলে, ‘ওদের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।’
খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া যায়, তারপর মাখন যেন ভয়ে ভয়েই আস্তে আস্তে বলে, ‘আজ অনেকগুলি টাকা জিতেছি।’
নলিনী সাড়া দেয় না।
‘প্রায় সাতশ।’
নলিনী তবু সাড়া দেয় না।
‘তোমায় একটা গয়না গড়িয়ে দেব—যা চাও।’
নলিনী চুপ করিয়া থাকে। নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবে ‘কে শুনতে চায় তুমি হেরেছ কি জিতেছ, কে চায় তোমার গয়না, একবার কাছে ডাকতে পার না আমায়?’
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মাখন বলে, ‘রাগ করেছ? না না, ঘুমোও আর জ্বালাতন করব না।’
(সমাপ্ত)