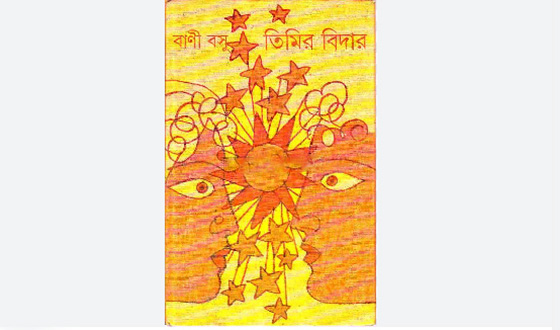রসিক ঘোষের লেনের মুখে দেখি ঝামেলা হচ্ছে। ধুস! সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছি। মেলা কাজ। সাইক্লোনের হাওয়া যেমন উল্টোপাল্টা এলোপাথাড়ি বয় আমাকেও তেমন বাইতে হবে এখন। হোমিওপ্যাথ এস ভটচায্যির ওখানে মায়ের নামে স্লিপ লেখানো, গণাদার দোকানে ওষুধের লিস্টি ফেলা, তারপর বিশুদার ঠেকে একবার, নিতাইকাকার ঠেকে একবার খেপ মারা। এস ভটচায্যি যদি নর্থ পোল তো গণা অধিকারীর দোকান সাউথ পোল। বিশুদা আমাদের এমেলে না এলেবেলে জানি না বাবা, বিরাজ করছেন পুব দিকে আর নিতাইকাকা? সে-ও আবার মধ্যপ্রদেশ মানে এম পি। তিনি যাকে বলে ফার্দার ইস্ট। কত টাইম লাগবে বলতে হলে গণকঠাকুর ডাকতে হবে। ক্যারিয়ারে ভাইপো বসেছিল, নামিয়ে দিই, বলি—যাঃ ভাগ্!
—খ্যানো? —বাজে আবদারের কাঁদুনি ওর গলায়।
—দেখছিস না ঝামেলা হচ্ছে? ওই দ্যাখ—চিৎকারটা শুনতে পাচ্ছিস?
—তুঁমি তো যাঁচ্ছ!
—তোর রিস্ক নিতে আমি পারব না। আমি একলা ঠিক কেটে বেরিয়ে যাব। যা।
তখনও ক্যানক্যান করতে থাকে ছেলেটা। বোঝে না এই সব ঝামেলায় লোকে যখন তখন একটা পটকা টপকে দিতে পারে। তখন?
—আরে বাবা তোর সচিনের পোস্টার তো? ও আমি ঠিক এনে দেব।
—ন্ না, তুমি আনবে না।
অনেক দিন থেকেই সচিনের পোস্টারের আবদার ধরেছে রিন্টিটা। বলছি পাচ্ছি না, রাহুল দ্রাবিড় নে, বাঙালির ছেলে সৌরভের নে, রয়েছে স্টকে—ন্ না, সেই এক জেদ, ও সচিনের পোস্টারই নেবে। আজ কে জানে কী উটকো কারণে আবার স্কুল ছুটি। সক্কাল থেকে বসে আছে আমার সাইকেলের ন্যাজে।
ইচ্ছে হয় কানে কষে একটা প্যাঁচ দিই। অনেক কষ্টে লোভ সামলাই। যতই যাই হোক রিন্টিটা আমাদের জেনারেশনেকসট-এর একমাত্তর। আমার খুব ন্যাওটাও। তা ছাড়া ওর মা? চাকুরে দাদার চাকুরে বউ! বাপ রে! তাকে ভয় পায় না, এমন বেকার পৃথিবীতে আছে? অবশ্য পৃথিবী মানে ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া ছাড়া আর কোথাও আমার মতো এমন আকাট রেকারই কি আছে? থাকলেও তাদের অন্ন-বস্তর ওষুধ-পথ্যের জন্যে দাদা-বউদি! এই কম্বিনেশন বোধহয় আর কোথাও নেই।
আমাদের এ পাড়াটা ওপর-ওপর বেশ। আসলে একটা নুইসান্স। বারো মাস ঝামেলা, বারো মাস বোমবাজি। পুরো চত্বরটাই। আছে আছে বেশ আছে, হঠাৎ একদিন যেন ডাকাত পড়ে। হল্লা, গালাগাল, বোম ছোড়াছুড়ি। রেললাইনের এ দিকটা পুরো কানা গদাইয়ের। আর ও দিকটা সমশের বা শামুর। স্রেফ নামটা বললে অবশ্য কিছুই বলা হয় না। কানা গদাই বললে কেউ যদি ভাবে একটা নোংরা, মোটা, খোঁচা দাড়ির একচোখো লোক, তা হলে তার কপালে কিছু সারপ্রাইজ আছে। গদাই একটা সাড়ে পাঁচ ফুটি তিলে খচ্চর, যার ফর্সা মাকুন্দ মুখ, পাথরের চোখ আর গেরেম্ভারি চাল দেখলে আপনার মনে হতেই পারে এ নির্ঘাত বিড়লা-আম্বানিদের ঘরের ছোট বাদশাজাদা। তিন হাজার টাকার জুতো, দশ হাজার টাকার রিস্টওয়াচ, গলার সোনার চেনটা কোন না ছ’ ভরির হবে! মাখনের মতো কাপড়ের ডোরা কাটা শার্ট আর ছুরির ধার পাতলুন পরে যখন ঘোরাফেরা করে তখন টপ এগজিকিউটিভ ভেবে আমার মতো চাকরিপ্রার্থীরা কুর্নিশ করতেই পারে। কার্ডবোর্ডের ব্যবসা করে যে গদাই কী করে অমন একটা কেতার বাড়ি বানাল এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই গদাই বলবে—ছিল।
কথাটা বুঝতেই পারছেন—সত্যি না। তা ছাড়া কী ছিল আর কতটা ছিল, এর থেকে মোটেই পরিষ্কার হয় না। জমিটা গদাইয়ের বাবা করুণাসিন্ধু যে কার থেকে ঝেঁপেছিল তা কেউই জানে না। আমার বাবা যে-সময়ে এখানে অনেক কষ্টে দেড়কাঠার কাঁচা একতলাটা পাকা করল তখনও ও জমি নাকি ভীষ্মের শরশয্যা ছিল। যে দিকে চাও শর আর শর। করুণাসিন্ধু স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে বস্তির মুখে থাকতেন, আর এই জমিটা সাফ করে করে ইট নামিয়ে রাখতেন। ব্যাপারটা কেউ সেভাবে লক্ষ করবার আগেই ওখানে ওদের চালা উঠে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলে করুণাসিন্ধু সংক্ষেপে বলতেন—কিনসি। আর কোনও ডিটেলের মধ্যে যাবার চেষ্টা করলেই বলতেন—ক্যান? কিনবা?—চালাঘরটা পাকাও হয়েছিল করুণাসিন্ধুরই আমলে। কিন্তু তার এই ফিলমি-কেতার প্রাসাদে পরিবর্তন তো আমরা চোখের সামনেই দেখেছি। বাকসো তৈরির কারখানাটা শুনেছি বজবজের দিকে। গদাই আমাদের স্কুলেই পড়ত। ক্লাস টেনের পর বছর দুই স্কুল ছেড়ে এই কারখানাটা নিয়ে পড়ে ছিল। সেই কারখানার এত আমদানি যে ওই প্রাসাদ, তার সামনে লন, গেটে বন্দুকধারী দারোয়ান, গারাজে অ্যামবাসাডর যেটা ইদানীং ফোর্ড আইকন-এ বদলে গেল? এ সব প্রশ্নের ভেতরে ঢুকতে পাড়া-বেপাড়ার কারওরই কোনও আগ্রহ হয়নি। সকলেই তো মোটমাট শান্তিতে-সোয়াস্তিতে বাস করতে চায়! যে যা প্রাণ চায় করুক, আমার ত্যানায় হাত না পড়লেই হল। আর হাঙর-কুমিরে কি আর পুঁটিমাছ ধরে?
আমার যেটুকু জ্ঞান-গম্যি তা শামু অর্থাৎ সমশেরের দৌলতে। সমশের পড়ত হাইমাদ্রাসায়। আমি ভবানীচরণ উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে। বছর তিন-চার ফেল করে শামু আমার ইয়ার হয়ে যায়, সে একরকম গদাইও। ও যখন স্কুল ছাড়ল তখন আমার দু’ বছরের সিনিয়র। বলে পরে নাকি এক্সটারন্যাল হয়ে পাশ করেছে, বি কম ক্লাসে ওকে কয়েকদিন দেখেওছিলাম। ওদের সঙ্গে আমার আসল দোস্তি খেলার সূত্রে। তখন একই মাঠে একই ক্লাবে বল পিটতাম। দৌড় আগে শুরু করে শামু, তারপর গদাই, তারপর আমি। শামু ক’বছর ফেল করে আমার সমান হয়ে যায়। গদাই বি কম ড্রপ করে। আর আমি বি কম পাশ করে ওদের সমান হয়ে গেলাম। সমানও কি? জীবনের পাশ-ফেলের হিসেব নিলে গদা ফার্স্ট ডিভিশন, শামু সেকেন্ড ডিভিশন, আর আমি পি-ডিভিশন। গোড়ায় গোড়ায়, যখন এই ভেদাভেদটা এমন প্রকট হয়নি তখন আমরা মাঠের ওধারে কালভার্টটার ওপর বসতাম। গদা কাগজ পাকিয়ে সরু সরু সিগ্রেট বানাত। কতদিন গদাইয়ের পাকানো তামাক খেয়েছি তিনজনে। আমি বলতাম—কী রে! তামুকে ড্রাগ-ফাগ দিচ্ছিস না তো? গদা ভারিক্কি চালে বলত—নে, নে, দিচ্ছি এই না কত! —ড্রাগকে আমার মহা ভয়! লেটুদাকে দেখেছি তো! আমাদের পাড়ার হিসেবে তো ব্রিলিয়ান্টই ছিল, এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাদবপুর পাওয়া চাট্টিখানি কথা না। ফিরে এল ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে। প্রথমে ফুঁকল বিধবা মায়ের গয়নাগাঁটি, তারপর ঘরের বাটি-ঘটি, তারপর যখন লোকের বাড়ি ঢুকে এটা ওটা সরাতে লাগল তখন লজ্জায় ঘেন্নায় রাধুপিসি, ওর মা গলায় দড়ি দিলেন। তখন ওর এক দূর সম্পর্কের কাকা এসে হাল ধরলেন, মানে লেটুদাকে ওর নিজেরই বাড়ি থেকে বার করে দিলেন।
শামুর ভয়-ডর ছিল না। একদিন বলল—ড্রাগ-ফাগ পেলে আমাকে একটু দিস তো গদা! বেহেস্তোটা কেমন একবার টেস্ট করে আসি।
শামুই আমাকে বলেছিল—গদার বাকসো-ফাকসো না কি সব শো। ওর ওয়ার্কাররা আসলে সমাজবিরোধী মানে অ্যান্টি-সোশ্যাল। তাদের কাজ নানারকমের তোলাবাজি, ব্ল্যাকমেল ইত্যাদি। শামু তখনও রেল-লাইনের ওপারের গুরু হয়নি। হয়ে গেল একদিন কনস্টেবল ঠেঙিয়ে। চায়ের দোকান দিয়েছিল। লোকটা রোজ-রোজ মিনি-মাগনা ওর কাছ থেকে চা খেত, চা আর ঝাল বিস্কুট। সারা দিনমানে তা অমন বারসাতেক তো হবেই। যে দিন অষ্টমবার চা আর তার সঙ্গে নানখাটাই চায়, সেদিন মেরেছিল এক থাবড়া। কনস্টেবলটাও মার ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু শেষমেশ শামুই ওর লাঠি কেড়ে নিয়ে ওকে বেধড়ক পেটে। শামু না হয় রাগ সামলাতে পারেনি, করে ফেলেছিল একটা গোলমেলে কাজ। জেল হল, সেখানে কী সব নিয়ম ভাঙল, মেয়াদ বাড়ল, তারপর দাগী ক্রিমিন্যাল হয়ে বেরোল। যা-ই হোক, একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝতে পারা যায়। কিন্তু গদাই কেন? যার একটা কার্ডবোর্ড বাকসোর কারখানা আছে তার তো কপাল খুলেই গেছে! গদাইয়ের ব্যাপারটা আমি সত্যিই বুঝি না। আমি তো একটা এস টি ডি ফোন বুথের ধান্দায় সাইকেলের টায়ার ক্ষইয়ে ফেললাম। এখনও লোন-টোন কিচ্ছু ল্যান্ড করতে পারিনি। বিশুদার কাছেই যাচ্ছি আজ তেরো মাস সাত দিন হয়ে গেল। নিতাইকাকার কাছে আরও আগে থেকে। কিচ্ছু গাঁথতে পারলাম না।
বিশুদার বাড়ি গিয়ে দেখি কেরোসিনের লাইন পড়ে গেছে। দীপু এসে আগে ঢুকছিল, আমরা অনেকেই প্রতিবাদ করতে বলল—এই দ্যাখ, জুতো রেখে গেছি, বড়-বাইরে পেয়ে গিয়েছিল তাই…। সত্যিই দেখি ওর খালি পা, লাইনে ওর জুতো মানে হাওয়াই-চটি, এত হাকুচ ময়লা যে ওটা যে দীপুর সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। দীপুর কেস খুব খারাপ। ওর বাবা ট্র্যাংগুলার পার্কের কাছে সায়া-শাড়ি-ব্লাউজ-ফল্স্ এ সবের স্টল দিয়েছিল। উচ্ছেদ হল। মাসতিনেক পর সংসার চালাতে না পেরে ছারপোকা মারার ওষুধ খায়। দীপুর ওপরে একটা দাদা, জমি-বাড়ির দালালি করত। দালালস্য দালাল। কেটেছে। নীচে একটা ভাই, দুটো বোন। দীপুর জন্যে বিশুদা আন্তরিকভাবে করছে। দীপুই বলে, আমরা আর কোত্থেকে জানব? কণ্ডিশন ওই, স্পেশ্যাল ট্রিটমেন্ট পাবে না, আমজনতার মতো কিউ মেরেই আসতে হবে। দীপুর মা ইদানীং গদাইদের বাড়ি রান্না করেন। ছোট ভাইটা গাড়ি ধোয়। দীপুর বড় বোন হরসুন্দরী ইস্কুলের থার্ড নয়, ফোর্থ নয়, একেবারে ফার্স্ট গার্ল। দিদিমণিরা না কি চাঁদা করে তার পড়ার খরচ জোগান। ছোটটা ‘লা-বেল’ বিউটি পার্লারে চুল-ফুল ঝাঁট দেয়। মুক্তাটার খুব আশা এই করতে করতেই ও পার্লারের আসল কাজগুলো শিখে যাবে, আস্তে আস্তে প্রোমোশন হতে হতে যাকে বলে স্কাই-ইজ-দা-লিমিট।
—কী রে মুক্তো, চুল ঝাঁটাতে চললি? —দেখা হলেই পেছনে লাগি।
—খবদ্দার মুক্তো-মুক্তো করবে না রুণুদা, আমার নাম মুক্তা, মুক্তামালা বুঝলে!
—দ্যাখ অন্যভাবে নিস না, একটু বিক্কৃতি সহ্য হবে না তো এইসব নাম রাখা কেন, বল? মুক্তা ডাকতে গিয়ে আপসে মুক্তো বেরিয়ে পড়ে।
—নামটা আমি রাখিনি, আমার বাবা রেখেছিল—মুক্তা মুখনাড়া দেয়, আর মুক্তাই রেখেছিল। এখন নিশ্চয় বাবাকে কৈফিয়ত দিতে ডাকবে না।
ঝটকা মেরে মুক্তা চলে যায়। মেয়েগুলোকে নিয়ে এই হল মুশকিল। ঠাট্টা-মশকরা বোঝে না। না হেসে কেমন করে বেঁচে থাকে, থাকতে পারে, সেটাই আশ্চর্য!
বিশুদার চেম্বার, মানে বৈঠকখানা ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে রোদ্দুর লম্বা হয়ে যায়। সানমাইকা-ঢাকা বেঞ্চির ওপরে নিশান, ফকির জ্যাঠা, রবি, অজয়, ভিকু, সঞ্জু, রতনাদের সঙ্গে বসে থাকি। কাগজগুলো ডাঁই করা থাকে টেবিলে। বাংলা কাগজ তো সব বটেই, ইংরেজিও এ দিকে যা-যা বেরোয় সব। বিশুদা নেয় না পায় জানি না। বেশিরভাগ দিনই টেবিলে একটাও পড়ে থাকে না। শরণার্থীরা যার যার মাপমতো তুলে নেয়। ঘর জুড়ে খালি খড়মড় আর খড়মড়। আজ একটা পাতা পেয়ে গেলাম।
‘বিরাটির কাছে গণ-পিটুনিতে দুই ডাকাতের মৃত্যু।’ দীপু বললে—ডাকাতগুলো কি পিটুনিতেই এমন রোগা হয়ে গেল? না, আগে থেকেই ছিল? এরা যদি ডাকাত হতে পারে তবে রুণু তুই আমি তো ডবল ডাকাত রে?
এইটা দীপুর বিশ্রী অভ্যেস। কোনও কাগজ নিজে পড়বে না। অন্য কেউ পড়লে আশপাশ থেকে ডিঙি মেরে মেরে পড়বে। কমেন্ট করবে।
‘মধ্য কলকাতার নামকরা স্কুলে টিচারের মারে ছাত্র হাসপাতালে। টিচার ফেরার। প্রিন্সিপালের সাফাই।’
দীপু বলল—মণিদের স্কুলেও একটা সিমিলার কেস হয়েছিল রে! খুব কমন হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা।
আমি একটু অবাক হই। —মেয়ে-ইস্কুলেও মারে?
—তবে? হাত-টান ছিল মেয়েটার। বন্ধুদের বাকসো থেকে পয়সাকড়ি, কলম-টলম দেদার হাতাত। ধরা পড়ে বেধড়ক মার খেল। কান কালা হয়ে গিছল।
—এরাই আসল শ্রেণী-শত্ৰু বুঝলি?
—কারা?
—কারা আবার? নবম থেকে দশম, দশম থেকে একাদশে যারা এগোতে দেয় না! আমি হেসে ফেলি।
—তুই হাসছিস?
হাসিটা আমি চট করে গিলে ফেলি। দীপুর কেস খুব খারাপ। ওর ভাইটা মাধ্যমিক পাশ করতে পারেনি। কখন মাথা গরম হয়ে যাবে, ছুরি-ছোরা ভুঁকিয়ে দেবে, কিংবা ছারপোকা মারার ওষুধ… নাঃ ওর মনটা অন্যদিকে নিয়ে যাবার জন্যে বলি—বিড়ি খাবি?
হাতটা অটোম্যাটিক বাড়ায় দীপু, বলে—শেষ পর্যন্ত যাকে মন্দ বলি সেই গদাই আমাদের ভগবান হয়ে দাঁড়াচ্ছে বুঝলি দীপু? এ সব এমেলে ফেমেলে কিস্যু না।
আমি বুঝে যাই দীপুর কাছাকাছি থাকাটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এইখানে বসে যদি ও এ-সব বলে! উশখুশ করতে থাকি। জায়গাটা একবার অকুপাই হয়ে গেলে হয়ে গেল। চারদিকটা একটু দেখছি, কাকে একটু ঠেসে বসতে বলা যায়। দীপু ধোঁয়া ছেড়ে বলল—মা তো আজকাল মহাজনদের বাড়ি কাজ পেয়েছে। গদাইরা তো ছেড়ে দিল। মাসের চোদ্দো তারিখ, মা ভাবেনি পুরো মাসের মাইনেটা দেবে। দিল তো!
শুনে একটু অবাক হই! মহাজন মানে এ এস মহাজন। এ তল্লাটের নামকরা বড়লোক। আমাদের পাড়া পাঁচমেশালি। দু’-চার জন পয়সা-অলা লোক যে থাকে না তা নয়, কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে যে প্রাসাদটা দেখা যায়, সেটা আদিত্য শংকর মহাজনদের।
শুনতে পাই বেসিক্যালি ওদের পয়সা কয়লার। এখন, এখন বলতে বহুদিনই সে-সব বেচে-বুচে দিয়ে ইলেকট্রনিক গুডস-এ টাকা লাগিয়েছে। ওদের টিভি, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজ এ সবের খুব নাম। শিগগিরই নাকি ডাবল ডোর ফ্রস্ট-ফ্রি, কুইক-কুল ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার এ সব বাজারে আনছে। অ্যাড দেখি। মহাজনরা আদতে কোন স্টেটের জানি না, এখানে কেন পড়ে আছে তা-ও না। বাঙালিদের মতোই তো থাকে। তবে ধনী লোকেরা যেমন হয়, একটু ট্যাঁশ-মার্কা। সেই বাড়িতে দীপুর মা এনট্রি পেল কী করে? গদাইয়ের কাজ ছাড়লই বা কেন?
দীপুরা অবশ্য ভাল চক্কোত্তি বামুন। ওর বাবা হকারি করুন, আর রাত্তিরে স্টলের ঘর লোচ্চাদের ভাড়াই দিন, বামনাই মেনটেন করে গেছেন বরাবর। এত কষ্টেও ওদের বাড়ির সবারই চাল-চলনের একটা সুনাম আছে। দীপুর মা যখন কাজে বেরোন, কেউ বলবে না রাঁধুনি যাচ্ছে। বড় জোর অফিসের চাকুরে। মণি মুক্তা দুই বোনই থাকে ফিটফাট। মেয়েদের এই ক্ষমতাটা আছে। দীপুটাই পারে না। একমুখ দাড়ি। গা দিয়ে খড়ি উঠছে, হাওয়াই চপ্পল থপাস থপাস করে ঘোরে, ওর ভাইটাও আজকাল কেমন রাফ মতো হয়ে উঠেছে।
আমাদের এই পাড়াটা, মানে শুধু রসিক ঘোষের লেন নয়, আশেপাশে যতগুলো অলিগলি রাস্তা আছে পুরো কয়েক কিলোমিটার এলাকাটা ভেতরে-ভেতরে কেমন অনিরাপদ হয়ে গেছে—চোরা ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছে টের পাই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বাঃ বেশ শান্তশিষ্ট তো! শান্তিপ্রিয় লোকেদের শান্তিপূর্ণ জায়গা। কিন্তু সেটা শুধু মেক-আপ। আসলে পুরো জায়গাটা শামু আর কানা গদাই ভাগাভাগি করে নিয়েছে বলেই এমনি দেখায়। ও দিকে রিজভি হোটেল, বসাকদের গয়নার দোকান, সাউ ফার্নিচার এ সব শামুর দখলে। এ দিকে ভগৎ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, কে এল ঘোষের ড্রাগিস্টস অ্যান্ড কেমিস্টস, ভজন সিং আর রফিকুলের ধাবা ইত্যাদি ইত্যাদি গদাইয়ের দখলে। শোনা কথা। কেউ জানে না। শামুরটা জানে। গদারটা ভেতরের খবর ছাড়া জানার উপায় নেই। সব মাস পয়লায় যে যার ভাগের টাকা দিয়ে দেয় তাই। শামুকে একদিন জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিলাম—হ্যাঁ রে, ফায়ার-আর্মস রেখে, দল মেনটেন করে তোদের পড়তা পোষায়? পুলিশের সঙ্গেও নিশ্চয়ই পার্সেন্টেজের ব্যবস্থা আছে। শামু চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়েছিল, হাতে খইনি ডলতে ডলতে বলেছিল—এবে ফোট।
জানতাম ডেবিট-ক্রেডিটের হিসেব শামু আমাকে দিতে চাইবে না। তবু একটা কৌতূহল আর কী! সবই তো ব্যবসা! ঠিক ব্যবসার নিয়ম মেনেই চলে। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। কড়ি আর তেলের মধ্যে যেটুকুন ফারাক সেইটুকুনই রোজগার। এই তো! সব রকম জীবিকা সম্পর্কেই আমার একটা কৌতূহল আছে। কীভাবে কী হয়! নিজের যেহেতু জীবিকা নেই, বিশেষ কোনও জীবিকার জন্যে তৈরি হওয়াও হয়ে ওঠেনি, তাই যা পাব আমাকে ধরতে হবে। আমি ক্রমাগত শূন্য হাতড়ে যাচ্ছি। ইন ফ্যাক্ট আমি রিকশঅলাদেরও জিজ্ঞেস করি—হ্যাঁ রে সিধু, মালিককে কত দিতে হয় রে?
—ওরে বাবা, রোজ তিরিশ টাকা।
—তোর কত থাকে?
অমনি সিধু ধানাই-পানাই শুরু করবে—এই রিকশা সারাই-ঝালাই লেগেই আছে, লাইনেও খুব পলিটিক্স দাদা, ওই কোনও রকমে চারটে পেট চলে যায়।
বিশুদার ওখানে আধঘণ্টাটাক থেকে কেটে পড়ি। যা লম্বা লাইন পড়েছে, আজকে কোনও চান্স নেই। এত লোকের এমেলের সঙ্গে কী কাজ থাকে এটাও আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। সবাই তো আমার মতো বেকার নয়। ধরুন ফকির জ্যাঠা, ইনি কেন আসেন? নিত্যদিন! গোড়ায় গোড়ায় ওঁর সামনে সিগ্রেট খেতাম না। তারপরে দেখলাম টূ মাচ হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ ওয়েটও করব, টেনশনে হাতে-পায়ে খিলও ধরবে, অথচ একটু ধোঁয়া ছাড়তে পারব না, ইঞ্জিন চলে? একদিন ধরিয়েই ফেললাম, ফকির জ্যাঠা কাগজটা আড়াল করে ধরলেন। আমার মনে হয় ফকির জ্যাঠা অবসরপ্রাপ্ত মানুষ, কাগজ পড়তেই এখানে আসেন। এসব লোকের অখণ্ড সময়। হাজারটা কাগজ পড়ে, মিলিয়ে মিলিয়ে পড়বে, অথচ এতগুলো ছেড়ে একটা কাগজ কেনারও হয় তো সামর্থ্য নেই। কত লোকের যে কত তুচ্ছ কারণে, কত জরুরি কারণে এমেলের সই লাগে, রেকমেন্ডেশন লাগে! ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই এমেলে লোকগুলো এতসব সামলায়ই বা কী করে! এ তো চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি! নাঃ এমেলে এম পি-দের মাইনেকড়ি সত্যিই বাড়িয়ে দেওয়া দরকার।
যাক গে, রসিক ঘোষ লেনের মোড়ে ঝামেলাটা কেন হচ্ছিল আমাদের শান্তিপূর্ণ এলাকায়—জানতে হচ্ছে। নেই কাজ তো খই ভাজ।
অতএব সাইকেল বাই। এর থেকেই বোধহয় বাইসাইকেল শব্দটা এসেছে। বাইসাইকেল তৈরির যুগেও তা হলে সাহেবরা মেঠো বাংলা জানত! টিকটিকি দেয়াল বাইছে, মানুষ গাছ বাইছে, মজুর বাঁশ বাইছে। আর বেকার সাইকেল বাইছে। তা ঝামেলা দেখি এখনও চলছে। জম্পেশ ভিড়। ডিঙি মারি।
আই ব্বাস! জগাদা আর অরবিন্দদায় লেগে গেছে। সামনে একটা কর্পোরেশনের বাই-ইলেকশন আছে বোধহয়। সেই জন্যেই কী! জগাদা হল গিয়ে লাল-পার্টির স্লিপার, মানে স্লিপিং পার্টনার। অর্থাৎ একটা সদস্যপদ আছে, তার জন্যেই পায়ও নিয্যস কিছু। পাড়ায় কোনও কাজিয়া হলেই লোকে জগাদার কাছে ছুটে থাকে, পরিষ্কার জেনে শুনে যে কিস্যুই হবে না। জগাদা এ এলাকার একটা জগদ্দল ভগ্নপ্রায় স্তূপের তেত্রিশ শরিকের একজন। ঠাকুর্দার আমলে যখন পয়সাকড়ি ছিল তখন জগাদারা বিশুদ্ধ কংগ্রেস ছিল, মনে-প্রাণে, নিবেদিত-প্রাণ একেবারে, অতুল্য ঘোষের চ্যালা ছিলেন জগাদার ঠাকুর্দা। তারপর তালপুকুরে ঘটি ডুবতে ডুবতে কাদায় একেবারে গিঁথে যেতে এবং বামফ্রন্ট চতুর্থবার ক্ষমতায় আসতে জগাদা-বলাদারা আপাদমস্তক লাল হয়ে গেল। একেবারে এনটায়ার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি। তারপর বছর দু’চার আগে এক কংগ্রেস ঠিকেদারকে পেঁদিয়ে রাতারাতি লাল সেলাম। অর্থাৎ কিনা পার্টির সক্রিয় কর্মী। এখন, সবাই জানে ঠিকেদারদের কোনও রাজনৈতিক চেতনা নেই, যেমন গুণ্ডাদেরও নেই। তাদের কোনও বিশেষ দলফল থাকে না। তারা নিজেরাই একেকটা দল। স্বভাবতই এই ঠিকেদারটাও কংগ্রেস ছিল না, ছিল জাস্ট একটা রামখচ্চর চাকলাদার, ফার্স্ট নেমটা ভুলে গেছি। গুহমজুমদারদের বাড়ি ভেঙে মাল্টিস্টোরিড-এর ঠিকে নিয়েছিল লোকটা। তা এমন ‘ম্যাটার’ দেয় যে এক রাত্তিরে নির্মীয়মাণ পাঁচিল ভেঙে পড়ে দুটি ভিখিরি একেবারে চেপ্টে যায়। জগাদা-বলাদা এই সুযোগে ইন নিয়ে নেয়। ভিখিরি দুটি সঙ্গে-সঙ্গে লাল হয়ে যায়, ঠিকেদার সাদা এবং সে মার খায়। শামু আমাকে পরে বলে মারটা লোক দেখানো ছিল। সিনেমায় যেমন হয় আর কী! চাকলাদারকে নিয়ে দু’ ভাই নাকি ওই ফাঁকে একটু রিহার্স্যালও দিয়ে নেয়। জনতার হাতে ধোলাই হলে চাকলাদার তো পুরোপুরি ফর্সা হয়ে যেত, সেই বুঝে সে আগেভাগেই জগা-বলাকে নেতৃত্বে ফিট করে দেয়। জগা-বলা রক্তচক্ষে ‘মজদুর হত্যার বদলা চাই ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ বলতে বলতে চাকলাদারকে এক পক্কড় মেরে বা মারার ভান করে থানায় নিয়ে যাবার আগে ডক্টর আসিফ আনোয়ারের নার্সিং হোমে নিয়ে যায়। তবে নাকটা নাকি সত্যিই ভেঙেছিল। ইয়া লাশ মাথামোটা বলাদা ঠিকঠাক তাক করতে পারেনি। মহলারও কিছু কমি ছিল। ডাক্তার আনোয়ারের সূত্রেই এত খবর শামুর জানা। তা সেই থেকেই জগাদা-বলাদা স্পেশ্যালি জগা আমাদের পাড়ার লাল দুর্গ। কিছু হলেই আরশুলার মতো শুঁড় নাড়ে। এখন তাকে লড়াই বলো তো লড়াই, সমাজসেবা বলো তো সমাজসেবা, সেশন জজগিরি বলো তো সেশন জজগিরি।
আর অরবিন্দদা? ওকে আমরা নিজেদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ বলি। কিন্তু দেওয়ালেরও কান আছে, তাই নামটা অরবিন্দদা জেনে গেছে। তারপর থেকে ওর রোয়াব আরও বেড়ে গেছে। সাদা ধবধবে পায়জামা পাঞ্জাবি। গলায় সোনার হার, গায়ের চামড়ায় ঘি-মাখনের চেকনাই, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, অরবিন্দদা আপাতত কংগ্রেস করছে। জগাদা যদি স্লিপিং হয়, অরবিন্দদা তা হলে ভেরি মাচ জাগিং। একজন রুলিং পার্টির পাত্তা-না-পাওয়া ফেলটুস, অন্যজন অপোজিশনের মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। যদ্দূর জানি জনান্তিকে অরবিন্দদা জগাদাকে করুণা করে থাকে—আহা জগাটা কিছু করতে পারলে না। আরে বাবা শুধু অ্যাম্বিশনে কি আর কিছু হয়! এলেম চাই, ব্যক্তিত্ব চাই।
জগাদার সরু গলার ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই কিছুক্ষণ শুনেও কিচ্ছু বোধগম্য হয় না। অরবিন্দদা মুখ খিঁচিয়ে বলছে শুনি—যা না যা, তোর আলিমুদ্দিনে যা, তড়পাচ্ছিস কেন? তড়পানোটা বন্ধ কর। ঢক থাকে তো যা! মুরোদ তো জানা আছে। বলে অরবিন্দদা একটা অশ্লীল ঝুমুর নাচের পোজ দিল। তেলে-বেগুনে জ্বলে জগাদা মারমুখো কুকুরের মতো কয়েক পা তেড়ে যায়। ‘তেখলেন তো? তেখলেন তো?’ জগাদা সব সহ্যি করতে পারে, এই আধা ক্যাপিটালিস্ট সিসটেমে সংসদীয় গণতন্ত্রের ফ্রেমে কাজ করতে করতে জগাদা অনেক অনেক সহ্যি করতে শিখেছে কিন্তু অপ-সমস্কৃত সে কিছুতেই সইবে না। প্রসঙ্গত জগাদা এইচ এস ফেল, অরবিন্দদা বলে বেড়ায় সে বি এ, এল এল-বি। কিন্তু কবে কোথা থেকে যে সে এ-সব পাশ করে এসেছে তা পাড়ার কেউই জানে না। গেঞ্জির কল আছে ওদের। চলন-বলন কথাবার্তাতে একটা গেরেম্ভারি ভাব। সেটা চেহারার জন্যে না তথাকথিত এল এল-বি’র জন্যে না গেঞ্জির কলের জন্যে তা আমরা আজও বুঝতে পারিনি। তবে ওর মোটা ফর্সা গেরেম্ভারি চেহারায় নাচের পোজটা রিয়্যাল অশ্লীল দেখাল। অশ্লীলতার একটা চুম্বুকী টান আছে আপনারা স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই। তো সেই টানে আমি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যাই, যদি আরও পোজ-টোজ দেয়। তা সে গুড়ে বালি! স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা। অরবিন্দদা জানে কীসের ঠিক কতটা ডোজ দিতে হয়। আমাদের মতো ল্যাবাকান্ত তো আর নয়! হতাশ হয়ে আমি সাইকেলে উঠে পড়ি। আই বাই সাইকেল। ন’টায় চা-মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছি এখন বারোটার কাছাকাছি। সূর্য মাঝ আকাশে গনগন করছে। পেটের মধ্যে ছুঁচোবাজি। ফার্মাসি থেকে ওষুধগুলো তুলে বাড়ি ফিরব। এঃ। রিন্টিটার জন্যে দুটো লজেন্স কিনে নিই। নাকের বদলে নরুন, সচিনের বদলে লজিন।
২
আমাদের এই পুরো পাড়াটার নাম নাকি একসময়ে ছিল জবরদখল নগর। সরকারি খাতায় উদ্বাস্তু শিবির কিন্তু স্থানীয় লোকেদের মুখে জবরদখল নগর। বাবা তখন বছর পাঁচেকের ছেলে, ঠাকুর্দা-ঠাকুমার হাত ধরে এখানে এসে পড়েছিল। পঞ্চাশের দশক, একান্ন কি বাহান্ন। ঠাকুমা বলতেন সে যে কী হেনস্থা, কী হেনস্থা কহতব্য নয়! যাদের জমি এখানে দখল করে দলে দলে প্রাণ-মানের ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য পূর্ববঙ্গীয়রা বসে গিয়েছিল, তারা মাঝে মধ্যেই চড়াও হয়ে গালাগাল দিত। কেউ-কেউ অনুনয়-বিনয়ও করত। ঠাকুর্দা ছিলেন সেকালের আদর্শ ইস্কুল মাস্টার, ফরিদপুরে অনেক জমিজমা ছিল। তবু কোনওক্রমে দুটো খাওয়া আর পরনের কাপড় জুটলেই মনে করতেন সব ঠিক আছে। ঠাকুমা কিন্তু ছিলেন রীতিমতো জাঁদরেল। একবার এইরকম একদল এসে শাসাচ্ছে, এক ভদ্রলোক বলছেন— মাস্টারমশাই আপনারা বলছেন আপনারা বাস্তুহারা, স্বাধীন দেশের সরকার আপনাদের জন্য কিছু করেনি, কিন্তু আপনারা! আপনারাই বা কী? আপনারা তো আমাদেরই উদ্বাস্তু করে দিচ্ছেন, বিশ্বাস করুন গলির গলি তস্য গলি বউবাজারের একতলায় ছেলেপিলে নিয়ে ভাড়া থাকি। এই জমিটুকু কিনেছিলুম একটু আলো-হাওয়ায় বাস করব বলে, বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা এখনও এই চুয়ান্ন বছর বয়সেও করে উঠতে পারিনি। সে আশাটুকুও গেল।
ঠাকুর্দা মাথা চুলকে, দাড়ি চুলকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ঠাকুমা নাকি ফ্রন্টে এসে যান। বলেন— আমি ধরেন আপনের বউমা, আপনি আমার শ্বশুরের মতন, একটা কথা জিগাই জবাব দ্যান তো! আপনের কয়টা পোলাপান?
—আজ্ঞে পাঁচটি, কেন?
—মেয়ে কয়টি?
—দুটি।
ঠাকুমা বলেন—আমাগ তিনটা ছিল। একটিরে ও পারেই হারাইসি। চক্ষুর সম্মুখ দিয়া নিয়া গেল কিসুই কইরতে পারি নাই। আর দুটিরে লইয়া পলাইয়া আইতে ছিলাম, কখন, কোন নিশিরাত্রিতে কোন যমে যে আর একটিরে কাছছাড়া কইরলো, এই এতগুলান দিনেও খুঁজিয়া পাই নাই। এখন এই চার খানি প্রাণ। বক্ষে পাষাণ, নিজেরা মাথায় বাড়ি মাইরা মাইরা মইরা যাইতে পারতাম। কিন্তু এই শিশু, পাঁচ বছুরা, এগারো বছুরা, ইয়াদের কী করি, কইয়া দ্যান, একটি আবার সে-ই মাইয়া।
পুরো দলটা থমকে গিয়েছিল। হঠাৎ কোনও জবাব দিতে পারেনি। এখন যেমন প্রতি দলে কিছু গুণ্ডা থাকে, তখন তো অতটা থাকত না। এঁরা সত্যিই জমিগুলোর মালিক ছিলেন। সস্তার জলা জমি। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের অনেক কষ্টের কেনা।
ঠাকুমা তখন বলেন—আমাগ সকল গিয়াসে। মান সম্ভ্রম-বিষয়-সম্পদ-পোলা-মাইয়া-সোয়ামি-স্ত্রী-ভাই-বুন। স্বাধীনতা সব খাইয়াসে। স্যাক্রিফাইস। আপনাদের কষ্ট, আশাভঙ্গ সকলই বুঝি। এইটুকু ধরেন আপনাগ স্যাক্রিফাইস। গরমেন্টরে বলেন অ-মশায়গণ আপনেরা তো সব গদি পাইলেন, আমরা কী পাইলাম? কিস্যু না, যা ছিল সকল হারাইসি। দুর্বৃত্তে নিজের মাইয়া টাইনা লইয়া গেল, কী অত্যাচার করল, কী কাটবা, কী রাখবা, কোথায় কোন আন্ধারে উয়াদের স্থান হইবে গিয়া, ভাবেন, একটু ভাবেন, এই নরক যন্ত্রণা তো অন্তত পক্ষে আপনাগর নাই।
ঠাকুমার কাছেই এ সব গল্প আমার শোনা। বাবা মুখচোরা মানুষ, কারও সাতে পাঁচে থাকতেন না। ঠাকুর্দার স্বভাব পেয়েছিলেন। বাবার কাছ থেকে কথা বার করা মুশকিল ছিল। আর এই অতীত খুঁড়তে কারই বা ভাল লাগে। তবে কিনা আমার কৌতূহল বরাবরই একটু বেশি। যেখানে যেটুকু পাই, জানতে ইচ্ছে করে, কী, কেন, কীভাবে কী হয়! তা সেই পুনর্বাসন, সেই জবরদখলত্ব আর রেফিউজিত্ব তো সোনার পশ্চিমবঙ্গে এখনও টিকে রয়েছে দেখি। ফুটপাত জবরদখল, খালপাড় জবরদখল, উড়ালপুলের তলা জবরদখল, বাজার বাড়তে বাড়তে বাজারের আওতা ছাড়িয়ে বসতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অফিসযাত্রী রবিনবাবু একদিন দলামোচড়ানো পুঁইশাকের পাতায় হড়কে কোমরের হাড় ভাঙলেন। তনিমা দিদিমণি আঁশবঁটি আর মোটরের তলা কোনটা বেছে নেবেন ভাবতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় পাননি। মহিলার পায়ের পাতার ওপর দিয়ে মোটরটা চলে যায়। এখন সেরে উঠেছেন, একটু খুঁড়িয়ে চলেন। কিন্তু রবিনবাবু তনিমা দিদিমণি দু’জনেই এখনও এই রাস্তা বাজারেই বাজার সারেন। রবিনবাবু কাকে যেন বলছিলেন— সময় কোথা? যে জম্পেশ বাজার করব? এই ফিরতি পথে লাউটা, কুমড়োটা, এই-ই আমাদের সুবিধে বুঝলেন না? তনিমা দিদিমণিরা বলাবলি করেন— এখানে চাষিরা, চাষিবউরা বসে, ওদের জিনিসগুলো অনেক ফ্রেশ, দামেও সস্তা, শাকে-পটোলে কেমিকেল রং দেয় না।
সেদিন দেখি শনিতলার বেঁটেদা তিনটে গামছা আর ক’ বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে ওখানেই বসে পড়েছে। পাশে আবার ক’খানা মেয়েদের ব্রেশিয়ার, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখা। বেঁটেদার হাইট সাড়ে তিন ফিট। কোমরের ওপর থেকে সবই ঠিকঠাক। গোঁফ দাড়ি, যন্তর সবই যে যার জায়গা মতো। কিন্তু হাঁটুর তলা থেকে পায়ের সাইজ বাড়েনি।
—কী বেঁটেদা, এসব কী?
—বেওসাটা শুরুই করে ফেললুম, বুঝলি না? কত লম্বা-চওড়ারাই বলে চাকরি পাচ্ছে না। ত আমার মতো বেঁটে!
—তা গামছা বুঝলাম। বিড়িও বুঝলাম। ওগুলো কেন?
ব্রেশিয়ারের ফোলা জায়গায় হাত বুলিয়ে ভেতরে মুঠো ঢুকিয়ে আরও নিটোল করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বেঁটেদা চোখ মটকে বলল— অ্যাডভাইস।
—অ্যাডভাইস? মানে?
—অ্যাডভাইস দেখায় দেখিস না? ছেলেদের গেঞ্জি তাতেও মেয়েছেলে হাত বুলোচ্ছে, ছেলেদের জাঙ্গিয়া সেখানেও ছোট ছোট জামা পরা মেয়েছেলে। এমন কী দাদের মলমেও দেখবি মেয়ে নাচছে। আসলে সেক্স না থাকলে কোনও কিছুই বিকোয় না শালা। তোদের বেঁটেদা সব খ্যাল রেখেছে। বেঁটে হলে কী হয় মাথার ঘি কিলোয় তোদের কারও থেকেই কম হবে না। বুঝলি? ফুলো ফুলো, সাদা-সাদা আহা, এই দেখে খদ্দের দাঁড়িয়ে পড়বে তারপর দেখবে আসল দরকারের মাল। বিড়ি আর চেড়ি— এই দুটি হল গিয়ে হত্যাবশ্যি জিনিস। পরনে গামছা আর মুখে বিড়ি থাকলে কোন শালা কার তোয়াক্কাটা করে, তুই-ই বল!
—বিড়ি তো বুঝলাম। কিন্তু ছিঃ বেঁটেদা তুমি চেড়িও সাপ্লাই দিচ্ছ না কি?
—আরে বুরবক কাঁহিকা, চেড়ি হল ওই গামছাগুলো। চেক-চেক দেখছিস না? চেক-চেকের বাংলা হল চেড়ি। এই সামান্য কথাটা বুঝলি না? ইংলিশ ইংলিশ করে দেশটা এমন খেপে গেল যে সামান্য বাংলা কথা ধরতে পারে না। তা বিড়ি আর চেড়ি এই হল গিয়ে হত্যাবশ্যি। আর বাকি যা দেখছিস তা স্বপন, নিশার স্বপন। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী— হেঁড়ে গলায় গান ধরে বেঁটেদা। কে বলে রবীন্দ্রসঙ্গীত জনগণের কাছে পৌঁছয়নি?
এই সময়ে নিমকি এসে দাঁড়াল।
—ব্রাগুলো কত করে?—আমি সরে যাচ্ছিলাম, বেঁটেদার চোখে দেখি কাতর অনুনয়। সে কোনও মতে বলল— সাইজ কত?
—বুঝতে পারছ না গো বেঁটেদা? ছত্তিরিশ গো ছত্তিরিশ!
আমার দিকে আড়চোখে একবার চাইল নিমকি। কটাক্ষপাত আর কী!
বেঁটেদা দেখলাম একটু ব্রীড়াবনত, থতোমতো খেয়ে গেছে।
—ব্র্যান্ডো জিগ্যেস করলে কিন্তু বলতে পারব না। এসব লোকেল মাল।
—আরে আমরাও তো লোকেলই গো—বলতে বলতে নগদ কুড়ি টাকার একটা কমলালেবু নোট ফেলে দিয়ে খবরের কাগজে মোড়া একটা ব্রেশিয়ার তুলে নিলো নিমকি। তারপর পেছন নাচাতে নাচাতে চলে গেল।
আমি বলি— এতক্ষণ তো খুব লেকচার ঝাড়ছিলে হেনচারিণী, তেনচারিণী, যেই খদ্দের এসে উপস্থিত হল, অমনি ওরকম কেঁচো মেরে গেলে কেন?
বেঁটেদা মাথা চুলকে বলল— আরে মেয়েছেলে দূর থেকে একরকম। ছায়া-ছায়া নরম নরম। কিন্তু এমন কাছ থেকে? বাপরে! আমার পেটের ছেলে পড়ে যাবে।
—তা তোমার বউনি তো হয়ে গেল! ভাল ভাল!
আমি বাজারের সরু পথ সাইকেল ধরে পার হই। ভেতরে একটা রাগ ঘুঁষি পাকিয়ে আছে। নিমকি বিহারের মাল। ওদের ওইরকম নাম হয়— রাবড়ি, জিলাবি, নিমকি, খাজা, খাস্তাগজা। তা হোক গে! আমি জন্মে থেকে নিমকিকে দেখে আসছি। নাকে শিকনি, ছেঁড়া ইজের খালি গা। যেখানে-সেখানে রোঁয়া ফুলিয়ে বেড়ালের মতো ঝগড়া করত। নিমকির মা এ দিকের হিন্দি ইস্কুলের ক্লাস ফোর, মানে ঝি। বাপের খোঁজ নেই। নিমকি হিন্দি ইস্কুলে ছ’-সাত ক্লাস পড়ে আর সুবিধে বোঝেনি। এইরকম ঢলে ঢলে বেড়ায়। জুতোর পালিশের মতো চকচকে কালো রং। ডেঁও পিঁপড়ের মতো পেছন উঁচু, বুক দুটো কেমন খোঁচা মেরে থাকে, যেন ভেতরে মাংস নেই, দা-কাটারি জাতীয় কিছু পোরা আছে। দু’-তিন বছর আগেও নিমকির চেহারায় একটা মার্কামারা বিহারি লাবণ্য ছিল, এখন দেখলেই বোঝা যায়— নিমকি গন কেস! তা সেই কেস যে কেন এত এলিজিব্ল্ তরুণ থাকতে আমারই পেছনে সেঁটে থাকে আমার বোধগম্য হয় না। বেঁটেদার কাছ থেকে সওদা করা ওর একটা বাহানা। আমি আছি দেখে স্রেফ ভিড়ে গেল!
রাগে ব্ৰহ্মরন্ধ্র অব্দি জ্বলতে থাকে। কোন হিসেবে এই নোংরা নিমকি নিজেকে আমার যোগ্য মনে করে! ও কি ভেবেছে বেকার বলে আমি একটা যা-তা! ও ফিলমের হিরোইনের মতো বুক আর পেছন নাচালেই আমি ভিজে যাব। ছোঃ! সশব্দে থুতু ফেলি। এইয্ যাঃ! পাশ দিয়ে মহাজনদের একটা গাড়ি যাচ্ছে, লাগল না কি? দেখি তামাটে কাচ নেমে যাচ্ছে, দাড়ি-গোঁফ কামানো মেয়েলি চেহারার ছোট মহাজন নাম বোধহয় মহেন্দ্র, আমার দিকে তাকিয়ে বলল— রাস্তার মাঝখানে থুতু ফেলাটা কি ঠিক হল ভাই? গাড়ির কাচ উঠে যায়। শব্দহীন গাড়ি ভেসে চলে যায়। লান্সার গাড়ি। বেঁটেদা বলে লাঞ্চার।
বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর বাপের থুতুদানিটা তো পথশোভার স্বার্থে দান করলেও পারে। তা বলব কী গাড়ি তার আগেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। অবশ্য কথাগুলো আমি বলতে পারতামও না। বড়জোর বলতাম— স্যরি। রাস্তাটা যেমন আপনাদের, তেমনি আমাদেরও, আপনাদের থুতু ফেলার জায়গা আছে, আমাদের নেই। বলতে কী আপনাদের তেমন স্যালিভেশন হয়ও না। আমাদের অ্যাসিড-ফ্যাসিড আছে, থেকে থেকেই পথে-ঘাটে থুতু পায়। তা বেঁটেদার মতো লোকেদের গ্যাঁট-গচ্চার মালের ওপর ফেলব? না আপনাদের লাঞ্চারের ওপর, বলুন! আর তো কোনও অলটারনেটিভ নেই! আর নিজের থুতু নিজে গিলব এমন আহাম্মক ডরপোকও আমাকে পাননি। এ সব কথাও অবশ্য আমি বলতে পারতাম না। কথাগুলো অবিকল শামুর স্টাইলে বলা। খুব ডিপলি একটা মানুষের সঙ্গে মিশলে এগুলো আপনা থেকে হয়ে যায়। এই সিচুয়েশনে শামু কী বলত, শামু কী করত! সঙ্গগুণ। যেমন আমার সংস্কৃত পণ্ডিত বাবার আমলে আমরা কখনও পেচ্ছাব পায়খানা যাইনি। তখন আমরা বড়জোর প্রস্রাব করতাম, বাহ্যে যেতাম, তখন মেয়েরা মেয়েছেলে ছিল না, মা জননী ছিল, তখন আমরা নিয়মিত গৃহদেবতার আরতির সময়ে অংশ নিতাম। বড় বড় মানুষদের, যেমন বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র, গাঁধীজি এঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম।
এখন আমাদের ভক্তি চটকে গেছে। এনাদের নাম উঠলেও আমরা এনাদের কাঠগড়ায় তুলি। পৃথিবীটা জীবনটা ফলাফলের। কর্মের মোটেই নয়। কার কোন কাজের ফলে টাকাপয়সা আসছে, সেটা দেখবার দরকার নেই, টাকাপয়সাটাই দেখবার। পানু তো বলে— বিদ্যেসাগর! বিদ্যেসাগর আমাদের কী করেছে রে! যা কিছু সব মেয়েদের জন্যে। বিধবা বিবাহ! আরে বাবা সব বিধবা বিয়ে বসলে হাজারে হাজারে যে সব কুমারী জন্মাচ্ছে তাদের বিয়ে হবে কী করে— তা সে ভেবেছিল?— আমাদের হাততালি আর হাসিতে বিরক্ত হয়ে পানু মহা উত্তেজিত হয়ে যায়।— আরে সেই থেকেই তো মেয়েগুলো তড়পে তড়পে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। আপিসে যা— মেয়েছেলে, ইস্কুল-কলেজে যা— মেয়েছেলে! বাসে-ট্রামে ওঠাও চাই গায়ে গা লাগিয়ে, আবার ছুঁচিবাইও ষোলো আনা। থানায় সুদ্ধু মেয়েছেলে। আর বছর ম্যালেরিয়া হয়েছিল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি, ও মা দেখি এক লেডি-ডাক্তার স্টেথো বার করছে। ‘আমি লেডি নই, আমি লেডি নই’ বলে খুব চিৎকার দিয়েছিলুম, শুনলে না, গম্ভীর মুখে ইনজেকশন দিয়ে নার্সকে কী সব ছাই-ভসসো বলে গটগট করে চলে গেল। তার ওপর নার্সটা আবার বলে কী জানিস? মুচকি হেসে বলে— লেডি নন, কিন্তু আপনি নির্ঘাত লেডি-কিলার।
সাম্য বলল—যা বলেছিস। বহু বিবাহই বা বন্ধ কেন? বড় বড় লোক, ফিলিম স্টার— এরা তো দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে, আইনকে কলা দেখিয়ে। আমাদের হিন্দু জনগণের বেলায় আলাদা নিয়ম কেন?
শামু বলল— খবরদার! আমাকে একলা পেয়ে খুব ডিং নিচ্ছিস, না? দলবল থাকলে দেখিয়ে দিতুম মজা।
আমার খুব খারাপ লাগল। শামু আমাদের ছোটবেলাকার খেলার সাথি। এখন ও গদার সঙ্গে নেই, তার চালচলন বড়লোকি হয়ে গেছে। কিন্তু শামু আমাকে অনেক খবরাখবর দেয়। আমার বাবা মারা গেলে শামু এসেছিল। শামুর বড় বোনের শাদিতে আমি বিরিয়ানি খেয়ে এসেছি। শামু আমাকে দল দেখাচ্ছে? কোথায় ছিল খেলার মাঠে শামুর দল, যখন একটা নামকরা নাক-উঁচু ক্লাবের প্লেয়ার আমাদের মাঠে খেলতে এসে ইচ্ছে করে লেঙ্গি মেরে শামুর ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছিল। আমার মনে পড়ছে সেই প্লেয়ারটার নাম ছিল মুস্তাক। এ কথা বলছি না যে কোনও কানাই-বলাই কাজটা করত না। কিন্তু কাকতালীয় হলেও খুব অদ্ভুত ছিল ঘটনাটা। ভাঙা পা নিয়েই মুস্তাককে এক বিরাশি সিক্কার চড় মেরেছিল শামু। হাসপাতাল-ওষুধপত্র-অপারেশন সব কিছুর ব্যবস্থা তো আমরাই করি। সেই থেকে শামুর ফুটবল শেষ। বড্ড ভালবাসত খেলাটা। কিন্তু পার্ক সার্কাসের ওই পয়সার ফুটানিঅলা মুস্তাক মির্জা ওর কেরিয়ার তো শেষ করে দিলই, কোনও মাফ চাওয়া না, কিচ্ছু না। ড্যামেজ দাবি করে ওদের বাড়ি আমরা ধাওয়া করেছিলাম। বাপস সে কী বাড়ি, বড়লোক বটে। ওরা সব নামকরা ইংরেজি স্কুলের ছাত্র, ওর বাবা ইংরেজিতে আমাদের হাঁকিয়ে দিল। সেই শামু আজ আমাকে দলবল দেখাচ্ছে।
আমি স্থির আহত চোখে ওর দিকে চেয়ে বলি—ওই কর, যেখানে তোদের ধর্মের লোকজন বেশি সেখানে তোরা আমাদের ঠ্যাঙা, আর যেখানে আমাদের ধর্মের লোকজন বেশি সেখানে আমরা তোদের ঠ্যাঙাই। ইতিমধ্যে পৃথিবী জ্ঞানে-বিজ্ঞানে মিলিয়ন পা এগিয়ে যাক। ইতিমধ্যে তোদের আর আমাদের ধর্মবাজগুলো বেশ কিছু গুছিয়ে নিক। সাতপুরুষের মতো। তুই আর আমি একই মাঠে মরে পড়ে থাকি। আমি ধর পাথরচাপা আর তুই ধর বেগুনপোড়া। একই খেলার মাঠে। একই ভাষায় মা মা চিৎকার করতে করতে।
কথাবার্তা গোলমেলে জায়গায় চলে যাচ্ছে এবং শামুর মুখ কালো হয়ে গেছে দেখে সত্য আমাকে থামাল। আমিও থেমে গেলাম। কিন্তু পানু আর থামে না। বলল— ব্যাপারটা একলা পাওয়ারও না, ডিং নেওয়ারও না, লজিক্যাল কথা বলছি। বুঝতে যাতে না পারিস তার জন্যে চতুর্দিকে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, জাল বিছোনো হচ্ছে। তোদের মেয়েরা লেখাপড়া করে না কেন রে? খালি আরবিটুকু শেখে, কেন? সত্যি কথা, আমাদের জন্যও জাল বিছানো চলছে। কিন্তু ভুলগুলো ধরিয়ে দেবার লোকও আমাদের আছে শামু। কথাগুলো সাম্য খারাপ বলেনি।
তবে এ ধরনের তর্কাতর্কি সবই এখন অতীতের ব্যাপার। সাম্প্রতিক অতীত। কিন্তু অতীতই। শামু খুব তাড়াতাড়ি কেউকেটা হয়ে যাচ্ছে। শামুকের খোলের মধ্যে ঢুকে থাকে। মাঝে মাঝে তার থেকে বেরিয়ে হঠাৎ-হঠাৎ এক একটা খবর দিয়ে যায়। নইলে রাস্তাঘাটে দেখা হলে একটা উচ্চাঙ্গের হাসি দিয়ে বলে—কী রে রুণু এখনও চাকরি খুঁজে যাচ্ছিস? না, সেলফ-এমপ্লয়মেন্টের স্বপন দেখছিস? আজকাল খুব ফিনান্স কম্পানি টম্পানি হয়েছে, এজেন্ট হয়ে ভালই কামানো যায়। দেখছিস নাকি? আমি বলি—এ-ই!
খবর থাকলে অবশ্য খবরটুকু শুনে নিই কান পেতে। তামাশা-মশকরা হজম করি নির্বিবাদে কেন না শামু আর আমাদের সেই শামু নেই। সে এখন ওস্তাদ সমশের। পেছনে রাজনৈতিক দাদারা আছেন। আমি যদি রেললাইনের ওপারে সিগ্রেট-লজেন্স-কোকোকোলার দোকান দিই তো শামুকে প্রতি মাসে চাদা দিতে হবে। শামু চাইবে না। আমাকেই অন্য দোকানদারদের থেকে খবরাখবর নিয়ে নিজে শামুকে পৌঁছে দিতে হবে।
—শামু, শামু-উ বাড়ি আছিস?
—কে রে? আরে রুণু না?
আমি একগাল হেসে বলব—দোকানই দিলাম শেষে, কেউ হুজ্জোতি করলে সামলে দিস ভাই। খরচখরচাও তো আছে তাতে। টাকাটা রাখ।
লুঙ্গির গেঁজেতে টাকাটা রাখতে রাখতে শামু বলবে—ধুস, তুইও যেমন, তোর আমার দোস্তি আজকের? তোর দোকানে হুজ্জোতি করবে শামু থাকতে? তোর জন্যে জানটাই দিয়ে দিতে পারি তা জানিস?
—সে আমি জানি—আমি বলব—তবু আমার দিক থেকে বললাম। তোর দিকটাও তো আমার দেখা দরকার।
—তা যদি বলিস তা হলে আলাদা কথা।
আর, দোকানটা যদি রেললাইনের এপারে করি? গদাইয়ের কাজ কারবার আরও জটিল, রাশভারি। সে নিজেই হয়তো তার গ্রে রঙের ফোর্ড আইকনখানা থামিয়ে মুখ বাড়াবে। পরম বিস্ময়ের গলায় বলবে—আরে, রুণু যে! যেন আমি বহুদিন প্রবাসী, দিল্লি কিংবা মুম্বই। আমি হাসব। গদাই বলবে—‘সুধা স্টোর্স’ দোকানটা তোমার? আমি বলব—হ্যাঁ। তো কী? গদাই বলবে—কী আবার। ভীষণ আনন্দের কথা যে শেষ পর্যন্ত ডিসিশনটা নিলে। নাইস থিং। আমরা পাড়ার লোকেরা ন্যাচারালি পেট্রোনাইজ করব। গারাজটাও তোমাদের পড়ে ছিল।
এই বলল তো গদাই? দু’-চার মাস পরে, জমিয়ে বসে যাবার পর একদিন একটা অচেনা ভীষণ দর্শন লোক, তার পেশি হাফপাঞ্জাবির মধ্যে দিয়ে দৃশ্যমান করে এসে ঘটা করে কোক চাইবে—দেব। সিগ্রেট চাইবে—দেব। ধরিয়ে নিয়ে ধীরেসুস্থে বলবে—ক্যাশে কত জমল?
তখনই আমার হাড় হিম হয়ে যাবে। এই সেই। গদার লোক।
—আমরা সিকিওরিটি বাবদ সামান্য কিছু নিয়ে থাকি।—আমার ভয় দেখে লোকটা মোলায়েম করে বলবে।
—কত?
—প্রফিটের ফাইভ পার্সেন্ট।
—তা এই চার মাসে তো প্রফিট হয়েছে সাকুল্যে এগারো হাজার টাকা ক’ পয়সা।
—রাউন্ড করে দিলেই হবে। তো এগারো হাজারের দশ পার্সেন্ট কত হচ্ছে?
—এগারশো।
—তো ফাইভ পার্সেন্ট?
—সাড়ে পাঁচশো।
—টেন নেওয়া হয়। আপনি নতুন আছেন আপনার সাড়ে পাঁচেই হোবে। লোকটা টাকা নিয়ে চলে যাবে।
পুরো কথোপকথনগুলো আমি বানিয়ে বললাম ঠিকই। কিন্তু বানানো হলেও এটাই সত্যি। আর সেই হেতু মা, দাদা, বউদি, সব্বাই আমাকে গারাজে দোকান দিতে জোর করলেও আমি একেবারেই কান দিচ্ছি না। খাল কেটে কেউ কুমির আনে?
৩
এঃ, দীপুটা মহা-ভাবনায় ফেললে। খ্যাপাটে ছিল, ঠিকই, বোধহয় পুরো খেপে যাচ্ছে। সেদিন আমায় একটা কোণে ঝুপসি দেখে একটা গাছের তলায় টেনে নিয়ে গিয়ে বলল—রুণু তোকে একটা কথা বলছি, কাউকে বলবি না বল।
—কী কথা?
দীপু বলল—আমার আর চাকরি-ফাকরি চাই না।
আমি জানি এই ইন্টারনেটের যুগে যেখানে শিক্ষিত ছেলেদের দশজনে একজন কম্প্যুটার জানে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের হাতে ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে কেউ থোড়ি থাকে, কিছু না কিছু একটা দালালি-ফালালি খুঁজে নেয়, সেখানে দীপুর মতো ছেলের চাকরি হওয়ার কথা না। লেখাপড়ায় ছিল মন্দ না, অঙ্কের মতো সাবজেক্টে এম এসসি করছিল, তখনই ঝপ্ করে ওর বাবার ব্যাপারটা ঘটে। বুঝতে পারি হকার বাবা অনেক কষ্টে পড়িয়ে শুনিয়ে একটা ভদ্র, সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিজেও দেখতেন, ওকেও দেখাতেন। দীপুটা একটা প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছে। ধরুন, এক গ্লাস জল তার তলায় ময়লা থিতিয়ে রয়েছে, হঠাৎ সেটাকে যদি ঝাঁকান, কী হবে? ময়লাগুলো পরিষ্কার জলের সঙ্গে মিশে যাবে, জলটা ঘোলা হয়ে যাবে। দীপুর মগজের সেই অবস্থা। ওদের হিসট্রিটা ভারী অদ্ভুত! ওর ঠাকুর্দা ছিলেন পুরুত বামুন। বেশ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কাজটা করে গেছেন। ছেলেকে অর্থাৎ দীপুর বাবাকে বলেছিলেন— ক্রমশ পুজো-আচ্চা কমে যাচ্ছে, এই জীবিকা নিলে আর করে খেতে হবে না। একটা নিশ্চিন্ত চাকরি খোঁজো। দীপুর বাবা তাই খুঁজেছিলেন, একেবারে নিশ্চিন্ত বলতে সরকারি চাকরি পাননি, উনি একটা বড় ফ্যাক্টরিতে ডেসপ্যাচে কাজ করতেন। ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেল। আবার যখন খুলল দেখা গেল উনি ছাঁটাই। ওঁর জীবৎকালে কোনও ট্রেড ইউনিয়ন ওঁর প্রাপ্য টাকাটা বার করে দিতে পারেনি। চলে গেলেন বস্তিতে, নিলেন হকারি।
পার্টিগুলোকে টাকাও খাওয়াতে হল। বড় ছেলেটি লেখাপড়ায় খাটো। কিন্তু মেজ এই দীপুর মাথা ছিল। বড় মেয়ে মণিটারও যে মাথা আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দীপুটাকে উনি পড়িয়ে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারি-এঞ্জিনিয়ারিং-এর লাইন ধরা তো দুরাশা। ও অঙ্ক নিয়েই পড়ছিল। তারপর বিনামেঘে বজ্রপাত। যারা বসিয়েছিল তারাই উঠিয়ে দিল। উনি বোধহয় পর পর এরকম দুর্দৈব সইতে পারলেন না। কাজেই ছারপোকা মারার ওষুধ…। সত্যিই, উনি বেঁচে থাকলে তো মাসিমা রাঁধুনিগিরি করতে পারতেন না। মণিমালাও স্কুল থেকে ওরকম সাহায্য পেত না। বড় ছেলেটিও নিজের পথ নিজে খুঁজে নিত না। সেই একটা কথা আছে না, ‘নেই তাই পাচ্ছো, থাকলে কোথায় পেতে?’ এখন ওঁর প্রাপ্য বকেয়া টাকাপয়সাগুলোও দীপুর মা পেয়ে গেছেন। কাজেই দীপু কিছু না করলেও ওদের দু’ বেলা দু’ মুঠো জুটে যাবে। কিন্তু তাই বলে মা রাঁধুনিগিরি করবেন, ছোট ভাই গাড়ি ধোবে, ছোট বোন চুল ঝাঁটাবে— আর সেই পয়সায় ও বসে বসে খাবে? ফ্যামিলিতে একটা আত্মহত্যা, আর একটি নিরুদ্দেশ, নিরুদ্দেশই বলব দাদাটাকে, তার ওপরে যদি আর একজন উন্মাদ হয়ে যায় সর্বনাশের বাকি কী থাকবে? দীপুটা তো দু’ চারটে টুইশনিও করতে পারত। আমি যেমন করি! বলতে কী অঙ্ক নিয়ে বি এসসি করেছে, এম এসসিরও বোধহয় এক বছর পুরো পড়া হয়ে গিয়েছিল, অঙ্ক তো সোনার সাবজেক্ট, পড়াতেই পারত! কিন্তু দীপু টিকে থাকতে পারে না। আমি দু’-একটা ওকে দিয়ে দেখেছি, তারা বলে ওরে বাবা দীপুদা বড্ড হাই স্ট্যান্ডার্ড। করতে করতে দীপু ছেড়ে দিত। কি তারাই ছাড়িয়ে দিত। আমার একটু রাগ হয়ে যায়। আমিও দাদার হোটেলে খাই। কিন্তু আমার জামাকাপড়, দু’-চারটে বিড়ি, ট্রাম-বাসের ভাড়া, আমার শেভিংক্রিম, বুরুশ, ব্লেড, চটি, জুতো, বাইরে দু’চার কাপ চা পকোড়া এসবের জন্যে কারও কাছে হাত পাতার কথা ভাবতেও পারি না। বাড়ির যত ফাইফরমাশ, বাজার থেকে কলের মিস্ত্রি, ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি, ইলেকট্রিকের বিল, রিন্টিটাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসা, সেজ মাসির গলস্টোন অপারেশন পি.জিতে, দিদির পিসশাশুড়ির শ্রাদ্ধ এ সব আমি নিজে যেচে করি। উশুল করে নিই। এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, আত্মসম্মান জ্ঞানের অভাব দেখলে আমার ভেতরটা চিড়বিড় করে। তবু ভাবলাম— বিশুদা এমেলে যখন ওর জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে…
সে কথাই বললাম— বিশুদা কিছু ব্যবস্থা করে দিল নাকি?
—তুইও যেমন, দীপু বলে, বিশুদাকে কে দেয় তার নেই ঠিক!
যাব্বাবা একটা এমেলে লোক…
আমি তেড়ে উঠি—কী যা তা বকছিস।
দীপু বলে—তুই মিছিমিছি রাগ করছিস রুণু। একটু ভাল করে ভেবে দ্যাখ, এমেলে ঠিকই। কিন্তু রুলিং পার্টির তো না! বিশুদার কট্টুকুনি ক্ষমতা! রুলিং পার্টি ছাড়া কেউ এখন কারুর কিছু করে দিতে পারে না।
—তা হলে রোজ যে অত লাইন পড়ে?
—আরে তুই তো রোজ যাচ্ছিস না, আমি তো নিয়ম করে সকাল ন’টা থেকে বারোটা একটা পর্যন্ত ধর্না দিই। কী বল তো! বেশির ভাগই র্যাশন কার্ড হারিয়ে ফেলেছে, কি একটা প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট চাই। কি ইনকাম সার্টিফিকেট, ফ্রি স্টুডেন্টশিপ, কি পাসপোর্ট কি কিছুর জন্যে। এগুলো হয়। কিন্তু আর কিস্যু হয় না। বিশুদা সব ঝুলিয়ে রেখে দেয়, সেই বলে না বাইরে ছুঁচোর কেত্তন আর ভেতরে কোঁচার …
আমি ওকে কারেক্ট করে দিই— বাইরে কোঁচার নর্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন।
—ওই হল। তার ওপরে বিশুদাটা কীরকম ক্যাংলা দেখেছিস। ধর আমি গেছি, ফর দা ফাইভ হানড্রেড্থ টাইম… মুখে বিগলিত হাসি, চোখে নেড়ি কুকুর, কান চুলকোচ্ছে যেন ন্যাজ নাড়ছে।
—সে আবার কী!
—মানে কী জানিস। মুখে বলছে—তোমার একটা ব্যবস্থা?— এই হয়ে গেল। স্কুলসার্ভিস কমিশনের এক হোমরা-চোমরাকে বলে দিচ্ছি। নেক্সট ইন্টারভিউতেই তোমার হয়ে যাবে। ভাল করে ভাইভাটা দিয়ো কিন্তু! বলে দেওয়া পর্যন্ত আমার হাত, তারপর… বলতে বলতে কাঠি দিয়ে কান খোঁচাবে। বুঝলি? ক্ষমতা নেই এক কড়া। বলবে ভাইভাতেই গেছ। বুঝলে? আর যতক্ষণ থাকব কাঙালের মতো চেয়ে থাকবে, ভোটটা দিয়ো, তোমাদের বাড়ির পাঁচটা ভোট শিওর তো! যদি একবার ক্ষমতায় আসতে পারি, ইস্স্-ফুড মিনিস্ট্রিটা কে ঠ্যাকায়! আর তখন দো হাত্তা টাকা টাকা টাকা…
বলতে বলতে দীপু হাতগুলো দিয়ে ইম্যাজিনারি টাকা লোফে আর হো-হো হা-হা করে হাসে।
—চুপ কর দীপু।…আমার মনে হল দীপু ইজ টকিং সেন্স। কিন্তু ধরনধারণ সুবিধের ঠেকল না,— তা চাকরি না হয় তুই না-ই করলি। অন্য কোনও ব্যবস্থা করতে পেরেছিস?
—তোকে বলব কেন?—দীপু চকচকে রহস্যভরা চোখে তাকায়।
—বলতেই তো ডেকেছিলি!
—তা-ই? ডেকেছিলুম বুঝি!
আমি পেছন ফিরি, বেকার হতে পারি। এত নষ্ট করার সময় আমার নেই। সচিনের পোস্টারটা আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে! হকারি উঠে গিয়ে এই একটা মস্ত গোলমাল হয়েছে। কোন জিনিসটা কোথায় পাবে তুমি জানবে না। মাছের বাজার জানো, কাপড়জামা-জুতোর দোকানও সব স্পেশালাইজড। কিন্তু পোস্টার। ও তো চিরকাল এসপ্লানেড কি গড়িয়াহাটের ফুটেই দেখেছি!
দীপু বলল— চুপ করে শুনবি। কমেন্ট করবি না। কাউকে বলবি না। আমি আজকাল একটা ভয়েস শুনতে পাচ্ছি।
—ভয়েস?
—ইয়েস। কখনও মনে হয়, আকাশ-বাতাস থেকে আসছে। কখনও মনে হয় ভেতর থেকে আসছে।
—কী বলছিস ছাতা?
—ছাতাও নয়, ছাই-ও নয়। এ ডিসটিংক্ট ভয়েস। কিছু বলছে। কী এখনও পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। ফিসফিসে তো! তবে আস্তে আস্তে বুঝতে পারব।
হঠাৎ আবার হা-হা করে হেসে দীপু আমার কাঁধে একটা থাবড়া মারল। তারপর ওর রোগা, বড় বড় চোখ, বেড়ে যাওয়া চুল, একমুখ পাতলা পাতলা দাড়ির ময়লাটে চেহারাটা দ্রুত আমার কাছ থেকে সরে গেল। আর পেছন ফিরে তাকাল না দীপু। যেন কেউ দেখে ফেলবে। আর তা হলেই সর্বনাশ। যেন একখানা সিক্রেট এজেন্ট।
আমি একটু হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ভয়েস? ভয়েস কী রে বাবা? হ্যালুসিনেশন হচ্ছে না কি দীপুর? বিশুদার ব্যাপারে তো বেশ ভাল কথাই বলল। সেন্সিব্ল। কিন্তু এ সব ভয়েস-টয়েস! এ তো পাগলামি! সর্বনাশ। ওর তো চিকিৎসা দরকার!
অন্যমনস্কভাবে সাইকেল বাই। যান্ত্রিকভাবে বেয়ে যাচ্ছি। লোকজন, গাড়িঘোড়া এড়িয়ে এড়িয়ে। মনটা দীপুতে নিবিষ্ট। শামু যেমন বন্ধু, গদা যেমন বন্ধু, পানু, সাম্য এরা যেমন বন্ধু, দীপুটাও তো তেমন আমার বন্ধুই! খুব ঘনিষ্ঠ নয়। দীপুদের ফ্যামিলি বরাবর কেমন আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো। মাসিমা যে পরের বাড়ি রান্না করেন, কি মুক্তা পার্লারে চুল ঝাঁটায়, কি ভুতো গাড়ি ধোয় এগুলো ওরা ভুলতে পারে না আমাদের সঙ্গে মিশতে এলে। আবার চক্কোত্তি বামুন, এক পুরুষ আগেও পুজো-অর্চনা করেছেন নিষ্ঠাভরে, এক ছেলে এম এসসি ড্রপ, আর এক মেয়ে ক্লাস টুয়েলভে উঠল ফার্স্ট হয়ে, এগুলোও ওঁরা ভুলতে পারেন না বস্তির সমাজের লোকেদের সঙ্গে মিশতে গেলে। বস্তির মধ্যে ওদের বাড়িটা যেন একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট। গেলে দেখি, সামান্য একটা দাওয়া, দাওয়ার পাশে রান্নার জায়গা। ভেতরে একটা ঘর। আর একটা এত ছোট যে তাতে কেউ থাকতে পারে বিশ্বাস হয় না। টিনের ঢাকনা দেওয়া একটা কলঘর। কিন্তু সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দাওয়ায় টবে ক’টা ফুলগাছ—রঙ্গন জবা এইসব বারোমেসে। ভেতরে তক্তপোশে পরিষ্কার চেক-চেক বেঙ্গল হ্যান্ডলুমের চাদর ঢাকা দেওয়া। কোথাও এতটুকু ধুলো ময়লা নেই। ছোট্ট ঘরটায় মণিমালা পড়ে। আমি মাঝে মাঝে ওকে এটা ওটা পড়া দেখিয়ে দিই। দেখেছি কী সুন্দর করে খবরের কাগজের মলাট দিয়ে বইগুলো গুছিয়ে-সাজিয়ে রেখেছে। একটি পেন, একটি পেনসিল, কয়েকটা লম্বা, লাইন ছাড়া খাতা। একটা লণ্ঠন। ঘরটাতে জানলা নেই বললেই চলে। যেটা আছে সেটা খুললেই পাশের কুঠুরির বাসিন্দাদের ঘরকন্না দেখা যায়। জানলাটায় একটা ছেঁড়া শাড়ির পর্দা দেওয়া আছে। কিন্তু পড়াতে গিয়ে দেখেছি, অনেক সময়ে ও-কুঠুরি থেকে এমন চিৎকার অকথ্য গালিগালাজ আর অসহ্য গন্ধ আসে যে মণি ওটাকে বন্ধই রাখে। এই ঘরেই রাতে দীপু আর ভুতো শোয়। বড় ঘরটাতে দুই মেয়েকে নিয়ে মা। কিন্তু ওঁদের বাড়ি গেলেই মাসিমা এত সংকুচিত হয়ে যান যেন ধরা পড়ে গেছেন। কিছু যেন লুকোচ্ছিলেন, লুকোনো হল না। মুক্তা থাকলে কথাই বলে না। মণিকে তারপর থেকে আমি বলেছি— তোমার দরকার হলে আমাদের বাড়ি চলে এসো বরং। মেয়েটা আসে। তবে খুব কম। খুবই বুদ্ধি ওর। আমার চেয়ে অনেক বেশি। পরিবারটার নানারকম দুর্দৈবর মধ্যে মণিমালাই একমাত্র পরিষ্কার মাথার ঠিক রেখেছে। অন্তত তাই আমার মনে হয়। এখন যদি দীপু এ সব ভয়েস-টয়েস বাধিয়ে বসে কে বলতে পারে নৈরাশ্য এ মেয়েটাকেও গ্রাস করবে কি না। বাড়ির আবহাওয়াই বা কেমন হবে! সে ক্ষেত্রে তো ফ্যামিলিটা ধসে যাবে একেবারে।
এইসব দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়েই বড় রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম। যাচ্ছি ছাত্র পড়াতে। হাতে এখনও একটু সময় আছে। তাড়াহুড়ো কিছু নেই। হঠাৎ নজর পড়ে গেল একটা মোটর পার্টস-এর দোকানে। সারি সারি সব টিনের প্লাস্টিকের কৌটো বা’টা সাজানো। চকচকে দোকান, বাইরে মোটা কাচের দরজা। ভেদ করে দেখা যাচ্ছে একটা চমৎকার সচিনের পোস্টার। বালক বালক নিষ্পাপ মুখখানা, টেস্ট-ক্রিকেটের ড্রেস পরা, হাতে ব্যাট, কিন্তু দেখা যাচ্ছে শুধু ব্যাটের আধখানা। নীল পটের ওপর আঁকা সচিন! ছবিটা দেখে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে গেলাম। আহা রে সচিন তুই তোর দেবদূত মুখ নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী হলি না কেন? অমন আন্তরিকতা, নিজের কাজে অমন মনোযোগ, পাঁচজনের সঙ্গে পা মিলিয়ে আবার নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে চলার শক্তি, নির্দ্বিধায় দক্ষতর ব্যক্তিকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া, বাজে আউট, আম্পায়ারের ভুলে বা বদমাইশিতে আউট হলেও অমন স্থৈর্য, কিন্তু প্রত্যয়, ব্যক্তিত্ব, এমন ক্যারিশমা যে বম্বের বিখ্যাততম নায়ককেও তোর পাশে ম্লান এবং খল দেখায়! রাজনীতি বুঝিস না, কিন্তু দলবাজি তো বুঝে গেছিসই! দে না বাবা ক’টা ছক্কা মেরে। এক একটাতে এই হতভাগাদের গড়া এক একটা পাপস্তম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে যাক। এক ছক্কায় জনগণের টাকা নিয়ে নয়ছয়, আর এক ছক্কায় জাতি-ধর্ম-বিদ্বেষ, আর এক ছক্কায় সরকারি ঘুঘুর বাসা… আর এক ছক্কায় বেসরকারি ঘুঘুর বাসা…
ঢুকে পড়লাম।
—কী চাই?
—সচিন।
—মানে?
—না, এই পোস্টারটা কোথায় পেলেন জিজ্ঞেস করছিলাম।
—ও আমাদের এক ক্লায়েন্ট দিয়েছে—একজন বলল।
আর একজন কীরকম খেঁকিয়ে বলল—খ্যানো বলুন তো!
দমে গিয়েছিলাম। তবু বলি— যদি কিছু মনে না করেন ন্যায্য দামে পোস্টারটা আমায় দেবেন?
—মামার বাড়ির আবদার না কি?—খেঁকি জন বললেন।
—না, না, মামার বাড়ি নয়। ভাইপোর। বাচ্চা তো! কোথাও জিনিসটা খুঁজে পাচ্ছি না। এদিকে সে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করার জোগাড়।
—ভাইপোকেই সামলাতে পেরে উঠছেন না। ছেলে হলে কী করবেন? ভালজন মৃদু হাস্যে বললেন।
মনে মনে আরও দমে গেলাম। সবে তেইশ। এখনই আমাকে পিতৃপ্রতিম দেখাচ্ছে না কি? ছেলে তো অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাচ্ছি না। যদ্দিন না হচ্ছে ভাইপোটাই ছেলে। ছেলের প্রতি স্নেহ-মমতা কেমন হয় তা যদিও আমার জানা নেই।
খেঁকি বললেন—আজকালকার বাচ্চাগুলো আর বাচ্চা নেই। টিভি দেখে দেখে টিভি দেখে দেখে এক একটি পাকা পক্কান্ন হয়ে উঠেছে।
এর মধ্যে পাকা পক্কান্নর কী হল বুঝতে পারলাম না। সে বেচারি তো আর ঋত্বিক রোশন কি ঐশ্বর্য রাই চায়নি।
—দেবেন নাকি? বাচ্চাটার কথা মনে করে? কত দাম বলুন। আমি পার্স বার করি।
—দাম নেই।
—মানে? অমূল্য?
—হ্যাঁ তাই। আমার দেয়ালের জিনিস আপনাকে দিতে যাব কেন খামোকা? এর পরে আরেকজন এসে বলবে—বাঃ আপনাদের গাছদানটা তো বেশ, আমার ভাইঝি ঠিক এইরকম একটা চায়…
আমি আর দাঁড়াই না। সচিনের ছক্কা এদের জন্যেও দরকার। এই মায়া-মমতাহীন সভ্যতা-ভদ্রতাহীন দোকানদার সমাজ। পুরো সমাজটাই দোকানদার হয়ে গেছে। পুরো দেশটাই। আমি বলছি না আমি ছোট বাচ্চার নাম করে কিনতে চাইছি বলেই ওরা আমাকে জিনিসটা দিয়ে দিক। কিন্তু কথাবার্তা বলারও তো একটা ধরন আছে। আমাদের ওরা চ্যাংড়া বলে, আমাদের মুখের ভাষাকে স্ল্যাং বলে, ওদের তো একজনের চুল বেশ পাকা আরেকজনের গোঁফেও পাক ধরেছে, ভদ্রভাবে কথা বলতে কী দোষ! বাবা মৃত্যুর আগে একটা কথা খুব বলতেন। বলতেন— এতদিন ধরে সমাজ চলেছে মোটামুটি ভারতীয় আদর্শে। অল্পে সন্তুষ্ট থাকো, সন্তোষ এবং শান্তিটাই আসল। গুরুজনদের শ্রদ্ধা করো, নিজের কাজটুকু মন দিয়ে করো, অবসর সময়ে ঈশ্বরচিন্তা করো। উপার্জন যদি খুব বেশি করো, তা হলে উদ্বৃত্তের কিছুটা দান করো। অতিভোগ ও শোষণের প্রক্রিয়া তখনও ছিল, কিন্তু আদর্শটা ছিল এই। দীর্ঘদিনের ইংরেজ-রাজত্বেও জনসাধারণ মোটের উপর এই আদর্শটাকেই পালনীয় এবং উৎকৃষ্ট বলে জানত। কে কতটা পালন করত সেটা আলাদা কথা। কিন্তু নতুন যে আদর্শটা আসছে সেটার ঝোঁক ভিন্ন জায়গায় পড়তে যাচ্ছে। ভূমা চাও, আত্মিক বা আধ্যাত্মিক ভূমা নয়, সাংসারিক ভূমা, বৈষয়িক ভূমা। চাহিদাটা বাড়াতে থাকো, আকাঙক্ষা কোথাও থামবে না। গুরুজনদের ছেড়ে কাউকেই শ্রদ্ধা করার দরকার নেই। যার সঙ্গে যে-রকম আদান-প্রদানের সম্পর্ক তেমনই করো, নিজের কাজ অবশ্যই মন দিয়ে, রক্ত দিয়ে মজ্জা দিয়ে করবে কিন্তু কাজের আনন্দে নয়, পাওনার আনন্দে। অবসর সময় বিনোদনে কাটাও। নিজের প্রবৃত্তির নিম্নতম খেয়াল খুশিকেও মর্যাদা দাও এই সময়টায়, তা নয়তো চাপ সামলাতে পারবে না। ঈশ্বর নেই। তা সত্ত্বেও যদি ঈশ্বরচিন্তা করলে তোমার বিনোদনের কাজটা হয়ে যায়, অর্থাৎ চাপটা কমে তা হলে করো। অর্থাৎ ঈশ্বর একটা কনভিনিয়েন্স। আর উদ্বৃত্ত? আরও কেনো, আরও ভোগ করো। শেষ পর্যন্ত ওই ফ্যালো কড়ি মাখো তেল। একটা দোকানদারি সমাজ-ব্যবস্থা।
আমরা অর্থাৎ আমি আর দাদা নিজেদের তালে থাকতাম। কে আর অত বাবার কথায় কান দেয়। কিন্তু বাবা অনেক সময়েই রাত্তিরের খাওয়ার সময়টা বাছতেন। মাকে উদ্দেশ করে বলতেন। বলতেন—একটা টোট্যাল চেঞ্জ অফ্ অ্যাটিচিউড। সেইটার সঙ্গে মানিয়ে তোমাদের প্রতিদিন চলতে হবে। আরও খাটো, আরও চাও, আরও কেনো—এই ফাঁদে পড়ে গেলে মহা মুশকিল। কেন না, প্রত্যেক মানুষের ক্ষমতা আলাদা, এবং সে ক্ষমতার সীমা আছে। এই সীমা খানিকটা বাড়ানো যায়। কিন্তু কোনও না কোনও জায়গায় থামতে জানতেই হয়। এবং থেমে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।
দাদা বলত—বাবা তুমি কতকগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট কথা বলে গেলে। চেঞ্জ তো হবেই। সারা পৃথিবীতে চেঞ্জ হচ্ছে। তুমি কি বলো সেই পুরনো ভারতবর্ষের দীনতা, বিনয়, শ্রদ্ধার আদর্শ যা দুর্বল ছাড়া কেউ মানত না সেটাই ভাল।
—না, তা আমি বলছি না। যদিও সেই আদর্শটার সামগ্রিক দোষগুণ বিচার করার ক্ষমতাও আমার নেই। কেন না আমিও ওই ব্যবস্থাটার প্রোডাক্ট। যেমন পেরেছি, যতটা পেরেছি মেনেছি। ধরো আমার বাবা মা খুব শোকাতাপা মানুষ ছিলেন, নিজের মাতৃভূমি, ভিটে, সন্তান ভয়াবহ ভাবে হারানোর দুঃখ কোনওদিন ভুলতে পারেননি। যে-জমির ওপর আজ আমাদের বাড়ি, তা কিন্তু সোজা কথায় চুরি। তাঁরা নিরুপায় হয়ে কোণঠাসা হয়ে তাঁদের অবস্থার আরও অনেকের মতো খালি জায়গা পেয়ে দখল করে নিয়েছিলেন। তাঁদের ওপর অন্যায় হল, তাঁরা অন্যদের ওপর অন্যায় করলেন, কিন্তু এই অন্যায়ের জন্য আমি মনের কোণেও তাঁদের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা পুষে রাখিনি। ‘বেশ করেছি, খুব করেছি’ এমনটাও কিন্তু আমি মনে করি না। পুরো ব্যাপারটাই খুব আনফরচুনেট। আমি দুঃখ পাই। কিন্তু তোমরা যেটা ফেস করতে যাচ্ছ সেটা অন্য রকম। ধরো তুমি, তোমরা মহাজনদের বিরাট প্রাসাদ, লোকজন, গাড়িজুড়ি দেখছ, দেখতে দেখতে মনে স্থির সংকল্প গড়ে উঠছে তোমাকেও অমন পেতে হবে। তোমার যা ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ ব্যবসা করা বা কোনও প্রযুক্তিগত বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা, তোমার নেই, অর্থাৎ তুমি কোনও ছোটখাটো বিড়লাঘরেও জন্মাওনি, বিল গেটস-এর ক্ষমতাও তোমার নেই। অথচ বাসনাটা তোমার প্রচণ্ড, সেটা তোমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এখন হয় তুমি কী করে ইজি মানি করা যায় তার হদিশ করবে, করতে করতে গাড্ডায় পড়ে যাবে, আর নয় তো হতাশা, ফ্রাসট্রেশন, ক্রোধ, অশান্তি—এই-ই তোমার সমস্ত জীবন। এটা কি কাম্য হতে পারে! এই অভিশপ্ত জীবন তো এড়ানোও যায়। মানুষের মনের মধ্যে এত লোভ ঢুকিয়ে দিতে নেই।
পাড়ায় ঢুকছি। গদাইদের বাড়িটা পড়ল, আশ্চর্য হয়ে দেখি দীপুর মা ঢুকছেন। উনি তো গদাইদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তারপরে বুঝি—আশ্চর্য হবার আর কী আছে! গদাইদের কাজ উনি কোনও মনোমালিন্য করে ছাড়েননি। বোঝাই যাচ্ছে সম্পর্ক ভাল আছে। মহাজনদের রান্না সেরে বাড়ি ফিরছেন। খবরাখবর নিতে গদাইদের বাড়ি হয়ে যাচ্ছেন। অন্য দিকে তাকিয়ে দেখি—গুহ মজুমদারদের মাল্টিস্টোরিডের খাঁচা হয়ে গেছে। ঢালাইও শেষ। এখন রাজমিস্ত্রির কাজ হচ্ছে। হাতে হাতে ইট উঠে যাচ্ছে, কামিনরা মাথায় সিমেন্টের কড়া নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে রিলে শুরু করেছে। একটা কেমন ছন্দ, যেন মৃদু দোলের কোনও নাচ। সেই ঠিকেদার চাকলাদার আসছে দেখি মোটরসাইকেল দাবড়ে। হেলমেট খুলে বাঁ বগলে নিয়েছে কায়দা করে, আপাদমস্তক দেখছে বাড়িটার। একটা হিরো হিরো ভাব। আমাকে দেখে এগিয়ে এল।
—কী হল সাহেব কোথায় চললে?
—বাড়ি ফিরছি।
—কিছু পেলে?
—কী পাব?
—নাঃ কাজ-কারবার নিশ্চয়ই খুঁজছ…
আমি কোনও জবাব দিই না, দাঁড়িয়ে থাকি।
—বসেই আছ, কোয়ালিফায়েড ছেলে, আমার একটা উপকার করবে নাকি?
—মানে?
—যদ্দিন না পার্মানেন্ট কিছু পাচ্ছ এই সাইটটা যদি একটু সুপারভাইজ করো…
শুধুই উপকার না পেইড উপকার বুঝতে পারলাম না। এমন কথার ধরন এদের!
—ধরো বেসমেন্টে একটা অফিস আছে, সেখানেই বসবে, প্ল্যানট্যান সব তোমার টেবিলে থাকবে, এভরিথিং …একটা হিসেব…
যাক, শুকনো পরোপকার টাইপ নয়, আমদানিও আছে।
বলি,—আমি কখনও করিনি।
—করোনি তো কী! করতে আরম্ভ করলেই শিখে যাবে। আমি তোমাকে মাসে পাঁচ হাজার করে দেব।
আমি হেভি চমকাই। বলে কী রে লোকটা? কোনও ট্রেনিং নেই। এক্সপিরিয়েন্স নেই, পাঁচ হাজার?
—কেন? এতদিন কি আপনার সুপারভাইজার ছাড়াই চলছিল?—জিজ্ঞেস করি।
—আর বলো কেন? এসব লাইনে সবসময়ে লোকে কাজ নিচ্ছে, কাজ ছাড়ছে। আমার কাছে যে ছেলেটি মানে লোকটি কাজ করছিল, সে বোধহয় অন্য কোথাও বেটার অফার পেয়েছে। আমি একটা বিশ্বাসযোগ্য লোক পাচ্ছি না। ঠিক আছে, পাঁচ হাজারটা যদি তোমার খুব কম মনে হয়, আরেক হাজার তোমার এবং তোমার ফ্যামিলির রেপুটেশনের খাতিরে বাড়িয়ে দিচ্ছি।
—আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন। —আসলে আমায় ভাবতে হবে এ মাকড়া হঠাৎ এত টাকা ছড়াচ্ছে কেন!
—যা বাব্বা আবার ভাবনা কেন? আমি কাজ কারবার ছেড়ে এখানে প্রায়ই আসতে পারি না। কী যে করছে এরা ভগবান জানেন। তুমি তাড়াতাড়ি মানে কাল পরশুর মধ্যেই জানিও। কাছেপিঠের লোক হলে কী হয় জানো? দুপুরবেলা টুক করে বাড়িতে খেয়ে আসতে পারবে।
এই বাড়িটার পাঁচিলেই ভিখারি চাপা পড়েছিল। অনেক দিন মানে দু’-তিন বছর হয়ে গেল বন্ধই ছিল। বোধহয় এ বার সব কেস-টেস ক্লিয়ার হয়ে গেছে। হুড়হুড় করে কাজ হচ্ছে। তবে চাকলাদার ছিল স্রেফ কনট্রাক্টর। এই ক’বছরে সে কি প্রোমোটারও হয়ে গেল? বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলাম মন্দ কী? জীবিকাটার সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। ঠিকই। কিন্তু আমাকে তো কিছু না কিছু ধরতেই হবে। সব জীবিকা সম্পর্কেই আমার একটা কৌতূহল আছে। কী করে কী হয়। আমার বি কম ক্লাসের এক বন্ধু তমোনাশ তো অটো চালাচ্ছে। হাতদুটো কালো হয়ে থাকে ডিজেল আর রাস্তার ধুলোয়। চুল সব সময়ে উড়ছে, এলোমেলো খড়কুটো। স্কুটার থামিয়ে ওই কালো হাতে রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল খাচ্ছে দেখি। আমায় দেখে বলল—টেপ তো একটু, হ্যান্ডলটা মার। একটু জল খেয়ে বাঁচি।
আমি বললাম—হাতটা ধো। ওই হাতে জল খাবি কী রে। গাড়িতে একটা বোতল কিংবা গ্লাস রাখলেও তো পারিস।
—রেখেছিলাম রে। নাচতে নাচতে বেরিয়ে চলে যায়।
—তো সাবান!
—এটা ভাল বলেছিস। রাখতে হবে। তবে কী জানিস—লাইফটাই এখন ডিজেল হয়ে গেছে। চড়বি নাকি?
—চল।
তখন রাত আটটা হবে। ভাগ্যক্রমে আমার দু’চাকার বাহনটি আমার সঙ্গে ছিল না! তাই কত কথা জানতে পারলাম। তমোনাশটা একটু ডাকাবুকো মতো ছিল। খেলাধুলো করত। চাকরি-বাকরি না হতে ওর বাবার এক বন্ধু অটোর পরামর্শটা ওকে দেন। লোন নিয়ে কিনেছে। দিনে সব খরচ-খর্চা বাদ দিয়ে শ তিনেক মতো হয়। মানে মাসে ন’হাজার। এত খেটে ন’হাজার, রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা, পুলিশের পাবলিকের গালাগাল। ময়লা, নোংরা। এর তুলনায় নির্মীয়মাণ বহুতলের বেসমেন্টের অফিসে বসে বসে হিসেব নিকেশ, মাঝে মাঝে অকুস্থলে গিয়ে কাজকর্ম দেখে আসা, মাসে ছ’হাজার! এ তো সোনার চাকরি! আকাশ থেকে টাকার থলি পড়া যাকে বলে। তারপর আবার নিজের বাড়িতে দুপুরবেলায় অফিসারদের মতো লাঞ্চ খেতে যাওয়া।
—তমোনাশ সাবানটা ভুলিস না! হাতে গ্লাভস পরলেও পারিস।
—কথাটা মন্দ বলিসনি। সাবান! ঠিক। গ্লাভস? অলরাইট। দু’ লেনের দুটো ট্যাকসির মাঝখান দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় নিজের তিন চাকা গুঁজে দিয়ে, বাঁদিকের লেনে এসে মোড়ে আমায় নামিয়ে দিল তমোনাশ—দেখা হবে, রণধীর…
হ্যাঁ আবার। —মুহূর্তের মধ্যে তমোনাশের অটো ভ্যানিশ।
৪
—কাকু, সচিন?— রিন্টি এমন করে বলল যেন সচিনকে ও নেমন্তন্ন করেছিল, আমার তাকে নিয়ে আসার কথা। মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল সচিন এল না, একটু ছুটি পেয়েছে, ফ্যামিলি নিয়ে অ্যান্টার্কটিকায় বেড়াতে গেছে।
বললাম— খুঁজছি তো, না পেলে কী করব বল।
—তুমি ভাল করে খুঁজছ না।
রিন্টির মা এসে তাকে এক ধমক দিল—কাকু চাকরি খুঁজবে না তোমার সচিন খুঁজবে?— খাইসে, বউদি মর্নিং স্কুলে পড়ায়। এসে গেছে।
বললাম—বউদি একটা কথা আছে।
—কী কথা? ব্যাঙের মাথা?
মা বলল—যা দিকিনি চান করতে যা, চান করে বেরোলেও তো পারিস। আমি আর তোর ভাত আগলে বসে থাকতে পারছি না।
—কে তোমাকে ভাত আগলে বসে থাকতে বলেছে?
মা কোনও জবাব দিল না। রান্নাশালের দিকে চলে গেল।
বউদি বলল—কী ব্যাং? সোনা ব্যাং না কোলা ব্যাং?
—একটা টেম্পোরারি কাজ পাচ্ছি। সোনা ব্যাং-ই বলতে পারো।
—সত্যি? বউদির চোখ চকচকে হয়ে উঠল অমনি।
—ছ’হাজার টাকা মাইনে।
—স্টার্টিং? সত্যি?—বউদির চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।
—আজ্ঞে। দেখো, আবার জ্বলতে আরম্ভ কোরো না।
—সত্যি? বলো না বাবা!
—আঃ, বললাম না টেম্পোরারি! কনসলিডেটেড।
—বলিস কী রে রুণু! বউদি এক পাক নেচে নিল। ফার্স্ট মাসের মাইনে পেয়ে আমাকে একটা সিল্ক বমকাই কিনে দিস।
—কত দাম?
—হয়ে যাবে, ধর হাজার চারেক।
আমি গম্ভীর হয়ে বলি, মাত্র? আর কিছু না?
—আর কিছু কী করে হবে বল। দু’হাজারে কি কানের কিছু ভাল হবে? আর একটু অ্যাড করতে হবে। তোর টিউশনির টাকা থেকে…
আমি মাথায় নারকোল তেল ঘষতে ঘষতে বলি—অত টক খেয়ো না। ছ’হাজার টাকার চাকরিও করব, আবার বাড়ি-বাড়ি ছাত্র পড়াতেও ছুটব। ও গুড়ে বালি।
—বা, বা, বা—এতদিন যে খাওয়াচ্ছি। পরাচ্ছি।
—পরাচ্ছ না। শুধু খাওয়াচ্ছ, ভাত, আলুসেদ্ধ, খেঁসারির ডাল, আর কলার বড়া।
—মারব এক থাবড়া রুণু। খেঁসারির ডাল কেউ খায়?
—কেউ না খেতে পারে, তোমরা খাও। তোমরা যদি না খাও—বেকার দেওরকে খাওয়াও। বউদি এবার এক হাত তুলে তেড়ে আসে।
মা না এসে পড়লে ঠিক একটি থাবড়া জুটত।
মা বললে—কী হচ্ছে রুণু?
—অমনি ‘কী হচ্ছে রুণু?’ কেন ‘কী হচ্ছে টুকু’ও তো বলতে পারতে! একচোখোমির কমপিটিশন হলে ফার্স্ট প্রাইজ পাবে।
—যা চান করে আয়।
চান করতে যাচ্ছি বউদি বলল—সত্যি? ভড়কি দিচ্ছিস না তো!
—আমার ঘাড়ে ক’টা মাথা?
চান করতে করতে অবশ্য আমার মনে হল টিউশনিগুলো না-ছাড়াই ভাল। চাকলাদারের বাড়ি কিছু অনন্তকাল ধরে হবে না। যে রেটে এগোচ্ছে তাতে হয়তো মাস ছয়েকের মধ্যেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। হয়তো সেইজন্যেই ছ’ হাজার ছড়াচ্ছে। তদ্দিনে আমার খানিকটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু ছ’ মাস ফুরোবার মাথায় মাথায় ঠিক এই চত্বরেই আরেকটা মাল্টিস্টোরিড হবে কী? ‘নির্মীয়মাণ বহুতলের জন্য অভিজ্ঞ সুপারভাইজার চাই’—এরকম কোনও বিজ্ঞাপনও তো… নাঃ চারটে মাত্র টিউশনি, গড়ে দেড়শো করে ছ’শো টাকা। এটা স্টপ করা ঠিক হবে না। সবগুলোই সন্ধেয়। কাজেকাজেই আমি দিনের বেলায় সংসারের খেপ খাটি। তা সেইটে হবে না।
মা কিন্তু শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। রান্নাঘরের সামনে একটা ক্যারমবোর্ডের মতো চৌকো জায়গা আছে। সেইখানে কেরোসিন কাঠের এক চারপেয়ে টেবিল আর চারটে লাল রঙের প্লাস্টিকের চেয়ার। মা মুখে গরস তুলতে গিয়ে থেমে গেল আমার ভাল খবর শুনে। তারপর গরসটা খেয়েই নিল। বোধহয় খুব খিদে পেয়েছে। কয়েক গরস খেয়ে বলল— ভাল করে ভেবে দেখেছ!
—কেন বলো তো! এর মধ্যে ভাবাভাবির কী আছে?
—সেই ভিখিরি চাপা পড়ার ঘটনাটা ভুলে গেছ বোধহয়।
—হ্যাঁ, তো তার সঙ্গে কী!
—তুমি যে ঘরটায় বসে কাজ করবে সেটাও ভেঙে পড়তে পারে। ভেঙে পড়ার চান্স আছে বলেই হয়তো লোকটা অত দিচ্ছে।
—সে ক্ষেত্রে তোমরা একটা বিরাট টাকা কমপেনসেশন পাবে। জগাদা-বলাদা-বিশুদা-অরবিন্দদা সব্বাই তো রয়েছে। কমপিটিশন করে টাকা বার করে দেবে।
মা’র মুখটা মুহূর্তে ভিমরুলের চাকের মতো গোমড়া হয়ে যায়।
আমি বলি—আচ্ছা মা, সেটা ছিল একটা পাতলা কাঁচা দেয়াল। জাস্ট জমিটা ডিমার্কেট করে রাখার জন্যে তোলা। হাফ পাঁচিল। এখন পুরো স্ট্রাকচারটা মানে ঢালাই টালাই সব শেষ। এখন জিনিসটা ভেঙে পড়বে?
—প্রদীপ কুণ্ডলিয়ার কেসটা বোধহয় তোমার মনে নেই। বেশ ছোট তখন তুমি। কিন্তু ল্যান্সডাউন রোডে যে একটা বহুতল ধসে ফ্যামিলিকে ফ্যামিলি সাবাড় হয়ে গেল, সে তো তোমার দেখার মধ্যে। সে-ও একদিনে হয়নি। কয়েক বছর বাস করবার পর হয়েছে।
—তুমি তো দেখছি সেই শরৎচন্দ্রের বিন্দুর মতো হলে। ছেলেকে পাঠশালে পাঠাবে না, ছোটটি পেয়ে যদি কেউ চোখে কলমের খোঁচা দিয়ে দেয়! সত্যি মা! দেখালে বটে!
—কী জানি বাবা, যা ভাল বোঝো করো। জীবনে তো কোনওদিন সুখ বলে জিনিস জানিনি, এখন তোমাকে নিয়ে আমার শান্তিটুকুও গেল। তপু কী ভাগ্যি পাশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি পেয়ে গেল, চাকুরে বউও ঘরে আনল। তাই, নইলে…
এইবার আমার রাগ হয়ে যায়। বলি—বেশ আমার না হয় সে ভাগ্য হয়নি, চাকুরে বউ একটা জোটাতে পারি অবশ্য। তাতে হবে?
মা সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত চোখ তুলে বলল—কেউ আছে?
—উঃ তুমি না! নেই। কিন্তু বিয়ের লোভে চাকুরে মেয়েরা আজকাল বেকারকেও বিয়ে করছে। এটাও একটা হিল্লে। তবে বউটি তোমার শান্ত, সুকুমারী, ছেলেমানুষটি নাও হতে পারে। হয়তো জাঁদরেল পোস্টাপিসের কেরানি। আমার থেকে বছর পাঁচ সাতের বড়। আমাকে একবার ‘রুণু—উ-উ’ বলে হাঁক ছাড়লে আমি পটোল তুলব। তোমাকেও…
—থাক থাক হয়েছে—মায়ের মুখে একটা ক্ষীণ হাসির আভা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। মা বললে—দ্যাখ পোস্টাপিসের কেরানি-টেরানি বলে অমন করে মেয়েদের সম্পর্কে বলবি না। এইসব মেয়েরা সংসারের অ্যাসেট তা জানিস? দশ হাতে দশ দিক সামলায়। তোর মতো চ্যাংড়াকে বিয়ে করতে তাদের বয়েই গেছে।
—সঙ্গগুণে তোমার অনেক চেঞ্জ হয়েছে মা। লাস্ট সেনটেন্সটা তো একবারে বউদির স্টাইলে বললে!
মা বলল—কে কাকে চেঞ্জ করে! এসব ভ্যালুজ আমার নিজের জীবন দিয়ে শেখা। তপু যখন টুকুকে নিয়ে এসে দাঁড়াল, টুকু ছিল কড়ে আঙুলের মতো রোগা, মুখ চুপসোনো এতটুকু, এতটুকুনি সে মুখ কালো না ফর্সা কিছুই বোঝা যায় না। তপুর পাশে একেবারে বেমানান। আদর করে ঘরে তুলিনি? কোনওদিন কারও সঙ্গে বউয়ের রূপগুণ নিয়ে গুলতানি করেছি? আজ যে তোর বউদি এমন গোলগাল, শ্রীছাঁদ অলা দাঁড়িয়েছে সে কার যত্নে? কেন যত্ন? ভ্যালুজ ছিল বলেই না? নিজেরও ছিল, তোর বাবারও ছিল, মেয়েদের মা জ্ঞান করা, শক্তি, ভাগ্য বলে গণ্য করা।
—দোহাই মা আর শক্তিটক্তি হয়ে কাজ নেই। ঠিক আছে আমি তক্কেতক্কে থাকব। তেমন তেমন কালোকোলো রোগাসোগা চাকুরে মেয়ে পেলে তোমার ভ্যালুজ প্রমাণ করবার জন্যে এনে ফেলব। কিন্তু উইদাউট নোটিস।
মা এমন করে আমার দিকে চেয়ে রইল যেন হিপনোটাইজ করে পেটের কথা জেনে নেবার চেষ্টা করছে।
আমি আর দাঁড়াই না। হাসি চেপে বাইরের ঘর। মা যতই বলুক কে কার থেকে শেখে ‘তোর মতো চ্যাংড়াকে’ ‘গুলতানি’এসব বউদি ব্র্যান্ড। মা বউমার দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাবিত হয়ে পড়ছে।
আর হবে না-ই বা কেন? বউদি আমাদের ঘরে ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোচ্ছে। এল যখন কী সলজ্জ, কী ডিফিডেন্ট, যেন কালো মেয়ে হয়ে ফর্সা ছেলেকে পাকড়ে মরমে মরে আছে। সব্বাই একধার থেকে বলতে লাগল কী চমৎকার বউ! যেমন ব্যবহার তেমন কাজকর্ম। ভোরবেলা স্কুল যাচ্ছে, স্কুল থেকে ফিরে মাস্টারির খোলস খুলে রেখে ঘরের লজ্জাবতী লতা, দাসানুদাসী। খালি আমার দিকে তাকিয়ে যখন ঘোমটার ফাঁকে ফিক ফিক হাসত, তখন আমার একটা ধন্দ জাগত মনে। শিরদাঁড়া দিয়ে হিমস্রোত বয়ে যেত। তারপর একদিন বাবাই ডেকে বললেন— বউমা, তুমি কি আমাদের বাঘ-ভালুক কি বেগার খাটানো মধ্যযুগীয় জমিদার মনে করো?
—না তো। কেন বাবা! যেন ভীষণ ইনোসেন্ট কিচ্ছু বুঝতে পারছে না।
—না তাই বলছি। হ্যাঁগো তপু-রুণুর মা, বউমা যদি ওর ঘোমটাটুকু খুলে ফেলে তোমার কোনও আপত্তি হবে?
মা বলে— আমার? আমি নিজেই কত ঘোমটা দিই! শাশুড়ি বেঁচে থাকতেই দিইনি! এখন বাইরে বেরোলে বড়িখোঁপা নিয়ে লজ্জা করে তাই একটু কাপড় ছুঁইয়ে রাখি মাথায়।
অমনি বউদি বললে—বড়ি কোথায় মা, আপনার কী সুন্দর মাথা সাজানো ঢেউ খেলানো চুল। আজকাল তো ছোট চুলই ফ্যাশন। লম্বা চুল কেউ রাখছে না আর। তার ওপর অত সুন্দর ব্রাউন রুপোলি কালার। এরকম তো আজকাল ডাই করে করাচ্ছে মেয়েরা।
ব্যাস বউদির পয়েন্ট পাওয়া শুরু হয়ে গেল। আমার মাতৃদেবী তো কোন ছার, আশি বছরের বৃদ্ধাকেও রূপের প্রশংসা করলে নিদন্ত মুখে এক মুখ হাসি ফুটে ওঠে। ও আমার দেখা আছে।
আমার সঙ্গে বউদির কনফ্রন্টেশনও শুরু ওখান থেকেই। একা পেয়ে বললাম—খোশামোদ করে হাত করে নিলে শাশুড়িকে, অ্যাঁ?।
—ও মা! খোশামোদ! খোশামোদ কোথায়! কী জানো রুণু, মায়ের রূপ, তাঁর চোখ চুল, নাক মুখ ছেলেদের আলাদা করে চোখে পড়ে না। মা মানে মা, যিনি হলেন…
আমি বলি—অরূপরতন।
—এইবারে একটা কথার মতো কথা বলেছ।
—আমাকেও হাতাবার চেষ্টা করছ।
—তোমাকে! দ্যাখো রুণু অন্যায্য কথা একদম বলবে না, আমি একজন সৎ শিক্ষয়িত্রী। ওসব আমি সইতে পারি না। কথাটা ভাল বললে তাই বললাম।
—যদি তোমাকে কালোমানিক বলি! সত্যি কথা তো! সইতে পারবে?
বউদি একটু করুণ মতো হেসে (সব চাল) বলল—মানিক কেন? কালোই বলো না, শুধু কালো, ধরো কেলেকুষ্টি কি রক্ষাকালী! আমি কিচ্ছু মনে করব না, সত্যেরে লও সহজে—কবি তো বলেই গিয়েছেন।
আমিও অত সহজে হারি না, বলি—মানিক লেগেছে তাই মানিক বলেছি। সত্যি কথাই বলেছি। আমিও সহজে মিথ্যে বলি না। তবে অপ্রিয় সত্যও আমি সাধারণত অ্যাভয়েড করি।
ঠিক আছে বাবা, মায়ের এত ভয়, চাকলাদারকে একবার বাজিয়েই নিই। যেন না ভাবে বেকার হাতে চাঁদ পেয়েছে।
পরদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সাইটে হাজির হয়ে গেছি। চাকলাদার একেবারে বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা। মুখের তলায় বাটি ধরলেই হয়।
—আরে এসো, এসো সাহেব।
আমি মাথা চুলকে বলি—একটা অসুবিধে হচ্ছে যে!
—কী অসুবিধে? চাকলাদার একই সঙ্গে ত্রস্ত এবং বিস্মিত। ছ’ হাজার টাকা নিলাম হেঁকেও জিনিস ঘরে উঠল না, এমন একটা হতাশ ভাব।
যাক, একজন চাকুরিদাতাকে অন্তত মাথা নত করে দাও হে করতে পেরেছি। লোকটা বেশ বিপদে পড়ে গেছে। যে-কোনও কারণেই হোক।
—মানে… আপনার এই সাইটেই তো দু’জন কনস্ট্রাকশন চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। তাই…বাড়িতে…
—সব্বোনাশ! সে কী কথা! পাঁচিল ছিল ল্যান্ড-ওনারের। আমার করা নয়। ঝুরঝুরে ঘুণধরা হয়ে গিয়েছিল। ল্যান্ড-ওনারের পাঁচিল, শাস্তি খেলাম আমি। এতদিন কোর্ট কাছারি! এখন এটা হচ্ছে সেন্ট পার্সেন্ট পারফেক্ট ইয়াং ম্যান, তোমার মাকে বোলো তোমার সেফটির ভার আমার ওপর। বলেন তো যে ক’দিন এখানে কাজ করবে—একটা মোটা টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স করে দিই। কী, দিতে হবে নাকি?
বলে কী লোকটা! তবে আমিও শেয়ানা আছি। আমি গম্ভীরভাবে বলি—আমার মা লাইফ ইনশিওর চান না, লাইফ শিওর চান।
—হাঃ হাঃ হাঃ হা। তুমি তো বেশ কথা বলতে পারো!
মাস্টারমশাই যেমন ভাল ছেলের পিঠ চাপড়ে দেন, তেমনি অবিকল।
কেন যেন ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটার ভাঙা নাকটা আচ্ছাসে মলে দিই। কেন যে এই ইচ্ছে! ফ্রাসট্রেশন থেকে বোধহয়।
বললাম, আমি তো অর্ডিনারি কমার্স গ্র্যাজুয়েট। একজন ম্যাথস অনার্স নিয়ে এম এসসি পড়া ভাল ছেলে আমার চেনা আছে। ট্রাই করে দেখবেন নাকি?
চাকলাদার হাঁ হয়ে বলল—তুমি তো আচ্ছা পরোপকারী ছেলে সাহেব? এমনটা আজকালকার দিনে দেখা যায় না—যা-ই বলো। তা ছেলেটি কে?
—দীপন চক্রবর্তী—ও-ই দিকে থাকে। খুব ভাল…
—দীপন-দীপন… মানে ওই ঝাঁকড়া চুল চশমাপড়া ছোকরা হাওয়াই চটি ফটাস ফটাস করে ঘোরে।
ঠিকই ধরেছেন ভদ্রলোক।
আমি বলি—হাওয়াই চটি কিন্তু ফটাস ফটাস করা যায় না, ধপাস ধপাস কি থপাস থপাস মতো আওয়াজ বেরোয়।
—রাইট য়ু আর। তোমার অবজার্ভেশন আছে। ছেলেটা চটিটা আগে ছুড়ে দেয়। তারপর আসে পা-টা।
—আপনার অবজার্ভেশনও খারাপ নয়, আমি বলি। —ও-ই।
—ও ম্যাথসের এম এসসি নাকি?
—এম এসসিটা পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।
—ফেল!
—উঁহু, বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায় বেকায়দায় পড়ে যায়।
—তোমারই বন্ধু, বলছ, ভাল ছেলে, এখনও চাকরি পায়নি?
—নাঃ!
—কিন্তু ও তো পাগলা!
অর্থাৎ দীপুর ‘পাগলা’ বিশেষণ অলরেডি জুটতে শুরু করেছে?
আমি বলি—অঙ্কের লোকেরা অমন একটু উদাস-উদাস, ভুলো স্বভাবের হয়ে থাকে। কাজের বেলায় পারফেক্ট।
—ভুলো মন নিয়ে আমার কাজ করবে কী করে?
—আমি বলছি—পারবে। এখন আপনি রাখবেন কি না রাখবেন সেটা আপনার চিন্তা।
—বাপস্ তুমি তো খুব…
—উদ্ধত!
এতটা জিভ কেটে চাকলাদার বলল—তাই কি আমি বলতে পারি! বলছি খুব প্র্যাকটিকাল। কথা বলতেও পারো। তো দ্যাখো তোমার বন্ধুটিকে আমি ঠিক মানে একলা রাখতে সাহস পাচ্ছি না। এক কাজ করো না, দু’জনে মিলে কাজটা করো, সুবিধেও হবে। ও অঙ্ক তুমি অ্যাকাউন্টস! বোরও লাগবে না… হ্যাঁ তবে স্যালারিটা কিন্তু শেয়ার করতে হবে।
—ন্যাচারালি!
—তা হলে ওই কথাই রইল। কাল থেকেই কিন্তু জয়েন করো। আমি ক’দিন পর একটু বাইরে যাব। তার আগে সব বুঝিয়ে দিতে চাই।
দীপুর কথাটা আমি ভেবে বলিনি, বিশ্বাস করুন। দীপুকে দেখে-দেখে আমার ফ্রাসট্রেশন বেড়ে যায়, একশো বার ঠিক। কিন্তু তাই বলে আমাকে অফার করা সাধা চাকরি আমি দীপুকে দিয়ে দেব, এতটা উদারচেতা পরহিতৈষী টাইপ আমি মোটেই নই। কীরকম একটা ইনস্টিংক্ট আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিল যেন। কেন, কী বৃত্তান্ত অত ভেবে ভেবে কূল পাইনি। ছ’ হাজারটা নিমেষের মধ্যে তিন হাজার হয়ে গেল। ভেতরটা করকর করছে ঠিকই, কিন্তু কেমন একটা স্বস্তি। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল একটা কথা আছে না। টাকাটা সুখ, আর এই ফিলিংসটা সোয়াস্তি।
দীপুর খোঁজে যাওয়া দরকার এখন। কোথায় থাকতে পারে? বিশুদার লাইনে আছে? না সেই ঝুপসি গাছটার তলায়…
দুটোই খুঁজে এলাম, পাত্তা নেই। বাড়িতে গেলাম। তালা দিয়ে বেরোচ্ছে মুক্তা।
—কী মনে করে? মুক্তার কথাবার্তা সবসময়ে কাটা-কাটা, কাঠ-কাঠ।
—দীপু কোথায়?
—জানি না।
—ভেতরে নেই?
—তালা দিয়ে রাখবার অবস্থা এখনও হয়নি।
বাব্বাঃ! বলে কী?
—আর কিছু? আমার তাড়া আছে রুণুদা।
আমি পেছন ফিরি। মুক্তা যেমন আমার সঙ্গে ঠাণ্ডা অভদ্র অনেক সময়ে রুক্ষ ব্যবহার করে, আমারও তাই করা উচিত। দীপুর সম্পর্কে ওর ওইরকম ঠাণ্ডা, অনুভূতিহীন উক্তিটাও আমার যাচ্ছেতাই লেগেছে। কী ভেবেছে মেয়েটা? নিজে একমনে বিউটিশিয়ানের কেরিয়ার করে যাবে, অন্য সবাই চুলোয় যাক?
দুপুরবেলা সম্ভাব্য সব জায়গাগুলোতে খোঁজটোঁজ করে ফিরে যাচ্ছি, দেখি দীপু ফতাস ফতাস করে আসছে।
—কী রে? কোথায় ছিলি? সারা সকাল তোকে খুঁজেছি। বিশুদার লাইনে নেই… দীপু বলল—লাইনেই ছিলাম বাবা।
—ধ্যাৎ—
—আরে আজকে নিতাইদার লাইনে ঢুকেছিলাম। দ্যাখ রুণু আফট্রল এম পি লোক, রোজ রোজ বিশুদার কাছে গেলে যদি ভাবে ওকে আমরা ইগনোর করছি। কিংবা ওর পার্টিকে সাপোর্ট করি না, তা হলে? দ্যাখ তোর আমার একটা ভোট পেরিয়ে গেছে, আমরা তো দাগী আসামি হয়ে যাব রে?
—তুই কি বিশুদার পার্টিকেই সাপোর্ট করিস?
—তা অবিশ্যি করি না, কিন্তু জানতেও তো দিচ্ছি না, বিট্রে করে যাচ্ছি।
—বিট্রে নয়। আমাদের ভোট হল সিক্রেট ব্যালট সিস্টেমে দেওয়া। কারও জানতে পারার কথা নয়।
—তবু জেনে যায়।
—অদ্ভুত কোনও কৌশলে। সে যাক। তা তুই কাদের সাপোর্ট করিস?
দীপু চোখ সরু করে আমার দিকে তাকাল—কোন পার্টির পে-রোলে আছিস শালা? আমার হাঁড়ির খবরে তোর কী কাজ!
আমি হেসে ফেলি—হাঁড়ির খবর সত্যিই একটা আছে রে দীপু। আমার আর তোর একসঙ্গে চাকরি। তিন হাজার ইচ্। টেম্পোরারি। স্কুলেরটা লেগে গেলে তুই ছেড়ে দিতে পারবি…এক নিশ্বাসে আমি বলে যাই। চাকরিটার কথাও বলি। তবে চাকলাদার যে আমাকেই ধরেছিল সে-সব ডিটেলে আমি যাই না।
—চাকলাদার?—দীপু খুঁতখুঁত করে। শালা ভিখিরি চাপা দিয়েছিল…
—ও বলছে সে ওর পাঁচিল নয়। আগেকার পুরনো বাড়ির ঘুণ ধরা পাঁচিল। তাও ও এত দিন ধরে শাস্তি পেল।
—বলছে? কিন্তু এই প্রোমোটার চাকলাদার কম্বিনেশনটা…বুঝলি…
—কিচ্ছু বুঝলাম না। আমরা ওর বাড়ির খুঁটিনাটি সুপারভাইজ করব। হিসেব পত্র দেখব। ভাল না লাগলে বা লোকসান বুঝলে ছেড়ে দেব।
—ডান—খুব চকচকে চোখে আমার দিকে চাইল দীপু।
আ-হ। ভীষণ একটা স্বস্তি। একটা আরাম বোধ হল আমার। কেন আমি বলতে পারব না। তবে কি আমি মহামানব-ফানব হয়ে যাচ্ছি! দীপু বাড়িতে তিন হাজার কনট্রিবিউট করতে পারবে, তার ব্যবস্থা করেই কি আমার এই উল্লাস!
৫
চাকরি শুরু হয়ে গেছে। চাকলাদার ঘুরে ঘুরে আমাদের মাল দেখাচ্ছে। চেনাচ্ছে। মিস্তিরিগুলো কত চোর বোঝাচ্ছে। কোথা থেকে কী মাল আসে, কত আছে, কত আসবে, সম-স্ত।
দিনতিনেক পরে বিকেলবেলায় বাড়ি ফিরে দেখি হরসুন্দরী স্কুলের ফার্স্ট গার্ল বেরিয়ে যাচ্ছে। মণি আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ি? ওর বাড়িতে সায়েন্স ম্যাথস-এর লোক মজুত থাকা সত্ত্বেও ও অনেক কিছুই আমাকে দেখাতে আসে। স্পষ্টই বোঝা যায় ও বাড়িতে কোনও সাহায্য পায় না, কোনও মানে দীপুর। আর কারও তো সাহায্য করার ক্ষমতাই নেই। মণি কি জানে না ওর দাদা আর আমি কাজে লেগেছি? ওদের বাড়িতে কি কারও সঙ্গে কারও কমিউনিকেশন নেই!
—কী রে চলে যাচ্ছিস? কী এনেছিস আজকে? বসে যা।
ঘষা কাচের মতো গ্রীষ্মের শেষবেলার আকাশ। দীপু এখনও সাইটে আছে। হেড মিস্ত্রির সঙ্গে কী সব জানি কথা বলছে। তা ছাড়া এটা আমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছি যেদিন আমি আগে যাব সেদিন আমি একটু তাড়াতাড়ি বাড়িও ফিরব। ওর বেলাও একই নিয়ম। সারাদিনের মধ্যে কিছুটা সময় সাইটে আমি বা ও একলা। আমার টুইশানিগুলো সন্ধেবেলায় বলে বেশির ভাগ দিনই আমি আর্লি টু গো অ্যান্ড আর্লি টু বি ব্যাকটাই পছন্দ করি।
মণি বলল—তোমার কাছে আসিনি।
—তবে?
—বউদির সঙ্গে দরকার ছিল। একটু ফর্মাল হেসে মণি চলে গেল।
পিকিউলিয়ার ফ্যামিলি তো? মণিটা অন্তত স্বাভাবিক ছিল আচার-ব্যবহারে, বুদ্ধিসুদ্ধিতে। এও যে দেখছি মুক্তার পথ ধরেছে! বউদিকে জিজ্ঞেস করতেই পারতাম কী বিশেষ দরকারে মণি এসেছিল তার কাছে। কিন্তু কেমন বাধল। কে জানে হয়তো নিতান্তই কোনও মেয়েলি দরকার।
সত্যি কথা, চাকলাদারের কাজটা আমার ভাল লাগছে। হিসেবপত্তর রাখা এ আর এমন কী! কিন্তু একনম্বর সিমেন্ট কাদের, বালি ম্যাক্সিমাম আজকাল ইলমবাজার থেকে আসছে, স্টোন চিপসের ঠিকানা পাকুড়। টিলা ব্লাস্ট করে করে চিপস হয়। ইট আসছে নীলগঞ্জ থেকে। কত সিমেন্টের সঙ্গে কত বালি মেশালে পলেস্তারা, কত সিমেন্টের সঙ্গে কত বালি, কত স্টোন চিপস মেশালে কাস্টিং… বিচিত্র রকমের সব তথ্য, তারপর এই মিস্তিরি আর কামিনদের একটা আলাদা ওয়ার্ল্ড, ভাবভঙ্গি, সবচেয়ে মজার— শূন্য অকুপাই করে একটা পেল্লাই স্ট্রাকচার উঠে যাওয়ার ম্যাজিক। প্রথমে খাঁচাটা পুরো করে নিয়েছে। এখন টপ ফ্লোর অর্থাৎ সাততলায় ইটের কাজ জানলা দরজার ফ্রেম বসানো এ সব শেষ করে ছ’তলার ইটের কাজ হচ্ছে। সাততলায় সিমেন্টের কাজ। ধাপে ধাপে নামছে।
রসিক ঘোষ লেন দু’ তিন বার পাক খেয়ে যেখানে এস এস আলি রোডের একপ্রান্তে পড়েছে, রাস্তাটা হয়ে গেছে পঁচিশ ফুট চওড়া, সেই কোনায় গুহমজুমদারদের বাড়িটার অবস্থান। ওরিজিন্যাল নাম ছিল গুহ-প্যালেস। সেই প্যালেস দু’তিন পুরুষের পর পলেস্তারা খসে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড হয়েছিল। অনেকটা জায়গা ফাঁকা ছিল সামনে। তাতে গাছপালা। বাড়িটা ছিল চৌকোমতো বেশ বড় দোতলা। এখন ওদের পাঁচ শরিকে এসে দাঁড়িয়েছে। বড় গুহর নাতি দেবল মাঝে মাঝে এসে আমাদের সঙ্গে গালগল্প করে যায়। কতটা উঠল সেটাও দেখে যায়। মেজ এখানে থাকে না, সিঙ্গাপুর, থার্ড হল মেয়ে, দেরাদুনের কোন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল, সেখানেই ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। ফোর্থ একটি মাল। হেন কুচুটেমি, বদমায়েশি নেই যা না কি সে করতে অরাজি। আমরা অত জানতাম না। দেবলের কাছেই শুনেছি এই সেজদাদুর জন্যেই তাদের বাড়ি শেষ পর্যন্ত বিক্রি করতে হল। সেজ এবং তার সঙ্গে তালে তাল দিয়ে যাওয়া ছোট। গুহমজুমদারদের সঙ্গে আমাদের কোনওদিনই ভাবসাব ছিল না। ওরা বিরাট বাড়ির মালিক, আমরা জবরদখল কলোনির বাসিন্দা। এই তফাতটা আমাদের অল্পবয়সে খুবই ছিল। কিন্তু দেবল আর ওর বাবা যেদিন প্রথম সাইটে এলেন দেবলের বাবা রমেন গুহ বললেন—আরে তোমরা? চেনা-চেনা লাগছে! কী যেন নাম?
দেবল বলল—চিনতে পারছ না? এটা দীপু আর ওটা রুণু। আমার এমন অবাক লেগেছিল! রমেনকাকা বললেন—তবে তো ভালই হল। আমাদের বাড়িটা এমন পিছিয়ে যাচ্ছে! জানো রুণু এই চাকলাদার কিন্তু আমাদের থার্ড প্রোমোটার।
আমি বললাম—তাই তো! আমাদের ধারণা ছিল উনি কন্ট্যাক্টর।
—হ্যাঁ তাই। প্রথম জনের নাম আমি করব না, আমাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে। দ্বিতীয় জন এক এক ইউ পিআইট, সে-ই চাকলাদারকে আনে। তা আমাদের পুরনো পাঁচিল ধসা নিয়ে সেই কেসের সময়ে তো সে চাকলাদারের ঘাড়ে সব চাপিয়ে কেটে পড়ল। কেস ফয়সালা হয়ে যাবার পর চাকলাদার বলল—আমিই আপনাদের এ বাড়ি করে দিচ্ছি। …তো এইসব গল্পগাছা উনি আমাদের সঙ্গে এমন করে করলেন যে মনেই হল না, আমরা কাছাকাছি থাকলেও কোনও জানাশোনা কথাবার্তা আমাদের মধ্যে ছিল না।
দেবল বলল—তোমরা আছ খুব ভাল হয়েছে। আমরা আরও ভাল করে এদের কাজকর্মের বিষয় জানতে পারব। কতটা এগোচ্ছে, কোথাও গাফিলতি হচ্ছে কি না।
সেই থেকে দেবল প্রায়ই আসে। আমাদের হিসেব-পত্র দেখে, বাড়িটা ঘোরে।
দীপু এ সবের মধ্যে থাকে না। হয় তো দুটো কথা বলল, তারপর বিনা নোটিসে উঠে চলে গেল। এক এক সময়ে জিনিসটা খুব বিশ্রী দেখায়।
একদিন বলি—কী রে দীপু, রমেনকাকা দেবল ওরা এলে তুই ওরকম অদ্ভুত ব্যবহার করিস কেন রে?
দীপু একেবারে ব্ল্যাংক চেয়ে রইল। খানিকক্ষণ পর আমি বললাম—কী রে জবাব দিচ্ছিস না?
—ওদের অত কী রে? দীপু ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল।
—কীসের অত?
—কোনওদিন আমাদের দিকে ফিরেও চায়নি। আমরা গরিব, আমাদের ওদের মতো পয়সা নেই। ঠিক আছে, তোর রিকোয়েস্টে চাকরি নিয়েছি, তো কী?
আমি হেসে বলি—দ্যাখ দীপু চিরদিন কারও সমান যায় না। ওরা এখন আর আগের মতো বড়লোক নেই। এই বাড়ি মেনটেন করতে পারত না বলেই তো এইভাবে ভিটে বিক্রি করে দিচ্ছে। তা ছাড়া আগেকার মেন্টালিটিও লোকের থাকছে না। দেবল-টেবল আমাদের জেনারেশন, আমরা এ সব মানি না। তা ছাড়া বাড়িটা তো ওদের, খোঁজ নেবে না?
দীপু চোখ পাকিয়ে বলল—কিন্তু আমি যে ভয়েস শুনি। তুই যেদিন চাকরিটা প্লেটে নিয়ে হাজির হলি সেদিনও শুনেছিলুম। এরা এলেও শুনছি।
—তোর ভয়েস টয়েসগুলো রাখবি? বাজে যত। চল তোকে একদিন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।
—চল, দীপু কেমন একটা চ্যালেঞ্জ নেওয়া গলায় বলল।
—রাজি?
—রাজি।
—তা হলে খোঁজ নিচ্ছি কিন্তু।
সঙ্গে সঙ্গে দীপু কেমন মিইয়ে যায়—ডাক্তারটা যদি আমাকে পাগল বানায়?
—দ্যাখ দীপু পাগল কাউকে বানাতে হয় না, পাগল মানুষ হয়। তোর হাবভাব আমার সুবিধের ঠেকছে না। সময়মতো চিকিৎসা হলে এফেক্টটা হবে।
পাগলদের পাগল বললে খেপে যায় সবাই জানে, দীপু কিন্তু খেপল না। এটা ভাল লক্ষণ। আরেকটু সাহস করে বলি সুতরাং—এ সব ভয়েস-টয়েস, কোথাও কেউ নেই, অথচ তুই শুনছিস এর মানে কী? সত্যযুগ তো আর নয় যে দৈববাণী হবে।
দীপু চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল। আমি বললাম—নেচারটা কী তোর ভয়েসের? কী শুনিস? বলবি তো?
—দ্যাখ রুণু, তুই আমার বন্ধু মানছি। ক’টা টিউশনি জুটিয়ে দিয়েছিস, এখন আবার এই তিন হাজার। সব ঠিক। কিন্তু তুই আমার প্রাইভেট ব্যাপারে নাক গলাবি না।
যা বাব্বা।
ঠিক আছে, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়াটুকু যখন রাজি হয়েছে, তখন আর কিছু না বলাই ভাল। বেগড়বাঁই করলে মুশকিল আছে।
চুপচাপ কাজ করে যাই। দীপু একবার মিস্তিরিদের সঙ্গে কথা বলতে উঠে গেল। আমি দেখেছি ডেস্ক-ওয়র্কে দীপুর মন নেই। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারলেই ভাল। মিক্সচারের কড়া উঠছে নামছে। উঠে গেল, আবার নতুন করে বালি-সিমেন্ট মিশেল হচ্ছে। তবে এখন ও আর চটি ফতাস ফতাস করছে না। আমি নিজে সঙ্গে করে ওকে নিয়ে গিয়ে একসেট জামা-কাপড় কিনিয়ে দিয়েছি। এক জোড়া পেছনে স্ট্র্যাপ দেওয়া চপ্পল। পরতে নানা বাহানা শুরু করেছিল। এই দ্যাখ গোড়ালিতে লাল দাগ হয়েছে, ফোস্কা পড়বে। বিনা বাক্যব্যয়ে কয়েকটা স্টিকিং প্লাস্টার এনে গোড়ালিতে লাগিয়ে দিয়েছি। এখন মুখে আর কিছু বলতে পারছে না। কিন্তু মুখটা অকারণ গোমড়া করে থাকে। —এরপর বোধহয় টাই পরাবি? —একদিন বলল।
আমি কোনও জবাব দিইনি।
একদিন হেড-মিস্ত্রি কলোরস বলল—কালোবাবু পাগলা হলেও শেয়ানা আছে।
কামিনগুলো হেসে অস্থির। গালে গুণ্ডি পুরে বলল একজন—তোমার থেকে ও শেয়ানা নাকি মিস্তিরি?
হেড মিস্ত্রি গম্ভীরভাবে বলল—যা যা কাজ কর। নয় তো ভেগে যা। কী বলেন গো রুণুবাবু?
আমি বলি—তোমার আন্ডারে যারা কাজ করছে, তারা তোমার দায়িত্ব। আমি ওর মধ্যে নেই। তবে তোমার দায়িত্ব পুরোই আমাদের দু’জনের—সে কালোবাবুই বলো আর ফর্সাবাবুই বলো।
লাল দাঁত বার করে কলোরস বলল—ফর্সাবাবু নয়, গোরাবাবু।
—ভাল। কিন্তু মিক্সচারগুলো ঠিকঠাক করো। প্রত্যেকবার নতুন মিশেল তৈরি করবে, আমাদের ডাকবে, এসে দেখে যাব। যে কেউ একজন।
খইনি মুখে নিয়ে কলোরস মিচকে হেসে বলল—এই যে বিল্ডিং ওপর থেকে নীচে নামছে, এরকম হয় না, নীচ থেকে ওপরে ওঠে, বাবু কি জানেন? মাপের কম বেশি করলে বাবু আপনি ধরতে পারবেন?
—মেপে মেপে তুলব, তোলাব—এই বাড়ির পাঁচিল চাপা পড়ে দু’জন মারা যায়। বাড়িটার বদনাম আছে।
—ভিখিরি তো, না কী বাবু?
—ভিখিরি তো কী?
—আজ্ঞে, ওদের পাঁচিল-চাপাই ভাল।
—বাঃ চমৎকার।
এদেরই যদি এই অ্যাটিচুড হয়, তা হলে বিত্তবান ক্ষমতাশালীদের কী হবে?
৬
প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে দীপুকে জিজ্ঞেস করলাম—কী করবি রে টাকাটা নিয়ে?
—তোর ধারটা শুধব, তারপর বাকিটা বিড়ি খাব।
—মানে?
—মানে তোর জানবার দরকার কী রে শালা? বলেছি না প্রাইভেট ব্যাপারে নাক গলাবি না!
—মাসিমার হাতে কিছু দিবি তো!
—অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে।
—মানে?
—খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তাঁতির এঁড়ে গরু কিনে। শুনিসনি? আমি একটা এঁড়ে গরু ছাড়া কী? দু’তিনটে মাস পরেই তো পুর্নমূষিক। ইতিমধ্যে ছেলের কাছ থেকে টাকা পেয়ে হয়তো মহাজনদের কাজটা ছেড়ে দিল। কিংবা বোনেদের বিয়ের গয়না গড়াতে শুরু করে দিল। তখন?
—তা তুই কি চাস না মাসিমা কাজটা ছেড়ে দিন কিংবা বোনেদের বিয়ের ব্যবস্থা হোক।
—মায়ের হেলথ তো ভালই। মহাজনরা ভাল মাইনে দ্যায়। ব্যবহারও ভাল। করতে দোষ কী! আর বোনেদের বিয়ে? ও ওরা নিজেরাই ম্যানেজ করে নেবে। ওর মধ্যে আমি নেই। আমার টেম্পোরারি কাজের কামাই আমি ওদের চুড়ি, হারে খরচ করতে গেলুম আর কী!
কিছু বললাম না। মুখটা আমার নিশ্চয় তোম্বা হয়ে গিয়েছিল। ও সেদিকে দৃক্পাতও করল না। গুনে গুনে সাতশো টাকা আমার হাতে দিয়ে চলে গেল। আমার ধার শোধ আর কী! সেয়ানা পাগল, কলোরস ঠিকই বলেছিল।
দ্বিতীয় মাসের মাইনেটাও সুন্দর পেয়ে গেলাম। তারপরই আরম্ভ হয়ে গেল ব্যাপক ঝামেলা। গুহমজুমদারদের বাড়ির সামনে দিকে অনেকটা খোলা জায়গা। কিন্তু পেছন দিকে বাড়ি, হবি তো হ, আবার জগাদাদের সেই ধ্বংসস্তূপ। শুনলাম জগাদারা নাকি মামলা ঠুকে দিয়েছে সাততলা বাড়ি হলে যতটা জমি পেছনে খালি রাখতে হয় তা রাখা হয়নি।
চাকলাদার মোটরসাইকেল দাবড়ে একদিন এল, বলল—কাজ তো এখন বন্ধ থাকবে সাহেব। কতদিন বুঝতে পারছি না। তবু তোমরা এসো, সাইটটা চোখে চোখে রাখবে। এত মালপত্র। রাতে আমি সিকিওরিটির থেকে লোক নেব। তবে তোমাদের অত টাকা আর দিতে পারছি না। দু’জনকে হাজার-হাজার দু’হাজার দেব, মামলা চুকে যাক, তারপর আবার…
—এ কি সহজে চুকবে?
—সবই টাকার খেলা, আঙুলে টুসকি দিয়ে চাকলাদার বোঝাল।
আমার হয়ে গেল মহা রাগ। বেশ মাস-মাস তিন হাজার করে আসছিল। মা আর দাদার মুখ কম গম্ভীর। বউদির হাসি-তামাশা বৃদ্ধির দিকে। এমনকী রাস্তায় মুক্তার মুখে মেজাজে পর্যন্ত একটা আলগা ভাব লক্ষ করেছি, যেন টেনশন মুক্তির লালিত্য। সন্ধে সাতটায় ‘লা-বেল’ বন্ধ হয়। রাস্তায় আমায় দেখে একদিন বলল—‘রুণুদা, ভাল আছ?’ মুখটা সামান্য একটু হাসি-হাসি। আমি বললাম—বাপরে, মুক্তাদেবী কুশল প্রশ্ন করেছেন আর আমি ভাল থাকব না? আমার ঘাড়ে ক’টা মাথা!’
তা এ সবই তো দীপুর মাসান্তিক তিন হাজারের ফল। দীপুর থেকে ওর বোনগুলো অনেক সংবেদনশীল। টাকাগুলো দীপু সত্যিই ফুঁকে দেয় কিনা জানি না। দিক বা না-দিক, মেয়েগুলো চায় দাদা একটা কিছু পাক। কিছু একটা করুক।
সোজা পার্টি অফিসে চলে গেলাম। জগাদা বিরাজ করছে। গম্ভীর মুখে বললাম— আমাদের চাকরিটা শুধু শুধু খেলে জগাদা, অ্যাঁ? কেন, তোমায় কি বিঁধছিল।
—তোর… তোদের চাকরি… কী ব্যাপার বল তো।
—তুমি ভালই জানো, —আমি বিশদে যেতে চাই না।
জগাদা খুব একটা চিন্তার অভিনয় করল। তারপর বলল—ও হো হো ওই গুহদের বাড়িটার কথা বলছিস? শুধু শুধু কী রে? নিয়ম… কর্পোরেশনের নিয়ম—একেবারে মাপে মাপ যতটা উঁচু হবে ততটা বেশি জায়গা পেছনে রাখতে হবে। রেশিও আছে একটা। টুয়েন্টি পার্সেন্ট অব হাইট!
—তা ওদের বাড়ি তো আজ হয়নি, চার বছর আগে থেকে হচ্ছে। অবজেকশনটা তখন দিতে পারোনি? বাড়ির স্ট্রাকচার উঠে গেল, সাততলা কমপ্লিট হয়ে গেল, পজেশন নেবার জন্যে লোকে যাতায়াত করতে শুরু করেছে, এখন তোমার হুঁশ হল?
—আরে বোস বোস, মাথা গরম করিসনি। সত্যিই আমার খেয়াল হয়নি। অত জটিল কর্পোরেশানের আইন কানুনের ব্যাপার। তা ছাড়া যখন শুরু হয়েছিল বলেছিল ছ’-তলা করব। তলে-তলে সাতের ভিত করেছে।
—তোমার কথা বিশ্বাস করব এমন গ্যারান্টি দিতে পারছি না জগাদা। ইউ আর এ ট্রাব্ল-মেকার। ইচ্ছে করে করেছ সবটা।
—সে তুই যা-ই বলিস রুণু, ও সাততলা আমি ভাঙিয়ে ছাড়ব। আর তুই বিশ্বাস করিস না করিস, আমার এক শুভানুধ্যায়ী আমাকে পয়েন্ট আউট না করে দিলে, আমি বুঝতামও না। অ্যাকশনও নিতাম না।
—কে সেই শুভানুধ্যায়ী? নাম বলো।
জগাদা বললে—তুই যে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলি একেবারে। পার্টি-অফিসে আসলে সময় নিয়ে আসতে হয়। যেমন ওই বিশু মল্লিকের কাছে যাস! যাবি তিণমূলের কাছে, খবর চাইবি সি পি এম থেকে এমন তো হয় না সোনা!
—বা বা বা। জানো যে-মুহূর্তে কেউ ইলেকটেড হয়ে যাচ্ছে সে জনগণের কথা, দুঃখ-দুর্দশা শুনতে বাধ্য। বিশুদা নিতাইকাকা এরা আমাদের মানে জনগণের খিদমদগার।
—আমি তো নই বাবা!
—আলবত তুমি কেন না তোমার পার্টি, পার্টি ইন পাওয়ার।
—সেইজন্যেই তো ন্যায় বিচারের জন্যে মামলাটা ঠুকে দিলুম। তা, রুণু ওটা কি একটা চাকরি হল? ইট-বালি-সিমেন্ট পাহারা দিচ্ছিস! ছিঃ, তোদের মতো এডুকেটেড ছেলে! আমি নেক্সট ইলেকশনে আসছি, তারপর দ্যাখ না কী করি, আমার এলাকায় যেখানে যত শিক্ষিত বেকার আছে, চাকরি হোক, কিছু হোক—একটা পাবে। ঘরে ঘরে আনন্দের বাতি জ্বলবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এলাকা। মন্ত্রী এলে আলাদা করে পরিষ্কার করাতে হবে না। বুঝলি? ঘাড় ধরে কর্পোরেশনের লোক দিয়ে কাজ করাব। বোমবাজি নেই। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-গরিব নেই—সব এক রং—ভাই-ভাই। —এ আমার অনেক দিনের স্বপ্ন রে!
গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছিল। মাকড়াটা মনের সুখে ডোজ দিয়ে গেল। আমিও মুখ হাঁ করে গিলে গেলাম। ‘ঘরে ঘরে আনন্দের বাতি’ ‘হিন্দু-মুসলমান ধনী-গরিব নেই’ কোত্থেকে মুখস্থ করে এসেছে বক্তিমেটা!
মুখটা আমার প্যাঁচার মতো দেখাচ্ছিল নির্ঘাত, কেন না শামু পার্টি-অফিসের মুখেই আমাকে ধরল—এ বে নিমপাতা চিবিয়েছিস?
—দ্যাখ শামু, ভদ্রলোকের ভাষায় কথা বলবি তো বল।
—গাণ্ডুটা তোকে কী সমঝাচ্ছিল রে? খেপচুরিয়াস হয়ে গেছিস?
—তোকে বলতে গেলাম আর কী! গুণ্ডা-দলের সর্দার একটা—
আমি ভাবছিলাম শামু এখানে কেন? কোনও স্বার্থ ছাড়া কি ও আসবে? শামু আমাকে খপাত করে ধরল। দেখলে বোঝা যায় না, কিন্তু এ ক্লাস স্টিলের কব্জাটা। বলল—এদিকে আয় শালা, তোকে আমার দু’-চারটে কথা বলার আছে। —আমার অনুমতির অপেক্ষা করল না। টেনে নিয়ে গেল একধারে, পার্টি-অফিসের সরু-নিচু দরজাটা ছাড়িয়ে বাঁদিকে, বেশ কিছু দূর, তারপর বলল—বল এবার কী বলছিলি!
—কিচ্ছু বলিনি, বলার ইচ্ছে নেই।
—যদি না বলিস তো শোন। যে-কথাগুলো আমাকে বললি, সেগুলো গদাকে বলতে পারবি? পারবি না। গাড়ি চড়ে ইলেকট্রিক জামা-কাপড় পরে ঘোরে। থোবড়াটা যেন চাঁদ থেকে নেমে এসেছে। তাই বলতে পারবি না। আমি শালা লুঙ্গি কোমরে তুলে পরি, বড় জোর একটা টেরিকটের সস্তা শার্ট-প্যান্ট, গুণ্ডার সর্দার! কেমন? তা আর কী বাকি রেখেছিস আমাদের জন্যে। একটা পাড়া দে, যেখানে নিশ্চিন্তে বাস করতে পারি, একটা চাকরি দে যেটা করতে পারি, একটা মানুষ দে যে মুসলিম পরিচয় শুনলে আঁতকায় না।
কেস খতরনাক হয়ে যাচ্ছে। অভিমান। রাগ। আমার মুখের নিমপাতা মুহূর্তে উবে যায়, মুখচোখ আর প্যাঁচা থাকে না। আমি বলি—আমি তো বি কম, দীপু তো প্রায় এম এসসি, চাকরি পেয়েছি? তুই তো মাধ্যমিক ফেল। ন্যায্য কথা বল শামু। তোদের মধ্যে যারা কোয়ালিফায়েড তারা চাকরি পাচ্ছে না? ইলেকশনে লড়ছে না? জিতছে না? ঠিক অন্য পাঁচজনের মতো চুরি আর দলবাজি করছে না? মুশকিল কী জানিস তারা তোদের জন্যে কিচ্ছু করছে না, কিচ্ছু না। সব বোঝে তোদের আঁতেলরা নিজেরা মানে না। কিন্তু তোদের মনে ভয়, ভক্তি জাগিয়ে রাখার ব্যাপারে কথাটি বলে না। আরে বাবা আমাদেরও তো পাণ্ডা ঠাকুররা বলে—পূজা দিস, একশো বিশ টংকার পূজা, পাপঅ হউচি। আমরা থোড়ি শুনি। একদল বোকা আছে। তারা মাছিমারা কেরানির মতো এগুলো ফলো করে যায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই।
শামু বলল—চল কোথাও একটা গিয়ে বসি।
আমি আপত্তি করি না। খেলার মাঠে আমাদের কোথাও বিভেদ ছিল না, বিপদে আপদেও না, কিন্তু সামাজিক প্রশ্নে একটা সংকোচ একটা প্রত্যাখ্যান কি ছিল না? নেই? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে কী করে এ সব হয়। কে কী ভাবে, কেন ভাবে! আমার নিজস্ব কতকগুলো ভাবনা আছে ঠিকই, পর্যবেক্ষণও আছে। কিন্তু সেইগুলোকেই আমি অকাট্য বলে ধরে বসে থাকি না। খুব জানতে ইচ্ছে করে। চাকলাদারের চাকরিটা করতে গিয়েও জিনিসটা হয়েছিল। এখন শামুর কথাতেও হল।
বড় রাস্তায় পড়ে আমরা একটা ধাবায় ঢুকে কোনার বেঞ্চিতে গিয়ে বসি।
—বল কী খাবি? শামু বলল।
—খাব না কিছু। লস্যি বানাতে বল!
—ঠিক হ্যায়, রোজ সিরাপ দেবে তো!
—নাঃ, এমনি।
নিজেরটা রোজ সিরাপ দেওয়া আমারটা এমনি অর্ডার চলে যায়।
শামু প্রথম চুমুকটা সড়াৎ করে টেনে নিয়ে বলল—রুণু, আমার ছোট বোনটাকে বিয়ে করবি?
—যা বাব্বা! হঠাৎ? আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়েছি।
—না, বলছি, ধর দীপুর বোন আর আমার বোন দু’জনের মধ্যে তুই বাছছিস, আমার বোন কিন্তু কালোর ওপর খুব সুন্দরী!
—দ্যাখ শামু, তোর কথাগুলোর কোনও মানে হয় না। প্রথমত আমি একটা বেকার, নিজেরই ভাত নেই তার শংকরা! আমি অমন বিয়ে-পাগলা নই। দ্বিতীয়ত বাছাবাছি আবার কী! আমার যাকে ভাল লাগবে, মনে হবে সারা জীবনের বন্ধু হবার মতো, তাকে বিয়ে করব, সে তোদের কারও বোন হবে না।
—আমার বোনকে তুই দেখিসনি।
—শুধু রূপ দিয়ে কিছু হয় না শামু।
—শোন রুণু আমাদের ওখানকার রমজান আলিকে চিনিস তো!
—কে? সেই লকড়ি-অলা?
—হ্যাঁ। ও হাসিকে নিকাহ্ করতে জেদ করছে। ওর বিবি অনেক দিন ধরে ভুগছে। ওর নজর পড়েছে…
—ও করতে চাইলেই তুই দিবি?
—তুই জানিস না রমজান আলির পলিটিক্যাল লোকেদের সঙ্গে খুব মাখামাখি।
—সে তো তোরও আছে!
—দুটো আলাদা। আমাকে ওরা ইউজ করে। কোথায় বুথ দখল করতে হবে, কোথায় চাঁদা তুলে দিতে হবে। কোথায় কাকে চমকে দিতে হবে। আর রমজান মিঞার সঙ্গে ওদের সোশ্যাল ওঠা-বসা। শিলিগুড়ি থেকে পালামউ থেকে কাঠ আসে রমজান চাচার গো-ডাউনে, চেরাই হয় ওর চেরাই কলে, তারপর রইসদের কাছে চড়া দামে বিক্রি হয়ে যায়। নেতারাও পেসাদ পায়। রমজান চাচার ইফতার-এ কারা কারা আসে জানিস! কেন আসে জানিস?
—শামু তোর যথেষ্ট তাকত আছে। সব দিক দিয়েই। তুই বোনকে বাঁচাবার চেষ্টা কর ওই রাক্ষসটার হাত থেকে। ওকে দূরে কোথাও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি পাঠিয়ে দে। চুপচাপ।
—আমার লাইফ যে হেল করে দেবে রে!
—কী ভাবে? আফট্রল তোর তো মাসল পাওয়ার আছে।
—তবু তুই হাসিকে বিয়ে করবি না?
—আরে খাওয়াব কী? তা ছাড়া বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য হাসি যদি আমাকে বিয়ে করে সেটা হাসির পক্ষে সম্মানজনক হবে?
—বাজে ওজর তুলিস না। তোর রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা আমি করে দেব। কথা দিচ্ছি।
—তা হয় না রে।
—হয় না কেন? ধর গুহমজুমদারদের তোকে পছন্দ হল। ওরা ওদের বাড়ির কোনও মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক করল, তোকে সিঙ্গাপুরে পাঠাল, কমপ্যুটার-ফার করিয়ে তোর চাকরি জোগাড় করে দিল। প্রস্তাবটা এল তোর মায়ের কাছে। করবি তো? উনি তো মেনে যাবেন?
—উনি মেনে যাবেন কিনা বলতে পারছি না। তবে আমি মানব না।
—তুই মানবি রুণু। তোর ঘাড় মানবে, আমি বলছি।
—তোকেও কিন্তু খোয়ার সইতে হবে, তোদের সমাজে। তারপর তোরা আমায় ধর্ম পালটাতে বলবি। এ সব বখেড়ার মধ্যে আমি যাব কেন?
—কিন্তু তোরা কি হিন্দু ধর্মই সেভাবে মানিস? পুজো-আচ্চা তোর মা হয়তো করেন, তুই কভি করিস না। তা হলে?
—তুই খানিকটা ঠিকই বলেছিস শামু।
—তুই লিবার্যাল হিন্দু?
—বলতে পারিস। তবে লিবারাল হিন্দু বলতে ঠিক কী বোঝায়, আমি অত পড়াশোনা করিনি, পুরো বলতে পারব না। আমি হলাম গিয়ে আমি। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় আমার বংশ শুরু হয়েছিল। দেশ বিভাগের ফলে মার খেতে খেতে এ বাংলায় এসে পড়েন আমার ঠাকুর্দা-ঠাকুমা। আমার বাবারও সে-সব স্মৃতিতে খুব পরিষ্কার ছিল না। তবে অনেকদিন রেফিউজি নামটা আমাদের নামের সঙ্গে জুড়ে ছিল। এখন নেই। কোনও মতে বহু স্ট্রাগল করে একটা জায়গা করে নিয়েছি। এখন আর পাঁচটা নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমান-শিখের মতো স্ট্রাগল করছি। আমার বিয়ের কথা ভাববারও সময় নেই। ধর্মের কথা ভাববারও সময় বহুত কম রে শামু।
—এই তোদের দোষ রে রুণু, অধার্মিক টাইপের হয়ে গেছিস, লেখাপড়া করে।
—শামু, যারা এগুলো সিরিয়াসলি মানে, করে, তারাই কিন্তু তোদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে রাখিস। বড় বড় কথা বলে কোনও লাভ নেই, মানুষ মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করবে এইটেই ধর্ম বলে আমার মনে হয়। নইলে ‘রাম-রহিম কৃষ্ণ-করিম’ ধুন গেয়ে কোনও লাভ নেই, আর পুজোই বল নামাজই বল করেও কোনও লাভ নেই।
৭
আর দু’-চার দিনের মধ্যেই গুহ প্যালেস-এর সাততলা ভাঙা হতে লাগল। কর্পোরেশন যে কনট্র্যাক্টরকে ঠিকে দিয়েছে সেই পালবাবু আবার চাকলাদারের খুব চেনা। হাত কচলে বললেন—কী বলব চাকলাদার আমার হাত পা বাঁধা। ইস্স্ অমন সুন্দর চারখানা ফ্ল্যাট। ভাঙতে বুক ফেটে যাচ্ছে। তুমি একটিবার পেছনের জমিটার মেজারমেন্টটা নিলে না!
চাকলাদার হতাশ মুখে বললে—আরে বাবা, আমি যখন এসেছি, তখন এদের ভিত গাঁথা সারা। আমি তো আর প্রথম নয়। এ বাড়ির পেছনে অনেক হুজুতির হিসট্রি আছে। তো আমি বিশ্বাস করেই এগিয়েছি। আমার মাথাতেই আসেনি ল্যান্ড মেজারমেন্ট নতুন করে করাতে হবে।
মাসখানেক ধরে সে কী হুজ্জোতি রে বাবা। সাততলার ডানদিকে অর্থাৎ পুব-দক্ষিণের ফ্ল্যাটটা সবচেয়ে আগে ঠ্যাঙঠেঙিয়ে ভাঙতে শুরু করেছে! সে কী আওয়াজ! সিমেন্টের কাজ সারা, প্লাস্টার অব প্যারিস প্রায় শেষ। ফ্লোরের জন্য চিপস এসে গেছে। গ্রিন, হলুদ, সাদা, মেরুন, চিকচিকে লজেন্সের মতো দানাগুলো, বস্তার মধ্যে হাত ঢুকোই আর মুঠো করে তুলে বাইরের আলোয় মেলে দেখি। আমারই বুকটা ভেঙে যাচ্ছে। তার চাকলাদার তার রমেন গুহ, দেবল গুহ!
দীপু কিন্তু নির্বিকার। স্রেফ পা নাচাতে নাচাতে সিগ্রেট খাচ্ছে। চোখ বোজা। থাকতে পারি না। দীপুর কেস ভাল নয় ডাক্তার স্বয়ং বলেছেন, চোখে চোখে রাখি, ওষুধ খাওয়াই, তা সত্ত্বেও একদিন ঝেঁঝে উঠি: কী রে? তোকে তো দেখে মনে হচ্ছে স্বগগে বসে আছিস, নন্দন কাননের ফুরফুরে হাওয়ায়, পারিজাতের গন্ধ পাচ্ছিস, না কি?
দীপু চুপচাপ একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে। কাগজটা খুলে দেখি লেখা—১ নং ধীরু বাগদি লেন, ঠিকানা ৭/৩—৫ তলা, ২ নং-উত্তম ঘোষ লেন—১৫ নং—৫ তলা, ১৬ নং—৫ তলা, ৩ নং—সি আই টি রোড মুখোমুখি— ৪২/২ ২৩/১—দশতলা, ১৭ নং—৭ তলা ও আট তলা ৪নং পিলখানা সেকেন্ড বাই লেন—৮/এ, ৯/এ, ১০/এ— ৬ তলা… এই রকম ২০ নং পর্যন্ত গেছে।
আমি কিছুই বুঝি না। —এগুলো কী?
দীপু চুপচাপ ফুঁকে যাচ্ছে।
—কী রে?
—বোঝা গেল না?
—না।
—এই বাড়িগুলো সব নিয়ম না মেনে করা হয়েছে। শুধু পেছনের জমির নিয়ম নয়। আরও অনেক নিয়ম যেমন দমকলের পার্মিশন নেওয়া হয়নি, রাস্তার ফুটেজের নিয়ম মানা হয়নি। ইত্যাদি ইত্যাদি।
—এগুলো নিয়ে কী করবি?
—চাকলাদারকে এক কপি, রমেন গুহকে এক কপি দিয়েছিলাম। জগাকে একটা ফাইট দিক।
—দিল না?
—না কিন্তু আমি জানতুম।
—ইস্স্স্, আমাকে একবার বললি না!
—কী করতিস!
—কিছু না হোক ঝাড়তাম।
—ঝেড়ে কী হবে? বুঝিয়ে দিত।
—কী বোঝাত তুই-ই বল।
—নিয়ম না কি এই যে কেউ নালিশ করলে এ সব নিয়ম ভাঙা হচ্ছে কি না হচ্ছে দেখা হবে, নইলে কর্পোরেশন চোখ বুজে নিদ যাবে।
—এ তো চোরের নিয়ম! যদি সত্যি থেকে থাকেও। ফোতো নিয়ম। —তারপরে একটু ভেবে বললাম—আচ্ছা দীপু, গদার কাছে গেলে হয় না। জগাকে একটু চমকে দিত কিংবা বিশুদা, কিংবা নিতাই কাকার কাছে!
—কে যাবে? তুই?
—তুই—আমি।
—কেন? তোর কী স্বার্থ? আমার কী দায় পড়েছে?
—এটা অন্যায়! অন্যায্য! স্বার্থ আমাদের চাকরিটা হুশ করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে।
—তুই বলছিস, যাদের ইনভেস্ট করা টাকা-পয়সা চৌপাট হয়ে যাচ্ছে তারা কেউ যাবে না, আমরা দুই ফিঙে আর ফড়িং ফড়ফড় করব!
—ওরা যাচ্ছে না-ই বা কেন? আফট্রল বিশুদা নিতাইকাকা দু’জনেরই বিস্তর পলিটিক্যাল পাওয়ার আছে, ওরা জগাদাদের অপোজিশনও বটে!
—চুক্কর, চুক্কর, চুক্কর—হঠাৎ দীপু হাত তুলে ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে। ফিসফিসিয়ে চিৎকার বলে যদি কিছু থাকে তো তাই। আমি চুপ করে যাই। ওকে লক্ষ করি। দীপু উঠে দাঁড়ায়, অফিসঘরের জানলার কাছে চলে যায় ঠিক যেন মোবাইলে একটা কল এসেছে। কথা বলতে আড়ালে গেল। ডান কানের কাছে হাত রেখে শুনল কিছুক্ষণ তারপর আবার আস্তে আস্তে পা টেনে এসে বসল।
আমি চুপ। কিছু বলি না।
একটু পরে ক্লান্ত বিধ্বস্ত গলায় বলল—ভয়েসটা কি তুইও শুনতে পেলি?
—না, ফোন ধরিনি।
—মানে তোর কাছেও আসে। তুই পাত্তা দিস না!
—আমার কাছে কোনও অলৌকিক অতিলৌকিক ফোন আসেনি, আসে না।
—ওঃ।
দীপু যেন খানিকটা রিল্যাক্সড্। কিছুক্ষণ পর বলল—ডেঞ্জার সিগন্যাল দিচ্ছে। আজকাল আরও স্পষ্ট।
আমার বিরক্ত লাগে, বলি—ঝেড়ে কাশ না। এই ইনফর্মেশনগুলো কোথায় পেলি?
আমি ভেবেছিলাম বলবে—ভয়েস।
কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে দীপু বলল—বিশুদা। —আর একটু চুপ করে থেকে দীপু বলল—আর জগাদাকে কেস লড়ার ক্লেম রাখার পরামর্শ কে দিয়েছিল জানিস?
—কে?
ভেবেছিলাম বলবে—অরবিন্দদা, কেন না, ওদের যত ঝগড়া তত ভাব। জগাদার মোটা বুদ্ধি, কিন্তু অরবিন্দ চলে পাতায়-পাতায়, তো আবার আমাকে অবাক করে দিয়ে দীপু বলল—চাকলাদার।
আমার হাঁ বোজে না। দীপু আমার দিকে স্ট্রেট তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করি—তুই কী করে জানলি?
এবার দীপু তৃতীয়বার আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল—ভয়েস।
৮
বউদি বলল—মুখখানা কেলে-হাঁড়ি করে ঘুরছ কেন বলো তো? মা আনাজ কুটছে। বউদি বোধহয় চুল শ্যাম্পু করেছে, মাথায় গামছা বাঁধা, দাদা বাজারে গেছে। রিন্টি তার ঘরের মেঝেতে একগাদা পেনসিল, ক্রেয়ন সব ছড়িয়ে বড় বড় হাতি, জেব্রার ঝাঁক, মিকি মাউস, টেডি-বিয়ার সব রং করছে। স্কুলের কাজ। বউদি হরসুন্দরীতে পড়ায়, সেখানে ক্লাস ফোর অবধি বাচ্চা ছেলেদেরও নেয়। কিন্তু রিন্টিকে বউদি ওই স্কুলে দেয়নি। হরসুন্দরী কিন্তু খুব ভাল স্কুল, নামটা ওরকম জগত্তারিণী-মার্কা হলে কী হবে। রাস্তা পার হয়ে বেশ খানিকটা রিকশা করে গিয়ে তবে রিন্টিদের সাহেবি স্কুল। আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত মাইনে আর সাজসজ্জা। অবশ্য, রিন্টি যখন ছোট্ট গলায় নীল টাই পরে, জুতো-মোজা পরে পিঠে ব্যাগ হাতে জলের বোতল, স্কুলে যায়, বেশ দেখায়। কিন্তু ও আজকাল মাকে মাম্মি বলছে প্রায়ই। যে-ই বলে— বউদির চোখ দুটো আনন্দে গর্বে চকচক করে ওঠে। আশে-পাশে যে যেখানে ওর মাসি-পিসি সব আন্টি, দাদার বন্ধুদের আগে ও আমার অনুকরণ করে বিজনদা, স্বপনদা বলত। এখন ওরা সব আংক্ল হয়ে গেছে। আংক্ল শুনে ওদেরও কেমন হরষিত দেখায়। খালি আশপাশের বাড়ির বুলুদি রত্নাদিরা খুঁতখুঁত করে, বলে—এই রিন্টি খবর্দার আন্টি আন্টি বলবি না। কেমন বুড়ি-বুড়ি লাগে। আমার সঙ্গে যখন বেরোয় তখনই আমি শাসাই—রিন্টি খবর্দার আমাকে আংক্ল বলবি না, বললে সচিন পাবি না। রিন্টি আশ্বাসের সুরে বলে, তুমি তো কাকু।
—ভ্যাট, বিজনদা, স্বপনদা ওরা তোর কাকু ছিল না?
—ওরা তো দাদা।
—না, দাদা নয়, আমার দেখাদেখি দাদা বলতিস, যেমনি তোর মাকে ‘টুকু’ ডাকতিস বাচ্চাবেলায়।
—আচ্ছা, আর বলব না। না বললে মিষ্টি মশলা দেবে তো!
এই বাচ্চাগুলোকে চিরকাল আমরা এমনিভাবে নষ্ট করে এসেছি। লক্ষ্মী হয়ে খেয়ে নাও তা হলে চকলেট দেব, দুধটা হাঁ ঢোঁক করে গিলে ফেলো, কী সুন্দর লজেন্স আনবে তোমার বাবা। এরাও কম সেয়ানা নয়, সব সময়ে কিছু না কিছু প্রাপ্তির আশা করে হাত পেতে আছে। মহা মুশকিল!
সুতরাং আমি লজিকের পথ ধরি, দেখি খোকাটাকে বিপথগামিতা থেকে যদি রক্ষা করতে পারি।
বলি—মিষ্টি মশলা তোকে আমি এমনিই খাওয়াব। কিন্তু যেগুলো করতে বলছি সেগুলোই ঠিক কাজ, তাই করবি। কিছুর লোভে করবি না।
—আমি লুভি নই—রিন্টি গোঁজ মুখে বলে।
—তা হলে বললি কেন মিষ্টি মশলা দিলে আর কাকুদের আংক্ল বলবি না।
—আমাদের ক্লাসে সবাই তো বলে, আন্টি, আংক্ল, মাম্মি, ড্যাডি…
—ঠিক আছে স্কুলে যা বলছিস বলবি, বাড়ি এসেই—পিসি-মাসি, জেঠু, কাকু, মা, বাবা বলবি।
রিন্টি একটু ভেবে-চিন্তে বলল—আচ্ছা।
সত্যি কথাই, হরসুন্দরী আর রিন্টির ‘ম্যাজিক মিরর’-এর মধ্যে তফাত অনেক। হরসুন্দরীর বইপত্রগুলো কেমন ফ্যাতা মতো৷ কাগজ বাজে, মলাট বাজে, অক্ষরগুলোও তেমনই বাজে লাগে সেই জন্যে। ভাষাটাই যেন বাজে মনে হয়। অপর দিকে ‘ম্যাজিক মিরর’-এ যে-সব টেক্সট বই তাদের বাঁধাই, কাগজ, রং—এ সবের বাহারই আলাদা। দেখলে পড়তে ইচ্ছে করবে, খুলে পাতা উল্টোতে ইচ্ছে করবে। খাতা সব স্কুলের। লাইন টানা, ডবল-লাইন, মলাটের ওপর সুন্দর লেবেল, আবার কোণে একটা করে মিকি-মাউস, কি ডোনাল্ড ডাক কি স্কুবিডু, মোটিফের মতো ছোট্ট করে একটা জলছবি ছাপ৷ পুরো গেট-আপটাই আলাদা। এই গেট-আপে যে ভাষা আসে সে ভাষাটাও ম্যাজিক। এই স্কুলে পড়লে অন্যদের প্রতি একটা ‘ছোঃ’ মনোভাব, নিজের প্রতি একটা ‘সাবাশ’ মনোভাব তৈরি হবেই। আচ্ছা মানলাম স্কুলগুলো ধনীদের স্কুল, চারশো-পাঁচশো টাকা টিউশন ফি। কিন্তু সরকারও তো ফট করে সব অবৈতনিক করে না দিয়ে এই পাঠ্য-বই খাতার স্ট্যান্ডার্ডটা উঁচু করে দিতে পারত। ঠিক আছে যে পারবে না তার জন্য বিবেচনা থাকবে আলাদা, যেমন ধরুন আমার দাদা যখন এইরকম একটা লোক্যাল স্কুলে পড়েছে, মাস গেলে দশ টাকা মাইনে দেবারও তার সামর্থ্য ছিল না। বইগুলো কিছুটা চেয়ে-চিন্তে চলে যেত। মাইনে কিন্তু প্রায়ই বাকি পড়ে যেত। আমাদের মতো ছেলেদের জন্য একটু কনসেশন থাকল, হাই-ইনকাম গ্রুপের বা মিডল-ইনকাম গ্রুপের জন্য যা ন্যায্য মাইনে হওয়া উচিত তাই হল। এটা কি খারাপ? বুঝি না বাবা। রিন্টির বইগুলো দেখলে আমারই লোভ হয়। যেন চকলেটের মোড়ক একেকটা। ভেতরের জ্ঞানগুলো চকলেট, একটু হয়তো ধৈর্য ধরে খেতে হয়, কিন্তু খাবার রুচিটা থাকে। সেই স্কুল, সেই বই আর সেই সিস্টেম থেকে যা শিখবে তা ঠিক হোক, ভুল হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক, বিদেশি হোক এ দেশি হোক—ওরা মানতে চেষ্টা করবে—এটাই স্বাভাবিক।
আর দাদা বা আমি যখন কলেজে পড়তাম! আরিব্বাস কী মজা! বারোটা টাকা খরচ করে এক এক ডিপার্টমেন্টের সাতটা আটটা এম এ, এম এ পিএইচ ডি-র কাছ থেকে শিখছি। মেয়েগুলো তো এন্তার সিল্কের শাড়ি পরে আসত, পার্ফুম লাগাত আচ্ছা করে। তার পরেও, ইচ্ছে হলে জাস্ট বেড়াতে আসত কলেজে। যদি বলেছি… কী রে এত ফাঁকি মারছিস?
—কে বললে ফাঁকি মারছি। কলেজে কী এমন লেকচার হয় যে শুনতে হবে? খালি লেকচার, লেকচার আর লেকচার। বারো টাকার লেকচার শুনে কী করব?
বাড়িতে ওরা বারোশো টাকার লেকচার আর নোটস-এর বিলি ব্যবস্থা করত। আমরা গরিবের ছেলে কে জানে বাবা, আমরা তো ক্লাস লেকচার সম্বল করেই পরীক্ষা-সাগর পার হয়েছি। খারাপ তো কিছু হয়নি। তবে? যে টিচারকে বারো টাকার ১/১২ টিচার মনে করে অগ্রাহ্য করছে তার কাছেই প্রাইভেট পড়বার জন্যে হত্যে দিচ্ছে পাঁচশো থেকে আটশো টাকা দিয়ে! জিজ্ঞেস করলে বলবে—ক্লাসে ওঁরা কিছু পড়ান না, বাড়িতে গিয়ে করকরে নোটগুলো হাতে তুলে দিলে তবে আসলি চিজ বেরোয়। আসলি চিজ মানে কী বলুন তো! নোটস। অপরের করা নোটস উগরে উগরে শেষ পর্যন্ত ওরা কতটুকু শেখে আমার বিস্তর সন্দেহ আছে। আমাদের যে কখনও অসুবিধে হয়নি তা নয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে ক্লাসের ফাঁকে স্যারেদের কাছে গেছি! লাইব্রেরিতে গেছি!
যাকগে বাবা, —আমি আদার ব্যাপারি, জাহাজের খোঁজে আমার কাজ কী? এ সব হাই-ফাই ব্যাপারে আমার নাক-গলানোর একটাই কারণ। আমার ভাইপোটা। রিন্টিটা স্কুলে একটা অলীক জগতে বাস করে। সে জগতের রহন-সহন, সে জগতের বাস্তব সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারের। এখানকার বাস্তব নয়। নীলকমল-লালকমল ছেড়ে ওরা ব্যাটম্যান-স্পাইডারম্যান হাতে তুলে নিচ্ছে। ‘আনি মানি জানি না’র খেলা ভুলে—রিংগা রিংগা রোজেস পকেট ফুল অব পোজিস্ —খেলছে। রাম দুই সাড়ে তিন বললে হাঁ করে চেয়ে থাকে, বলতে হবে—ইনি মিনি মাইনি মোও। রিন্টিরা অলীক জগতের অলীক মানুষ। কোনওদিন চারপাশের বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারবে না। যদি সেরকম করিৎকর্মা হয়, বিদেশে চলে গিয়ে বাঁচবে, আর তা নয়তো এখানে বাস করবে বিদেশির মতো। খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না, সব কিছু ঘেন্না করবে। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের যেমন স্বাধীনতার পর মনে হয়েছিল তাঁরা এ-দেশের নন, ইংল্যান্ড তাঁদের হোম, সেই হোমে গিয়ে সেখান থেকে অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্য খেয়ে তবে বুঝেছিলেন আসল সত্যটা, এই রিন্টিরাও তেমনি এ দেশের মাটিতে বিদেশি হবে, বিদেশের মাটিতে হবে না ঘরকা না ঘাটকা। আরেক রকমের ঘেটো— হ্যাঁ, ঘেটোই তো।
দূর ছাতার! সেই মোটর-পার্টস-এর দোকানের লোকটা বলেছিল বটে— ভাইপোকেই সামলাতে পারছেন না? ছেলে হলে কী করবেন? তা ছেলে আমার আর হয়েছে! ছ’হাজার টাকার চাকরি পেলাম, দানশীল উদার-মহৎ সেজে বন্ধুর সঙ্গে সেটা ভাগ করে নিলাম, এখন সেটাও ওয়ান-থার্ড হয়ে গেল। হায়!
কেলে-হাঁড়ি মুখ আমার হবে না তো কি বউদির হবে? বিএ অনার্স বিএড ভালই স্কেল পাচ্ছে, দাদার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাজ, রেলে। পাস পায়। সংসার চালাচ্ছে, মাকে দেখছে, ভাইকে দেখছে। বউদির মুখ ঝলমল করবে বই কী!
আমি বিরক্ত হয়ে বলি—তুমি নিজের চরকায় তেল দাও না!
—দিচ্ছি তো! —গামছা বাঁধা মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বউদি বলে, নিজের চরকায় দিয়েও আমার কিছু তেল বাঁচে। সেইটা তোমাকে ধার দিতে চাইছি। যা ক্যাঁচ কোঁচ করছ!
আমি সোজাসুজি মাকে বলি—মা, তোমাকে আর এ মাস থেকে তিন হাজার করে দিতে পারছি না। বাড়িটাতে হেভি ঝামেলা লেগে গেছে। এক হাজার দেব।
মা বলল—আমি তখনই বলেছিলাম! লোকটা আটঘাট বেঁধেই নেমেছে।
—তোমাদের মতো ভবিষ্যদ্দর্শী তো আমি নই! কী আর করা যাবে, তা ছাড়া আমি যা পাই, যতটুকুই পাই, তা-ই আমার লাভ। ও তোমরা বুঝবে না।
মা আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল—বুঝব না কেন? আমাদেরও তো তাই। যতটুকু পাই ততটুকুই লাভ।
আজকে বাজারে খয়রা মাছ পেয়েছি। এমনিতেই বউদি আর রিন্টি ছাড়া আমরা কেউ ওই গোদা-গোদা কাটা পোনা পছন্দ করি না। আজকাল ইনসেকটিসাইডের চল হয়ে ছোট মাছের খুব আকাল। ধান খেতের চিংড়ি খলসে, চুনো-চানা সব মরে যাচ্ছে। আজকে খয়রাটা পেয়ে গেলাম। চান করে আসতে মা বলল—তোর বউদি তোর জন্যে বসে আছে, আমরা তিনজনেই বসে খাই। আয়।
তিন-চারটে খয়রা মাছ আমার পাতেই ফেলে দিল। খানিকটা গরম সর্ষের তেল সেই সঙ্গে। গরম ভাতে খয়রা ভাজা তেলসুষ্ঠু খেতে একেবারে ইলিশের মতো লাগে। ডাল, আলু ভাতে, আর শাকের চচ্চড়ি। মেনু এই। ও মা, দেখি মা আরও দুটো খয়রা আমার পাতে তুলে দিল।
—এ কী? কী করছ? তোমাদের কই?
মা অম্লানবদনে বলল—খেয়েছি দুটো। আজকাল খয়রার গন্ধটা আমার ঠিক ভাল লাগে না। আর টুকুকে তো পোনাও দিয়েছি।
—দাদার জন্যে রাখলে না?
—আরে এসব গরম গরমই খেতে ভাল। রাতে ভাল লাগবে না। তপুকে ডিম ভেজে দেব এখন।
আমার ভুরুটা কুঁচকে থাকে। খয়রা মাছে মায়ের কোনওদিন অরুচি দেখিনি। বউদি অনেক কুচো মাছ খায় না, কিন্তু খয়রা কড়া করে ভেজে দিলে বেশ তারিয়ে তারিয়েই খায়। দাদারগুলো ঝাল করে রেখে দেওয়া যেত। একেবারে শুকনো করে, সর্ষে লংকা দিয়ে! এসব আমাকে ভোলাবার চেষ্টা, আমি বুঝি। যেন দুটো খয়রা মাছ ভাজা পেলেই আমার তিন হাজারের দুঃখ চলে যাবে। এদের ছেলেমানুষি আর যাবে না। যেমন ইম্ম্যাচিওর, তেমনি সেন্টিমেন্টাল!
বউদি উঠে গেল। রিন্টি না হলে ঘুম থেকে উঠে পড়বে। আচ্ছা মা-ন্যাকরা ছেলে হয়েছে বটে! মা বলল —হ্যাঁ রে রুণু, গ্যারেজটাতে দোকান দেওয়ার কথা কিছু ভাবলি? ছোট করে একটা মনোহারি…
—অনেক টাকা ক্যাপিটাল লাগবে।
—তোর দেওয়া টাকা সব আমি জমিয়ে রেখেছি। আট হাজারের চেয়ে কিছু বেশিই হবে। বাকিটা তোর দাদা পি এফ থেকে ধার করে দেবে বলেছে।
—ব্যবসা-ট্যাবসায় হেভি ঝুট-ঝামেলা মা। তোমাকে আগেও বলেছি।
—ওই কর। ঝুট-ঝামেলা কোথায় নেই! এই যে গুহদের বাড়ি হচ্ছে, এখানে ঝুট-ঝামেলা হল না? তোর যদি তোর দাদা বা বউদির মতো নিশ্চিন্তির চাকরি ভাগ্যে না থাকে, তুই একটু সাহস করে ব্যবসা-ট্যাবসার কথা ভাবতে পারবি না? কে বলতে পারে ওর থেকে তুই-ই হয়তো একদিন…
—গোদরেজ হয়ে যাব?
—আলমারি? আলমারি হবি কেন?
—যাচ্চলে, গোদরেজ একটা ফ্যামিলির পদবি, যাদের ওইসব আলমারি ফালমারি।
—তাই বল। তা হতেও তো পারিস। শুধু একটু সাহস কর। আর দ্যাখ, বেশ ঘটা করে একটা ওপনিং হবে। নিতাইকে ফিতে কাটতে ডাকবি। বিশু প্রেসিডেন্ট। রমরম করে চলবে তোর দোকান। তোর বাবা যে কী বুদ্ধি করে এই গ্যারেজটা করে গিয়েছিল। আমি তখন বলেছিলাম—হেসে বাঁচি না, কবে তোমার ছেলেদের গাড়ি হবে… তোর বাবা বলেছিল—কত কাজে লাগবে। ওপরে একটা নিচু হোক, যা-ই হোক, এক্সট্রা ঘরও তো পেলে? তা এখন দেখছি সে ঠিকই…
বাবার বুদ্ধির কথা বলতে গেলে মায়ের আর জ্ঞান থাকে না। কোথায় যে থামবে! আমি বলি—ওটা তুমি ভুলে যাও মা।
—কেন। পরের গোলামির চেয়ে দোকানদারিটাই তোর সম্মানে লাগছে?
—না মা না। ওর ভেতর অনেক হ্যাঁপা আছে। ধরো একদিন কিছুর মধ্যে কিছু না। দোকানটা লুঠ হয়ে গেল। তখন? এরকম তো হামেশাই হচ্ছে আজকাল!
—আশ্চর্য তো! শাটার থাকবে, ভেতরে কোল্যাপসিবল থাকবে। লুঠ অমনি হলেই হল? মগের মুলুক না কি?
—এইবার একটা খাঁটি কথা বলেছ মা, নির্ভেজাল সত্য। মগেরই মুলুক। একেবারে খাপে খাপ। বছরে তিনবার জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, চাল-গম গুদামে পচছে, অথচ না খেতে পেয়ে মানুষ চোর ডাকাত হয়ে যাচ্ছে, কিংবা ফ্যামিলিক্কে ফ্যামিলি আত্মহত্যা করছে এমন শুনেছ কখনও? এ হতে পারে? কারখানার পর কারখানা দুমদাম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের লিডাররা দেখো তো চমচম খাচ্ছে হাত চেটে, শ্রমিকরা মাসের পর মাস বেরোজগার, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, কারও ভ্রূক্ষেপ নেই দায় নেই, মন্ত্রী-আমলা সব নিশ্চিন্তে বিজনেস ক্লাসে স্পেশ্যাল চার্টার্ড প্লেনে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবতে পারো? ‘এক দেহ, এক প্রাণ, একতা—’এই স্লোগান গর্জে গর্জে সব স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করছে।
ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ? মাই ফুট! ধর্মের মতো ফ্যানাটিসিজম আর কোনও কিছুই পয়দা করতে পারে না, আসলে ধর্ম-নিরপেক্ষ নয়। ধর্ম মুখাপেক্ষী দেশ এটা। মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার বেড়ে যাচ্ছে, মানুষের থাকবার জায়গা নেই। এদিকে লাউডস্পিকার যদি গীতা আওড়ায়, ওদিকে আর একটা লাউড-স্পিকারে আজান শুরু হয়ে যায়, গ্রন্থসাহেব পাঠই বা বাকি থাকবে কেন? এক পাড়ায় তিনটে সর্বজনীন দুর্গাপুজো, কালীঠাকুর একটু বেঁড়ে করবার অর্ডার হলে নেতাদের মাথায় হাত পড়ে, নিজের পাড়ার কালী বেঁড়ে হয়ে গেলে মান যাবে। ঈদের নামাজ রাস্তায় রাস্তায় উপছে পড়ছে। আজকাল ছট পুজোর সময়েও ট্র্যাফিক জ্যাম হচ্ছে। ভিড়ের চোটে কতজনের সলিল সমাধি হচ্ছে গঙ্গায়। সেকুলার মানে কী? না, যে কোনও দেবতা, যে কোনও পরব, সব সরকারকে সাধারণ মানুষকে মানতে হবে। জ্যাম হবে, স্ট্যাম্পিড হবে, মৃত্যু হবে। হোক।
—তুই কি খেপে গেলি না কি? মা হাত ধরে আমাকে থামায়! দোষের মধ্যে গ্যারেজে একটা দোকান দিতে বলেছিলাম। তো এক কাঁড়ি বক্তৃতা শুনিয়ে দিলি!
—নাঃ, তুমি ওই ‘মগের মুলুক না কি’ না কী একটা বললে না! তাইতেই ফ্লোটা এসে গেল। আমি নিশ্বাস ফেলে বলি।
—পলিটিকস করছিস না কি আজকাল? ওইজন্যে বিশু মল্লিকের কাছে যাওয়া বেড়ে গেছে।
—মা পলিটিকস যারা করে তারা এসব বলে না! তারা সব জানে। খুব ভাল করে জানে কীসে ভাল আর কীসে মন্দ। ভাল-মন্দের পরোয়া তাদের নয়। তারা শুধু দেখে কতটা কী বললে, কী বলে মানুষকে খ্যাপালে বোকা বানালে ভোট সাগরটা পার হওয়া যায়। পারের খেয়া অবশ্য আছেই, সত্যি ভোটের ওপর নির্ভর করবার দরকার পড়ে না। তবু একটা বাইরের ঠাট বজায় রাখতে তো হয়! বলতে হয় এসো এসো ভোটারগণ, শুনে যাও— ধান বুনলে ধান দেব, কালো গোরুর দুধ দেব, কাতলা মাছের মুড়ো দেব আর দেব কী? দেশ জুড়ে ছাপ্পা ভোটের জাল রেখেছি। লাস্ট সেন্টেন্সটা অবশ্য উহ্য।
—একটু ভেবে দেখিস রুণু। এখনও পর্যন্ত টাকাটা আর তোর দাদার অফারটা আছে। তুই যে-সব কথা বললি, ঠিক কথাই বলেছিস। কিন্তু তবু তার মধ্যে দিয়েই তো মানুষ খাচ্ছে পরছে, রুজি-রোজগার করছে, জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে, কারও খুব ভাল, কারও খুব খারাপ হচ্ছে। বাইরের অবস্থা যা-ই হোক না কেন, জীবিকার চেষ্টা তো। আমাদের করতেই হবে! অর্থাৎ মা আমার কথাগুলো গ্রাহ্যই করল না।
বলতে পারতাম— মা, এই তোমাদের এই আমাদের দোষ। চারপাশে যা-ই ঘটে যাক আমরা একটা ক্ষুদ্র গেরস্থালি জীবন কাটিয়ে যাবার জন্যে আপ্রাণ করি। এতে করে আমাদের অদম্য টিকে থাকবার শক্তিও যেমন প্রমাণ হয়, তেমন আমাদের পাহাড়-প্রমাণ অসচেতনতা, অজ্ঞতা, অসাড়তাও প্রমাণ হয়। আর যদি সইতে না পারি? তা হলে একদিকে আছে গলায় দড়ি, ছারপোকা মারার ওষুধ, বহুতলের ছাত। আর অন্যদিকে পরিকল্পনাহীন, পরিচালনাহীন, আবেগ-সর্বস্ব জ্বলে ওঠা। মাঝখানে আমরা হলাম পিঁপড়ে, লক্ষ লক্ষ বছর বিবর্তনহীন বেঁচে আছি।
বললাম না। মা বেচারি ভাবছে মায়ের কথায় ছেলে যদি একটু সৎসাহস পায়। পাবেই, নিশ্চয় পাবে। ভাবুক, কয়েকটা দিন ও রাত মায়ের তৃপ্ত, টেনশনহীন কাটুক না, আমি কিছুতেই গদা-র খপ্পরে পড়ব না। গদাকে মাস-মাস তোলা দিয়ে যদি আমায় ব্যবসা করতে হয় তো তার থেকে আমার মৃত্যুই ভাল।
৯
পরদিন সাইটে গিয়ে দেখি দীপু আবার সেই থ্যাপাস থ্যাপাস হাওয়াই চটি, আর ন্যাতা মতো প্যান্ট আর পাঞ্জাবি পরে এসেছে। আমার চোখে বোধহয় রাগ, হতাশা, এগুলো পড়তে পেরে গেছিল। আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই বলল—চটিসনি রুণু, এক হাজার টাকা মাইনেয় কাবলি-স্যামসন হয় না, পাটভাঙা প্যান্ট শার্ট পরতেও সাবান লাগে, আয়রন লাগে। এতদিন মুক্তাটা করে দিচ্ছিল। এখনও ওকে বেগার খাটাতে আমার বাজে লাগে।
—তোর তা হলে বাজে-লাগা না-লাগা ব্যাপারগুলো আছে?
ও বলল, আলবাত আছে। মরমে মরে থাকি রে রুণু। তুই যবে থেকে সেই পাগলের ডাক্তার সিনহা না কী ওর কাছে নিয়ে যাচ্ছিস তবে থেকে আমার বেশ বিবেক গজিয়েছে।
—ইয়ার্কি মারিস না দীপু। এখানে এভাবে কাজ করলে কে তোকে মানবে?
—দূর। তুইও যেমন, কে কাকে মানছে এখানে?
—মানছে। আলবাত মানছে। এবার হঠাৎ সাইটে এসে কেউ যদি তোকে আমার বেয়ারা ভাবে?
—বেয়াড়া কিছু হবে না তাতে। তা ছাড়া আমি তো তোর বেয়ারাই।
—চমৎকার!
—কী আশ্চর্য! কবে থেকে দ্যাখ তুই যা যা হুকুম করছিস তামিল করে যাচ্ছি। চাকরি নে, চাকরি নিলুম। জামা-কাপড়-জুতো কেন, জামা-কাপড়-জুতো কিনলুম। পাগলের ডাক্তার দেখা। পাগলের ডাক্তার দেখালুম— এতেও যদি বেয়ারা না হয়…
আমি হাল ছেড়ে দিই। কলোরস বলেছিল বটে—সেয়ানা পাগল! এক একটা মানুষ আছে যেন জুতোর সুকতলা, যেমন বেঁটেদা, নুয়েই আছে। এক এক জন আছে মানিয়ে চলে, কত ধানে কত চাল বোঝে, কম্প্রোমাইজ করে, কিন্তু একটা সীমা পর্যন্ত যেমন আমি, আর এক একটা মানুষ আছে যাদের তুমি কিছুতেই কাণ্ডজ্ঞান, ধানচালের হিসেব শেখাতে পারবে না, একরোখা একবগ্গা, কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, অথচ গুণ আছে, যোগ্যতা আছে— দীপে শালা এই জাতের। একেক সময়ে মনে হয় পায়ের চটি খুলে বেধড়ক পিটি। কিন্তু ওই! সীমা! একটা সীমা পর্যন্ত আমি নামতে বা উঠতে, রাগতে বা না-রাগতে পারি, তার এ দিক ও দিক আমার কাছে ব্ল্যাঙ্ক, একটা কালো পাথরের দেয়াল। আমাকে আটকে দেয়।
বিকেল সাড়ে চারটেয় আমি চলে আসি। দীপে তার পরেও কিছুক্ষণ থাকে। সারাদিন আমাদের কাছে হবু ফ্ল্যাট-ওনারদের যাওয়া-আসা। কবে কাজ শুরু হবে, তারা অ্যাট অল ফ্ল্যাট পাবে কি না। সময় পেরিয়ে যাবে, জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, প্রোমোটার যদি এসক্যালেশন চায়? আপনিই ভেবে দেখুন ভাই, সেটা কি উচিত হবে? কী বলছেন দাদা। আচ্ছা বুদ্ধি তো আপনার? বলেছে ডিসেম্বরে পজেশন দেবে। বড় জোর এক মাস কি দু’ মাস পেছোতে পারি, নইলে টাকা ফেরত চাইব। ভেবেছে কী চাকলাদার? আপনারা মশাই পাঁচ রকম কথা বলবেন না, ইউনাইটেড থাকুন, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। যেমন যেমন বাড়ি এগোচ্ছে টাকা দিয়েছি, টোয়েন্টি পার্সেন্ট, থার্টি পার্সেন্ট, ফিফটি পার্সেন্ট। যেই ঢালাই হয়ে গেল, এখন বলবে বাড়ি দেবে না? চাকলাদারের ছাল তুলে নেব। এইসব কথা সারাদিন আমাদের আশে-পাশে টরে-টক্কা, টরে-টক্কা করে, দীপে বসে বসে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকোয়। আমি বলি— আমাকে কেন বলছেন?
—বলব না মানে? আপনি চাকলাদারের রিপ্রেজেন্টেটিভ নয়?
—না। আমি জাস্ট সাইটে উপস্থিত থাকি, এই সব খোলামেলা তো!
—ওই হল। ঠিক আছে সাততলা নিয়ে ডিসপিউট আছে, অন্যগুলো হোক।
এক ভদ্রলোক ককিয়ে উঠে বললেন— বলেন কী! আমার যে সাততলাতেই। হরি, হরি আপনারা শেষ পর্যন্ত পড়শি হয়ে পড়শির সব্বোনাশ করছেন?
শেষ পর্যন্ত আমাকে বলতেই হয় একটা না একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। একটু হয়তো দেরি হবে। এই যা! হবে না মানে? এটা তো মগের মুলুক নয়!
বলেই আমি জিভ কামড়ে ফেলি! মায়ের সঙ্গে আমার তর্কাতর্কি বা বলা ভাল মায়ের প্রতি আমার দীর্ঘ লেকচারটা মনে পড়ে যায়। সেখানে প্রতিপাদ্য ওইটাই ছিল— দেশটা পুরোদস্তুর মগের মুলুক। পুরো কেঅস। মাৎস্যন্যায় চলছে। বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খাচ্ছে। বেশি পাওয়ারফুল কম পাওয়ারফুলকে, ধনীতর দরিদ্রতরকে, পেশিবাজ অপেশিবাজকে… এই ভাবেই…।
থার্ড মাসের মাইনেটা হাতে এসেছে, আমরা এখন পালা করে করে আবার নিতাইকাকা বিশুদা করছি, দীপু আমাকে ঝুপসি গাছটার তলায় ডাকল। আমি প্রমাদ গনি—
—কী রে, ভয়েস?
—না, ইনফর্মেশন।
—কে দিলে? বিশুদা?
—না, আমার দুটো চোখ, দুটো কান, নাকের ফুটো।
—কী ইনফর্মেশন?
—রাত্তিরে সাইটে সিকিওরিটি কে থাকে জানিস?
—কে?
—জনাব সমশের আনোয়ার।
—সত্যি? যাঃ। চাকলাদার যে বলেছিল সংস্থা থেকে লোক নেবে!
—নিয়েছে তো! পাড়া-মস্তানের চেয়ে ভাল সিকিওরিটি হয়? শামু একটা সংস্থা নয়?
—তুই কী করে জানলি?
—আমি ছ’টা বাজলেই ফিরে যাই। কোনওদিনই সিকিওরিটি তখন আসে না। বালি ছাড়া অন্য মালগুলো তো আমরা নীচের হলে ঢুকিয়ে দিয়েছিই। বারো লিভারের দুটো তালা মেরে বেরিয়ে আসি। যে ওই দুই তালা তোড়তে পারবে সে আমাকেও পটকে দেবে শালা। কাল একটু দেরি হয়েছে। দেখি শামু আসছে জিনস পরা, গায়ে কালো হাতাঅলা গেঞ্জি না টপ, মুখে সিগারেট, চুল পরিষ্কার আঁচড়ানো। কোমরের কাছটা যেন কেমন ঠেকল। নির্ঘাত রিভলভার। আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে মিনিট পনেরো স্রেফ বাওয়ালি করে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম— কোথায় যাচ্ছিস?
বললে— ফুফার বাড়ি, স্ট্রোক হয়েছে, দেখতে যাচ্ছি। তা তুই বাড়ি যাবি না? হাজার টাকা মাইনে দিয়ে চাকলাদার তোদের কি কিনে রেখেছে?
—না, এবার যাব বলে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছি। শামুও অনেকটা চলে গেছে। কিছুদূর গিয়ে বাঁকের মুখে হঠাৎ কী মনে হল— চোখ ফিরিয়েছি, দেখি কী শামু ডাবল-ব্যাক করে আসছে, তারপরে সাজানো ইট আর বালির ঢিবির পেছন দিয়ে নিঃসাড়ে ভেতরে ঢুকে গেল।
—তা তুই কী করে বুঝলি ও-ই সিকিওরিটি? অন্য কোনও মতলবে ঢুকেছিল এ-ও তো হতে পারে!
—দ্যাখ রুণু ওস্তাদ সমশের আনোয়ার ছিঁচকে চুরি করতে পড়ো বহুতলে ঢুকবে না এটুকু বোঝার শক্তি যদি আমার মতো হাফ-পাগলের থাকে তো তোর মতো কোয়ার্টার-পাগলেরই বা থাকবে না কেন?
আমাকে ভাবায় কথাটা। কিন্তু ছিঁচকে চুরির কথা হচ্ছে না। অন্য কোনও। অন্য কিছু…
—আচ্ছা দীপু এটা তো গদার এরিয়া, গদার এরিয়ায় শামুকে সিকিওরিটি…
—হতে পারে গদার এরিয়া। কিন্তু শামু হল পাতি-গুণ্ডা, হোয়্যার অ্যাজ গদা হল হাই-ফাই। মাফিয়া-টাফিয়া বলা যায়। শামু এই সাইটে একটা নাইটওয়াচের চাকরি পেলে তাকে হাম্পু দেবে এত ছোট দিল গদার নয়। ওরাও কতকগুলো এটিকেট মানে। বুঝলি? তা ছাড়া যে মুহূর্তে শামু বাড়িটার ভেতরে গুপ্তি হয়ে গেল, আমি…
—ভয়েস শুনলি?
—এগ্জ্যাক্টলি।
আমি জানি, গদার প্রতি দীপুর একটু, মানে তিল পরিমাণ হলেও পক্ষপাতিত্ব আছে। কেন না, দীপুর মা গদার বাড়িতে রান্না করতেন, গদারা ওঁকে ভালই মাইনেকড়ি দিত। সম্ভবত ব্যবহারও ভালই করত; এমনকী বেশি মাইনের জন্যে যখন মাসিমা মহাজনদের বাড়ি চাকরি নিলেন, গদারা রাগ করেনি। ওদের মধ্যে আসা-যাওয়া আছে। কে জানে মাসিমাকে দরকারে হয়তো ওরা ধারকর্জও দিয়েছে কিংবা দান-খয়রাত! হয়তো সেই পক্ষপাতিত্বের জন্যেই দীপু ও সব এটিকেট-ফেটিকেটের ভাঁওতা দিল। আমার যদ্দূর ধারণা গদার অভিজাত মাফিয়াগিরির আভিজাত্য ওই ছুরির ধার পাতলুন আর রসগোল্লা-লোফা মুখটুকুনিতে। সিকিওরিটিম্যানের চাকরিটা কি আর গদা নিজে করবে? ওর সেই কার্ডবোর্ড বাক্সের কারখানার ওয়ার্কাররা তা হলে আছে কী করতে? যাদের আমি আমার গারাজের ইম্যাজিনারি ‘সুধা-স্টোর্স’-এ তোলা নিতে আসার দিবা-দুঃস্বপ্ন নিশা-দুঃস্বপ্ন দেখি! এলাকার পজেশন, মোড়লি, খবর্দারির অধিকার কি কেউ রাইভ্যালকে ছাড়ে?
যাই হোক শামু সিকিওরিটিতে রইল, কি গদার গদারু সিকিওরিটিতে রইল তাতে আমার কীই-বা আসে যায়?
চাকলাদার লোকটা সম্পর্কে আমার কোনওদিনই কোনও মোহ ছিল না। জগাদা-বলাদাকে দাঁড় করিয়ে যেভাবে ও পাবলিকের ঝাড়টা এড়িয়েছিল তাইতেই বোঝা গেছিল লোকটি এলেমদার। জগাদাও যেভাবে ঘটনাটাকে ইউজ করে নিজের আখের গুছিয়ে নিল, তাতেও পরিষ্কার দু’জনের মধ্যে একটা আঁতাত থাকা সম্ভব। তবু ব্যাপারটা হজম করতে পারছি না। নিজের তৈরি ফ্ল্যাট নিজেই লিগ্যাল পয়েন্ট অন্যকে দিয়ে তুলিয়ে বন্ধ করা, ভাঙানো… হাম্পুটা ঠিক কার কার পেছনে? পয়লা নম্বর লুজার গুহমজুমদাররা। তারা আশা করে আছে তাদের পৈতৃক বাড়িটি ডেভেলপ করিয়ে তারা এখানে আলাদা-আলাদা ফ্ল্যাটও পাবে আবার হাতে কিছু টাকাও পাবে। সে গুড়ে বেশ বালি পড়েছে। দোসরা লুজার এই ফ্ল্যাটের হবু ওনাররা যাঁরা হয়তো সারা জীবনের সঞ্চয় ঢেলে এখানে একটা আশ্ৰয় তৈরি করার আশায় আছেন। এটা অবশ্য পুরোপুরি এম আই জি ফ্ল্যাট নয়, প্রতি ফ্লোরেই একটা করে দেড় হাজার স্কোয়্যার ফুটের আছে। সেগুলো শুনেছিলাম ঘ্যাম হবে, তাদের কেউ কেউ হয়তো অনেক সম্পত্তির মধ্যে এটা একটা জাস্ট করে রাখছে। কিন্তু সেটাও তো লোকসান। এটাও আমার আশ্চর্য লাগছে শামুকে রাতের সিকিওরিটিতে রেখেছে, ঠিক আছে। তো সেটা নিয়ে এত লুকোছাপার কী আছে? শামু মস্তান তাকে সবাই ভয় পায়, ঠিক আছে, কিন্তু সে আমাদের দোস্ত-ও তো বটে! সে একটা কাজ পেলে আমাদের আপত্তি থাকবার কথা না। তবে? সেই ফিরে-ফিরে গদার প্রসঙ্গই আসছে। আমাদের নয়, গদাকে লুকোতে চাইছে চাকলাদার, কেন না গদা এই এরিয়ার লর্ড। আচ্ছা, গদার লোক রাখতেই বা চাকলাদারের কী অসুবিধে ছিল?
জট পাকানো মাথা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে পৌঁছে গেছি বিশুদার ওয়েটিংরুমে। এত অন্যমনস্ক ছিলাম যে এতটা পথ কখন পার হয়েছি, কখন ওয়েটিংরুমে ঢুকেছি, একটা কাগজ হাতে তুলে নিয়েছি, বুঝতেই পারিনি। যেন একটা মেশিন। একটা অভ্যাসে ফিট হয়ে গেছি। হুঁশ হল যখন কাগজে দেখলাম শনিতলার মোড়ে খুব ঝামেলা হয়েছে। লোক্যাল লোক নাকি খেপে গিয়ে কয়েকটা সাধারণ মজুরকে পিটুনি দিয়েছে। ব্যাপার হল ওখানকার বিখ্যাত সাত বিঘের তালাও—তিন বিঘে কবেই বুজে মজে গেছে কেউ খেয়ালও করেনি, বাকি পাঁচ-বিঘের বিশাল ঘোড়ার খুরের মতো দিঘিটাতে লোক্যাল সবাই কাপড় কাচা, বাসন মাজা, শৌচকার্য, চান করা সবই চালাত। একদিন সকলের খেয়াল হয় দিঘিটা আরও ছোট হয়ে গেছে, অর্থাৎ দিঘিটা ভরা হচ্ছে। রাত জেগে পাহারা দিয়ে ওরা ধরে ফেলে নিশুতি রাতে ট্রাকের পর ট্রাক রাবিশ মাটি সব ফেলা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে। ওরা দেখতে পেয়েছে টের পেয়ে ট্রাকগুলো উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করে। কয়েকটা মজুর ঝুড়ি হাতে ধরা পড়েছে। পাবলিকের হাতে তারা প্রায় আধমরা।
শনিতলার মোড় আমাদের এখান থেকে দশ মিনিটের রাস্তা। তালাওটাও আমরা যথেষ্ট চিনি। জায়গাটায় প্রচুর ঝুগগি-ঝুপড়ি আছে। দু’-চারখানা পাকা বাড়ি আর একটা মিশ্র বস্তি। ওইখান থেকে আমাদের কলের মিস্ত্রি, কাজের লোক, ধোপা, ছোটখাটো কাঠের ছুতোর স-ব আসে। বেশি কথা কি বেঁটেদা ওইখানেই থাকে। নিমকি নামে সেই ধিঙ্গি মেয়েটাও থাকে ওই বস্তিরই বেঁটেদার উল্টোদিকের প্রান্তে। আমি সশব্দে বলে উঠেছি—আচ্ছা মজুরগুলোর কী দোষ?
পাশ থেকে পতিতকাকা বলে উঠলেন: কে মজুর? কেন মজুর? কী দোষ?
আমি বলি, কাকা শনিতলার তালাওটার খবরটা পড়েননি?
—শনিতলা? আমার কপালে যে শনি গেঁড়ে বসে আছে তার পরে আবার শনি? কাকা একটা ‘যেতে দাও’ ‘যেতে দাও’ ভঙ্গি করলেন হাত দিয়ে।
আমার কিন্তু খবরটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগল। এরকম খবর আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। আবার এ-ও দেখা যায় কোনও না কোনও রাজনৈতিক পার্টির অর্থাৎ যারা জনগণের কাছে ফ্রম টাইম টু টাইম ভোট চায় তাদের একাধিক কেডার এমনকী ছোটখাটো আঞ্চলিক নেতাও এর ভেতরে আছে। রুই কাতলা রাঘব বোয়ালও পেছনে থাকে— টের পাওয়া যায় বেশ। কীভাবে কেউ এ সবের মধ্যে থাকতে পারে, মানে কেমন করে ক্ষমতাটা হয়, কী ভাবে সেটা প্রয়োগ করে, কীভাবে সাকসেসফুল হয়, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। আসলে আমি তো আদার ব্যাপারি, বড় বড় জাহাজের কাণ্ডকারখানা কী বুঝব! আমার আংশিক সুপারভিশনে তৈরি বাড়িটা কর্পোরেশন ভাঙছে, হবু মালিকরা কপাল চাপড়ে হাহাকার করছে তাতেই আমি যেন চোর দায়ে ধরা পড়েছি, ভীষণ একটা অপরাধবোধ জাগছে মনের মধ্যে এত দুর্বল আমি। কাওয়ার্ড বললেই হয়। সেখানে কোনও জনগণের কাছে ভোট চাওয়া পার্টির লোক কতটা সাহস থাকলে জনগণের পুকুর বোজাতে নামতে পারে? ধরুন, পুকুরটা কার? কারওর না কারওর তো বটে! যদি কারও ক্লেম না থাকে তা হলে সরকারের খাস? তা-ও যদি না হয় তা হলে পুকুরকে জিজ্ঞেস করতে হয়— পুকুর তুমি কার? চারপাশে উবু হয়ে বাসন ধুচ্ছে ঝোপড়ির মেয়ে-বউরা, চান করছে মরদ, সাঁতার কাটছে বালক-বালিকা, এখন এরা তো বলবে— এ পুকুর আমার! পাবলিক প্লেস যাকে বলে! কার থেকে কিনল তা হলে এরা পুকুরটা! জনগণ বিক্রি করেনি। সরকার ঘোষণা করে দিয়েছে কোনও জলা দিঘি পুকুর ফটাফট বোজানো চলবে না। তা হলে সরকারও বিক্রি করেনি। এখন ব্যক্তিগত বা শরিকি মালিকানা কার? কাদের? তাদেরই খুঁজে পেতে পুকুরটা এরা কিনেছে না কি? রাবিশগুলো কোথা থেকে আনে? ট্রাক ভাড়া কত? মজুরগুলো কোন পাড়ার? সব আমার জানতে ইচ্ছে করে। নিজে তো পারিনি। পারি না। তাই অসীম কৌতূহল আমার এই সব পারগতা সম্পর্কে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ছুটে চলে যাই, সব জেনে নিই। মৃতপ্রায় মজুরগুলো? মরে তো আর যায়নি। মৃতপ্রায়! ও ঠিক বেঁচে উঠবে। ওদের কাছ থেকে তখন কিছু কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে, এখন ধরুন আশপাশের অনেক লোকই আমার চেনাশোনার মধ্যে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি জানতে পারা যায়! মানে এই পুকুর-চুরি জাতীয়। কীভাবে কী করা যায়! নট দ্যাট আমিও পুকুর-চুরিতে নামতে যাচ্ছি। কিন্তু এই যারা চিট ফান্ড খুলে রাশি রাশি লোকের বিশ্বাস ভাঙিয়ে কোটি কোটি টাকা করে, এইভাবে পুকুরকে পুকুরই লোপাট করে দিতে পারে তাদের আই কিউ তাদের গাটস আমাকে অবাক করে। আমার মনে হয় তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করি— আচ্ছা দাদা। একটা সত্যি সত্যি ভাল বিশ্বাসযোগ্য ব্যাঙ্ক, কী একটা ভাল দেখে পুকুর পরিষ্কার করা, নদী ড্রেজ করা এগুলোতে কী আরও বেশি আই কিউ, বেশি গাট্স লাগে? যদি তা না-ই লাগে তা হলে সেটা না করে এইটা করলেন কেন দাদা! মানে চয়েসটার কারণ কী? রিস্ক ফ্যাক্টরটা তো এটাতে বেশিই থেকে যায়, তাই না? তা হলে? কারণটা কী? ফাঁকা থেকে টাকা? আরে দাদা গরিব-গুরবো লোকের বিশ্বাস অর্জন করতেও তো খ্যামতা লাগে, সে খ্যামতা ধরেন, সেটা ভাঙিয়ে লোকগুলোর টাকা আত্মসাৎ করবার পর নিজের ছেলে-মেয়ে মা-বাবার মুখের দিকে তাকাতে অসুবিধে হয় না? ধরুন আমি এমনই একটা কিছু করলাম, আমার সে আই কিউ নেই তবু ধরুন করলাম। করে টরে সচিনের পোস্টার হাতে বাড়ি ঢুকছি। এমন সময়ে আকাশ থেকে একটা বিরাট সোনালি বেলুন নামছে। নামছে নামছে হেলতে-দুলতে। সবাই তাকিয়ে আছে, উঁচুর দিকে মুখ, নামল বেলুনটা, রিন্টি সচিনের পোস্টার আঁকড়ে পিন ফুটিয়ে দিল বেলুনটার গায়ে, ফটাস করে ফেটে গেল বেলুন আর তার জায়গায় পড়ে রইল স্তূপীকৃত টাকা টাকা টাকা, সোনা সোনা সোনা। কার বেলুন? বাবার অদৃশ্য মুখ বলে উঠল, …আ…আ…আমার। মা বলল— কোথা থেকে পেলি রুণু? দাদা বলল অসম্ভব গম্ভীর গলায়—কী ব্যবসা তোমার? বউদি ঢুকে যাচ্ছে নিজের ঘরে। নির্বাক, ভীত। রিন্টির হাত থেকে সচিনের পোস্টারটা পড়ে গেল। অত কম আঘাতেও ফুটো হয়ে গেছে উঠোনের মাঝখানটা। ধোঁয়া উঠছে, ধোঁয়া। তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে নিজের খয়রা মাছ আমার পাতে-তুলে-দেওয়া মা, পূর্ব রেলের পেটি ক্লার্ক দাদা যে নাকি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার করে আমাকে টাকা দিতে চাইছে ব্যবসা করবার জন্য, মাথায় গামছা-বাঁধা ছোট্ট ইয়ার্কি মেরে মন ভাল করে দেওয়া বউদি আর…আর…কাকু—আমাকে একটা সচিনের পোস্টার কিনে দাও না কচি গলার এই আবদার। গর্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি আমি, আমার বেলুনের মৃতদেহ আমার টাকা টাকা টাকা সোনা সোনা সোনা স-ব স-ব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
১০
বিশু কাকার অ্যাটেন্ড্যান্ট ঝানুদা এই সময়ে এসে ডাকল— রুণু, এই রুণু! বোধহয় কয়েকবার ডেকেছে। আমি একেবারে অন্যমনস্কভাবে ধোঁয়াভরা একটা গর্তে পড়ে যাচ্ছিলাম, শুনতে পাইনি।
—কী রে? পীরিত-টিরিত মচাচ্ছিস? না কি?
—অ্যাঁ? আমি একেবারে চমকে উঠেছি।
—তোকে বিশুদা ডাকছে।
আইব্বাস! বিশুদা আমাকে আউট অফ টার্ন ডাকছে! শালা! কপাল খুলে গেল মনে হচ্ছে!
ভেতরে ঢুকে দেখি ধবধবে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা বিশুদা এগজিকিউটিভদের ঘুরন-চেয়ারে। বিশুদা বোধহয় এভরি-ডে একটা নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। এক্কেবারে আনকোরা নতুন। না হলে এত কড়কড়ে এত সাদা হওয়া সম্ভব নয়। অনেক রকমের নীল-ফিল আমি ব্যবহার করে দেখেছি— ও রকম হয় না। এ খাতে বিশুদার খরচ কত কে জানে? সে যতই হোক, পাবলিক দেবে। বিশুদা ওয়েটিং রুম দিয়েছে। পাবলিক ওকে পায়জামা-পাঞ্জাবিটুকু আর দিতে পারবে না?
বিশুদা বললে— আয় আয় রুণু। বোস। ওই পড়ো বাড়িটাতে এখনও পড়ে আছিস? —আমার মুখে কোনও দুঃখ কিংবা খোশামোদের বাক্য কেন যেন আসে না। বলি— এ-ই! একটু হাসি।
—তোকে একটা কাজ দিচ্ছি। দ্যাখ দিকি করতে পারিস কি না!
বুকের ভেতরটা লাফিয়ে ওঠে উড়ুক্কু মাছের মতো। কী কাজ? এল ডি সি না এইচ ডি সি? না কি আরও ভাল কিছু!
—বাইরে পতিতকাকাকে দেখলি?
—হ্যাঁ।
—কেমন দেখলি?
—ফ্রাষ্ট্রেটেড দেখাচ্ছিল।
—পাঁচ বছর রিটায়ার করে গেছে। পেনশন পাচ্ছে না। শালার সরকার যা এনেছিস না! পতিতকাকাকে দেখ, তোর নিজের ফ্রাসট্রেশন কমে যাবে। পাঁচ বছর পেনশন নেই। মানে রোজগার নেই। পঁয়ষট্টি বছর বয়স হল, সেটা সার্টিফিকেটে। কোন না আরও দু’চ্চার লুকিয়েছে মানে সত্তরের কাছে গেছে বয়স। নো রোজগার। হেঁটে-হেঁটে জুতো ক্ষয়ে গেল। আমি একটা চিঠি দিচ্ছি। তুই ওঁকে নিয়ে হুগলি ডি-আই অফিসে যা। একা পাঠাতে সাহস পাচ্ছি না, বুঝলি। কমজোর, হতাশ লোক। ট্রেনে অক্কা পেলে মুশকিল আছে। যাকগে তুই ওঁকে সঙ্গে করে হুগলি ডি-আই অফিসে নিয়ে যাবি। ডি-আইয়ের হাতে চিঠিটা দিবি। অন্য কারও হাতে দিবি না। কেষ্ট বলে একটা খচরা আছে, সেই কেস ঘুলোচ্ছে কাকার স্কুলের সঙ্গে যোগসাজশে। তার হাতে দিবি না। নতুন ডি আই লোকটা নিরপেক্ষ। যদ্দূর শুনছি। দ্যাখ দিকিনি গিয়ে!
যাব্বাবা! চাকরি ভেবে এসেছিলাম। জুটল বেগার? পতিতকাকার এমন অবস্থা যে ট্রেনে পটোল তুলতে পারে! মুশকিলটা তো তখন আমারই হবে। বিশুদা পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করল— এই নে তোর পথ খরচা। —তবু ভাল।
উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পা ঠুকে একটা মিলিটারি সেলাম ঠুকি। —জো হুকুম। বিশুদা দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে হাসে, বলে— দ্যাটস লাইক এ গুড বয়।
পতিতকাকা বললেন— দিয়েচে? সত্যি বলচো রুণু, বিশু শেষ পর্যন্ত দিল? ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যে! তার ওপর তুমি সঙ্গে যাচ্চ। খুব একটা রিলিফ হচ্চে। ট্রেন ধরতে, ভিড় ঠেলতে, দাঁড়াতে যেন আর জোর পাচ্চি না। তোমার খুব অসুবিদে করে যাচ্চ না তো!
—না না। আমি তো বেকার বসে আছি।
একবার ভাবলাম পাতাল রেলে যাই। এসপ্লানেড থেকে হাওড়ার বাস ধরব। টার্মিনাস, বসতে পাওয়া যাবে। কিন্তু পতিতকাকাকে বলতে তিনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন— ওরে বাবা অত সিঁড়ি নামতে উঠতে বাবা আমি পারব না। শেষ পর্যন্ত রথতলার মিনিতে এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিটে অর্থাৎ বারোটা পাঁচে হাওড়া পৌঁছোই। কী ভাগ্য বর্ধমান লোক্যাল তখন দাঁড়িয়ে ছিল, কাকাকে দাঁড় করিয়ে দৌড়ে টিকিট কেটে আনি। একটা কামরায় যদি বা উঠে পড়েছি লাস্ট মিনিটে দেখি দুটো বেঞ্চি জুড়ে এক দল ছেলে তাস খেলছে। আচ্ছা তো! কাকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্রোতের মতো ঘামছেন।
বিবেচনার আশায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে উত্ত্যক্ত হয়ে অবশেষে বলি— একটু সরে বসুন। বয়স্ক মানুষ দাঁড়াতে পারছেন না।
একজন বললেন— আচ্ছা রবিন, এতক্ষণ তোমার হাতে ইস্কাবনের সাহেব নিয়ে বসে আছ? নাও এখন ট্রাম্পড্ তো হয়ে যাবেই! তোমার মতো গর্দভের সঙ্গে বসা মানে…।
—আরে চটছ কেন— আর একজন বলল— রবিন নভিস এটা তো মানবে? একটু ধৈর্য ধরো। সবে তো রং চিনল!
আমি আর দ্বিতীয় কথা বলি না। ঠেসে এক জনকে সরিয়ে দিয়ে পতিতকাকার জন্যে জায়গা করে দিই। সসংকোচ সেখানে বসে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে যাবেন, ঠেসা লোকটি ধাঁ করে ঘুরে বসে আমার দিকে কয়েকটা বারুদের গোলা ছুড়ে দিল। বেশি বয়সও নয়। আমার থেকে জোর বছর পাঁচেকের বড়।
—আস্পদ্দা তো কম নয়? তুমি কে হে বাহাদুর?
আমি বলি— তোমার যম। কে যেন আমার মুখ দিয়ে কথাগুলো ঠেলে বার করে দিল।
—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। অন্য একজন মারমুখো হয়ে ওঠে। ঠেসা লোকটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে— তুমি? তুমি বলছ? যম?
আমি বলি— হ্যাঁ, তুমি ‘তুমি’ বললে আমাকেও বলতে হয়। আর ‘যম’টিও এগজ্যাজারেশন নয়। বিখ্যাত প্রোমোটার আর চাকলাদারকে চেনো? আমি তার চিফ সিকিওরিটি ম্যান। বিশ্বনাথ মল্লিককে চেনো, এম এল এ আমি তাঁরও মাসলম্যান। বেশি গড়বড় করলে… কথা শেষ করি না। তারপর বলি— আমার সঙ্গের ভদ্রলোক বয়স্ক অসুস্থ, ওঁকে বসতে দিতে হবে। ট্রেনটা তাস পেটবার জায়গা নয়। নিজেদের কোলের ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে যত খুশি খেলো না, কে বারণ করেছে? অন্য লোকের জায়গা হাম্ করতে দোব না। সমস্ত কথাগুলোই বলি খুব শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে।
তাস পার্টির একজন মাঝবয়সি লোক বললেন— তুমি সেদিনের ছোকরা। আমাকে ‘তুমি’ করে বলছ।
—আপনারা ‘আপনি’ বললেই আমিও আপনি বলতে পারি। এই তো দেখুন, শুরু করে দিলাম।
গুম হয়ে চার বর্ধমান-যাত্রী তাস-টাস তুলে বসে রইল।
পতিতকাকা খুব ঘামছেন। আমি বলি— কিছু যদি মনে করেন—আপনাদের কারও কাছে খাবার জল আছে?
মাঝবয়সি ভদ্রলোক একটা প্লাস্টিকের বোতল বার করে দিলেন। আমি সামান্য একটু জল পতিতকাকার ঘাড়ে-মুখে ছিটিয়ে দিই, বলি—হাঁ করুন কাকা, একটু জল খান।
—আমার লাগবে না বাবা।…
—আপনি এখন আমার রেসপনসিবিলিটি কাকা, যা বলব শুনতে হবে। হাঁ করুন, দেখি। —খানিকটা জল খাইয়ে বোতলটা ফেরত দিই। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস দাদা!
ভদ্রলোক একটু নড়েচড়ে বসেন। বোতলটা তখনও হাতে ধরা।—আপনি একটু খাবেন নাকি?
—আমি বলি, না, আমি চালিয়ে দিতে পারব।
—খান না।
—দরকার নেই। থ্যাঙ্কস।
হুগলি স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্ম হেঁটে রিকশা ধরেছি, পতিতকাকা বললেন, বাপরে। তুমি কি সত্যিই ওই চাকলাদার লোকটার সিকিওরিটিম্যান না কি? রুণু?
আমি হেসে বলি— যেমন বিশুদার মাসলম্যান তেমনি আর কী? কী জানেন কাকা, এই লোকগুলো আসলে কাওয়ার্ড। এদের ভয় দেখাতে হয়।
—আমি তো ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছি। ট্রেনে কলার ধরে তোমাকে দু’ঘা দিলে তো…
—আরে গতস্য শোচনা নাস্তি। কাকা, যা হয়ে গেছে বা যা হতে পারত হয়নি— তা নিয়ে বৃথা ভাববেন না।
ঠুনঠুন রিকশা চলেছে, পতিতকাকা বললেন— বেশ বলেছ বাবা, ‘যা হতে পারত হয়নি’ ‘বৃথা ভাবনা’ বেশ বলেছ! দেখো তুমি সাকসেসফুল হবে।
—আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক কাকা। এখন যে কাজে চলেছি সে কাজে আগে সাকসেসফুল হই!
—আশা খুবই কম রুণু। পাঁচ বছর হয়ে গেল। স্কুলের সব্বাই পেয়ে গেছে, আমার পরে হেডমাস্টারমশাই রিটায়ার করলেন, নিজের খাতাপত্র সব আপ-টু-ডেট করে রেখেছিলেন, সার্ভিস বুকও সার্ভিস শেষ হবার আগেই আন-অফিসিয়ালি জমা পড়ে গেছিল, মাসখানেকের মধ্যে সব পেয়ে গেলেন। নির্লজ্জতাটা ভাবতে পারো? একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হেড অন্যদের বাদ দিয়ে নিজেরটা গুছোচ্চে?
—অন্যরাও সব পেয়ে গেল তো বলছেন, আপনি কি হেড মাস্টারের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন?
—দূর দূর, তুমিও যেমন? ঝগড়া করার দম-আমার আচে? টুইশনিতে ডুবে আছি।
—কেন পতিত কাকা, এখন তো আপনাদের স্কেল ভাল হয়ে গেছে।
—আরে সময়মতো মাইনেটা কবে পেয়েছি বলো! তা ছাড়া আমাদের এজ গ্রুপ বেনিফিট তেমন পেল কই! ছেলেটাকে ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে বাঙ্গালোরে এঞ্জিনিয়ার হতে পাঠিয়েছি। ওর ঝোঁকটা আছে তো! তা খর্চা কত! মেয়ের বিয়ে গেল! গিন্নির হার্টের ব্যামো, জলের মতো টাকা বেরিয়ে যায়। প্রতিদিন ব্যাচ পড়াই, কোনওমতে চালিয়েচি, চালাচ্চি রুণু, যে কোনওদিন বুড়ো ঘোড়ার মতো পড়ব আর মরব!
—তা আপনাদের নতুন হেডমাস্টার?
—আরে সে তো আমাদের হাঁটুর বয়সি। কোনও কথাই শুনতে চায় না। খালি ফাজলামি! মাস্টারমশাই, আমি এখনও কিছুই জানি না। ক্লার্কদের হাতে। ওদের কথা শোনাতে পারছি না। আপনি একটু চেষ্টা করুন না! শুনলে অবাক হবে রুণু, আমি বুড়োমানুষ বিয়ারের বোতল কিনে দিয়ে এসেছি, তবে আমার পঁচিশ বছরের পরিচিত ক্লার্ক যুগলবাবু কাগজপত্রগুলো তৈরি করে দিয়েছেন।
ডি-আই অফিসে ঢুকে এই মতো কথাবার্তা হল।
কেষ্টবাবু—আপনি আবার এসেছেন?
—পাওনা-গণ্ডা তো কিছুই পাইনি, আসব না? গ্র্যাচুইটি, পেনশন, পাঁচ বছরের এরিয়ার, রিভাইজড স্কেলের…
—হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরো পৃথিবীটাই তো আপনার পাওনা।
আমি একটু এগিয়ে গিয়ে কড়া গলায় বলি—এত বাতেল্লা কীসের এখানে? অ্যাঁ? বহোৎ বহোৎ বাওয়ালি শুনছি!
চোখে যথাসম্ভব তাচ্ছিল্য নিয়ে কেষ্ট নামধারী বললেন—ইটি কে মাস্টারমশাই?
—ইটি ওনার বডিগার্ড। আমি বলি। —কেস কে হ্যাজাচ্ছে পাঁচ বছর ধরে দেখতে এসেছি।
—বাপরে, আপনি কি ভোটে-টোটে দাঁড়াচ্ছেন না কি, মাস্টারমশাই? এমন একখানা বডিগার্ড! —লোকটা চোখ কপালে তুলে যেন ভিরমি খাচ্ছে এমনি ভাবে বলল…
—আমি বলি—কিচাইন মাৎ কর, যা হয়েছে হয়েছে। ফার্দার লোকসান যাতে না হয় তাই এম এল এ সাহেব আমাকে ফিট করেছেন। ইংরেজি বাংলা সব কাগজের জন্য চিঠিপত্তর রেডি। নাম ধাম সুদ্ধ বের করে দোব। জার্নালিস্ট ফেউ লাগিয়ে দেব পেছনে, চাকরি নট, এঁর পুরনো হেডুর পেনশন বন্ধ। নতুন হেডুকে শো-কজ। মানবাধিকার কমিশন কেস করবে। সমঝ লিয়া!
—বাব্বা! তেল তো কম নয়? পলিটিক্যাল লিডার আবার সম্পাদকেষু আবার হিউম্যান রাইটস? ত্র্যহস্পর্শ যে দেখচি। —তাচ্ছিল্য লোকটার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। তারপর ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল—হুলিগান এনে ভাল করেননি মাস্টারমশাই।
পতিতকাকা একেবারে ভয়ে জড়সড় হয়ে বললেন—ও হুলিগান নয়, ভাই। আসলে ট্রেনে আজকে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে কতকগুলো লোকের সঙ্গে তাইতেই… রক্ত এখন গরম তো… আমার দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকালেন একবার।
আমি বলি—যাকগে ফালতু কথা ছাড়ুন, আমাদের ডি-আইকে একটা চিঠি দেবার আছে, বলে কাউন্টারের দরজা খুলে ঢুকতে যাচ্ছি, লোকটা হাঁ হাঁ করে তেড়ে এল, —কার হুকুমে এখানে ঢুকছ হে ছোকরা?
—আমার ওপরতলার নির্দেশ আছে সোজা ডি-আইয়ের কাছে গিয়ে চিঠিটা দিতে হবে। এখানে কেষ্ট বলে কে এক মাল আছে তাকে যেন ইগনোর করি।
রাগে টকটকে লাল হয়ে গেছে লোকটার মুখ। সেই অনুপাতে ফ্যাকাশে পতিতকাকা।
—আমাকে তুমি অপমান করছ? কোন সাহসে?
—আপনাকে তো কিছু বলিনি! সেই কেষ্টা লোকটা নাকি এক নম্বরের…
পতিতকাকা আমার কনুই টেনে ধরে বললেন—রুণু কী করচ? ইনিই কেষ্টবাবু!
—আপনিই? তাই বলুন। ভাবছিলাম পাঁচ বছর ধরে শিক্ষকের পেনশন আটকে রেখে আবার বাতেল্লা দেয় এমন মাল এখানে ক’টা আছে! ভাল, এখন যেতে দিন।
—জানো, মন্ত্রীর চিঠি পর্যন্ত আমার কাছেই দিতে হয়! মন্ত্রী আমাকে ফোন করলে তবে…
—বিশেষ ইনস্ট্রাকশান আছে আপনার কাছে না দিতে, মাস্টারমশাই আসুন, বলে ভেতরে ঢুকে যাই। ডি-আইয়ের ঘরের কাটা দরজা দিয়ে ঢুকি।
—নমস্কার সার, বিশ্বনাথ মল্লিক এম এল এ কি আপনাকে কোনও ফোন করেছিলেন? আমরা ওঁর চিঠি নিয়েই আসছি।
ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আসুন সার আসুন, আমি আপনার অপেক্ষাই করছিলাম। —আমি দাঁড়িয়ে থাকি। পতিতকাকা বসেন, দরদর করে ঘামছেন। আমি চিঠিটা এগিয়ে দিই, ভদ্রলোক জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলেন—জল খান, জল খান। ছি ছি ছি পাঁচ বছর ধরে…
—অন্তত পনেরোবার যাতায়াত করেচি ভাই। একবার ইস্কুল একবার ডি-আই অফিস। এখন এই রোদে খুব রিসকি হয়ে যাচ্চে আসা-যাওয়াটা। তাই বিশু এই রুণুকে সঙ্গে দিল। ভাল ছেলে। তবে অল্প বয়স তো! রক্ত গরম, অন্যায্য জিনিস সইতে পারে না। ও কেষ্টবাবুকে খুব চটিয়ে দিয়েচে।
—তাই নাকি? ডি-আই একটু হাসলেন—আমি তো চটাতে পারছি না, অন্য কেউ কাজটা করে দিলে ভালই। শুনুন মাস্টারমশাই, আপনাকে আর আসতে হবে না, কেষ্টবাবু অর নো কেষ্টবাবু মাস দেড়েকের মধ্যে আপনার পাওনা-গণ্ডা আমি বার করে দিচ্ছি। একদম ভদ্রলোকের এক কথা।
পতিতকাকার অবস্থা দেখে ভদ্রলোক রসগোল্লা আনালেন, নুন-চিনির শরবত সঙ্গে। —অত দূর এখন যাবেন, একটু খেয়ে নিন।
বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা খেয়ে নিই। কোন সকালে চা-মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছি। পতিতকাকাও নিশ্চয়ই এতদূর আসার জন্যে তৈরি হয়ে আসেননি।
বেরোবার সময়ে কেষ্টবাবুর পাশ দিয়ে দৃক্পাত না করে বেরিয়ে আসি। ভস্ম করে দিচ্ছে লোকটা। আমাদের দু’জনকেই।
আমি বলি—কাকা আপনি কি বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে বেরিয়েছেন!
—না বাবা। তুমি?
—আমিও না।
—চলুন স্টেশনে গিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।
—আমার লাগবে না। তুমি খাও, নিশ্চয় খাবে বাবা।
—আগে চলুন তো!
স্টেশনের কাছাকাছি একটা মোটামুটি দোকানে—ভাত, ডাল আর মাছভাজা খেলাম দু’জনে। আমার গ্যাঁটের কড়ি খর্চা করে। খেয়ে দেয়ে ছায়া-ছায়া দেখে একটা গাছের তলায় বসি, প্ল্যাটফর্মের ওপরেই। এক বোতল মিনার্যাল ওয়াটার কিনি।
পতিতকাকা বললেন—রুণু, কাজ হবে তো?
—আলবৎ হবে কাকা!
—কিন্তু কেষ্টবাবু যে!
—আরে বাবা ডি-আই তো নিজে বললেন কেষ্টবাবু অর নো কেষ্টবাবু!
—কী জানো এসব জায়গায় একটা ক্লার্কের যা প্রতাপ, অফিসারদের তা নেই!
—দেখা যাক। দেড় মাস তো টাইম দিয়েছেন!
—তুমি বাবা অত তেরিয়া মেজাজ না দেখালেই পারতে, কিছু মনে কোরো না।
—কাজ হবে কাকা, দেখবেন, গ্যারান্টি। ওই কেষ্টবেটা চোর আর কারও সঙ্গে অমন করতে সাহস পাবে না। কী জানেন? এসব প্রশ্রয় পেলেই বাড়ে। কাজটা যে খারাপ করছে এ জ্ঞান কি আর ওর নেই? আপনারা গিয়ে হাতজোড় করেন, বাপু বাছা করেন, তাতে ওর মীন ইগো ফুলে-ফেঁপে ওঠে। এখন ও প্রথমটা জ্বলবে, ফুঁসবে। তারপর বাড়ি গিয়ে নিজের অজান্তেই ভাববে। কেন অমন হল! আপনার মুখ, আরও যাঁদের যাঁদের সঙ্গে অমন করেছে সবার মুখ ওর চোখের সামনে ভাসবে। একটু না একটু শিখবেই ঘটনাটা থেকে।
—তোমার অনেক আশা রুণু, তোমরা সব ছেলেমানুষ, রক্ত গরম, আশা করো, স্বপ্ন দেখো, আমাদের ও পাট শেষ। রিয়্যালিটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছি।
আমি সাধারণত মাথা খুব গরম করতে পারি না। ইচ্ছে হল কাউকে আচ্ছা করে প্যাঁদানি দিই, কিন্তু ওই ইচ্ছে পর্যন্তই। ওই যে সীমা। আমার একটা সীমা আছে, কালো পাথরের দেয়ালের মতো! কিন্তু পতিতকাকার সমভিব্যাহারে আমার যে অভিযান তা সব অর্থেই দুঃসাহসী। ওঁকে ভাবিত মুখে বাড়ি পৌঁছে দিই। চারটে বাজছে, বাড়িতে আর ঢুকি না। সোজা সাইটে চলে যাই। দীপে বসে বসে ঢুলছে। আমি ওকে ঠেলে তুলি।
—কী রে সে-ই যে বিশুদার কাছে গেলি—একেবারে বেপাত্তা!
আমি স-ব বলি। তারপর চিন্তিত মুখে বলি—আচ্ছা দীপু, আমি কি হিরো-ফিরো হয়ে যাচ্ছি না কী বল তো! একটা কি চেঞ্জ আসছে?
দীপু অবাক গলায় বলল—যাব্বাবা, তুই তো বরাবরই হিরো! পাড়ার মেয়েগুলো সব তোর নামে মুচ্ছো যায়, আমার দুটো বোন, শামুর বোন, ওদিকে নিমকি আর শিমকি, গদার ভাগ্নী কুর্চি…
—থামলি কেন? আরও কতক চাট্টি বল।
—আরে এ তো গেল মেয়েদের কথা! ছেলেরা! ছেলেগুলোরও তো তুই হিরো—ধর সঞ্জু, বাদাম, মুস্তাফা, খলিল, রাজু, এই জুনিয়রগুলো তো আছেই, তার ওপর আছে তোর ব্যাচমেটরা যেমন ধর পানু, সত্য, শামু, গদা, আমি…।
আমি তেড়ে উঠি—আমাকে তোরা একটা গুডি-গুডি বাধ্য ভালমানুষ, যাত্রাদলের বিবেক গোছের ইমেজ দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছিস, না? দাঁড়া শালা, এমনি মুখ ছোটাব যে সমশের পর্যন্ত ঘাবড়ে যাবে!
দীপু বলল—সে তুই ছোটা না, তাতে করে তোর হিরো হওয়া আটকাচ্ছে না।
মনটা কেমন খিঁচড়ে গেল।
১১
প্রায়ই দেখি মণির সঙ্গে একটি অচেনা মেয়ে আমাদের বাড়ি ঢুকছে। কিংবা বেরোচ্ছে। মণি একটু হাসে—বউদির সঙ্গে দরকার ছিল। ভাল রে ভাল। আমি বরাবর তোর অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার মাধ্যমিকের বিদ্যেয় যেটুকু কুলোয় সায়েন্সও। হতে পারিস তুই ভাল মেয়ে, চট করে বুঝে নিস। আজকাল আর দরকার হচ্ছে না। তা বলে ‘বউদির সঙ্গে দরকার ছিল’ বলে মুখ মুছে চলে যাবি? অন্য মেয়েটি কেমন মুখ ফিরিয়ে থাকে, খুব চকচকে কালো। কিন্তু চুলের বেণী ছাড়া মাথার আর কোনও অংশ দৃশ্যমান হয় না। যাক গে বাবা, যা করছে করুক। আমার কী? ঘাড় থেকে নামলে আমি বাঁচি, বিনি পয়সার টিউশনি যত!
বউদিকে বললাম—আজকাল কোচিং ধরেছ না কি?
—বাঃ পয়সার দরকার না? বাড়ির একজন মেম্বার যদি শাশ্বত বেকার হয়।
—আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, তবে এ তো পয়সা-দেওয়া পার্টি নয়?
—মহানুভবতার কি মনোপলি নিয়েছ না কি?
যাব্বাবা, একবার বলছে পয়সার দরকার কোচিং করছে আরেকবার বলছে মহানুভবতার কেস। মহিলা বলতে চায়টা কী! এত কমপ্লিকেটেড এই মহিলা— কোনটা এর ফাজলামি, আর কোনটা সিরিয়াস আজও বুঝতে পারি না। ‘শাশ্বত, বেকার’ অন্য যে কোনও বউদির মুখে শুনলে যে কোনও বেকার দেবর রাগে খাওয়া-দাওয়া পরিত্যাগ করত। উল্টে দু’কথা শুনিয়ে দিত। আমার এই বউদিটি কিন্তু এই সব টার্ম খুব অভিসন্ধিমূলক ভাবে ব্যবহার করে। আমাকে এইভাবে গারাজে সুধা স্টোর্সের দিকে ও নিরন্তর ঠেলে। পরিষ্কার বুঝতে পারি। অফারটা নিচ্ছি না বলে ওর সমূহ দুশ্চিন্তা, আপত্তিও।
আরেকটু সন্ধে হলে রিন্টিকে নিয়ে বেরিয়েছি। আজ টুইশনি নেই। অনায়াসে ছেলেটাকে নিয়ে দু’-এক চক্কর ঘুরে আসা যায়। রিন্টিকে নিয়ে প্রবলেম হল, বেরোলেই কিছু না কিছু একটা ওর চাই। ওর ধারণা কাকা মানেই দোকানে যাওয়া, দোকানে যাওয়া মানেই ওর ধনী কাকার পকেট থেকে মালকড়ি বেরোবে, এবং ওর কিছু প্রাপ্তিযোগ হবে। দোকানপাতি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? বেরিয়ে এক চক্কর গিয়েছি কি না গিয়েছি দেখি পুলিশে পুলিশ। পিল পিল পিল করে পুলিশ বেরোচ্ছে। আমি শাঁ করে কেটে বেরিয়ে যাই, বড় রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়েছি, দেখি বেঁটেদা আসছে। আমি সাইকেল থামাই। —বেঁটেদা ও বেঁটেদা অত পুলিশ কেন গো এ দিকটায়?
—শনিতলায় বোধয় ওদের আর ঘুরতে ইচ্ছে করছে না। বুঝলি না? তাই এ দিক ও দিক রোঁদে বেরিয়েছে।
—নাঃ একে নিয়ে পারা যাবে না।
—তোমার বেওসা কেমন চলছে?
—চলে যাচ্ছে, একদিন আসিস, ভ্যারাইটি বাড়িয়েছি।
—যেমন?
—এই ধর সেপ্টিপিন, পাতলুনে লাগাবার দড়ি, কাপড় শুকুতে দেবার কিলিপ, গোলাপখাস আম…..
—যাব্বাবা সেপটিপিনের সঙ্গে গোলাপখাস আম?
—তাতে কী হয়েছে! তোরা এই জাতি-বিভেদটা মোটে ভুলতে পারিস না। আরে দুটোই তো মানুষের দরকার, তাই না? তা ছাড়া গোলাপখাস আমের বন্ন দেখেছিস তো? টুকটুক করছে একবারে! দেখে লোকের অ্যাটাক হবে, তা’ পরে কাছে এসে দেখবে—শুধু তো আম নয়, পাতলুনের দড়ি, কোমরের গামছা, সেপটিপিন স-ব রয়েছে। ওয়ান ডোর পলিসি যাকে বলে। এক দিন আয় না, সিগ্রেটও রাখছি, তবে বাক্সের মধ্যে। নইলে নেতিয়ে যায়।
বেঁটেদার খুব তাড়া, সে ছোট ছোট পায়ে এগিয়ে যায় তুরতুরিয়ে।
রিন্টি জিজ্ঞেস করে— কাকু বেঁটেদা ছোট অথচ বড় কেন?
—ওই রকমই। তুই যেমন লক্ষ্মী অথচ দুষ্টুও।
রিন্টি কী বলতে যাচ্ছিল। নিমকি-শিমকি দুই সুন্দরী দেখি সন্ধেবেলার সাজ, হাওয়াই শাড়ি, আর খড়ির মতো পাউডার, কাজল, রুজ, লিপস্টিক মেখে বেরিয়ে পড়েছে।
—রিন্টিবাবু। রিন্টিবাবু—দুই বোনে দাঁড়িয়ে গেল। ভ্যালা জ্বালা। ওদের বাচ্চা-প্রেমে বিস্তর খাদ আছে—আমি বুঝতে পারি। পেরেও কিছু করতে পারি না।
রিন্টি বলে—শিমকিদি চারদিকে এত পুলিশ ঘুরছে কেন? পাড়ায় চোর ঢুকেছে না কি?
নিমকি বললে—তুমি জানো না বুঝি? মহাজনদের বাড়ির কে একজন গায়েব হয়ে গেছে। সক্কাল থেকে!
রিন্টি গায়েব মানে জানে না, কিন্তু জিজ্ঞেস করতেও ওর ইগোতে লাগে। ও প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করছে গায়েব মানে মৃত্যু না খুন। মৃত্যুতে পুলিশ আসার কথা নয়। তবে বোধহয় খুন।
আমি অবাক।—সত্যি? ঠিক জানেন?
দুই বোনে এ এদিক থেকে ও ওদিক থেকে আঙুলে শাড়ির আঁচল পাকিয়ে, সারা শরীরে রবিনা ট্যান্ডনের মতো ঢেউ-ফেউ জাগিয়ে বললে—আপনি জানেন না? সকালের দিকে ওরা চুপচাপ ছিল, কাউকে খবর দেয়নি। বোধয় নিজেরাই খোঁজ খবর করছিল, এখন…..
আমি আর দাঁড়াই না। শাঁ শাঁ করে সাইকেল বাই। ব্যাপারখানা কী? কে গায়েব হল? মহাজনদের বাড়ি আমাদের বাড়ির পেছন দিকে। কিন্তু এনট্রান্স অন্য রাস্তা দিয়ে। দুর্গের মতো বাড়ি। ছাতে কোনওদিন কাউকে উঠতে দেখিনি। কাজের লোকেদের ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। কিন্তু পরিবারের লোকেরা কালো কাচঅলা গাড়ি ছাড়া বিশেষ বেরোয় না। তিন খানা গাড়ি ওদের গারাজে। কিছু দূরে ডাক্তার আনোয়ারের গারাজেও ওদের একখানা জগদ্দল টয়োটা স্টেশন ওয়াগন আছে। ব্যাপারখানা কী দেখতে হচ্ছে তো! কাকে সেফলি ধরা যায়। দীপুকে? সে-পাগলাকে এখন কোথায় পাব? জগাদাকে? সে আজকাল খুব ইমপর্ট্যান্ট লোক হয়ে গেছে। ওই বাড়ি ভাঙানোর পর থেকে। পার্টিতে তার খুব কদর, আর স্লিপিং নেই বেশ জাগিং জাগিং একটা ভাব এসেছে। সব সময়ে জগাদাদের পার্টি অফিসে গুচ্ছের লোক। বিশুদাকে সন্ধেবেলা পাওয়া যায় না। দুষ্ট লোকে বলে বিশুদা সন্ধেবেলায় আর স্বজ্ঞানে থাকে না। পুরো রঙিন স্বপ্ন-দেখা ভাবুক গোছের হয়ে যায়। এই সময়ে যদি কেউ বিশেষ ক্ষমতা-সূত্রে বিশুদার দেখা পায়ও বিশুদা তাকে রঙিন ভারতবর্ষের সূত্রাবলি বোঝাতে থাকে। এক নম্বর স্বাস্থ্য, দু’নম্বর শিক্ষা, তিন নম্বর খাদ্য, চার নম্বর জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, পাঁচ নম্বর বেকার, ছ’ নম্বর জবরদখল উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন, সাত নম্বর রাস্তাঘাট পুকুর-খাল-বিল নদী-সমুদ্দুর। আট নম্বর—ডিফেন্স, ন’ নম্বর….। নম্বরের নাকি আর শেষ থাকে না, ইনফিনিট সিরিজ। সব বিশুদা করে দেবে, একবার ওকে পেধান মন্ত্রী করে দাও তোমরা, বাস। এই সামান্য খবর জানবার জন্যে নিতাইকাকার কাছে অদ্দূরে যাবারও কোনও মানে হয় না। সে এম পি মানুষ কখন দিল্লিতে থাকে, কখন এখানে থাকে তারই নেই ঠিক। তারপর অবসর সময়ে, নেই অবসর, তবু যেটুকু থাকে, বাথরুম, ভোজন, শয়ন, স্বপন…সব সময়েই নিতাইকাকা জ্বালাময়ী ভাষণ অভ্যেস করে যায়। তার জ্বালাময়ীর জন্যে তার বিশেষ সুখ্যাতি। পার্লামেন্টের অধিবেশন চলার সময়ে টি ভি খুলে একটু ধৈর্য ধরে বসলেই নিতাইকাকার সংক্ষিপ্ত জ্বালাময়ী শোনা যায়।
দীপু এখন আমার বন্ধুও বটে, কলিগও বটে। দু’জনেই চাকলাদারের টেম্পোরারি জব করছি মন-প্রাণ দিয়ে। দীপুর বাড়ি যাই।
—দীপু, দীপু-উ!
—কে?—মাসিমা বেরিয়ে আসেন।
—দীপু নেই?—বলেই খেয়াল হয় আরে, মাসিমাই তো মহাজনদের হাঁড়ির খবর জানবেন!
—দীপু কি কোনওদিন রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরে বাবা!
—মাসিমা, মহাজনদের বাড়ি কী হয়েছে? খুব পুলিশ দেখছি?
—মহাজনদের বাড়ি? পুলিশ? কী হয়েছে? আমি জানি না তো!
—আপনি আজ সকালে যাননি?
—হ্যাঁ-অ্যা। বারোটা নাগাদ আমার কাজ হয়ে গেছে তারপরই চলে এসেছি।
—তার মানে আপনি আসার পর হয়েছে ব্যাপারটা। কেউ অপহৃত হয়েছে শুনতে পাচ্ছি। কে, কী বৃত্তান্ত, কিছুই জানি না।
—বলো কী? পুলিশ! পুলিশ পর্যন্ত এসেছে?
এই সময়ে ধূলিধূসরিত দীপুকে দূর থেকে আসতে দেখতে পেলাম।
আমাকে দেখে দীপু থমকে গেল। তারপরই অবশ্য মায়ের দিকে ফিরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি বললাম মাসিমা কিছু জানেন না, সকালে কাজ সেরে ফিরে এসেছেন। তখনও সব নর্ম্যাল।
দীপু বললে—মহেন্দ্র হাপিশ। ডায়মন্ডহারবার থেকে ফেরবার পথে তারাতলা রোডে কোথায় কাছি দিয়ে গাড়ি আটকেছে। মহেন্দ্রকে কালো অ্যামবাসাডর তুলে নিয়ে গেছে, ড্রাইভারের কবজিতে গুলি, গাড়িতেও দু’ চারটে ছ্যাঁদা। ওই লান্সারটা রে।
ডায়মন্ডহারবারে ওদের ফ্যাকটরি। শো-রুম একটা হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের কাছে, থিয়েটার রোডে, আর একটা শুনেছি দমদম ক্যানটনমেন্টের কাছাকাছি। সল্ট লেকে আর একটা তৈরি হচ্ছে।
দীপুর মা বললেন—প্রতিদিন হয় মহেন্দ্র নয় জগদিন্দ্র ফ্যাক্টরি যায়। ওদের জন্যে কত যত্ন করে লাঞ্চ প্যাক করে দিই। জগদিন্দ্রর আবার ব্লাড সুগার, তার খাবার-দাবারে ভীষণ ধরা কাট। মহেন্দ্রর এদিকে ভাল মন্দ না হলে চলে না। আজই তো ফিশ তন্দুরি, স্যালাড, মেয়নেজ দিয়ে স্যান্ডউইচ আর চকলেট পুডিং করে দিয়ে এসেছি। ফ্লাসকে কফি। বাইরে ওরা জলটা পর্যন্ত খায় না।
আমরা তিনজনেই বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বেশ কিছুক্ষণ পর দীপু বলে; সমানে একটা ডেঞ্জার সিগন্যাল পাই। সমানে। যেন ওঁ-ওঁ করে একটা সাইরেন কোথাও বেজে উঠেই থেমে গেল। একটা লাল আলো দব্দব্ করে জ্বলার শব্দ। কিন্তু সেটা যে এই রকম একটা ব্যাপার হবে তা তো আমি ঘুণাক্ষরেও…নাঃ, রুণু, ভয়েসটা আমাকে বিট্রে করছে, না আমিই ভয়েসটাকে বিট্রে করছি বুঝতে পারছি না রে।
আমার এত বিরক্তি ধরে যায় যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে উদ্যত হই। মাসিমা হঠাৎ একটু ব্যস্ত হয়ে বলেন—রুণু এক মিনিট। ভেতর থেকে উনি প্লেটে করে কয়েকটা নারকোল নাড়ু নিয়ে আসেন। রিন্টিকে কীরকম আনমনাভাবে আদর করে বলেন—আমাদের বাড়ি প্রথম এলে খোকন, মিষ্টিমুখ করবে না? রিন্টি আমার দিকে চায়। আমি জানি ও নারকোল নাড়ু ভীষণ ভালবাসে। আমি ঘাড় নাড়ি। ও তৎক্ষণাৎ দুটো তুলে নেয়। একটা মুখে পুরে দেয়। মাসিমা বলেন—রুণু তুমি দুটো নাও। আমি বলি —‘আমার একদম ইচ্ছে করছে না পিসিমা, প্লিজ।’ —‘আচ্ছা একটা, অন্তত একটা, মণি এসে খুব রাগ করবে নইলে আমার ওপর’—কী আর করা! আমি একটা তুলে নিয়ে মুখে ফেলি। আর সঙ্গে সঙ্গে এক অবর্ণনীয় সুস্বাদে আমার মুখের ভেতরটা ভরে যায়। একে কি নারকোল নাড়ু বলে? এরকম নারকোল নাড়ু আমি জীবনেও কখনও খাইনি। অজান্তেই আমার হাত চলে গেছে প্লেটের দিকে। আর একটা তুলে আমি দীপুর মুখের ভেতর ঠেসে দিই। চারজনের মুখেই একটা আলগা হাসি এসে যায়। দীপু বোধহয় আমার জিভের উল্লাস পড়তে পারে। বলে—মা তো এইরকমই সব খাবার-দাবার বানায়। তবে বামনী তো সব সময়ে জিনিসপত্তর পায় না। মাঝে মাঝে জঙ্গলের বাঘ বামনীর নাড়ু খেতে চেয়ে দোকানে দোকানে হুড়ুম হুড়ুম করে পড়ে জিনিস এনে দেয়, সে গল্প মনে আছে। তো?
আমি বলি—মাসিমা, আপনি আর আমি একটা কেটারিং বিজনেস খুলি চলুন। হ্যাঁ সাবধানে থাকবেন, ওদের বাড়িতে সবাইকার ওপর এখন পুলিশ চড়াও হবে, ঝামেলা করবে।
মাসিমা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়েন। আমি আর এগোই না। ফিরতি পথ ধরি।
১২
পরের কয়েক দিন ধরে, পাড়াতে ওই একটাই খবর। মহেন্দ্র মহাজন অপহরণ। বাড়িতে বাড়িতে ঝুপড়িতে ঝুপড়িতে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে। কাগজে বড় বড় করে ছেপেছে খবরটা। মহেন্দ্র মহাজন, মহাজন ইলেকট্রনিক্স্-এর বাড়ির ছোটকর্তা, বয়স উনচল্লিশ। দুটি বাচ্চার বাবা, একজন এগারো আরেকজন সাত, বৃদ্ধ এ. এস মহাজন ও মিসেস মহালক্ষ্মী মহাজনের কনিষ্ঠ পুত্র, বিকেল চারটে নাগাদ ডায়মন্ডহারবারের ফ্যাকটরি থেকে ব্রেসব্রিজ হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর ব্রাউন রঙের লান্সার গাড়িতে। ড্রাইভার মদনলাল চালাচ্ছিল। রাস্তা ফাঁকা। দু’ পাশে ঝোপড়ি, গাছপালা, ব্রেসব্রিজের কাছে একটি লোক টলতে টলতে গাড়ির সামনে এসে পড়ায় মদনলাল জোর ব্রেক কষে। এবং কাঁচ নামিয়ে গালাগাল দিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার কানের কাছে পিস্তল চেপে ধরে কেউ। মহেন্দ্র সম্ভবত একটু তন্দ্রায় ছিলেন। জার্কে তিনি জেগে যান। প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও পেছন থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে তাঁর লাঞ্চ বাক্সটি তিনি পিস্তলধারীর হাতে ছোড়েন। পিস্তল লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায় বটে কিন্তু মদনমোহনের ডান ঊরুতে গুলি বিঁধে যায়। সে যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়ে যায়। ইতিমধ্যে জনাদুই লোক পেছনের দরজা দিয়ে মহেন্দ্রকে কবজা করে। সম্ভবত তাঁর নাকে মুখে ক্লোরোফর্মভর্তি রুমাল চাপা দেওয়া হয়। ভিন্ন একটি গাড়ি করে তারা মহেন্দ্রকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। মদনলালের যখন জ্ঞান ফেরে তখন সন্ধের ছায়া নেমে গেছে। সে প্রথমে দিক ভুল করে ব্রেসব্রিজের দিকে চলে যায়, তার পর আবার অনেক কষ্টে গাড়ি চালিয়ে নিকটবর্তী পেট্রল স্টেশনে এসে সব জানায়। এবং তাদের সাহায্যে থানায় ও বাড়িতে ফোন করে। গোটা ঘটনাটার কোনও সাক্ষী নেই। সাক্ষী কাচভাঙা রক্তাক্ত-সিট লান্সার এবং ডান-ঊরু গুরুতর জখম মদনলাল। সে হাসপাতালে। অপারেশন হচ্ছে। কিঞ্চিৎ সুস্থ হবার পর দফায় দফায় তার জবানবন্দি নেওয়া হবে। গাড়ি এবং তার মধ্যে যা কিছু ছিল, লাঞ্চ বক্স, ফ্লাস্ক, ফাইল ভর্তি ব্রিফকেস সমস্ত পুলিশের জিম্মায়।
সারা শহর আমাদের এলাকা নিয়ে আলোচনা করছে। দারুণ ইমপর্ট্যান্স। পাড়ার অপেক্ষাকৃত ছোটদের কেমন একটা গর্ব এসে গেছে। চলাফেরায় একটা গেরেম্ভারি ভাব। পেছন দিকে মহাজনদের বাড়ি একটা ভূতের বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। মহেন্দ্র-জননী মহালক্ষ্মী দেবীকে একদিন সকালে আমাদের চোখের সামনে দিয়েই নার্সিং হোমে নিয়ে গেল। এ এস ভোরের দিকে একটা মারুতি জেন-এ করে বেড়াতে বেরোতেন। সম্ভবত আলিপুরের দিকে গিয়ে হাঁটতেন। তিনি আর বেরোন না। দু’ চার দিন পর মহেন্দ্রর দুটি ছেলে মেয়ে আর জগদিন্দ্রর তিনটি পুলিশ পাহারায় স্কুল-কলেজ যেতে থাকল। জগদিন্দ্রও দুটি সিকিওরিটিম্যান নিয়ে অফিস যেতে থাকলেন। কিন্তু বাড়িটা তার দুর্গ-গড়ন, তার প্রচুর লোকজন ও স্বল্প কয়েকজন মনিব মনিবানি ও বাচ্চা কিশোর-কিশোরী নিয়ে একদম চুপ। খালি থেকে থেকে রাতের দেহ ফুঁড়ে বুলেটের মতো বেরিয়ে আসে অ্যালসেশিয়ানের গর্জন। গর্জনে গাম্ভীর্যের থেকে তীব্রতা যেন বেশি। কুকুরটা টেন্স্ হয়ে আছে।
এরই মধ্যে প্রথমে মাধ্যমিক পরে উচ্চ-মাধ্যমিকের খবর বেরোল। সন্ধেবেলা টিউশানিতে বেরোচ্ছি মণিমালা তার সেই অচেনা সঙ্গী নিয়ে এসে হাজির। দু’জনেই বিনা নোটিসে ঢিপ করে প্রণাম করল, আমি সরে যাবার সময় পেলাম না।
—রুণুদা, আমি স্টার পেয়েছি। ম্যাথ্স্ বাংলা আর ফিজিক্সে লেটার, কেমিস্ট্রিতে একটুর জন্যে মিস করেছি।
—বাঃ, খুব ভাল। মনে-মনে বলি আর্ডিনারি কমার্স গ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী স্টার? লেটার? আনন্দ করব না মুখ লুকোব বুঝতে পারি না।
মণি বলল—আর এ আমার বন্ধু, ও-ও মাধ্যমিক ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। আমি বলি—বাঃ, কংগ্র্যাচুলেশনস্ মণি, বউদির কাছে যাও। আমি এখন পড়াতে যাচ্ছি তো।
সন্ধে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। আমার ট্যুইশন সারা। তুলতুল নামে একটি ছেলে এবং টুম্পা বলে তার দিদিকে পড়িয়ে এলাম। টুম্পা যেমন মনোযোগী, পড়াশোনায় ভাল করার জন্যে বদ্ধপরিকর, তুলতুল ঠিক তেমনি ফাঁকিবাজ। বকামির দিকে যাচ্ছে, ওর মুখে আমি সিগারেটের বদবু পাই। আমি পড়ানোর সময়ে স্মোক করি না। কিন্তু পকেটে প্যাকেট থাকে। কোনও অদ্ভুত হাতসাফাইয়ের কৌশলে তুলতুল তার থেকে দু’ চারটে সরিয়েছে আগে। তার পর থেকে আমি আর প্যাকেট নিয়েই যাই না। তাতে আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে। কেন না দু’জনকে পড়ানোর প্রচণ্ড মানসিক পরিশ্রম আর ক্লান্তির পর রাস্তায় বেরিয়েই আমার একটা দুটো ধোঁয়া লাগে। বেরিয়েই কোনও দোকান পাই না। মনটা খিঁচড়ে যায়।
আজকে একটু রুক্ষ ব্যবহার করে ফেলেছিলাম। পড়াতে পড়াতে তুলতুলের মুখে গন্ধ পাই। কড়া চোখে তাকিয়ে বলি—তুলতুল, আমার জিনিস সব গোনাগুনতি থাকে, সরালে আমি টের পাই। একবার দু’বার করেছ, আর করো না। চুরির অভ্যাসটাও অতি বদ, স্মোকিংটাও খারাপ।
—আপনিও তো খান! এত আস্পদ্দা ছেলেটার, একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে আমার মুখের ওপর বলল।
—খাই, কিন্তু নিজের পয়সায় খাই। কারও থেকে চুরি-চামারি করি না। তা ছাড়া হ্যাবিটটা করে ফেলেছি বলে পস্তাচ্ছি এখন। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে ছেড়ে দিতে পারব।
টুম্পার মুখটা লাল। এভিডেন্টলি ও জানে ব্যাপারটা এবং লজ্জা পায়। তুলতুল কী একটা ছুতোয় ভেতরে গেল। একটু পরে দেখি ওর মা চা আর টোস্ট নিয়ে আসছেন। খাবারগুলো আমার সামনে বসিয়ে বললেন—মাস্টারমশাই, তুলতুল আমার তিনটে ছেলে-সন্তান চলে গিয়ে তবে হয়েছে। ওকে কিছু বলবেন না। আমরা ওকে বকাঝকা করি না।
আমি সোজা বললাম—স্মোক করলেও বলব না? আমার পকেট থেকে সিগারেট সরালেও বলব না?
—আমার ছেলে আপনার পকেট থেকে সিগারেট সরিয়েছে? আপনি বলতে পারলেন কথাটা? ওকে আমরা হাতখরচা দিই, তা জানেন?
—খুব ভাল, তা হলে সেটাতেও খেয়েছে। আমার পকেট থেকেও সরিয়েছে। সে যাকগে, ও এই বয়স থেকে স্মোক করবে আপনারা কনট্রোল করার চেষ্টা করবেন না, এমন যদি ব্যাপার হয় এই ছেলেকে পড়ানোর রিস্ক্ আমি নিতে পারব না। টুম্পা ইজ ডিফারেন্ট। ও অত্যন্ত মনোযোগী, ভাল করার চেষ্টা করে। কিন্তু তুলতুল যদি এইভাবে চলে ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
ভদ্রমহিলা কালো মুখ করে চলে গেলেন। আমার ট্যুইশনটা বোধহয় গেল।
আমাদের এ অঞ্চলটা আসলে ছোটদের বড় হওয়ার পক্ষে ভাল নয়। আমরাও ছোটবেলায় এসব এলিমেন্ট ফেস করেছি। শনিতলার সাড়ে-বত্রিশভাজা থেকে প্রচুর ছেলেপিলে বার হত, অনেক খেলেছি তাদের সঙ্গে, তলাওটায় সাঁতার শিখেছি ওদেরই কাছ থেকে। কিন্তু যেই স্কুলে উঁচু ক্লাসে উঠে গেলাম, ওরা ড্রপ আউট করতে লাগল। আমি, পানু, সত্য টিউটরের কাছে অঙ্ক সায়েন্স পড়তে থাকলাম। ওরা নিজেরাই সরে যেতে থাকল। কেমন একটা লজ্জা, সংকোচ, একটা কমপ্লেক্স। ওরা কেউ বিড়ি বাঁধে, কেউ চায়ের দোকানে কাজ করে, কেউ বাজারে সবজি নিয়ে বসে, কেউ আড়ত থেকে মাছ নিয়ে আসে, কেউ কর্পোরেশনে জঞ্জাল তোলার খবর্দারি করে। এখন ভাবলে খুব খারাপ লাগে। এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়া আরম্ভ করেছিলাম। আমরা ভদ্রলোক, নিঃস্ব না হলেও দরিদ্র। ওরা ভদ্রলোক নয়, ওদের চারপাশে মা-বাবা-সৎমা-সৎবাবা-বহু ভাইবোন-অবৈধ সম্পর্ক, খোলাখুলি যৌনতা ও বড়দের সমস্ত কাজকারবারের বে-আব্রু পরিবেশ। কখনও ওদের কথা ভাবিনি, হেল্প করার চেষ্টা করিনি। এই সামাজিক তফাতটা মেনে নিয়েছি। এখন কেমন লজ্জা হয়। দুঃখ হয়। ওদের সঙ্গে যোগাযোগের সেতুটা ছিল কর্পোরেশন স্কুল। কর্পোরেশন স্কুল থেকে ক্লাস ফোরের পর আমরা যোগদারঞ্জন বিদ্যালয়ে গেলাম। আরও বড় হবার পরও শামু, খলিল, রাজু, সঞ্জুদের সঙ্গে জমিয়ে ফুটবল খেলেছি। কিন্তু এরা আমাদের সঙ্গে খেলতে আসতেও সাহস পেত না। বিড়ি খেত, মুখ-খিস্তি করত, একেবারে অন্যরকম একটা জগতের বাসিন্দা হয়ে গেল আস্তে আস্তে।
এখন দেখি, এই ব্যবধানটা বেশ কমে এসেছে। তথাকথিত ভদ্রলোকের ছেলেরা একটু নেমেছে, আর ঝুপড়ির ছেলেরা উঠেছে। এই যে নামা আর ওঠা এ কিন্তু কমিউনিজম-ঈপ্সিত সোশ্যাল ইকোয়ালিটি বা ক্লাসলেস সোসাইটি নয়। আসলে আমাদের বাড়ির ছেলেরা আচার-আচরণে সভ্যতা-ভব্যতায় স্ট্যান্ডার্ড হারিয়ে ফেলছে। আর যারা নিজেদের ভব্যতার ও কুশ্রী পরিবেশের লজ্জায় দূরে থাকত তাদের সাহস বেড়েছে, তারা এখন নিজেদেরই শর্তে তুলতুলদের ঘাড়ে হাত রাখছে। আর তুলতুলদের মা-বাবারা ছেলে-মেয়ে মানুষ করার নতুন নিয়ম কানুনে দিশেহারা হয়ে ভালমন্দ বুঝতে পারছেন না। তুলতুলের মা-বাবার মতো স্নেহান্ধ পিতামাতা আগেও ছিলেন, তাঁদের অনেকে নিজেরাও মন্দ-অভ্যেস ভুল চিন্তাধারার ধ্বজাধারী ছিলেন। কিন্তু এখনকার ব্যাপারটা অন্য। এখন লোকে ধৃতরাষ্ট্র নয়। জন্মান্ধ নয়। জেনেশুনে গান্ধারীর মতো চোখে পট্টি বাঁধতে চায়। ভাল বাবা, বাঁধ, পরে বলিসনি টিউটরটা বখা ছিল। তারই সঙ্গে পড়ে উচ্ছন্নে গেছে। তুলতুলদের বাড়ি আমি আর পরের দিন থেকে পড়াতে যাব না। টুম্পাটার জন্যে খারাপ লাগে। ওর তো কোনও দোষ নেই! কিন্তু কী আর করা যাবে, আমি এমন কিছু এ-ক্লাস টিউটর নই যে টুম্পার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার চেয়ে ভাল টিউটরই হয়তো ওর জুটে যাবে। ক্ষতিটা আমার। আমিও এমন কিছু এ-ক্লাস ছাত্র নই। কিন্তু যেটুকু শিখেছি এমন খেটে-খেটে নিজের চেষ্টায় শিখতে হয়েছে যে ওই জায়গাটায় আমি সলিড। আর সেইজন্যেই সামান্য নিচু ক্লাসের অঙ্ক ইংরেজি সায়েন্স, একটু টেক্সট বইটা পড়ে, ইলাসট্রেশনগুলো পড়েই বুঝে নিতে পারি। ভালও লাগে বেশ। আমার কাছে তো আর স্টার পাওয়া ছেলেমেয়ে পড়তে আসবে না। এই রকম সাধারণদের মধ্যে থেকেই একটু আধটু ভাল-মন্দ আমার জোটে। মণিমালার মতো ছাত্রীর টিউটর হবার সৌভাগ্য আমার হত না, যদি ওদের অবস্থা একটু ভাল হত, কিংবা দীপেটা রেসপনসিব্ল্ হত।
এই সময়েই আমার চোখে পড়ল ব্যাপারটা। কালো প্যান্ট, কালো আঁট টি শার্ট পরা শামু সুট করে গদাদের বাড়ি ঢুকে গেল। তাজ্জব কী বাত! এক কালের এক মাঠের এক দলের খেলোয়াড় এখন ভিন্ন মাঠে রাইভ্যাল গ্রুপ। এ যেন ইন্ডিয়ার ন্যাশন্যাল টিমে পঞ্জাব, বাংলা, মহারাষ্ট্র সব জায়গাকার প্লেয়ার মিলে-জুলে খেলছিল। দেশের মাটিতে এসে আবার সব আলাদা ইস্ট জোন, ওয়েস্ট জোন…। তা যেন হল, ওরা কি আবার কোনও ন্যাশন্যাল টিমে ডাক পেয়েছে নাকি এতদিন পরে?
শামু গদা মিলে যাক কে না চায়! আমাদের মতো ছোটবেলার বন্ধুদের তো জিনিসটা ভালই লাগবার কথা। ওরা মিলে-জুলে গদাইয়ের কারখানাটা চালাক। আমাদের রেল লাইনের এপার-ওপার লোকের ওপর অযথা জুলুম অত্যাচার বোমবাজি বন্ধ হয়ে যাক। আমিও নিশ্চিন্তে একটা ছোটখাটো ‘সুধা স্টোর্স’ খুলে ফেলি। মা খুশি হোক, দাদা বউদি খুশি হোক। কিন্তু শামু দিনের বেলায় একটা দামি সিল্কের লুঙ্গি তার ওপরে সাদা টেরিকটের পোশাকি শার্টটা পরেই যাক। যাক বুক ফুলিয়ে, মুখে হাসি নিয়ে। গদা দরজায় নক শুনে খুলে দিক। ধবধবে পায়জামা-পাঞ্জাবিতে গদাকে বিশুদার চাইতেও ভাল দেখাবে।
—আরে শামু তুই? পথ ভুলে না কি?
—এ বে শ্শ্ শালা। অনেক দিন ধরে ভাবছি ছোটকালের দোস্তিটা একটু ঝালিয়ে নিই, মর্চে পড়ে গেছে।
—সাবাশ। আমিও ঠিক ওই কথাই ভাবছিলাম, বুঝলি শামু? তুই ব্যাক-ভলিতে যে গোলটা করে সবুজ সঙ্ঘকে ডুবিয়েছিলি, সেইটার কথা ভাবছিলাম এক্ষুনি স্টার স্পোর্টস-এ খেলা দেখতে দেখতে। জাস্ট এক্ষুনি, বিশ্বাস কর। আয় আয় ভেতরে আয়।
গদাদের বাইরের ঘরে বসে শামু বলবে—এ বোমবাজি, লোকজনের কাছ থেকে ভিক্ষে এ আর ভাল্লাগে না শালা। তোকে একটা প্রোপোজাল দিচ্ছি, দ্যাখ পছন্দ হয় কি না।
—বল। শুট ম্যান শুট।
—তোর কার্ডবোর্ডের কারখানাটা? ওর সিকিওরিটিতে আমাকে রেখে দে না। বাইসেপসগুলো দ্যাখ। কারাটের কথা তো জানিসই। আর স্টিলের নীলচে খোকাখুকুগুলো তো আমার কথায় ওঠে বসে—জানিসই। দ্যাখ ভেবে। চাকরিটা যদি দিস, আমি তোর সেলসের দিকটাও যথাসাধ্য দেখব। বাঙালির ছেলে, করেই দেখাই কিছু। খেয়োখেয়ি ভুলে! আফটার অল তুই আমাদের টিমের স্টপার।
গদা বলবে—সিরিয়াসলি বলছিস? এ উঞ্ছবৃত্তি আমারও আর ভাল লাগছে না, সত্যি বলছি। পাড়ায় হেঁটে বেরোতে পারি না। সব কেমন যেন চোখে তাকায়।
কিন্তু রাতের অন্ধকারে কালো প্যান্ট কালো বেল্ট পরে শামু শুট করে গদার বাড়ি ঢুকে গেলে পরবর্তী আলাপ-আলোচনাটা আর ওভাবে ভাবা যায় না। আমার কল্পনা আর খেলে না, খেলতে চায় না।
খুব টেন্স্ হয়ে বাড়ি আসি। বাথরুমে গিয়ে আচ্ছাসে জল ঢালি, মাথায় গায়ে। বেরিয়ে আসতে মা বলল—আচ্ছা রুণু, তোর কী আক্কেল বল তো, গা মুছিসনি, পুরো গেঞ্জি পায়জামা ভিজে উঠেছে।
রাফ গলায় বলি—ঠিক আছে।
বউদি বলে—ওকে বলব মা?
—বলো।
—আমাদের সরকার কাকা বুঝলে রুণু একটা লাখটাকার প্রোপোজ্যাল দিয়েছেন। ওঁর মেয়েটি তো একমাত্র। রং কালো বলে দু’ চারবার পাত্রপক্ষ রিজেক্ট করবার পর এখন সে ধরেছে আর ও ভাবে বিয়ে করবে না। সরকার কাকার ইচ্ছে একটি ভাল ছেলেকে নিজের বাড়িতে রেখে ব্যবসার, ওঁর মাছের ভেড়ি আছে জানিস তো—ব্যবসাটা ভাল করে বুঝিয়ে তার হাতেই মেয়ে দ্যান। শুভশ্রীরও আপত্তি নেই। উনি তোকে খুব পছন্দ করেন। শুভশ্রীরও…
আমি বউদির কথার কোনও জবাব দিই না। রূঢ় হাতে সামনে থেকে রিন্টিকে সরিয়ে দিই। তারপর দোতলার সিঁড়ি উঠতে উঠতে রূঢ়তর গলায় বলি—মা, এখন আমার খিদে নেই। খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখো।
রাত ক্রমশ বাড়ে। আমি আমাদের ছোট্ট দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাই। ভীষণ একটা অস্থিরতা, একটা অন্ধ রাগ। আপনিও তো খান? একটা তেরো বছরের কিশোর মুখ তেরিয়াভাবে বলছে। ওকে আমরা বকাঝকা করি না, ও আপনার পকেট থেকে সিগারেট সরায় কথাটা আপনি বলতে পারলেন? জানেন ওকে আমরা হাত খরচা দিই! চুল আঁট করে আচড়ানো পেছনের ক্লিপ থেকে ঝুলছে, ছাঁট-কাট হীন স্লিভলেস ব্লাউজ, বগলের মাংস ফুলে ফোড়ার মতো বেরিয়ে আছে, টোপা কুলের মতো মুখ, ঢাউস-কোমর গান্ধারী। মেয়েটা যে অত পড়াশোনায় ভাল, দেখতে পায় না। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ভাগে পড়বার ব্যবস্থা করেছে। ভেড়ি! ভেড়ি! ভেড়ির ব্যবসা? করে কারা? অশিক্ষিত ধূর্ত, ফন্দিবাজ, প্রায় অ্যানটিসোশ্যাল, কালো মেয়ে মানে হতকুৎসিত। এই ভাবেই আমার ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে। শুধু দাদা-বউদি নয়। তারা তো পর বললেই হয়। কিন্তু নিজের মা, মা। তিনি আমার ঘর-জামাইগিরির বন্দোবস্তে সায় দিচ্ছেন। বা বা বা বাঃ। এইজন্যে বাজার থেকে খয়রা, কাজলি আনি, সিগারেট কমাবার চেষ্টা করছি, টুইশানি করে করে নিজের চার ভাগের তিন ভাগ খরচ চালাই। আমার বয়সী ছেলেরা সত্য, পানু, শামু, গদা, দীপু এদের থেকে সেইজন্যেই আমি এতদিন বেশি ভদ্র, বেশি মিশুক, বেশি সিনসিয়ার, বেশি রেসপনসিব্ল্ হতে চেষ্টা করেছি! কে আমাকে বারণ করত যদি আমি সত্যর মতো সাহাদের বাড়ির মেয়েকে নিয়ে পালাতাম, কে বারণ করত যদি শামুর মতো বোমা বাঁধতাম, দীপুর মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মায়ের রোজগারে, বোনের রোজগারে খেতাম। গদার মতো মাফিয়া হতেই বা কে আমায় বাধা দিত! গদা আমাকে খুবই পছন্দ করত। ভিড়ে যেতেই পারতাম! কাদের জন্যে তা হলে আমার এত ভদ্রতা, এত সুখ্যাতি, এত চেষ্টা! ভেড়ি! মাছের ভেড়ি! শুভশ্রী? ঘরজামাই?
হঠাৎ চোখে পড়ে আপাদমস্তক আলো-নেভানো মহাজনদের বাড়িটা তারার আলোয় ভূতের বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের অবশ্য খুব পালিশ, চিৎকার করে টিভি-ক্যাসেট বাজে না ওদের বাড়ি। কিন্তু এই রকম শান্ত গ্রীষ্মের রাত্তিরে যখন দক্ষিণ থেকে হু হু করে হাওয়া বয়, তখন চ্যানেল ফাইভ, গোলাম আলি কি সুচিত্রা মিত্র ভেসে আসে। সেতার-সরোদ-বাঁশি এ সবও শোনা যায়। এগুলো কোনটা কার বাজনা বলবার বিদ্যে আমার নেই। পাশ্চাত্য সুরও আসে ভেসে। ভাল লাগে খুব, ধরতে পারি না কিছুই যদিও। ওদের বাড়ির সঙ্গীত রুচি খুব ব্যাপক এইটুকু বোঝা যায়। কিন্তু আজ কোনও আওয়াজ, কোনও সুর শুনতে পেলাম না। ভীষণ খারাপ হয়ে গেল মনটা। মহাজনদের বাড়ির অভূতপূর্ব বিপর্যয়ে আমাদের পাড়ায় অনেকেই খুব খুশি। যেমন সত্য। সত্য বলছিল এক পাড়ায় থাকবে অথচ কারও সঙ্গে মিশবে না এত অহংকারের উচিত সাজা হয়েছে। এ রকম মতামত অনেকেরই। অনেকে আবার খুব উদাসীন। সহানুভূতি বলতে ঠিক যা বুঝি, সমব্যথা, দুঃখিত হওয়া এরকমটা বোধ হয় কারওরই হয়নি। যেটা হয়েছে সেটা হল কৌতূহল, রোমাঞ্চকর নাটকের মঞ্চ হবার একটা গর্ববোধ। পাড়ার নাম মহেন্দ্র অপহৃত হওয়ার সুবাদে কাগজে উঠে গেছে। জবানবন্দি সূত্রে কিছু ছবিও। নিজেদের রাস্তা, নিজেদের বাড়ি, নিজেদের বিশেষত্বহীন মুখ কাগজের পাতায় দেখে বুক দশহাত। কীরকম যেন বিচ্ছিন্ন একটা অভিশপ্ত দ্বীপের মতো বাড়িটা।
সত্যিই ওরা কেন এখানে আছে? অত বড় বাগান, পৈতৃক ভিটের মমতা ছাড়তে পারেনি, না কি? ওদের বাড়ির বউরা? সাধারণত বউয়েরা এসে এইসব বায়না ধরে। পশ এরিয়ায় যেতে হবে, এই গাড়ি কিনতে হবে, বাড়ি এরকম সাজানো হবে—এদের বাড়ির বউয়েদেরও কি এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য ছিল না? থাকলেও গ্রাহ্য হয়নি? এ এস-কে আমরা অনেকবার দেখেছি। টুকটুকে বৃদ্ধ। চুলগুলো সব সাদা। চেহারাটা একসময়ে বেশ ভারী ছিল, এখন আলগা হয়ে গেছে। কিন্তু চলাফেরা বেশ স্মার্ট। খটখট করে হেঁটে যান। বরং ওঁর স্ত্রীকে যা দেখলাম নার্সিং হোমে নিয়ে যাবার সময়ে—মোটা, থলথলে বৃদ্ধা, যেন এ এস-এর চেয়েও বয়সে বড়। কিন্তু কাউকে দেখেই খুব রিজিড মনে হয়নি। মনে হওয়া দিয়ে অবশ্য কিছু হয় না। কে ভেতরে ভেতরে কী, এ সব বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু মহাজনরা পাড়ার লোকের সঙ্গে একেবারে মেশে না কথাটাও ভেবে দেখতে গেলে সেন্ট পার্সেন্ট ঠিক নয়। পুজোর সময়ে চাঁদা চাইতে গেলে আমাদেরও অল্পতর বয়সে এ এস নিজের বিশাল বসার ঘরে বসাতেন, শরবত, মিষ্টি আসত। হাসিমুখে দু’ হাজার-এক, তিন হাজার-এক চাঁদা দিতেন। এখন বোধহয় আরও বেশি দ্যান, বিনা প্রতিবাদে। কেন? পুজোর সময়ে কী যেন ফাংশন হল সে-বার, এ এস-কে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল। উনি এসেছিলেন। রাস্তার এক পাশে তক্তা মেরে তৈরি করা মঞ্চে বসে মালা-টালাও পরলেন। বক্তৃতাও করেছিলেন দু’ চার লাইন। জগদিন্দ্র বোধহয় জগাদা অরবিন্দদাদের সমসাময়িক, দেখা হলে হাসে, নড্ করে। মহেন্দ্র তো আমার সঙ্গে গাড়ির কাচ নামিয়েও কথা বলেছে, জাস্ট কী খবর, ভাল তো!—এইরকম। ওদের বিয়েতে রিসেপশন অন্যত্র কোথাও ক্লাবে-ট্লাবে হয়েছিল। কিন্তু নিজেদের বাগানে একদিন পাড়ার লোকেদের পংক্তিভোজন করিয়েছিল ভাল কেটারার দিয়ে। —এর চেয়ে বেশি সামাজিক আদান প্রদান কি কোটিপতিদের সঙ্গে আমাদের সম্ভব? ওরা যদি মিশতে চাইতও, আমরা পারতাম? আমাদের বাড়ির বিয়েতে আমরা কখনও ওদের নেমন্তন্ন করেছি?
হঠাৎ কেমন মনে হল ওদের ঐশ্বর্য, ওদের সামাজিক প্রতিপত্তি, ওদের কালচার, ওদের বউ ছেলেমেয়েদের রূপ এই সবেতে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমরাই এত বড় আঘাতটা ওদের দিয়েছি। পাড়াটা যেন ওত্ পেতে ছিল বুনো শেয়ালের মতো। ঝোপঝাড়ের আড়ালে-আবডালে, সেইসব শেয়াল এক গ্রীষ্মের নির্জন রাস্তায় বাগে পেয়ে টুঁটি টিপে ওদের নিয়ে গেছে। এখন বোধহয় তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে।
ধনী আর দরিদ্র, ক্ষমতাশালী আর ক্ষমতাহীনের এই যুদ্ধ অঘোষিত, অলিখিত। এ কি কোনওদিনও ঘুচবে না? ওরা আমাদের অবজ্ঞা করবে, এড়াবে। আমরা ওদের হিংসে করব, ওদের শোকে আনন্দ করব!
—রুণু, খাবি না? —পেছনে মায়ের গলা।
—যাচ্ছি, যাও।
—এগারোটা বেজে গেছে। রুটিগুলো ঠাণ্ডা কড়কড়ে হয়ে গেল।
—যাচ্ছি।
মা বোধহয় এত রাগতে আমাকে কখনও দেখেনি। আর টু শব্দটি না করে চলে গেল। কে জানে নিজে খেয়েছে কি না। আমার মা আপাতদৃষ্টিতে খুব সেন্টিমেন্টাল অবশ্য নয়। বাবার মৃত্যুর পর মাকে মাছ খাওয়াতে, পাড়-ওয়ালা শাড়ি পরাতে আমাদের খুব বেগ পেতে হয়নি। আমরা বলেছিলাম মা তোমাকে আমাদের খুব দরকার, তোমারও আমাদের। ওসব নিরামিষ-টিষ নিয়মের কোনও মানে হয় না। তবু যদি করা সম্ভব হত, না হয় করতে কিন্তু মাছটুকুই একমাত্র প্রোটিন যা আমরা সহজে জোগাড় করতে পারি। ডাল-রুটি খাওয়া শরীরও আমাদের নয়। তুমি স্বাস্থ্য হারাবে মা, তখন আমরা কী করব? মা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল —তোদের বাবাও এসব মানতেন না। —একটু কম সেন্টিমেন্টাল আর বেশি প্র্যাকটিক্যাল বলে মা নিজের অম্লশূলের ব্যথার কথা মনে রেখে খেয়ে নিয়েছে আশা করা যাক। এখন আমার রাগটা অনেক পড়ে এসেছে। কিন্তু এই একাকিত্ব আমার যেন আরও কিছুক্ষণ দরকার। খেতে এত অনিচ্ছাও আমার আগে কখনও হয়নি। রাগ-অভিমান এমনই জিনিস না কি? খিদে ভুলিয়ে দেয়! যে খিদের জন্য ভুবনময় এমন মরণ-বাঁচন যজ্ঞ?
নিস্তব্ধ রাত, কোথাও তীক্ষ্ণ সুরে মোবাইল বাজছে। দক্ষিণ থেকে প্রবল প্রবলতর হাওয়া এসে আমাকে, আমার ছাতকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই হাওয়া কত দূর থেকে বয়ে আনছে এই শব্দ। অন্ধকারের মধ্যে মহাজন বাড়ির জানলাগুলো খোলা ছিল। আমার মুখোমুখি জানলাটা কেউ বন্ধ করে দিল।
নীচে গিয়ে লক্ষ্মীছেলের মতো মুসুর ডাল দিয়ে ভাত আলুর দম আর পটোল ভাজা খেয়ে উঠলাম। রুটি কড়কড়ে হয়ে যাবে, খেতে পারব না বলে মা রুটিগুলো নিজে খেয়ে, ভাতটা আমার জন্যে রেখে দিয়েছে। মায়ের রুটি একদম সহ্য হয় না। হঠাৎ আমার কী যে হল আরশুলা ফড়ফড়ে সেই একতলার কেরোসিন কাঠের টেবিলে মাথাটা উপুড় করে রাখলাম। চোখের জলে কাঠ ভিজে যেতে লাগল। কখনও মনে হতে লাগল মায়ের জন্য কাঁদছি, পরক্ষণেই মনে হল নিজের জন্যে কাঁদছি, তার পরেই মনে হল আমার চোখের জলের মধ্যে আবছা নাইলনের পর্দার ওপাশে যেন মহেন্দ্র মহাজন দাঁড়িয়ে আছে। —রাস্তার মাঝখানে থুতু ফেলাটা কি ঠিক হল? —কালো কাচ নিঃশব্দে উঠে যায়, নেমে যায়।
আমি কেঁদে যেতে লাগলাম। কেঁদে যেতে লাগলাম। আমারই বয়সি কোনও তরুণী মেয়েরই মতো হয়তো। এবং সারা রাত ঘুমের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল গদাই। শামু। নানা কম্বিনেশন। কখনও গদাই শামুকে ফুটবলের মতো হেড মারে শামু শূন্যে চলে যায়। কখনও শামু গদার কোলে বসে গলা জড়িয়ে চুমু খায়, কখনও দু’জনে হাত ধরাধরি করে আমার কাছে এসে বলে পার্লামেন্টের সামনে হিউম্যান বম্ব ফাটাচ্ছি, তুই আমাদের সঙ্গে আছিস তো? আমি সানন্দে রাজি হয়ে যাই, যেন শুশুনিয়ার পাহাড়ে মাউন্টেনিয়ারিং-এর পয়লা পাঠ নিতে যাচ্ছি। তারপরই কোথা থেকে মহেন্দ্র মহাজন এসে বলে—এটা কিন্তু ঠিক করছ না শামু। শুভশ্রী কালো বলে কি সে মানুষ নয়? শামু উল্টো দিক থেকে এসে বলে—শুভশ্রী আমার বোন কিন্তু খুব সুন্দরী। তুই বিলকুল ভুল শুনেছিস। এখন দেখ ভেড়া চড়াতে যদি রাজি থাকিস তো শুভশ্রীর সঙ্গে তোর বিয়ে দিই, গদা সাক্ষী। এমনি উল্টোপাল্টা ঘটনার মধ্যে কখন যেন মা এসে বলল—রুণু আমি তা হলে যাচ্ছি, যাচ্ছিরে! আমি শামুর কথা শুনতে ব্যস্ত ছিলাম, ঘাড় নেড়ে বললাম—ঠিক আছে যা-ও। এই সময়ে তুলতুল ছুটতে ছুটতে এসে বলল—মাস্টারমশাই ও দিকে দেখুন ওই যে! আমি তাকিয়ে দেখি মহাসমুদ্রে সবুজ তুফান। একটা মাছ রাখার ঝুড়ি তার ভেতর দিয়ে ভেসে যায়। ঝুড়ির মধ্যে আমার মায়ের মাংস। মা পরপারে চলল। মা-মা বলে চিৎকার করে আমি জেগে উঠি। আমার দেড়তলার ঘরে পাক দিয়ে দিয়ে সেই চিৎকার ফেরে। যেন আমি নয়। অন্য কেউ, অন্য কারা, সমস্ত পাড়া, সারা পৃথিবী মায়ের মৃত্যু টের পেয়ে আর্তনাদ করছে।
১৩
খটখটে দুপুরে বেরিয়েছিলাম। রোদ যেন আগুনের তাত। ড্রাই হিট। নিশ্চয় বিয়াল্লিশ কি তেতাল্লিশ হবে। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার পুরনো বইয়ের দোকানে বি এসসি পাস কোর্সের একটা ফিজিক্সের বই কিনব। আজকাল দীপুর কাছে আমি ফিজিক্সটা শিখছি। নিজের ছাত্র-জীবনে যতটা শক্ত লাগত, এখন আর ততটা লাগে না। পড়াতে কাজে লাগে। হায়ার সেকেন্ডারির সিলেবাসও মাঝে মাঝে হ্যান্ডল করতে হচ্ছে। একটু বেশি না জানলে ওভাবে সীমাবদ্ধ পড়ানো যায় না। হঠাৎ খেয়াল হল রোদটা আর নেই, তাপ কমে গেছে, মুখ তুলে দেখি, পুরো আকাশটা নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জ ছায়ায় হয়ে গেছে। অলৌকিক আলো পড়েছে কলেজ স্ট্রিটের গলিতে। নতুন রং করা প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা ইউনিভার্সিটির আশুতোষ বিল্ডিং যেন ডানা মেলে ওড়বার জন্য প্রস্তুত অতিকায় পৌরাণিক পাখি। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড়ের হুটোপাটি শুরু হয়ে গেল। বইপত্রের ওপর পলিথিন চাপা দিয়ে স্টলওলারা কোথায় সরে পড়েছে। প্রবল হাওয়া আমাকে কখনও পেছনে কখনও সামনে টানছে, আর তেমনি ধুলো। চোখেমুখে এক-একটা ঝাপটা লাগছে আর মনে হচ্ছে গেল বুঝি চোখ দুটো। ট্রামলাইন পেরিয়ে দুড়দাড় করে ছুটি। বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট কফি হাউসের তলাটা ভিড়ে ভিড়। ওপরে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না। ওপরেও কি কোনও চেয়ার খালি পাব? ওপরে গিয়ে কিন্তু দেখলাম যথেষ্ট ভিড় হলেও উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা খালি টেবিল। আমার দিকে পেছন করে বসে একটি ছেলে কিছু পড়ছে। বোধহয় ওর অর্ডার এখনও আসেনি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলি—এক্সকিউজ মি, বসতে পারি?
ও মুখ তুলে তাকাল। দেখি—দেবল, দেবল গুহ। আমাকে দেখে কেমন চমকে গিয়ে একটা ফ্যাকাশে অপ্রস্তুত হাসি হাসল।
—কফি বলেছ?
—হ্যাঁ। তুমি কী নেবে?
—কফিই বলছি, ব্যস্ত হয়ো না। —আমি অবশ্য এক প্লেট পকোড়ারও অর্ডার দিলাম।
একটু এদিক ওদিক কথাবার্তার পর বলি—তোমাদের বাড়িটা অমন দুম করে বন্ধ হয়ে গেল, কিছু করছ না?
ম্লান মুখে দেবল বলল—কী করব বলো, স্বয়ং পার্টির লোক যদি নিজের আখের গুছোবার জন্যে তোমার পেছনে লাগে, তুমি কী করতে পারো? রক্ষকই ভক্ষক। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি—চাকলাদারই যে জগাদার কানে মন্তরটি দিয়েছে সে কথা ও জানে কি না। চেপে গেলাম। দেখিই না নিজে থেকে কী বলে! আমি শুধু বলি—দেখো সব রোগেরই তো ওষুধ আছে। জগাদাকে একটু ধরে পড়ো না, কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ নিয়ে বাড়িটা যাতে তোমাদের করতে দেয়, মানে কেসটা তুলে নেয়।
দেবল বলল—জগাদা নেক্সট ইলেকশানে কর্পোরেশানের টিকিট পাচ্ছে। এখন কখনও নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করে?
—তবে এক কাজ করো না, সাততলাটা পুরো ভেঙে ছ’তলা অব্দি করো, শেষ করে দাও।
—চারটে ফ্ল্যাটওনার ফিফটি পার্সেন্ট টাকা দিয়ে দিয়েছে। কী ভাবে তাদের সামলাব বলো!
—ওদের টাকা ফেরত দিয়ে দাও। কর্পোরেশনের নিয়মে আটকাচ্ছে, করতে পাচ্ছ না, এর ওপর তো আর কথা নেই। দুটো শাপমন্যি করবে—এই তো?
—সেটাই তো! চাকলাদার বলছে ওর সিক্সটি আর আমাদের ফর্টি পার্সেন্ট শেয়ার। এখন, লাভের শেয়ার যখন এই, লোকসানের শেয়ারও তখন একই থাকবে। সাততলার চারটে ফ্ল্যাটের পাওয়া-টাকা থেকে ফর্টি পার্সেন্ট ও আমাদের দিয়ে দিতে বলছে।
—কিন্তু… তোমরা কি ফ্ল্যাটটা থেকে এখনও কোনও টাকা পেয়েছ? এটা তো পুরোটাই প্রোমোটারের করার কথা। সে-ই নেবে, সে-ই বিল্ড করবে, তারপর ভাগাভাগি হবে। আমি তো এরকমই জানতাম!
—আরে চাকলাদার তো ঠিক সে-অর্থে প্রোমোটার নয়। ঠিকেদার একটা। দু’জন প্রোমোটারের সঙ্গে গণ্ডগোল হবার পর ও নিজেই সাজেস্ট করল ও-ই করে দেবে পুরোটা। প্ল্যান-ট্ল্যান তখন তো সব রেডি! আমরা আর আপত্তি করিনি। টাকা যেমন যেমন পাচ্ছে ও আমাদের দিচ্ছেও কিছু কিছু।
—আচ্ছা! তা কর্পোরেশনের স্যাংশন কি ঠিকঠাক ছিল?
—ওই তো গ্যাঁড়াকল! আগের প্রোমোটার বলল সাততলার ভিত করছি। দমকলের একটা পার্মিশন পেলেই সাততলাটা তুলে দেওয়া যাবে। এখন বেশি পেলে কে আর না চায় বলো!
—তো তাই যদি হয়, এখন পার্মিশনটা বার করার চেষ্টা করো না!
—আরে ভাই বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। শোনোনি! একবার যখন পার্টিতে ছুঁয়েছে…
—তা হলে লোকসানটা পুরিয়েই দাও। পুরো বাড়িটা তৈরি হয়ে গেলে তো অন্তত পক্ষে ফ্ল্যাটগুলোও পাবে!
—অত সোজা নয় ভাই, আমাদের আরও শরিক আছে না? সেজদাদু আর ছোড়দাদুকে তো চেনো না? একজন বিপত্নীক আরেকজন ব্যাচেলর মানুষ অত টাকা টাকা কেন করে বুঝি না। ফ্যামিলি নেই, কিছু নেই। ওরা রাজি নয়।
—তোমরা এখন থাকছ কোথায়? প্রোমোটারদের তো নিজেদের খরচে তোমাদের রাখবার কথা, যদ্দূর শুনি। এতে চাকলাদারের আরও লোকসান হচ্ছে জট ছাড়াতে চেষ্টাটা সে-ই বা করছে না কেন?
—বললাম না চাকলাদার সে-ভাবে প্রোমোটার নয়! ওরকম ব্যবস্থাও আমাদের গোড়া থেকেই হয়নি। এক দাদু থাকেন সিঙ্গাপুর। এক দিদা থাকেন দেরাদুন। আমরা থাকি মামার বাড়ি। আর দুই দাদুরও বাড়ি আছে। কাজেই ওটার ওপর জোর দিইনি।
খুব ম্লান মুখে দেবল বসে রইল। আমি ঝড় থামলে, যে সামান্য এক পশলা বৃষ্টি হয়ে রাস্তা আধভিজে হয়ে উঠেছে তার সোঁদা গন্ধ নিতে নিতে নিজস্ব বাসে উঠে পড়লাম।
যবে থেকে বাড়ি-ওঠা বন্ধ হয়েছে রমেন গুহ বা দেবল কেউ এ মুখো হয়নি। এত বড় একটা বাড়ি, এত সম্পত্তি, টাকা এভাবে আটকে আছে, লোকে কী করে সহ্য করে কে জানে! আমি হলে তো পাগল হয়ে যেতাম। আসলে সেই কবি বলেছেন না— ‘অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়!’ আমার দেড়তলার ঘরটা থেকে দাদা যদি আমাকে বার করে দেয় আমি কী করব জানি না। এমন মুখ-খিস্তি করব যে দাদার চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে, কিংবা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে শামুর কাছ থেকে একটা বোমা এনে টপকে দেব, যা শ্শালা হোল বাড়ি উড়ে যা! কিংবা রাগে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পাতাল রেলে ঝাঁপ? তা-ও হয়তো দিতাম। কিচ্ছু বলা যায় না। অথচ এদের একটু মুখ শুকনো হওয়া ছাড়া হেলদোল নেই!
ফিজিক্সের টেক্সট বুকখানা দীপুর কোলে ফেলে দিলাম, —দ্যাখ এতে হবে? উল্টে পাল্টে দেখে বলল—ঠিক আছে। তোকে যেটা বলেছিলাম সেটা আরও ভাল, কিন্তু বেসিক্স্-এর পক্ষে এটা খারাপ নয়। এটা শেষ করে একটু লাইব্রেরি থেকে আনা। তোর তো আজকাল কলেজের ছাত্তরও হচ্ছে! পড়ে নিবি। আটকালে আমি আছি।
এত ভাল বোঝায় দীপু, যখন ব্যাখ্যাতার ভূমিকায় থাকে তখন ওর চোখ থেকে সেই এলোমেলো পাগল-ছাগল চাউনিটা উবে যায়। কেন যে ছাত্র পড়িয়েও অন্তত কিছু রোজগার করে না! এইসা রাগ হয়ে যায় না একেক সময়ে। কিন্তু কাউকে বলে কিছু করানো যায় না। দীপুর কাছে যদি ওর কেসটা নিয়ে কথা বলতে যাই কীভাবে এড়াবে জানেন! ধরুন বললাম—আচ্ছা দীপু ট্যুইশনি করে তো তুই যথেষ্ট রোজগার করতে পারিস!
—সবাইকে দিয়ে কি আর সব কিছু হয়! —উত্তর হবে।
—আমি জানি না, তোর হয়তো ভাল লাগে না, কিন্তু সংসারের কথা ভেবেও তো একটু চেষ্টা করতে হয়!
—সংসারের কথা আমি ভাবছি না তোকে কে বললে? বিশু রাসকেল?
অর্থাৎ দীপু তাতছে।
—ভাববার কোনও লক্ষণ তো দেখি না!
—দুটো ব্যাপার আছে রুণু, সাবজেকটিভ আর অবজেকটিভ। অবজেকটিভ দিকটা দেখতে পাচ্ছিস না বলে যদি জিনিসটাকেই অস্বীকার করিস তা হলে ভগবানকেও অস্বীকার কর। সাইবেরিয়াটাও অস্বীকার করা যায়।
—সে আবার কী! ভগবান ছাড়, কিন্তু সাইবেরিয়া আছে সবাই বলছে, জোগ্রাফি বলছে, কাগজ বলছে।
—আমিও তো বলছি—আমার ভাবনা আছে—এটাও তোর কাছে হিয়ারসে, কাগজের কথাটাও তোর কাছে হিয়ারসে। আগে যা দেখে আয় সাইবেরিয়া আছে। তারপর বলিস।
—মাসিমা রোজগার করছেন তবে খাচ্ছিস, ছোট ভাই-বোনদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।
—মা-ই তো শাবককে খাওয়ায়। ওটা তো মায়েরই কাজ। তা ছাড়া মায়ের যা লাইফ তাতে মা যদি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে কোনও কাজ না করতে পারে, ডিপ্রেস্ড্ হয়ে যাবে। মা-ও ছারপোকার…
—চুপ কর দীপু। বাজে বকিস না।
—তুইও বাজে বকিস না। নিজের চরকায় তেল দে। আমি কী করব না করব আমার প্রাইভেট ব্যাপার। তুই নাক গলাবার কে রে?
কেউ যদি এভাবে তোমাকে অপমান করে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, তা হলে আর কিছু করার থাকে না।
একদিন বললাম—তুই সন্ন্যাসী হয়ে চলে যা না!
—কেন? তাতে তোর কী সুবিধে?
—আমার? তোর নিষ্কর্মা বৃত্তি দেখলে আমার কেমন গা কিসকিস করে। আগেকার দিনে প্রায়ই গৃহস্থ ঘরের ধর চার ছেলে-মেয়ের বাবা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-মা-বাবা সব ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়, মিনি-হিমালয়ে গিয়ে গাঁজায় দম দিত, কেন জানিস?
—কেন আবার? ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ’ সেই কেস। ঈশ্বরের ডাক শুনত!
—তোর মাথা! অত সোজা! চারটে-পাঁচটা বাচ্চা-কাচ্চা তৈরি করেছে, দু’ বেলা বউয়ের হাতের পাখার বাতাস খেতে খেতে চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় সাঁটাচ্ছে, ধর বাবা মারা গেলেন, অমনি বিবাগি হয়ে গেল! যে-বাবার সঙ্গে জ্যান্তে দিনে চারটে কথা হত কি না সন্দেহ!
—স্পিরিচুয়াল নয়? তা হলে কী?
—তা হলে আর কী! দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে সে-সব ফেলে ভোঁ দৌড়। নইলে যে পরিমাণ লোক আমাদের দেশে সন্ন্যাসী হয়েছে তাতে তো আধ্যাত্মিকতার বান ডেকে যেত রে দেশে। ওই সন্ন্যাসীগুলো কী করে বল তো! স্রেফ গুলতানি করে,ভ্যাগাবণ্ডগিরি করে আর চালাকি করে ভিক্ষে করে। গাঁজায় দম মারলেই ইহকাল পরকাল শীত-গ্রীষ্ম সব বিস্মরণ হয়ে যায়। ব্যাস, আর কী! উপরি-লাভ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, ভয়।
—কী যে বলিস রুণু। তোর মাথাটা একবারে খেয়েছে এস এফ আই। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ সব ভড়ং?
—তারা কেন হবে? এই এলেবেলে সন্ন্যাসীগুলো যারা কুম্ভমেলা সাগরমেলায় ঘোরে, গ্রাম-ট্রামের ধারে বটগাছ—তাদের তলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে চিমটে হাতে রাগ দেখায়, আবার জ্ঞান দেয়। এখন খবরের কাগজে যাদের ছবি দেখছিস রে নিত্য, তুই বিশ্বাস করিস এদের কিছুমাত্র বৈরাগ্য, অনাসক্তি, মহত্ত্ব বা আর কিছু গুণ আছে?
—তুই আমাকে এইগুলোর মতো হয়ে যেতে বলছিস? দীপু আহত অবিশ্বাসের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।
—হয়ে যেতে বলব কেন? তুই তো অমনিই। যখন-তখন রাগে চিমটে ছুড়িস, আবার কীসব দৈববাণী শোনার ভড়ং করিস, ত্রৈলঙ্গস্বামীর মতো বোমভোলা ভাব! সবটাই আছে শুধু ভেকটা নেই। গেরুয়া, রুদ্রাক্ষের মালা, জটা, ত্রিশূল, গাঁজার কলকে। তা নিয়ে ফ্যাল!
—তুই আমার ভয়েসকে ভড়ং বললি রুণু? অথচ তোকেই আমি একমাত্র বিশ্বাস করে বলেছিলাম কথাটা।
দীপু গুম মেরে ইটের পাঁজার ওপর সেই আবোল-তাবোলের রাজাটার মতো বসে রইল।
এইভাবেই বোধহয় তাকে আবিষ্কার করে চাকলাদার।
কেন না শুনতে পেলাম, চাকলাদারের গাঁজাখোরের মতো বিরাট গলা—কী ব্যাপার দীপু মাস্টার। তুমি এখানে বসে? তোমার সুবল সখাটি কোথায় গেল?
দীপু বোধহয় কোনও উত্তর দেয়নি। কেন না চাকলাদার পড়ো অফিস ঘরটায় এসে গেল। বলল—ও সাহেবও তা হলে আছে? শোনো ভাই, আরও একটা ডিসিশন নিতে হচ্ছে। দু’জনকে রাখতে পারছি না। একজনকে রাখব। ওই এক হাজার। তোমরাই ঠিক করো কে থাকবে। আমার খুব বাজে লাগছে ব্যাপারটা। কিন্তু যদ্দিন না কাজ আরম্ভ করতে পারছি… আমার দিকটাও তোমরা বোঝো। কাজ শুরু হয়ে গেলেই শিওর ডেকে নেব। তখন আবার সেই আগেরকার মাইনে। শেষ হলে অন্যত্রও।
বেশ একখানা লেকচার। লম্বা। আমার পারা চড়ছে, চড়ছে।
—চাকলাদারবাবু আপনার এই সো-কল্ড, চাকরিটা কি আমি সেধে সেধে নিয়েছিলাম?
—না, ইয়ে, তেমন তো কোনও…
—আপনিই বরং সেধে সেধে টাকার লোভ দেখিয়ে এই থ্যাংকলেস জবটায় আমাদের ভিড়িয়েছেন। সত্যি কি না?
—থ্যাংকলেস তো আমারও। আমার আরও।
—না আপনার নয়। আপনি সেদিন আঙুলে টুসকি মেরে বলেননি, সবই টাকার খেলা, তা সেই টাকার খেলাটা খেলতে দেরি করছেন কেন? সাততলা বাদ দিয়ে বাকি ফ্লোরগুলো তুলে ফেলা যায় না, এ কথা আমি এত ইডিয়ট নই যে আমাকে বোঝাবেন। জগা মিত্তিরের সঙ্গে টাকার রফাটা করে নিলেই সে কেস তুলে নেবে। সেইটা করছেন না মানেই আপনার অন্য কোনও অভিসন্ধি আছে। এটা বুঝি না এত ক্যাবলা আমি নই।
কিছুক্ষণ ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল চাকলাদার। তারপরে বলল—
—অভিসন্ধি? কী অভিসন্ধি আমার এর মধ্যে তুমি খুঁজে পেলে? তুমি তো আচ্ছা ছেলে! কী অভিসন্ধি হতে পারে!
—সেটা আমি কেন বলব? আপনার অভিসন্ধি আপনারই থাক। এর মধ্যে আমাকে আর জড়াবেন না। আমি চললাম।
লোকটাকে আর একটাও কথার সুযোগ না দিয়ে আমি গনগন করতে করতে চলে আসি।
ইটের পাঁজার ওপর থেকে দীপু চিৎকার করে বলল—চললি?
—হ্যাঁ চললাম।
কিন্তু বিকেলে যখন দীপু আমার বাড়ি এসে বলে গেল—ও কাজ ছাড়ছে না, আমি যখন নিজের ইচ্ছেয় ছেড়ে দিয়েছি তখন ও করছে, করবে, তখন সত্যি কথা বলব কী ক্ষোভে ঘেন্নায় আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। এই সেই বন্ধু রোজগার দেবার তাগিদে আমি আমার চাকরি যার সঙ্গে স্বেচ্ছায় স্বপরিকল্পনায় ভাগ করে নিয়েছি!
দীপু ভীষণ চালাক-চালাক চোখে বলল—বুঝলি না রুণু, লোকটার একটা সুপারভাইজার ভীষণ দরকার। নয়তো ভেতরটা জবরদখল হয়ে যাবে, তখন হাজার ঝামেলা। একটা কুকুর হোক বাঁদর হোক ওর চাই-ই। এদিকে টাকাটা কমাতে চাইছে। মওকা বুঝে আমিও দাঁও মেরেছি। ওই ভূতের বাড়িতে কে পাহারা দিতে আসবে বল? আসলেও চুরি চামারির মতলবে আসবে। সততা, সিনসিয়ারিটি এগুলো এসব কাজে বড্ড লাগে রে! অথচ মিচকে পটাশ ছিঁচকে চোর থেকে যত্ত থার্ড ক্লাসের ভিড় তো এই বিজনেসে! আমিও বলেছি—ঠিক আছে। এত করে বলছেন যখন করব কিন্তু দেড় হাজারের কমে নয়। কস্তাকস্তি করে সাড়ে বারোশো’য় রফা হয়েছে। ভাল নয়?
কী বলব একে! এই আড়-পাগলার মতো ঘুরছে। এই মাতা-কর্তৃক শাবকের ক্ষুন্নিবৃত্তির ফিলসফি আওড়াচ্ছে, এই ভয়েস শুনছে, আবার এই মওকা বুঝে দাঁও মারছে!
সংক্ষেপে বলি—তোর হবে!
—বলছিস! আগে যে বলতিস হবে না!
—বলে থাকলে ভুল বলতাম। আই বেগ ইয়োর পাৰ্ডন।
—তোর ফিজিক্সের কোনও অসুবিধে হবে না। যখনই দরকার হবে চলে আসবি। অফিস ঘরটা তো এখন একা এনজয় করব। আ-হ কী আরাম।
—তুই এবার যা—বলবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ওই যে সীমা! সীমাটা একেবারে কালো পাথরের দেয়ালের মতো। ইচ্ছে ওইখানে এসে ঠেকে যায়। মনে পড়ে যায় উচ্ছিন্ন হকার বাবার আত্মহত্যা, মাসিমার রাঁধুনিগিরি, মুক্তাটার চুল ঝাঁটানো, দীপুটার ভ্যাগাবন্ড-গিরি, এক মিনিটের একটা সামান্য ভগ্নাংশের মধ্যে সমস্ত এক সঙ্গে মনে পড়ে যায়। বলি না। তবে দীপু চলেই যায়। ও চট করে কারও বাড়ি আসে না। সামাজিকতা, বন্ধুর বাড়ি এসে চা খেতে খেতে আড্ডা এ জিনিস ওর নেই। ওর পার্মানেন্ট ঠিকানা—রাস্তা। দীপন চক্কোত্তি কেয়ার অফ রাস্তা। সে রসিক ঘোষের লেনও হতে পারে, শনিতলার মোড়ও হতে পারে, গড়িয়ার কাছে বাই-পাস কানেক্টরও হতে পারে। এনি রাস্তা। তেষ্টা পেলে রাস্তার কলে জল খেয়ে নেবে। সারাদিনে হয়তো দু’ভাঁড় চা আর তেলেভাজা, ঝালমুড়ি…
—এ সব খেয়ে শরীরটা নষ্ট করিসনি দীপু—যদি বলি, ও বলবে—না রে, দানাদারও খাই। দানাদার, ক্ষীর কদম্ব।
একে আপনি কী বলবেন?
১৪
মহালক্ষ্মী মহাজন মারাই গেলেন। হার্টের ট্রাবল ছিল। ছোট ছেলের সন্ধান পাওয়া না যাওয়ায় বেচারির করোনারি অ্যাটাক হয়। সেই যে নার্সিং হোমে গেলেন, আই সি ইউ থেকে আর বেরোতে পারেননি। একদিন দেখলাম একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল, তার ভেতর থেকে স্ট্রেচারে করে এক রুপোলি রঙের বৃদ্ধার মরদেহ বেরোচ্ছে। জগদিন্দ্র এসে নার্সিং হোমের লোকেদের সঙ্গে হাত লাগালেন। হঠাৎ দেখি সত্য, পানু আর আমিও জুটে গেছি। বৃদ্ধ এ এস বিরাট সিটিংরুমটার মধ্যে একটা একানে চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। বাড়িটার দেয়াল, দরজা, জানলা, আসবাবপত্র, সাজসজ্জা সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা কবরের তলার নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে। কেউ কাঁদছে না। অন্তঃপুর থেকে নাতি-নাতনিরা এসে দাঁড়াল প্রথমে। চমৎকার একটা সোনালি জরিপাড় সিলকের শাড়ি, বোধহয় পরিয়ে দিয়েছে নার্সিংহোম থেকেই, রুপোলি চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। কাঁধ অবধি। কপালে চন্দনের তিলক। নাতি-নাতনিরা কেউ ফুল, কেউ মালা দিল। সব আট থেকে সতেরোর মধ্যে বয়স। একটি বছর দশ-এগারোর মেয়ে হঠাৎ ‘দাদি’ বলে একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। এ বোধহয় মহেন্দ্রর। সবচেয়ে বড় ছেলেটি তাকে কাছে টেনে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। দুই বউ এলেন, সব শোকের সাদা শাড়ি পরা। আরও তিন-চার জন বউকে দেখলাম। খুব ক্লোজ মনে হল। হয়তো মেয়ে, আমরা জানি না। প্রত্যেকে ফুল বা মালা দিয়ে প্রণাম করলেন তারপর মুখের ওপর কাপড় চেপে নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেলেন।
অ্যাম্বুলেন্সটা আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গুরুদ্বার থেকে সৎকার-এর গাড়ি এসে দাঁড়াল। এবার স্ট্রেচারের চার কোণ ধরে বৃদ্ধাকে তুললাম জগদিন্দ্র, সত্য, পানু আর আমি।
কাগজে বেরোল খবরটা—মহেন্দ্র মহাজনের কোনও সন্ধান মেলেনি। কোনও খবর নেই! তাঁর মা মিসেস মহাজন হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু পুলিশ কী-ই বা করতে পারে? মহাজন ফ্যামিলি পুলিশের সঙ্গে একেবারেই সহযোগিতা করছে না। তবে ড্রাইভার মদনলালের পোস্ট-অপারেশন শারীরিক অবস্থা এখন অনেক ভাল। মদনলালকে হাসপাতালেই জেরা করছে পুলিশ। যেটুকু জানা গেছে, তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তা প্রকাশ করতে চাইছে না।
শব-সৎকারের পর যখন মিছরি শরবত কোনও মতে গলাধঃকরণ করে চলে আসছি, বৃদ্ধ এ এস আস্তে আস্তে উঠে এলেন, আমার মাথায় হাত রাখলেন, সত্য আর পানুর হাত ছুঁলেন, বললেন—থ্যাংকিউ বয়েজ। গলাটা ঈষৎ ভাঙা।
আমার এই তৃতীয় শবযাত্রা। প্রথমটা ছিল আমার নিজের বাবার। বাজার করে এসে বসলেন, এক গ্লাস জল চাইলেন, বউদি জলটা এনে হাতে দিচ্ছে বাবা ঘুরে পড়ে গেলেন, সেরিব্র্যাল স্ট্রোক। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বা বাড়িতে দীর্ঘদিন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কি বাক্শক্তিহীন দুরারোগ্য রোগীকে তিলে-তিলে মরতে দেখার দুর্ভাগ্য আমাদের হয়নি। বিধাতাপুরুষ বোধহয় মনে মনে একটু বিচার করেছিলেন—তিন প্রজন্ম ধরে এরা ভুগছে। কোথায় ফরিদপুরের একশো বিঘে জমির জমিদারি, স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টারগিরির মর্যাদা, বিশ-পঁচিশটা মুনিষ মাইন্দার খাটছে আর কোথায় কলকাতার প্রান্তিক ড্রেনহীন, কোনও নাগরিক সুযোগ-সুবিধাহীন জবরদখল কলোনি। দিবা-রাত্র দূর-দূর। কী সংগ্রামের মধ্যে টিউকল, দখলীকৃত জমির পাট্টা পাওয়া। প্রথমে কর্পোরেশন স্কুল। তারপরে বড় স্কুল। লণ্ঠনের আলোয় আপ্রাণ পড়া মুখস্ত করে সেকেন্ড ডিভিশন পাওয়া। কোথাও কোনও কাজের লোকজন নেই। আলু সেদ্ধ ভাত খেয়ে পরের জমিতে ভিটে তোলবার দুঃসহ মানসিক পীড়ন। হয়তো বিধাতৃশক্তির মধ্যে বিবেকের উদয় হল। তাই। দ্বিতীয় যাত্রা—দীপুর বাবা। ওরে বাবা, সে প্রথমে বাঙ্গুর হাসপাতাল, তারপরে লাম্বার পাংচার-টার ফেল মারলে লাশকাটা ঘর। সেখান থেকে ডোমেদের সঙ্গে কুৎসিত ঝগড়া করে শব ফিরে পাওয়া, শবদাহ করে প্রায় মাঝরাতে বাড়ি ফেরা, কীরকম পাথর চোখে চেয়ে মাসিমা বললেন —ভালই হয়েছে। একটা মুখ একটা পেট কমে গেল, কী বলো রুণু! কিন্তু ওই মুখটাই যে আর সব পেটের জোগাড় করত, তার কী করছি! একবার আলোচনা করলে পারত, সে-কালে আমরা ওষুধটা খেতাম, ও বাঁচত! একটা নিঃসম্পর্ক ব্যাটাছেলের আর কী লাগে? একটা গামছা আর এক বান্ডিল বিড়ি! —এমন নিস্তাপ গলায় চাহনিতে কথাগুলো বললেন যে মনে হল—আলোচনাটা যে হল না আজও, চমৎকার, কিন্তু অলটারনেটিভটা আরও চমৎকার হত, আলোচনার অভাবে যে হতে পেল না এটাই মাসিমার আফসোসের কারণ। আমার শিরদাঁড়া দিয়ে যেন হিমবাহ নামছিল, চার পাশে ওরা পাঁচ ভাই বোন কেমন ছিটোনো ধুলোবালির মতো বসেছিল, এঃ একটা ভুল হয়ে গেল এরকম একটা ভাব। সত্যিই দেখুন মেয়েদের কত কী লাগে! অতি বৃদ্ধা হবার আগে পর্যন্ত পর্যাপ্ত লজ্জাবস্ত্র চাই। এখন সে যদি স্বেচ্ছায় করিনা কপূর-ফপুর হতে চায় তো আলাদা কথা, নইলে বস্ত্র চাই-ই, ছেলেদের, বাড়ন্ত ছেলেদের, মেয়েদেরও দুরন্ত খিদে। এটুকুতে হবে না আরও চাই। বাবা-মা তোমাদের ভাগগুলো দাও, পেট ভরছে না। তা ছাড়া চাই কিছু না কিছু লেখাপড়া, কোনও বৃত্তির প্রশিক্ষণ, মেয়েদের বিয়ে চাই। নইলে পাবলিকের ভোগে যাবে। কিন্তু আত্মীয়স্বজনহীন একজন বয়স্ক ব্যাটাছেলের কীই-বা লাগে! মাসিমা খুব চমৎকার সাম-আপ করেছিলেন, বেঁটেদাও যেটা পরে পরিষ্কার বুঝেছিল—চেড়ি আর বিড়ি।
—আর এই মৃত্যু? এ শোক শুধু শোক নয়। কেমন দুরন্ত অভিমানে ঠোঁট ফোলানো শোক। কাঁদব না। না, ফুঁপিয়েও না, যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ নয়, যে-কষ্ট দিয়েছ তার কোনও তল নেই। কী ক্ষতি করেছিলাম কার? কিচ্ছু না। জন্মসূত্রে ব্যবসার পেশা পেয়েছি, লাভ-লোকসানের হিসেব, কোনটা কীভাবে করতে হয় এসব বহু জন্মের শিক্ষা ও অভ্যাসের উত্তরাধিকার। আমরা বড়বাজারি কারবারি নই যে ঘিয়ে সাপের চর্বি, তেলে শেয়ালকাঁটা বা ইনজেকশনের অ্যাম্পুলে জল ভরে বিক্রি করেছি। বিদেশি ইলেকট্রনিক গুডস্-এ বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। আমাদের কয়লাখনিগুলো শেষ হয়ে যাবার পর বাজারের চাহিদা বুঝে তৈরি করছিলাম, আরও বড়, আরও ভাল সব জিনিস, একটা কমপিটিশন দেবার চেষ্টা করছিলাম। মাথা খাটিয়ে ভাল উপার্জন করেছি, সুখে থেকেছি। আরও সুখের বিষয়, ফ্যামিলিটাতে কোনও ক্ল্যাশ অফ ইনটারেস্ট ছিল না, ফাটল ধরেনি। কী ক্ষতি করেছিলাম কার যে আমাদের বাড়ির ছোট ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গেলে? আমাদের মাকে মারলে? —আমি যেমন কোনও বিধাতৃপুরুষের করুণা বা বিবেকবোধ দেখতে পাই আমাদের বাবার যন্ত্রণাহীন তাৎক্ষণিক মৃত্যুতে, ওরা হয়তো তেমনি বিধাতৃপুরুষের ঈর্ষা, বিদ্বেষ দেখে। পাড়ার সবাইকার চোখ-টাটানোও দেখে। এই শবযাত্রার পর আমি প্রথম সত্যি করে বুঝতে পারলাম— ধনী লোকেরাও আমাদেরই মতো মানুষ। তাদের শান্ত থাকা, তাদের অশ্রুহীনতা, চূড়ান্ত শোকের সময়েও ধীর থাকা এক ধরনের শিক্ষার ফল। ভেতরে-ভেতরে সেই একই আকুলতা, আর্তনাদ, হাহাকার, সেই ছোট মেয়েটির ‘দাদি’—বলে কেঁদে ওঠা! সংযম, কিন্তু সারাদিন একই চেয়ারে স্থবির বসে থাকা। ভাঙা গলা ‘থ্যাংকিউ বয়েজ।’
এবারে ঘন-ঘন মহাজনদের খবর বেরোতে লাগল। এখনও যখন মুক্তিপণ চেয়ে ফোন টোন আসেনি, তখন মনে হয় এ বিজনেস রাইভ্যাল্রি। কোন কোন হাউজের সঙ্গে মহাজনদের কারবার ছিল, ক্লোজ কম্পিটিশন ছিল তার লিস্টি বেরোতে লাগল। তদন্ত চলছে। মদনলালের সাক্ষ্য থেকে নাকি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাদি পাওয়া গেছে। একটা কাগজের স্কুপ-নিউজ-মদনলালের সাক্ষ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। ডি. সি. ডি ডি-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, নো কমেন্ট। মহেন্দ্র কি বেঁচে আছেন? এ নিয়েও নানারকম কাগুজে জল্পনা চলে। এক কাগজ বলে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মহেন্দ্রর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম। পরদিনই লালবাজার থেকে প্রতিবাদ বেরোয়। এমন কথা তাঁরা কখনও বলেননি।
মহেন্দ্র তো একা নন। মাঝে-মাঝেই কোনও ধনী ব্যবসাদার কি টপ এগজিকিউটিভ এভাবে হাপিস হয়ে যাচ্ছেন। নিশ্চয় এটা একটা চক্র। আর সেই চক্র ভেদ করতে পারছে না পুলিশ? হয় তারা পুরো অপদার্থ। আর নয় গদ্দার। শুধু আমি কেন, আমাদের পাড়া কেন, সমস্ত জনসাধারণের এই ধারণা। তবে হ্যাঁ, যাচ্ছে ধনী লোকেরা, হাঙর-কুমিরে কি আর পুঁটি মাছ ধরে! এই বিশ্বাসে, আশ্বাসে জনসাধারণ চুপচাপ আছে। ধনী লোকেরা নিজেদের খরচে নিরাপত্তারক্ষী রাখছেন। পুলিশকে কিছু বলছেন না। ভরসা নেই।
কিন্তু আমাদের মতো জনসাধারণেরও হাজারো দুঃখের মধ্যে আরও দুঃখ মানে বিপদের দিন আসে। একদিন রমজান আলি আমাকে রাস্তায় ধরলেন।
—কী খবর রুণু ভাইজান?
হঠাৎ কেন কাকার বয়সি লোকটার ভাইজান হয়ে গেলাম জানি না।
—খুব তো পড়াচ্ছ। টিউটর বলে নাম বেরিয়েছে বাজারে।
আমি কিছু বলি না।
—সমশেরের বোন হাসিনাটাকে তো মাধ্যমিক পাশ করিয়ে ছাড়লে? ভাল ভাল, কথাটা কী জানো? তোমাদের মধ্যে যেমন-যেমন মেয়েলোকের লেখাপড়ার চল হয়েছে, তেমন তেমন সংসারের শান্তি ঘুচেছে। মুখে মুখে কথা, অভব্য পোশাক, ব্যভিচার, ডাইভোর্স।
আমার রাগ হয়ে যায়, বলি—হাসিনা মাধ্যমিক পাশ করেছে, আবার আমার কাছে পড়ে—এ খবরটা খুবই আনন্দের। শুধু আমিই ব্যাপারটা জানি না। আর লেখাপড়ার বিরুদ্ধে, বিশেষ করে মেয়েদের লেখাপড়ার বিরুদ্ধে তিন শতক আগের ভোঁদা কথাগুলো বন্ধ করুন। আপনার মতো লোকেদের জন্যেই আপনাদের মেয়েগুলোর এত কষ্ট। পুরো সমাজটা আপনাদের পিছিয়ে আছে।
—তুমি তা হলে আমাদের মেয়েদের কষ্ট ঘোচাবার, সমাজটাকে এগোবার ঠিকে নিয়েছ?
—নিতে পারলে তো ভালই হত। কিন্তু সে সাধ্য কোথায়!
—কেন! ঘাবড়াবার কী আছে? ছোট করে শুরু করো। প্রথমে হাসিনা, তারপর সাকিনা, তারপর আমিনা টামিনা…
আমার এবার হাসি পেল। মনে পড়ে গেল এই লোকটা হাসিনাকে বিয়ে করতে চাইছে। প্রথম বউকে তালাক দিয়েছে। দ্বিতীয় বউ এখন শয্যাশায়ী।
—রোজগারপাতি কী করছ আজকাল!
—যাই করি, দেশের দামি জিনিস তো পাচার করছি না।
—এত্ত তেল! বেকার-বেগানার আবার জবান!
রাগে মুখ লাল সাদা হচ্ছে লোকটার।
আমি পেছন ফিরি। যথেষ্ট হয়েছে। ডেঞ্জারাস লোক।
বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবি—সমশেরের বোন মাধ্যমিক পাশ করেছে? একদিন শামু বলেছিল বটে ও রবীন্দ্রনাথ পড়ে। বাঃ! কিন্তু আমি ওকে পড়িয়ে পাশ করিয়েছি এমন গুজব কী করে রটল! গুজবটা সত্যিই রটেছে না আলিচাচা জাস্ট অন্ধকারে ঢিল ছুড়েছে?
বাড়ি এসে বউদিকে বললাম কথাটা। বউদির মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।
—কী ব্যাপার বলো তো বউদি, তুমি চেনো হাসিনাকে? জানো খবরটা? বউদি খুব ভয়ে ভয়ে মাথা হেলাল।
—জানো? আশ্চর্য? কী জানো? আমাকে বলোনি তো!
তখন বউদি যা বলল তাতে আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।
দীপুর বোন মণিমালা নাকি হাসির খুব বন্ধু। সে-ই হাসিকে বই ধার দিত। পড়াত বরাবর, হাসির ভীষণ আগ্রহ, মাথায় কিছু বস্তুও আছে। মণিই এসে বউদিকে ধরে হরসুন্দরীতে হাসিকে ভর্তি করে নিতে। ক্লাস নাইনে। ভর্তি হবে কিন্তু স্কুলে যাবে না, মাধ্যমিকটা যদি অন্তত এইভাবে পাশ করতে পারে। বউদি না কি সেই মর্মেই হরসুন্দরীর বড়দির কাছে দিনের পর দিন দরবার করে। মেয়েটি আসবে না। কিন্তু সে অ্যাটেনড্যান্সের পার্সেন্টেজ পাবে, অনগ্রসর এলাকার মেয়ে। এত আগ্রহ, বাড়ি এবং পাড়া বড়ই রক্ষণশীল, সে কি এইটুকু সুযোগ পেতে পারে না? বড়দির বাসায় রাত্তিরে মণির সঙ্গে অনেক বার গেছে হাসি। বড়দি নিজে হাসিকে ইংরেজি পড়িয়েছেন। বউদি তাকে হিসট্রি জোগ্রাফি পড়িয়েছে। মণি বাকি সব দেখিয়ে দিয়েছে। আমার কাছ থেকে মণি মাধ্যমিকের সময়ে যে সাহায্য পেয়েছে, স্বভাবতই সে সবই হাসিও পেয়েছে। যে-দিন মণি নিজেদের পাসের খবর জানাতে এসেছিল সে-দিনও নাকি হাসি ওর সঙ্গে ছিল। মা আর বউদি ওদের লুচি বেগুনভাজা রসগোল্লা খাইয়েছিলেন।
বলতে বলতে আমার অমন সাহসিকা ফাজিল বউদি কেঁদে ফেলল। আমি বললাম, ও কি? কাঁদছ কেন? একটা কাজের মতো কাজ করেছ তো!
—মেয়েদুটো এসে অত করে ধরল, কী করি বলো!
—কী আশ্চর্য, বেশ করেছ, এর মধ্যে কৈফিয়তের কান্নাকাটির কী আছে?
—কিন্তু রমজান লোকটা যে ভাল নয়! তোমার সঙ্গে হাসির নামটা যে জড়িয়ে দিয়েছে।
—আমি তো ওকে বলেছি—আমি কাজটা করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু করিনি, বিন্দুবিসর্গও জানি না ব্যাপারটার।
—তুমি বড্ড সরল রুণু। তুমি বললে আর ও অমনি বিশ্বাস করে নিল! এ রকম হয় না কি? এসব ডেঞ্জারাস লোক। তা ছাড়া কিছু প্রমাণ তো রয়েই গেছে।
—প্রমাণ? কীসের প্রমাণ?
—তোমার নাম লেখা বই যা তুমি মণিকে দিয়েছিলে। তোমার হাতে লেখা নোটস যা তুমি মণিকে দিয়েছিলে সে-সব তো এখন ওর কাছে। ওর বাকসো খুঁজলেই মিলবে।
—যা বাব্বা, একজনের বই, নোটস আরেকজনের কাছে যেতে পারে না? যে নিয়মে আমার কাছ থেকে মণির কাছে গেছে, সেই একই নিয়মে …
—এসব তো স্ট্রেট ফরোয়ার্ড সহজ সরল লোকের ভাবনা। রমজান লোকটা হাসিকে বিয়ে করবার জন্যে মরিয়া হয়ে গেছে, সে এখন নানারকম সন্দেহ করবে।
—একজন লোক মিথ্যে সন্দেহ করবে বলে আমাদের ভয় পেতে হবে! আচ্ছা তো! ওর হাসিকে বিয়ে করতে ইচ্ছে তো করুক গে না বিয়ে, আমি কি কিছু বলতে যাচ্ছি?
বউদি এইবার খুব করুণ গলায় বলল—কথাটা তুই বললি রুণু? আমি ঠিক শুনেছি তো!
—হ্যাঁ বললামই তো! তাতে কী হয়েছে?
—আজ যদি কেশবকাকা মণিকে বিয়ে করতে চায়, তোরা পাড়ার ছেলেরা চুপ করে থাকবি?
আমি হেসে ফেলি—কেশবকাকা?
—কেন? বউদি বলে, কেশবকাকা কি রমজান আলির থেকেও খারাপ পাত্র?
—তা অবশ্য বলা যায় না! কিন্তু কেশবকাকার তো কেশব কাকি রয়েছেন? কী করে তিনি ইচ্ছে করবেন? ছুঁকছুঁক করছে না কি বুড়ো ভাম? মারেগা এইসা ঝাঁপড়!
—দ্যাখ দ্যাখ রুণু, নিজেই দ্যাখ মণির বেলায় তোর রি-অ্যাকশনটা কীরকম হল। একেবারে স্পনটেনিয়াস! রমজানও তো একটা বুড়ো ভাম-ই। কোন না চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বয়স হবে। তারও তো ঘরে বিবি রয়েছে! একটা আঠারো বছরের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে চাইছে। ওর বড় ছেলে আর মেয়ে দুটোই হাসির থেকে বড়।
—আমরা কী বলব! বলতে গেলে ওই রমজান চাচার চাচি-ই হয়তো এসে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে যাবে। ওরা এতেই অভ্যস্ত।
—এতে কোনও মেয়ে অভ্যস্ত হতে পারে না রুণু, বাজে কথা বলিস না।
—তা সে তুমি যা-ই বলো। রেজিস্ট করতে হবে হাসিকে। তার পরিবারকে। আমাদের কিছু করবার নেই।
—এই কথাই তা হলে বলব তাকে?
—কাকে? হাসিকে?
—আর কাকে!
—সে আমার পরামর্শ নিয়ে চলে তা তো জানতাম না! আর একটা না-জানা জিনিস!
বউদি পায়ের আওয়াজ করে চলে গেল। দুম দুম করে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু মানুষটা এতই হালকা যে সে চেষ্টা ফলবতী হল না।
আমার ভেতরটা কেমন একটা উল্লাসে ফেটে পড়ছে! মণি, আমার বন্ধুর বোন, মণিমালা আমার ছাত্রী নিজে পারাবার পার হতে চাইছে, আরেকটি মেয়েরও মুক্তি সে সম্ভব করেছে। দু’জনেরই প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশ। মণি তার সমাজ থেকে কিছুটা হলেও সাহায্য পেয়েছে, হাসি পায়নি। পায়নি কী? কীসের সমাজ? মণি হাসি দু’জনেই নির্ভেজাল বাঙালি। এক ভাষায় কথা বলে। চেহারার ধরন একরকম। অর্থের দিক থেকে দেখতে গেলে দু’জনেই নিম্ন মধ্যবিত্ত। নিম্নবিত্ত বলাটাই ঠিক ছিল। কিন্তু মণি আর দীপু দু’জনে মিলে ওদের নিম্নবিত্ততাকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে লাফিয়ে পার হয়ে গেছে। শামুকে পয়সাকড়ির দিক দিয়ে হয়তো উচ্চমধ্যবিত্ত বলা যেত, কেন না স্থানীয় ব্যবসাদারদের কাছ থেকে তোলা আদায় করে অর্ডারমতো লোক চমকিয়ে, জায়গায় জায়গায় নাইট ওয়াচের টেম্পোরারি কাজ করে সে ভালই কামায়। কিন্তু ওর দুই মা। প্রথমার দ্বিতীয় সন্তান সে। প্রথম জন মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেছে। শামুর পরে ওর নিজের মায়ের আরও একটি ছেলে সামসুল, মেয়ে হাসি। সৎমার পাঁচটি সন্তান বেশ ছোট ছোট। সবচেয়ে ছোটটির বয়স বোধহয় বছর আষ্টেক। ঠিক যতদিন ওর আব্বা মারা গেছেন। এদের সবাইকার ভার একা শামুর কাঁধে যার নাকি মাধ্যমিকটাও পাশ করার সুযোগ হয়নি। কোনও কারখানার শ্রমিক-ট্রমিক হবার ট্রেনিংও নেই। একটু সময় করে যে ট্রেনিং নেবে, ন’জন পরিজনকে নিয়ে সে ফুরসতটুকু পর্যন্ত ওর নেই। তারপর বাড়িতে দুই মায়ের ঝগড়া, বাচ্চা ভাইবোনগুলোর ক্যাঁচাকেঁচি লেগেই আছে। ওর মোক্ষ ছিল ফুটবলে। পাটা জখম হয়ে সে-দিকটাও বরবাদ হয়ে গেল। কাজেই সাংস্কৃতিকই হোক আর আর্থিকই হোক মধ্যমান এখনও ওর নাগালের বাইরে। কিন্তু হাসির মুক্তির ইচ্ছে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তার বুদ্ধি প্রমাণ করে আরোহণের ক্ষমতা ওদেরও আছে। মণি, আমার ছাত্রী এটা সম্ভব করল। মণি যে স্টার পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করেছে, তার চেয়েও বড় কৃতিত্ব এইটা। কথাটা কি মণি বুঝতে পারছে? যদি না পারে তো ওকে আমি বুঝিয়ে দেব। সুযোগ পেলে।
আমার আরও আনন্দ আমার ছুঁচ-হয়ে-ঢুকে-ফাল-হয়ে-বেরোনো ঘটি বউদি এই মুক্তি নাটকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে। আর পাঁচজন চাকুরে স্ত্রী বা মায়ের মতো নিজের টাকা পয়সা, বুদ্ধিবৃত্তি সব নিজের লোকেদের সুখ-স্বার্থের জন্যেই খরচ করেনি। সে একটি অনগ্রসর সমাজের মুসলিম মেয়ের জন্য তার বসকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে অদ্ভুত শর্তে, মেয়েটির নিজস্ব পরিবেশের শর্তেই স্কুলে ভর্তি করিয়েছে, পড়িয়েছে, এবং করেছে নিশ্চয় নিজের খরচে। কেন না, বেতন মাফ হলেও, সেশন ফি ইত্যাদি বাবদ কিছু খরচ তো আছেই।
প্রথম যখন দাদা বাড়িতে ঘোষণা করল সে ঘটি মেয়ে আনতে যাচ্ছে, বাবা আপত্তি করেছিলেন। ওরা মিলেমিশে থাকতে পারে না। দু’জনেই চাকুরে, খুবই মুশকিলের কথা হবে তপু যদি আলাদা হয়ে যায়। মা বলেছিল —আমি ঘটি না হলেও বাটি তো বটে! আমি কোনওদিন আমার বাঙাল শ্বশুর-শাশুড়িকে অযত্ন করেছি! অমন বলো না।
আমি তখনও এত লায়েক হইনি। কিন্তু বলেছিলাম—বাবা, এ কথাটা তুমি ঠিক বললে না। আমরা এই জেনারেশন কি আর প্রকৃত অর্থে বাঙাল আছি? বাঙাল ভাষার টোন আমার চেয়ে কোনও পশ্চিমবঙ্গীয় অভিনেতা হয়তো বেশি ভাল আনতে পারবেন। আমাদের এখানেই জন্ম-কর্ম, এখানেই মিশে গেছি। বাবা নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—জাতিগত চরিত্র চট করে যায় না রে রুণু। তা বাবার আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণ করে টুকু-বউদি আমাদের পরিবারের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মানিয়ে নিয়েছে। আমার মা-বাবা দাদার চেয়েও বউদিরই কৃতিত্ব এতে বেশি আমি বলব। বউদিও খুব স্ট্রাগলিং পরিবারের মেয়ে। অল্প বয়সে বাবা গত, ছোট বোনটির বিয়ে দিয়েছে, মায়ের দেখাশুনো করেছে, যখন বিয়ে হয় তখন দাদাকে কথা দিতে হয়েছিল, মায়ের দেখাশোনা করতে যা টাকা খরচ করতে হয় সে তার রোজগার থেকে করবে। ওদেরও বাপের বাড়ির একটাই ভরসা ছিল। তিন শরিকের একখানা বাড়ি। তা হোক নিজের বাড়ি তো! দু’খানা ঘর, একটা রান্নাঘর, একটা কলঘর, আর একটা দালানঘর। মাঝখান থেকে দেয়াল উঠেছে পার্টিশনের। বউদির মা এক ভদ্রমহিলাকে পেয়িং গেস্ট রেখেছিলেন। মহিলা কোনও বেসরকারি অফিসে ভাল কাজ করতেন। এ থেকে ওঁদের খরচের টাকাটা অনেকটাই উঠে আসত। বউদির মাস-মাইনে দাদা কখনও চায়নি, বউদিও কখনও দেয়নি। সে বাড়ির জন্য খরচ করে নিজের মতে, নিজের রুচি অনুযায়ী। এই খাবার-টেবিল চারটে চেয়ার এবং রান্নাঘরের গ্যাস উনুন তার কীর্তি, নিজের বাচ্চার সমস্ত খরচ সে-ই সামলায়। বাবা থাকতে বাবার, এবং এখন মায়ের ওষুধপত্র বউদিই কেনে। আমার ঘরের স্ট্যান্ডিং ফ্যানটা বউদির উপহার। তা সেই বউদি মায়ের সংসার, এখন অবশ্য মা আর নেই, ওদের অংশটুকু ওরা কোনও সরকারি চাকুরেকে ভাড়া দিয়েছে, সেটা বউদি আর তার বোনের মধ্যে ভাগ হয়। যাই হোক মায়ের সংসার, আমাদের সংসার চালিয়েও আর একটি মেয়ের লেখাপড়ার আংশিক খরচ ও দায়িত্ব নিয়েছে সম্পূর্ণ নিজের তাগিদে—ভাবতে আমার বুকখানা দশহাত হয়ে যেতে লাগল।
ছাতের মধ্যে সিগারেট খেতে খেতে জোরে জোরে পায়চারি করতে থাকলাম। যেন লটারি জিতেছি। অনেক, অনেকক্ষণ পর, প্রায় দেড় ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবার পর হঠাৎ আমার খেয়াল হল—এ কী রে বাবা! এত উল্লাস কেন? কীসের? সারা জীবনটাই তো আমার ডিস্যাপয়েন্টমেন্টে ভরা। খুব খারাপ বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল না, কিন্তু তেমন ভাল কিছু কোনওদিনই করতে পারিনি। এক একটা রেজাল্ট বার হত আর আমার মনের মধ্যেটা অন্ধকার হয়ে যেত। আবার আলোর দিকে উঠতাম বন্দি গাছের মতো, এবার আরও চেষ্টা করব। নিশ্চয় ভাল হবে। নিশ্চয়। আবার হল না। এই ভাবেই চলেছে। কোথাও কোনও চাকরি পাইনি আর পাব বলেও আশা নেই। ট্যুইশানিগুলোর জন্যে পড়াশোনার অভ্যেসটা আছে, বরং বেড়েছে, আর হাতে পয়সার খুব অকুলান হয়নি, কিন্তু একটা মেয়ে পাশ করেছে বলে, আর অন্য দুটো মেয়ে তাকে সাহায্য করেছে বলে, এবং সাহায্যকারী দুটি মেয়েই আমার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এ কী উল্লাস! যে মেয়েটি পাশ করল, আমি ফার্স্ট ডিভিশন পাইনি কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও যে পেয়েছে সে-ও তো আমার বন্ধুরই বোন। যেমন মণি, তেমনই হাসি। তফাত তো কিছু নেই! তা হলে তিনজনেই সামহাউ রিলেটেড টু মি। কিন্তু এত উল্লাস, এত আনন্দ! সেই গুপি বাঘার ‘আহা কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে’, যেন মনের মধ্যে ঘুরছে ফিরছে! তবে কি আমি সোশ্যাল রিফর্মার-ফিফর্মার হয়ে যাচ্ছি? হায় ভগবান, আমি সামান্য মানুষ তুমি আমার এ কী করলে?
১৫
জুন থেকে ভারী বর্ষা নেমে গেছে। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় পয়লা জুন। ঘ্যানঘ্যানে প্যানপেনে টাইপটা অবশ্য এখনও হয়নি। মেঘমেদুর মরসুম হয়, নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জ ছায়ায় ভরে যায় চতুর্দিক। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে। তার সঙ্গে থেকে থেকে গরম-ভাপ বেরোয়। মণি কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে, হাসিও শুনলাম হয়েছে। শামুই নাকি ভর্তি করে দিয়েছে নিজে গিয়ে। জুলাই থেকে ক্লাস শুরু হবে। প্রায়ই দেখি বউদির সঙ্গে গুলতানি করতে আসে। যেহেতু কেউ কোনওদিন সেভাবে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি, আমি হাসির দিকে চাই না। কথা বলা তো দূরের কথা। মেয়ে-ক্যাংলা ছেলেদের দেখলে আমার কেমন ঘেন্না হয়। আমিও লুকিয়ে-চুরিয়ে ওইরকম বাথরুমে-উঁকি-মারা টাইপ ভাবিসনি বাবা! তা ছাড়া ওরা আমাকে কেন জানি না একটু এড়িয়েই চলে। আমি যখন থাকি না, তখনই আসে। কোনও কোনওদিন হয়তো ট্যুইশন থেকে বাড়ি ফেরবার সময়ে দেখি অন্ধকারে দুটি মেয়ে বেরিয়ে গেল। রিন্টি দরজার চৌকাঠ থেকে আব্দার করল —কালকেও আসবে। আসবে তো?
—দেখি! মণির গলা।
কোনওদিন হয়তো বলবে—রুণুদা ভাল তো!
আমি বলব—তুমি ঠিক আছ তো!
—আমরা কম্পুটার শিখছি। কলেজে আছে। মাইনের বাইরে আর খরচ লাগে না। রুণুদা আমি দুটো ট্যুইশন করছি।
—বাঃ খুব ভাল, আমার অন্ন মারিসনি আবার!
অন্ধকারে হাসির আওয়াজ।
মণি বলে—দেখে দেখে বাচ্চাদের নিচ্ছি তো ওইজন্যেই।
এইচ এস পাশ করবার পর মণিমালার মধ্যে একটা চটুলতা এসেছে যেন। আগে ছিল কেমন গম্ভীর, বিষণ্ণ-বিষণ্ণ, ভীষণ সিরিয়াস, আমার অনেক সময়ে মনে হত বলি—ঈশ্বর সার্কামস্টান্স যাই দিয়ে থাকুন, মগজটা এক্সেলেন্ট দিয়েছেন। অমন রামগরুড় হয়ে থাকিস কেন রে?
তো এখন, রামগরুড় ভাবটা পুরোপুরি কেটে গেছে। চলার ভঙ্গিতে যেন একটা দোলা, একটু ছটফটানি, হাসি। যাক মেয়েটার মনের ভেতর থেকে একটা বিশাল ভার নেমে গেছে। সংসারে হয়তো সামান্য সচ্ছলতাও এসেছে। দীপু যাই তোক হাজার বারোশো কামাচ্ছে। ওর ভাই ভুতো কবে ড্রাইভিং শিখল জানি না, সন্তোষপুরের দিকে কাদের গাড়ি ড্রাইভিং-এর চাকরি পেয়েছে, উপরন্তু একটা থাকার ঘর, সেখানেই থাকে, মনিবের বাড়ি থেকে খাবার পায়, মুক্তারও নিশ্চয় উন্নতি হয়েছে। আজকাল দেখি নিজেও খুব ভুরু-টুরু প্লাক করে ছোট চুলে লক-ফক কেটে ফিটিং সালোয়ার-কামিজ পরে ঘুরে বেড়ায়। ‘লা-বেল’ আজকাল ইউনিফর্ম দিচ্ছে, লাল রঙের। সেটা পরে মাঝে-মাঝে দোকানের বাইরেও বেরোতে দেখেছি। একদিন জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় চললি—এই দুপুরে?
একবার মুখ ঝামটা দেবার চেষ্টা করল অবশ্য—তোমার জেনে কী হবে?
—না, তোর এই লাল রঙের ফ্রকটা বেশ। তাই বলছিলাম।
—ইয়ার্কি মারবে না রুণুদা, এটা ফ্রক নয়। ড্রেস।
—ওই হল, আমরা ভেতো বাঙালি, ট্যুইশন-মাস্টার অতসব জানব কোত্থেকে বল! তা তোর যদি কোনও সিক্রেট অ্যাপো-ট্যাপো থাকে তা হলে না-ই বললি।
—বলে আমি বত্রিশ দাঁত বার করে হাসি। মুক্তা বলে, ভাল হবে না কিন্তু।
—এই তো পথে এসেছিস! ‘ভাল হবে না কিন্তু’টা টিপিক্যাল মেয়ে মেয়ে। এবার বোধহয় বলবি—দূর অসভ্য।
মুক্তা রাগতে গিয়ে হেসে ফেলে বলে— বিয়ে বাড়িতে সাজাতে যাচ্ছি। আঙুলে টুসকি মেরে বলল—মালকড়ি আসবে।
চুল ঝাঁটানো থেকে বিয়ে-বাড়িতে সাজাতে যাওয়ায় প্রোমোশন হয়েছে মুক্তামালার। ভাল ভাল। আমারই খালি শুধু যাওয়া-আসা, শুধু স্রোতে ভাসা। একটু-একটু ঈর্ষার হুলও যেন ফুটতে থাকে বুকে। কিছু না অন্তত যদি ঠেলে একটু ওপর দিকে উঠতে পারতাম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি কতদিন। সেই বাইনোমিয়্যাল থিয়োরি, সেই কুয়েত থেকে পরিশোধিত খনিজ তৈল রপ্তানি হয়। সেই আটাশের থিয়োরেম। সেই সন্ধি-সমাস, সিংগুলার হ্যাভ লিখো না ধন, শব্দটা প্রোনাউনসিয়েশন নয় চাঁদ। সেই লেজার, জার্নাল আর বুক-কীপিং-এর বিরক্তিকর খুঁটিনাটি। একমাত্র দুপুর একটা দুটো নাগাদ বাড়ির ভাত মেরে গুহ প্যালেসের ভূতের বাড়িতে গিয়ে দীপুর সঙ্গে সময়টা ভাল কাটে।
একদিন দীপু বলল, ওরা একদম আসা বন্ধ করে দিল কেন বল তো!
—কারা!
—ওই তোর গুহক মিতা?
—ওহ! ওরা হতাশ হয়ে গেছে।
—শোন রুণু একটা কাজ করবি? তুই তো কিছু করবার জন্যে ছটফট করছিস।
—কী করব বল। নিজের পায়ে কুড়ল মারা ছাড়া আর যা বলবি!
দীপু একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। —নিজের পায়ে কুড়ল মারা কিনা জানি না। কিন্তু কুড়ুল কোথাও একটা আছে। ভয়েস বলছে।
—আবার তোর ভয়েস?
—শিওর ভয়েস। ভয়েস না থাকলে কে আমায় এই ভূতের বাড়িতে আগলে রাখত!
—আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। কী তোর মতলব বল।
—রুণু, গুহমজুমদাররা আসে না, জগাদা ইলেকশন নিয়ে ব্যস্ত। এসব ভাবার আর সময় পাচ্ছে না। চাকলাদার শালা বহোৎ ধড়িবাজ আছে। ও শালা আসে। চারদিক ঘুরে ঘেরে দেখে, ম্লিচ ম্লিচ শব্দ করে। আর চলে যায়। ভয়েস বলছে—পেছনে কিছু আছে। ডিপ, ডিপার, ডিপেস্ট।
—থাকতে পারে। আমরা কী করব?
—তুই সে-দিন বলছিলি না, দেবল গুহ নাকি বলেছে ওর দুই খুড়ো কম্প্রোমাইজ করছে না কিছুতেই! একদিন যাবি খুড়োদের কাছে?
—কী কম্মে? কম্প্রোমাইজ করাতে?
—ধর তাই। আমি ঠিকানাটা জোগাড় করেছি। মতিলাল নেহরু রোড, সাতের দুই।
—যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শির ঘুম নেই। আমরা কে যে যাব? আমাদের ইন্টারেস্ট কী? কী ক্যাপাসিটিতে যাব? রমেন গুহ কি আমাদের উকিল রেখেছে? না চাকলাদার!
—আহা রাগ করছিস কেন? চলই না। একটু কেসটা শুনে আসব। ধর একটু বুঝিয়ে আসব। কতটা ক্ষতি ওঁদের হচ্ছে। ধর না কেন, চাকলাদারের লোকই সাজলুম। ইন এনি কেস, আমরা তো চাকলাদারের লোকই। ওর কাছেই তো আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট।
—আমার নয়।
—আহা আজ নয়। একদিন তো ছিল। চল না রুণু। লক্ষ্মীটি, আমার মনটা কেমন করছে। ভয়েস বলছে কিছু কর। কিছু কর!
দীপের পাগলামিতেই সুতরাং এসেছি।
প্রিয়া সিনেমার পাশ দিয়ে ঢুকি। মতিলাল নেহরু মোটামুটি চওড়া রাস্তা। কিন্তু তার থেকে ডালপালা যেগুলো বেরিয়েছে সেগুলো যথেষ্ট সরু। গায়ে গায়ে বাড়ি। অর্থাৎ এই সব পুরনো কলকাতার তলানি। দোতলা তিনতলা বাড়ি সব দাঁড়িয়ে আছে সলিড। ক্ষয় ক্ষতি নেই এমনি সলিড। আমাদের একালের পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের বাড়িগুলো ভূমিকম্প-টম্প হলে একেবারে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। কিন্তু এসব বাড়ির স্বাস্থ্য টসকাবে না। খুঁজে খুঁজে অবশেষে গেট পাই। সরু গেট, সরু প্রাইভেট গলি। কিছুটা গিয়ে তবে ডানদিকে সদর দরজা সেও তেমন চওড়া নয়। খুঁজে পেতে বেল টিপি। অনেকক্ষণ বাজতে থাকে বেল। কেউ নেই না কি? ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে, এমন সময়ে দরজাটা খুলে গেল। মানে আধখোলা, ওদিকে চেন, একটা রুক্ষ বুড়োটে গলা শোনা গেল— আমরা চাঁদা দিই না। অসময়ে বিরক্ত কোরো না।
আর একটা লেস-রুক্ষ গলা বলল— কোনও কোম্পানির কোনও জিনিস-মিনিস কেনবার ইচ্ছেও আমাদের নেই। বিদেয় কর, বিদেয় কর…
বাপ রে!
আমি বললাম— আমরা আপনাদের মাল্টিস্টোরিড-এর ওখান থেকে আসছি।
—কী দরকার?
—দরকার এপার থেকে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। ভেতরে যেতে হবে।
—কে পাঠিয়েচে? রমেন? ও সব হবে না। যে টাকা নিইনি সে টাকা দেব না।
—আজ্ঞে না। দীপ্ত টিপিক্যাল ঘটি ভঙ্গিতে বলল—, আমরা ঠিকেদার চাকলাদারের লোক।
—সে তো একটা পাঁঠা।
যাক লোকটা যে একের নম্বরের খচ্চর সেটা এই দুই বুড়ো এখনও বুঝতে পারেনি। পাঁঠা ভেবেই ক্ষান্ত আছে।
যাই হোক, এইবারে দরজা খুলে গেল। অন্ধকার প্যাসেজে একটা ধোঁয়া-কালি মাখানো আবছা বালব জ্বলছে। বাইরে থেকে এসে ভাল করে কিছু দেখা যায় না। এইটুকু দেখলাম যে-বৃদ্ধ দরজা খুললেন তিনি খটখটে রোগা, একটা আধময়লা ফতুয়া আর একরঙা লুঙ্গি পরা, পেছনের দিকে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি হৃষ্টপুষ্ট থপথপে মতো, তাঁর পরনে গামছা, মানে বেঁটেদার সেই অব্যর্থ নিদান— চেড়ি।
বাঁ পাশে একটি দরজার তালা খুলল। ভেতরে টিউব লাইট জ্বলল, পাখা চলল। একটি তক্তপোশ, একটি পড়ার টেবিল আর তিনটি চেয়ার। আচ্ছা কিপটে বুড়ো তো! গুহ মজুমদারদের বাড়ির দুই শরিক। আবার নিঃসন্তান! এসব লোকের আসলে একটা বাতিক হয়ে যায়। টাকা খরচ করবে না, কাউকে দেবে না, পচাবে, আর যখন অক্কা পাবে তখন সেই টাকা নিয়ে ভাইপো, ভাগ্নে ইয়ার বেরাদরদের সঙ্গে আগে মাইকেল যেত, এখন ডিস্কো যাবে। সারা জীবনের সঞ্চিত, ভোগ না-করা ধন দু’-চার বছরে স্রেফ হাওয়া হয়ে যাবে। পাঁঠা আর কাকে বলে!
আমরা আহ্বান ছাড়াই ভেতরে ঢুকি এবং তক্তপোশের ওপর বসি। একটা কেঠো চেয়ারে মুখোমুখি বসে কেঠো বুড়ো। বলে, আগে সেজদাকে আসতে দাও, তারপর কতা হবে।
তা মিনিট কয়েকের মধ্যেই প্রথম বুড়োর মতোই একরঙা লুঙ্গি আর আধময়লা ফতুয়া পরে দ্বিতীয় বুড়োর আবির্ভাব হল। থপ থপ করে তিনি আর একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। সেজদা। যিনি নাকি একটি মাল, কুচুটেমির রাজা— অ্যাকর্ডিং টু দেবল।
ছোটজন বললেন— এবার বলো চাকলাদার কী বলছে।
—এতদিন ধরে বাড়িটা পড়ে রয়েছে। কাজও হতে পারছে না। আর কবে আপনারা ভোগ করবেন দাদু, চাকলাদারের সঙ্গে একটা রফা করে নিতে কী দোষ।
দীপু বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে বলল। পাগলা-খ্যাপা ভাবটা একদম নেই। একটা চাকরি, নিয়মিত চাকরি ও বেতন, সে যত কমই হোক মানুষের মধ্যে কী আমূল পরিবর্তন আনতে পারে তা দীপুকে দেখে বুঝছি। আজকে ও সেই আমার কিনিয়ে দেওয়া চেক শার্ট আর কালো জিনস পরে এসেছে। পায়ে স্ট্র্যাপ দেওয়া স্যান্ডাল। চুল-ফুল তেমন ভাল করে আঁচড়ায়নি। কিন্তু ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে, চশমায়, কালো ধারালো মুখ দেখাচ্ছে অন্যরকম।
—রফার শত্ত যদি অমনি গলাকাটা হয়, কী করে রফা করব?
—একটু বুঝিয়ে যদি বলেন, —আমি বলি।
—কেন? চাকলাদার, রমেন এরা তোমাদের বলে-কয়ে পাঠায়নি।
—দাদু ওঁরা যা-ই বলুন, কিছু সূক্ষ্ম পয়েন্ট তো আমাদের না জানাও থেকে যেতে পারে! তাই…কথাগুলো দীপে বলল। দীপে!
—সূক্ষ্ম তোমার মাতা! কী? না সিক্সটি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট ভাগ হয়েছিল, এখন চারটে ফ্ল্যাট কমে গেচে, কার ভাগে কত পড়বে তার ক্যালকুলেশন নতুন করে হবে। তা হোক না! খুব শক্ত অঙ্ক? চার ছয়ে চব্বিশটা ফ্ল্যাট এখন। ন’ খানা ফ্ল্যাট আর কিছু টাকা আমরা পাই। তো সেটা করে দিলেই তো হয়। হচ্চে না কেন!
—কেস এখন সাব-জুডিস তো! জগাদা কেস তুলে না নিলে,… মানে জগাদাকে কিছু কমপেনসেশন দিলেই তো…
—তাই বলো। তোমরা জগা মিত্তিরের লোক। ভাল, জগা টাকা চায়। তা সে-টাকা আমরা দুই বুড়ো দেব কেন? ঘাটের দিকে পা, দেখবার-শোনবার বেলায় কেউ নেই, দেবার বেলায় সেজ-ছোট টাকা বার করবে, কেমন?
—আজ্ঞে সাততলার ফ্ল্যাট বুকিং-এর শেয়ার তো কিছু আপনারাও পেয়েছেন, সেই…
হাঁ হাঁ করে উঠলেন দু’জনে, —চাকলাদার তোমাদের এই বুঝিয়ে পাঠিয়েচে? একটা কানাকড়িও পাইনি! সব ওই রমেন গাপ করেচে। নিজের ভাইপোকে তো আর খচ্চর, গর্ভস্রাব বলে গালাগাল দিতে পারি না। ও থুতু ছুড়লে নিজেরই গায়ে এসে পড়বে। কেমন কি না? ওই হতভাগা সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করবার চেষ্টায় আচে, কী দাদা?
সেজদাদু বললেন— খুবই দুঃখের কতা। বিবাহ করিনি। ভাইপোদের কোলে পিঠে করে আপন সন্তানের ন্যায় মানুষ করিচি। তার এই প্রতিদান।
ছোটদাদু বললেন— মেজদার ফ্যামিলি সিঙ্গাপুরে। মেজদা নেই আর। তার ছেলে-মেয়েরা এখন আধা-সায়েব। কে অস্ট্রেলিয়ায়, কে আমেরিকায় সেটল করেচে। তাদের এই ইন্ডিয়ান রুপি ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাটে কোনও আগ্রহ নেই। লেখাপড়া করে সব কাগজপত্তর রমেন-দেবলকে পাটিয়ে দিয়েচে। আমাদের এক দিদি কোনকাল থেকে দেরাদুনে পোস্টেড, জামাইবাবু মিলিটারিতে ছিলেন। দু’জনেই এখন রিটায়ার্ড। দিদি শয্যাশায়ী। জামাইবাবু তাকে দেখাশুনা করেন। মিলিটারির স্টার পাওয়া লোক ওদের এসব ছেঁদো ফ্ল্যাটে কোনও ইন্টারেস্ট নেই। একটি মাত্র মেয়ে। ডাক্তার। তার বরও ডাক্তার। ইংরেজ সায়েব। তারা লন্ডনের কাচে থাকে। খুঁজেপেতে তাদের কাচ থেকেও দানপত্তর বার করে নিয়েচে। পথের কাঁটা আমরা এই দুই ঘাটের মড়া। ওয়েট করচে। তাই বাড়ির কাজ বন্ধ। সাব-জুডিস না ছাই। কর্পোরেশনে তো ভেঙে দিয়ে গেচে— শুনতে পাই, জগার সমাদান তো হয়ে গেল। আবার সাব-জুডিস কীসের?
আমি বলি— সবটা ভাঙেনি, একটা ভেঙেছে।
—তাই নাকি? তা’লে তো এর মধ্যে আরও কতা আচে! শরীরটা গেচে মাতা তো যায়নি। মিলিটারি অ্যাকাউন্টস-এ চল্লিশ বচর! ঘাসে মুক দিয়ে তো আর চলি
সেজ বললেন, আমি তো পা বাড়িয়ে বসে আচি। একটা জব্বর স্ট্রোক হয়ে গেছে। কিন্তু ওদের জব্দ কেমন করে করতে হয় আমি জানি।
ছোট সতর্ক গলায় বললেন— এ ছোকরা দুটিকে এত কথা বলচ কেন সেজদা! এরা কার লোক তা-ই তো এখনও বুঝতে পারলুম না।
সেজদা বললেন— কতার হাঁড়ি তো তুমিই হাট করে দিলে খোকন। বলো না, বলো না। কিন্তু মুক খুললেই তোমার হলহল গলগল।
দু’জনে ঝগড়া লেগে যায় আর কী!
দীপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল— আপনারা ভয় পাবেন না, আমাদের ভুলও বুঝবেন না। আমরা ওখানকার পাড়ার ছেলে। চাকলাদার আমাদের সাইটে সুপারভাইজার রেখেছিল। ভেতরের কথা আমরা কিছুই জানি না। অথচ কতকগুলো ঘটনা ঘটে চলেছে দেখতে পাই যেগুলোর কোনও মানেই হয় না। দেখতে দেখতে মনে হল ইনভেস্টিগেট করি।
—ভাল, তা ইনভেস্টিগেট হল? এখন কাকে রিপোর্ট করবে? চাকলাদারকে না জগা মিত্তিরকে না রমেন গুহকে?
—বললুম তো, কারও সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক নেই। স্বাধীনভাবে জিনিসটা বোঝবার-জানবার চেষ্টা করছি।
—করে কী করবে?
—হয়তো কিছু করব, হয়তো কিছুই করব না।
—শুদু জানার আহ্লাদেই আটখানা, না কী? —ছোট শ্লেষের গলায় বললেন।
দেখুন দাদু— এবার আমি আসরে নামি— আপনারা তো পাড়ায় থাকলেও একটু স্বতন্ত্র থাকতেন। পাড়ার ছেলেরাও একটা শক্তি! একটা ফোর্স! যদি আর একটু কম রিজিড হতেন, মেলা-মেশায় আর একটু— মানে উদার আর কী… তা হলে পাড়ার ছেলেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনাদের হেল্প্ করত!
—বটে! কোন পাড়ার ছেলের সঙ্গে দাদুগিরি করব বল তো! ওখানে তো সব হয় গুণ্ডা, আর নয় বাঙাল, রিফিউজি।
আমি বলি— তাই? আমিও রিফিউজি দাদু, এখন আর নই অবশ্য, উদ্বাস্তুদের ছেলে, আর এই দীপু এ কিন্তু কোনওকালেই বাংলাদেশ থেকে আসেনি, তবু উদ্বাস্তু, এরকম, মানে আমাদেরই মতো আরও অনেক আছে।
—রাগ-ঝাল করো না বাপু। রেখে-ঢেকে কথা বলতে আর এ বয়সে পারি না।
—আচ্ছা আসি।
প্রণাম ট্রনাম করি না।
বাইরে বেরিয়ে বলি— কথা বলে গলা শুকিয়ে গেছে, আয় একটু ঠাণ্ডা খাই। দীপু ব্ল্যাঙ্ক চোখে পা বাড়াল। ওর চোখে আবার সেই শূন্যতা। কী করে একই মানুষের চোখ এভাবে রং পাল্টায়, তল পাল্টায় এ এক অষ্টম আশ্চর্য! একটু আগেই তো আপনি আজ্ঞে করে দিব্যি দুই বুড়োর কাছ থেকে কথা বার করে নিল। এক্ষুনি আবার দেখছি চোখে যেন চোখ নেই। বা চোখে দীপু নেই। আমিও ন্যাচার্যালি নেই। ও একা। কী ধরনের অন্যমনস্কতা এটা? সারা পৃথিবীর সমস্ত লোকের থেকে যেন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বা সব মানুষেরই মাঝে মাঝে যে একাকিত্ববোধ হয়, সেই সমস্ত একাকিত্ব ওর চোখ থেকে দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে।
দু’জনে দুটো ঠাণ্ডা খাই। যান্ত্রিকভাবে ও স্ট্র চুষে যায়।
—দীপু পান খাবি? যতটা না পানের লোভে তার চেয়ে বেশি ওকে কথায় ফেরাতে আমি বলি। কোনও জবাব আসে না।
—দীপু? এই দীপু!
—প্রথম যেদিন রমেন গুহ আর তার ছেলে সাইটে এসেছিল, তোকে কী বলেছিলুম মনে আছে?
—না, বিরক্ত হয়েছিলি।
—হ্যাঁ, কেন না স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম কিনকিন করে বেল বাজছে। আজ কথাটার সত্যতা প্রমাণ হল। হল তো? ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না এমনি ভাব! কথা বলে, চেহারা দেখে কেউ বুঝবে আসলে কত ধড়িবাজ, কত নিষ্ঠুর? দে আর ওয়েটিং ফর দি ডেথ অব দেয়ার গ্র্যান্ডফাদারস। ওই দু’জনই শুধু পথের কাঁটা।
আমারও মনের মধ্যে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল। যখন গদা মাফিয়া হয়ে গেল, শামু গুণ্ডা হয়ে গেল তখনও লেগেছিল। গুহদের বেলায় তার সঙ্গে মিশে ছিল বিস্ময়। যাদের টাকা পয়সার অভাব নেই, তারা কেন জোচ্চুরি করবে? পরক্ষণেই মনে হয়— কী আশ্চর্য! চুরি-জোচ্চুরির কি ধনী-দরিদ্র আছে। কত ধনী লোকই তো শরিকি বিবাদ করে মরছে আরও দুটো ঘর, আরও চাট্টি ইটের জন্য, যাদেরই অনেক থাকে, তারাই তো প্যাঁচ কষে, কীভাবে অন্যকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা যায়। সারা পৃথিবী জুড়েই তো এই চলছে! জার্মানি ইহুদিদের বঞ্চিত করেছিল, ইহুদিরা প্যালেস্তানীয়দের বঞ্চিত করছে। জাপান দীর্ঘদিন চিনকে বঞ্চিত করেছে, চিন বঞ্চিত করছে তিব্বতিদের। আমেরিকা লেগেছে ইরাকের পেছনে, ইরাক লেগেছিল কুয়েতের পেছনে, রক্তনদী বইয়ে ভারত টুকরো করে পাকিস্তান হল, আবার রক্তসাগর বইয়ে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হল। নেহরু বললেন ভারতের গদি চাই, গদি পেয়ে বললেন ইন্টারন্যাশন্যাল ফিগার হওয়া চাই, ইন্টারন্যাশন্যাল ফিগার হয়ে বললেন ডাইনাস্টি চাই। এইভাবে খুড়োর কল অদৃশ্য সুতো দিয়ে পৃথিবীর তাবৎ দেশকে, পার্টিকে, মানুষকে টানছে। দেবলটা আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড়, আমারই মতো কমার্সের ছাত্র। এম-কমটা করেছে অবশ্য। বাড়ির অবস্থা ভাল। চার্টার্ড করছে, সেও দুই নিঃসন্তান বৃদ্ধের সম্পত্তি ছলে-বলে-কৌশলে হাতাতে চায়? এমনিই তো পেত। পরিবারহীন দুই বৃদ্ধের হাড়ির হাল তো দেখে এলাম। ওঁদের দেখা-শোনা করতে কতটুকু শ্রম, সময় খরচ হত ওদের?
দু’জনে একরকম চুপচাপ বাড়ি ফিরি। দীপু একেবারে অপরিচিত। আমার মনটা ভীষণ খারাপ। এর চেয়ে দেবলরা ভাল আর ওর খুড়োরা খারাপ বেরোলে আমি খুশি হতাম। কিংবা হয়তো রমেন গুহ প্যাঁচগুলো কষছেন। দেবল জানে না। আমাদের বয়সি একটা ছেলে, যে এখনও ছাত্র, সে তার দাদুদের ঠকাবার জন্যে বাবার পাতা জালের খুঁটো ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কেমন যেন ভাবা যায় না। আমার চোখে খালি ভেসে উঠছে ওর কফি-হাউজে দেখা মুখটা। আমাকে দেখেই কেমন পাঙাশ মতো হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য নিজেকে সামলে নেয়। কিন্তু ওই পাঙাশ হয়ে যাওয়াটা অপরাধীর চিহ্ন। ও আমাকে কফি হাউজে এক্সপেক্ট করেনি। বাড়িটা যে কেন এগোচ্ছে না, তার কতটা আমি জেনে ফেলেছি, এটা ও বুঝতে পারছিল না। ওর বাবা পাকা খেলুড়ি। কিন্তু দেবল এখনও কাঁচা—এই ধরা পড়লাম, ইস ধরা পড়লে এরা কী ভাববে— এই জাতীয় সংকোচ ওর এখনও আছে। আর বছর পাঁচেকের মধ্যে ঘাগু হয়ে যাবে। ঘাগু এবং ঘুঘু।
বাস থেকে নেমে দীপু নিচু গলায় বলল— এতক্ষণ কেন কথা বলছিলুম না বল তো!
—কেন আর! ভয়েস শুনছিলি!
—অত সোজা নয় রে রুণু। ভয়েস আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা কিনকিন শোনাবে অত তালেবর আমি এখনও হইনি।
—তা হলে?
—আরে বুঝতে পারছিস না? শত্রু তো চতুর্দিকে। জগাদা, চাকলাদার রমেন গুহ, শামু… সব্বাই তো জড়িয়ে আছে! কে কার লোক, কোথায় কখন লোক লাগিয়ে রেখেছে— কে বলতে পারে? শুনে ফেললে? তুই কি মনে করেছিস মতিলাল নেহরুতে ওদের কোনও স্পাই নেই? আমাকে কেউ নজরে রাখছে না?
—সর্বনাশ। এ তো খেপবার দিকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল! এতদিন শুধু ভয়েস ছিল। এখন আবার পেছনে স্পাই সন্দেহ শুরু হয়েছে। আমার বি কম ক্লাসের এক বন্ধুর হয়েছিল বলেই আমি জানি। —জানো রণধীর, সব সময়ে কেউ আমাকে ফলো করে যাচ্ছে।
—সে কী? কেন?
—আরে আমার নোটস, আমার মস্তিষ্কের ঘিলু, এসব তো সুপার ক্লাস। খবরটা চাউর হয়ে গেছে, ব্যাস, লোক লাগাও স্টার্ট করে গেছে।
—শোনো অতনু ওসব ছাড়ো। পড়াশোনা একটু কম করো তো! অত পড়লে মাথা গরম হয়ে যাবে। ভাল করে মাথায় তেল ঘষে স্নান করবে।
—পড়াশোনা কে করছে? ওসব আমার মগজের মাইক্রো চিপস-এ কবে ভরা হয়ে গেছে। ফটোগ্রাফিক মেমারি কথাটা শুনেছ? হরিনাথ দে-র ছিল। ওই মাইক্রো চিপসগুলোই মুশকিল বাধিয়েছে। নোটসগুলো না হয় দিয়ে দিলুম। কিন্তু ওরা তো তাতে থামবে না, মগজ ঘেঁটে মাইক্রো-চিপসগুলো নিয়ে যাবে।
একে বলে প্যারানইয়া। দীপুকে চাকরি দিয়ে তো তার খুব উপকার করেছি দেখছি!
—দীপু প্লিজ।
—কেন? কী হল?
—বাজে বকিস না।
—বাজে কীরে? এখানে এসে আশেপাশে কেউ নেই দেখে মুখ খুললুম। তুই-ই বল— এত বড় একটা ফাঁদ যারা ফেঁদেছে, জগাদাকে দিয়ে অবজেকশন, ইনজাংশন, কর্পোরেশনের বাড়ি ভাঙা, আমাদের, পাড়ার বেকার ছেলেদের একগাদা পয়সার লোভ দেখিয়ে আধ-খাওয়া বাড়ি পাহারায় রাখা, শামুর মতো নামকরা গুণ্ডাকে রাত-পাহারায় রাখা, তারা তাদের খুড়োদের ওপর নজর রাখবে না? আমরা ওখানে গেলে আমাদের পেছনেও স্পাই লাগাবে না!
—তা হলে গেলি কেন? এতই যদি জানিস! সেই বলে না, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তাঁতির এঁড়ে গোরু কিনে।
—রুণু। তোকে কেউ ভেল্টু বানাচ্ছে, বানিয়ে দাবার বোড়ের মতো ব্যবহার করছে। তুই চুপ করে থাকবি? রাজা-মন্ত্রীর দান উল্টে দেবার চেষ্টা করবি না? শ্শালা। দীপন চক্কোত্তির সঙ্গে মাজাকি!
আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি— দ্যাখ দীপু, যা জেনেছিস, জেনেছিস। ওই দাদুরাও তো এদের জব্দ করবে বলছে। তোর আমার আর এর ভেতরে মাথা গলাবার দরকার নেই। আফটার অল— আমরা কর্পোরেশনের ক্যানডিডেট কি পেছনের বাড়ির অংশীদার নই। এ বাড়ির শরিকও নই। প্রোমোটার-ঠিকেদার কিচ্ছু নই। আমাদের কোনও রাইট, কোনও স্টেটাসই নেই নাক গলাবার। এক কাজ কর, নেহাতই যদি ঘেন্না করে, চাকরিটা ছেড়ে দে। সাড়ে বারোশো কি একটা টাকা হল না কি? তোর ভাই ড্রাইভারি করে এর চেয়ে বেশি রোজগার করছে।
অন্ধকারে দীপু হাসল, বলল— তুই কি ভাবছিস চাকলাদার এখন আমায় অমনি অমনি ছেড়ে দেবে? সব জেনে গেছি না? এখন ছাড়তে চাইলে, লোক দিয়ে আমায় খুন করিয়ে দেবে।
আমি শিউরে উঠি।
—একেবারে খুন? নাঃ দীপু তোর একটা খোপড়ি আছে বটে!
—শোন রুণু, হঠাৎ একদিন শুনবি নির্মীয়মাণ গুহ প্যালেসের ওপর থেকে দীপন চক্কোত্তি ঝাঁপ খেয়েছে। পাড়ার সবাই বলবে— হ্যাঁ এরকম একটা ফ্যামিলি-হিস্ট্রি ওদের আছে বটে। চাকলাদার তোকে দিয়ে বলাবে— হ্যাঁ দীপুটা ডিপ্রেশনে ভুগত, আধ-পাগলা মতো ছিল, কখন কী করবে, কী বলবে ঠিক নেই। বাস, এস্ট্যাব্লিশড হয়ে যাবে এটা স্রেফ আত্মহত্যা। বাবা ছারপোকা মারার ওষুধ খেয়েছিল। ছেলে সাততলা থেকে ঝাঁপ খেয়েছে। কারণ এক। ডিপ্রেশন। রোজগার না থাকার ডিপ্রেশন।
আমার হঠাৎ কীরকম ভয় ধরে যায়। দীপু যা বলছে তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। আমি, আমিই ওর সর্বনাশের উপলক্ষ হতে যাচ্ছি। যদি চাকরিটা ওর সঙ্গে ভাগ করে না নিতাম, তা হলে এই মতিলাল নেহরুর ঠিকানা বার করা, সেখানে যাওয়া, দাদুদের সঙ্গে কথা বলা এসব আমার মাথাতেই আসত না। বসতে বলেছে বসেছি। কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক আছে বাবা, অল্প টাকায় করেছি। পোষাচ্ছে না, ছেড়ে দিচ্ছি। মিটে গেল। আমার এই চরিত্র। কিন্তু দীপুর চরিত্র আমার থেকে আলাদা। এটা আমি বুঝিনি।
আমি বলি— যথেষ্ট করেছিস। যা জানার সব জানা হয়ে গেছে। ফার্দার আর কিচ্ছু করতে যাবি না দীপু। অন গড।
—খুব ঘাবড়েছিস, না? ভাবছিস দীপুটাকে এই বিপদের মুখে তুই-ই ঠেলে দিলি! ভাগাভাগির চাকরিটাতে দীপুকে না ডাকলেই হত। এত দূর যাবার শখ তোর নেই।
আমার কেমন গা-ছমছম করতে লাগল। অবিকল যা ভাবছিলাম সেগুলোই অবলীলায় বলে গেল দীপু।
আমি রাগ দেখাই— দীপু আমি সিরিয়াসলি বলছি, ইটস নান অব ইয়োর বিজনেস। তুই এ সবের মধ্যে থাকিস না। তোর মা রয়েছেন, বোনেরা, ভাই, বাবা নেই, একটা অসহায় স্ট্রাগলিং পরিবার। এগুলো ভুলিস না। ভুলতে নেই।
—ঠিক —দীপু বলল, আমরা এভাবেই ভাবি। ওরা মরছে, আমি তো ঠিক আছি। ওরা তলিয়ে যাচ্ছে, আমি তো ভেসে আছি, ওরা চুরি-জোচ্চুরি করছে আমি তো করছি না। এ ভাবেই…তবে একটা কথা ঠিক বললি না দীপু, আমাদের চক্কোত্তি ফ্যামিলি স্ট্রাগলিং হতে পারে, কিন্তু অসহায় নয়। সব্বাই, ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান সেন্ট পার্সেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এক সময়ে আমরা সবাই বাবার ওপর ভূত-পেতনির মতো ভর করেছিলুম। মানুষটা পারল না। ছারপোকা মারার ওষুধ খেল। তার পর থেকে আমরা সবাই সামহাউ ব্যাপারটা বুঝে গেছি, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি মরে গেলে ওদের কারও একটুও অসুবিধে হবে না। আমরা সব্বাই মরে গেলে এমন কি মা-ও নিজেরটা ঠিক চালিয়ে নিতে পারবে।
—উফ, দীপু তুই থামবি?
—নাউ ইউ আর রিভোল্টিং। কিন্তু রুণু আমি শুধু টিকে থাকার কথা বলেছি, যেটা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে স্ট্রং ইনস্টিংকট। তার মানে দুঃখ, বেদনা, দয়া-মায়া এসব নেই তা বলছি না। আমরা, চক্কোত্তি বাড়ির কেউ অসহায় না। আমিও না। এটুকুই। যাঃ বাড়ি যা।
আমার পথ দীপুর পথের থেকে অন্য দিকে বেঁকে গেল।
১৬
এ দিকে বিশুদার অনুরোধে হুগলি ডি-আই অফিসে আবার যেতে হল। দেড় মাস হতে চলল, এখনও টুঁ শব্দ নেই। পতিতকাকা শয্যা নিয়েছেন। হঠাৎ বিশুদা আমার দিকে মুখ তুলে বলল— শামুকে নিয়ে যেতে তোর অসুবিধে আছে? আমি একটু চমকে যাই। চালাক লোক, বিশুদা ঠি-ক লক্ষ করেছে।
বলল— কী তাজ্জব কাণ্ড দ্যাখ! ডি আই পর্যন্ত এম এল এ-কে মিছে কথা বলছে, বললে পতিতপাবন সেনের অর্ডার বেরিয়ে গেছে, পূর্ত ভবনে খোঁজ নিতে। তা পতিতকাকা তো এখনও কোনও চিঠিপত্র পাননি। এদিকে বেচারি শয্যাশায়ী। যেতেও পারছেন না।
—শামু যেতে রাজি?
—সে ভার আমার। তুই রাজি কি না বল।
—শামু কি হাত-ফাত তুলবে না কি?
—আরে না না, একটু কড়কে দেবে।
—আমি তো কিছু কম কড়কাইনি।
—দ্যাখ! আবার আমি ফোন করেছি ডি-আইকে। বলছে ক’দিন ছুটিতে ছিল। রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট জানে না। তোদের পাঠাচ্ছি বলে দিয়েছি, যা কিছু দরকারি ইনফর্মেশন কি কাগজপত্র যেন তোদের হাতেই দেয়। এই নে পতিতকাকার লেটার অফ অথরিটি। আমি অ্যাটেস্ট করে আমার সিল দিয়ে দিয়েছি।
সুতরাং শামুর সঙ্গে আবার হুগলির ট্রেনে চড়ে বসি। ট্রেনে আজ সেই তাসপার্টি নেই দেখলাম। থাকলে আজ মজা মন্দ হত না। শামু একেকটাকে একেক দিকে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে দৃশ্যটা বড্ড দেখতে সাধ হচ্ছে।
কেষ্টবাবু মুখ নিচু করে নস্যি নিচ্ছিলেন। রুমাল দিয়ে উদ্বৃত্ত নোংরা ঝেড়ে মুখ তুলেই আমাদের দেখে স্থির।
—সেই পতিতপাবন সেনের কেস না?
—আজ্ঞে।
—তাঁর দু’-চারটে ভুল বেরিয়েছে, কাগজপত্র ঠিক নেই।
—পাঁচ বছর পরে সেটা বলবার টাইম হল? —শামু ঠাণ্ডা গলায় বলল।
—তা কী করব! কাজ কি কম না কি? প্রতিদিন হাজার হাজার টিচার রিটায়ার করছে।
আমি বলি—কী কাগজ চাই আর?
—উনি যে বছর এম এ দিয়েছেন তার লাস্ট ডেট।
—তাই বুঝি? এটা লাগে?
—না লাগলে আর বলছি কেন?
—ওটা যদি জোগাড় করে আনা যায়ও তখন বলবেন পরীক্ষায় যে যে গার্ড দিয়েছিল, তাদের নাম চাই। সেগুলোও যদি জোগাড় হয়ে যায় তখন গার্ডদের বাপের নাম, শালার ঠিকানা, অকুপেশন এগুলোও দরকার হবে তো!
—বাজে কথা বোলো না ছোকরা— কেষ্ট খেঁকিয়ে ওঠে— যা লাগে তাই-ই বলেছি।
শামু হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে বলল—ঠিকাছে ঠিকাছে— রুণু তোরা ছেরাদ্দের সময়ে জিনিসের বদলে, মাথা-টাথা না কামালে তার বদলে বামুনকে মূল্য ধরে দিস না?
—তা দিই।
—এ শালাকেও মূল্য ধরে দে। পতিতকাকার চিঠিটা আমরা আজকেই হাতে হাতে নিয়ে যাব। আর ওই পূর্ত না ফূর্তর চিঠিটা আমরাই রেজিস্ট্রি ডাকে ফেলব। দে শালাকে।
কী জিনিস বেশি ছিল শামুর গলায় আমার থেকে, জানি না, লোকটা একটাও কথা বলতে পারল না।
—কত? কুইক।
ঢোঁক গিলছে, ঠোঁট চাটছে লোকটা। বুঝতে পারছে না এটা ফাঁদ কি না। আশেপাশে আজ কেউ নেই। ক্লোজ দাঁড়িয়ে শামু একটার পর একটা পাঁচশো টাকার নোট বার করছে। আমি এই সময়ে টুক করে ডি-আইকে ডেকে আনি।
—টাকা কীসের? অ্যাাঁ এত টাকা? —ডি-আই পেছন থেকে ধাক্কা খাওয়া গলায় বলে উঠলেন।
আমি শামুরই মতো মস্তানি গলায় বললাম, ইনি পুরুত বামুন, সার মূল্য না ধরে দিলে কাজ করেন না। পতিতপাবন সেন শয্যাশায়ী। বুড়ো বয়সে দিনের পর দিন ব্যাচের পর ব্যাচ ছাত্র পড়িয়ে যাচ্ছিলেন, খাটুনিটা সহ্য হয়নি, একেবারে বিছানা নিয়েছেন। কী করি বলুন, কারওর দ্বারাই কিছু হল না, এম এল এ, ডি আই, কেউ সিধে করতে পারলেন না এই টেঁটিয়া কেরানিটাকে। আপনার সামনেই তাই এটাকে ঘুষ দিয়ে যাচ্ছি, সাক্ষী থাকুন।
—এ কী কাণ্ড, ছি, ছি, ছি। কেষ্টবাবু!
—আমি তো নিইনি সার।
—জানেন আপনারা ঘুষ দেওয়াও একটা দণ্ডনীয় অপরাধ।
—বিলক্ষণ জানি— শামু বলল, তা দেওয়ার জন্যে নয় আমায় জেল খাটান, কিন্তু নেওয়ার জন্যে এ নস্যিদানিটাকেও খাটাতে হবে। ও বলছে নেয়নি, ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে ও নিচ্ছিল, বহুদিন ধরে নিচ্ছে। আপনি আসাতে বাধা পড়েছে। কথাটা আপনিও জানেন।
—আপনারা বসুন বসুন। আমি নিজে এক্ষুনি চিঠি তৈরি করে দিচ্ছি।
ঘণ্টাখানেক পরে পূর্ত ভবনের চিঠিখানা পাই, সেটা রেজিস্ট্রি করে আমরা সেই একই দোকানে এসে বসি যেখানে পতিতকাকার সঙ্গে বসে লাঞ্চ খেয়েছিলাম।
বললাম— কী রে শামু। কী খাবি? তোর খাওয়া পাওনা।
বলল— মাল্লু খাওয়াতে পারিস? মাল্লু? মাথাটা গরম হয়ে গেলে বুঝলি শরীরটাও গরম করতে লাগে। নইলে ব্যালান্স থাকবে না। তোর তো আবার এ সব চলে না।
—চলবে না কেন? কিন্তু আজ নয়। আজ পতিতকাকার চিঠিটা ওঁর কাছে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।
—বহুত মায়া-দয়া তোর শরীরে, না রে রুণু? তবু আমার বোনটাকে রমজান আলির থাবা থেকে বাঁচাবি না! বোনটা মাধ্যমিক পাশ করল ফার্স্ট ডিভিশনে। আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। জানিস তো ওকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছি?
—এইটাই তো কাজের কাজ করেছিস শামু। বোনটাকে সাপোর্ট দে, বিয়ে শাদির কথা এখনই ভাবছিস কেন? রমজান আলির সাধ্য কী তোর বোনকে বিয়ে করে তুই যদি না দিস!
—এই ক্ষমতাটা আমার নেই। কেন, কী বৃত্তান্ত তুই বুঝবি না রুণু।
—এ কথাগুলো বলিসনি শামু, আমার খারাপ লাগে।
চা খেতে খেতে গুম হয়ে বসে রইল শামু। কিছুক্ষণ পরে বলল —রমজান বহোৎ খতরনাক মাল আছে, তোকে সাবধান করে দিলুম রুণু। যা বাড়ি যা।
—তুই যাবি না?
—আমার এখানে এক দোস্ত আছে, চলে যাচ্ছি। ওর কাছে মাল পাওয়া যাবে। একসঙ্গে বসে না খেলে মজাও নেই।
আর দিন পনেরোর মধ্যে পতিতকাকার পেনশনটা হয়ে গেল। এরিয়ার সব জমা পড়ল ওঁর অ্যাকাউন্টে। একদিন কোনওমতে কাকাকে ট্যাক্সি করে পূর্ত ভবনে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। বাকি যা করার আমিই করেছি। অ্যাকাউন্ট থেকে প্রথম টাকা তুলে আনলাম আমিই। কাকিমাকে বললাম— কাকাকে মুরগির স্যুপ খাইয়ে যান, আর মৌসাম্বির রস।
—আমি এমনিই সেরে গেছি রুণু। পতিতকাকা হাসিমুখে বলেন।
—ওটা তো একটা সাময়িক ফিলিং কাকা, শরীরটার দিকে নজর দিন। নেগলেক্ট করবেন না। কাকিমা আপনারও কিন্তু চেহারা ভাল ঠেকছে না। মুরগির স্যুপটা আপনাকেও খেতে হবে।
—অনেক ধার হয়ে গেছে, বুঝলে বাবা!
—কত?
—তা লাখ টাকার মতো।
—বেশ তো শোধ দিয়ে দিন। স্যুপটাও খান। অসুবিধে তো কিছু দেখছি না।
—তুমি আমাদের জন্যে যা করলে, জীবনে কোনওদিন ভুলব না…
পতিতকাকা এমন করতে লাগলেন যেন আমি আমার পকেট থেকেই পেনশন, গ্র্যাচুইটিগুলো ওঁকে দিয়েছি দয়া করে। টাকাগুলো ওঁর প্রাপ্য ছিল না।
কী জোচ্চোর এই সিস্টেম! পাঁচ বছরেরও বেশি একজন সাধারণ মাস্টারমশাই মানুষকে বসিয়ে রাখে! ভেতরটা রাগে জ্বলছে। কিছুদিন আগেই কাগজে খবর বেরিয়েছিল একজন মাস্টারমশাই এ রকম ভিক্ষে করছেন। কাগজে বেরোতে নাকি কেসটার সুরাহা হয়। না কি! কেউ তো দেখতে যাচ্ছে না সত্যি সুরাহা হয়েছে কি না! এখন, মানুষটার জীবন থেকে এতগুলো বছর যে বিনাদোষে উঞ্ছবৃত্তি করে, দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় নিদ্রাহীন কেটে গেল, তার কমপেনসেশন দেবে কোন শালা?
বিশুদা ঘুরন চেয়ারে এক পাক ঘুরে গিয়ে বললে— একটা মস্ত উপকার তুই করলি রুণু! তোদের মতো তরুণরা যদি এভাবে এগিয়ে আসে, তবেই সমাজটার সর্বাঙ্গীণ দুরবস্থার একটা সুরাহা হবে।
আমার কেমন রাগ হয়ে গেল, বলি— তা তোমরা রয়েছ কী করতে? জন-প্রতিনিধি বলে কথা! ভোট দিয়ে পাঠিয়েছি। তার পরেও সমাজের সর্বাঙ্গীণ দুরবস্থার সুরাহা আমাদের মতো বেকার তরুণদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছ? বাঃ!
—পতিতকাকার জন্যে শেষ পর্যন্ত আমায় কী করতে হয়েছে জানিস?
—কী?
—মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলি— আপনাদের পার্টির লোক না হলে কি মাইনে পেনশন…এ সবও দেবেন না দাদা!—ছি ছি ছি এ কী বলছেন! উনি বললেন। —পেনশনার ভদ্রলোক কোনও পার্টিরই না। আর আমি ওঁর জন্যে বলছি। তা বিরোধী এম এল এ-র কথা তো আপনাদের ডি আই পর্যন্ত গ্রাহ্য করছে না। পাঁচ বছর পার হয়ে ছ’-বছর হতে চলল পতিতপাবন সেন পেনশন, গ্র্যাচুইটি, কোনও এরিয়ার কিচ্ছু পাননি। একটা মানুষের চলে? এ তো ধরে বেঁধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, নয় কি? এর চেয়ে তো পেনশন-প্রাপ্ত ষাট বছুরেদের ওপর দিয়ে একটা স্টেনগান চালিয়ে দিলেই হয়। টট্টর টট্টর টট্টর, ব্যস সব শেষ।
উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে হুগলি ডি-আই অফিসে ফোন করলেন। নিজে। তবে পতিতকাকার কেসটা হল।
আমি বললাম, হ্যাঁ অন পতিতকাকাজ বিহাফ আমি, আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ বিশুদা। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতাটারও ভেবে দেখতে গেলে কোনও মানে হয় না।
—কেন বল তো! —বিশুদা অবাক হয়ে সামনে ঝুঁকে বসল।
—প্রথমত পেনশনটা যে শালা আটকে ছিল, সেই কেষ্টা একটা পেটি ক্লার্ক সে সাহসটা কোত্থেকে পায়, হৃদয়-ফিদয়ের কথা ছেড়েই দিলাম। লোয়ার ডাউন একটা সিসটেমের নাট-বল্টু যখন এমন হয়, তখন দোষটা কিন্তু ওপরে যারা আছে তাদের, সে তোমার ওই মন্ত্রীই বল, আর তোমার মতো এম এল এ-ই বল।
—আমার দোষটা কোথায় রুণু! আমি আমরা কি পাওয়ারে আছি।
—গ্যারান্টি দিতে পারো, পাওয়ারে এলে স্বর্গরাজ্য না হোক, এ সবের প্রতিকার হবে? অন গড, তোমার ইষ্ট দেবতার দিব্যি, গ্যারান্টি দিতে পারো?
বিশুদা কিছুক্ষণ থতমত খেয়ে রইল। জাস্ট ক’ সেকেন্ড। তারপর বলল—চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু গ্যারান্টি কী করে দেব বল। ধর সমাজটা সর্বস্তরে পচে গেছে। রাস্তায় ময়লা ফেলতে হয় না এটুকু শেখাতেই জান চলে গেল। তার পর এত মানুষ। একেবারে থিকথিক থিকথিক করছে। কতক জন্মাচ্ছে, কতক নেবারিং স্টেট থেকে এসে যাচ্ছে, কতক আবার বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে এসে যাচ্ছে। ইনফিলট্রেশন। অনেস্টলি একটা চেষ্টা করতে পারি, তার পরেও দেখ, আমরা এক একটা দল, টিম ওয়ার্ক করি, সব কিছু দলের নির্দেশে হয়। ইনডিভিজুয়ালি কিছু করার সুযোগও কম। আমার নিজের তো ইচ্ছে করে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ গড়ে দিই। মানুষ জন্মাবে নির্দিষ্ট হারে, সবাইকার জীবিকার ব্যবস্থা থাকবে, কেউ কাউকে অনর্থক ঘোরাবে না, ঘুষঘাষ নেবে না, কেউ রাস্তায় ময়লা ফেলবে না, নর্দমায় প্লাস্টিক ফেলবে না। হাসপাতাল হবে স্বর্গের মতো, স্কুল-কলেজে মনুষ্যত্বের শিক্ষাও দেবে। আরও কত সাধ, স্বপ্ন দেখি, জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি। কিন্তু দ্যাখ এত-র পরেও, পতিতকাকার কেসটা এভাবে করে দেবার পরও তোরা হয়তো আমায় ভোট দিবি না।
—তুমি তো বলছ গ্যারান্টি দিতে পারছ না, তা হলে?
—গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে রুণু, তুই আমার নিজের ছোট ভাইটির মতো তাই বলছি দল আছে না? নিজের দল। অন্যের দল। তুমি যেই একটু শক্ত হাতে সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছ, জনগণ অভিমানে মুহ্যমান, সেই সময়ে অন্য দলগুলো এই অভিমানের ফায়দা তুলবে। পদযাত্রা, আইন-অমান্য, বনধ্, মিটিং করে করে এসব অন্যায়, আমরা এর প্রতিবাদ করি এইসব বলে জনগণকে কনফিউজ করে দেবে! একটা ডামাডোল, হট্টগোল, তারপর আবার যে কে সেই।
—গোলি মারো দলকে!
বিস্ফারিত চোখে বিশুদা বলল— আমার দলকে আমায় গোলি মারতে বলছিস, তোর সাহস তো কম নয়!
—গোলি মারো, ওয়ান অ্যান্ড অল। যারা শুধু নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে, ভাল কাজ করলেও করে সুদ্ধু ভোটের জন্যে, ভোটবাক্সের দিকে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে, গোলি মারো সেই পার্টি সিস্টেমকে।
—তো তার বদলে কোন সিস্টেম আসবে?
—সে বড় বড় মাথারা ভাবুন। আমাদের কথা তো বড় নাইভ শোনায় কি না! আসি বিশুদা।
বিশুদাকে মুহ্যমান রেখে আমি বেরিয়ে আসি। আরও দু’ কথা আমাদের তরফে শোনাতে পারতাম বিশুদাকে। আমার বা দীপুর এত দিনেও কিছু হল না কেন? আমরা তো একেবারে ফ্যা ফ্যা নই! দীপু বেচারি একটা স্কুলের চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে আছে। আমার কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। এস টি ডি, আই এস ডি বুথে চারদিক ছেয়ে গেছে এখন, আর সে ক্ষেত্রেও গদাকে আমায় তোলা দিতে হবে। কাজেই ও চিন্তাও ছেড়ে দিয়েছি। এখন বিশুদা যা জোগাড় করতে পারে। কর্পোরেশনে বিশুদার যথেষ্ট হোল্ড আছে, জগাদা বলছিল। একটা অন্তত ইন্টারভিউয়ের সুযোগও কি পেতে পারি না? আসল কথা, বিশুদা আমার বা দীপুর কারওই ভোট সম্পর্কে শিওর নয়। দাসখত লিখে দিতে হবে পায়ে, তবে যদি একটা বিস্কুট দয়া করে কুকুরের মুখে ছুড়ে দেয়। অথচ বিশুদা নিজে কী? কলেজ ড্রপ-আউট। জাস্ট গদার মতো। ছাত্র-পরিষদ করত, তারপরে যখন রাজনীতির বৃহত্তর আসরে নামল তখন কংগ্রেস ভাঙছে, ইন্দিরা-কংগ্রেস ভাঙল, বিশুদাও ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়ে এল। নিতাইকাকা বিশুদার রাজনৈতিক গুরু, তার সঙ্গে বিশুদার মুখ দেখাদেখি নেই। বিশুদা তবু ভদ্রভাবে কথা বলে, নিতাইকাকা সোজাসুজি বলে— বিশে ওই ছুঁচোটা? ওর কাছে যাস নাকি? ও তো একটা ফোর-টোয়েন্টি! অথচ নিতাইকাকা নিজেই বা কী! কংগ্রেস ভাঙার সময়ে এ কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিস্তর ঘাটের জল খেয়েছে। আদর্শ না কচু! কোন ফ্যাকশনে থাকলে খাবার সুবিধে, দাপিয়ে বেড়াবার সুবিধে এটাই দেখেছে। নিতাইকাকাও কলেজ ড্রপ-আউট। পতিতকাকার থেকে বছর দশেকের জুনিয়র। পতিতকাকাই একবার বলেছিলেন, নিতাই সব ক’টা পরীক্ষা টুকে পাশ করেছে। তার ওপর ছিল তোতলা। অথচ এখন অত ভাল বক্তৃতা দেয় কেমন করে কে জানে? মানুষ চেষ্টা করলে কী না পারে!
১৭
ক’দিন খুব জ্বর এসেছে। জ্বর-ফর আমার কখনও হয় না। কোনও অসুখই আমার ধারে কাছে ঘেঁষে না। স্বাস্থ্য কিংবা মাসল বাতিক আমার নেই। সকাল বেলায় আধঘণ্টা ফ্রি-হ্যান্ড করি, তারপর কয়েকটা যোগাসন। সর্বাঙ্গাসন, পশ্চিমোত্তান, জানুশিরাসন, পদহস্তাসন, শেষে পদ্মাসনে বসে খানিকটা মনঃসংযোগ। এ আমার বহু দিনের অভ্যেস। দেড়তলার ঘরখানা একেবারে একলার জন্যে পাওয়ায় আমার এই সুবিধেটা হয়েছে। যতক্ষণ বাইরে আছি যেমন স্বাধীনভাবে কাটাতে পারি, বাড়িতেও যতক্ষণ থাকি আমি স্বাধীন। এই ঘরটায়। ঘরটা আমার মনের মতো করে সাজিয়ে রাখি। দেয়ালে একটা, দরজার পেছনে একটা— দুটো পোস্টার। দেয়ালেরটা একটা নিসর্গ দৃশ্য— পাহাড়, পাহাড়তলি, পাইন বন, নুড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জলধারা, পেছনে আকাশটা নীল। এইটা দেখতে আমার ভাল লাগে, ৮ ফুট উচ্চতার ঘরে, পোস্টারের ওই পাহাড় যেন আরও অনেকটা উচ্চতা নিয়ে আসে। উচ্চতা, শীতলতা, বিস্তার, ক্লেদহীন বাতাস। কলেজে পড়বার সময়ে দু’বার এক্সকার্সনে গিয়েছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে। একবার দার্জিলিং আর একবার পুরী। খুব সম্ভব এই ছবিটা আমাকে দার্জিলিঙের সেই উজ্জ্বল নীল শীতের আকাশ, ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘায় নিয়ে যায়। ঘরে ঢুকেই আমি সুইচ টিপে আলোটা আগে জ্বেলে দিই। খাটের ওপর বসে পড়ি। তার পর দেয়াল জোড়া ওই নিসর্গের দিকে চেয়ে থাকি। প্রথম টুইশানির মাইনে পেয়ে ষাট টাকা দিয়ে ওটা কিনেছিলাম। বাঁধানো-টাঁধানো হয়নি, জাস্ট সেলোটেপ দিয়ে আটকানো। মাঝে মাঝে ফটাস করে খুলে যায়, তখন আবার ফ্রেশ সেলোটেপ লাগাতে হয়।
দ্বিতীয় পোস্টারটা আমার দরজার পেছন দিকে আটকানো। অর্থাৎ দরজা বন্ধ করলে তবে দেখতে পাই। এটা অত বড় নয়। ল্যান্ডস্কেপটার অর্ধেক। মারাদোনা। সবুজ মাঠ, অস্পষ্ট জনতার রঙিন উঠে দাঁড়ানো, মাঝখানে মারাদোনার ডান পা সটান মাটির সঙ্গে ৩০ ডিগ্রি কোণে উঠে গেছে, সাদা-কালো বলটা দূরে গোলপোস্টের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। গোলকিপার একটা শূন্যে উড়ন্ত লম্বা রেখা; প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু রুখতে পারেনি।
এই ছবিটাও আমাকে কেমন উল্লাসে ভরে দেয়। যেন ওই জনতার মধ্যে আমি আছি। সব সময়ে ওই রকম উল্লাসে উল্লম্ফনে। মারাদোনার পায়ের তলার ওই ত্রিশ ডিগ্রি কোণে আছি। বলটার জ্যোতিষ্কের মতো ছুটে যাওয়ায় আছি। গোলকিপারের সটান ঊর্ধ্ব ঝাঁপে আছি। আর সমস্তর মধ্যে থেকে দুরন্ত হিরো-ওয়রশিপে শুষে নিচ্ছি মারাদোনার শক্তি, মারাদোনার কৌশল, তার প্রতিভা, তার শ্রেষ্ঠতা।
খুব যত্ন করি আমি ঘরটার। একটা পেডেস্ট্যাল ফ্যান আছে ঘরে, বউদি দিয়েছিল। দুটো জানলা, আমি ওগুলোতে সস্তা লনের মৃদু হলুদ রঙের পর্দা লাগিয়ে রাখি। দু’দিকেই তারের আটসাঁট বাঁধনে বাঁধা। আমি যদি ইচ্ছে করি ওরা সরবে, হাওয়া ইচ্ছে করলে সরবে না। একটা তক্তপোশ আছে, একজনের চেয়ে একটু বেশিই ধরে যায় তাতে। মাঝে মাঝে রিন্টি এসে শোয় তাই। রিন্টি শুলে সে-রাতটা আমার খুব ভাল কাটে, গল্পে, বাচ্চার স্পর্শে, প্রশ্নে, ঘ্রাণে। রিন্টিটা আমার ন্যাওটা খুবই। কিন্তু ওই যে! বহুৎ মা-ন্যাকরা। তাই অনেক দিন আমার কাছে শুয়ে গল্প করতে করতে হয় তো ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মাঝরাতে আমাকে ঠেলে তোলে— কাকু ও কাকু, ছোট বাইরে। ছোট বাইরে যেতে হলে কয়েক ধাপ উঠে দোতলার কলঘরে যেতে হবে, এই সুযোগটাই ও নেয়। কলঘর থেকে বেরিয়ে শুট করে মা-বাবার ঘরে ঢুকে যায়।
তক্তপোশে একটা পাতলা তোশক তার ওপর একটা একটু হেভি চাদর পাতা থাকে। তলায় একটা নরম চাদর ওপরে আবার বেড কভার, এত বিলাসিতা আমার পোষায় না। দেয়ালে একটা আলনা আটকানো আছে, তাতে আমি হ্যাঙারে করে আমার শার্ট-প্যান্ট, ইভন গেঞ্জি পায়জামা, ঝুলিয়ে রাখি। সব আমার নিজের কাচা, ইস্ত্রি করা, খুব মাঝে মাঝে লন্ড্রিতে দিই।
একটা বেঁটে আলমারি আছে ঘরটায়। এটা আমার ঠাকুর্দার। কোনও নিলাম টিলাম থেকে কিনেছিলেন বোধহয়। ভাল টিক-উডের আসবাব। কখনও পোকা-মাকড় হতে দেখিনি। এর ভেতরের দুটো তাকে আমার যাবতীয় সম্পত্তি। এবং এর মাথাটা আমি টেবিল হিসেবে ব্যবহার করি। একটা পলিথিনের টেবল ক্লথ দিয়ে ঢাকা থাকে ওপরটা, পাশে একটা কাঠের চেয়ার। দেয়ালে একটা খোঁদল করা তাকে কিছু বই থাকে, পত্র-পত্রিকা থাকে। দুটো মোল্ডেড চেয়ারও এক কোণে থাকে, কেউ এলে, বসেটসে। ঘরটা আমি নিজে ঝাঁট দিই। নিজে মুছি। লাল মেঝে টুকটুক করে সব সময়ে। বাড়িতে কোনও চৌকো কিছু এলে তার কার্ডবোর্ডের বাকসোটা আমি ঘরের কোণে ওয়েস্টপেপার বক্স হিসেবে ব্যবহার করি। এই। আর একটা কথা— ঘরে আমি কক্ষনো সিগারেট খাই না। বিশ্রী গন্ধ একটা নিচু ঘরের সিলিং থেকে ঝোলে। সিগারেট খেতে হলে ছাদ। কলঘরে আগে খেতাম। বউদি আপত্তি করাতে সেটা বন্ধ করতে হয়েছে। সত্যিই, আমি একটা স্মোকার হয়েও যদি আমার ঘরে সিগারেটের গন্ধ সইতে না পারি, তা হলে এক চিলতে কলঘরে একজন নন-স্মোকার মেয়ে কী করে সইবে! মা-বাবা-দাদা কখনও বলেনি, চালিয়ে যাচ্ছিলাম, বউদিই একদিন আমাকে ডাক দিল— রুণু শোনো।
তখন নতুন বউদি। বাড়িতে একটা গোটা মেয়ে বন্ধু হাসছে, খলখল করে কথা বলছে, ব্যাপারই আলাদা। ডাকতেই বাধ্য ছেলেটির মতো গিয়ে দাঁড়াই। কলঘরের দরজাটা হাট করে খোলা, —কী ব্যাপার, বউদি?
—তুমি গিয়েছিলে তো!
—কেন? গন্ধ-টন্ধ বেরোচ্ছে না কী? আচ্ছাসে জল ঢেলেছি তো! —আমার লজ্জায় লাল হবার জোগাড়।
বউদি বলল— জল ঢেলেছ কিন্তু তোমার চারমিনারের গন্ধ ভাই হাজার জলে হাওয়ায়ও যায় না। প্লিজ, কলঘরে সিগারেট খেয়ো না।
আমি খুব বুঝদার মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাই। কোনও ইগোমূলক বিদ্রোহ আমার মধ্যে ফণা তোলে না। তা ছাড়া দোতলার কলঘর প্রতিদিন পরিষ্কার করাটাও আমার একটা অভ্যেস। এটাও নাকি আমার বাপ-ঠাকুর্দার থেকে পেয়েছি। মা বলে— তোর ঠাকুর্দা? তখন তো ইট পাতা, টালির চালের একটা দু’ কামরার ঘর, তো সেখানকার টিনের ঢাকনা দেওয়া কলঘরও তোর ঠাকুর্দা নিজে হাতে পরিষ্কার করতেন রোজ। তোর বাবাকে তো তুই নিজেই দেখেছিস।
—আচ্ছা মা, নিজের বলতে কি আমার কিছুই নেই! বাথরুম পরিষ্কার করা পিতৃ-পিতামহ থেকে প্রাপ্ত। ছবি আর হলুদ রং ভালবাসা মাতা এবং মাতামহ থেকে প্রাপ্ত, চেহারাটা দাদার মতো।
—কেন সিগারেট? সিগারেটটা তোর একদম নিজের।—মা হাসত।
জ্বর-ফর আমার হয় না। রোদে-জলে-ঝড়ে হরদম ঘুরছি। ছাতা-ফাতাও পোষায় না। গত পরশু একটা মুষলধার নেমেছিল। এমন মাঠের মাঝখান, মানে ময়দানে যে কোথাও আশ্রয় নিতে পারিনি। পুবে হাওয়া দিচ্ছে, খাচ্ছি। গাঢ় কালো মেঘ গুমগুম করতে করতে এগিয়ে আসছে, দেখছি। প্রাণে ফুর্তি জেগেছে আর কী। এত ছোট ঘরে, সরু গলিতে, অপরিসর ঘিঞ্জি এলাকায় থাকি যে, মাঝে মাঝে ময়দানে এসে না বসলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আর যে-দিন আসি, সে-দিন আর উঠতে ইচ্ছে করে না। চা-অলারা বিরক্ত করে, এক ভাঁড় হয়তো খেয়েছি, তবু আরও খেতে হবে। ঝালমুড়ি, বাদাম ভাজা এসব হেঁকে হেঁকে কাছ দিয়ে ঘুরে ঘুরে যায়। এক ঠোঙা হয়তো চিনেবাদাম কিনলাম। কুটকুট করে অনেকক্ষণ চলে বলে এটা আমার পছন্দ। সন্ধেটা গাঢ় হয়ে গেলেই কিন্তু মেয়েদের উৎপাত শুরু হয়ে যায়।
—যাবেন?
আমি চুপ।
—বলে দিন না হ্যাঁ কি না।
—না।
—চলুন না বাবা, বেশি নোব না।
—এই যে বললেন হ্যাঁ কি না বলে দিতে!
প্রায় ভেংচির মতো একটা মুখভঙ্গি করে মক্কেল কেটে পড়ে।
আবার কিছুক্ষণ পরে আসবে শার্ট-প্যান্ট পরা মিচকে টাইপের একটা লোক। এসে পাশে বসে পড়বে। সিগারেট ধরাবে। উশখুশ করবে। তারপর খাপ খুলবে।
—ওয়েট করছেন কারওর জন্য?
—না।
—তবে?
—তবে কী?
—কম্প্যানি চাই, কম্প্যানি! ভাল কলেজ গার্ল আছে। এই ধরুন সবে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ঢুকেছে কলেজে। ভাল লাগবে গ্যারান্টি দিতে পারি।
এক তাড়া দিই—উঠবেন! এখান থেকে?
আরও একটু রাত হলে অনেকদিন পুলিশ এসে ধরে। রুক্ষ গলায় বলে—কী ব্যাপার? ময়দানে সেঁটে গেছেন যে দেখছি!
—তাতে আপনার কী? ময়দানটা আপনার?
—কোন ময়না আসবে?
—এলে আপনার দিকে উড়িয়ে দেব।
—আরে মশাই, এসব জায়গা সন্ধে সাতটার পরে ডেঞ্জারাস। উঠে চলে যান।
—কী আছে আমার, যে নেবে? সস্তা একটা ডিজিটাল ঘড়ি, এক প্যাকেট সিগারেট, একটা দেশলাই।
—প্রাণটা তো আছে?
—তা আছে, তা শুধু-শুধু প্রাণটা নিয়ে নেবে বলছেন! মেয়ে নই যে শরীরটা নেবে।
—আপনি তো আচ্ছা আহাম্মক! আমি সার্জেন্ট বলছি জায়গাটা ভাল নয়, উঠে পড়ুন। আপনি তবু স্টিক করে থাকবেন! আর একটা কথা ছেলেদের শরীরও নেয়, এমন ঘটনাও দেখছি। আজ ভাই উঠে যান।
তো গত পরশু মেঘ দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখি বড় বড় চার পাঁচ ফোঁটা গায়ে পড়ল। এত বড় স্ফটিকের মতো দানাগুলো যে রীতিমতো চাপ পড়ল গায়ে। ব্যাপক লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে হাওয়া যে-দিক থেকে বৃষ্টি তাড়িয়ে নিয়ে আসছে সে-দিকে পিঠ পেতে দাঁড়াই। আয় বিষ্টি ঝেঁপে ধান দেবো মেপে। আয় বিষ্টি। আর কোথায় যায়! সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো একটা জলের তোড় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কনকনে, বরফের মতো ঠাণ্ডা ওই ছুরির ফলার মতো ধারালো, দাঁতে-নখে বৃষ্টির হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে এবার দৌড়োই। দৌড়োতে দৌড়োতে বাস স্টপ পর্যন্ত পৌঁছে যাই। কোথাও কোনও ছাদ মেলেনি। তখন আমাকে নিংড়োলে পুরো একটা জাহ্নবী বেরোবে। সেই ভাবেই ভিড় বাসে দমসম হয়ে, লোকের গালাগাল খেতে খেতে বাড়ি এসেছি। বাড়ি আসার পথে আবার হাঁটুসমান ময়লাজল ঠেলেছি। বাড়ি এসে চান। জামা-কাপড় কাচা, আপাতত বৃষ্টিহীন ছাদে একটা সিগারেট এক কাপ গরম চা। তারপরই হ্যাঁচ্চো! যাচ্চলে আপাতত এইটুকুতেই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করলে হবে?
রাত্তিরে দুধ রুটি খেয়ে শুয়ে পড়ি। মাঝরাত থেকে জোর কাঁপুনি। চাদরটা তুলে গায়ে দিই। তারপর তোশকটাও তুলে মুড়ি দিই। সকালে দরজায় দুমদাম ঘা। মাতৃদেবী। কী রে! ন’টা বেজে গেছে। কী হল? মুখ চোখ লাল?—দেখি।
—দেখতে হবে না, এসেছে।
—কী?
—ম্যালেরিয়া।
তা অবশ্য ম্যালেরিয়া নয়, ফুলু। হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়েছি ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম থার্টি। ক্যালপল খেয়েছি। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে। চ্যাট চ্যাট করছে বিছানা। যাচ্ছেতাই লাগছে।
রিন্টি লাফাতে লাফাতে ঢুকল—কাকু তোমার চিঠি। তোমার চিঠি। তার পেছন পেছন অনিবার্যভাবে তার মা —রিন্টি, কাকুর ঘাড়ে পড়বে না। খবর্দার বলছি।
—চিঠি? আমার চিঠি? জীবনে কখনও আমার নামে কোনও চিঠি আসেনি। এল তাই ব্যাপারটা খেয়াল হল। তেইশ বছর সাত মাস সতেরো দিনের জীবনে একটাও চিঠি পাইনি! কী আশ্চর্য! চিঠি লিখেছি। পোস্ট কার্ড। মাকে দার্জিলিং থেকে…পুরী থেকে,—পৌঁছনো সংবাদ, তার সঙ্গে প্রকৃতিমুগ্ধতা! কিন্তু পাওয়ার সুযোগ কখনও হয়নি। বন্ধুরা সব আশেপাশেই থাকে। কলেজের বন্ধুরা? প্রায় যোগাযোগহীন। যে যার জীবনসংগ্রামে। এত চিঠি ছেড়েছি, একটাও ইনটারভিউয়ের চিঠি আজ পর্যন্ত আসেনি। আ-মা-র চিঠি?
উঠে বসি। রিন্টির হাত থেকে কোনওমতে খামটা উদ্ধার করে দেয় আমাকে বউদি। —ইনটারভিউ?
আমি ছোট আয়তাকার সাদাটে খামটা দেখাই, ওপরে কালি দিয়ে লেখা আমার নাম-ঠিকানা, যেন নামাবলির ছাঁদের লেখা মাত্রা টেনে টেনে। বলি—তুমিও যেমন! এমন খামে ইনটারভিউয়ের চিঠি আসে? টাইপ্ড্ নয়। কিছু নয়।
বউদি দাঁড়িয়ে থাকে, রিন্টি দরজা বন্ধ করে। হাতে রবারের বল, মারাদোনা-দর্শনে মগ্ন হয়ে যায়—আমি জ্বরকম্পিত হাতে জীবনের প্রথম চিঠি খুলি।
—আপনি বলেছিলেন প্রতিরোধ আমাকেই করতে হবে, আমার ফ্যামিলিকেই। আপনারা কেউ, আপনি, পারবেন না। আমার ফ্যামিলি ক্রীতদাস। পারবে না। প্রতিরোধ করলাম।
কোনও সম্বোধন নেই। কোনও সই নেই। জাস্ট দু’ লাইনের চিঠি।
—দ্যাখো তো বউদি, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।
বউদি উল্টে-পাল্টে দেখল। বলল—লেখার ছাঁদটা! আরে এ তো হাসির লেখা! তারপর আমার জ্বরো বিছানায় বউদি হতবুদ্ধির মতো বসে পড়ে। —হাসি কেন এই চিঠি লিখল? তোকে?
আমায় শামুর প্রস্তাব, তার রাগ, হতাশা মনে পড়ে যায়—তা-ও তুই আমার বোনটাকে রমজানের থাবা থেকে বাঁচাবি না?
বউদি বলল—মনে পড়েছে রুণু। ওকে বিয়ে করার জন্যে ওই রমজানটা খেপে উঠেছে বলে আমি তোকে, পাড়ার ছেলেদের কিছু করতে বলেছিলাম। তুই ওদের নিয়মকানুনের দোহাই দিয়ে বলেছিলি—ওদেরই রুখতে হবে এটা। তোদের কিছু করবার নেই! কথাটা আমি হাসিকে বলেওছিলাম, কেন না পাড়ার ছেলেদের, স্পেশ্যালি তোর সাহায্য ও মুখ ফুটে চেয়েছিল।
আমি উঠে দাঁড়াই, আলনার দিকে হাত বাড়াই, শার্টটা আমার হাতে; বউদি দু’ হাত দিয়ে আমাকে আটকায়—কী করছিস রুণু? কোথায় যাচ্ছিস? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? জ্বরে টলছিস! তা ছাড়া এই চিঠি, ওদের বাড়ি… ভয়ানক রিস্কি হয়ে যাবে…
—তুমি বুঝছ না বউদি, মেয়েটা যদি ছারপোকা মারার ওষুধ-ফসুদ খেয়ে থাকে, এখনও গেলে বাঁচানো যাবে। দিস ইজ টেরিবলি সিরিয়াস। তুমি মেয়ে, তুমিই ভাবো। আর কী উপায় ওর থাকতে পারে!
বউদি বলল—দাঁড়া দাঁড়া। একটু—একটু ভাবতে দে। রুণু তোর কালকেও চার জ্বর উঠেছিল। প্যারাসিটামল খেয়ে খেয়ে কমছে, আবার বাড়ছে, টাইফয়েড কি ভাইর্যাল ফিভার এখনও বোঝা যাচ্ছে না। শোন, তুই পারবি না। আমি…আমি যাচ্ছি।
—তুমি? তুমি কোথায় যাবে? পাগল নাকি! কখনও গিয়েছ? শনিতলার কাছে? এটা আরও রিস্কি। তা ছাড়া এটা আমার দায়। আমার দায়িত্বহীন কথাবার্তার ফল। তুমি কেন…
বউদি বলল—মেয়েটা আমার ছাত্রী! ছাত্রীদের জন্যে আমরা… আচ্ছা, তুই জামা কাপড় পর। দু’জনেই যাব। নে রেডি হ।
বলে বউদি বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।
দমাদ্দম করে দরজায় ঘা মারতে থাকি আমি। শরীর টলে, মুখ টক বিস্বাদ জলে ভরে যায়, তারপরে হঠাৎ ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত ভয়ংকর অচেনা অসুখ পাক খেয়ে খেয়ে উঠে আসে, ব্যাঙের ছাতার মতো মাথার দিকে ছড়িয়ে যায়, আমি কিছু ধরবার প্রাণপণ চেষ্টা করি। মারাদোনার বল নিয়ে আমি দরজার গোড়ায় আছড়ে পড়ি।
১৮
উৎকট আলো ঘরে। সামনে ডাক্তারবাবু। হাতে থার্মোমিটার। আমি বিছানায়। পাশে মা। সত্য। একটু দূরে রিন্টি। হাতে ছেঁড়া মারাদোনা। চুপটি করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।
ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশনটা মায়ের হাতে দিলেন। মা দিল সত্যর হাতে— দাঁড়াও একটু।
সত্য বলল—আগে কিনে আনি না, পরে দিয়ে দেবেন।
ডাক্তারবাবু বললেন—এইটা আপনারা ভুল করেন বউদি, এই হোমিওপ্যাথি, তা-ও আবার নিজে নিজে। ভোগান্তি বেড়ে যায় এতে।
আমি কথা বলতে চেষ্টা করি। পারি না। গলা দিয়ে কেমন একটা আওয়াজ হয়। ডাক্তারবাবু বলেন—জল দিন। বউদি, ওকে একটু জল খাইয়ে দিন।
জল খেয়ে অনেক কষ্টে ক্ষীণ গলায় বলি—কী হয়েছে?
—কী আবার হবে? —ডাক্তারবাবু বললেন—ভাইর্যাল ফিভার মনে হচ্ছে, ওই সব ক্যালকাটা ফিভার ক্যালকাটা ফিভার বলছে না? তা সত্ত্বেও ব্লাডটা টেস্ট করতে হবে। নাও ইয়াং ম্যান, টেক অ্যাবসলিউট রেস্ট। এক উইক তো বটেই। জ্বরটা গেলেও প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়বে।
আমার আর শক্তি নেই কথা-বলার, নড়া-চড়ার, কখন সত্য ওষুধ এনে দিয়েছে, মা খাইয়ে দিয়েছে, ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ বকবক করে চলে গেছেন কিছুই জানি না। ঘুম, একটা অসুস্থ ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মা গলায় জল ঢেলে দিচ্ছে, মিছরি-টিছরি জাতীয় কিছুর শরবত, দুধ, এক ঢোঁক দু’ ঢোঁক খেয়েই আমি আবার তলিয়ে যাচ্ছি। দাদা আর মায়ের কাঁধ ধরে একবার বাথরুম গেলাম। বিনবিন করে ঘাম দিচ্ছে পরিশ্রমে। কোল্যাপ্স্ করছি। দাদার গলা শুনতে পাচ্ছি—‘এ ভাবে হয় না মা, তুমি একটা বোতল কি বালতিটালতির ব্যবস্থা করো।’ সুতরাং বালতির ব্যবস্থা হয়। অনেক রাতে অল্প ঘুমের তলা থেকে ভেসে উঠে দেখি—মেঝেতে বিছানা করা, মা চোখের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে শুয়ে আছে। রাস্তার থেকে যথেষ্ট আলো আসে ঘরটাতে। সবই দেখা যায়, কেমন একটা স্বর্গীয় আবছায়ার মধ্যে। আমি পাশ ফিরে আবার ঘুম যাই। টাপুরটুপুর বৃষ্টি পড়ে নদী এল বান। শনিঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান। এক কন্যে পড়া করেন, আর কন্যের মান, আরেক কন্যে গোঁসা করে যমের বাড়ি যান।…
আপনি তো আচ্ছা জ্বর মশাই? আমি সার্জেন্ট বলছি চলে যান, তবু জ্বরে স্টিক করে আছেন? কত কাজ জানেন? জ্বরে থাকলে চলে? তুমুল ঝড় আসছে, বৃষ্টি আসছে, সত্যি-সত্যি হড়্পাবান। কূল ভাসানো, দিক ভোলানো প্রলয়ঙ্করী…।
—মা—গলা দিয়ে স্বর ফোটে না।
মা—আ—
আস্তে আস্তে উঠে বসে মা—জল খাবি রুণু?
—দাও। কত রাত হল?
—দেড়টা বেজে গেছে।
—তুমি ঘুমোওনি?
—ঘুমিয়েছি।
—বউদি?
—ঘুমিয়েছে।
—এসেছে? কখন এল?
—অনেকক্ষণ।
—এ ঘরে একবারও এল না!
—এসেছে, অনেকবার, তুই ঘুমিয়েছিলি।
আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করি না। জানি না মাকে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কিনা। তা ছাড়া আমার শরীর মনও খুব-খুব নিস্তেজ হয়ে রয়েছে। ভাবনা-চিন্তা করবার ক্ষমতা নেই। বৃষ্টি পড়ে বান আসে, আমি শুধু অসহায় সেই বানে ভেসে যেতে পারি—ঝমঝমাঝম বিষ্টি পড়ে সাগর এল বান/শনিঠাকুরের শাদি হবে তিন কন্যে দান। এক কন্যে পড়েন শোনেন/আর কন্যের মান/আর, এক কন্যে গোঁসা করে যমের বাড়ি…যমের বাড়ি…যমের বাড়ি যান।
…যা ব্বাবা, তুই তো বরাবরই হিরো! মেয়েগুলো তো সব তোর নামে মুচ্ছো যায়। আমার বোন দুটো, শামুর বোনটা, গদার ভাগ্নী…। শুধু মেয়ে কেন? তুই তো ছেলেদেরও হিরো। সঞ্জু, বাদাম, মুস্তাফা, খলিল, রাজু, তারপর ধর আমাদের ব্যাচমেটদের মধ্যে শামু, সত্য, পানু, গদা, আমি…।
কে বলেছে রে দীপু? তোর ভয়েস? না কি মাজাকি করছিস আমার সঙ্গে? আমি হিরো ছেড়ে একটা জিরোও নই রে! আমার এক কড়ার মুরোদ নেই। যদি হিরো হতাম তা হলে আমাদের পাড়া থেকে একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষ গায়েব হয়ে যেত? আজ দু’মাসের ওপর হতে চলল তার কোনও খোঁজ নেই? তোকে তো আমিই চাকলাদারের মুখে ঠেলে দিলাম। না বুঝে। কিন্তু যদি না-বুঝব তো হিরো হব কী করে? আর কড়ে আঙুলটাও তুললাম না বলে শামুর বোনটা জহর ব্রত করে নিল। কড়ে আঙুলটাও তুলিনি। উপরন্তু ক্রিটিক্যাল টাইমে এমন সুবিধেবাদী জ্বর বাধিয়ে বসে রইলাম যে একটা মেয়ে, ছোটখাটো কালোমানিক-কালোমানিক বউদি-শ্রেণীর মেয়ে আমাকে নিরাপদে রেখে পক্ষ বিস্তার করে বিপদের মুখে উড়ে চলে গেল। হায় ঈশ্বর, তুমি আমার এ কী করলে…।
সকালবেলা। চড়চড়ে রোদ্দুর। আমার পুবের জানলা দিয়ে অগ্নিস্রোত ঘরে ঢুকে যায়। জেগে উঠি। অবধারিত মাতৃদেবী। মা, মা গো, আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। তুমি ছাড়া জীবন আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি একটি রণরঙ্গিণী ছোট্ট কৃষ্ণকামিনীকে দেখতে চাই। তার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।
—হরলিক্সটা খেয়ে নে।
—দাও।
—আগে মুখটা ধো। দাঁড়া পেস্ট ব্রাশ আনি।
বালতি করে জল কেউ আমার ঘরের কোণে রেখে গেছে। আরেক বালতিতে আমি মুখ ধুয়ে কুলকুচি করি। চোখে মাথায় জল দিই।
—মা, জামাটা ছাড়ব, ওই ছাই রঙের পাঞ্জাবিটা দাও প্লিজ।
—দিচ্ছি, আগে হরলিক্সটুকু খেয়ে নে।
হরলিক্স খাই। জামা বদলাই, মা পেছন ফিরে দাঁড়ায়, পাজামাটাও বদলাই, গামছা জলে ভিজিয়ে একটু স্পঞ্জ মতো করে নিই।
—এখন একটু ভাল লাগছে?
—অনে-ক। বউদি কোথায় মা?
—সে কী রে? আজ শুক্রবার, টুকু স্কুলে চলে গেছে।
—রিন্টিকে কে পৌঁছে দিল?
—তপু।
—কে আনবে?
—টুকু নিয়ে ফিরবে।
—অনেক দেরি হয়ে যাবে না?
—তা কি তুই যেতে চাস? না আমাকে যেতে বলিস?
রাগ করো না জননী, আমার কিছু কথা আছে যে! তোমাকে বলতে, জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছি।
মৌসুম্বির রস করে এনেছে মা।
—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?
—বাঃ রান্না করব না?
—সারা রাত জেগেছ, আবার এখন রান্না?
—তা, কে করবে? তোর দাদা? না রিন্টি!
রাগ করো না জননী, একা থাকতে ভাল লাগছে না। তোমার মাতৃমুখ যে এত মধুর, এত তাপহারী—আগে জানিনি।
—দুধ-পাঁউরুটি এনেছি।
—খেতে ইচ্ছে করছে না।
—জোর করে খেতে হবে। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন। ডালের স্যুপ, চিকেন স্যুপ। দুধ,—এসব সমানে খেয়ে যেতে হবে, না হলে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়বি।
–দাও।
দু’ ঘণ্টা পরেই আবার ডাকি—মা, মা।
—কী?
—দেবে না? চিকেন স্যুপ, পাঁউ-পাঁউ?
—খিদে পেয়েছে? বাঃ—মায়ের মুখ হাসিতে ভরে যায়।
মা তাড়াতাড়ি মুসুর ডালের পাতলা স্যুপ, আর ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট নিয়ে আসে। আমার একটুও খিদে পায়নি। তার চেয়েও বড় কথা খেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু ‘দুর্বল হয়ে যাব’ ওই কথাটা আমাকে স্পৃহা দিচ্ছে। খাদ্য স্পৃহা। স্যুপ-স্পৃহা, হরলিক্স-স্পৃহা। দুর্বল হয়ে গেলে আমার চলবে না। আমাকে জ্বরটা ছাড়লেই উঠে দাঁড়াতে হবে। অ্যান্টিবায়টিকে সাঙ্ঘাতিক দুর্বলতা আর অরুচি হয়। এটুকু যদি জয় করতে না পারি, তবে আমার এই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্বের আর কোনও মানে থাকবে না।
তৃতীয়বার ফলের রস খেয়ে আর পারি না। আবার সেই মোহনিদ্রা আমাকে অধিকার করে। কখন কোথা দিয়ে দুপুর, বিকেল কেটে যায়, আমি বুঝতে পারি না।
—মা।
—একটু চা খাবি কি!
—লিকার, একটু দাও, আধকাপ। বউদি কোথায় মা?
—বাজারে গেছে।
—কেন? দাদা?
—দাদার আজকে ফিরতে দেরি হবে, তোর ব্লাড রিপোর্ট নিয়ে ফিরবে।
রাত তখন আট সওয়া আট হবে—মা চিকেন স্যুপ আর টোস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকল। তখন আর পারি না আমি, ফেটে পড়ি—সবই কি তোমাকেই করতে হবে? বউদি একটু খাবারটাও আনতে পারে না?
—কী যে বলিস? আমি তো তবু যা করছি বাড়ির ভেতরে। যত দৌড়ঝাঁপ তো ওরই। এখন ছেলেকে পড়াচ্ছে, পরীক্ষা এসে গেছে।
—হুঁ, ওইটুকু পুঁটকের আবার পরীক্ষা।
রাত্রের দুধ নিয়ে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। আধা অন্ধকারে মুখ দেখতে পাচ্ছি না। আমার ঘুম পাচ্ছে।
—শুনলুম বউদি কাজ-কর্মে সেবা-যত্নে শাশুড়িকে সাহায্য করছে না বলে মাতৃভক্ত দেবর খুব চটে গেছে?—আমি তড়াং করে উঠে বসি। মাথা ঘুরে যায়। আবার শুয়ে পড়তে পড়তে বলি—
—আশেপাশে মা বা দাদা আছে?
—না।
—কী খবর? শেষ?
—শেষ কোথায় কেউ কি জানে রুণু? সে পালিয়ে গেছে।
দীর্ঘ দীর্ঘ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি মাথাটা বালিশের ওপরে ভারহীন পড়ে যেতে দিই।
—নাও দুধটা খাও।
—কী ব্যাপার কী হল একটু খুলে বলবে?
—আমি প্রথমে দীপুদের বাড়ি যাই। তারপর মণি আর মাসিমাকে নিয়ে শামুদের বাড়ি। দেখি সব মুখ গম্ভীর করে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে উঠোনটার ওপরে। শামুর মা ঘরের ভেতরে শুয়েছিলেন। আমাকে দেখে অবাক হয়ে শামু উঠে এল। তখন একপাশে ওকে ডেকে চিঠিটা ওর হাতে দিই। আমার তখন হাত কাঁপছে রুণু, ভাবছি হাসিকে বোধহয় হাসপাতালে নিয়ে গেছে। কে নিয়ে গেছে, সেটাই শুধু বুঝতে পারছিলুম না। ওদের সবাইকে তো চিনিও না। শামু বলল—ভাবি, হাসি কাল কলেজে গিয়ে আর ফেরেনি, মাকে বলে যায়, বন্ধুর বাড়ি শাদির দাওয়াত আছে, একটা ব্যাগে ভাল শাড়ি নিয়ে যাব, বললে—সামসুল কি আমাকে যেন মা পাঠায় রাত আটটা নাগাদ। সঙ্গে চলে আসবে। সামসুল ভবানীপুরে সেই বিয়েবাড়ি গিয়ে খোঁজ নেয়। দাওয়াত ছিল ঠিকই। খুব জাঁক। বন্ধুর দাদার শাদি। কিন্তু ওর সেই বন্ধু মালিনী বলে, সব্বাই এসে গেল, এখনও হাসিনা এল না। সাড়ে ন’টা অবধি সেখানে অপেক্ষা করে সামসুল ফিরে আসে। সেই থেকে ওর কোনও পাত্তা নেই।
—কারও কাছে কিছু লিখে রেখে যায়নি?
—না। রমজানের সঙ্গে নিকাহ-র দিন নাকি স্থির হয়ে গিয়েছিল। ও বেঁকে বসাতে মায়ের কাছে মার খেয়েছিল। সেই থেকে গুম হয়ে ছিল।
—ওরা হাসপাতালটালে খবর নিয়েছে? —বলতে আমার গলা কেঁপে গেল।
—হ্যাঁ, মর্গ-টর্গ সব, এ ক’দিন গঙ্গায় কোনও তেমন দুর্ঘটনার খবরও তো নেই। খবরটা ওরা এখনও প্রকাশ করেনি। রমজানকেও বলেনি। আমাদেরও চুপচাপ থাকতে বলেছে। যা হয় ভেবে-চিন্তে করবে।
—মণিও কিছু জানে না?
—কিচ্ছু না। আকাশ থেকে পড়ল। খুব শক্ড্। কথা বলতে পারছিল না।
১৯
দিন তিনেক পর আমার জ্বরটা ছেড়েছে, সন্ধেবেলা একটা বই নিয়ে আধশোয়া হয়ে পড়ছি। একটা প্রবল গুনগুন আওয়াজ শুনি। যেন অনেক মৌমাছি একসঙ্গে উড়ছে। কী ব্যাপার?— পুবের জানলা দিয়ে দেখি —বেশ দূরে রসিক ঘোষের মোড়ের থেকে একটা ভাল সাইজের জনতা আসছে। উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে বলতে আসছে। মোড়টা পেরিয়ে গেছে, কিছুক্ষণ আর দেখা যায় না। কী ব্যাপার? এ কী? রসিক ঘোষ পেরিয়ে গেছে, আড়াআড়ি রাস্তা রহিম শেখ ক্রস করে গেল, ক্রমশ গুনগুনটা বেশ ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো শোনাচ্ছে, জনতাটা আমাদেরই বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। একেবারে সামনে রমজান আলি, কোমরে চেক লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবি, মাথায় লেসের কাজ করা টুপি। দাড়িটা ছোট করে ছাঁটা, মেহেদি ছোপানো, গোঁফ কামানো, টুপির আশপাশ থেকে যে চুলগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো আগে কাঁচাপাকা ছিল, এখন তরমুজের বিচির মতো কালো।
আমাদের বাড়ির বেল বাজছে। চ্যাঁ-অ্যা করে বাজছে। কে খুলে দেবে? কে আছে এখন? আমিই টলতে টলতে যাই। হঠাৎ কোথা থেকে বউদি ছুটে নেমে যায়। দরজা খুলছে। দেড়তলা থেকে স্পষ্ট শুনতে পাই রমজান আলির ভারী ঘড়ঘড়ে গলা—হাসিনা কোথায়? কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? রুণুবাবু কোথায়?
—রুণুর ক্যালকাটা ফিভার হয়েছে। নিজের ঘরে শুয়ে আছে।
—বাড়ি খুঁজে দেখতে দিন, আমরা খুঁজে দেখব হাসিনাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে রুণু সরকার।
—আপনারা কি পুলিশ? সার্চ ওয়ারেন্ট আছে যে ভদ্রলোকের বাড়ি সন্ধেবেলা চড়াও হয়েছেন?
—পুলিশের বাপ আমরা, এই কে আছিস এই মেয়েছেলেটাকে সরিয়ে দে তো! আমি উত্তরের জানলা দিয়ে একটা হাঁক দিই—সত্য…
তারপরে ঝাপ খেতে খেতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাই।
রমজানের পাশেই সামসুল। একটা কাগজ মেলে ধরে রাগি গলায় বলল—রুণুদা, এই চিঠি হাসি তোমাকে লিখেছিল?
—হ্যাঁ। —আমি বউদিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দাঁড়াই।
—কোথায় রেখেছ তাকে? —সামসুলের এত চড়া গলা আমি আগে কখনও শুনিনি। —চিঠিটা পড়ে কি মনে হচ্ছে আমি তাকে লুকিয়েছি! পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের জানিয়েছি। আমার গলাও সমান চড়াতে চেষ্টা করি।
—ততার সঙ্গেই আশনাই ছুঁড়িটার! তোরই কীর্তি। —খিঁচিয়ে ওঠে রমজান।
—খবরদার। আমি গর্জে উঠি। আশনাই যদি হয়ই তা হলে কি তোর সঙ্গে হবে? কবরে পা তিনবারের বার নিকাহ করতে যাচ্ছিস একটা মেয়ের বয়সি মেয়েকে! লজ্জা নেই? তোর ভয়েই দিশেহারা হয়ে সে পালিয়ে গেছে। সাবধান সামসুল বেশি নকশালি মারিস না। তোদের কেস সব আমি বিলা করে দেব। এই মুহূর্তে যা এখান থেকে। ফোট।
ততক্ষণে ভিড় জমতে শুরু করেছে। পাড়ায় যে যেখানে ছিল ছুটে এসেছে। সত্য, সত্যর দুই শালা অমল আর কমল সাহা, রহিম শেখ লেন থেকে সেলিম বিশ্বাস আর তার তিনটে ভাই খলিল, মুস্তাফা, সঞ্জু। তা ছাড়া রবিনবাবু, দুলাল মিস্ত্রি, সোমেশ্বর, জিতেন রাহা, ভানু কানু, আরও অনেক, অনেক, অন্ধকারে প্রভূত চেনা মুখের আদল।
দাদা আপিস থেকে ফিরছে। এত লোক দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। রমজান দাদার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতদুটো ধরে বলল—তোমাকে আমি ভদ্দরলোক বলে জানি তপুবাবু। তোমার এই ভাই আমার হবু-বিবিটাকে লুকিয়ে রেখেছে। পালাবার মতলব করছে এখন জ্বরের ভান করে।
—কী বলছেন আপনি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! রুণু। এ সব কী?
—আমি জানি না। জানি না দাদা।
—জানিস না, মাজাকি মারছিস আমার সঙ্গে, জেলের ঘানি তোকে না টানাই তো আমার নাম…
দাদা তীব্র স্বরে বলল—চাচা, আপনি আমার ভাইকে গালাগাল দিচ্ছেন? গত দিন দশেক ধরে ও ক্যালকাটা ফিভারে ভুগছে। রুণু, তুমি কাঁপছ। ভেতরে যাও!
বউদিকে অপমান করেছে, ও শালাকে আমি দেখে নেব—আমি চ্যাঁচাই। ওর লুঙ্গি আমি খুলে নেব। মাফ চাক বউদির কাছে। দাদা এগিয়ে এসে আমার গালে একটা ঠাস করে চড় কষাল। বলল—বলছি তো ঘরে যাও। শুনছ না কেন? টুকু চলে যাও বলছি। যা-ও।
বউদি আমাকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে আসে। দু’জনেই কাঁপছি, ভেতরের উত্তেজনায়, রাগে, ভয়ে। বউদি কাঁপতে কাঁপতে বলল— ওকে যদি কিছু করে।
আমি কাঁপতে কাঁপতে বলি, সত্যরা আছে।
নীচে অনেকক্ষণ উত্তেজিত চেঁচামেচি চলল। দাদা বলছে শুনছি— আচ্ছা আচ্ছা অনেক চেঁচামেচি হয়েছে। রমজান চাচা আপনার কেসটা কী? সামসুল— তোমরা এত লোক মিলে সন্ধেবেলায় আমাদের বাড়ি, ঝগড়া-ঝাঁটি, গালাগালি—এসব কী? কেসটা কী? কেসটা? সবাই চুপ করো। বলুন বলুন তো চাচা। এ-ই গোলমাল থামাও।
—আরে তপুবাবু—এই সামসুলের বোন হাসিকে বিয়ে করব, ওদের কথা দিয়েছিলাম। তা সেই মতো রেডি হচ্ছি। হাসিটাকে ওই আপনাদের দীপু-পাগলার বোন আর আপনার ভাই মিলে পড়াল। পাশ করাল। কলেজ যেতেই বাস আর তার মাটিতে পা পড়ে না।
—ছি ছি—আপনি বলছেন কী? সামসুলের বোন আমাদের বাড়ি? হ্যাঁ মণিমালার সঙ্গে টুকুর কাছে পড়তে আসত মাঝে মাঝে। তাতে হয়েছে কী?
—আপনার বিবিও এ সব্বোনাশের মধ্যে আছেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি।
—লেখাপড়াটা সব্বোনাশ! আপনি বলছেন কি চাচা? শুনলে লোকে কী বলবে?
—সব্বোনাশ ওই আশনাইয়ের আস্পদ্দা—বুঝলেন? সে পালিয়েছে। সমাজ, ফ্যামিলি কিছু আর মানে না। আমি তখনই সাবধান করেছিলুম শামুকে…
—সামসুল! তোমার বোন…
—হ্যাঁ তপুদা ক’দিন আগে বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন যাবে বলে ব্যাগে জামাকাপড় ভরে কলেজ চলে গেল। আর আসেনি।
—তারপর? তোমরা থানায় খবর দিয়েছ?
—না। এখন সামসুলের সুর অনেক স্বাভাবিক—বদনামি হবে, হাসপাতাল-টাল খোঁজ করেছি। কোথাও নেই। পরদিন টুকুভাবি আর মণিমালা গিয়ে আমার দাদাকে এই চিঠি দিয়ে আসেন। চিঠিটা রুণুদার নামে এসেছিল।
কিছুক্ষণ চুপ। দাদা বোধহয় চিঠিটা পড়ছে। একবার, দু’বার…
কিছুক্ষণ পর আবার দাদার গলা—এর থেকে তো একটুও মনে হয় না তোমার বোনের নিরুদ্দেশের সঙ্গে আমার ভাইয়ের কোনও সম্পর্ক আছে সামসুল! চাচা, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের প্রাইভেট ব্যাপারে আমরা কেন কথা বলব। কিন্তু এই মেয়েটি কীসব প্রতিরোধটোধ লিখেছে। ফ্যামিলি ক্রীতদাস লিখেছে—এসব তো ভাল কথা নয়! ও আপনাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক নয়, বোঝাই যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আপনি কি গায়ের জোরে বিয়েটা করবেন? ইস্স, কত ভয় পেয়েছে তবে একটা সদ্য কলেজে পড়া কনজারভেটিড পরিবারের মেয়ে পালাতে পেরেছে! ও যদি কোনও হঠকারিতা করে বসে, তা হলে কিন্তু চাচা প্রধান দোষটা হবে আপনারই। আপনারা এখন যান। আমি রুণুকে-টুকুকে জিজ্ঞেস করছি। যদ্দূর পারি আপনাদের হেল্প্ করব কথা দিচ্ছি।
আস্তে আস্তে ফাঁকা হতে শুরু করল নীচেটা। সত্য, অমল, কমল ধাঁই ধাঁই করে ওপরে উঠে এল। কী ব্যাপার রে রুণু?— তুই তো এত বোকা ছিলি না।
—উফফ। আমি একটু হতাশ। কাতর প্রতিবাদ করি। বউদি বুঝিয়ে বলে— রুণু ওকে ভাল করে চেনে না পর্যন্ত। রমজানকে কী করে ওই মেয়ে বিয়ে করবে তোমরাই বলো।
—চেনে না, তো এরকম ডায়ালগ লিখল কী করে?
—ও আমার কাছে সাহায্য চাইত, আমিই রুণুকে একদিন বলি— তোমরা পাড়ার ছেলেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে এমন একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে, তাইতে রুণুই বলে— ওকে, ওদের নিজেদেরই এবারে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমরা ইনটেরফিয়ার করতে গেলে পুরো কমিউনিটি তো ভুল বুঝবে! সেটা আমি ওকে বলি। তাই হয়তো অভিমানে এ চিঠি রুণুকে দিয়েছে।
—আপনি তো ঠিকই করেছেন, রুণু তো ঠিকই বলেছে। কিছু করেনি তাইতেই পুরো শনিতালাও হাজির হয়ে গেল, কিছু করলে না জানি কী হত? সাবধানে থাকিস রুণু—অমল-কমল-সত্য চলে গেল। তারপর দাদা আমাকে ধরল।
—রুণু, সত্যি কথা বলো, মেয়েটার সঙ্গে তোমার…
—অনগড দাদা, আমি তাকে ভাল করে দেখিনি পর্যন্ত।
—আমি কিছু মনে করব না, তুমি নির্ভয়ে বলো। ভালবেসে ফেলেছ, কী করা যাবে! বলো!
বউদি বলল—সত্যি, ও হাসিকে চেনেই না।
—তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি, কথাটা জিজ্ঞেস করেছি যাকে উত্তরটা তাকেই দিতে দাও।
—দাদা, কতবার বলব আমি হাসিকে মণির সঙ্গে দু’ চারবার আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি, তখন হয়তো আমি টুইশন সেরে হা-ক্লান্ত হয়ে ফিরছি।
—তাহলে মেয়েটিই তোমার প্রেমে পড়েছে। এখন কথা হচ্ছে, গেল কোথায়? এরা থানায় খবর না দিয়ে খুব ভুল করেছে। পাতাল রেল-টেল— আজকাল কতরকমের সুযোগ-সুবিধে হয়েছে!
পরের কয়েকদিন দাদা শামু সামসুলকে নিয়ে থানা-পুলিশ করল। এখন অনুসন্ধানের জাল আরও নিয়মমাফিক বিছোনো হচ্ছে। শুনলাম নাকি ওসি শামুকে বলেছেন— আরে সমশেরভাই, তোমারই বাড়ি থেকে তোমার বোন চুরি? এ যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!
শামু নাকি জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলেছিল— চুরি নয়, ফেরার।— যাক যাক। চুরির থিয়োরিটা শামু অন্তত মানে না। কিন্তু কে যে এই ডামাডোলে কতকগুলো বোমা টপকে দিল শনিতলার বস্তিতে তা এক ঈশ্বরই জানেন। শনিতলায় বাঙালি, বিহারি, ওড়িয়া, হিন্দু এবং মুসলমান নিম্নবিত্তদের বাস। অবশ্য কিছু সম্পন্ন মুসলমানও আছে।
শুনলাম কতকগুলো ঘর উড়ে গেছে। মাঝরাত্তিরে ফেটেছে বোমাগুলো। নারী শিশু বেশ কিছু মরেছে। সত্যদের বাড়ির কাজের লোক এসে বলল— নিমকি শিমকির মা শেষ। দুই বোন হাসপাতালে, কী হবে বলা যাচ্ছে না। আরও কয়েকজন গেছে। বেঁটেদার হাত উড়ে গেছে একটা।
অসম্ভব মন খারাপ। একটা ঘটনা, যাতে আমার অজান্তে আমি জড়িয়ে আছি, সেইটা নিয়ে আমাদের এলাকা আবার ফিরে গেছে সেই শামু-গদা সমঝোতার আগের দিনগুলোয়। কিন্তু শামু, গদা বা রমজানের গায়ে পুলিশ হাত দেয়নি। ধরেছে আরও কিছু ছুটকো গুণ্ডাকে।
গায়ে জামাটা গলিয়ে বেরিয়ে যাই। মা এখন ছাদে। তুলসীতলায় পিদিম দিচ্ছে। রিন্টি আর বউদি বোধহয় ঘরের মধ্যে কোনও গেম খেলছে। রিন্টিকে আটকে রাখবার জন্যে বউদি আজকাল এই কৌশল ধরেছে। লুডো সাপলুডো। যতক্ষণ না জিতছে রিন্টির শান্তি নেই। সুতরাং খেলা অনেকক্ষণ চলে, বেস্ট অব থ্রি, বেস্ট অব ফাইভ, বেস্ট অব সেভ্ন। আমি নিঃসাড়ে বেরিয়ে পড়ি।
সাঁঝবাতি জ্বলছে গলিতে গলিতে। রসিক ঘোষ পেরিয়ে এস এস আলির মোড়ে আসি। আমি যাব বড় রাস্তায়। গাড়ির হর্ন, অনেক মানুষের চলাফেরার স্বাভাবিক আওয়াজ হই-হট্টগোল আমি শুনতে চাই। ‘গুহ প্যালেসে’র কাছে এসে দেখি—দীপু বেরোচ্ছে। দীপুর পরনে সেই পুরনো রদ্দি শার্ট আর পাজামা। পায়ে থ্যাপাস থ্যাপাস হাওয়াই চপ্পল।
লজ্জা হল ভাবতে এই ডামাডোলে দীপুর কথা, দীপুদের কথা আমি একবারও ভাবিনি। অথচ ওরা থাকে শনিতলার বস্তির মুখেই।
—কী রে কেমন আছিস?—আমার গলায় উদ্বেগ বোধহয় ভালই ধরা পড়েছিল।
দীপু হেসে বলল—তুই যেমন রেখেছিস!
—মানে?
—মানে কি আর তুই জানিস না? তুই শালা প্রেম করবি আর বোম পড়বে আমাদের ঘরে। মজা মন্দ নয়।
—ভাল হবে না দীপু। আমার বন্ধু হয়ে এরকম আলটপকা মন্তব্য যদি তোর মুখ থেকেই বেরোয় তা হলে বোমটা এবার আমাকে টিপ করেই ছোড়া হবে। আমি নিশ্চিত ডেড অ্যান্ড গন। খুশি হবি? খুশি হবি তাতে?
—তোর তা হলে বোম-টোমের ভয় আছে?
—আলবাত আছে। আমি তোর মতো ভবঘুরে খ্যাপা-পাগল নই।
—ভবের আর কট্টুকুনি ঘুরলুম রে রুণু, এতেই ভবঘুরে বলছিস! পাগলাই বা তেমন করে হতে পারলুম কই? বলে দীপে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে গান ধরল—
তেমন একজন পাগল পেলাম না
ভোলামন, তাইতে পাগল হলাম না…
আমি পাশ কাটাতে যাই। দীপু আমাকে বজ্রআঁটুনিতে ধরে, রুণু বেঁটেদাকে দেখতে যাবি না?
—তাই তো যাচ্ছি!
—আর নিমকি-শিমকি?
—গেলে তো ওদের সঙ্গেও দেখা হবে।
—তোর সঙ্গে দেখা হলেই দু’ বোন ভাল হয়ে যাবে। শালা সব মেয়ে তোকে দেখে মুচ্ছো যাবে? কতক চাট্টি আমার দিকেও তো পাঠাতে পারিস!
—এসব চ্যাংড়ামি আমার ভাল্লাগছে না দীপু। বললি না তো মাসিমা, মণি, মুক্তা সব কেমন আছে?
—ফর্চুনেটলি অর আনফর্চুনেটলি আমাদের কিছু হয়নি। যারা বোম মেরেছে তারা দেখে দেখে একেবারে গরিব নিঃসহায়, মেয়েমানুষ আর বাচ্চার সংসারে মেরেছে।
—সত্যি বলছিস?
—বলব না? দ্যাখ রমজানের কিছু হয়নি, শামুদের কিছু হয়নি। আমরা গরিব, তবু বোধহয় ভদ্দরলোক বলে মানে, আমাদেরও তেমন কিছু হয়নি।
—‘তেমন কিছু’ মানে?
—না, ওই!
—কী বল না।
—মুক্তাটাকে আওয়াজ দিচ্ছে, আশে-পাশে, এই আর কী!
—দীপু এটাকে লাইটলি নিস না। সাবধান হ৷ এতদিন দিচ্ছিল না, এখন দিচ্ছে। এর মানে কী?
—কীভাবে হব? তুই-ই বল। মেয়েটাকে তো কাজে বেরোতে হবে? ন’টায় বেরোয়, সাড়ে সাতটায় ফেরে। মণিটা অবশ্য বেলা থাকতে থাকতেই ফেরে।
—তুই এক কাজ কর, মুক্তার ‘লা-বেল’-এ গিয়ে ওকে তিনটে সাড়ে তিনটেয় অফ করে দিতে বল কিছুদিনের জন্যে। বিপদের কথাটা বল।
—সাড়ে তিনটে তো আরও বেটার সময় রে, রাস্তা থেকে মুখ বেঁধে মেয়ে তুলে নেওয়ার উৎকৃষ্ট সময়।
আমার ভেতরটা আবার থরথর করতে থাকে। কথা বলতে পারি না।
—ব্যবস্থা একটা করেছি। একটা সাহারা।
—কী ব্যবস্থা?
—গদাকে বলেছি। গদা বলেছে ও দেখছে।
গদার নাম শুনে আমার রাগ হয়ে যায়। মাফিয়া, গুণ্ডার সর্দার একটা, চুরি-জোচ্চুরি করে ম্যানশন বানিয়েছে। সে হবে কারুর সাহারা! যদি-বা হয় কড়ায় গণ্ডায় দাম বুঝে নেবে।
একটাও কথা না বলে পা বাড়াই। হলই-বা দুঃখের দিনে গদাইরা ওর মাকে রাঁধুনির কাজ দিয়েছে, মান বাঁচিয়েছে, তাই বলে এতটা পক্ষপাত?
—এই রুণু, একটু দাঁড়িয়ে যা।
—কেন? আমি থেমে গিয়ে বলি।
—মন খারাপ করিসনি। ও বোমবাজি তোর জন্যে হয়নি। মানে তুই রিমোটলিও এর সঙ্গে যুক্ত নয়।
—তা হলে?
—শনিতলাওটা যারা বুজে ফেলছিল, কাজটা তারাই করেছে। দাঙ্গা বাধবে। পুলিশ এলে লাঠালাঠি হবে। কিছু নিকেশ হবে। কিছু জেল। ওরা যুক্তভাবে একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়েছিল মনে আছে। এটা তারই প্রতিশোধ। এই ডামাডোলে ঐক্য নষ্ট হবে, অনেকে এলাকা ছেড়ে চলে যাবে… তখন আবার জমি ভরাট, বিশাল কমপ্লেক্স… ওয়েস্ট টাওয়ার সুইমিং পুল-নেচারের কোলের ওপর যদি বাস করতে চান। এটা একটা বহুতল কমপ্লেক্স নয় শুধু… এটা একটা লাইফ-স্টাইল…
আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। শেষে শুধু বলতে পারি, তুই কী করে জানলি? কে বলল তোকে?
দীপু বলল—ভয়েস।
২০
বেঁটেদাকে দেখে আমার চোখ ফেটে জল এল।
বাঁ হাতটা ব্যান্ডেজ করা। কতটা কাটা গেছে বুঝতে পারছি না। বেঁটেদা এখন অ্যানেস্থেশিয়ার ঘোর থেকে জেগে উঠেছে। কিন্তু বিহ্বলতা কাটেনি। আমাকে দেখে কিন্তু হাসল। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল— এখন থেকে ডান হাতেই খাওয়া, ডান হাতেই ছোঁচানো, বুঝলি রুণু! লোকে আমার হাত থেকে জিনিস কিনবে তো রে?
আমি ওর ডান হাতটা ধরে চুপ করে বসে রইলাম। বেঁটেদার কেউ নেই যে দেখতে আসবে। জনরব শুনেছি বেঁটে হওয়ার অপরাধে বছর দশেকের ছেলে বাবা-মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল। হিজড়েরা যেমন হয়। তারপর নানা ঘাটের জল খেতে খেতে আমাদের এই এলাকায়। খুব সম্পন্ন না হলেও বেঁটেদার জন্ম নাকি মোটের ওপর ভদ্র পরিবারে। কোনও শহরের উপকণ্ঠে। কোথায়, কী বৃত্তান্ত বলতে চায় না। অভিমান ভেতরে আছে কি না জানি না, মুখে বলে— ‘বেঁটে ছেলে, পা ছোট, ধড় বড়, এমন ছেলে আবার কেউ সংসারে রাখে? সংসারের অকল্যেণ হবে না?’ আমি যবে থেকে দেখছি বেঁটেদা সদানন্দ পুরুষ, লাল দোপাট্টা মলমল, ডম ডম ডিগা ডিগা… ববিতা-আ, ও মাই ডার্লিং এইসব ফিলমি গান হেঁড়ে কর্কশ গলায় গাইতে গাইতে নিস্তব্ধ শুনশান শীতের রাতে বাড়ি ফিরত। পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে গামছা। বেঁটেদা খুব সম্ভব শনিতলায় আর পাঁচজনের পাশাপাশি একটা ঝোপড়ি তুলে নিয়েছে। সবাই যা করছে তাই করেছে। একেক সময়ে আমার মনে হয় বেঁটেদা বাঙালিও নয়, বিহারি। কোনওদিন তো এসব খোঁজ করিনি, বাজারে অদ্ভুত কম্বিনেশনের সওদা নিয়ে বসেছিল তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, গান-টান গেয়ে গেয়ে অদ্ভুত ক্লাউন চেহারার লোকটা ঘুরত, মজা মারতাম, আজ বাঁ হাতটা কার বোমার ঘায়ে শেষ তাই খেয়াল হয়েছে বেঁটেদাও মানুষ, তার একটা শরীর আছে, ডান হাত বাঁ হাত আছে। বাঁ হাতটা যেতে বেঁটেদার প্রধান সমস্যা তাকে খাওয়ার হাতেই ছোঁচাতে হবে, সেই হাতেই আবার তার সওদা বেচতে হবে, এখন ডান বাঁ এক হয়ে গেলে, হকার হিসেবেও সে অচ্ছুত হয়ে যাবে কি না।
—কত বড় বড় লোক যে আমাকে দেখতে আসছে। আমি তো কোথায় বসাব কীভাবে কী করব… একেবারে বোকা মেরে গেছি রে! প্রেথম এল বিশুদা এমেলে, তারপর জগন্নাথবাবু, বলরামবাবু, দুই ভাই, তারপর অরবিন্দদা, তুই আসার ঠিক আগেটায় কে এল জানিস?
—কে?
—এম পি সায়েব, নিতাইলাল ভটচায। বলতে বলতে বেঁটেদা কেঁদে ফেলল, —কী এমন হয়েছে বল যে এত বড় বড় মাথা আমার জন্যে ভাববে! তোরা ছোটভাই, আসবি বইকী! কিন্তু..
—তা এঁরা কি শুধু দেখেই গেলেন, না কিছু বললেন টললেনও— আমি আমার গলার শ্লেষ গোপন করতে পারি না। কিন্তু বেঁটেদা সে-সব ধরতে পারে না। বলে সব্বাই প্রমিস করে গেল কমপেনসেট আদায় করে দেবে! এখন, সব্বাই যদি কিছু কিছু করে দেয়, তো সে তো অনেক টাকা রে রুণু, ব্যাংক-ট্যাংক আমার বড্ড ভয় করে, তুই যা করার করে দিস।
আমি চুপ করে ছিলাম, বেঁটেদা বলল— দিবি তো? তোকেও কিছু দোব। নিয্যস। তার মানে বেঁটেদাও ভালই বুঝে গেছে, বিনা স্বার্থে, বিনা পারিশ্রমিকে কেউ কারও জন্যে কিছু করে না। ছোট স্কেলে বুঝতে পারছে। কিন্তু বড় স্কেলে অর্থাৎ জগা, বিশু, অরবিন্দ, নিতাইয়ের স্কেলে বুঝতে পারছে না।
বেঁটেদার পাশের বেডেই আলম। তারও দেখলাম পায়ে প্লাস্টার, মাথায় ব্যান্ডেজ, ডান পাটা ট্র্যাকশনে রাখা। আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল।
কেউ দর্শনীয়ভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিলেও গিয়ে খোঁজখবর করব এতটা বুকের পাটা আমার নেই। তবু বুকের মধ্যে অনেকটা হাওয়া টেনে গেলাম।
—আলম!
—বলেন!
—কেমন আছ?
—যেমন রাখছেন! ডান পাটা বোধয় গেল গিয়া। আল্লার কিরা আমি এর শোধ নিয়া ছাড়ুম। এ আপনেরে কইয়া দিলাম।
আলম হল ইনফিলট্রেশন। বাংলাদেশি মুসলমান, বনগাঁ বর্ডার দিয়ে এসেছে পশ্চিম বাংলায় যে বাংলা থেকে আলমের নানা-দাদারা স্বেচ্ছায় ভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তবু আলম এই বাংলাকেই বেশি বাসযোগ্য মনে করেছে। অনেক বাংলাদেশি মুসলিমও চলে এসেছে কাজ-কামের খোঁজে। র্যাশনকার্ড পেয়েছে, ভোটার লিস্টে নাম তুলিয়েছে। রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলই বোধহয় ওর পা-টা বাঁচাতে পারবে না। কেন না পা তো ভোট দেয় না! আমি ওর এই প্রতিহিংসা-বৃত্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী বলব! ওর জায়গায় থাকলে আমি কী বলতাম! আমি পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি, যেমন করে পারি আমি আমার অন্ন জোগাড় করে নেব, কারণ পেট মানবে না, ক্ষুধা, ক্ষুধা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আমি এক চারণভূমি থেকে ভিন্ন চারণে প্রস্থান করেছি। নির্মায়ায়। পেরিয়ে গেছি মরু, নদী, পাহাড়, সাগর, শুধু এই জঠরের তাগিদে, শস্য বুনেছি, হাত দিয়ে তৈরি করেছি কারুমায়া, সব স-ব মূলত এই পেটের জন্যে। হে এম এল এ হে এম পি হে ক্ষমতাবান, হে বিত্তবান, তোমারও যেমন খিদে পায়, আমারও তেমনি খিদে পায়। খিদে মেটাতে আমি উঞ্ছবৃত্তিও করতে পারি, আবার দস্যুবৃত্তিও করতে পারি। খিদের কোনও দেশ কাল নেই। পাত্রাপাত্রভেদ নেই। সদুপায় কদুপায় নেই।
কিছু ভাবিনি কী বলব, ভাবছিলাম চুপচাপ পেরিয়ে যাব, ও তো আমাকেই ওর দুরবস্থার জন্যে দায়ী করছে। সম্পূর্ণ না জেনে, যে ও আরও গভীর চক্রান্তের শিকার! যদি দীপুর ভয়েস সত্যি হয় অবশ্য। কিন্তু পেরোতে গিয়েও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম, শুনলাম বলছি— তোমার বাঁ দিকে দেখো, বেঁটেদার বাঁ হাতটা গেছে, ডানদিকে তোমার পা জখম, কে কার বিরুদ্ধে লড়বে আলম?
নিমকি এখনও অজ্ঞান, ওর মাথায় লেগেছে। খুব সম্ভব আরও বড় হাসপাতালে পাঠানো উচিত। অপারেশনের জন্য। কর্তারা না কি আশা দিয়েছেন পি জিতে পাঠাচ্ছেন। শিমকির চোট সে তুলনায় কম, বোমার শব্দে আর কাঁপুনিতে ওদের টালির ছাদ ধসে পড়েছিল। ওর চোট তার থেকেই। সারা শরীরে কাটাছেঁড়া, ব্যান্ডেজ, স্টিকিং প্লাস্টার।
—শিমকি এখন একটু ভাল আছ!
—জ্বলছে—শিমকি বলল।
—যাই হোক, ওষুধ পড়েছে, ব্যান্ডেজ-টেজ হয়েছে, আগের চেয়ে তো অনেক…
—শরীর নয়কো, মন…মন জ্বলছে…আপনি অন্য মেয়ের সঙ্গে পুড়কিবাজি করবেন, আর আমাদের ওপর বোম পড়বে! ভাল রে ভাল! কী ভদ্দরলোক! মা বলত না—অমন ভদ্দরের মুখে ঝাড়ু মারি। ঠিক বলত… বলতে বলতে, শিমকির দু’চোখ দিয়ে জলের ধারা নামল।— যে মা ও কথা বলতেন, তিনি আর নেই।
আমি পাথরের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। কী বলব! কাকে বলব! কেনই-বা বলব!
—যান, যান, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন! কোথায় সেই পীরিতকে লুকিয়ে রেখে এসেছেন, যান তার সঙ্গে কেলি করতে যান।
আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না, বলি— তোমরা…তোমরা আমাকে ছোটবেলা থেকে জানো চেনো, ওই শনিতলাওয়ে কত সাঁতার কেটেছি সে সময়ে, তোমরাই যদি মিথ্যে রটনা বিশ্বাস করো তা হলে তো অন্যে করবেই। বোমটা এরপর সোজা আমার মাথার ওপর পড়বে। বিনা কারণে। খুশি হয়ো তখন।
বেশ একদল নানা বয়সের বাচ্চাও ওয়ার্ডের এক ধারে রয়েছে। এদের অল্পস্বল্প চোট। সে সবের চিকিৎসা হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু এরা স-ব এই বোমবাজিতে অনাথ হয়ে গেছে। কারও কারও বাবা বা মা মৃত্যুমুখী, অজ্ঞান, যুঝছে। হেরে যাবে, সবাই বুঝছে।
কয়েকটা ছোট কট-এ দুগ্ধপোষ্য শিশুদের স্থান হয়েছে। একজন সিস্টার দেখি একটা বড় বোতলে দুধ নিয়ে একটি শিশুর মুখে ধরলেন। পরম আগ্রহে সে যেই টানতে শুরু করেছে, এক মিনিট, তারপরেই বোতলটা টান মেরে খুলে নিয়ে আরেকটা বাচ্চার মুখে ধরলেন মহিলা, এইরকমই চলল কিছুক্ষণ। আমি বেকার, আমার অনন্ত সময়। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি।
—কী করছেন এটা?—আর থাকতে পারি না, বলি।
—কী?
—এইভাবে একটু খাইয়ে টেনে নেওয়া, একই বোতল দশটা বাচ্চার মুখে…
—এইরকমই ইনিস্ট্রাকশন আছে।
—কে দিলেন?
—কে দেয়?
—ডাক্তার বা মেট্রনের বোধহয় দেবার কথা, কিন্তু আপনার ইনস্ট্রাকশন মনে হচ্ছে আরও ওপর থেকে এসেছে!
—ওপর-টোপরের ভয় আমাকে দেখাবেন না। অত সহজে ভয় খাওয়ার মেয়ে আমি নই! তা ছাড়া, আপনি কে? এই বাচ্চাগুলোর বাবা?
আমি বললাম—আপনিও যেমন ওদের মা নন, আমিও তেমনই ওদের বাবা নই। আপনি ইনিস্ট্রাকশন পালন করুন, আমি আপনাকে নমস্কার করে— আসি।
ভেতরটা কীরকম একটা অক্ষম রাগে ফুঁসছে। যদি পাই, একবার হাতের কাছে ওই বেজম্মাগুলোকে, একবার কেউ বলে দিক, অকাট্য প্রমাণ দিক তারপরে দেখাচ্ছি কত ধানে কত চাল, ধম্মের কল কোন বাতাসে নড়ে। দেখছি আমি হিরো কি জিরো, ব্যায়াম করি কি করি না, টুঁটি টিপে ধরে বঁটিতে গলা কাটব। একবার, একবার শুধু কেউ বলে দিক। আমি একটা একদা উদ্বাস্তু-পরিবারের বেকার ছেলে, যেমন মস্ত কিছু ভাল নই, তেমনি মস্ত কিছু খারাপও নই। কারুর বিরুদ্ধে আমার নালিশ ছিল না, লোকের সাধ্যমতো উপকার করবার চেষ্টা করেছি। অপকার কারও করিনি কখনও। সেই আমাকে উপলক্ষ করে দাঙ্গা লাগবে? ধান্দাবাজরা তার সুযোগ নেবে? এতগুলো মানুষ ঘরছাড়া, অঙ্গহীন, অনাথ হবে, মরে যাবে? সত্যি কথা বলতে কি হাসির ওপর পর্যন্ত এবার আমার হেভি রাগ হতে লাগল। প্রেমে পড়েছে? প্রেম মাই ফুট। পালাত, আমাকে চিঠি লিখে পালাবার দরকারটা কী ছিল? বুড়ো ভামটা, আলুর বস্তাটা নিকাহ নিকাহ করে এগিয়ে আসছিল তো তার মুখে থুতু দিতে পারেনি! কাটারি নিয়ে তেড়ে যেতে পারেনি! একজন একজনকে বিয়ে করবে না বলে দাঙ্গা? নিরীহ মানুষের সম্পত্তিনাশ, প্রাণনাশ?
ফুটতে ফুটতে রসিক ঘোষের মোড়ে পৌঁছেছি হঠাৎ দেখি একজন লম্বা রোগা দাঁড়িগোঁফঅলা লোক, একটা হাত স্লিং-এ ঝোলানো, মাথায় ব্যান্ডেজ, বিশ্রীভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে। আমাকে খুব দুর্বলভাবে হাত তুলে থামতে ইশারা করছে। আমি দাঁড়িয়ে যাই। আর একজন দাঙ্গার ভিকটিম না কি? কী বলতে চায়? আরও নিকটবর্তী হল লোকটা। তারপর ভাঙামতো গলায় জিজ্ঞেস করল— সৈয়দ সৈফুল আলি রোডটা কোথায় বলতে পারেন? এখান থেকে কতদূর?
—এই তো আর একটু, আপনি আসলে উল্টো দিক দিয়ে ঢুকেছেন। বড় রাস্তা থেকে স্ট্রেট এস এস আলিতে ঢুকতে পারতেন, ‘মহাজন হাউস’ বলে একটা বিরাট বাড়ি আছে ঢুকতেই…
কীরকম অস্বাভাবিক উত্তেজিত হয়ে লোকটি বলল—আছে? আছে, এখনও আছে? ‘মহাজন হাউস’। ও থরথর করে কাঁপছে। তখন ভাল করে দেখি এ তো মহেন্দ্র? অদ্ভুত একটা গা ছমছমে চেনা চেনা মতো লাগছিল। কিন্তু এত দাড়িগোঁফ, রোগা কালো, ঝাঁকড়া মতো চুল!
আমারও উত্তেজনা চরমে ওঠে— মহেন্দ্রদা আমি রুণু, রণধীর সরকার। চিনতে পারছেন না! তপোধীরের ভাই, আপনাদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িটা দেখা যায়।
কোনওরকমে আমার হাতটা ধরে ফেলে মহেন্দ্র— চুপ, একদম চুপ, কথা বললে দে উইল কিল মি। প্লিজ গাইড মি আ বিট। আমি কিচ্ছু চিনতে পারছি না। আই অ্যাম লাইক আ ব্লাইন্ড ম্যান ইন আ ব্লাইন্ড লেন… প্লিজ রুণু অর হোয়াটেভার…
আমি একটা রিকশা ডাকি। গায়ের মধ্যে কী রকম শিরশির করছে। কোনওক্রমে মহেন্দ্রকে তুলি, পর্দা ফেলে দিতে বলি। তারপর ‘মহাজন হাউজ’-এ গিয়ে বেল দিই।
ভেতরে সেই অ্যালসেশিয়ানটা ডাকছে গাঁউ গাঁউ করে। আস্তে আস্তে দরজাটা ফাঁক হল, কোনও কাজের লোক, চেনের ওপারে আলোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বলি এ এস কিংবা জে মহাজন আছেন?
—কী দরকার?
—বলুন একটি চেনা ছেলে দেখা করতে এসেছে। একটা হারানো জিনিসের ব্যাপারে।
একটু পরেই ভেতরে আলো জ্বলে উঠল। আরও একটা আলো, আরও একটা জোর আলো। প্রথমে জগদিন্দ্র, তারপরে একটি ইয়াং ম্যান আমি চিনি না, তারপরে এ এস, তারপরে বাড়ির মেয়েরা, বাচ্চারা। আমি সাবধানে রিকশার পর্দা তুলে মহেন্দ্রকে নামাই। দরজার ফাঁকে মুখ রেখে বলি— দেখুন, দরজা খুলে দিন, মহেন্দ্ৰদা। মহেন্দ্রদা এসেছেন।
দরজা খুলে গেল, তীব্র একটা আর্ত মেয়েলি চিৎকার, সোনা রঙের একটি একহারা বউ আলুথালু অবস্থায় ছুটে এসে মহেন্দ্রকে জড়িয়ে ধরল। পাগলের মতো কাঁদছে, বুকে মাথা ঘষছে, কোনও অদৃষ্টকে অভিশাপ দিচ্ছে আবার আশীর্বাদ করছে…।
আমার পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চোখভর্তি জল এ এস বললেন, মাই বয়, কোথায়, ওকে কোথায়, কীভাবে? তুমি কি সামহাউ কিডন্যাপার্সদের সঙ্গে জড়িত? বলো, আমি কিছু বলব না। আর কারও কাছে আমার নালিশ নেই। দে হ্যাভ কেপ্ট দেয়ার ওয়ার্ড। দে হ্যাভ রিটার্নড্ হিম। অ্যাট লঙ লাস্ট।
আমি প্রমাদ গনি। দাঙ্গার সঙ্গে জড়িয়ে গেছি। এবার কি কিডন্যাপার্সদের সঙ্গেও জড়াব? খুলে বলি কীভাবে ওঁকে পাই।
সবাই গোল হয়ে আমায় ঘিরে। একটা বিশাল ডিভানে মহেন্দ্রকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। কী রকম বেভ্ভুল ভাবে অসংলগ্নভাবে বলে যাচ্ছেন ওঁর অভিজ্ঞতা। আমাকে অন্ধকার ঘরে চোখ বেঁধে রাখত, পা, ওরা আমাকে শট দিত বার বার, আমি কত করে বলতাম আমি এমনিই ঘুমব। শট দেবার দরকার নেই। শুনত না। ওরা কিছুতেই শুনত না, শাসাত। পা, আমি আমার নাম ভুলে গেছিলাম। আমি কে, কোথায় আমার ঠিকানা, বেঁচে আছি না মরে গেছি। ভাবতাম আমি মরে গিয়ে নরকে এসেছি। ধস্তাধস্তিতে গাড়িতে গুলি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই, তো যখন জ্ঞান হল দেখলাম একটা অন্ধকার ঘরে মোম জ্বলছে। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা কিছু লোক, তখনই বুঝি আমি মরে গেছি, নরকে এসেছি। এ এস বললেন— রেস্ট করো, রেস্ট করো সোনা, একসঙ্গে অত কথা বোলো না। তোমরা ওকে কিছু খেতে দাও। স্যুপ, দুধ, হালকা কিছু, সারদা তুমি আনো খাবার, শর্মিলা তুমি ওর কাছে থাকো, বান্টি, বুলা তোমরা বাবাকে ছেড়ে নড়বে না।
আমি বললাম— একজন ডাক্তার তো এখখুনি ডাকা দরকার। যাব?
—ফোনে ডাকছি, ব্যস্ত হয়ো না ভাই, —জগদিন্দ্র অন্য ছেলেটিকে ইশারা করলেন, সে বোধ হয় ফোন করতে চলে গেল। তারপর জগদিন্দ্র ক্রুদ্ধ চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন— পাঁচ কোটি টাকা নিয়ে সোনাকে এই কন্ডিশনে ফিরিয়ে দিয়েছে। হি ইজ অলমোস্ট আউট অফ হিজ মাইন্ড। গুলি করেছে, হাতুড়ে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। লুক অ্যাট হিজ ফিজিক্যাল কন্ডিশান। পা, আই’ল কিল দেম, কিল দেম অল। আই’ল নট স্পেয়ার আ সিঙ্গল ওয়ান।
এ এস বললেন— দিস ইজ আনথিংকেবল, আমার দিকে চেয়ে বললেন, ইয়াং ম্যান, আমরা বহু অ্যাসেটস বিক্রি করে কোনও মতে টাকাটা জোগাড় করেছিলাম। আন্ড দে ট্রিটেড হিম লাইক দিস। আমি ওদের ছেড়ে দেব না। তুমি কী বলো?
আমি যেন হঠাৎ ওঁদের পরামর্শের যোগ্য হয়ে উঠেছি। ওঁদের সমান সমান। বয়সে, অভিজ্ঞতায়, সামাজিক অবস্থানে।
আমি বললাম— নেভার। দে শুড বি ব্রট টু বুক। এক্ষুনি পুলিশে এবং কাগজে খবর দেওয়া উচিত। তবে আপনারা কিন্তু আপনাদের সিকিওরিটি একটুও শিথিল করবেন না। একটু পরে বললাম, এবার আমি যাই?
এ এস হঠাৎ আমার হাত দুটো ধরে বললেন— আরও একটু থাকো, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, উই আর ওল্ড পিপল, খুব হেল্পলেস লাগে, বাবা! আইসোলেটেড, যেন আমাদের কেউ নেই। আমার মনে আছে, তুমি নিজে এগিয়ে এসে আমার স্ত্রীর শেষ যাত্রায়… চোখ মুছতে লাগলেন এ এস।
—আমি বসছি। কী ভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, আমাকে বলবেন। আমি তো এই কাছেই থাকি।
চুপচাপ বসে বসে পারিবারিক মিলন দৃশ্য দেখতে থাকি।
—পা। তুমি আমার কাছে এসো। তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? মা কই? মা! শর্মিলা প্লিজ কিস মি, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি বাড়ি এসেছি। রুণুর সঙ্গে দেখা না হলে আমি খালি এই রাস্তাগুলোয় ঘুরতাম, ঘুরতাম, কিচ্ছু চিনতে পারতাম না, তারপর এক সময়ে পড়ে মরে যেতাম।
জগদিন্দ্রর স্ত্রী দুধ নিয়ে ঢুকলেন।
—সোনা পিয়ে নাও।
—ওহ তুমি? ভাবি তুমি? আমি ভাবিনি আবার তোমাদের দেখতে পাব।
জগদিন্দ্র বললেন— সারদা, দুধে একটু ব্র্যান্ডি মিক্স করে দাও।
দুধটা খেল মহেন্দ্র। তার পর একেবারে নেতিয়ে পড়ল, মহেন্দ্রর স্ত্রী ও বাচ্চাগুলো ককিয়ে কেঁদে উঠল। জগদিন্দ্র বললেন, শর্মিলা— স্টে স্ট্রং, এরকম করলে চলবে না, ডক্টর সেন এক্ষুনি আসছেন।
ডাক্তার এসে যাবার পর আমি চলে এলাম।
পরের দিন জোর খবর। এরা বোধহয় বাতাসের মুখে খবর পায়। এত ডিটেল তো আমিও শুনিনি। মহেন্দ্রর ডান হাতে গুলি লেগেছে, অপটুভাবে অপারেশন করা হয়েছে, মাথার অবস্থা ভাল নয়। মাথায় ভারী কিছু দিয়ে মারা হয়েছে। ভদ্রলোক এমন একটা শক খাওয়া অবস্থায় আছেন যে মাঝে মাঝে হিস্টিরিক হয়ে যাচ্ছেন। দুর্ঘটনার দিন গাড়িতে বসে ওঁর কেমন ঢুল এসেছিল। তারপরেই ড্রাইভার মদনলালের কানের পাশে পিস্তলটা দেখতে পান এবং দুই বাক্সের টিফিন কেরিয়ারটা ছুড়ে মারেন। তারপরেই গাড়ির দরজা খুলে দুষ্কৃতীরা ওঁকে ধরে। উনি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন, তখন ওরা গুলি করে এবং মাথায় আঘাত করে। তিন মাস হয়ে গেছে একটা অন্ধকার ঘর একটা বাতি জ্বলছে এ ছাড়া আর ওঁর কিছু চোখে পড়েনি। ঘরটা মাঝে মাঝে বদলে যেত। কিন্তু একই রকমের অন্ধকার। শেষটায় একটা অসহ্য গরম ঘরে ছিলেন। কালো মুখোশ পরা কয়েকজন লোক যাওয়া-আসা করত, খাবার দিত। ওই রকমই একজন তাঁর হাত থেকে গুলি বার করে। ইদানীং অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে সেখানে। দু’মাসের পরে এ এস একটা ফোন পান। পাঁচ কোটি টাকার দাবি করে কেউ। ওঁরা অনেক দরদস্তুর করেও টাকার অঙ্কটা কমাতে পারেননি। দুর্বৃত্তরা হয় জানত না নয়তো বিশ্বাস করেনি পাঁচ কোটি টাকা মুক্তিপণ দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন ওঁরা নন। ওঁরা ভয়ে পুলিশকে কিছুই বলেননি। কিন্তু পুলিশ তলে-তলে তদন্ত করে চলেছে। অনেক কিছু জানতেও পেরেছে। আপাতত তদন্তের স্বার্থে কিছুই প্রকাশ করা হচ্ছে না। অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ির কাছাকাছি রাস্তায় মহেন্দ্রকে ফেলে ওরা চলে যায়। উনি আকাশ দেখেন। কিন্তু বাড়ি চিনে ফিরতে পারেন না। একটি স্থানীয় ছেলের সাহায্যে বাড়ি পৌঁছন। সময় কতটা কেটেছে, তিন মাস না তিন বছর সে সম্পর্কে ওঁর কোনও ধারণা নেই।
২১
পরদিন বেলা বারোটা নাগাদ মাসিমা অর্থাৎ দীপুর মাকে মহাজন হাউজের দরজার সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল পুলিশ। সত্য খবরটা দিল। মহেন্দ্রর ফ্লাস্কে কফির তলানিতে নাকি অ্যালজোলাম পাওয়া গেছে। মাসিমাই নিজে হাতে দুই ভাইয়ের টিফিন করে দিতেন। ফ্লাস্কে কফি ভরে দিতেন। এগুলো সবই ছিল ওঁর ডিউটি। আমি সোজা দীপুদের বাড়ি চলে গেলাম। মণি কলেজে যায়নি। চুপ করে বসে আছে। বলল— দাদা আর মুক্তা থানায় গেছে। ছোট ভাইকে কোনও খবর দেওয়া হয়নি। কাগজে নামটা দেখে যদি আসে।
মণি আমাকে দেখে বলল— এ সব কী হচ্ছে রুণুদা? কিডন্যাপ, দাঙ্গা…এ সব কী? মা কারও খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিতে পারে তুমি বিশ্বাস করো! —ওর মুখে একটা শক-খাওয়া ভাব, কান্না নেই।
আমি মাথা নাড়ি, তারপর বলি— আমি হাসির সঙ্গে প্রেম করেছি, তাকে লুকিয়ে রেখেছি, এটাই কি তুই বিশ্বাস করিস?
—না—এবার চোখের জল মুছতে মুছতে মণি বলল, আমি সামসুলদা, রমজান চাচা এদের অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম— ওরা বোঝেনি।
—শামু? শামু কিছু বলেনি?
—না, কেমন গুম হয়ে ছিল।
আমি জানি কেন। শামু ভাল করেই জানত হাসির সঙ্গে আমার কিছু নেই। কিন্তু ও বোধহয় ভাবছিল হাসিকে বাঁচাবার জন্যে ও যে আমাকে বারবার রিকোয়েস্ট করছিল, তার ফলে ওকে কোনওভাবে পালাতে এবং লুকিয়ে থাকতে আমি সাহায্য করেছি।
—কী হবে রুণুদা? মাকে…এভাবে…মা একেবারে ভেঙে পড়বে।
—আমি যাচ্ছি, সত্য প্রকাশ পাবেই!
—এখনও… এখনও আশা করো রুণুদা— এখানে সত্যের কোনও স্থান আছে? সত্য প্রকাশ পায়?
—তুই ভাব মণি, তোকে ভাবতে বারণ করছি না। কিন্তু মাথাটা ঠিক রাখ। বিপদে কেউ হাতে পায়ে কাজ করবে, কাউকে শান্ত মাথায় ভাবতে হয়। অন্যদের শান্ত করতে হয়, সেবাও করতে হয়। আমি যাচ্ছি।
—আমাকে একটা খবর দিও।
—কেউ না কেউ আসবেই। হয় আমি, নয় ওরা কেউ।
আমি, মণি, মুক্তা, দীপু, শামু, সত্য, পানু— আমরা সব একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি। নিমকি শিমকি বেঁটেদা— এরাও। হয়তো সামাজিক স্তর বিন্যাসের ভিন্ন পরতে। কিন্তু এক সঙ্গে। আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা মূলত ভাই-বোনের। আমি অন্তত কখনও পাড়ার মেয়েদের দিকে অন্য চোখে তাকাইনি। জানি না এটা অস্বাভাবিক কি না। কিন্তু আমরা যারা জীবনসংগ্রামে এইভাবে সর্বক্ষণ লিপ্ত, তাদের যৌবনের ওই অংশটা জাগেনি, জাগলেও আমরা হয়তো জিতেন্দ্রিয়। হয়তো। তেমন তেমন হলে আমাদের হাত আমাদের শান্ত করে, কারও সঙ্গে ইনভলভ্ড হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারি না। আমরা খালি চেষ্টা করে যাচ্ছি— কীভাবে মানুষের মতো খেয়ে, পরে, চিকিৎসিত হয়ে, প্রিয়জনদের খাইয়ে, পরিয়ে, অসুখে চিকিৎসা করিয়ে একটা সুস্থ সচ্ছল সামাজিক পরিচয় নিয়ে বাঁচব, ও সব চিন্তা আরও অনেক অনেক পরে। আমাদের কাছে এই প্রেমে পড়া, হিড়িক দেওয়া, শারীরিক ভাবে লিপ্ত হবার জন্যে আকুলি-বিকুলি এগুলোই অস্বাভাবিক লাগে। সত্য যখন সাহা বাড়ির শিবানীর প্রেমে পড়ল, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে ইলোপ করল— আমরা যতই বন্ধু হই কেউ তাকে আশ্রয় দিইনি, মদত করিনি। নিজেরা অনর্থক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব এ চিন্তা যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল একটা ধিক্কারবোধ, আত্মসম্মান যেটুকু ভদ্র দরিদ্রের সবে-ধন নীলমণি সেটুকু বিকিয়ে যাওয়ার গ্লানি। ইসস্ সত্যটা এই কীর্তি করতে পারল? ওরা সাত ভাই বোন, ও সবার বড়, বাবা গণাদার দোকানে সেলসম্যান। মা কোনও এক নারীসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সেলাই-বোনা করেন, সত্যর পরের ভাই ব্রত প্রচুর কাঠ-খড় পুড়িয়ে স্রেফ মেধার জোরে ‘টেকনিক্যাল স্কুলে’ পড়ছে, বোনগুলোও সেলাই করে, আচার তৈরি করে মায়ের সঙ্গে, কে সেভেন, কে এইট পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। প্রেম করে ইলোপ-টিলোপ যদি তারা করত তবে ব্যাপারটা বোধগম্য হত। কারণ মেয়েগুলোর তো কোনও জীবন ছিল না। ভবিষ্যৎ ছিল না! বিয়ে ছাড়া শেষ পর্যন্ত যেহেতু মেয়েদের গতি নেই, সেহেতু যেন তেন প্রকারেণ একটা বিয়ের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিলে ওদের দোষ দেওয়া যেত না। কিন্তু ওরা নিয়মিত আচার আর সোয়েটার বানিয়ে যেতে থাকল। আর ওদের সবার বড় দামড়া গো-খোরটা বড়লোকের মেয়ে নিয়ে পালাল। এখন সাহারা সত্যকে অ্যাকসেপ্ট করেছে কিন্তু ওর ফ্যামিলিকে করেনি। সাহাদের মদের ব্যবসায় সত্য যুক্ত আছে কিন্তু শিবানী একবারের বেশি কখনও শ্বশুরবাড়ি যায়নি, সত্য কিছু সাহায্য ওঁদের করতে পারে কি না, করে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
আমি যে এতদিন ধরে মণিকে পড়াচ্ছি— প্রেম হতে পারত তো! টিউটর আর ছাত্রী। দু’জনেরই অল্প বয়স। একেবারে টিপিক্যাল কেস! কিন্তু কই, হয়নি তো! মণিটা ওর ফিজিক্স-কেমিস্ট্রিতে চুবে থাকত। ইংরেজিটা আমাকে দেখাত নিয়মিত। তখন রেগুলার বকুনি খেত— তুই আবার বিগিনিং বানান ভুল করেছিস? বলেছি না ‘বাই’ আর ‘উইথ’-এর ব্যবহারে তফাত আছে! কথাটা ইনডিসক্রিমিনেটলি, ‘ন্যান্টলি’ নয়। বাংলা চিরকালই ও খুব ভাল জানত। ও বরং আমাকে জ্ঞান দিত। —রুণুদা প্লিজ ‘সাথে’টা বোলো না, স্ট্যান্ডার্ড বাংলাতে ‘সঙ্গে’টাই অ্যাকসেপ্টেড। সারা রবীন্দ্রনাথ খুঁজে দেখো কোথাও গদ্যে ‘সাথে’র ব্যবহার নেই। গানে, কবিতায় প্রচুর আছে। কিন্তু কোনও ভাল বাংলা গদ্যে সে তুমি রবীন্দ্রনাথই বলো, আর বুদ্ধদেব বসুই বলো—‘সাথে’ পাবে না। বুদ্ধদেব তো পুরো বাঙাল ছিলেন, ছিলেন না?
আমি যদি বলতাম আর তোদের গেলুম, খেলুম, হালুম হুলুম, নেবু, নঙ্কা, নুচি…?
—শুধু শুধু ভাষা নিয়ে ঝগড়া কোরো না রুণুদা, গেলুম-খেলুম রবীন্দ্রনাথও লিখে গেছেন। উনিই আমাদের ফাইন্যাল রেফারেন্স। কিন্তু তা সত্ত্বেও গেলাম, খেলামটাই এখন স্ট্যান্ডার্ড বলে মানা হয়, আমার বাবা পর্যন্ত নুচি বলতেন, আমার দিদিমাকে ‘আঁব’ বলতে শুনেছি ‘আম’কে। কিন্তু আমরা আর বলি কি? একটা আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই স্ট্যান্ডার্ড বাংলা তৈরি হয়ে উঠেছে।
থানার পথ ধরি। দেখি শামু আসছে। কথা বলতে সত্যি বলতে কী আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শামুই বলল— দীপুর মায়ের খবরটা শুনেছিস তো!
—হ্যাঁ, যাচ্ছি তো!
—আমি ওর জামিনের ব্যবস্থা করেছি। জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেবে।
—তুমি! জামিন?
—কেন, আমি বন্ধুর মায়ের জন্য এটুকু করতে পারি না?
—কী জানি! কী পারো আর কতটুকু পারো। —আমি উদাস ভাবে রাগ লুকিয়ে, যথাসম্ভব রাগটাকে সামান্য অভিমানের চেহারা দিয়ে বলি— তা কেসটা কী? ওঁকে অ্যাট অল ধরেছে কেন?
—ড্রাইভার মদনলাল সাক্ষ্য দিয়েছে, ছোটসাহেব গাড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, ও কোনওদিন কোনও সাহেবকেই এ ভাবে ঘুমোতে দেখেনি। ফ্লাস্কে কফি তখনও একটু পড়ে ছিল। ওরা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে ঘুমের ওষুধ পেয়েছে। এতদিন ছোট মহাজন ফেরেননি বলে ওরা ওয়েট করছিল। এক মাস আগে মুক্তিপণের টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। অথচ ছোট মহাজন ফিরছিলেন না। খুব ওয়ারিড ছিল পুলিশ। ফেরা মাত্র অ্যাকশন নিতে শুরু করেছে।
—বলো কী? এক মাস আগে টাকা দেওয়া হয়ে গেছে! মহাজনদের তো নরকযন্ত্রণায় কেটেছে! ফেরত দিলই যদি তো আরও আগে দিল না কেন? পাঁচ কোটি র্যানসম কি চালাকি কথা!
—বোধহয় ফিজিক্যাল কন্ডিশান অত খারাপ ছিল বলে দেয়নি। বাঁচবে কি না বাঁচবে!
—না বাঁচলে কি ওরা মুক্তিপণের টাকাটা ফেরত দিত?
—দিত হয়তো, ওদেরও একটা এথিক্স্ আছে।
—তা ভাল, তুমি ভাল জানবে।
—কেন? এ কথা কেন বললে? শামু অদ্ভুতভাবে মারমুখো হয়ে বলল।
—তোমার চেয়ে ভাল করে একথা কেউ জানে না শামু! নিজে সত্য জেনেও বন্ধুর ওপর হামলা যে রুখতে পারে না, চায় না, এথিকস-টেথিকস তো তারই জানবার কথা!
—আরে ছোড়ো ইয়ার। গুসসা মৎ হোনা। হয়ে গেছে ঝোঁকের মাথায় একটা অন্যায়। আমি কী করতুম বলো? যদি কিছু বলতে যেতুম ওই হারামি কামিনা রমজান আমাকে ছাড়ত না কি! —যাই হোক, হাসিটা যেখানেই থাক, মনে হচ্ছে ভালই আছে। বেশ ভেবেচিন্তে কাজটা করেছে। ও যদি একটা ভাল ছেলেকে শাদি করে নিয়ে থাকে— তাতেও আমার আপত্তি নেই। ভাবতে পারিস রমজান আলির দোসরা বিবি জাহানারা চাচি, চাচার ছেলে বিইয়ে বিইয়ে শয্যা নিয়েছে। এখন ফ্রেশ মেয়ে খুঁজছে, নিজের মেয়ের বয়সি। আর আমরা —উঃ!
—ভাল, তোমরা কী? ক্রীতদাস— হাসিনা লিখেছিল, —কেন?
—আরে তোকে বলতে বাধা কী? অনেক টাকা ওর কাছে আমাদের ধার-দেনা রয়েছে। শুধতে পাচ্ছি না কিছুতেই। মাকে এসে বললে— হাসিকে দিন, নইলে আমার বাল-বাচ্চাগুলো কে মানুষ করবে, হাসিকে আমি নবাবের বেগমের হালে রাখব। মা-ও রাজি হয়ে গেল। টাকার জন্যে রমজান চাচা জাহানারা চাচি দু’জনের কাছ থেকেই তো গাল খেতে হত মাকে! দু’বেলা!
—এ কথা একবারও মনে হল না, এই ভুল বোঝাবুঝি থেকে একটা মারদাঙ্গা লাগল। এতগুলো মানুষ মারা গেল, বাচ্চাগুলো অনাথ হল! মনে হল না?
—ইয়াকিন কারো ইয়ার বোমাগুলো কে টপকালে, আমি জানি না।
—বোমা তো তোরাই বাঁধিস। তুই আর গদা। তোদের গুদোম ঘরে এত বোমা জমা আছে শামু যে কোনওদিন একটা আগুনের ফুলকি পড়লে গোটা পাড়াটা উড়ে যাবে।
—আরে মহা মুশকিল তো! চল, এক্ষুনি চল আমার বাড়ি। কোথায় বোমার গুদাম, চল নিজের চোখে দেখে আসবি।
—আমার সাধ্য কী সে-সব বার করি। —বলে আমি মুখ ফিরিয়ে নিই।
মাসিমা জামিনে ছাড়া পেলেন কিন্তু মহাজনদের বাড়ির কাজটা ওঁর গেল। লজ্জায় উনি যেতেই চাইছিলেন না। আমরা বোঝালাম না গেলেই ওঁকে ওঁরা অপরাধী ভাববেন। সাহস করে উনি শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু এ এস বলেছেন ওঁকে আর তাঁদের দরকার নেই।
ঠিক আছে— লেট ল’ টেক ইটস কোর্স।
দীপুরা, এবং আমরাও বৃহত্তর পাড়াতে খানিকটা একঘরে হয়ে রয়েছি। বদনাম একবার রটলে, গায়ে আলকাতরা লাগার মতো, চিটে আর উঠতে চায় না। মানুষকে জনা জনা ধরে কত বোঝানো যায়। আর বোঝাবই-বা কেন? বিশুদা সুদ্ধু একদিন ডেকে বললেন— কাজটা তুই ভাল করিসনি রুণু। বিচক্ষণতা দেখাতে পারিসনি।
—যা আমি করিনি, তার জন্যে কৈফিয়ত দিতে আমি আর পারব না বিশুদা।
—তোর আজকাল খুব তেল হয়েছে।
—বিনা দোষে এভাবে অপমান করলেও জবাব দেব না?
—বিনয় শেখ, তা নয়তো ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
—বিনয় অর নো বিনয়, ভবিষ্যতে বালব জ্বলার চান্স দেখতে পাচ্ছি না।
জগাদা একদিন রাস্তায় ধরল— কী রে রুণু, আজকাল খুব মস্তান হয়েছিস।
আমি খুব শান্তভাবে বলি— তোমার চেয়েও?
—আমি? তোর তো আস্পদ্দা কম নয়। মস্তানি রুখতে আমি প্রাণটা ছাড়া এখনও পর্যন্ত সবই দিয়েছি, তা জানিস?
আমি বললাম— ও ছার প্রাণ গেলেই বা কী! থাকলেই বা কী।
—তুত্তুই এ কথা বললি? বলতে পারলি? জগাদার সরু মুখটা আরও লম্বা হয়ে গেছে। চোখ দুটো বড় বড়।
—ও সব ছাড়ো। আটকালে কেন? পড়াতে যাচ্ছি!
—ওই মেয়ে-ফুসলোনো, দাঙ্গাবাজির পরেও তোর টুইশানগুলো আছে?
—আমি আর মেয়ে-ফুসলোনোর মতো হিরোইক কাজ করতে পারলাম কোথায়? তুমি চেষ্টা করলে পারতে কারণ, বাড়িক্কে একটা গোটা বাড়ি ফুসলোনোর অভিজ্ঞতা তোমার আছে!
—মানে? তুত্তুই বলতে পারছিস এ কথা? কর্পোরেশনের নিয়ম ভাঙলে ইস্টেপ নেব না?
—নিশ্চয় নেবে, এ এলাকার কাউন্সিলর-এর টিকিটটা পেতে হলে তো তোমাকে কাজটুকু দেখাতেই হবে। তবে তোমার আই কিউ যা তাতে করে চাকলাদার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে না দিলে— টিকিটটা বোধহয় আর পাওয়া হয়ে উঠত না।
মুখটা ছাইয়ের মতো হয়ে গেল জগাদার। বললে— চাকলাদার বলেছে তোকে? মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর…
—রাজনীতি করতে গেলে তোমাকে এর চেয়ে সংযত হতে হবে জগাদা। আই কিউ না হলেও চলে কিন্তু আর কিউ মানে রি-অ্যাকশন কোশেন্টটা ঠিকঠাকমতো থাকা দরকার। চলি…
প্রায় মাথার চুল খামচানো অবস্থায় জগা মিত্তিরকে পেছনে রেখে আমি এগিয়ে চলি, টুম্পাদের বাড়ির দিকে। টুম্পা-তুলতুলদের ট্যুইশানটা কোনও অজ্ঞাত কারণে বাতিল হয়নি। ছেলেমেয়ে দুটির বাবা আজকাল প্রায়ই পড়ার ঘরে এসে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। মাঝে মাঝে ছেলের দিকে এমন কটমট করে তাকান যে আমারই হৃৎকম্প হয়।
অরবিন্দদা বললে— ব্রেভ ইয়াং ম্যান তোর গাট্স্ আছে। ওয়েল-ডান।
—কোনটা!
—ওই বৃদ্ধস্য তরুণী ও তৃতীয়া ভার্যার ব্যাপারটা বন্ধ করা!
আমার এত রাগ হয়ে যায় যে আর কিউটা আমারই গণ্ডগোল হয়ে যায়। ঠাণ্ডা স্বরে বলি— ব্রেভ ওল্ড ম্যান, তোমারও গাট্স্ আছে। ওয়েল ডান!
—মানে?
—মানে তুমিই ভাল জানো। রাদার তুমি-ও…আচ্ছা চলি।
পেছনে দুটো চোখ থাকলে দেখতে পেতাম কী ধরনের আর কিউ ও মুখে খেলা করছে। তবে এমন মাংস মুখে যে কোনও ভাবের খেলাই চট করে দেখা যায় না।
আর নিতাই ভটচায? এরা যদি চলে ডালে ডালে সে চলে পাতায় পাতায়। তিনটে সেক্রেটারির একটাকে দিয়ে ডেকে পাঠাল। খাস কামরায় তলব হল। উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল নিতাই ভটচায। খাস বিলিতি কায়দায় একেবারে। তারপরে বলল— কংগ্র্যাচুলেশনস।
—কীসের জন্যে?
—কীসের জন্যে? তোর বিনয় দেখলে তোর বাবার কথা মনে পড়ে যায় রুণু। অজিতদাও এমনি ছিলেন।
আমি চুপ করে থাকি।
—নেতারা তো শুধু একটা ছকে কাজ করে যায়। এত মিটিং, সেশন, এত জনসংযোগ করতে হয় যে প্রাণ একেবারে কণ্ঠাগত। একটু সময় বার করতে পারি না আমরা যে সোসাইটির কথা একটু আলাদা করে ভাবব। সে-দিক থেকে দেখতে গেলে সমাজ সংস্কারকরাই আসল। সোসাইটির মধ্যে থেকে, তলা থেকে তাকে বদলায়, চেষ্টা করে অন্তত, সাফল্য হয়তো সেই মুহূর্তেই আসবে না, কিন্তু ইন দা লং রান আসতে বাধ্য। হয়তো সেটা দেখতে আমরা থাকব না। কিন্তু তোর অল্প বয়স। তুই দেখে যাবি।
আমি চুপ করে থাকি। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় দেখি।
—এই যে পতিতদার পেনশনটা করে দিলি, এটা দুর্দান্ত কাজ।
আমি বলি— আমি করিনি, তোমার জ্ঞাতিশত্রু বিশু মল্লিক করেছে কাজটা।
—ধুর ও কী করবে! তুই যে বার বার গেলি, ইয়াং ম্যান দেখলে ঘুষখোরগুলো ভয় পেয়ে যায়। এখন তো সব জায়গাতেই ওদের রাজত্ব! কোটি কোটি টাকা… কোটি কোটি টাকা এক শিক্ষাবিভাগ থেকেই হাপিস করে দিলে রে! পুরো দেশটা লুঠেরাদের হাতে চলে গেল। সে যাক, দাঙ্গা একটা বাধল তোকে উপলক্ষ করে। ডোন্ট মাইন্ড রুণু, শামুর বোনটাকে তুই অজ্ঞাতবাসে সাহায্য করেছিস, করছিস কি না জানি না। আমি অত কানপাতলা নই। যদি না করে থাকিস ভাল, করে থাকলে আরও ভাল। কিন্তু দাঙ্গাটা থামালি, দাঙ্গার ভিকটিমদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিস। বেঁটে তোর কথা খুব বলছিল। আলম বলে ছোকরা সেও দেখলাম তোর গুণ গাইছে। বললে— রুণুবাবুকে যে না-পাক ভাববে সে নিজে না-পাক। …আমি তোর ব্যাপারটা দেখছি। ইউ শুড বি প্লেসড সামহোয়্যার যেখানে তুই প্রপারলি ইউটিলাইজড হবি। ও হ্যাঁ এ এস মহাজন অ্যান্ড ফ্যামিলি তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ একেবারে। সত্যিকারের হৃদয়বান ছেলে… ওকে দেখলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর ভরসা হয়।
আমি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলাম। দীর্ঘ জ্বালাময়ী শেষ হলে জিজ্ঞেস করি—‘হৃদয়বান’ ‘ভবিষ্যৎ প্রজন্ম’ কথাগুলো কি ওঁরাই ব্যবহার করলেন?
—তা কি আমি করলাম?
—না, ওঁরা এতটা ভাল বাংলা জানেন— বলেন জানতাম না। সব সময়েই ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলেন দেখি।
—য়ু আর রাইট। আমি নিজের অজান্তেই ওঁদের কথাগুলো ট্রানস্লেট করে নিয়েছি। বুঝলি?
বুঝলাম, এবার উঠি নিতাইকাকা! ট্যুইশন আছে তো!
—এই যে, পড়িয়ে শুনিয়ে ছেলে-মেয়েগুলোকে মানুষ করে তোলার ব্রত নিয়েছিস, এটাই কি কম মহৎ? পশ্চিমবাংলায় তো স্কুল-কলেজ সব উচ্ছন্নে গেছে। পরিকল্পিতভাবে পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এরা।
—ব্রত ট্ৰত নয় নিতাইকাকা, তুমি ভুল করছ— আমি বলি— না করলে বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না। তাই করতে বাধ্য হচ্ছি। নইলে কে শালার পাথর ঘষে ঘষে গর্ত করবার চেষ্টা করে!
আমি বুঝতে পারছি একটা বিপজ্জনক ব্যাপার ঘটছে। আমার সেই কালো পাথরের দেয়াল! সেই সীমার দেয়াল? তাতে একটা চিড় ধরেছে। ঠিক বিদ্যুতের রেখা আকাশে যেমন আঁকাবাঁকা আলোর আঁকি-বুকি কেটে দেয় তেমনই।
২২
বাড়িতে বোধহয় গুম মেরে থাকি। আমি অতটা বুঝতে পারি না। কিন্তু সবাই যেন আমাকে একটু সমঝে চলছে। রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরলেও গরম ভাত পাচ্ছি। মা বসে থাকছে। রিন্টিটা কাছে ঘেঁষছে না, সচিনের পোস্টারের আবদার ধরছে না, দাদা বাড়ি ফিরে জিজ্ঞেস করছে— রুণু ফিরেছে? খেয়েছে? অফিস বেরোবার সময়ে একটু উঁকি দিয়ে যায় —রুণু। বেরোচ্ছি, বুঝলি? কিংবা, কী রে উঠেছিস? —একেবারেই এলেবেলে কথাবার্তা। কোনও মানে নেই। আছে, কথায় নেই, কথা বলার চেষ্টায় আছে। মনোযোগ, একটু অতিরিক্ত। যেন কেজো সম্পর্কটার ওপরে যাওয়ার চেষ্টা। দাদা চিরকাল আমার অবস্থাটা বুঝেছে। আমি যে বসে নেই, প্রাণপণে চাকরির চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিছুতেই পাচ্ছি না, কিন্তু ফাঁকটা অজস্র ট্যুইশনি দিয়ে ভরাচ্ছি, দাদার ঘাড়ে চেপে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবার কোনও ইচ্ছেই যে আমার নেই এটুকু আমি দাদাকে বোঝাতে পেরেছি। বেকার ভাই নিয়ে মানুষের যে একটা সামাজিক লজ্জা থাকে সেটাও সম্ভবত দাদার নেই। কেন না, আমরা সামাজিক ভাবে যাদের স্টেটাস থাকে, সে গোত্রের তো নই! আমার কোনও চাহিদা নেই, নিজেরটা নিজে চালিয়ে নিই, সংসারের যাবতীয় গাধার খাটনিগুলো খাটি। আর বউদি? সত্যিই মনে হয়, অনেক ভাগ্য করলে কারও সংসারে এ রকম বউ আসে। আমাদের তো আর কোনও ভাগ্যই নেই। এই বউদি-বউমা ভাগ্যটা আছে। বউদি সারাক্ষণ ছুতো করে করে আমাকে কথায় টানবার চেষ্টা করে। আমি কেন গম্ভীর, কী ভাবছি!
—রুণু। রিন্টির অঙ্কের খাতাটা একটু দেখো না, কী যে ভজঘট ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে আমি বুঝতে পারছি না।
—আমি পারব না।
—বাঃ তুমি তো রেগুলার পড়াচ্ছ।
—অত ছোট ছেলে আমি পড়াই না, তা ছাড়া ওসব সাহেবি-স্কুলের কায়দা বোঝার মতো মগজ আমার নেই।
—সব সময়ে স্কুল নিয়ে অত খোঁটা দাও কেন বলো তো?
—খোঁটা দিইনি। সত্যি কথাটা বলেছি— দেয়ালে লম্বিত আয়নায় আমি প্রাণপণে চুল আঁচড়াতে থাকি। ভীষণ কাজ যেন আমার। একটা ইমপর্ট্যান্ট মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হবে যেন।
সত্য, পানু, অমল, কমল কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলি না। —ওই ‘কেমন আছ?’ ‘এই চলে যাচ্ছে ভাই,’ জাতীয়। বাস। কিন্তু দীপুর বাড়িতে আমি এখন নিয়মিত যাই। মাসিমার চাকরি গেছে, মাথার ওপর ঘুমপাড়ানি প্রয়োগের অ্যালিগেশন ঝুলছে। রোজগার, সম্মান, বিশ্বাসযোগ্যতা সব এক ধাক্কায় নেমে গেছে। মণি সাধ্যের অতিরিক্ত ট্যুইশন করছে, মুক্তার অবশ্য মাইনে বেড়েছে। কিন্তু ছেলে তিনটে? সেই আছে না? একটা পাগল একটা গোঁয়ার! আর বড়জন তো হারাধনের প্রথম ছেলে। কবেই ‘একটি কোথা হারিয়ে গেল’ হয়ে গেছে।
একটাই তো ঘর। সন্ধেবেলার ট্যুইশন যাবার আগে বসে থাকি গিয়ে। মাসিমার ভাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন কষ্ট হয়।
—ব্যাপারটা কী বলো তো? —উনি বিহ্বল হয়ে বলেন।
—আপনি তো গদার বাড়ি বেশ ছিলেন। মহাজনদের বাড়ি যেতে গেলেন কেন?
—গদাই তো আমায় বিজ্ঞাপনটা দেখায়, ডবল মাইনে। মাসিমা আপনি যান। আমরা চাই আপনি ভাল থাকুন। তা দেখ কী থেকে কী হয়ে গেল।
—কেউ আপনাকে ফ্রেম করেছে। কিন্তু কেন? কীভাবে? ফ্লাস্কটা আপনি কার হাতে দিতেন?
—একটা পিকনিক বাক্স মতো আছে ওদের। একটা খোপে ছোট ফ্লাস্ক। একটাতে টিফিন বক্স, একটাতে কাঁটাচামচ এইরকম ভাগ ভাগ করা। তাইতে ভরে দিতাম। মদনলাল, কিংবা বাড়ির কাজের লোকেরা কেউ— তারক, নওরতন, কি ফুলি তুলে দিয়ে আসত।
—তখন মহেন্দ্রদা কোথায়?
—গাড়িতে বসে থাকতেন। উনি বসলে তবে খাবার, ব্রিফকেস সব যেত।
—সেই বিশেষ দিনে, কে নিয়ে গিয়েছিল বাক্সটা মনে করতে পারেন?
—ভাবতে হবে।
—ভেবে রাখুন। কোর্টে কেস উঠলে কাজে লাগবে।
মাসিমা কেঁপে উঠলেন।
অসম সাহসী মহিলা, স্বামী মারা যাওয়ার পর, বড় ছেলে দায় এড়িয়ে পালিয়ে যাবার পর সংসারের সমস্ত ভার, চার ছেলেমেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিতে এবং সে-জন্য রাঁধুনিগিরি করতে পর্যন্ত পিছপা হননি। তিনি সাহস আশা হারিয়ে ফেলছেন, অথচ তাঁর কাছে ছেলেরা কেউ একটু ভরসা দেবার জন্যও মজুত নেই। মেয়ে দুটোই শুধু অক্লান্ত খেটে যায়।
আমার এক এক সময়ে মনে হয় দীপে শালাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিই।
বাড়ির লোকেদের ওপর, পাড়ার লোকেদের ওপর যে আমার খুব একটা রাগ হয়েছে তা কিন্তু মোটেই নয়। আসলে মাথার মধ্যে সর্বক্ষণ একটা ঘুরঘুরে পোকা ঘুরঘুর করে ঘুরতে থাকে। পোকাটা মগজের মধ্যে কিছু একটা কেটে চলেছে— ধৈর্য, সহনশীলতা, রসবোধ, একটা ‘ঠিক আছে, হয়ে যাবে’ গোছের ভাব। ‘হয়েছে, হয়ে গেছে,— ঝেড়ে ফেলে দাও— সামনের দিকে তাকাও, নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবো’ গোছের নিজেকে নিজে দেওয়া উপদেশ যাকে বলা যায় অটো-সাজেশন, যার বলে আমরা নৈরাশ্য, শোক, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি কাটিয়ে উঠি। ফলে, আমি আর ঠিক আমাতে নেই। আর সবাই আমাকে ঠিক চিনতে পারছে না বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আলকাতরায় স্টোন চিপস-এর মতো, আমি আটকে আছি দাঙ্গাটায়, মহেন্দ্র মহাজনে, মাসিমার গ্রেপ্তারে। কিছুতেই ভুলতে পারছি না আমার দেড়তলার ঘর থেকে দেখা শোনা সেই জনতার ক্রুদ্ধ গর্জন, সেই অপমান— ‘এই কে আছিস, মেয়েছেলেটাকে সামনে থেকে সরিয়ে দে তো!’ অপমান মানুষকে কেমন ছোট করে দেয়। যে বউদিকে বন্ধু বলে দিদি বলে, একজন অত্যন্ত সহৃদয় বুদ্ধিমতী নারী বলে আমাদের পুরো সংসারটা প্রায় একটা উচ্চ বেদিতে বসিয়েছে, মা তার দোষ দেখতে পান না, দাদা তাকে পরম নিশ্চিন্তি এবং ভরসা জ্ঞান করে, আমি তাকে একটা ‘ওয়ান্ডার’ বলে মনে করি, যদিও কক্ষনও ঘুণাক্ষরেও সেটা জানতে দিই না, সেই বউদিকে এককোপে যেন লোকটা তার সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে গেল। বউদিকে যখনই দেখি— ‘মেয়েছেলেটা’ এই কথাটা আমার মাথার মধ্যে বোলতার মতো বোঁ-ও-ও করে ঘোরে। এই মেয়েটির, এই মানুষটির একটা অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করার মতো ‘মেয়েছেলেটা’ দিকও আছে! বউদির ওপরও কেমন একটা বিরাগ-বিতৃষ্ণা হয়। এর কী সাইকলজি আমি জানি না। মনে হয়, ওহ্ যেটাকে তোমার বুদ্ধি, তোমার সপ্রতিভতা, মাধুর্য, ব্যক্তিত্ব বলে জেনেছিলাম, সেটা তা হলে খুব ঠুনকো জিনিস। আমাদের ভুলিয়ে রেখেছিলে। কিন্তু ওই দুর্বৃত্তটাকে ভোলাতে পারোনি। ও ঠিক দেখতে পেয়েছিল, চিনতে পেরেছিল! ‘মেয়েছেলে’ ‘মেয়েছেলে’ আমার মগজটা চিৎকার করে, মাথায় খুন চেপে যায়, মনে হয় আর কাউকে না পারি নিজেকেই নিজে গলা টিপে শেষ করে দিই। বউদির মুখের দিকেও আমি তাকাতে পারি না। যেন কেউ তার কাপড় খুলে নিয়ে গেছে। আমি বউদির সমস্ত আসা-যাওয়া কাজ-কর্মের মধ্যে একটা অনুক্ত ধিক্কার শুনতে পাই। —ছিঃ রুণু, লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দিতে পারলে না? পারলে না, না দিলে না? কারণ তোমার মনের ভেতরেও ওই ‘মেয়েছেলে’— ঘৃণাটা তুচ্ছ জ্ঞান করাটা আছে? কী জানি, বউদি হয়তো এসব কখনওই ভাবে না। কিন্তু আমি ভাবি, এবং ভাবি বউদি ভাবছে। আর অক্ষম ক্রোধে আমার সামনের কালো পাথরের দেয়ালটার ওপর ঘুষি মারি, ঘুষি মারি— ভাঙ শালা, ভাঙ শালা, ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ।
কাগজে বেরিয়েছে— পুলিশ না কি আরও অনেক ক্লু পেয়েছে। জাল এবার গুটোবে ধীরে ধীরে। মহাজনদের পাঁচ কোটি টাকা হাওয়ালা মারফত দুবাই, আবুধাবি চলে গেছে।
রবিবার, জাস্ট এলোমেলো ঘুরতে বেরিয়েছি। উল্টো দিক থেকে দেখি অরুণ হনহন করে আসছে— মুখের মধ্যে একটা ভয় খাওয়া ভাব, কে যেন ওকে তাড়া করেছে, কোনও ভয়াল ভীষণ। অরুণ পতিতকাকার ছেলে, বাঙ্গালোরে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ও যে এসেছে তা-ই আমি জানতাম না। বলতে যাচ্ছিলাম কী রে অরু, কবে… অরুণ যেন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। —‘রুণুদা, একটা ডাক্তার, ডাক্তার বলতে পারো, রোববার… কাউকে পাচ্ছি না, সকাল থেকে বাবার শরীরটা বড্ড খারাপ। বোধহয়…’ বলতে বলতে অরুণের স্বর কেঁপে যাচ্ছে, গলা ধরে যাচ্ছে। সর্বনাশ, কাকে ডাকি? ছুটে যাই গণাদার দোকানে, ওখানে কে যেন বসেন। গণাদা বলল— দূর, আজ রোববার কখনও ডাক্তার পাস? ওষুধের দোকানই খোলা পাবি না, আমিই একা খোলা রাখি।
ও রোববার বুঝি মানুষের অসুখের ছুটি? আমি কড়া গলায় বলি।
গণাদা বলে, আরে ডাক্তারেরও তো শরীর-স্বাস্থ্য আছে, না কি?…
—সব্বাইকে একই দিনে শরীর-স্বাস্থ্য চর্চা করতে হবে? সব ডাক্তারকে? সব ওষুধের দোকানদের?
—আমাকে ঝাড়ছিস কেন ভাই, আমি তো খোলা রেখেছি। খোলা রাখি। তা কী হয়েছে পতিতকা’র? সিমটমটা কী?
—নিশ্বাসের কষ্ট। বাবার তো হাঁপানি আছেই!
আমি গণাদার দিকে তাকাই। বলি— অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে?
—আছে।
—তবে দাও, মানে নিয়ে এসো। আমি তো ফিট করতে জানি না। কুইক গণাদা।
দোকানটা, দোকানটায় সবে ধূপ দিয়েছি। এখনও খোকা আসেনি।
—চুলোয় যাক তোমার দোকান, তুমি আসবে কি না বলো!
আমার মুখের চেহারা দেখে গণাদা অক্সিজেন সিলিন্ডারটা বার করে আমাদের দিল। বলল এগিয়ে যা, আমি শাটার ফেলে আসছি।
পতিতকাকা পেনশন ভোগ করলেন তার মানে কাঁটায় কাঁটায় একমাস। চার হাজার তিনশো সাত টাকা। হার্টের ট্রাবল হয়েছিল, কাকিমাকে পর্যন্ত বলেননি, প্রাণপণে টুইশানি করে ছেলের পড়ার খরচ আর নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনটুকু জোগাড় করছিলেন। কাছা গলায় ঘুরছে অরুণ। আমাকে বলল— বাবার এরিয়ার দিয়ে আমার পড়া শেষ হবে রুণুদা, আমি ভাল চাকরি পাব, …তখন বাবা…বাবাটা… রুণুদা আমি বাঙ্গালোর যেতে চাইনি। বলেছিলাম আমি সাধারণ ছেলে বাবা, জয়েন্ট পাইনি, সেটাই মেনে নাও। আমাদের মতো…আমরা কে কবে লাখপতি এনজিনিয়ার হয়েছি বাবা, ছাড়ো। বাবা কিছুতেই শুনলে না। বললে আমার তিনটে সন্তান চলে গিয়ে তুই রয়েছিস। আমার জীবন যেমন হয়েছে হয়েছে, তোকে— তোকে আমি যতদূর পারি ওপরে তুলে দেব। যদি… যদি রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটগুলো ঠিক সময়ে পেত… উদয়াস্ত খাটুনি। বাবা নিজের ট্রিটমেন্ট করাল না, এখন দেখছি, ডাক্তার সেনের প্রেসক্রিপশন রয়েছে ইসিজি করাতে লিখেছেন, আরও কী কী সব, হল্টার কার্ডিওগ্রাম, ট্রেডমিল টেস্ট, বাবা কিচ্ছু করায়নি।
আমি বললাম— তোর শ্রাদ্ধের চিঠি আমাকে দুটো এক্সট্রা দে তো!
—নাও না, কাকে বলতে হবে, বলো। বাবার কাজ আমি ঘটা করে করব।
—কেন? ভূতভোজন করাবি কেন? আমার ভুরু কুঁচকে যায়।
আমার দিকে অবাক চোখে তাকায় অরু—ভূত?
—হ্যাঁ নানা কিসিমের ভূত। ধর মামদো ভূত, গো ভূত, প্রেত ভূত… খবর্দার ভোজন-টোজন করিয়ে কাকার কষ্টের টাকাগুলো নয়ছয় করবি না। ওগুলো তোর পড়াশুনো, কাকিমার চিকিৎসা, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া এসবের জন্যে। ভক্তি করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কর, মিষ্টি ফিষ্টি খাইয়ে দিবি, একটা রসগোল্লা এক গ্লাস মিনারেল ওয়াটার। ব্যাস। একদম ফুলস্টপ। আর অরু, সারা জীবন মনে রাখবি কাকা তোর জন্যে কী করেছেন। কাকার আত্মা তাতেই তৃপ্ত হবে। ভূতভোজনের চেয়ে এটাই ইমপর্ট্যান্ট।
—লোকে কী বলবে রুণুদা?
—ও, আমাদের জেনারেশনের ছেলে তুই, এখনও লোকে কী বলবে ভেবে কাজ করিস! কোন হারামজাদা কবে এসে তোর বাবার পাশে দাঁড়িয়েছিল?
—তুমি তো দাঁড়িয়েছিলে, বিশুদা, শামুদা…
—তা হলে সাহস থাকে তো, শুধু এই তিনজনকে চিঠি দে!
—কী যে বলো রুণুদা!
—শোন অরু, তুই যদি সেই বেম্মো ভোজন, নিয়মভঙ্গের এলাহি ঘটাপটার বন্দোবস্ত করে থাকিস, তা হলে আমার চিঠিটা তুই রেখে দে। আমি যাব না। অ্যান্ড আই’ল কার্স ইউ অ্যাজ এ কাওয়ার্ড, একটা কাওয়ার্ড যে বাবার কষ্টের টাকাগুলো স্রেফ ‘সুপুত্তুর’ সুনামের জন্যে ফুঁকে দিচ্ছে। আমাকে ক্ষমা কর।
অরু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল— তুমি ঠিকই বলেছ। এক্কেবারে ঠিক। আমার নিজের যদি টাকা থাকত, সে আলাদা কথা। কিন্তু এর একটা পয়সা তো আমার নয়! সব বাবার না ভোগ করতে পাওয়া টাকা। শ্রাদ্ধ আমি ভালভাবেই করব। কিন্তু ও সব বাদ। মাকে একটু বোঝাতে হবে। মা এখন শোকার্ত। নানান ইমোশন… সেন্টিমেন্ট…।
—মাকে বল এফ ডিগুলো ভাঙানো যাচ্ছে না। বল আর দেনা করলে ডুবে যাবি। তোরও বাবা মতো অবস্থা হবে। ভাল ডোজ দে কাকিমাকে, নইলে মেয়েদের এইসব ইমপালসিভ, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে সেন্টিমেন্টে চলবার অভ্যেস বন্ধ করতে পারবি না। আর শোন, পারিস যদি দুটো শ্রাদ্ধের চিঠি নিয়ে আমার সঙ্গে চল।
—কাল গেলে হবে?
—ঠিক আছে।
—কোথায়? কাকে রুণুদা?
—সে তুই চিনবি না। চলই না।
কাছা গলায় — অপ্রত্যাশিত শোকের ধাক্কায় ধ্বস্ত ছেলেটাকে টেনে নিয়ে যাই হুগলি ডি-আই অফিসে। প্রথমেই কেষ্টা, সেই কেষ্টা ব্যাটাই চোর।
আমাকে দেখে চমকে বললে—আবার এসেছ? আবার কী? হাটো হাটো।
আমি অরুকে এগিয়ে দিয়ে বলি—এবার আলাদা কেস, ঘোষদা। নেমন্তন্ন। দয়া করে পায়ের ধুলো দিলে মৃতের আত্মার বড্ড শান্তি হবে।
—ঘোষ লিখেছ কেন? কৃষ্ণপদ ব্যানার্জি।
আমি বলি—ওই হল, ঘোষও যা ব্যানার্জিও তা। কৃষ্ণপদ ঘুষ কি লেখা যায়?
—তুমি তুত্তুমি … আস্পদ্দা তো কম না …
—রিল্যাক্স দাদা, রিল্যাক্স, চিঠিটা কার ছেরাদ্দের, পড়বেন না?
রাগি হাতে চিঠিটা খুলল কেষ্টপদ। খানিকটা পড়ে ব্ল্যাংক চোখে আমার দিকে তাকাল।
আমি বললাম—ধরে নিন, আপনার ছেলে, আপনার ছেরাদ্দের চিঠিটা আপনাকে মানে যার কুচুটে চোট্টামির জন্যে আপনি মারা গেলেন তারই হাতে দিতে এসেছে।
শক-খাওয়া লোকটাকে পাশ কাটিয়ে ডি-আইয়ের ঘরে ঢুকে যাই।
—কে? ও তুমি ভাই! বিশ্বনাথদা কেমন আছেন?
—বিশ্বনাথদা ভালই আছেন, পতিতপাবনদা মারা গেছেন।
—পতিতপাবনদা … আমি তো ঠিক …
—আপনার কত কাজ! তুচ্ছ জিনিস কি আর স্মরণে থাকে! এটা ওই পতিতপাবন সেনের শ্রাদ্ধের চিঠি, পাঁচ বছর পর ছ’ বছরের মাঝামাঝি — মস্তান নিয়ে এসে হুমকি দেবার পর যাঁর পাওনা-গণ্ডাগুলো চুকিয়ে ছিলেন! আবার বিধবার পেনশনের জন্যে আসতে হবে তো! চিঠিটা আগাম দিয়ে যাচ্ছি। দাও, অরুণ, দাও।
অরু হকচকিয়ে গিয়েছিল, একটা ব্ল্যাংক খামে ভরা চিঠি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে। আমি নাম লিখি অলকেশ দত্ত। চিঠিটা নিয়ে উনি চমকে ওঠেন। এ কী চন্দ্রবিন্দু দিয়েছ কেন?
আমি চিঠিটা ফেরত নিয়ে জিভ কাটি—ইসস্ দেখুন তো, কে মারা গেলেন আর কাকে চন্দ্রবিন্দু মারছি। ছ্যাঃ। তবে সরকারের কতগুলো টাকা বেঁচে গেল, বলুন তো? কেমন কল করেছেন? চন্দ্রবিন্দুটা কেটে দিয়ে বেরিয়ে আসি।
অরু বলছে শুনছি—দয়া করে একবার পায়ের ধুলো দেবেন কাকা।
কেউ কোনও উত্তর দিল না।
ভাবতে ভাবতে রাস্তা হাঁটি। একেবারে অন্যমনস্ক। অভ্যাসে রিকশা, ঠ্যালা, এক আধটা গাড়ি পাশ কাটাই। কী এত ভাবছি! ভেবে, আমার মতো একটা সাধারণ কমার্স গ্র্যাজুয়েট, একদা রিফিউজির বেকার ছেলে, কী করতে পারে? বুঝতে পারি কাগজে দেখা কতকগুলো ছবি আমার মাথায় মৌমাছির মতো ঘুরছে। কী ছবি? মহেন্দ্র মহাজন, হাতে ব্যান্ডেজ, মাথায় ব্যান্ডেজ, চোখে বিহ্বল শূন্য দৃষ্টি, যেন গাছপালা, মানুষজন, রাস্তাঘাট, যানবাহন কিছু চিনতে পারছে না। পাশে মদনলাল, পায়ের যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত। পাশে মদনলাল হাসপাতালের বেডে শয়ান। পাশে মদনলাল স্বাভাবিক, আহত হওয়ার আগে যেমন ছিল, পাশে মহেন্দ্র কিডন্যাপ হবার আগে যেমন ছিলেন, তারাতলা রোড, সোজা গেলে বজবজ। বাঁয়ে বেঁকে ডায়মন্ডহারবার, ব্রেসব্রিজ। ব্রেসব্রিজ… মাথায় এই ছবিগুলো নিয়েই দীপুর হানাবাড়িতে হানা দিই। দেখি আপন মনে খ্যাপার মতো হাসতে হাসতে হাতে খইনি ডলছে।
—তুই খইনি ধরেছিস?
—ধরাল একজন।
—তুইও ধরে নিলি? খইনিতে টোব্যাকো তো আছেই, ব্রাউন শুগারও নিচ্ছিস নাকি?
—নিতে পারি।
—তুই শ্ শালা— মাকে পুলিশ মুরগি করছে আর তুই …
—বাওয়ালি থামা রুণু, চ’ তোকে একটু আলোকপাত করি।
ইটের পাঁজা থেকে দীপে উঠে দাঁড়ায়। একটু নড়বড়িয়ে ওঠে, কিন্তু জাতে পাগল হলে হবে কী, তালে শালা আছে ঠিক।
—চ।
—কোথায় যাব? তোর সঙ্গে কোত্থাও যাব না। তুই একটা সাজা-পাগল, দায় এড়াবার জন্যে সেজে থাকিস। টো-টো কোম্পানি কাঁহিকা—আমি তোর সঙ্গে কোত্থাও যাব না।
—আরে চলই না, একটা বহুৎ ইনটারেস্টিং জিনিস দেখাব। না দেখলে পরে কিন্তু পস্তাবি। তখন বলবি—আমায় কেন বলিসনি?
ফুটতে ফুটতে দীপুর পেছন পেছন অসমাপ্ত বাড়ির সাইড-রেলিং-হীন ঢালাইয়ের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকি। দোতলা পেরিয়ে যায়, তিনতলা পেরিয়ে যায়, চারতলা পেরিয়ে যায়। একেবারে সাততলায় পৌঁছে দীপু থামে। একদিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ-পুবে সেই ভাঙা ফ্ল্যাট। ইটকাঠগুলো ভাঙা পড়ে আছে। কেউ একটু পরিষ্কার পর্যন্ত করেনি। কিন্তু ঢালাইয়ের খাঁচাটা এখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্য তিনটে ফ্ল্যাট একেবারে আস্ত নতুন, দরজা লাগানো। খালি বাইরের রংটা হয়নি।
—ভাঙলই যদি, তো সবগুলো ভাঙল না কেন? —আমি আপন মনে বলি।
দীপু খইনিঅলা দাঁতে বিকট হাসতে থাকে।
—এটারও তো ঢালাইয়ের ছাদ, বিম, পিলার সব ঠিক আছে। এগুলোই-বা ভাঙেনি কেন? —আমি আবার বলি।
—অ্যায়। দ্যাট ইজ দা কোয়েশ্চেন—দীপু আওড়ায়। য়ু আর অন দা রাইট ট্র্যাক। আমি শালা মাল আগলাই, গ্রাউন্ড ফ্লোরের ওপরে এখন আর কাজ নেই। পাগলাটা! ইটের পাঁজায় বসে গাঁজায় দম দিই। ভাঙেনি কেন? … আমি দীপুর দিকে তাকাই, কেন বল তো?
—রি-বিল্ড করতে যাতে মিনিমাম খৰ্চা হয়! এ তো সোজা হিসেব!
আমি চোখে প্রশ্ন নিয়ে দীপুর দিকে তাকিয়ে থাকি।
দীপু বলে—কেস বুঝলি না? ‘হারাধনের দুইটি ছেলে ধরতে গেল ভেক/ একটি মলো সাপের বিষে রইলো বাকি এক।’ তুই বোধহয় জানিস না তোর প্রিয় কমরেড দেবল গুহর ছোট দাদু মারা গেছে।
—বলিস কী রে! জানি না তো! ওই যিনি হার্টে ভুগছিলেন!
—না, তাঁর ছোট। সেই খটখটে, খেঁকুরেটা। বুঝলি রুণু স্বামী-স্ত্রী হরবখত্ দেখবি দু’জনেই ভুগছে। এ বলে আমি আগে, ও বলে আমি আগে। দু’জনের মধ্যে বেটার অবস্থা যার সে-ই কেটে পড়ল। যার যেমন আয়ু। ভগবানের মাপা নিয়ম একেবারে। কেউ কিস্যু করতে পারবে না। অন্য হেটো রুগীটা একা-একা আর কদ্দিন যুঝবে? গেলেই, জগামিত্তির কেস তুলে নেবে, দমকলের স্যাংশন এসে যাবে, কর্পোরেশনের পারমিট বার হয়ে যাবে। ষাট-চল্লিশের হিসেব এক্কেবারে আগের মতো। চল্লিশের সোল প্রোপ্রাইটার রমেন গুহ, ডাইরেক্ট ডিসেন্ট-এ দেবল গুহ। ওনারদের টাকাটাও সুদে বাড়ছে।
—তা ছাড়াও কিছু ছুটকো কাজ কম্মো আছে। বুঝলি? সেগুলো শেষ হোক! —দীপু বলে চলে, ধর না কেন ওই দক্ষিণ-পশ্চিমের ফ্ল্যাটটা!
সে ফ্ল্যাটটার দিকে এগিয়ে যায়। টুকটুক করে টোকা দেয়।
আমি আশ্চর্য হয়ে শুনি ভেতর থেকে কে ফিসফিসে গলায় বলছে, কে? কে?
—আমি দীপুদা।
দরজা খুলে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে সমশের-সামসুলের বোন হাসিনা না? আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। আমি, আমি নাকি পাড়ার সবচেয়ে স্মার্ট ছেলে, আমার একেবারে বাক্য হরে যায়। একটা কথাও বলতে পারি না।
দীপু বলে—ঘাবড়াচ্ছিস কেন হাসি। এ তো রুণু! রুণু রে!
হাসি দু’-হাতে মুখ ঢেকে ফেলে।
ঘরটার চারপাশে চোখ চালিয়ে দেখি, জানলাগুলোর কাচ সব বন্ধ। কাচের মধ্যে দিয়ে আলো আসছে কিন্তু অসহ্য গুমোট। ভেতরে একদিকে এক সেট এঁটো থালাবাটি গেলাস, আর একদিকে একটা মাদুর আর বালিশ। বালিশের পাশে স্তূপীকৃত বইখাতা।
—তুই এভাবে ওকে এখানে লুকিয়ে রেখেছিস! আমার স্বরে আর রাগ নেই। শুধু প্রচণ্ড বিস্ময়!
—আরে আমি একটা পাগলা, বাউন্ডুলে, আমার মাথায় এত আসে? শামু, শামু ভাই, ওকে লুকিয়ে রেখেছে! রমজানকে রেজিস্ট করতে। না কী রে হাসি!
শামুর নাম করবার সঙ্গে সঙ্গে হাসি একটা আঁক মতো শব্দ করে পরক্ষণেই সেটা গিলে নিল।
দীপু বলল— বলে দেব না তো কী! আগে দোষটা রুণুর ঘাড়ে চেপেছিল। এবার চাপবে আমার ঘাড়ে। আর কী করে রিসক্ নিই বল? যা হল? দুরাত্মাদের ছলের অভাব থাকে না, বুঝলি তো! তা রুণু আমাদের সেরকম মিতে নয়। যতই অপমান হোক কাউকে বলবে না। তোর পড়াশুনো কী রকম চলছে?
—ভাল।
—এই অসহ্য গরমে আট কাঠ বন্ধ করে … তুমি থাকো কী করে? অবশেষে আমি বলি। হাসি মুখ নিচু করে বলল—সইতে তো হবেই! এরকম নয় তো ওরকম!
—ওর হাত ফাতগুলো দ্যাখ — ঘামাচি হয়ে হয়ে ফোস্কা মতো পড়ে গেছে।
সত্যি, দেখি মুখটাও হাসিনার অসম্ভব খসখসে, যেন ব্রণয় ভরে গেছে।
—রাত্তিরে শামু খাবার নিয়ে, বরফ নিয়ে আসবে, মাঝ রাত হলে জানলাগুলো খুলে দেবে — তখন হাসিনা বেগম খেয়েদেয়ে গায়ে-মুখে বরফ ঘষে চাঁদের আলোয় নিদ্ যাবে। নয় রে হাসি! —থাক আর না, কে কোত্থেকে টিকটিকি করবে। আয় রুণু। হাসি দরজা বন্ধ কর।
—তোর সঙ্গে ষড় করেই শামু করেছে নিশ্চয় কাজটা? —আমি ফিরতে ফিরতে শুকনো গলায় বলি।
—তুই কি খেপেছিস? শামু হল গিয়ে চাকলাদারের নাইট-ওয়াচম্যান, গেঞ্জির ভেতরে বুলেট-প্রুফ জ্যাকেট, কোমরে ছ-নলা রিভলভার, হাতে ইয়া গুলি, পাগুলো স্টিলের মতো, শালা একটা লাথি ঝাড়বে তো তুই আমি কেন চাকলাদার বিশুদা সুদ্ধ ও-ই কোণে ছিটকে পড়বে। দু’জনের লাশ কী সাইজের, ওজন কত—ভাব একবার।
—তা হলে? চাকলাদার জানে?
—জানে বই কী! তবে এটা না! এটা শামুর নিজস্ব সিক্রেট। একেক জনের একেক ধান্দা আর কী! চাকলাদার কুমীরটা গভীর জলে ঘাপটি হয়ে আছে এখন। কোস্ট ক্লিয়ার দেখলেই সিনে চলে আসবে। এখন তোর চাকলাদারের আরও কত তালাও-ফালাও বোজাবার আছে!
—তুই বলছিস, শনিতালাও বোজাবার পেছনেও ও?
—আলবৎ।
—তার মানে দাঙ্গাটাও …
—রুণু, তোর আর কবে আই কিউ বাড়বে? এসব কেউ একা করে? বখরাদার থাকে। চোরের পেছনে জোচ্চোর তার পেছনে বাটপাড় তার পেছনে …। তোরা ভাবিস গডই সব। কিন্তু শালা, গডের পেছনেও গডফাদার থাকে। থাকে কি না?
—তুই জানিস, শামু জানে?
—শিওর।
—তুই কী করে জানলি?
—আরে ভয়েসটা খালি কিনকিন কিনকিন করে। শামু যে-ই আসে অমনি। এমন শেয়ালের মতো গুঁড়ি মেরে আসে, যেন শুধু আধভাঙা বাড়ি পাহারা দিতে আসছে না, গুপ্তধন চোরাই ধন-টন কিছু পাহারা দিচ্ছে। ব্যাস ভয়েসের কিনকিন স্ট্যান্ড করতে না পেরে একদিন ভর দুপুরে সোজা সাততলায়। তারপরেই ডিসকভারি চ্যানেল।
—শামু যে তোকে এখনও নিকেশ করে দেয়নি, এ তোর ভাগ্য দীপু। সাবধানে থাকিস।
—কী যে বলিস! বন্ধু কখনও বন্ধুকে নিকেশ করে? তা ছাড়া হাসির ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকস্ কে দেখিয়ে দেবে এই খোঁচড়ের দেশে, দীপু পাগলা ছাড়া? মেয়েটা শিওর এইচ এস-এও ফার্স্ট ডিভিশন পাবে। দেখে নিস।
আমি সিঁড়ির দিকে যাই। একেবারে অন্যমনস্ক। যাক হাসির পাত্তা করা গেল। যাক শামু, ওর দাদা-ই ওকে সাহায্য করেছে। শামুর মধ্যে যে একটা ভাল দিক আছে আমি বরাবর জানি। তবে শুধু এই পর্যন্ত হলে চমৎকার হত ব্যাপারটা। আমার ওপর হামলাটা আমি ‘লেট বাইগনস্ বি বাইগনস্’ করে দিতে রাজি আছি। শুধু ওই ‘মেয়েছেলেটা!’ ভুলতে পারব না। আর দাঙ্গাটা? … বেঁটেদার বাঁ হাত, আলমের ডান পা, নিমকির ভেজিটেবল হয়ে যাওয়া, ওদের মায়ের মরে যাওয়া। বাচ্চাগুলো … উঃ, এটা আমি কিছুতেই কিছুতেই … কিছুতেই … ভেতর থেকে কী যেন একটা গরম লাভার মতো বেরিয়ে আসতে চায়। পেছন থেকে দীপু আমাকে একটা হ্যাঁচকা টান দিল।
—এই রুণু মস্তান, যাচ্ছিস কোথায়?
—আর ভাল্লাগছে না দীপু, ছাড়।
—ডিসকভারি চ্যানেলে আজ ভাল প্রোগ্রাম। না দেখলে পস্তাবি। তখন আমায় দোষ দিস না!
হঠাৎ আমার ভেতরে একটা শিকরে রাজ নখওলা একটা শিকারি ডবারম্যান উঠে দাঁড়ায়, হঠাৎ আমিও একটা আশ্চর্য কিনকিন কিনকিন মগজের মধ্যে শুনতে পাই। জোরে চেপে ধরি দীপুর হাত।— সত্যি? কোথায়? কোথায় বল।
দীপু চোখ সরু করে বলে—শুনতে পেয়েছিস, না?
—ইয়েস।
দীপু চোখ বড় বড় করে দু’হাতে আমার দু’হাত জড়িয়ে ধরে যেন আমরা এতদিন পরে ঠিকঠাক এক লেভেলের বন্ধু হলাম। উত্তর পুবের ফ্ল্যাটটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ও। একটা চাবি বার করে পকেট থেকে। ঘোরায়। ক্যাঁচ শব্দে হাট হয়ে যায় দরজা, দেখি একটা শূন্য ঘর, সব জানলা বন্ধ, অন্ধকার, অসহ্য গুমোট। একটা অসুখ-অসুখ গন্ধ। ভেতরে একটা ফোল্ডিং খাট, একটা কুঁজো। আমি ঢুকে পা টিপে টিপে যাই, খাটটার ওপর বিছানা, তাতে কী আছে? কুঁজোটা? কুঁজোটায় কী আছে?
দীপু বলে —হল্ট। একটা জিনিসও ছুঁবি না। অল দিস ইজ এভিডেন্স। যা দেখলি দেখলি চলে আয়। এই হচ্ছে সেই চোরাই ধন যা পাহারা দেবার জন্যে শামুর মতো ওস্তাদ লাগে।
—এত কাছে? আর কেউ টের পেল না!
—রাক্ষসরা যে-দিন কাছে বলত সে-দিন দূরে যেত, যে-দিন দূরে বলত সে-দিন কাছে। মনে নেই? নাকের ডগায় কে খুঁজে দেখবে রে? এখানে ওকে শিফ্ট করে বোধহয় শেষ মাসটা রাত্তির একটা নাগাদ, যখন দেখে বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। কোনও ভাল ডাক্তার তো পাচ্ছিল না! তো শামুর রেফারেন্সে ডাক্তার আনোয়ার অপারেশনটা করেছিলেন, এখানেই। অ্যাম্পুল ফাম্পুল, ওদিকের রাবল-এর মধ্যে অনে-ক আছে, সব এভিডেন্স, টাচ করিনি। এখানেই ওকে অজ্ঞান অবস্থায় মাঝরাত্তিরে নামিয়ে, গাড়িতে ভরে হোল কলকাত্তা ঘুরিয়ে রসিক ঘোষের মোড় থেকে একটু দূরে রাস্তায় জাস্ট নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। জ্ঞান হলে যেতে পারে যাবে, কেউ সাহায্য করলে করবে, আর যদি না পারে? হি’ল সাকাম টু হিজ উন্ডস্। পাঁচ কোটি টাকার সওদা—ডেড অ্যান্ড গন। কী করা যাবে?
আমার চোখে আগুন জ্বলে। আমি বুঝতে পারি আমার ভেতরে একটা ভূমিকম্প হচ্ছে, লাভা আর ছাই ছিটকে উঠে যাচ্ছে আকাশে। গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে, শহর গ্রাম সব চাপা দিয়ে দেবে।
গুমগুমে স্বরে জিজ্ঞেস করি—এটা যে তুই জানিস, শামু জানে?
—শিওর!
—তোকে খতম করে দেবে দীপু। শিগগির থানায় যা।
—থানা? —দীপু হেসে উঠল। ইউ মীন শনিতলা থানা? সব্বোনাশ! তুই এ-ও জানিস না ও থানাটা শামুর চেয়েও ডেঞ্জারাস! তবে গেছি, তুই ভাবিস না —দীপু আমার পিঠ চাপড়ে দেয়। আসল জায়গায় গেছি — ডি.সি.ডি.ডি, লালবাজার। লোকটা টিপিক্যাল খোঁচড় নয় — ভয়েস বলল। কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত এভিডেন্সসুদ্ধ নাটের গুরুগুলোকে ধরবে। ইনক্লুডিং শামু।
—বলিস কী রে! শামু জানে তুই …
—শামু রাজসাক্ষী। ঘাবড়াস না। শালা আমাকে খতম করবার ভয় দেখিয়েছিল। হাসি সঙ্গে সঙ্গে ছারপোকা মারার বিষটা—সেই যে রে যেটা আমার বাবা খেয়েছিল—খুব হ্যান্ডি। হাসি সবসময়ে সঙ্গে রাখে। আমাতে হাসিতে মিলে অনেক কষ্টে ওকে বুঝিয়েছি।
—অত সোজা নয় দীপু। ও ওর ওপরের গডফাদারটাদারকে সাবধান করে দেবে না তুই কী করে জানলি?
—রিল্যাক্স ম্যান, ও এখন পুরোপুরি ক্যালকাটা আই-বির কবজায়। ইনটারপোলে খবর চলে গেছে। কিছু করতে পারবে না। পুলিশ যা বলছে মুখ বুজে ও তাই করছে। নইলে ল্যাংচা খেয়ে যাবে। গদ্দাম্।
—তা হলে ওর পেছনের লোকগুলোই ওকে খতম করবে।
—সে দ্যাখ রিস্ক্ নিতেই হবে। যা করেছে তার মাশুল তো ওকে কোনও না কোনওভাবে দিতে হবেই। তবে ওর বিপদের সম্ভাবনা মিনিমাম রাখার চেষ্টা হচ্ছে। যা কিছু কমিউনিকেশন এখন ভায়া দীপু পাগলা। এই দ্যাখ—দীপু আলাদিনের আশ্চর্য পিদিমের মতো একটা ছোট্ট মোবাইল বার করল পকেট থেকে। আমি ওর কথা শুনছি এক কান দিয়ে আর এক কান দিয়ে শুনছি মনের ছবিগুলো কী বলছে। শটাশট জুড়ে যাচ্ছে ছবিগুলো। কিনকিন কিনকিন মদললালকে তুমি স্বপ্নে দেখেছ। আসল মদনলাল অত তাগড়া অত বিভীষণ নয়। কিন্তু সে স্বপ্নের মদনলালই। কোথাও দেখেছ, তুমি খেয়াল রাখোনি, তোমার স্বপ্ন খেয়াল রেখেছে। স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন। হঠাৎ বুঝতে পারি আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাল্টে যাচ্ছে। চেরা জিভে আগুন, চোখে আগুনের হলকা, পাগুলো একটা বিরাট অগ্নিশিখাময় ল্যাজ। আমি ড্রাগন হয়ে যাচ্ছি। ঊর্ধ্বশ্বাসে পুচ্ছ তুলে হলকা ছড়াতে ছড়াতে বুক হড়কে স্লিপ করে করে আমি পিছলে নেমে যেতে থাকি যেন ওখানে কোনও সিঁড়ি নেই, একটা ঢালু উৎরাই শুধু। দীপু পেছন থেকে ছুটে আসে। —কোথায় চললি? কোথায়? এই রুণু?
আমার সামনে কালো পাথরের দেয়ালটা চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে, আমি অবলীলায় সেই ফাটল দিয়ে বেরিয়ে যাই, ছুটে যাই একটা ধূমকেতুর মতো। রসিক ঘোষ, রহিম শেখ, অবনী শেঠের গলি উপগলির ধুলো উড়িয়ে একটা ম্যানশনের বেল টিপে ধরি। কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে একটা চাউনি আমায় আপাদমস্তক জরিপ করে নিয়ে বলে—কাকে চান? —চাকর নয়। চাকরানি নয়। দারোয়ান বা বডিগার্ড নয়—স্বয়ং মালিক।
—চিনতে পারছিস না? আমি রুণু রে! প্রাণপণে আগুনের হলকাকে হাসিতে পরিণত করি আমি, একটা পার্সোন্যাল দরকারে তোর কাছে এসেছি ভাই। একটু সময় দিবি?
ডবল তালা-অলা গ্রিলের গেট, কোল্যাপসিব্ল সব খুলে যায়—ও বাইরে এসে দাঁড়ায়। ও স্টপার আর আমি স্ট্রাইকার।
আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করি না। শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে টুঁটি টিপে একেবারে রাস্তার মাঝখানে টেনে আনি ওকে।
—বল গদা মাসিমাকে কেন মহাজনদের বাড়ি পাঠিয়েছিলি?
—কী হচ্ছেটা কী? রাস্তার মাঝখানে? ছাড়ো, ছাড়ো কলারটা…। মহাজনরা আমাদের ডবল মাইনে হেঁকেছিল, যাবেন না কেন? আমি কেন বাধা দেব?
—সব্বাই তোর মতো গদ্দার গুখোর হয় না শালা? তুই ওয়েলউইশার সেজে পাঠিয়েছিলি ফ্রেম করবি বলে। ওদের ভেতরের নিয়মকানুন সব কথার ছলে জেনে নিতিস মাসিমার থেকে। অ্যালজোলামটা কফিতে মিশিয়েছিল তোর শাগরেদ মদনলাল। তা সত্ত্বেও মহেন্দ্র টিফিনবক্স ছোড়ায় তোদের প্ল্যান একটু কাঁচে, শুয়ার মদনলালটা গুলিতে জখম হয়। ইচ্ছে করে শালা ব্রেসব্রিজের দিকে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। নির্জন বলে। তার মানে পুরো কিডন্যাপটার পেছনে তুই।
চাপা গলায় গদাই বলে—গাড়ল, গাড়ল একটা। পুরো কিডন্যাপ! হুঁঃ! প্রাণপণে ছাড়িয়ে নেয় আমার হাত।
চতুর্দিকে সলিড ভিড় জমে গেছে। সত্য, অমল কমল সাহা। সেলিম বিশ্বাস আর তার তিন ভাই খলিল, মুস্তাফা আর সঞ্জু, অরুণ, পানু, সামসুল … যে যেখানে আছে। অনেক ভিড়। অজস্র মুখ। মুখ চিনি নাম জানি না। অনেক মানুষ যারা অবমানবের জীবন কাটিয়ে এসেছে এতদিন। আমি জানি না আজকের ধাক্কায়ও তারা মানব হবে কি না। না হলে আর কোনও আশা নেই।
নিজের কোমর থেকে এতক্ষণে পিস্তল বার করেছে গদা। —পথ ছেড়ে দাও। নইলে গুলি করতে বাধ্য হব — জনতার দিকে তাকিয়ে সে বলে। কেউ পথ ছাড়ে না। তখন আমার দিকে পিস্তল তাক করে শয়তানটা। ড্রাগন লাফিয়ে উঠে ওর কাঁধে ল্যাজের আছাড় মারে — ছিটকে যায় পিস্তল। পুলিশের গাড়ির তীব্র সাইরেনের শব্দে কেঁপে ওঠে রসিক ঘোষ, রহিম শেখ, অবনী শেঠ আর শনিতলার অলিগলি। চারদিক থেকে ছ’ সাতটা সশস্ত্র গাড়ি এসে ঘিরে ধরে আমাদের।
হাতে হাতকড়া বেঁধে পুলিশের খাঁচায় ওঠে গদা—মাস্টার কিড্ন্যাপার, শামু—ওয়াচম্যান, রমজান আলি, চাকলাদার দাঙ্গাবাজ, রমেন গুহ, জগা মিত্তির ডাক্তার আনোয়ার আরও অনেক ছোট ছোট নাট বল্টু—বিধ্বংসী যন্ত্রের, তাদের চিনি না, জানি না। মহেন্দ্র মহাজন অপহরণ কেসের সমস্ত সন্দেহভাজন লোককে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। এটা ফার্স্ট রাউন্ড। এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, মস্তান, ক্যাডারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরা সমশের আর গদাকে কাজে লাগাত, রমজান আলির এরা জিগরি দোস্ত।
কিন্তু আমি তো সত্যিই মৌলিক প্রজাতির পৌরাণিক ড্রাগন নই! নই কারাটের ব্ল্যাকবেল্ট। কিংবা নাগাদের হেড-হান্টার। কোনও দিন বডিবিল্ড করিনি। সামনের কালো পাথরের দেয়ালটা স্রেফ মনের জোরে ভাঙবার জন্যেই আমার আপ্রাণ চেষ্টা। জাস্ট কিছুক্ষণের জন্য আমার একটা মেটামরফোসিস হয়েছিল, কুরূপা চিত্রাঙ্গদার সুরূপায় রূপান্তরের মতো, একটা দীর্ঘ ঐকান্তিক মানসিক প্রয়াসের ফল। তাই ঘটনাগুলো ঘটে যাবার পর আমি শেকড়হীন ফোঁপরা একটা গাছের মতো পড়ে যাই। বুঝতে পারি, মাটিতে আছড়ে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু পড়িনি। কারা আমাকে ধরে নিয়েছে, নিয়ে যাচ্ছে। আমার বডির তলায় আপাদমস্তক একটা মানুষের হাতের স্ট্রেচার। ড্রাগন হবার ক্লান্তিতে, ড্রাগুনে আগুন বয়ে জ্বলে পুড়ে যাওয়ার অসহ্য যাতনায় আমি ছটফট করি। ঘোরের মধ্যে বুঝতে পারি আমার কব্জিতে ছুঁচ, মুখে গ্যাস-মাস্ক। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, ডুবছে, ভাসছে নানা মুখ—মা, রিন্টি, দাদা, দীপু, মণিমালা, মুক্তামালা, হাসি, সামসুল, অমল, কমল, সত্য, পানু, সাম্য, সেলিম, এ.এস, জগদিন্দ্র, অরুণ এবং বউদি। চিৎকার করে বলতে চাই—বেঁটেদা, মহেন্দ্রদা, নিমকি-শিমকি, পতিত কাকা, আলম, হাসি, দাঙ্গায় মৃত এবং অনাথরা শোনো, মাসিমা শুনুন, বউদি শোনো—আমি শালা দীনদুনিয়ার মালিক বস নই, জান-প্রাণ আর ফিরিয়ে দিতে পারব না, কিন্তু তোমাদের ওপর বর্বর মস্তানি, বজ্জাতি, তোমাদের বে-ইজ্জতির বদলা আমি নিয়েছি। এবার, এইবার আমি রিন্টির জন্যে সচিনের পোস্টারটা ঠিক পেয়ে যাব, যে সচিন শুধুই ছক্কার পর ছক্কা, ছক্কার পর ছক্কা, ছক্কার পর ছক্কা, ছক্কার পর ছক্কা …।