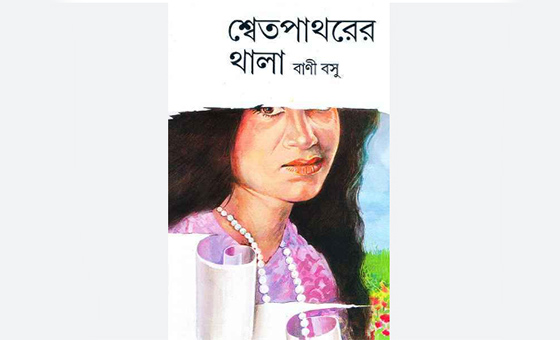
পঁয়তাল্লিশ নম্বর শ্যামবাজার স্ট্রিটের বাড়ির বয়স এ বাড়ির মুড়োয় লেখা আছে, যার থেকে হদিশ পাওয়া যায় বাড়িখানার পত্তন এ শতকে নয়। একশ পুরো না হলেও পঁচাশির কাছাকাছি বয়স গেছে। মা গঙ্গা খুব কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়ায় তাঁর জলো হাওয়ায় এবং বঙ্গোপসাগর দক্ষিণে একশ পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে হওয়ায় সাগরের নোনা হাওয়ায়ও বটে কলকাতার বাড়ি ইংল্যান্ডের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ ম্যানর হাউজের মতো দীর্ঘদিন টেঁকে না। তবু বিলিতি কোম্পানির পয়লা নম্বরের জিনিস—মাৰ্বল, থাম, খিলেন, টালি, আসল বর্মা-টিকের জানলা, দরজা, বরগা এবং চুন-বালির বিশ ইঞ্চির গাঁথনি এই সব বাড়ির প্রাচীনত্বকে এখনও সাড়ম্বরে রক্ষা করে চলেছে। সযত্নে পালিশ করা এর প্রাচীনত্ব যার আরেক নাম আভিজাত্য, আরেক নাম প্রশ্নহীন অতীতমুখিতা, আরেক নাম? সংস্কার এবং তা কু-উপসর্গযুক্ত।
মার্বলের সাদা-কালো ছক-কাটা চল্লিশ ফুট লম্বা দালান। এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো হাঁটলে তবে কালো পাথরের সিঁড়ি। আবার দালান, একতলার। অমনি চল্লিশ ফুট লম্বা। অমনি সাদা-কালো ছক। তার মাঝামাঝি অবধি হেঁটে গেলে তবে খাবার ঘরের দরজা। এই সমস্তটা হাঁটতে দুপুর দুটো অর্থাৎ ঠিক দ্বিপ্রহরে, ক্লান্ত দুর্বল শরীরটা তার থরথর করে কাঁপতে থাকে। সৈন্য-ব্যারাকের মতো বাড়ির গড়ন। দক্ষিণ চেপে সারি সারি ঘর, দোতলারগুলো তো বটেই, একতলার ঘরগুলোও কলকাতার বিখ্যাত দখিনা পবন সময়মতো পেয়ে থাকে। উত্তরে দালান। লাল নীল সুবজ হলুদ কাঁচ দিয়ে তার মাথায় কারুকার্য। তিন পাট করা জানলার শার্সিতেও তাই। সূর্য উত্তরায়ণে গেলে মার্বলের মেঝের ওপর চার রঙের হোরিখেলা হয়ে থাকে। পূবমুখী বাড়ি। ছাদে উঠলে সূর্যোদয় দেখা যায়। সামনের অনেক দূর পর্যন্ত প্রায় সমান মাপের দোতলা বাড়ি নিয়েই পল্লী। দূরে, ঠিক দুটি তালগাছের মধ্য দিয়ে সূর্যদেব যখন উঠে আসেন তখন শ্যাওলা-ছ্যাতলা-পড়া, টবের ফুল গাছঅলা, এ মুড়ো ও মুড়ো টানা তার বা নারকেল-দড়িতে কাপড়-শুকনো বৃদ্ধ ছাদগুলোও আলোয় আলো হয়ে যায়। কিন্তু জবাকুসুমসঙ্কাশ তরুণ তপনের কাছে তাদের আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠবার প্রার্থনা যে জাগেই এমন কথা বলা যায় না। কারণ সেই সব অলৌকিক প্রত্যূষে পাড়ার প্রান্তে টিউব-ওয়েলের ঘটাং ঘটাং একবার চড়ায় ওঠে আবার খাদে নামে, বাসন মাজার ঝনঝন শব্দ, ঝাঁটার শপাং শপাং এবং নিদ্রোত্থিত গৃহিণীদের কর্কশ নির্দেশাদি ভোরবেলার বাতাবরণে এমন একটা দুটো বিবাদী স্বর চড়িয়ে রাখে যে বৈদিক উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিতই হোক আর রাবীন্দ্রিক সুরই হোক, বিষণ্ণ মুখে পশ্চাদপসরণ করতে পথ পায় না।
বাড়ির পশ্চিমে খোলা আধকাঁচা উঠোনে চাকরবাকরদের টালি-ছাওয়া পাকা ঘর। মস্ত মস্ত চৌবাচ্চা-অলা কলঘর এবং অযত্নের বাগান। কোথায়, কবে, কোন পাখি ঠোঁটে করে আধ-খাওয়া ফল ফেলে গিয়েছিল। কাঁচা উঠোনের মাটি ফাটিয়ে সেখানে বঙ্কিম ঠামের এক চিরসবুজ, চিরফলন্ত পেয়ারা গাছ। পাশে জোড়া নিম। সে-ও পাখ-পাখালিরই মালিগিরিতে। নিমের ছায়া ভালো, বলে সবাই। এই তিনে মিলে পশ্চিম দিক এমন ছায়া করে রাখে যে দুপুর বারোটার পর সূর্য হেললে শেষ বেলার রোদ আর এ বাড়ি পায় না। পেতে হলে ছাদে উঠতে হবে। দালানে এখন লম্বা ছায়া পড়ে গেছে। উত্তরের শনশনে হাওয়া ঢুকছে লাল-নীল কাচ শার্শির এক আধটা ভোলা পাল্লার ফাঁক দিয়ে। পায়ের তলায় হিমের ছুঁচ। গায়ের কালো পশমি চাদরটা ভেদ করে হাড় হিম করে দিচ্ছে উত্তুরে হাওয়া।
বাড়ির আর সব ঘরে শান্তিনিকেতনী পর্দা ঝুললেও খাবার ঘরের দরজা ফাঁকা। ঢুকতে, বেরোতে এঁটো-কাঁটা লাগবে। বাড়ির ছেলেরা, কর্তারা বাসি-টাসি মানার ধার ধারে না। ওসব পবিত্রতা খালি মেয়ে-মহলের জন্যে। শাশুড়ি বলেন মেয়েছেলের চরিত্তিরেই বাড়ির চরিত্তির। ব্যাটাছেলের দস্তখত আর মেয়েছেলের সহবত। ব্যাটাছেলের এক এক আঁচড় সইয়ে এক এক থলি টাকা উঠে আসবে। আর মেয়েছেলের শীল-শাল, হায়া-লজ্জা, আচার-বিচারেই বাড়ির মান-ইজ্জত। লোকজনের অভ্যেস বড় খারাপ তার ওপর, নোংরা কি ভিজে হাতটা ঝপ করে হয়ত পর্দায় মুছে ফেলল। চোদ্দবার অমন নোংরা হবে দিনে। তার চেয়ে দরজা ন্যাড়া থাক। সেই ন্যাড়া দরজা-পথে দেখা যায় ডান দিক ঘেঁসে খাবার টেবিল পড়েছে, যা এ বাড়ির বড় ছেলে বিদেশ থেকে ফিরে চালু করেছিল অনেক আপত্তি, অনেক মন কষাকষির পর। পাশে ফ্রিজ। তারও বয়স বেশি নয় এবং তাকে চালু করতেও সেই একই মানুষ ও একই রকম মন কষাকষি। সব এঁটো-কাঁটা সকড়ি হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম ফল দুধ দই মিষ্টি ছাড়া কিছু থাকত না। এখন সবই থাকে। খালি সকড়ি আর আ-সকড়ির তাক আলাদা। এখন না হলে চলে না। গ্রীষ্মের দিনে শরবত, ঠাণ্ডা জল—পাঁচটা মানুষকে ঠাণ্ডা খাইয়ে কেরামতি দেখাবার জিনিসও বটে। এ জিনিস কিছু সবার ঘরে নেই। বাঁ দিকের কোণে কালো কম্বলের আসন। সামনে পরিষ্কার করে মোছা মেঝের ওপর সাদা পাথরের থালা। কাশীধামের জিনিস। পাশে গেলাস, বাটি, সবই একদম সাদা, শ্বেতশুভ্র পাথরের। পবিত্র নিষ্কলঙ্ক।
থালার ওপর ছোট ডেকচি থেকে আতপান্ন বেড়ে হঠাৎ ডুকরে উঠলেন মাঝবয়সী গিন্নি-বান্নি মানুষটি। চুলগুলি চার ভাগের এক ভাগ সাদা। চওড়া সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। চওড়া লাল নকশি পাড় শাড়ি। তিন থাক দাঁত দেওয়া। এই রকমের রাঙা পাড় শাড়ি ছাড়া উনি পরতে চান না। দু হাত ভর্তি ঝমঝমে চুড়ি লোহা রুলি শাঁখা। কান্নাটি তার চেয়েও ঝমঝমে। কণ্ঠের জোরেও বটে, শোকের জোরেও বটে: ‘কোথায় গেলি রে খোকা! একবার দেখে যা বাছার আমার কষ্টটা দেখে যা একবার। দুধের বাছাকে কেমন করে এ জিনিস ধরে দিই রে!’
বসেছিলেন আরও দুজন। একজন খুড়শাশুড়ি। তিনি চট করে চোখে আঁচল চাপা দিলেন। দ্বিতীয় জন বড় ননদ। তিনি চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। এসরাজের আর্তনাদ-মলিন আবহসঙ্গীতসহ এ এমনই এক গা-ছমছমে দৃশ্য যে কোনও এয়োতিই একে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। খাবার জন্য সবে যে ঘরে পা বাড়িয়েছিল, এতক্ষণ দালান হাঁটার ক্লান্তি তার পায়ে, এতক্ষণ পাথরের ঠাণ্ডায় পা পেতে রাখার কালশিটে তার দু পায়ের আঙুলে। শরীরের ভেতরটা দুর্বলতায় এবং আকস্মিক উত্তেজনায় কাঁপছে। হঠাৎ সে বলে উঠল—‘যা দিলে আপনারও কষ্ট হয় না, আমিও খেতে পারি এমন জিনিস দিলেই তো পারেন মা। রোজ রোজ এ নিয়ে এত কান্নাকাটির দরকার কি? আর এ আমি সত্যিই খেয়ে উঠতে পারছি না, পারছি না…।’ শেষের শব্দগুলো বিকৃত রুদ্ধ কান্নায়।
ঘরের মধ্যে যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হল।
বড় ননদ চলে যাবেন বলে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই অবস্থাতেই একটু ন যযৌ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যুগপৎ শাশুড়ি ও বউ-এর মুখ দুটো দেখে নিলেন। তারপর হঠাৎ একটু বেগেই বেরিয়ে গেলেন।
শাশুড়ি সেই যে উদ্যত কান্না গিলে মুখখানাকে নিচু করে ফেলেছেন আর তোলেননি। খুড়শাশুড়ির চোখের জল শুকিয়ে মুখটা কিরকম বিহ্বল হয়ে রয়েছে। যেন তাঁকে কেউ থাবড়া মেরেছে হঠাৎ। আলু-কাঁচকলার হবিষ্যান্ন আজ আর কিছুতেই বন্দনার গলা দিয়ে নামল না। ক্রোধে-ক্ষোভে-লজ্জায় গলার মধ্যে পিণ্ড, পাকিয়ে গেল।
ঊনিশশ’ পঞ্চান্ন সাল সবে আরম্ভ হয়েছে। জানুয়ারির শেষ। শীত খুব জানান দিচ্ছে। এখনও, স্বাধীনতার সাত আট বছর পরেও বুঝি কমলালেবু, আপেল, প্লাম কেকের সাহেবি ডালির প্রত্যাশায় আছে। এ বাড়িতে এই শীতের অর্থ এবার অন্যরকম। এ শীত মৃত্যুর, ক্ষতির, বিষাদের, যে বিষাদের কূল এখনও দূরে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আজ তিন চার মাস হতে চলল অভিমন্যু ভট্টাচার্য এ বাড়ির বড় ছেলে, বন্দনার স্বামী, চার বছরের অভিরূপের বাবা। যোগীন্দর অ্যান্ড যোগীন্দরের চীফ ডিজাইনার হঠাৎ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেছেন। মারা যাবার বয়স তো হয়ইনি, চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই মানুষটিকে কোনক্রমেই ত্রিশের বেশি বলে বোঝা যেত না। এক সময়ে নামী স্পোর্টসম্যানও ছিলেন। ফার্স্ট-ডিভিশন ফুটবলার। বাঁ হাঁটুর মালাইচাকি ঘুরে যাওয়ায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যোগব্যায়াম, মূলারের ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ চার্ট এবং ঘড়ি ধরে অনুসরণ করে শরীর-স্বাস্থ্য রেখেছিলেন সোজা, মজবুত, ঘাতসহ, তরুণ। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারেননি। কোনও অসুখ-বিসুখের বালাই-ই ছিল না শরীরে। ট্যুরে গিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশ। রাশিয়ার কোল্যাবরেশনে নতুন স্টীল প্লান্ট বসেছে। ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি পৌঁছলেন ভর সন্ধেবেলা। মা বাবাকে আসতে যেতে প্রণাম করার রেওয়াজ। বাবার পায়ের ওপর নত হয়েই চট করে উঠে দাঁড়ালেন। বাবা বললেন—‘কি হল রে?’
—‘না কিছু না। আমি চান সেরে আসছি বাবা।’
রূপ চৌকাঠ থেকেই বাবার কোলে ওঠার বায়না নিয়েছিল। সে প্রচণ্ড বাবা-ভক্ত। তার হাতটা ধরে অভিমন্যু বললেন—‘কোলে উঠলে কিন্তু সেই মজার জিনিসটা দোবো না রূপু।’ বাবার হাত ধরে মজার জিনিস পাবার আশায় লাফাতে লাফাতে দোতলায় উঠল ছোট্ট অভিরূপ। ঘরে ঢুকেই বন্দনাকে বললেন—‘বুকে ক’দিন ধরেই একটা চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে বুঝলে! কাজের ভিড়ে মন দেবার সময় পাইনি। একটা কার্বো-ভেজ থার্টি বার করো তো বাক্স থেকে!’ বন্দনা ওষুধের বাক্সটা নামিয়েছে তাক থেকে, শুনছে হাসতে হাসতে বলছেন—‘বুকের বাঁ দিক ব্যথা, তার মানে হার্ট, তার মানে ফেল, তার মানে চললুম এ যাত্রায়, বুঝলে কিছু?’
বন্দনা বলল—‘কি হচ্ছেটা কি? সব তাতেই হাসি-ঠাট্টা। যা-তা খেয়েছো বুঝি?’
—‘বাঃ, অফিস পাঠিয়েছে নিজের স্বার্থ দেখতে। খাতিরের খাওয়া চারবেলা, খাবো না?’
—‘খেয়েছে তো ওই সব রিচ রান্না আর …’
—‘ওঃ বন্দনা, তুমি এমন করছো যেন খেয়ে সাঙ্ঘাতিক একটা পাপ করে ফেলেছি। আরে বাবা, খাওয়ার জন্যেই তো জীবন! তবে তুমি রাগ করো না, আমি শুধু বুড়ি ছুঁয়েছি।‘
—‘অর্থাৎ?’
—‘তুমি যেমন কনে-বউ হয়ে ষোড়শ ব্যঞ্জনের বুড়ি ছুঁয়েছিলে ঠিক তেমনি।’
—‘সত্যি?’
—‘সত্যি। আসলে তো চালিয়েছি মাছ-পোড়া, মাংস-পোড়া আর কাঁচা সবজি দিয়ে। তবু যে কেন এই বায়ুপুরাণ!’
বন্দনা বলল—‘এখনও ব্যথা কমছে না? দাঁড়াও আমি এখুনি ডাঃ সেনগুপ্তকে ফোন করে দিচ্ছি।’
—‘আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও’ খপ্ করে বন্দনার হাতটা ধরে ফেললেন অভিমন্যু।
—‘কথায় কথায় অত ডাক্তার-বদ্যি কিসের, অ্যাঁ? কার্বো-ভেজে কমছে না দেখলে তবে ঠিক করব এটা বায়ুপুরাণ নয়, হৃৎ-পুরাণ। তখন খাবো একটা স্পাইজেলিয়া সিক্স, নাম শুনেছো জীবনে? তারপর ক্রেটিগাস মাদার গরম জলে কয়েক ফোঁটা ফেলে …।’
বলতে বলতেই অভিমন্যু বাথরুমের দিকে এগিয়েছিলেন। ধবধবে টার্কিশ তোয়ালে এক হাতে, সবুজ বর্ডার দেওয়া, অন্য হাতে পাটভাঙা পায়জামা-পাঞ্জাবি। এ বাড়ির সবাই গামছা ব্যবহার করে, অভিমন্যু ছাড়া। পায়জামার অভ্যাসও অভিমন্যুর একার। বাকি সবাই ধুতি, কিম্বা লুঙ্গি। এসব খানিকটা বিদেশে গড়ে ওঠা অভ্যাসও বটে, খানিকটা বন্দনার ইচ্ছের জোরেও বটে। অভিমন্যুর চোখের তলায় সামান্য কালি, ঘুমোতে না পারার, সর্বক্ষণ ঘিনঘিনে ব্যথা লেগে থাকার। পরিষ্কার কামানো মুখে একটু এই এতটুকু সবুজ শ্যাওলার ছোপ। মুখে নির্ভেজাল সরল, বিজয়ীর হাসি। দৃশ্যটা চোখ বুজলেই চোখের সামনে ভাসে।
বাথরুম বন্ধ করবার পরই হঠাৎ সেই অব্যক্ত যন্ত্রণাময় চিৎকার—‘বন্দনা-আ-আ।’
সুটকেস থেকে জামাকাপড় বার করছিল বন্দনা। খাটের গায়ে একে একে সাজিয়ে রাখছে। ব্যবহৃত রুমাল, গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার সব বালতিতে। শার্ট তোয়ালে, পায়জামা, পাঞ্জাবি ধোবার বাক্সে ফেলবে বলে জড়ো করছে। সেই চিৎকার যেন বুকের মধ্যে দমাস করে একটা শেল ফাটালো।
—‘বন্দনা-আ-আ-আ।’
বাথরুমের দরজাটা কোনমতে খুলে দিয়ে মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছিলেন। চোখ দুটো ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। সে কি যন্ত্রণায়? ভয়ে না বিস্ময়ে?
—‘কলি কলি, শিগগিরই সেনগুপ্তকাকাকে ফোন কর’ —বলতে বলতে বন্দনা মাথাটা কোলে তুলে নিয়েছে, তার ঘোমটা খসে পড়েছে, চুল এলানো, কাঁধের ওপর এখনও অভিমন্যুর একটা শার্ট, ধোবাকে দেবে না নিজে কাচবে, বিচার করছিল বলে কাঁধের ওপর তুলে রাখা, পড়ি-মরি করে চতুর্দিক থেকে ছুটে আসছে ননদ কলি, মিলি, কাকিমা, শাশুড়ি। ছেলেরা বাড়িতে কেউ নেই। শ্বশুরমশাই ভাগ্যিস আজকাল রোজ কোর্টে যান না। তাঁর খড়মের দ্রুত আওয়াজ—‘ওকে আগে একটু কোরামিন দাও, কোরামিন দাও, দশ পনের ফোঁটা। নেই? তোমাদের বাড়িতে কি কিছু থাকে না? কলি, ফোনটা করেছো? সে কি? হাত কাঁপছে, দাও, আমায় দাও, সামান্য একটা কাজও কি মেয়েদের দিয়ে হবে না?—হ্যালো, সেনগুপ্ত, সেনগুপ্ত আমি কাশীনাথ। ‘কাশী, ছেলের বোধহয় স্ট্রোক হচ্ছে, করোনারি, শিগগিরই এসো, দেরি নয়।’
ডাক্তার এসে মৃত্যু-যন্ত্রণার অন্তিম পর্ব দেখলেন। অক্সিজেন-সিলিন্ডারটা পৌঁছলো প্রয়োজনের ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে। ততক্ষণে সব শেষ।
তিন মাস কাবার হয়ে চার মাসে পড়ল সময়। আকস্মিক এই মৃত্যুর সীমাহীন আতঙ্ক ও বীভৎসতা এখনও পর্যন্ত বন্দনাকে বোবা করে রেখেছে। প্রস্তরীভূত। জড়বৎ। শুধু মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত হয়। ঘুমের ঘোরে সে বিছানার চাদর মুঠো করে আঁকড়ে আপ্রাণ চিৎকার করে ওঠে। স্বামীর সেই অমানুষিক যন্ত্রণায় বিকৃত মুখের ছবি, সেই ভয়বিস্ফারিত কেমন যেন অবাক হয়ে যাওয়া শেষ অভিব্যক্তি ঘুমের মধ্যে থেকে থেকে হানা দেয়। শুধু একবার রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে পেরেছিল—‘আমি কি মরে যাচ্ছি বন্দনা? আমি কি সত্যি-সত্যি মরে যাচ্ছি?’
মৃত্যুর জন্য কোনও প্রস্তুতি ছিল না ভদ্রলোকের। কর্মব্যস্ত, পরিপূর্ণ জীবনযাপনে মগ্ন আনন্দমুখর জীবনটার মাঝখানে থেকে মানুষটাকে যেন কেউ নির্মম হাতে ছিঁড়ে নিল।
শুধু স্বামী বলে নয়, অসামান্য প্রিয়জন বলেই নয়, বন্দনা যেন কোনও সম্পূর্ণ তৃতীয়-ব্যক্তির চোখ দিয়ে ঘটনাটাকে দেখতে পায়, এবং দেখে তৃতীয় ব্যক্তি হয়েও যন্ত্রণায় আছাড়ি-পিছাড়ি করতে থাকে। লম্বা-চওড়া, সুঠাম স্বাস্থ্যবান মানুষটা। সব সময়ে হুল্লোড়ে, হাসিতে, আড্ডায় সবাইকে মাতিয়ে রাখত। আত্মীয়মহলে তো বটেই, অফিসে-ফ্যাকটরিতে পর্যন্ত কি জনপ্রিয় ছিল সব কিছু হেসে উড়িয়ে দেবার এই ক্ষমতায়। ওয়ার্কার-মহলের মুখভার, ম্যানেজমেন্ট আগে খুঁজবে ভটচায্যি সাহেবকে। পার্সোনেল-এর দায় তাঁর নয়, জনসংযোগের দায়ও তাঁর নয়, তবু এসব ব্যাপারে কোনও গুরুতর সমস্যা হলে ভট্চায্যির ক্যারিশমার ওপর সবাইকার প্রথম আস্থা। পরিপূর্ণ জীবনের প্রতিমূর্তি যেন। আহা! যখন সব শেষে শুয়েছিল। মুখটা কালো, কার প্রতি যেন দুরন্ত অভিমানে চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে আছে। বন্দনা, আমি কি সত্যি সত্যি মরে যাচ্ছি? সে দৃশ্য দেখে বুকফাটা আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বন্দনা। শুধু বেঁচে থাকার আহ্লাদেই যে অষ্টপ্রহর আটখানা হয়ে থাকত, সেই মানুষটির অকালমৃত্যুর কাছে তার ব্যক্তিগত শোকও যেন নগণ্য।
ভয়ঙ্কর কিছু একটা করতে ইচ্ছে যায়। দৌড়ে গিয়ে চিতায় উঠে পড়া, কিম্বা ছাদের ওপর থেকে লাফ খাওয়া, কিম্বা গঙ্গায় ঝাঁপ, কেরোসিন গায়ে ঢেলে লকলকে আগুনের বেড়ে…। বীভৎস কিছু একটা। তুলসীচন্দন দিয়ে চোখের পাতা দুটি আস্তে বুজিয়ে দিচ্ছেন শাশুড়ি। ছেলের মাথাটি কোলের ওপর আড় হয়ে পড়েছে। সেই শিশুকালের মতো, সন্ধের ঝোঁকে যখন শেলেট-পেনসিল হাতে জাদুর চোখে ঘুম আসত। সারা মুখটা মায়ের চোখের জলে ভেজা। মেজ ছেলে শান্তিপুরের নতুন ধুতি আনছে। ছোট ছেলে কুঁচনো চাদর। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে ছেলেদের বন্ধু-বান্ধবরা ফুল, অগুরু, খই, ফুটো পয়সা। মৃদু গলায় মাসতুত ভাইটি ডাকল ‘বল হরি।’ ‘হরিবোল’ গলা বসে গেছে ভাইদের, তাবৎ শ্মশানযাত্রীর। হরিনাম নয়, পুরুষ কণ্ঠের দুর্লভ কান্না। এক দিক দিয়ে ছেলেকে বার করা হচ্ছে, যে মাত্র ঘণ্টাকয় আগে সুটকেস হাতে এই গেট দিয়েই ঢুকেছিল। আরেক দিক দিয়ে অজ্ঞান অচৈতন্য বউটির দেহ কেউ মাথার দিকে, কেউ পায়ের দিকে, কেউ কোমরের কাছে ধরে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে সাদা, ঠাণ্ডা, খালি ঘরে। ছেলের জন্য ডাকা ডাক্তারের বিদ্যা বউয়ের চিকিৎসায় কাজে লাগছে এবার।
শ্রাদ্ধ? শেষ কাজ। সে তো করতেই হয়। গুরুজনের চোখের ওপর দিয়ে কনীয়ানের প্রেতকার্য। শ্রাদ্ধের দিন বাড়ির যেখানে যত ঠাকুর দেবতার ছবি ছিল সব আছড়ে ভাঙছিল বন্দনা। কোথা থেকে তার শরীরে এত জোর, এত ক্রোধ এল সে জানে না। ময়না ডালের কীর্তন দিয়েছেন কর্তা। সবাই সেইখানে। মাথুর পালায় ভাবাবেশে ঘন ঘন মূর্ছা হচ্ছে মূল গায়েনের, হুঙ্কার দিয়ে চলছে দোহারকি। সেরেস্তা-ঘরে শ্রাদ্ধ-কর্ম। বৈঠকখানায় একদিকে শান্তিপর্ব, আরেকদিকে গীতা পাঠ। পাল্লা দিয়ে চড়ছে, নামছে পণ্ডিতদের গলার স্বর। কাকার কোলে-বসে সদ্য চার বছর অতিক্রান্ত অভিরূপ শ্রাদ্ধ ঘরে। রোগিণীর কাছে তখন কেউ ছিল না। হঠাৎ আছড়ে পিছড়ে কাচ-ভাঙার শব্দে সব এক এক করে ছুটে এসেছিল। কৃষ্ণ, কালী, অন্নপূর্ণা, গুরুদেব যা যা পেয়েছে আছড়ে-আছড়ে ভাঙছে বউ। মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। হাত-ভর্তি রক্ত। বাড়িতে ওর হাতের কাছে সত্যি এতো ঠাকুরের ছবিও তো ছিল। ঠাকুরের ছবি ঘরে রাখলে, ঘর নিরাময় হয়, সুখে-শ্রীতে উছলে পড়ে সংসার এই বিশ্বাস। ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল দিনের পর দিন। সেই অসহায় নিদ্রার মধ্যে দিয়েই পাড়া ভেঙে ব্রাহ্মণ ভোজন হল। বাড়ির বড় ছেলে, রাজার মতো ছেলে গেছে, কেউ যেন বাদ না যায়। সে যা-যা খেতে ভালোবাসত তা সবাই খাক। বিশ্বাত্মা পরিতৃপ্ত হোক। তারপর এঁরা সব মাছ-হাত, মাছ-মুখ করলেন সাতাশ বছরের অচৈতন্য উন্মাদিনী শাঁখা ভেঙে, লোহা খুলে, হা-হা সিঁথি, শুকনো-মুখ, সাদা-কাপড়ে পরিত্যক্ত ভিখারিণীর শবের মতো পড়ে রইল একধারে। এই বিয়োগান্ত সামাজিক নাটকের আসল নায়ক যে এই নায়িকা এই রুক্ষকেশী, ধূম্রলোচনা, ধূমাবতী এ কথা কুশীলবদের কারও খেয়াল রইল না।
দিনের পর দিন। সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকাল নিত্যকর্ম হল ঘুম। ঘুম, ঘুম আর ঘুম। যাতে কোনও ছিদ্রপথে শোক ঢুকে না পড়ে তার চূড়ান্ত ডাক্তারি ব্যবস্থা। শরীর রক্ষার জন্য এক ঘুম থেকে জেগে উঠে আরেক ঘুমে চলে যাবার হাইফেন-সময়ে সামান্য কিছু খেয়ে নেওয়া, স্নায়ুতন্ত্র ভয়ঙ্কর বিচলিত থাকায় সেই খাবারও প্রায়শই বমি করে ফেলা। অতঃপর দুর্বল ঘুরন্ত মাথা, টলমলে দেহটাকে টেনে এনে আবার শয্যায় ফেলে দেওয়া। সবাই ভেবেছিল এ জীবনটাও বরবাদই হয়ে গেল বুঝি। বাড়ির প্রথম শিশুটির বুঝি সম্পূর্ণ অনাথ হতে আর দেরি নেই। শুধু বুড়ো ডাক্তার সেনগুপ্ত মাথা নেড়ে নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন: ‘ভরা যৌবনের জীবন, তার ওপর স্ত্রী-শরীর, এতো আদরের শরীর, যত্নের স্বাস্থ্য, ও কি সহজে যায় মা!’
একদা একদিন এইরকম ওষুধ-ঘুম থেকে সহসা জেগে উঠে বন্দনা বুঝতে পারছিল না সে কোথায়। তার চোখের সামনে তখন একটা ফিকে নীল পট। তাতে লম্বা কালোকালো ডোরা আর মাঝে একটা ছোট্ট কালো বল। কিছুই মাথায় নিচ্ছিল না। মাঠ তো সবুজ হয়! নীল মাঠ? ডোরাগুলো কি? ওই বল কোন খেলার? কোন খেলুড়ির? কখন সে খেলা শুরু হবে? দুর্বল মস্তিষ্কে এই সব অস্ফুট প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল। তারপর একটা খয়েরি চিল, যাকে বন্দনার চোখে কালোই দেখাল, হঠাৎ বাচ্চা ঘোড়ার মতো তীব্র হ্রেষাধ্বনি করে ঝপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা কালো ফুটকির ওপরে, বন্দনা সহসা বুঝতে পারল এটা চিল, ওটা পায়রা, দলছুট বেচারা পায়রা, নীল বিস্তারটা মাঠের নয়, আকাশের। ডোরার মতো দেখতে ওগুলো গরাদ। সংসার কারাগৃহের লৌহগরাদও বটে আবার পঁয়তাল্লিশ নম্বর শ্যামবাজার স্ট্রিটের দোতলার ঘরের দক্ষিণের জানলার গরাদও বটে।
এই সময়ে ছোট কালো বলটা নড়েচড়ে উঠল। খোঁচা খোঁচা চুলে ভরা একটা ছোট্ট শিশু মাথা। ওর বাবা নেই। মা থেকেও নেই। বিশাল সংসারে ছোট্ট পাঁচ বছরের রূপ একা। এখনও সেই ঘর সেই-ই আছে। কিন্তু হায়, আশ্রয় নেই আর। রূপ সেই প্রচণ্ড প্রতারণার দিকে মহানির্বেদে পেছন ফিরে কিসের প্রত্যাশায় আকাশমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে জানে না। ভীষণ রোগা। কাঁধের হাড় দুটো উঁচু হয়ে আছে। কচি মাথাটা কুচকুচে কালো কদমছাঁট চুলে ছাওয়া। বন্দনার ঠিক পায়ের কাছে খোলা জানলাটা। তার ফ্রেমে আটকে আছে আকাশ। স্তূপের পর স্তূপ মেঘপাহাড়। একটা স্তূপের ওপারে সূর্য। আলোর ছটা বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে সারা আকাশ জুড়ে। পাহাড়-পর্বতের মাথা জাগানো সেই আকাশ-সমুদ্রে সাঁতার কাটছে একলা স্বভাবের চিল, ঘুরপাক খাচ্ছে তীব্র শিসের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দলবদ্ধ পায়রা।
এই ছবিটা বোধহয় বন্দনার চিরকাল মনে থাকবে। উদার আকাশের পটে পিং পং বলের মতো একটি শিশুমস্তক। একদিকে বিরাট আর একদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। কী অনন্ত, অবাধ! কী সীমাবদ্ধ, ভঙ্গুর, কী শক্তিহীন!
বুকের মধ্যে যেন বাঘে আঁচড়াচ্ছে। বন্দনা খাট থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে হোঁচট খেলো, বুঝতে পারল তাড়াতাড়ি চলাফেরা করার শক্তি তার নেই। আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। রূপ প্রথমে বুঝতে পারেনি কে। মা প্রাণপণে তার চোখ টিপে ধরে আছে।—‘কে?’ আঃ ছাড়ো না! কে? ছোট্ট অভিরূপ চিলের গলায় চেঁচায়। কেমন বিরক্ত, খ্যাপাটে সুর।
—‘ভাল্লাগছে না বলছি, ছাড়ো! ছাড়ো না!’
বন্দনা ওর চিবুকটা ধরে আস্তে আস্তে সামনে ঘোরায়। মাতৃস্পর্শ ভুলে গেছে ছেলেটা। আসলে মাতৃস্পর্শ-মাতৃগন্ধ তো কোনও অলৌকিক ব্যাপার নয়, চুড়ির রিনিঝিনি, বিশেষ পাউডার বা মাথার তেলের গন্ধ সমস্ত মিলিয়ে মাতৃ-আবহ। বন্দনাকে দেখে অবাক হয়ে তাকাল, তারপর তার ছোট্ট দুটো তুলতুলে ঠোঁটে হঠাৎ জোয়ার এল। বন্দনা দেখছে ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে, চোখের কূল ভরে ভরে উঠছে। ছেলের মুখ বুকের মধ্যে গুঁজে নিয়ে বন্দনা মনে মনে বলল—‘ঈশ্বর যদি না-ই থাকেন, রূপু তোর আমি আছি। বিশ্বজননী যদি তাঁর কর্তব্য ভুলে যান, তোর এই শক্তিহীন মা একাই সংগ্রাম করবে।’ রূপ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার মায়ের মনে হল ও যেন শুধু অভিরূপই নয়, অভিমন্যুও। নির্মম বিশ্বপ্রকৃতির হিংস্র হাতের মুঠোয় অসহায় মানুষ। বলছে—‘আমাকে কেড়ে নিও না। পৃথিবী বড় সুন্দর। আমাকে আর একটু বাঁচতে দাও।’ দাঁতে দাঁত চেপে বন্দনা বলে—‘আমাকে শেষ না করে তোকে কেউ আর নিতে পারবে না। একবার হেরেছি তাই বলে কি বারবার হারব?’
অধ্যায় ২
—‘মা!’ দেশ থেকে-আসা রাশীকৃত তেঁতুল কুটে কুটে জড়ো করছিলেন দুই জায়। কিছু হবে ছড়া-তেঁতুল, কিছু হবে তেঁতুলের কাই-আচার। তাছাড়াও অম্বলে, রান্নায়, বাসন-মাজার…সারা বছরের ব্যবস্থা। ডাক শুনে চমকে মুখ তুলে তাকালেন।—‘ওকি বউমা, তুমি! কি দরকার? ডাকলে না কেন? নিচে নামলে কি করে? কি সর্বনাশ, যদি পড়ে যেতে।’ শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন শাশুড়ি। আঁচল খসে পড়ল চাবিশুদ্ধ ঝনাৎ করে।
—‘পড়ে যাব কেন? রূপু বলছে খিদে পেয়েছে।’ কেমন শূন্য চোখে তাকাল বন্দনা,—‘এখন ও কি খায়?’
সব ভুলে গেছে ও। ছেলে কখন খায়, কি খায় কিচ্ছু মনে নেই। দুজনে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, শেষে কাকিমা বললেন,—‘এই তো মা, এক্ষুনি চান করেই ভাত খাবে। এখন তো আর কিছু খায় না। বায়নাদেরে হয়েছে তো খুব। দাঁড়াও আমি দেখছি।’ কাকিমা বঁটি কাত করে রাখলেন।
বন্দনা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—‘না, না, বায়না করেনি, খিদে পেয়েছে ওর। আমি চান করিয়ে দিচ্ছি কাকিমা। তার আগে খাওয়ার মতো কিছু নেই?’
কাকিমা তাকালেন বড় জায়ের দিকে, চিন্তিত মুখ। শাশুড়ি বললেন—‘আচ্ছা একটা কমলালেবু দিচ্ছি, এইটে খেতে বল ততক্ষণ। অন্য কিছু খেলে খিদে নষ্ট হয়ে যাবে।’
লেবুটা হাতে করে সিঁড়ির দিকে এগোল বন্দনা। সে যেন নতুন করে হাঁটতে শিখছে। তার ননদ কলি নেমে আসছে দোতলা থেকে। তরতর করে। দুদিকে দুবেণী। কাঁধে ব্যাগ, কলেজ যাচ্ছে নিশ্চয়ই। সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল—‘বউমণি, তুমি যে নিচে নেমেছ? কখন উঠলে? কখনই বা নামলে? খোকামণি কোথায়?
বন্দনা লেবুটা তুলে ধরে কৈফিয়তের সুরে বলল—‘এই যে, খোকার জন্যে লেবু নিয়ে যাচ্ছি। ওর খিদে পেয়েছে।’ কিরকম যেন বাচ্চা, ভীতু বালিকার মতো কথাগুলো। অসংলগ্ন।
কলি বলল—‘এস বউমণি, আমি তোমায় ওপরে পৌঁছে দিই।’
—‘তোমার কলেজের দেরি হয়ে যাবে না?’ রেলিং ধরে ধরে আস্তে আস্তে উঠতে উঠতে বন্দনা বলল—‘আমি ঠিক উঠতে পারব।’
কলি একবার ওপরে তাকাল, একবার নিচে। আর দেরি করলে সত্যিই ফার্স্ট পিরিয়ডটা মিস হয়ে যাবে। লেকচারের মাঝখানে ক্লাসে ঢোকা একদম পছন্দ করেন না এ কে বি। সে দু তিনটে সিঁড়ি টপকে এক লাফে নিচে নামল, আবার পেছন ফিরে তাকাল—‘বউমণি ধরে ধরে যাও। মাথা ঘুরে গেলে মুশকিল হবে। আমি আসছি তাহলে।’
বউমণিকে দেখলেই আজকাল কেন কে জানে বড়দার বিয়ের দৃশ্যগুলো মনে পড়ে যায়। বাসি বিয়ের দিন সন্ধেবেলায় রান্নাঘর থই-থই করছে অন্ন-ব্যঞ্জনে। বিশাল একটা রুপোর থালায় সব কিছু-কিছু উঠেছে, রুপোর বড় মেজ, সেজ, রাঙা, ফুল, ছোট বাটিতে হরেক ব্যঞ্জন। বড় রুই মাছের মুড়ো ল্যাজা। বাটি থেকে উঁচিয়ে রয়েছে। পায়েসের সুগন্ধে রান্নাঘর ম’ম। রান্নাঘরে বামুন ঠাকুর, মা, কাকিমা। চাঁদের আলো রঙের শাড়ি, লাল ব্লাউজ, এক গা গয়না পরে নতমুখে বউমণি এসে দাঁড়াল। মা বললেন—‘দ্যাখো বউমা, চোখ চেয়ে দ্যাখো ভালো করে, এই সব তোমার। তোমার রসুইঘর। তোমার অন্ন। তোমার ব্যঞ্জন। তোমার কল্যাণে এইরকম রোজ রোজ হবার সামর্থ্য হোক আমার খোকার।’ কাকিমা হেসে বললেন—‘মনে মনে “উইশ’’ করো।’ মা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—‘উইশ-ফুইশ আবার কি রে ছোট গিন্নি? একটি বর আমরা ওকে দিয়েছি, আর দুটি বর ও দেব্তাদের কাছ থেকে আমাদের জন্যে মেঙে নিক।’
—‘তা ও পারবে, যা লক্ষ্মীমন্ত বউ তোমার,’ কাকিমা বন্দনার থুতনিতে আদর করে বলেছিলেন। পেছনে কখন বড়দা এসে দাঁড়িয়েছে। বরেরা তো বাসিবিয়ের দিনেই বউয়ের পেছনে সবচেয়ে বেশি ঘুরঘুর করে! তা বড়দা বলল—‘আর বর চেয়ে আমাকে ফ্যাসাদে ফেলে কাজ নেই। এই সমস্ত রান্না যদি রোজ হয় তাহলে ফার্স্ট থিং তো মা আর কাকিমাকে সারাক্ষণ হেঁশেলেই কাটাতে হবে, আর এই সব খেয়ে কলিটার এইসান পেট ছাড়বে…’
কলি প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে উঠেছিল—‘আহা, খালি আমারই, না? আর সবার বুঝি সোনায় গড়া পেট?’
বড়দি বলল—‘তুই আর সরু গলায় চেঁচাসনি। একেই তো সানাইয়ের প্যাঁপোঁয় কাজ-কর্ম করা দায় হয়ে উঠেছে। কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছি না। এই দাদা, তুই এখন এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন রে? কালরাত্রির দিন বউয়ের মুখ দেখলে কি হয় জানিস?’
—‘কি হয় বল না রে খুকি! তুই একটা অথরিটি লোক। আমাদের একটু শেখা-টেখা!’
—‘খবর্দার ঠাট্টা করবি না। কি হয় মুখে উচ্চারণ করতে নেই, তা জানিস? যা যা ভাগ এখান থেকে, ভাগ বলছি।’
কাকিমা এই সময়ে বললেন—‘না, না, জন্মের ভাত-কাপড়টা ওকে দিয়ে দিইয়ে দাও, নিয়ে-টিয়ে বন্দনা বউ একেবারে ঘরে যাক।’
ফুলকাটা পেতলের ট্রেতে করে সুতরাং কাপড় এল, সেটা দু আঙুলে তুলে দাদা বলল—‘জন্মের ভাত কাপড়? বাব্বাঃ বাঁচা গেল। এই নাও বাবা, জন্মের মতো দিয়ে দিলাম। এরপর একদম ফ্রি।’
বউমণি মুখ নিচু করে মিটিমিটি হাসছে। বড়দি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—‘ফিচলেমি হচ্ছে, না? এটা সিম্বলিক তা জানিস। সারা জীবন যত অন্ন বস্ত্র লাগে সবই দিতে হবে। এক্সট্রাও অনেক দিতে হবে। জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, আরও নানান খানান আছে, সে সব এখনই ফাঁস করছি না। কি বল, বন্দনা?’
দাদা ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলেছিল—‘যাক তোদের সিম্বলে যখন শাড়ি দিয়েছিস, শাড়ির ওপর দিয়েই যাবে শুধু, তারপরই ফ্রি।’—‘কিসের অত ফিরি ফিরি করছিস রে মুখপোড়া?’ পিসিমা এসে পড়েছেন। পিসিমা এসে না দাঁড়ালে যজ্ঞিবাড়ি ঠিক জমে না। বললেন—‘তুই আর ফ্রি নেই। আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেছিস, বুঝলি?’
কলি রাস্তা পার হয়ে বাস স্টপে এসে দাঁড়াল। অনেক দিন সে ভালো করে বউমণিকে দেখেনি। নিজের ঘরে শুয়ে বসে থাকে, বাইরে বেরোয় না, বউমণির এই অসুখ, এই বিষাদকে কলি ভয় পায়। খোকামণি তার কাছে একবার, খুড়তুত বোন মিলির কাছে একবার খায়, মায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়ে, কাকাদের ছায়ায় ছায়ায় ঘোরে। ওকে স্কুলে দেবার কথা হচ্ছে। কিছুটা সময়ও অন্তত সমবয়সী বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে ভুলে থাকবে। কিন্তু বাড়িশুদ্ধ সবাই যেন আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছে বউমণি বলে একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষ এখানে আছে। সে কি ছিল, আর কি হয়েছে! আজ সিঁড়ি দিয়ে তাকে টলতে টলতে উঠতে দেখাটা কলির কাছে একটা মস্ত ধাক্কা। ও যে এমন হয়ে গেছে, এত রোগা শ্রীহীন, একটা রঙচটা কাঁচকড়ার পুতুলের মতো তা কলি আগে খেয়াল করেনি।
কনডাকটর বলল—‘টিকিট দিদি টিকিট।’
নামবার সময় হয়ে এসেছে, কলি তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে পয়সা বার করে দিল। একদম অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।
‘কলি, তুমি শাড়ি পরতে ভালোবাস?’ নতুন বউদি সামনে একগাদা সিল্কের শাড়ি মেলে বলছে। চোদ্দ বছরের কলি সবে শাড়ি ধরেছে, বাইরে শাড়ি, বাড়িতে ফ্রক, এখনও সামলাতে পারে না, কিন্তু শাড়ি তার প্রাণ, ঘাড় নেড়ে বলছে—হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ।
—‘এইগুলোর থেকে যেটা ইচ্ছে বেছে নাও।’
সবচেয়ে সুন্দরটা, লাল-নীল-হলুদ ফুল ফুল ঝকঝকে জমকালোটা কলি বেছে নিচ্ছে। মেজদা বসে বসে বউদির সঙ্গে গল্প করছিল। নতুন বউয়ের সঙ্গে গল্প করতে সবারই ভালো লাগে। সে বউ যদি আবার এমনি শিক্ষিত, এমনি হাসি-খুশি, রসিক, এমনি মিষ্টি হয়। মেজদা বলল—‘এ হে হে হে, কলি, টিকেয় আগুন হয়ে যাবে যে রে শেষটায়।’ বউমণি বলে উঠল—‘এ কি কথা মেজদা! কলি তো একদমই কালো না। তাছাড়াও চাপা রঙে লাল খুব সুন্দর খোলো।’
কলি মুখ গোঁজ করে বসে আছে। নেবে না ওই শাড়ি, কিছুতেই না। মেজদা বললে—‘পাচ্ছিস নিয়েই নে। সেই কবে তোর বর দেবে তার জন্যে হত্যে দিয়ে বসে থাকাটা কি ঠিক?’
—‘কেন দাদারা বুঝি দিতে পারে না?’ বউমণির চোখে ছদ্ম তিরস্কার।
—‘আরে সেই কথাই তো বলছি।’
—‘আরে সেই কথাই তো বলছি। আমার কাছে লবডঙ্কা। আমার বউ এলেও আগে থেকে বলে দেবো, এ বাড়ির বড়বউ একটা শাড়িছত্রের গোলমেলে প্রিসিডেন্ট ক্রিয়েট করে গেছেন, তুমি যেন সেইমতো চলো না, নৈব নৈব চ।’ মেজদা হাসতে হাসতে বলছে কিন্তু কলির গায়ে যেন হুল ফুটছে। সে কি ভিখারি? চাইতে এসেছে? বউমণি ভালোবেসে দিচ্ছে তাই। সে-ও বউমণিকে দেবে। বউমণি রেগে গেছে—‘মেয়েদের ব্যাপারে কেন নাক গলাতে আসেন বলুন তো? আপনি এখন যান। আমরা দুজনে এখন সব গুছিয়ে তুলব। হয় যান, নয় বসে বসে দেখুন। একটাও কমেন্ট নয়। আর আপনার বউ আপনার হাতে পড়বার আগে আমাদের হাতে পড়বে, তখনই তাকে যা শেখাবার শিখিয়ে দেবো। কি বল কলি?’
চার দাদার কোলের বোন। বড়দার পরে অবশ্য বড়দি। একেবারে পিঠোপিঠি। কিন্তু কলির প্রায় শৈশব অবস্থায় বড়দির বিয়ে হয়ে গেছে। চার দাদার যত আদর, যত ঠাট্টা-ফাজলামি সব কলিকে নিয়ে। এমন পেছনে লাগত যে কাঁদিয়ে ছেড়ে দিত। মেজদাকে বার করে দিয়ে বউমণি দরজায় খিল তুলে দিল, বলল—‘নাও, এবার নাও।’
—‘নেওয়ার কি আছে বউমণি, থাক না তোমার আলমারিতে। যখন দরকার হবে তখন পরব,’ কলির অভিমান এখনও যায়নি।
—‘সে তো পরবেই। আলমারির সব শাড়িই যখন দরকার হবে পরবে। একটা তোমার নিজস্ব করে নাও। নাও কলি, লক্ষ্মীটি, না হলে আমি ভীষণ দুঃখ পাব।’
—‘তাহলে তুমি বেছে দাও। আমি তো বুঝতে পারি না। কোনটা আমাকে মানাবে দেখে দাও।’
‘ঠিক? আমিই বেছে দিই তাহলে?’ বউমণি শাড়ির স্তূপের মধ্যে থেকে সেই লাল-হলুদ-নীল ফুল ফুল মিষ্টি শাড়িটাই তুলল। বলল—‘এইটাই সবচেয়ে মানাবে তোকে কলি। এমন চকচকে আয়নার মতো রং, পরে একেবারে লাল হয়ে উঠবি।’
তারপর খুড়তুত বোন মিলি এল। মিলি শাড়ি পছন্দ করল। তিনজনে মিলে বউমণির ঢাউস দুটো আলমারি গোছানো হল।
সেই কাশ্মীরি সিল্ক পরে বড়দার মৃত্যুর পরও বন্ধুর বিয়েতে গেছে কলি। সবাই বলেছে, ‘কি সুন্দর, কি অপূর্ব দেখাচ্ছে তোকে, কোথাকার সিল্ক রে? কোথা থেকে কিনেছিস? ও কি তোর চোখে জল কেন রে কলি? দাদা দিয়েছিলেন, না? বড়দা!’ কলি মাথা নাড়ছে। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে মেক-আপ নষ্ট হচ্ছে, অস্ফুট গলায় বলছে—‘বউদি, আমার বউমণি দিয়েছিল রে।’
বন্ধুরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দাদার স্মৃতি হলে কান্নার মানে বোঝা যায়, বউদি তো আর মরে যায়নি রে বাবা! চন্দনা বলে—‘নে, নে, বর দেখবি চল। মোছ চোখের জল। ইস কাজল বাঁচিয়ে। বর যা হয়েছে না? দেখে আমিই এইসান একসাইটেড হয়ে গেছি যে আমারই টপ করে বিয়ে করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে।’
কলির ভালো লাগে না। বউমণি মরে যায়নি। কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকারও তো কোনও মানে হয় না। শুষ্ক প্রেতিনীর মত, একাম্বরা, রুক্ষ চুল, হাঁটতে পারছে না, হাঁপাচ্ছে, ওষুধ খেয়ে খেয়ে চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। সেই উজ্জ্বল, হাসিখুশি, নিতান্ত সরল, আমুদে বউমণি যে তাদের সবাইকে বিশেষ করে তাদের দুই বোনকে এতো ভালোবাসত!শনিবার ম্যাটিনি শো-এ সিনেমা যাওয়া মানেই সে, মিলি আর বউমণি, লুকিয়ে লুকিয়ে রেস্টুরেন্টে খাওয়া, ‘শ্রী’তে যাবার নাম করে এক এক দিন মেট্রো, কি লাইটহাউজে চলে যাওয়া, তারপর ট্যাক্সি করে হুশ, শ্রী সিনেমার কাছে এসেই তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি। বউমণি বলবে—‘এখানেই ছেড়ে দিই। কি বল?’
ট্যাকসিটা চলে গেলে রাস্তার ওপর তিনজনের কি ধুম হাসি।
—‘এই শ্রী-তে কি হচ্ছে ভালো করে দেখে রাখ। এই মিলি তুই ঠিক উল্টো-পাল্টা করবি।’
—‘আমি না, আমি না, দিদি, কলি।’
বাড়ি ঢুকতেই চায়ের গন্ধ। সাড়া পেয়ে কাকিমা বলছেন—‘বাঃ খুব তাড়াতাড়ি এসে গেছ তো বন্দনা বউ! যা রে কাপড় বদলে আয় সব, চা হয়ে গেছে।’
তিনজনে মিলে দুদ্দাড় ওপরে, মাঝে বউমণির ঘর। বড়দা আসতে এখনও দেরি আছে। ঢুকে তিনজনে বিছানায় গড়িয়ে পড়ছে হাসতে হাসতে বন্দনা বলছে—‘ট্যাকসির কথাটা জানলে কাকিমা কি বলবেন?’
কলি বলছে—‘তিন মেয়েতে মিলে একলা একলা নীরাতে ঢুকে খেয়ে আসার কথাটা?’ আবার হাসি।
—‘ইটালিয়ান ক্যাসার্টটা কি দুর্দান্ত, না?’
—‘সাঙ্ঘাতিক। বউমণি ওই পাতলা বিস্কুট তো আমি ডেকোরেশন বলে ফেলেই দিচ্ছিলুম।’
—ওকে ওয়েফার বলে। ডেকোরেশন তো বটেই। কিন্তু সব ডেকোরেশনই শেষ পর্যন্ত পেট্টায় নমো করবার। কেকেও তো চেরি থাকে, আইসিং থাকে, সেগুলো ভেঙে ভেঙে খাস না?’
—‘আইসিং কি গো?’
—ওই যে রে সাদা সাদা নকশাগুলো।
—‘হ্যাঁ খাই তো। আমাদের দোলের মঠের বিলিতি সংস্করণ বলো?’
—বউমণি, আবার কবে বেরোবো।’
খোকামণিকে বেড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরছে রতন। ভালোমানুষের মত মুখ করে বন্দনা বলছে—‘কোথায় রে? শ্রী না চিত্রা?’ যেন কিছু বুঝতে পারছে না দুই ননদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে।
—‘না, না,’ মিলিটা অধৈর্য হয়ে উঠেছে—‘না, না বউমণি, এসপ্লানেড, এসপ্লানেড। মেট্রো, নিউ এম্পায়ার, লাইটহাউজ, গ্লোব।’
—‘বাস রে বাস। কি লম্বা লিস্টি দিচ্ছিস!’
—‘ইঃ রে আমার! ইংরেজি ছবি বুঝতে পারিস?’ কলি বলছে।
—‘সব কথা বোঝবার দরকার হয় নাকি? তুই বুঝেছিস? কি অপূর্ব ছবিটা বলতো আঃ ‘গন উইথ দা উইন্ড,’ ওঃ বউমণি রেট বাটলারকে যদি হাতের কাছে। পেতুম!’
—‘কি করতিস?’ বউমণি হাসছে।
—‘উঃ কি যে করতুম!’ হাত মুখ সব মিলিয়ে মিলি একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে।
—‘তুই কলি?’
—‘স্কার্লেটটার মতো বোকামি অন্তত করতুম না!’
আবার তিনজনের হু হু হাসি।
—‘বউমণি তোমাকেও বলতে হবে। ওসব চলবে না।’
—‘এই খবর্দার, বন্দনার চোখে-মুখে চাপা হাসি, ‘আমার রেট বাটলার এসে গেছে।’
হাসতে হাসতে দরজার খিল খোলা হচ্ছে, বড়দার মাথার চুল এলোমেলো, ভারি ব্যাগটাকে টেবিলে রাখতে রাখতে বলছে—‘এতো হাসি কিসের, অ্যাঁ? অ্যাত্তো হাসি? এই মিলিয়া, কলিয়া, আমার বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করছিস রে তোরা!’
বেশি দিনের কথা নয়, মাত্রই বছরখানেক। অথচ মনে হয়, কতদিন, কতদূর, কোন গতজন্মে কিংবা স্বপ্নে এসব ঘটেছিল বোধহয়। এখন কলি মায়ের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে এসপ্লানেড পাড়ায় যায়, মাঝে মাঝে। কিন্তু তেমন জমে না। বন্ধুদের হই-হুল্লোড়ের মাঝখানেও হঠাৎ-হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। বউমণির শাড়ির গন্ধ, চুলের গন্ধ, মোড়ের দোকান থেকে তবক দেওয়া পান কিনে তিনজনে খাওয়া আর হাসা। তিন ননদ-ভাজে। তিন অসম বয়সী বন্ধু মিলে। ‘গন উইথ দা উইন্ড’, ‘গ্যাস লাইট’, ‘জোয়ান অফ আর্ক …।’
—‘এই কলি, কলি তোর রোল কল করছেন।’
—‘হানড্রেড অ্যান্ড ফাইভ। কলিকা ভট্টাচার্য,’ স্যারের চোখ সোজা কলির মুখের ওপর। মুখ চেনেন, নামও জানেন। বসে রয়েছে ক্লাসে, অথচ জবাব দিচ্ছে না। এম. এ ক্লাসে ক’টাই বা মেয়ে, সবাইকার বায়ো-ডাটা স্যারেদের নখদর্পণে। স্যারের মুখে বিরক্তি, বিদ্রূপ। —‘হ্যাললো শকুন্তলা, আর য়ু থিংকিং অফ ইয়োর দুষ্মন্ত?’ ক্লাসশুদ্ধ ছেলে-মেয়ে অসভ্যের মতো হাসছে। হো-হো করে। কলির মুখ লজ্জায় নিচু। লজ্জায়, অপমানে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে আর কোনদিন এ. কে. বির ক্লাস করবে না। কোনদিন না। তখন বুঝবেন একঘর ছেলের মাঝখানে এরকম নিষ্ঠুর নির্লজ্জ ঠাট্টা করবার ফল কি। সবাই হাসছে কলি বুঝতে পারছে। একমাত্র তার মুখোমুখি বেঞ্চে ছেলেটি নির্বিকার। মুখ সামান্য বিরক্তিতে কুঁচকে আছে। পরিমল। অনুরাধা পাশ থেকে কনুইয়ের গুঁতো দিচ্ছে। —‘এই কলি, এই, দ্যাখ পরিমল রেগে গেছে। তোর হয়ে। অন ইয়োর বিহাফ। য়ু শুড বি গ্রেটফুল। হি, হি।’ অনুরাধা ইংলিশ মিডিয়াম থেকে এসেছে, কথায় কথায় ইংরেজি বলে, ছেলেদের সঙ্গে মেশেও খানিকটা, নানারকম খবরাখবর সংগ্রহ করে আনে। কারুর কোনও ভাবান্তর ওর চোখ এড়ায় না।
ক্লাস শেষ হতে সে কলিকে ঠেলতে ঠেলতে পরিমলের পাশ দিয়ে বার করে।
—পরিমল বলছে—‘আমি দুঃখিত। ক্ষমা চাইছি।’
কলির মুখ লাল। কিছু বুঝতেও পারছে না, বলতেও না।
অনুরাধা হাসছে—‘কিসের ক্ষমা? কেন ক্ষমা?’
—‘এ. কে. বির হয়ে। ওঁর রুচিবিরুদ্ধ উক্তির জন্যে। আই অ্যাম অ্যাশেমড অফ হিম।’ কলি পালাতে পারলে বাঁচে। পরিমলের সামনে থেকে। অনুরাধার পাশ থেকে।
পরিমল ধুতি শার্ট পরা, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। খুব গম্ভীর। হাসলে দাঁত দেখা যায় না। খুব দায়িত্বশীল, ভদ্র এবং পরিচ্ছন্ন। সিগারেট টানে না। মাঝে মাঝে খুব গভীর দৃষ্টিতে কলির দিকে চেয়ে থাকে। এটা অনুরাধার আবিষ্কার। প্রথমে অনুরাধা ভেবেছিল, সে-ই এই জরিপের লক্ষ্য। তাই একদিন অন্য বেঞ্চে বসল। সেদিনই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। পরিমল মুখুজ্জের নিরীক্ষণের বিষয় স্মার্ট, চোখে-মুখে কথা বলা, তুখোড় মেয়ে অনুরাধা নয়, শ্যামলা, লাজুক, মুখচোরা কলিকা ভট্টাচার্য। অনুরাধা বলে—‘ডাক্তারি পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছে। এসে এখন আর্টস-ক্লাসে জুটেছে রে কলি, তুই কি মাটিয়া কলেজের সামনে দিয়ে রোজ যাতায়াত করতিস না কি?’
অধ্যায় ৩
পঁয়তাল্লিশ নম্বরের বাথরুমে শাড়ি নিয়ে ঢোকার চল নেই। হয় ভিজে কাপড়ে আসতে হবে। নয়তো শুদ্ধু কাপড়ে অর্থাৎ একখানা মটকার কাপড় আছে, তাই পরে। এই মটকার কাপড় না-কাচা, ময়লা এবং অনেকজনের পরা হলেও সবসময়ে পবিত্র। কেন তার যুক্তি খুঁজতে যাওয়া বৃথা। ভিজে-কাপড়ে বেরোতে বন্দনার বরাবর লজ্জা করে। ব্যাটাছেলে কারুর সামনে পড়ে গেলে তো কথাই নেই। মেয়েদের বিশেষত গুরুজনদের সামনে পড়লেও বিশ্রী অস্বস্তি হয়। একখানা মটকার কাপড়, ব্লাউজ নয়, পেটিকোট নয়, শুদ্দু কাপড় সারা গায়ে ব্যান্ডেজের মতো জড়িয়ে দোতলার কোণের বাথরুম থেকে দালানের মাঝবরাবর নিজের ঘরে আসত সে। স্নানের সময়টাও নিজের ইচ্ছে এবং সুবিধে মতো হলে চলবে না। সকালে উঠে বাসিমুখ ধোয়ার পরই চান-টান করে নেওয়া এ বাড়ির নিয়ম। চান সেরেই বাইরে বেরিয়ে দেখতে হবে ব্রাশ মুখে, গামছা কাঁধে মেজদা কি ছোড়দা দাঁড়িয়ে। কি যে অপ্রস্তুত অবস্থা। ওর জড়োসড়ো ভাব দেখে একদিন অভিমন্যু বলেছিল—‘একটা বিদ্রোহের স্লোগান ছেড়ে দেবো নাকি ভট্চায্যি বাড়িতে?’
—‘কিরকম স্লোগান?’
—‘কলঘরেতে বউমেয়েদের জামাকাপড় নিয়ে যেতে দিতে হবে দিতে হবে।’
—‘সর্বনাশ। তাহলে রান্নাঘর খাবার ঘরে ঢোকা একদম বন্ধ হয়ে যাবে যে! অচ্ছুৎ হয়ে যাব!’
—‘তবে? পুরুষমানুষদের কলঘর আলাদা করতে হবে করতে হবে।’
—‘করতে হবে, করতে হবে করে না চেঁচিয়ে নিজেই করে দাও না।’
সেই দক্ষিণ দিকে নিচ থেকে পিলার তুলে দ্বিতীয় স্নানঘর তোলবার তোড়জোড় হল। বন্দনার ঘরের ঠিক পাশে খানিকটা ফাঁকা দালান আছে। তারপর কলিদের পড়ার ঘর। এইটুকুর সঙ্গে বাইরে থেকে খানিকটা যোগ করে বেশ বড়—বাথটব, বেসিন, কমোড, শাওয়ার-অলা টালিবসানো, এক আধুনিক বাথরুম। হঠাৎ, আধখানা পিলার তোলার পর শ্বশুরমশাই সেটা বন্ধ করে দিলেন। ঘরের লাগোয়া বাথরুম অস্বাস্থ্যকর। অরুচিকর, অশুচি। পিলারগুলো এখনও বেকার পড়ে রয়েছে। লোহার শিকগুলো জড়িয়ে মাকড়সার জাল। কলঘর থেকে মটকার সেই কাপড় জড়িয়েও এখন আসা যায় না। সেটার চওড়া লাল পাড়। বন্দনা ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে বুকের ওপর আড়াআড়ি তোয়ালে ফেলে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি আলনার দিকে গেল। একি? আলনার ওপর এই টুকটুকে লাল শাড়িটা কে রাখল? লাল জমি। তাতে ঢালা সোনালি জরির পাড়। সোনার পাতের মতো চকচক করছে। ভেতরে ছোট ছোট বুটি। এই শাড়ি অভিমন্যু শেষ বিবাহবার্ষিকীতে উপহার দিয়েছিল। মাত্র সেইদিনই পরা হয়েছিল। পরে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোঁরায় দুজনে খেতে যাওয়া হয়েছিল। ফেরবার সময়ে ফ্লুরি থেকে ছেলে এবং বোনেদের জন্যে একগাদা চকোলেট, পেস্ট্রি। পাটভাঙা শাড়িটা ইস্ত্রি করে ভোলাও হয়নি। অনেক সময়ে একবার পরা শাড়ি বন্দনা খাটে তোষকের তলায় রেখে দেয়। এটা হয়ত সেই নিয়মেই তোষকের তলায় থেকে গিয়েছিল। শয্যার ওপর থেকে একটা মানুষ কর্পূরের মতো উবে গেছে। আরেকটা মানুষ আপাদমস্তক ভিতর-বাহির পাল্টে গেছে। অথচ জড় বস্তু বলেই দুটি মানুষের জীবনের সঙ্গে পাটে পাটে জড়ানো ওই শাড়ি একইরকম রয়ে গেছে! এখনও ওতে তাদের স্পর্শ, তাদের গন্ধ মাখানো। শাড়িটা নাকের কাছে ধরে বন্দনা যেন অভিমন্যুর আফটার-শেভ লোশনের গন্ধ পেল। একমুহূর্ত। একমুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল বন্দনা। কিন্তু ঠাণ্ডাটা সর্বাঙ্গে ফুটছে। বসন্তের হাওয়া। কেমন গা শিরশির করে। কোথায় গেল ওর পরবার কাপড়টা? কোথাও কোনও চিহ্ন নেই। রূপের ছোট ছোট সার্ট প্যান্ট পাজামা গুছোনো রয়েছে। আলনার পেছনে পড়ে গেল না কি? না তো! পেছন ফিরে নিচু হতে খাটের তলায় কোণে দলা পাকানো কি যেন একটা দেখা গেল। খাটের তলা থেকে দোমড়ানো মোচড়ানো কালোপাড় শাড়িটা বেরোল। কি ভাবে ওখানে গেল ভাববার সময় নেই। ঝেড়ে-ঝুড়ে এটাকেই পরতে হবে। একটা কাচা হয়েছে। দুটো ধোপার বাড়ি গেছে। এই একটাই মাত্র আছে এখন। কারও খেয়াল হয়নি চারটের বেশি এই শাড়ি বন্দনার দরকার হতে পারে। কে খেয়াল করবে? খেয়াল করার লোক তো চলে গেছে। হঠাৎ শিউরে উঠল বন্দনা। খেয়াল করার লোকটি থাকলে তাকে এ জিনিস পরতে হত না। দুটো আলমারি ভর্তি থাকে-থাকে শাড়ি সাজানো রয়েছে। তার কতো পরাই হয়নি। কি যে উল্টোপাল্টা চিন্তা! কালো-পাড় শাড়িটা চার ভাঁজ করে বিছানার ওপর রেখে হাত দিয়ে সমান করতে লাগল বন্দনা। বিশ্রী কুঁচকে গেছে। জায়গায় জায়গায় ময়লা। এমন সময়ে কোথা থেকে চিলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এসে শাড়িটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রূপ। কান্নায়, রাগে মুখখানা লালচে-কালো। অনেকক্ষণ থেকে কেঁদে কেঁদে চোখ রগড়াচ্ছে বোধহয়, মুখময় সেই রগড়ানির কাদা।
—‘এই কাপড়টা বিচ্ছিরি, নোংরা, এই কাপড়টা বাঁদর, শালা, ননসেন্স, ড্যাম, ড্যামিট, ইডিয়ট’—কাপড়টাকে ঘুসি মারছে আর পাগলের মতো ছড়া কাটছে রূপ। তার পাঁচ বছরের জীবনে যেখান থেকে যত গালাগাল শিখেছে। বাড়িতে পাড়ায় যেখান থেকে যত কটু-কাটব্য সংগ্রহ করতে পেরেছে সব এখন তার মুখ দিয়ে গরম ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসছে। তার অস্থির দাপাদাপির মধ্যে থেকে শুধু এইটুকু বার করতে পারল বন্দনা যে এই কাপড়টা নাকি মদনার মায়ের, এটা ওর মায়ের নয়। ওর মা টকটকে লাল, কিংবা সবুজ সবুজ, কিংবা পিংক পিংক শাড়ি পরবে খালি, নইলে ও খাবে না দাবে না, স্কুল যাবে না। দেশবন্ধুর পার্কের পুকুরে যেখানে গত বছর ছোটির দাদা নাইতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিল সেইখানে গিয়ে ডুবে যাবে। কী ভয়ঙ্কর!
ছেলের চিৎকারে, কান্নায় তখন ঘরের দরজায় সারা বাড়ির লোক জড়ো হয়ে গেছে। শাশুড়ি হাউ-হাউ করে কাঁদছেন। চোখের জলে সব ঝাপসা, বন্দনা ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না মুখগুলো। শ্বশুর, খুড়শ্বশুর, ছোট দেওর, কলি, কাকিমা সবাই আছে। সবার মুখে উদ্বেগ, আতঙ্ক। দুঃসহ শোক আবার ছায়া ফেলেছে তার। হাতড়ে হাতড়ে আলমারি খুলল সে, অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়েই একটা হালকা নীল জমির শাড়ি বার করল। হলুদ পাড়। ছেলের দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলল—‘এইটে পরি সোনা! এটা যে আমার খুব ভালো লাগে, জানো না? লাল টুকটুকেটা যে তোমার বউ-এর জন্যে রেখে দিয়েছি।’
আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল রূপ—‘বউকে আমি খুন করে ফেলব।’
এতটুকু বাচ্চার শরীরে যে কোথা থেকে এতো জোর এল, এত জেদ! দাঁত দিয়ে সে সারাক্ষণ ‘মদনার মার শাড়ি’টাকে কুটি-কুটি করে কাটতে লাগল। অনেক করে বুঝিয়ে সুজিয়ে, বউ যে কত লক্ষ্মী, কত বেচারা, লাল শাড়িটার জন্যে সে যে কতদিন ধরে হা পিত্যেশ করে করে আছে, না পেলে অভিমানে সে যে কি করে ফেলতে পারে—এত রকম বলে কয়ে বন্দনা যখন ফিকে নীল শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।
ছেলেকে শিশুকালের মতো চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে বাইরে এল। কোথাও কারো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ। এতগুলো জ্যান্ত মানুষ বুকের মধ্যে ধরেও যেন কবরখানা। অনেক দূরের কোনও ঘর থেকে খালি পাখা চলার ঝিকঝিক আওয়াজ আসছে। বন্দনার মনে হল সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সে একাই শুধু জেগে। অনেক বেলা। রোদ হেলে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে। কিংবা ও পাট আজকে বন্ধ। রূপের পাশে এসে নির্জীবের মতো শুয়ে পড়ল বন্দনা। শীত-শীত করছে। গায়ে একটা চাদর টেনে দিল। বিকেলের দিকে ছেলেকে ডাকতে গিয়ে গায়ে হাত দিতেই হাতটা ছ্যাঁক করে উঠল। প্রচণ্ড জ্বর। হু হু করে উঠছে। থার্মোমিটার বগলে দিতে দেখতে দেখতে চার ছাড়িয়ে গেল।
চা দিতে কলি ঢুকেছে, বলল—‘থার্মোমিটার কেন গো বউমণি?’
—‘রূপের অনেক জ্বর রে কলি, ডাক্তারবাবুকে একটু ডাকতে বলবি?’
বন্দনার মনে হল তার নিজেরও জ্বর। কেমন বমি-বমি পাচ্ছে। গা শির শির করছে। সারা সকালবেলাটা ভিজে কাপড় গায়ে কেটে গেছে। একে ঋতুবদলের সময়। তার ওপর এই তো শরীর! হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।
এই সময়েই রূপ বেঁকতে শুরু করল। হাত পা ঠকঠক করে কাঁপছে। মুখে ফেনা, গোঁ গোঁ আওয়াজ। তারস্বরে চিৎকার করতে করতে কলি ছুটে চলে গেল। শাশুড়ি দৌড়ে এলেন। ‘বউমা, মুখে চামচে ধরো, ছোট গিন্নি শিগগিরই আঁশবটি নিয়ে এসো, আঁশবটি ঠেকাও গায়ে। কলি জল নিয়ে আয়। জল নিয়ে আয়।’
বন্দনা ছেলের মাথাটা কোলে নিয়ে কাঠের মতো বসে।
কাকিমা বললেন—‘বেশ করে ব্রহ্মতালুতে বরফজল ঢাললা বন্দনা। জ্বরটা মাথায় চড়ে গেছে। তড়কা। ভয় খেয়ো না মা।’
ডাক্তারবাবু এসে সব বিবরণ শুনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। হাতে কলম, প্রেসক্রিপশন লেখার প্যাড। ভালো করে বুক-পিঠ দেখে শুনে বললেন—‘কোথাও কিছু গণ্ডগোল নেই। শক থেকে জ্বর এসেছে মনে হয়। ওষুধ আমি দিচ্ছি। জ্বর কমে যাবে। কিন্তু ছেলেকে যদি মানুষ করতে চাও, সুস্থ সবল ভাবে বাঁচতে দিতে চাও মা তো ও আঘাত পায় এমন কিছু করো না। সেনসিটিভ ছেলে, এই বয়সে বাপকে হারালো। সব সময়ে তার কোলে, পিঠে, দেখেছি তো! তার সেই ছেলে একবারও বাপের নাম মুখে আনে না, ওর এতবড় শোকটা তোমরা বুঝলে না? এই বেশে তোমাকে ওর অচেনা লাগে, ও ভয় পায়। ফিলিং অফ ইনসিকিওরিটি।’
ছেলে তখন জ্বরের ধমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাথার কাছে ঠাকুমা বসে, পায়ের কাছে দাদু। তাঁদের দিকে ফিরে বয়স্ক ডাক্তার বললেন—‘কাশীদা, এখনও পর্যন্ত এটা তড়কাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এর থেকে শক্ত ব্যামো, মৃগী-টৃগি দাঁড়িয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আর তাহলে এ ছেলের জ্যান্ত মড়া হয়ে থাকা কেউ আটকাতে পারবে না। বউদি, আর কোনদিন বন্দনা-বউমাকে সাদা কাপড় পরতে দেবেন না। বুঝলেন?’ ওদিক থেকে কোনও সাড়া এল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ডাক্তারবাবু ব্যাগ তুলে নিয়ে চলে গেলেন।
কিন্তু কেউ অনুমতি দিক আর না দিক, বন্দনা আর কোনদিন সেই কালোপাড় সাদা শাড়ি গায়ে তোলেনি। হাতে যেমন চুড়ি পরত, গলায় সরু সোনার চেন। কানে মুক্তো, আঙুলে হীরের আংটি যা দিয়ে অভিমন্যু সর্বপ্রথম তার হাত ছুঁয়েছিল। রূপ তার পছন্দের লাল শাড়িটা মাকে পরাতে পারেনি বটে, কিন্তু তার ড্রয়িংখাতা ভর্তি মোম রং আর প্যাস্টেলে শুধু একটাই ছবি। চারদিকে খাড়া খাড়া সবুজ ঘাস। তার ওপর দিয়ে দোলনা। বিন্দুর মতো সব ছেলেমেয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু দুজনকে এদের মধ্যে স্পষ্ট চেনা যায়। ছোট্ট ছেলে তার মায়ের হাত ধরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটির মাথায় গোল্লা-পাকানো পাকানো চুল, পাশে তার মা, কাঁধের পাশে মস্ত খোঁপা দেখা যাচ্ছে, তাতে ফুল গোঁজা। পরনে লাল শাড়ি। তলায় ছবির নাম—‘মা এবং নূপ।’
অধ্যায় ৪
খুড়তুত ননদ মিলি এসে বসল। ওরা বড় একটা এ ঘরে আসে না আজকাল। কলি এম. এ পড়ছে, সময় কম। মিলিরও এবার বি এস-সি ফাইনাল ইয়ার। কেমিস্ট্রিতে বড্ড মুখস্থ করতে হয়। সারাদিনই দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করছে মিলি। তাছাড়া ওদের আগ্রহবিন্দু এখন পঁয়তাল্লিশ নং শ্যামবাজার স্ট্রীটের দোতলার ঘর ছেড়ে অন্যত্র সরে গেছে। সে ঘরে সেই নতুন নতুন গন্ধওয়ালা হাসি-খুশি হইহল্লার মানুষগুলি আর থাকে না। জাদুকরের ফুসমন্তরে তারা উধাও হয়ে গেছে। সিন্ডারেলার রাজকুমারী বেশ যেমন রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল! বন্দনার জুড়িগাড়ি এখন লাউয়ের খোল, কোচম্যান জোড়া টিকটিকি, সাত ঘোড়া সাতটি নেংটি ইঁদুর। সুন্দরী রাজকুমারীর জায়গায় ধুলোকালিমাখা ঘুঁটেকুড়ুনি। যদি আবার একটা বিয়ে লাগে বাড়িতে, তখন ওদের আগ্রহ শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়িকে ঘিরে কিছুদিনের জন্য ফিরে আসবে। কোনও একজন চাঁদের আলো রঙের খড়মড়ে নতুন শাড়ি, ঝকঝকে সোনার গয়না লালহলুদ সুতো বাঁধা হাতওয়ালা শ্রীময়ী মুখ তাদের সবসময়ে টানবে। আপাতত টানের মানুষগুলি রুনু, নমিতা, সুচরিতা, সর্বাণী, এ. কে. বি, এস. এম, প্রদীপ, সুপ্রকাশ, পরিমল ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের খবর পঁয়তাল্লিশ নম্বর রাখে না। মিলির আবার আরেক পাগলামি আছে। সে ক্রিকেট-পাগল। অ্যালবাম জুড়ে ক্রিকেটারদের ছবি—পলি উমরিগর, লালা অমরনাথ, হাজারে, মুস্তাক আলি, ফাদকার, মানকড়, নীল হার্ভে, কাউড্রে, লেন হাটন এবং পলি উমরিগর। পলি পলি করে মিলি পাগল। তার অটোগ্রাফ অভিযান, ক্রিকেট কমেন্টারি শোনা, ফটো কাটিং, কাগজের ছবি আটকানো এবং সেই বৈভব ভালো করে দেখতে দেখতেই অবসর সময় কেটে যায়।
সকালের প্রথম দিকটা রূপকে নিয়ে দেখতে দেখতে কেটে যায় বন্দনার। সে স্কুলে চলে যাবে পৌনে দশটা নাগাদ। ফার্স্ট ট্রিপের বাস। ফিরতে ফিরতে সাড়ে তিনটে। এই সময়টুকু বন্দনা একা। সমস্ত বিশ্ব তার সমাজ-সংসার নিয়ে একটা বিশাল স্রোতোস্বান সমুদ্র, মাঝখানে অনন্ত নির্জনতার মধ্যে একটি মৌনী জলটুঙ্গি ঘরে প্রেতিনী এক। যার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। বর্তমানও নিভু-নিভু, আছে শুধু অতীত। সে প্রেতিনী ছাড়া কি? ঘরখানা তার লম্বায়, চওড়ায় বিরাট। সেই ঘরের কোণে কোণে ইচ্ছে করলে ছড়িয়ে যাওয়া যায়, নিজেকে তুলে দেওয়া যায় পনের ফুট উঁচু সিলিং-এ। বড় বড় জানলা আছে। তার বাইরে তাকালেই বাড়ির মাথায় মাথায় খোলা আকাশ দেখা যায়। বারো মাস তাতে একটা দুটো ঘুড়ি ওড়ে। একমুঠো আকাশ নয়, বেশ উদার আকাশই। ছাদে ছাদে কাপড় শুকোচ্ছে, কোনও কোনও ছাদে বাহারি বাগান। কিন্তু বন্দনা এভাবে নিজেকে ছড়াতে পারে না। প্রত্যকটি ছাদের দিকে তাকালে তার মনে হয় কৌতূহলী চোখে কেউ চেয়ে আছে। অপবিত্র কৌতূহল। আকাশটা এত নির্বিকার, নির্বিকল্প যে বন্দনা সেখানে কোনও উত্তর কোনও ভাষা খুঁজে পায় না, সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে ঘরের চতুর্দিকে কালো কালো ছায়া। বন্দনা ভাবে রোদ থেকে চোখ ফেরানোর জন্যে এমন হচ্ছে। কিন্তু বারবার চোখ কচলালেও, অনেকক্ষণ সময় কেটে গেলেও একই রকম ছায়া কোণে কোণে ওৎ পেতে থাকে। ফিকে নীল, রঙ-জ্বলা হলুদ চৌকোনা নিজের কোলের দিকে তাকিয়ে বন্দনা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। ওই ছায়ারা হয় সরে যাক, নয় তাকে একেবারে গ্রাস করে নিক।
আজকে মিলি আসতে ছায়াগুলো তড়িঘড়ি সরে গেল। মিলির চান করা চাপ-চাপ কোঁকড়া চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। ক্যান্থারাইডিন হেয়ার-অয়েলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। চান করে গায়ে পাউডার দিয়েছে। ঘাড়ে গলায় সাদা ছোপ। ছাপা শাড়ির আঁচল খাঁটের প্রান্ত বেয়ে মেঝেয় লুটোচ্ছে।
—‘আজ বুঝি তোর সকাল-সকাল ছুটি হল?’
—‘না গো বউমণি আজ বন্ধুর গাড়িতে লিফট পেয়েছি।’
‘তুমি কি করছিলে?’
—‘কিছু না।’
—‘কিচ্ছু না?’
—‘না রে।’
—‘বউমণি আমাকে একটা কার্ডিগ্যান বুনে দেবে? ডিজাইনটা তোমায় এনে দেবো। রুইতন শেপের জালি, ধারে ধারে গিঁট গিঁট মতন, তুমি নিশ্চয় দেখেছ। নতুন উঠেছে গো, খুব সুন্দর। দেবে বুনে?’
—‘দেবো। কিন্তু অনেক দেরি হবে।’
—‘তাতে কি? এ বছর তো শীত হয়েই গেল। পরের বছর পরব।’
—‘আমি যদি ভুল করে ফেলি?’
—‘যাঃ।’
বউমণি কত সোয়েটার অবলীলায় বুনেছে ছ বছর ধরে, তার আবার ভুল? মিলি বিশ্বাস করতেই পারে না।
তারপর চুপি চুপি গলায় বলল—‘একটা কথা বলব বউমণি, কিছু মনে করবে না?’ বন্দনা বলল—‘বল না কি বলবি!’
—‘জ্যাঠাইমা আর মা বলছিল খোকামণি যখন স্কুলে চলে যায় তখন তো তুমি শাড়ি খুলে ফেললে পারো। আর ডাক্তার-জ্যাঠা কি তোমায় এতো গয়নাও পরতে বলেছিলেন?’
কথা শুনে বন্দনা মিলির মুখের দিকে বোকার মতো চেয়ে রইল। বুঝতে দেরি হল। কি বলছে রে বাবা! খোকামণি মানে ছেলে স্কুলে গেলে সে শাড়ি খুলে ফেলতে পারে? মানে? শাড়ি খুলে কি পরবে? সালোয়ার-টালোয়ার? নাকি সায়া-ব্লাউজই তার পক্ষে যথেষ্ট! ডাক্তার-জ্যাঠা? গয়না? আস্তে আস্তে বুঝতে পারল। নিজের শাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল রঙ ফিকে হয়ে আসা তুঁতে রঙের টাঙাইল একটা। এগুলোর রঙ থাকে না। ফিকে হতে হতে দুপুরের আকাশের মতো একটা ঘষা-ঘষা নীল হয়ে এসেছে। ভেতরের শাদা বুটিগুলো মিলে-মিশে গেছে। একটু ছাই-ছাই রঙ ধরেছে শাদা পাড়ে আর বুটিগুলোয় কষে পরা হয়েছিল শাড়িটা। ধোপার বাড়িও গেছে। তাই এই দশা। এই রঙিন শাড়ি রূপ স্কুলে চলে গেলে তাকে খুলে ফেলতে বলছে মিলি। খুলে বোধহয় সেই কালো পাড় শাদা শাড়ি পরতে হবে। মিলি অবশ্য বলছে না। মিলিটা বোকা, সরল। তাকে দিয়ে তার মা-জেঠিমা বলাচ্ছেন। নিজেদের বলতে কিন্তু-কিন্তু লেগেছে। কিছুদিন ধরেই ওর কেমন মনে হত সামনে থেকে যেন সবাই সরে সরে যাচ্ছে। সে তো চট করে ঘর থেকে বেরোয় না। তবু ছেলেকে খাওয়াবার সময়ে, স্কুলে পাঠাবার সময়ে তাকে তো যেতেই হয়। সে সময়টা বাড়িতে মোটামুটি সবাই থাকে, দেওররা ছাড়া। অথচ বন্দনার দৃষ্টি পরিধির মধ্যে যেন কেউ থাকে না। শাশুড়ি রান্নাঘরের মধ্যে, কাকিমা যেন মনে হয় খাবার ঘরের কপাটের আড়ালে সরে গেলেন, খুড়শ্বশুর ছেলের হাত ধরে রাস্তায় নামেন, স্কুল বাসে তুলে দেবেন, কিন্তু শ্বশুরমশাইকে দেখতে পাওয়া যায় না। ‘মা’ বলে তিনি যেন অনেকদিন ডাকেননি। সবাই যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর। এ সবের তাহলে একটা মানে আছে? এবং সে মানে এই রঙ-চটা তুঁতে নীল শাড়ি?
ওর হতভম্ব ভাব দেখে ততক্ষণে ছোট ননদ ‘আসছি একটু’ বলে পগার পার।
একটা ঝাপসা ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠবার মতো বন্দনা হঠাৎ তার পারিপার্শ্বিক সজাগ চোখে দেখতে পেল। এতক্ষণ সে চুপচাপ খাটে বসেছিল। উঠে দাঁড়াতে উল্টো দিকের আলমারির লম্বা আয়নায় তার পুরো দৈর্ঘ্যের ছায়া পড়ল। বন্দনার মনে হল সে ভূত দেখছে। ডিগডিগে রোগা, বিবর্ণ, কণ্ঠার হাড় উঁচু। সেই গর্তে বোধহয় এক পো তেল ধরে যাবে। চোখের তলায় ঘন কালি, হাতে কয়েকগাছি চুড়ি ঢলঢল করছে, একটি অসুস্থ, আধপেটা খাওয়া, অপরিণত দেহ, অপুষ্টিতে ভোগা বালিকামূর্তি আয়নার ভেতর থেকে তার দিকে ভীতু চোখে চেয়ে রইল। বন্দনার যেন হঠাৎ খেয়াল হল, সে আর ননদ-দেওরদের সবার সঙ্গে টেবিলে বসে খায় না। কোনও কোনও দিন ছুটির সকালে বা রাতে নির্দিষ্ট খাবার সময়ে নিচ থেকে দেওরদের দরাজ গলার তর্কাতর্কি ভেসে আসে। ননদদের সরু গলার হাসি। শ্বশুরমশাইয়ের গলা-খাঁকারি। সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছে। তার বেশ কিছুক্ষণ পর, এক কিম্বা দেড়ঘণ্টা বাদে, মিলি কিম্বা কলি এসে বলে যায়—‘বউমণি তোমার হয়ে গেছে, মা খেতে ডাকছে।’ নিচে গিয়ে দেখে খাবার ঘরের এক কোণে কম্বলের আসন পাতা। একটি পাথরের গ্লাসে জল, সাদা পাথরের থালায় দলা পাকানো আতপচালের ভাত। বেশির ভাগ দিনই কয়েক রকম আনাজসেদ্ধ, ডালসেদ্ধ আর ঘি থাকে। কোনও কোনও দিন সেদ্ধর বদলে কোনও তরকারি। অম্বল। রাত্রে লুচি, পরোটা। কিন্তু খাদ্যটা ভালো হলেও দিনের পর দিন খেতে খেতে প্রচণ্ড অম্বল হয়, মুখ সব সময়ে টকে থাকে। রুটি খেলেও সহ্য হয় না। আমাশা হয়ে যায়। বেশির ভাগ দিনই রাত্রে খায় না বন্দনা। শাশুড়ি দুধ নিয়ে সাধাসাধি করলে দুধটুকু কোনমতে গলাধঃকরণ করে নিয়ে শুয়ে পড়ে। রাত্রে পেটের মধ্যে কেমন একটা অচেনা অনুভূতিতে ঘুম ভেঙে যায়। সর্বক্ষণ গা-বমি-বমি করতে থাকে। দুঃখ, বিষাদ, দারুণ মানসিক অবসাদের সঙ্গে শারীরিক কষ্টগুলো এতদিন এমন নিঃশেষে মিশে ছিল যে আলাদা করে তাদের শারীরিক বলে বুঝত না বন্দনা। আজ এক চমকে বুঝতে পারল এ সমস্তই দিনের পর দিন অর্ধাহার, অনাহার এবং অনভ্যস্ত আহারের ফল। তার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে অবশ্য এঁদের দুঃখের শেষ নেই। দুধ-ছানা-ফল ইত্যাদি নিয়ে শাশুড়ি সাধাসাধিও করেন। বলেন—‘শরীর টিঁকবে কেন? নিজের দিকে না তাকাও, ছেলেটির দিকে তো তাকাতে হবে বউমা!’ কিন্তু সে সাধ্য-সাধনাতে কোনও জোর থাকে না। তিনি সাধাসাধি করবেন এ-ও যেমন স্বাভাবিক, সে সাধাসাধিতে ফল হবে না সে-ও যেন ঠিক তেমনি স্বাভাবিক। অনেক সময়ে কাকিমা বলেন—‘দিদি, ওর গলা দিয়ে খাবার নামে না গো আর! তুমি আমি বলে করব কি?’ চোখে আঁচল চাপা দেন কাকিমা। কিন্তু সাতাশ বছরের পরিপূর্ণ যৌবনের জঠরাগ্নি সে তো বাধা মানে না। গভীর রাতে সকলে যখন নিশ্চিন্তে ঘুমোয় তখন সেই বাড়বানল তাকে জাগিয়ে রাখে। কষ্টে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে গরম জল পড়ে। খাটের বাজুতে মাথা রেখে অবসন্নের মতো পড়ে থাকে বন্দনা, মনে করে এটা ওর শোকেরই প্রতিক্রিয়া। অবসন্ন হয়ে একটা ঘোর লাগে, ঠিক ঘুম নয়, সেই ঘোরের মধ্যে বন্দনা স্বপ্ন দেখে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। জানলা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে ওমা এ তো বৃষ্টি নয়! জল নয়! শিলের মতো কি যেন পড়ছে! ওমা শিল তো নয় মাছ! খণ্ড খণ্ড মাছ ওলট পালট খেতে খেতে ভীষণ বেগে বন্দনার জানলায়, জানলার সিলে, বন্ধ শার্শিতে, বন্ধ চেতনায় এসে আছড়ে পড়ছে। কী হীন কি দীন এই নিষিদ্ধ স্বপ্ন! বন্দনা মাঝরাত্তিরে পশ্চিমের বাথরুমে যায়। বমি করে আসে। ওঠে শুধু জল। টক জল।
আসলে বন্দনা কোনদিন মাছ ছাড়া খেতে পারত না। অত্যধিক মৎস্য-প্রীতির জন্যে বাবা-কাকা আদর করে বেড়াল বলে ডাকতেন। মাতৃহীন কন্যা, মাছ খেতে ভালোবাসে, বাবা মাছ খাইয়ে কৃতার্থ হয়ে যেতেন। রুই, কাতলা, ইলিশের সময়ে ইলিশ, তপসের সময়ে তপসে। চিংড়ি, পার্শে, কই, মৌরলা। বন্দনার শ্বশুরবাড়িতে আর এক কাঠি বাড়া। নিরামিষ রান্নার রেওয়াজই নেই। পোস্তচচ্চড়ি এঁরা পেঁয়াজ ছাড়া খেতে জানেন না, ডালে রসুন ফোড়ন, আলুবেগুনের তরকারিতে কুচো চিংড়ি, চচ্চড়িতে মাছের মুড়ো, এ পড়বেই। খুব সম্ভব সেই জন্যই এখন তার জন্য বেশির ভাগ দিন ভাতে-ভাত-এর আয়োজন হয়। এখন মাছের হেঁশেল আলাদা হয়ে গেছে। অত রকম রান্না সেরে এঁরা আর নিরামিষ রান্না করে উঠতে পারেন না। বোধহয় ভালো জানেনও না। অথচ এদিকে ভীষণ গোঁড়া।
অভিমানে বন্দনার চোখে জল এল। এতদিন ধারণা ছিল শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসেন। বিয়ের পর মাতৃহীন কন্যা বলে বন্দনার বাবা যখন অত্যধিক কাতর হয়ে পড়েছিলেন, শাশুড়ি বলেছিলেন—‘ভাবছেন কেন বেইমশাই। ও আমার মেয়ে হল। বউ নয়। মেয়ে। বউমা বলে ডাকতে ভালোবাসি তাই ডাকি। নইলে আমার কলি, কলিও যা বন্দনাও তা।’
সত্যিই, কোনদিন বন্দনার মনে হয়নি, শ্বশুরবাড়িতে সে কিছু খারাপ আছে। আগে সংসারের নানান কাজ, বিশেষত তদারকি করতে হত, এখানে চা-টা পর্যন্ত মুখে ধরা হয়, ছাড়া-কাপড়টা পর্যন্ত লোকে কেচে দেয়। একটু কড়া শাসন, বাইরে বেরোনোর ব্যাপারে একটু সংযম, নিয়ম মেনে চলতেই হয়। কিন্তু বন্দনার কোনদিন তা নিয়ে কোনও নালিশ ছিল না। তার এতবড় দুঃখের ওপর সেই শ্বশুর-শাশুড়ি কি করে অমন নিষ্ঠুরতা করতে পারলেন? শাশুড়ি হয়ত অশিক্ষিত বলে পুরনো সংস্কার আঁকড়ে আছেন, কিন্তু শ্বশুরমশাই? তিনি যে তাকে কত মা মা করে ডাকেন, কত আপনজনের মতো ব্যবহার করেন তিনিও তো বলতে পারতেন!
দশ-এগার বছর বয়সে মা চলে গেছেন। স্ত্রীলোকহীন সংসারে বাবা-কাকার তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা, গানবাজনা নিয়ে মেতে থেকেছে, বৈধব্যের নিয়মকানুন, মেয়েলি আচার-বিচারের কিছুই সে জানে না। এসব নিয়ে কোনদিন চিন্তা করারও দরকার হয়নি। দু বেণী ঝুলিয়ে কলেজ গেছে হালকা মনে, বাড়ি ফিরে স্কিপিং রোপ, সেতার, রেডিও, সিনেমা, গল্পের বই। সংসারের আর পাঁচটা সাধারণ দৃশ্যের মতো দেখেছে থানপরা শূন্যসিঁথি বিধবাদের। আভরণহীন, শূন্যদৃষ্টি, মুখে হয় বিষাদ নয় কেমন একটা কাঠিন্য। কিন্তু প্রিয়জন বিয়োগের সন্তাপ ছাড়াও যে তাঁদের জীবনে আর কোনও দুঃখ থাকতে পারে এবং তা অসহনীয়ও হতে পারে তার বেণীদোলানো মাথায় সে চিন্তা কখনও আসেনি। আজ নিজে সেই থানকাপড়ের দলে ভর্তি হয়ে সেই দীর্ঘ, কঠিন, নিঃশব্দ মিছিলের অন্তর্বর্তিনী হয়ে বড় মর্মান্তিকভাবে বোধোদয় হল।
হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো তার মনে হল আচ্ছা তার শাশুড়ি, খুড়শাশুড়ি এঁরাও তো তার সঙ্গে খান না। ওঁরা তাহলে সবই খান। আচ্ছা, তার স্বামী-বিয়োগের শোক যেমন প্রচণ্ড, শাশুড়ির পুত্রশোকও কি তেমনি প্রচণ্ড নয়, তাহলে? স্বামীহারা স্ত্রীর রসনা যদি খাদ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাবে বলে লোকে প্রত্যাশা করে, পুত্রহীনা মায়ের ক্ষেত্রেও তো তাই-ই হবার কথা। অর শুধু মা-ই বা কেন? বাবা? বাবা কি ছেলেকে কম ভালোবাসেন? অভিমন্যুর বাবা খোকা-অন্ত প্রাণ ছিলেন। খোকার সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া কোনও কাজ করতেন না। ছেলেও ছিল ভীষণ পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত। বাবা বারণ করলেন বাথরুম ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। আগে কেন কথাটা বলেননি, পিলার অর্ধেক উঠে যাবার পর কেন বললেন এসব প্রশ্নই আর তার মনে এল না। কোনও খেদও না। অথচ একটা বিলাস- বাথরুমের কি শখই ছিল! আচ্ছা, বিপত্নীকের দুঃখই বা কম কিসে? আজ যদি অভিমন্যু থাকত, বন্দনা চলে যেত, অভিমন্যুর কি এরকম বুকের শিরছেঁড়া যন্ত্রণা হত না? তার জন্যে কি নিরামিষ হেঁশেল হোত? এমনি আলাদা আয়োজন? আলাদা প্রয়োজন? এতদিনে বন্দনা বুঝতে পারল হিন্দু নারীর জীবনে বৈধব্যকেই কেন সবচেয়ে বড় অভিসম্পাত মনে করা হয়, আর কেনই বা গুরুজনরা বিবাহিত মেয়েদের ‘জন্ম-এয়োস্ত্রী হও’ বলে অমন গুরুভঙ্গিতে আশীর্বাদ করে থাকেন! প্রিয়জন বিয়োগের দুঃখের চেয়েও বোধহয় শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে ওঠে সারা জীবন বঞ্চনার এই নিষ্ঠুর শাস্তি। আয়নার দিকে চেয়ে বন্দনার মনে হল গত শতাব্দীর কঙ্কাবতী কন্যার সঙ্গে আজকের বন্দনা ভট্চায্যির মৌলিক কোনও পার্থক্যই নেই। যতদিন কঙ্কাবতীর দশার মধ্যে মোটা দাগের নিষ্ঠুরতাগুলো চোখে পড়ত ততদিন করুণাসাগর তার দিকে ধাবিত হয়েছে। আজকের এই যন্ত্রণা নীরব এবং গোপন।
এরপরই খাবার ঘরে সেই বিস্ফোরণ—‘এ আমি আর খেতে পারছি না, পারছি না।’
অধ্যায় ৫
কলি আর মিলি, কলিকা আর মল্লিকা দুইজাঠতুতো, খুড়তুত বোন। দুজনের অবস্থার এবং চরিত্রের একটা আপাত-মিল থাকলেও, আসলে কিন্তু সূক্ষ্ম কতকগুলো তফাত আছে। মল্লিকা মাত্রই এক সন্তান, দাদা ছেড়ে তার আর কোনও বোনও নেই সহোদর। তার আবদার পূর্ণ হবে না এমন হতে পারে না। বাড়ির নিয়ম মেনে মিলি যা খুশি চাইতে পারে, যা খুশি করতে পারে। কোনও বাধা নেই। টেস্ট ক্রিকেটের সীজন-টিকিট, গ্র্যান্ড-এ গিয়ে বিদেশী খেলোয়াড়দের অটোগ্রাফ নিয়ে আসা, ক্রিকেট-পাগলদের সঙ্গে পত্র-মিতালি। এমনকি বাবাকে সঙ্গে নিয়ে পলি উমরিগরের সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় কফি খাওয়া এবং তাঁর স্বাক্ষরিত ফটোগ্রাফ জোগাড় করা, এ সমস্তই মিলি তার ইচ্ছেমত করে থাকে। বাবা মা তাকে কিছুতে বাধা দেন না, চাঁদটা নেহাত পেড়ে দেওয়া যায় না, তাই। তবে জ্যাঠাইমার প্রবল প্রতাপ এবং জ্যাঠামশাইয়ের ব্যক্তিত্বের কাছে তার বাবা-মাকে খানিকটা নমনীয় হয়ে থাকতেই হয়। প্লেয়ারদের বাড়িতে ডেকে ভাই-ফোঁটা দেবার ইচ্ছেটা যেমন তার পূর্ণ হয়নি। পত্র-মিতালির চিঠিগুলোও সব জ্যাঠামশাইয়ের হাত-ফেরত হয়ে আসে। জ্যাঠাইমা মায়ের কথাবার্তায়, মতামতে সায় দিয়ে সাউখুরি করাও মিলির একটা তোষামুদে অভ্যাস। এ ভাবে সে জ্যাঠাইমার নেকনজরে থাকবার চেষ্টা করে, নিজের অজান্তেই। যেহেতু মা- বাবার তাকে অদেয় কিছু নেই, তাই তারও যে অন্যদের কিছু দেয় আছে, এখনও পর্যন্ত মিলি সে কথাটা শেখেনি। পরে কি হবে বলা যায় না। তবে তার চেয়ে দু বছরের বড় দিদি কলির তার ওপর বেশ প্রভাব আছে।
কলিও কম আদরের নয়। বড়দি কণিকার বিয়ে হয়ে গেছে বহুকাল, বড়দি থাকেও দূরে, মাদ্রাজে। আসা-যাওয়া খুব কম। চার ভাইয়ের কোলে এক বোন। সেজভাই আবার নিজের মতে ক্রিশ্চান বিয়ে করার অপরাধে বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত। তার এবং তার পরিবারের সঙ্গে এ বাড়ির কোনও সম্পর্কই নেই। তার ওপর বড়দা মারা গেছেন হঠাৎ। সবচেয়ে ছোট কলি। তার বাবা মা বলেন বাড়িতে মেয়ে না থাকলে মানায় না। ওরা দুই বোন থাকায় বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। দুদিকে দুটো বেণী ঝুলিয়ে, ধনেখালি ডুরে শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে কপালে কুমকুমের টিপ দিয়ে দুই বোন বাবা-মা-কাকা-কাকী-দাদাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় দুটো গাঁদা ফুলের তোড়ার মতো। কিন্তু কলির জীবনে শোকের কীট প্রবেশ করেছে। মিলির মতো নির্ভেজাল হাসি-খুশিতে ডগোমগো হয়ে থাকা আর যেন তার আসে না। এক একটা অভিজ্ঞতা তার কিশোরী জীবনে প্রবেশ করে আর তাকে একটু একটু করে বদলে দিয়ে যায়। মিলির থেকে মাত্র দু বছরের বড় হলেও খেলার খবর, সিনেমার পাতা আর অনুরোধের আসরের কাল সে যেন কবেই কাটিয়ে এসেছে। কলির জীবনের প্রথম দুঃখ তার সেজদার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া। সেজদা লেখাপড়া মন দিয়ে করত না, গান-বাজনা করত, হোটেলে যারা গান-টান গায় তাদের সঙ্গে মিশত। পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ন বাজাত দারুণ সুন্দর। একদম শ্যামবাজারের বাড়ির মতো নয়। কলির জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদ এই সেজদাই এনে দিত। খুব ভাব ছিল তাই। সেজদা মজাদার খাবার জিনিস নিয়ে আসত। বীফ কাবাব, হ্যাম স্যান্ডউইচ। ছাদে গিয়ে দুজনে খেতো। মিলিকে ডাকত না। মিলি একটু লাগানে ভাঙানে স্বভাবের আছে। পেট-আলগা। মায়ের সঙ্গে রোজ রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওর গল্প হয়। কোন ছেলে ওর দিকে চেয়ে শিস দিয়েছিল, কবে কে বাসে গা ঘেঁসে বিশ্রীভাবে দাঁড়িয়েছিল—এসব লজ্জার কথাও অনায়াসে মাকে বলে দিতে পারে। বীফ কাবাব, হ্যাম স্যান্ডউইচের কথা ওর পেটে থাকবে না। সেজদা বেচারি নিপাট ভালোমানুষ এক অঙ্কের দিদিমণিকে বিয়ে করল চুপিচুপি। মীরা ইসাবেলা মণ্ডল। প্রথম কলিকেই জানিয়েছিল, কলির সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল একদিন সিনেমা দেখাতে গিয়ে। কে বলবে ক্রিশ্চান। রঙ ময়লা, মিষ্টি মুখ, ঠিক যেন কলির এক দিদি। এতগুলো দাদা আর ওই আহ্লাদি বোন না থেকে এরকম একটা দিদি যদি থাকত তো কাজ দিত। বোনের আদুরেপনা আর বোকামি, দাদাদের খুনসুটি একেক সময় অসহ্য মনে হয় তার। কলি বলেছিল—‘বল না সেজদা, বাড়িতে বলেই দ্যাখ না।’
সেজদা উদাস হয়ে বলেছিল—‘নাথিং ডুয়িং। হোটেলঅলা ওল্ড ম্যান জানতে পারলে, এখুনি আমাকে খড়ম পেটা করে তাড়াবে।’
—‘মা? মা নিশ্চয় বাবাকে বোঝাবে!’
—‘মা? ওরেব্বাবা! সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগ্রেস। মোর ফেরোসাস দ্যান বস্। তার অমতে বাড়িতে বউ আসবে, আবার ক্রিশ্চান, আবার ছোট জাত! তুই কি পাগল হয়েছিস কলি? একটু গুছিয়ে নিই, একটা বড় হোটেলে কাজ পাবার কথা হচ্ছে। তখন জানিয়ে কেটে পড়ব। তুই মাঝে মাঝে চলে যাবি। ঠিকানাটা তোকে জানিয়ে যাব।’
ঠিকানা জানিয়ে যাওয়া কিন্তু সেজদার আদৌ হয়নি। বেচারি এক রাত্তিরে খবরটা জানিয়েছিল, খাওয়া-দাওয়ার পর, বাবার সেরেস্তায় গিয়ে, বজ্রাহত কাশীনাথ ভট্টাচার্য তাকে সেই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বার করে দেন। তখন কলিরা ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালবেলা উঠে আর সেজদাকে দেখেনি। নাম উচ্চারণ করলে পর্যন্ত রক্তচক্ষু দেখতে হয়। এখনও।
কলি অপেক্ষা করত, সেজদা হয়ত কলেজে দেখা করতে আসবে। বলে যাবে ঠিকানাটা। কেমন আছে খবরাখবর দেবে, নেবে। কিন্তু সেজদা যেন উবে গেল। কলেজ থেকে ফিরতে ফিরতে কলির মনে পড়ত সেজদার কথাগুলো—‘ইন এনি কেস, দ্যাখ আমায় চলে যেতে হবে। দাদা এঞ্জিনিয়ার। স্টার-পাওয়া ছেলে। মেজদাটাও ঘষটে ঘষটে কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে যাবে। ভেবলু কিছু না হোক একটা উচ্চশ্রেণীর কেরানিগিরি তো হাঁকড়াবেই! কিম্বা হয়ত বাবার জুনিয়র হয়ে কোর্টে বেরোবে। আমি দ্যাখ আই এস সিটাতে ঠেকে গেলুম। তার ওপর ব্যাঞ্জো, পিয়ানো, অ্যাকর্ডিয়ন এগুলো এমন টানে আমায় আর অন্য কিছু করতেই ইচ্ছে যায় না। হোটেলের অ্যাকর্ডিয়ন-বাদককে তোদের ভট্চায্যি বাড়ি টিঁকতে দেবে?’
কলির সুমসৃণ সহজ সরল জীবনে এই প্রথম ধাক্কা। গোড়ায় গোড়ায় লুকিয়ে কাঁদত। মিলিটা ন্যাকা, একদিন গিয়ে কাকিমাকে বলে দিল।
—‘জানো মা, দিদি সেজদার জন্যে কাঁদে।’
—‘এই চুপ চুপ। বড় গিন্নি জানতে পারলে কি বট্ঠাকুর টের পেলে আর রক্ষা থাকবে না।’
কলি তখন মিলিকে বলেছিল—‘তুই কি আমার হাসি-কান্নার ওপরও ট্যাক্স বসাবি? এক্সাইজ অফিসার না কি রে তুই?’
মিলি বলেছিল—‘তা নয়। কিন্তু ভেবে দ্যাখ সেজদাও তো আমাদের কথা, আমাদের বংশমর্যাদার কথা ভাবেনি। কোন্ কেরেস্তান রাক্ষুসীকে বিয়ে করে বসে রইল!’
—‘কার কথা রিপিট করছিস রে? মার? কেরেস্তান-রাক্ষুসীটা তো তোর ডিকশনারির না?’
মিলি হেসে ফেলেছিল—‘মা-জ্যাঠাইমা বলাবলি করছিল তো!’
অত দুঃখেও কলির হাসি আসে—‘তুই-ও অমনি অবিকল তুলে নিলি গলায়? পারিসও বাবা।’
তারপরই তাড়াতাড়ি বড়দার বিয়ে হয়ে গেল। বউমণি এল ঘর আলো করে। সে কি রোশনাই! তিনদিন ধরে কি ধুমধামের যজ্ঞি! সারাক্ষণই সবার মুখ চলছে। তপসে মাছের ফ্রাই হচ্ছে, ছোট চুবড়ির এক চুবড়ি নীলকণ্ঠ ঠাকুর ভাইবোনেদের সামনে ধরে দিয়ে গেল, —‘চেখে দ্যাখো তো দাদাদিদিরা নীলকণ্ঠ বামুনের নাম থাকবে কি না!’ রসে টইটম্বুর ভাসছে লালচে কালো পানতুয়া, প্রথম রসটুকু ঢুকতেই গরম গরম আগে কলি-মিলি। মায়েরা সব সময়েই বলে থাকেন—‘পরের বাড়ি চলে যাবে দুদিন পরেই, ওদের আদর-খাতির আলাদা।’ কিন্তু কলি জানে এই সমস্ত আদরের পেছনে একটা ভয়াল ভ্রূকুটি রয়েছে। সে জানে না সচেতনে, কিন্তু তার অন্তরাত্মা জানে এ বাড়ির সন্তান বাবা-মার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে কোথায় কোথায় চলে যেতে পারে, কেউ খোঁজ রাখার পর্যন্ত দরকার মনে করবে না। বউমণির বিয়ের আসরে সব্বাই জিজ্ঞেস করছে ‘টুবলু কোথায় গেল? টুবলুকে দেখছি না তো?’
—‘চাকরির ইনটারভিউ দিতে গেছে।’
—‘কোথায়?’
—‘বম্বের দিকে।’
সেই চাকরির ইনটারভ্যু সেজদার এখনও চলছে।
তাই মিলি যখন অপরাধীর মতো মুখ করে বলল—‘দিদি একটা কথা শুনবি?’ কলি বলল—‘কি কথা? ছাদে যেতে হবে? ওদের কোনও গোপন কথা থাকলেই ওরা ছাদে যায়। বাড়ির বড়রা কেউ নেহাত দরকার না পড়লে ছাদে যায় না। ছাদে ওদের সমস্ত গোপন কথা নিরাপদ। কলির মনে হল মিলি নিশ্চয়ই সেজদাকে দেখেছে।
ছাদের চিলেকুঠরিতে ঠাকুরঘর। কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে তারপর। সেই সিঁড়ির ওপর বসে ওরা গল্প করে। শীতের দুপুরে-সকালে পড়া তৈরি করে।
মিলি বলল—‘রাগ করবি না?’
—‘না, কেন? কি করেছিস?’
কলি নিজের এমন কোনও সাম্প্রতিক অন্যায় ভেবে পেল না, যা নিয়ে মিলি নালিশ করলে সে বকুনি খেতে পারে।
মিলি বলল—‘আমি বউমণিকে একটা কথা বলে ফেলেছি, বউমণি বোধহয় খুব কষ্ট পেয়েছে।’
—‘কি বলেছিস?’ কলি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।
—‘আমি বলিনি রে দিদি। আসলে মা, জ্যাঠাইমা সব সময়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তো।’
—‘কি আলোচনা?’
—‘এই বউমণি রঙিন শাড়ি পরে, গয়না পরে, বিশেষ করে কানের গয়না বিধবাদের পরতে নেই, সংসারের অকল্যাণ হয়।’
—‘তুই এই সব বললি গিয়ে বউমণিকে?’
মিলি ঢোক গিলল—‘না, এতো কথা বলিনি।’
—‘বড়দের পেছন পেছন পাকামি করে ঘোরবার তোর দরকার কি রে মিলি? সমস্ত কথাগুলো গিলবি, কোথায় কতটুকু বলতে হয়, তোকে কি মানায় না মানায় কিচ্ছু বুঝবি না, ছি ছি! ডাক্তার-জ্যাঠা সেদিন কি বলে গিয়েছিলেন খেয়াল আছে? বউমণি ওরকম বিশ্রী সাজলে খোকামণি মরে যেতে পারে, তা জানিস?’
—‘সেটাই বলছিলুম, জ্যাঠাইমা বলছিল খোকামণি স্কুলে চলে গেলে তো বউমা ওসব গয়না-টয়না খুলে রাখলে পারে। একেই তো সংসারের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল, আবার যদি…’
—‘বললি? তুই একথা বললি? মিলি তুই শুধু বোকা নয়। কি অদ্বিতীয় নিষ্ঠুর তা যদি জানতিস। তুই দুদিন পরে বি এস সি দিয়ে গ্র্যাজুয়েট হতে যাচ্ছিস, তোর একটা সাধারণ বুদ্ধি পর্যন্ত নেই? ছি ছি!’
বেশি ছিছিক্কার মিলি আবার সইতে পারে না। ফোঁস করে উঠল —‘লোকে নিন্দে করলে? আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে নিয়েই তো ঘর করতে হয় আমাদের।’
—‘মা-কাকিমা সেকেলে লোক। তারা নিজেদের মধ্যে যে-সব আলোচনা করে সেই কথাগুলো তোর বউমণির কাছে গিয়ে না লাগালে ঘুম হচ্ছিল না? ভাব তো মিলি তোর যদি, আমার যদি এমনি হত!’
মিলির হাতে সোনার মকরমুখো বালা, গলায় মটরদানা, কানে তারের কাজ করা মাকড়ি, জ্যোতিষী দেখিয়ে মা তিনখানা আংটি পরিয়ে দিয়েছেন—মুক্তো, চুনী আর গোমেদ। মিলি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। বলল—‘আমি খুব খারাপ করেছি না রে দিদি? বউমণি সত্যি কি হয়ে গেছে! আমার কথায় কেমন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, চোখ দুটো যেন পাগলের মতো, আমি সইতে পারিনি, পালিয়ে এসেছি। সেদিন থেকে সুযোগ খুঁজছি, কখন তোকে বলব।’
মিলি এতো কাঁদতে লাগল যে কলি নিজের চোখের জল মুছে, ওকে সান্ত্বনা দিতে বাধ্য হল। বলল—‘মিলি শোন, যা করে ফেলেছিস, ফেলেছিস। আর কক্ষনো এ ধরনের কথা বউমণির কানে তুলবি না। চল, একদিন আমরা বউমণিকে নিয়ে সিনেমা যাই।’ ‘বলবি?’
মিলি ভয়ে ভয়ে বলল—‘আমি বলতে পারব না দিদি বউমণি বোধহয় আর কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না।’
কলি সান্ত্বনা দিয়ে বলল—‘বউমণি ওরকম মানুষই নয়। ক’টা দিন যাক। আমিই বলব এখন।’
মিলি বলল—‘আগে জ্যাঠাইমাকে জিজ্ঞেস করে নিস।’
অন্যমনস্ক গলায় কলি বলল—‘তা অবশ্য।’ আগে বউদিকে না জিজ্ঞেস করে আগে মাকে জিজ্ঞেস করার কথায় তার মন কেন যেন সায় দিল না। অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারটা আগেও ছিল, কিন্তু এখন যেন তার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। এটা অনুভব করতে ভালো লাগল না।
দুজনে অনেকক্ষণ ধরে হাত ধরাধরি করে ঠাকুরঘরের সিঁড়ির ধাপে বসে রইল। চুপচাপ। বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে হু হু করে। কোথা থেকে নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ আসছে। মন কেমন করে। কার জন্যে যেন ভীষণ মন কেমন করে। সে কি বিতাড়িত সেজদা? সে কি অকালমৃত বড়দা সে কি বিধবা শ্রীহীন বউমণি? নাকি অন্য কেউ? কলি বুঝতে পারে না। বুকটা এতো টনটন করতে থাকে যে মনে হয় গলার মধ্যে দিয়ে উপছে বেরিয়ে আসবে। কাদের বাড়ি আবার রেডিও খুলে দিয়েছে। গান হচ্ছে—‘আমি যে গান গেয়েছিলেম, জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়, মনে রেখো।’ ক’টা দিনই বা জীবনের কেটেছে। কলির বয়স কুড়ি। মিলির আঠার বছর তিন-চার মাস। কারুরই অতীত এখনও ভালো করে তৈরি হয়নি। তবু সেই অপরিণত অতীতের দুঃখে, নাকি আসন্ন ভবিষ্যতের আশঙ্কায় দুজনে হাতে হাত জড়াজড়ি করে বসে থাকে। মিলির ভাবটা যেন সব মুশকিলের আসান তার দিদি করে দেবে। এই মুহূর্তে তার মা-বাবার ওপরও ভরসা নেই। তাঁরা অন্য জগতের অন্য ধাতুর লোক। জীবনের সব পথ মা বাবার হাত ধরে হাঁটা যায় না। জীবনের এই ধাপে বরং তার দু বছরের বড় দিদি তার ভাষা বুঝবে, তার ভুলের ক্ষমা জুটিয়ে দেবে।
অধ্যায় ৬
জুন মাসের দুপুরবেলা। গরমের ছুটির পর সবে স্কুল খুলেছে। রূপ স্কুলে চলে গেছে। বন্দনা তার ঘরের কাজ সারছে। জানলা-দরজায় ধুলো পড়ে, রোজ না ঝাড়লে গরাদে হাত দেওয়া যায় না। আসবাবপত্রের ওপরেও এখন পাতলা ধুলোর সর। রূপের টেবিল এলোমেলো হয়ে থাকে। রঙের প্যালেট, জলের মধ্যে রঙগোলা, তুলি ডোবানো। বই, খাতাপত্তর যেগুলো সেদিনের রুটিন অনুযায়ী নিয়ে গেছে, গেছে। কিন্তু বাকি সব উল্টোপাল্টা। এই সময়ে সব কিছু গুছিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে ঝকঝকে করে তোলবার কাজটা পরিপাটি করে করবে এই সংকল্প তার।
ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। খোলাই আছে। মোটা পর্দার আড়াল। ননদেরা পর্দা ঠেলে ঢুকে আসে, শাশুড়িরাও তাই। তাহলে হয়ত ছোট দেওর। কেন? দরজার কাছে গিয়ে বন্দনা দেখল শ্বশুরমশাই। খুব অন্যমনস্ক ছিল নিশ্চয়ই নয়ত খড়মের শব্দ শুনতে পেত, খোলা দালানের পথে অনেক দূর থেকেই।
‘আসুন বাবা, ভেতরে আসুন’— মাথার কাপড় টেনে বন্দনা বলল। কাশীনাথবাবু বললেন—‘যোগীন্দর অ্যান্ড যোগীন্দর প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর কাগজপত্রগুলো সব পাঠিয়েছে। এবার টাকাকড়িগুলো সব পাওয়া যাবে। খোকা তোমাকে আর তোমার মাকে জয়েন্ট নমিনি করেছে দেখছি। দুজনেরই ফিফটি-ফিফটি শেয়ার। টাকাটা আনতে তোমাকেই যেতে হবে মা, খোকার কিছু বকেয়া পাওনাও আছে। আমি নিজে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। কাল সুবিধে হবে?’
—‘ক’দিন পরে গেলে হয় না?’ বন্দনা থতমত খেয়ে বলল। সে এতদিন বাইরে বেরোয়নি, মানুষজনের মুখ না দেখে কাটিয়েছে যে হঠাৎ বাইরে বেরোবার প্রস্তাবে সে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আরও সঙ্কোচ অভিমন্যুর অফিসে যেতে। অফিসের বার্ষিক উৎসবে রানীর মতন সেজেগুজে গেছে। গান, নাটক, স্পোর্টস হত সব শ্রেণীর কর্মচারীদের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের জন্য। কত পার্টিতে অভিমন্যুর সমপর্যায়ের এবং আরও উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করেছে। তার নরম অথচ সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বের জন্য বিশেষ জনপ্রিয় ছিল সে অভিমন্যুদের অফিসের এই সব নানাবিধ উৎসবে অনুষ্ঠানে। সেখানে এই অনাথিনী, ভিখারিনীর বেশে স্বামীর পাওনা টাকার ভিক্ষা হাত পেতে নেবার জন্য যেতে হবে ভেবে শিউরোচ্ছিল সে। খবরটাও একদম হঠাৎ। প্রস্তুতি ছাড়া, নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে না নিয়ে সে পারবে না, পারবেই না।
কাশীনাথবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—‘দেরি না করাই ভালো। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেল। অমনি একেবারে ব্যাঙ্কের কাজটাও সেরে আসব।’
বন্দনা চেয়ে আছে দেখে একটু ইতস্তত করে থেমে থেমে বললেন—‘মোট পঞ্চাশ হাজারের মতো টাকা, আমি বলছিলাম কি সবটাই একসঙ্গে আমার অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে রাখি। কি বলো?’
বন্দনা হঠাৎ আতঙ্কে স্থির হয়ে গেল। ইনি বলছেন কি? আজ এক বছরেরও বেশি সময় হল একটা পয়সারও মুখ দেখেনি সে। কিছুদিন আগে এল আই সি’র দরুন হাজার তিরিশেক টাকা পাওয়া গিয়েছিল। অভিমন্যু লাইফ ইনসিওর করাতে চাইত না। কেমন একটা বিরাগ ছিল ওর ব্যাপারটার ওপর। বলত—‘কমপালসারি সেভিং-এর আমার দরকারটা কি? আমি কি অসংযমী, না বদখেয়ালি? তাছাড়া আমি চিরকাল বেঁচে থাকব। শুধু শুধু কতকগুলো টাকা প্রিমিয়াম গুনতে আমার বয়ে গেছে।’ এক এজেন্ট বন্ধু অনেক বলে কয়ে, অনেক কাঁদুনি গেয়ে ওইটুকু করিয়েছিল। রূপ তার নমিনি ছিল। সে নাবালক বলে তার অভিভাবক হিসেবে ঠাকুর্দাদা সে টাকা তুলেছেন, বন্দনাকে তার বিলি-ব্যবস্থার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেননি। অভিমন্যুর সব সঞ্চয় তার বাবার সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে থাকত। সেসবের খবরও সে কিছু রাখে না। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একটি পয়সারও মুখ দেখেনি। অবশ্য তার দরকারই বা কি? কিন্তু স্বামী সব সময়ে তার হাতে কিছু টাকা রাখত। বলত—‘নিজেকে পরাধীন-টিন ভেবো না যেন, এটা তোমার একদম নিজস্ব। নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করবে।’ মাসের শেষে হিসেব দিতে গেলে অভিমন্যু নানা উপায়ে মুখ বন্ধ করে দিত। সেই টাকা দিয়ে বন্দনা ননদদের সিনেমা দেখিয়েছে, রেস্তোরাঁয় খাইয়েছে, দেওরদের প্রতি শীতে নতুন নতুন সোয়েটার বুনে দিয়েছে। শাশুড়িদের স্কার্ফ; ননদদের কার্ডিগ্যান। স্বামীকে পুল-ওভার, স্লিপ-ওভার, হাতওয়ালা কার্ডিগ্যান, ছোট হাতা টি শার্ট। জন্মদিনে উপহার দিয়েছে সবাইকে। ইচ্ছে করলে তার থেকেও সঞ্চয় করতে পারত, করেনি, দুহাতে বিলিয়ে দিয়েছে। দেওয়াতে তার বরাবরই ভীষণ আনন্দ। আর বাপের বাড়ির তো কথাই নেই। বাবা-কাকা তো সংসার-খরচের টাকা সব তার হাতেই রাখতেন। অল্পবয়স থেকেই পয়সা-কড়ির মাসিক হিসেব করে চলা তার অভ্যাস। শূন্য হাতে কেমন অসহায় লাগে।
উত্তর দেবার সময়ে বন্দনা নিজের গলার স্বর নিজেই চিনতে পারল না। —‘না, বাবা।’
কাশীনাথবাবু প্রতিক্রিয়া একটু দেরিতে এল। কেমন খসখসে স্বর, গলাটা যেন হঠাৎই বসে গেছে। কেটে কেটে বললেন—‘কি না! আমার অ্যাকাউন্টে টাকা রাখবে না? বেশ, তুমি যদি মনে করো তোমার আলাদা অ্যাকাউন্ট দরকার, তো তাই হবে।’
ফেরবার সময়ে তাঁর খড়মের শব্দ বন্দনার কানে বাজতে লাগল। সিঁড়ি দিয়ে তিনি নেমে যেতেই মনটা ব্যাখ্যার অতীত গ্লানিতে ভরে গেল। যেন সারা শরীরে তার কাদা লেগে গেছে। কেন যে নিজেকে এতো ক্লিন্ন লাগল সে ভেবে পেল না। টাকাকড়ির বিষয়ে কোনদিন ভাবতে হয়নি, কোনও মতামত দিতে হয়নি। অভিমন্যু কোনদিন তার সঙ্গে আলোচনা করেনি তার টাকা নিয়ে সে কি করবে। একটা সাজানো যৌথ পরিবারের চৌখুপি কাটা ছকে সে যেন একটা ঘুঁটির মতো এসে বসে গিয়েছিল। তার জন্য কোনও নিয়ম বদলাবার দরকার হয়নি, কোনও ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি, বাড়িতে ন’জন সদস্যের জায়গায় দশজন হয়েছিল এই পর্যন্ত। বন্দনা কোথাও এতটুকু ভার হয়নি। সকলকে সে তারা যেমন তেমনিভাবেই মেনে নিয়েছিল। অভিমন্যু শুধু তার জন্য কিছু মাসিক হাত-খরচ বরাদ্দ করেছিল। কথায় কথায় বাবার সঙ্গে তার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের কথা সে জানতে পেরেছিল। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সবচেয়ে কৃতী সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন ছেলে সংসারের দেখাশোনা করবে, তাই এই ব্যবস্থা। অন্যরকম কিছু যে হতে পারে সে সম্ভাবনার কথা কি কেউ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল। প্রভিডেন্ট ফান্ড, এল আই সি’র নমিনি সে কাকে করল, কাকে অভিভাবক রাখল রূপের, এত সব সংবাদ বন্দনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ছ বছরের বিবাহিত জীবনে তাদের সম্পর্কটা ছিল হাসি আনন্দ আহ্লাদের, বিশেষ করে অভিমন্যু তার থেকে এগার বছরের বড় হওয়ায়, বন্দনার নির্ভরশীলতা ও সমর্পণ ছিল একেবারে প্রশ্নহীন।
সেই স্বামী দু ঘণ্টার মধ্যে তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল এখন সে তার রেখে-যাওয়া টাকাকড়ির বিষয়ে কথা বলছে, নিজস্ব মতামত দিচ্ছে, সিদ্ধান্ত নিচ্ছে—এই পরিস্থিতিটা বন্দনার সমস্ত অস্তিত্বকে যেন টেনে কাদা-মাটির মধ্যে ফেলে দিল। সে বাতাসে বিচরণ করত, এখন পচা ডোবায় পড়ে কোনমতে কাদা ঠেলে ওঠবার চেষ্টা করছে। অনুভূতিটা এইরকম। শ্বশুরমশাই স্পষ্টই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। সে যেন সূক্ষ্মভাবে বয়স্ক মানুষটিকে অপমান করল। অভিমন্যুর অবর্তমানে সে তার বাবার ওপর নির্ভর করতে পারছে না, যদিও অভিমন্যু তার টাকা-পয়সাঘটিত ব্যবস্থাদির মধ্যে দিয়ে নিজের বাবার ওপর তার নির্ভরতা তার বিশ্বাস বারবার প্রকাশ করে গেছে। অভিমন্যু পেরেছিল, বন্দনা পারছে না। এই খবরটা আজকের ছোট্ট সংলাপটুকুর মধ্যে দিয়ে ফাঁস হয়ে গেল। যা গোপন থাকলে ভালো হত, তা চাউর হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটার স্থূলতা, নগ্নতা বন্দনাকে লজ্জায় আপাদমস্তক এমনি মলিন করতে থাকল যে শ্বশুরমশাইনেমে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে সে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে রূপের চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে কেঁদে ফেলল। কাঁদল কতদিন পর! এত কান্না কেঁদেছে যে মনে হয়েছিল চোখের জল বুঝি সব ফুরিয়ে গেছে। শরীরটাকে নিংড়োলেও আর জল বেরোবে না। কিন্তু চোখের জল কতরকমের হয়, সবই তো শুধু শোকের নয়! সেই বহুবিধ চোখের জলের সঙ্গে তার পরিচয় করাবে বলেই তার জীবন যেন ভূমিকা হিসেবে জুন মাসের এই রোদ- ঝনঝনে সকালবেলাটাকে বেছে নিয়েছে।
ড্রয়ার থেকে চিঠি লেখার প্যাড বার করল বন্দনা। এ তার গায়ে হলুদের তত্ত্বের গোলাপি ফুলছাপ লেটার প্যাড। ব্যবহার করার দরকার হয়নি। তাদের জীবনে বিরহ বিশেষ ছিল না। বন্দনার এমন কোনও অন্তরঙ্গ সখীও ছিল না যাকে গোলাপি লেটার প্যাডে চিঠি দেওয়া যায়। কিন্তু এই ছাড়া আপাতত কিছু নেই। এতেই লিখতে হবে। তারপর খামের জন্য শাশুড়ির কাছে যেতে হবে। তিনি বলবেন—‘কাকে চিঠি লিখলে বউমা?’ এমনিই জিজ্ঞেস করবেন। অতিসাধারণ মেয়েলি কৌতূহল। তবু ভালো লাগে না।
বন্দনা অনিচ্ছার সঙ্গে বলবে—‘কাকাকে।’
—‘বে-ই মশায়ের চিঠি আজকালের মধ্যে এসেছে বুঝি? কই দেখিনি তো? উনি তো বলেননি?’
যেন কাকা সম্প্রতি চিঠি দিয়ে না থাকলে বন্দনা একটা অতিরিক্ত চিঠি তাঁকে দিতে পারে না।
কাকাকে চিঠি দিয়ে অবশ্য খুব যে একটা লাভ আছে, তা-ও নয়। প্রথম মুশকিল চিঠি কাকার কাছে পৌঁছবে কি না। কখন যে কোথায় থাকেন? বছর দেড়েক হল সরকারি চাকরি থেকে আগেভাগে অবসর নিয়ে নিয়েছেন। দাদা অর্থাৎ বন্দনার বাবা মারা যাবার পর থেকেই উড়ু-উড়ু করছিলেন। রিটায়ার করার পর যেন পাখা গজালো। হিমালয়ের নেশা চিরদিনই ছিল। এখন আর কাকাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদও তাঁর কাছে পৌঁছেছিল অনেক দেরিতে। খবর পেয়েও আসেননি। শুধু শ্বশুরমশাইকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন বুড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর মতো মনের জোর তাঁর নেই। কাশীনাথবাবু স্বয়ংই বুড়ির দ্বিতীয় পিতা। এই অকল্পনীয় বিপর্যয়ে তিনিই যেন বুড়িমাকে কোলে তুলে নেন।
নানান জায়গা থেকে এখন কাকার চিঠি আসে, হরিদ্বার, কাঠগুদাম, আলমোড়া, রিলকোট, মিলাম। তাতে কোনও সান্ত্বনার ভাষা থাকে না, কোনও ব্যক্তিগত কথাই না। খালি হিমালয় আর হিমালয়। বন্দনা ড্রয়ার থেকে কাকার শেষ চিঠিটা বার করে খুলল। উত্তর দেওয়া হয়নি এ চিঠির। বেশির ভাগেরই জবাব বন্দনা দেয় না। কিন্তু সে জবাব দিক না দিক, কাকার চিঠি নিয়মিত এসে যায়। কাকা লিখেছেন:
বুড়িমা,
এমন একটি আকাশের তলায় দাঁড়াইয়া আছি, যেখানে সভ্যতার ধোঁয়া-কালি পৌঁছয় না। আকাশই যে আদিমাতা, আকাশই যে সেই বহুকথিত ফার্স্ট প্রিন্সিপল, তাহা বুড়িমা এইস্থানে দাঁড়াইয়া তোমার ঠিকই উপলব্ধি হইবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এগারহাজার ফুট উচ্চে আছি। বাতাস একটু পাতলা। ধীরে ধীরে অভ্যাস হইয়া যাইবে। কোথাও তৃণাদি গুল্ম অবধি লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু সামান্য দূরে (যদিও প্রকৃতপক্ষে বহু দূর) অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘা একদিকে এবং মহিমময় এভারেস্ট আরেক দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে দেখিতে কুয়াশার আড়ালে চলিয়া যাইতেছে, আবার সূর্য কিরণে হাসিয়া উঠিতেছে। কাঠের নির্জন, আক্ষরিক অর্থে জনহীন বাংলোয় কাচের মধ্য হইতে এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিতেছি, এ যে কি অতীন্দ্রিয়ানুভূতি সৃষ্টি করে, আমি সামান্য মানুষ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি এ ক্ষমতা নাই। যেন স্বর্গের দ্বার আমার সম্মুখে উন্মুক্ত। এই তুষার, এই পর্বতপৃষ্ঠ ওই দূর-দৃষ্ট শৃঙ্গগুলি ইহারাই স্বর্গের পথের প্রথম সোপান ইহাতে সন্দেহ নাই। শুধু সৌন্দর্য ও নির্মলতার কারণে নয়। এই পীঠের উপর পা রাখিয়া দেখিতেছি পৃথিবীতে ক্রোধ নাই, লোভ নাই, মাৎসর্য নাই, শোক দুঃখ কিছু নাই, শুধু অখণ্ড শান্তি ও আনন্দ, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। এই আনন্দ বাহিরে, এই আনন্দ অন্তরে, ইহা জীবন এবং অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া যে নিষ্ঠুর ব্যক্তিগুলি সাম্প্রতিক কালে অগণিত মানুষ খুন করিয়াছে, তাহাদেরও যদি সূর্যোদয়ের সময়ে সুবর্ণ জ্যোৎস্নাময় কাঞ্চনজঙ্ঘা ও এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ দেখানো যাইত তাহারাও ইহা উপলব্ধি করিত। মা আমি কবিত্ব করিতেছি না, দর্শনতত্ত্বও লিখিতে বসি নাই। কবি অথবা ঋষি করিয়া ঈশ্বর আমাকে পাঠান নাই। কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস মানব-জন্ম দুঃখের জন্য, বিষাদের জন্য, হত্যা-হানাহানি-ঈর্ষা-বিদ্বেষ-জড়ত্বের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। অনন্ত সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিব বলিয়া অনন্তমাধুর্য আস্বাদন করিব বলিয়া, অনন্ত আনন্দ হইব বলিয়া মনুষ্য হইয়াছি। শুধু আমি নহে, পৃথিবীতে যতেক পৃথক দেহযন্ত্রে এক আমি-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সেই প্রত্যেক স্বতন্ত্র দেহাশ্রিত ‘আমি’ আনন্দ লাভ করিবে। করিবেই। মনুষ্যের শেষ পুরস্কার ইহাই।’
আশীর্বাদক কাকা।
সান্ত্বনা নেই। তবু বারবার উল্টেপাল্টে চিঠিটা পড়ল বন্দনা। কাকার হাত ধরে দেশবন্ধু পার্কে গান্ধীজীর বক্তৃতা শুনতে যাওয়া। চিড়িয়াখানায় হাতির শুঁড়ে পয়সা দেওয়া, জিরাফ দেখা, কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে এসপ্লানেড পর্যন্ত এসে পড়া শীতের রবিবারের সকালে। খুব কড়া সিগারেট খেতেন কাকা, ডান হাতের আঙুলগুলো নিকোটিনে হলুদ হয়ে থাকত। বন্দনা যখন ছোট্ট ছিল ওর ধারণা ছিল কাকা মাত্রেরই আঙুলের ডগা ওরকম তামাটে হলুদ হয়ে থাকে। কাকাত্বের এটা একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মা যখন অল্প বয়সে মারা গেলেন তখনই কাকা ঠিক করে ফেলেছিলেন সংসার করবেন না। বাবা বহুবার চেষ্টা করেছেন। কাকার সেই এক কথা—‘যা দুরন্ত মেয়ে দাদা, তোমার একার কর্ম নয়। এ মেয়েকে মানুষ করতে হলে আমায় হাল ধরতে হবে।’ বাবার কাছে রাত, কাকার কাছে দিন। লেখাপড়া গান বাজনা সবই কাকার উৎসাহে। নয়তো বাবা মায়ের মৃত্যুর পর ভীষণ মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন। সেই কাকার অপরাজিত চিরকুমার স্নেহময় ব্যক্তিত্বটি যেন চিঠিগুলোর মধ্যে থেকে বন্দনার হাত ধরবার জন্য উঠে আসে। সে ড্রয়ার হাঁটকায় কাকার আরও চিঠির জন্য। সাদা বণ্ড পেপারে সারি সারি পিঁপড়ের শ্রেণীর মতো লেখা। একটা লাইনও একটু বেঁকে যায় না। শুদ্ধ ভাষার বাঁধুনি কোথাও আলগা নেই। অক্ষরগুলো সামান্য কুঁকড়োনো। সই করবেন সব সময়ে এক লাইনে ‘আশীর্বাদক কাকা।’ ‘বুড়িমা,
কালামুনি গিরিপথের অভিমুখে চলিয়াছি। এ জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সাত হাজার একানব্বুই ফুটের মতো উঁচু। সবুজে সবুজ। দুটি ছোট ছোট ঝর্ণাধারা। এই উপত্যকার ‘প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে’ আরও আরও প্রাণের আশ্বাস লইয়া বহিতেছে। চারিদিকে যেদিকেই চাহি রক্তবর্ণ রডোডেনড্রন গুচ্ছ। এপ্রিল হইতে জুলাই অবধি ইহারা ক্রমাগত ফুটিতে থাকিবে। শীতের বরফ গলিবার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের খাঁজে মাথা চাড়া দেয় সবুজ তৃণগুচ্ছ। সরলসুন্দর মানবশিশুর সহিত ইহাদের আমি তফাত করিতে পারি না। ভেড়া এবং ছাগলেরা তখন নির্ভয়ে চরিবে। তাহাদের পাহারা দিবে বড় বড় পাহাড়ি কুকুর। হঠাৎ-হঠাৎ যেন মনে হয় সেই অতীত যুগে ফিরিয়া গিয়াছি যখন মানুষ পশুপালক ছিল, কৃষিকাজ শেখে নাই। গৃহপালিত পশুর দল লইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে সবুজের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত। সঞ্চয় করিত না। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিত। এবং পশুর সহিত গায়ে গা লাগাইয়া বসবাস করিত। জটিলতাহীন সে জীবন তো ভালোই ছিল! উচ্চ হিমালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসীরা এখনও আদিমানবের জীবনযাপন করে। মাতৌলি, মাপা, বরফু—সঙ্গীতময় নামগুলি গ্রামের। নভেম্বর হইতে প্রায় মে মাস পর্যন্ত ইহারা নিম্ন হিমালয়ে অস্থায়ী বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বাস করে, গ্রীষ্মে পথ তুষার মুক্ত হইলেই ঢালু পাহাড়ের বিস্তীর্ণ তৃণাঞ্চল বা বুগিয়াল বাহিয়া ইহারা বকরি চরাইতে চরাইতে চলিবে, ক্রমাগত উপরে উঠিয়া যাইবে। সবুজ ঘাস এবং গোলাপি ফুলের দেশে। ইহারা এ অঞ্চলের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক। আমার কোনও গিরিশৃঙ্গ জয় করিবার স্বপ্ন নাই। দূর হইতে দেখিয়াছি ত্রিশূলীর মুকুট হইতে দিব্য স্বর্ণ ঝরিয়া পড়িতেছে। গায়ে গা লাগাইয়া পরম মিত্রের মতো দণ্ডায়মান হরদেওল। ওই গিরিশিরায় জমাট ঝুলন্ত তুষার দ্বিপ্রহরে প্রলয়ঙ্কর নির্ঘোষে ভাঙিয়া পড়িত। কুয়াশায় চতুর্দিক ঢাকিয়া যাইত, চলিতে থাকিত ঝড়ো বাতাস। পৃথিবীর আদিম চরিত্র যদি দেখিয়া লইতে চাও, তাহা হইলে এখানে আসিতে পারো। আমি বকরিওয়ালাদের সহিত পুরা এক পক্ষকাল বুগিয়ালে তাহাদের জীবন যাপন করিলাম।…’
বন্দনা অনেকক্ষণ ধরে কাকার সঙ্গ করে। কাকার হাত ধরে বেড়াতে যায়। কুয়াশায় ঢাকা ঘুম, অর্ধেক মেঘাবৃত অর্ধেক সোনার বরণ কাঞ্চনজঙ্ঘার সামনে আটচল্লিশ সালের এপ্রিলের সকালে দাঁড়িয়ে থাকে, একপাশে বাবা, একপাশে কাকা।
দু এক মাস আগে কাকা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠিতে লিখেছিলেন—বন্দনা কি তাঁর সঙ্গে অমরনাথ যাবে? তবে রূপকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। যদি বন্দনা রাজি থাকে তিনি তাহলে ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করবেন। চিঠিটা এসেছিল কনখল হরিদ্বার থেকে। অনেক চিঠিই ওখান থেকে আসে। কে জানে ওখানে স্থায়ী আস্তানা করেছেন কি না। নিজের কথা তো কিছুই লেখেন না। কিন্তু বন্দনার রূপকে ছেড়ে যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, সে এখন স্কুলে যাবার আগে পর্যন্ত মায়ের আঁচল আঁকড়ে থাকে। স্কুলবাস যতক্ষণ না মোড় পেরিয়ে বাঁক নিচ্ছে, ততক্ষণ বারান্দায় দাঁড়ানো মায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। বাড়ি ফিরে আর কোন দিকে চাইবে না, যেন জাদুকরের নিষেধ আছে, খুড়শ্বশুর ডাক দ্যান—‘দাদাভাই, দাদাভাই, এদিকে একবার শুনে যাও।’ আর দাদাভাই! সে ততক্ষণে উর্ধ্বশ্বাসে তার মায়ের খোঁজে ছুটেছে। ঘরে ঢুকে মা তার গোটাগুটি আছে কি না দেখে তবে শান্তি।
প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে—‘বারান্দায় দাঁড়াওনি কেন, আগে বলো!’
—‘ঠিক বুঝতে পারিনি রে, তোর বাস কি কাঁটায় কাঁটায় এক সময়ে আসে?’ কিম্বা বন্দনা হয়ত বলে—‘ঘুম এসে গিয়েছিল রূপু।’
আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার হয়—‘এবার থেকে তুমিও দুপুরবেলা আমার মতো টাস্ক করবে।’
—‘বেশ তো, তুই আমাকে দিয়ে যাস টাস্ক্।’ অমনি রূপের ভারি হাসি পেয়ে যায়।
—‘চালাকি, না? আমি টাস্ক দেবো আবার তুমি সেগুলো পটাপট সেরে রেখে আবার মজা করে ঘুমিয়ে পড়বে, না? সে হবে না।’
রূপের কথাবার্তা থেকেই পরিকল্পনাটা বন্দনার মাথায় এল। শ্বশুরমশাইকে একদিন বলল —‘বাবা, আমি মনে করছি পড়াশোনা করব। পরীক্ষা দেবো আবার।’
—‘তুমি তো গ্র্যাজুয়েট হয়েই গেছ আবার কিসের পড়াশোনা?’
—‘কেন, স্পেশ্যাল অনার্স পড়তে দিচ্ছে আজকাল, তাছাড়াও এম এ তেই তো ভর্তি হতে পারি।’
—‘ভেবে দেখি, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে দেখি।’ কাশীনাথবাবু বললেন।
মায়ের মত হল না। প্রথমে বললেন—‘ওই তো তোমার শরীরের অবস্থা! কি করে তুমি ট্রাম-বাস করবে?’ তারপর ছেলের দোহাই দিলেন।
—‘ছেলের অযত্ন হবে, দেখেছ তো তোমাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারে না।’
বন্দনা বলল—‘আমি কি আর সব ক্লাস করব। যে সময়টা রূপ স্কুলে থাকে, সেই সময়টাই খালি যাব।’
তখন উনি বললেন—‘খোকা পছন্দ করত না।’ এ কথাটার কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু এরপর আর কথা চলে না।
সে তাহলে কি করবে? সংসারের কাজ-কর্ম তাকে দিয়ে হয় না। রান্নাঘর পুরোপুরি শাশুড়িদের দখলে। সেখানে আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই। ননদেরা নিজেদের ঘর গুছোয়। দাদাদের ঘর গুছিয়ে দেবার লোক আছে। নিজের ঘরটুকু গুছিয়ে, রূপের পড়াশোনা দেখেও তার হাতে অঢেল সময়। বাড়িতে জমা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী তার বারবার করে পড়া হয়ে গেল। পড়তে আর ভালোও লাগে না। মনের স্থৈর্য, মনোযোগ বলে কিছু নেই, হাতে পায়ে কাজ করতে পারলে হয়ত সে মুক্তি পেত। সে কয়েকবার এগিয়েছেও। কিন্তু শাশুড়িরা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন। ‘ও কি? ওকি? তুমি চা করছ কেন? তোমাকে করতে হবে কেন। আমরা এতগুলো মানুষ থাকতে? যাও গে যাও ঘরে যাও। খোকনকে দেখো গে যাও।’ এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গীয় বাড়িতে বউয়েদের আদর খুব। কাজকর্ম শাশুড়িরা, কিম্বা লোকজনেই করে। গোড়ায় গোড়ায় তার শাশুড়ি তাকে চুল বেঁধে মাথায় সিঁদুর দিয়ে তবে ছাড়তেন। নাপতিনী আসত নিয়মিত, আলতা পরাতে। কিন্তু সামান্য চা-করা, খাবার দেওয়া এ কাজগুলোও করতে না দিলে সারা দিন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে তার সময় কাটবে কি করে? ছাদে ঠাকুর ঘর, দুবেলা ঠাকুরকে ফুল ফল দেওয়ার অধিকারটাও এঁরা তার কেড়ে নিয়েছেন। সেই কবে শোকের মাথায় ঠাকুরের ছবি ভেঙেছিল! দিনের পরে দিন যায়। রূপ স্কুলে চলে গেলে হাতের সামান্য কাজ সারবার পর মনে হয় সময় থাবা গেড়ে তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে আছে। তার কি বীভৎস চেহারা। ঘরের ওয়ালক্লকটার টিকটিকোনি শুনতে শুনতে মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হয়। ঘড়িটা প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেন্ডে কিছু না-কিছু অপ্রীতিকর, হতাশাজনক খবর তাকে শোনায়। বন্দনা শোনে: ‘কেউ নেই, নেই কেউ, নেই নেই নেই। একা তুমি, একা একা, একা থাকো, কেউ আসবে না আর, এই ভাবে দিন যাবে, ভেবে ভেবে, দেখো দিন, যাবে কি না, তুমি নেই, সে-ও নেই। নেই, নেই, নেই নেই…। কোয়ার্টারের ঘণ্টা বাজে কিরকির করতে করতে, ঢং ঢং শব্দে ঘড়িটা বলে ‘তুমি অনাথা, ‘তুমি বিধবা’, ‘তুমি শেষ।’
এইভাবে দিন যায়। দিন কাটে। যেন মনে হয় কাটে না। কাটবে না। কিছুতেই কাটবে না আর। তবু কেটে যায়। একই রকমের রাতের পরে একই রকমের দিন, কোনও প্রাতেই তার সূর্য-ওঠা সফল হয় না। একা ঘরে অসহায়, নিরুপায় কষ্টে তার মাথার চুল দু হাতে ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।
অধ্যায় ৭
এ কে বি বলেছিলেন গ্রীষ্মের ছুটিতে নিয়ম করে সপ্তাহে একদিন ওঁর বাড়ি যেতে। শ্রীলাকে আর ওকে। অনুরাধারা বলল—‘দারুণ লাকি তুই কলি, এ কে বি যেসব নোট্স্ দেবেন, সাজেশান দেবেন সেগুলো কিন্তু আমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিতে হবে।’
কলি হাসিমুখে বলল—‘দাঁড়া আগে যাই! গ্রীষ্মের ছুটিতে বেরোতে হলে বাবার অনুমতি নিতে হবে। সে এক মহা ফ্যাচাং।’
কথাটা শুনে বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলেন, বললেন—‘বয়স কত?’
কলি থতমত খেয়ে বলল—‘কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে, প্রায় একুশ-হতে চলল।’
—‘কুড়ি বছরের ছোকরা তোমাদের পড়ায়?’ বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন—‘কতবার ডবল পোমোশন পেয়েছে? দ্বিতীয় স্যার হরিনাথ নাকি?’
তখন কলি বুঝল, বাবা এ কে বির বয়সের কথা জিজ্ঞেস করছেন। বলল—‘ও, মানে পঞ্চাশ, টঞ্চাশ হবে। আমি কি করে বলব?’
—‘বিবাহিত?’
—‘হ্যাঁ।’ কলি এবার খুব অপমানিত বোধ করছে।
—‘ছেলেপিলে কটি?’
—‘জানি না, ওঁর মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ে।’
—‘অ, তা যাবে যাও। তবে অত দিগ্গজ হয়ে কি হবে?’
আর শোনবার দরকার ছিল না। কলি জামা-কাপড় বদলাতে ছুট্টে চলে গেল।
বৈঠকখানা রোডে থাকেন এ কে বি। দোতলায় উঠে একটা মস্ত ঘর। আপাদমস্তক বইয়ে ঠাসা। শ্রীলা যথারীতি আসেনি। মাস্টারমশাইরা ভালো ছাত্রী বলে তাকে সাহায্য করতে চাইলে কি হবে, শ্রীলার ওসব ভালো লাগে না, বলে—‘ধুৎ, এই কাঠফাটা গরমে আমি রাস্তায় বেরোই আর কি? তার চেয়ে পাখার তলায় একটা জমজমাট গল্পের বই নিয়ে শুলে আখেরে কাজ দেবে।’
শ্ৰীলা নেই দেখে এ কে বি একটু নিরাশ হলেন। বললেন—‘কন্যাটি বড়ই ফাঁকিবাজ। ঠিক আমার কন্যাটির মতোই। সামান্য একটু গাইড্যান্স পেলেই ফার্স্ট ক্লাসটা হয়ে যেত।’ কলির বুকের মধ্যে চমকে ওঠে—পরিমল ঢুকছে। এ কে বি বললেন ‘এসো, এসো।’ স্যারের মেয়ে অরুন্ধতীও এসে বসল অবশ্য।
এ কে বি বললেন—‘দেখ বৎস এবং বৎসাগণ আমার তিন রকম আলাদা আলাদা স্ট্যান্ডার্ডের নোটস আছে। ছাত্র-ছাত্রীর ধারণ ক্ষমতা বুঝে আমি তা দিয়ে থাকি। উপস্থিত আসরে অরুন্ধতী যেমন বি গ্রেডের নোটস পাবার অধিকারী। কিন্তু আমার নিজস্ব কন্যা বলে তাকে কিঞ্চিৎ কডা জিনিস গলাধঃকরণ করতেই হবে।
অরুন্ধতী ঠোঁট গোল করে বলল—‘কে চেয়েছে তোমার এ গ্রেডের নোটস। আমাকে বি গ্রেডই দাও না।’
—‘না, না, না, না।’ এ কে বি মাথা নাড়লেন—‘অত সহজে তুমি পার পাবে না বৎসে। তোমাকে এই ভারি এবং কড়া জিনিসই গ্রহণ করতে হবে। ইহাই তোমার নিয়তি।’
পরিমল হাসছিল, বলল—‘স্যার, তফাতটা কি দেখতে পারি?’
এ কে বি তার কথায় কান না দিয়ে বললেন—‘সি গ্রেড সর্বসাধারণের জন্য, বি গ্রেড, ভাষাজ্ঞান আছে অথচ কনসেপশন নেই এমত ছাত্রকুলের জন্য, এবং বলা বাহুল্য এ গ্রেড—উচ্চাকাঙ্ক্ষী, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছাত্রদের জন্য। কিন্তু একটা কথা, এই নোট্স বন্ধুদের মধ্যে বিতরণের জন্য নয়।’
কলির মনে পড়ল অনুরাধার দাবির কথা। এ কে বি তখনও বলছেন—‘কেন, সেকথা আমি আগেই বলেছি, সবাইকার হজমশক্তি এক রকমের নয়। সুতরাং বৎসগণ, সাবধান।’
পরিমলের হাতে একগোছা টাইপকরা কাগজ তুলে দিয়ে এ কে বি চলে গেলেন। পরিমল বলে যাবে, অন্যরা লিখবে, কলিকে কার্বন কপি করতে হচ্ছে। কার্বন কপিটা পরিমল পাবে।
বিকেল তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ স্যার এসে তলায় দাগ দেওয়া জায়গাগুলো ব্যাখ্যা করে দিলেন। কলি এবং পরিমলকে দুটি বই দিলেন, সেদিনের মতো অধিবেশন শেষ হল।
বই ব্যাগে পুরে দুরুদুরু বুকে কলি উঠে দাঁড়াল। এবার অরুন্ধতী বাড়ির ভেতরে চলে যাবে, স্যার সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। রাস্তায় বেরোবে সে একা পরিমলের সঙ্গে। এরকম পরিস্থিতিতে ভট্টাচার্য- বাড়ির মেয়েরা বোধহয় কোনদিন পড়েনি। রাস্তায় বেরিয়ে সে মুখ নিচু করে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। পেছন থেকে পরিমল ডাকল—‘শুনুন।’
কলি দাঁড়িয়ে পড়ল, তেমনি পেছন ফিরে। পরিমল বলল—‘আমার ভাগের নোটসগুলো তো দিলেন না!’
—‘ওঃ, ভীষণ ভুল হয়ে গেছে!’ কলি লাল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে সে কার্বন কপিটা বার করল।
—‘আপনি আচ্ছা স্বার্থপর তো!’ পরিমলের গলায় হাসি, —‘অতক্ষণ গোটা নোটটা ডিকটেট করলাম, পুরস্কার স্বরূপও অরিজিন্যালটা পেতে পারি না?’
কলি থতমত খেয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি তার হাতের লেখা কপিটা বার করল, আবার। সেটা নিয়ে পরিমল বলল—‘যাক, আপনার হাতের লেখাটা আমার পাওয়া হয়ে গেল। এমনি চাইলে তো আর দিতেন না!’
কলি বলল—‘আমার হাতের লেখা? হাতের লেখা কি হবে? কি করবেন?’ ভীষণ উদ্বিগ্ন তার গলার স্বর, হৃৎকম্প হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে।
—‘যাক গলার স্বরটা ভালো করে শোনা গেল। এই সুবাদে।’ পরিমল বলল ‘হাতের লেখা নিয়ে আর কি করব। হাতের লেখা তো আর খাবার জিনিস নয়! থাকবে আমার ফাইলে, ভালো লাগবে আমার।’
কলি চট করে মুখ তুলে তাকাল, অনুরাধাদের ঠাট্টা-তামাসার কথা মনে পড়ল, তারপর পর পর বাবার মুখ আর সেজদার মুখ। সে হঠাৎ শরীরে তীব্র মোচড় দিয়ে উল্টো দিকে ঘুরল, দৌড়নো সম্ভব নয়। সম্ভব হলে সে দৌড়েই সেখান থেকে চম্পট দিত।
সিংদরজা পেরোলেই বাঁ দিকে বৈঠকখানা, ডানদিকে বাবার সেরেস্তা ঘর। বাবা আজকাল কোর্টে বেরোনো কমিয়ে দিয়েছেন। কলি শুনতে পেল বৈঠকখানায় বাবার বন্ধু হরিহরকাকুর গলা।—‘কি হে কাশীনাথ, আজ তোমার চালে তেমন ফোঁস নেই কেন? বলি পরশুদিনের শোধ নেবে না?’
কাশীনাথ বললেন—‘আমি কি তোমার মতন ক্যাছাখোলা নাকি? দস্তুরমত সংসারী মানুষ। বিষয়-চিন্তা আছে, ছেলেপুলেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে।’
কলি আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি প্যাসেজ পেরিয়ে উঠোনের দিকে পা চালাল।
বাবার কানে চটির শব্দ ঠিক পৌঁছেছে। চেঁচিয়ে বললেন—‘কে এলি? কলি? এতো দেরি?’
—‘হ্যাঁ বাবা,’ কলির জবাব দূর থেকে এল। এখন বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস নেই তার। এখনও মুখ লাল, বুকে গুরগুর শব্দ, চোখ ছলছল করছে। বাবার বন্ধু-বান্ধবের সামনে উকিলি জেরার মুখোমুখি হওয়া এখনই সম্ভব নয়।
দাবার নেশার চেয়ে আড্ডার ঝোঁকই কাশীনাথবাবুর বেশি। রবিবারের আড্ডা জোর আড্ডা। অন্যান্য দিন বিকেলের দিকে দু একজন উঁকি দ্যান। যদি যথেষ্ট বন্ধুসমাগম হয় তো দাবার ছক পড়ে। এবং ফাঁকে ফাঁকে গল্পগাছা করতে করতে হঠাৎ বিনা আড়ম্বরে একজন কারুর কিস্তি মাৎ হয়ে যায়।
কাশীনাথবাবুর গলায় গলায় বন্ধু তারাপদবাবু এক টিপ নস্য নিয়ে বললেন—‘একটা জিনিস খুব অন্যায় করছ হে কাশী।’
—‘কি অন্যায় আবার করলুম হে!’
—‘মেজছেলের বিয়েটা দাও! যদ্দুর জানি তোমার বড় মেয়ের কোলে চারটি পর পর ছেলে। বড়র পরই মেজ, তার বয়স তো গড়াচ্ছে!’
—‘বড় মেয়ে আমার খোকার পরে’—কাশীনাথবাবু বললেন—‘মেজর সঙ্গে বড়র বছর ছয়েকের তফাত।’
তারাপদবাবু বললেন—‘তা হলেও তোমার মেজছেলের বিয়ের বয়স হয়েছে স্বীকার করবে তো! এভাবে চললে ছেলে যে তোমার বিবাগী হয়ে যাবে! একজনকে একভাবে হারালে আরেকজনকে যে অন্যভাবে…না, না কাশীনাথ শোক পুষে রাখাটা ঠিক নয়। ওতে সংসারের স্বাস্থ্যহানি হয়। দেখো, যে গেছে সে তো আচ্ছা করে বুকে দুরমুশ পিটেই গেছে। কিন্তু তুমি-আমি যদি সেইটি নিয়েই বাকি জীবন মনমরা হয়ে বসে থাকি তো জীবনের ধর্মকে উপেক্ষা করা হয় হে, জীবন তখন তোমার ওপরে শোধ নেবে। আমার কেসটা থেকেই শিক্ষা নাও না! কোলের ছেলেটি গেল। গিন্নি এমন শোকার্ত হয়ে পড়লেন যে আর বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। পাগল-পাগল ভাব। অগত্যা রাণু আমার বড় মেয়ে সংসারের হাল ধরল। বাকি ভাইবোনগুলিকে পড়ানো, শোনানো, আমাদের যত্ন-আত্তি, রুগীর সেবা, মেয়েটার হাড় কালি হয়ে গেল ভায়া। সদাসর্বদা মুখ শুকনো, অল্পবয়সেই যেন সাত গিন্নির এক গিন্নি এমনি চেহারা, এমনি কথাবার্তা। কি বলব কাশী, মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলুম না। যেই দেখে বলে এ যে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, বয়স লুকুচ্ছেন! মেজ-সেজর বিয়ে হয়ে গেল। ছেলেটার পর্যন্ত দেখেশুনে লাগিয়ে দিলুম। এখন সেই বউয়ে আর তার বড় ননদে বাড়িতে ধুন্ধুমার লেগে আছে। কাক-চিল বসতে পায় না এমনি গলার জোর। গিন্নি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন, মাঝে মাঝে বলেন—কি গো এর একটা বিহিত করো, আমি যে আর পারি না। আমি বলি— বিহিত এর হবে না গিন্নি। এ তো তোমারই কীর্তি। একজনের শোক আঁকড়ে রইলে, আরেকটা সন্তান যে জ্যান্ত মরে গেল খেয়াল করলে না। জীবন এইভাবে শোধ নেয় ভায়া। ছাড়ান ছুড়িন নেই।’
কাশীনাথবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—‘কথাটা ঠিকই বলেছ। আমার যে কতদিকে কত জ্বালা। ভাবছিলুম আর ক’টা দিন যাক। বড় বউমা বড্ড মনমরা হয়ে থাকেন, তাঁর চোখের ওপর দিয়ে…’
—‘থাকবে না, মনমরা থাকবে না।’ অচিন্ত্যবাবু বললেন,—‘বাড়িতে একটা উৎসব লেগে গেলে দেখবে ঠিক মেঘ কেটে যাবে।’
—‘তা যাবে কি না জানি না ভায়া। তবে কথা আরও একটা আছে। আমার ছোট মেয়ে ডাগর হয়ে উঠল। খুব পা হয়েছে। এখানে যাচ্ছে, সেখানে যাচ্ছে, —‘বাবা আসি,’ ‘বাবা যাই?’ বললেই কি হয় রে ভাই। আমার অবস্থায়, আমার বয়সে ভাবতে হয় কোথায় যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে। ওর বিয়েটা এবার দেওয়া দরকার।’
তারাপদবাবু বললেন—‘ভালো তো! পাঁজি পুঁথি দেখে দুজনের মাথাই একদিনে মুড়িয়ে দাও। এক লক্ষ্মী যাবে তো আরেক লক্ষ্মী আসবে।’ গলা খাটো করে তারাপদবাবু বললেন—‘তা ছাড়াও, তোমার মেয়ের বিয়ের খরচাপাতি উঠবে কি করে যদি ছেলেরটা আগে না দাও।’
—‘সেটা একটা কথা বটে। খোকাটা দুম করে চলে গিয়ে আমাকে বসিয়ে দিয়ে গেছে। অমন সা-জোয়ান রোজগেরে সন্তান। দেখো দিকিনি এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় আরাম করব পায়ের ওপর পা তুলে, তা না ছেলের বউ, তার ছেলে সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে।’ কাশীনাথবাবুর গলা ভারি হয়ে এল।
বন্ধুদের সঙ্গে এই কথাবার্তার জের টেনেই পরদিন দুপুরে গিন্নির কাছে কথাটা পাড়লেন কাশীনাথ।
—‘একবছর তো কবেই পার হয়ে গেছে, এবার মেজর বিয়েটা না দিলে কর্তব্য অবহেলা করা হয়।’
গৃহিণী বললেন—‘এ কথা তো একশবার। তার উপর গাবলুর বোম্বাইয়ে ট্রান্সফার হবার কথা হচ্ছে। সঙ্গে বউ না দিলে তো আতান্তরে পড়বে! কিন্তু আমার দুটো কথা বলবার আছে।’
—‘বলো না কি বলবে!’
—‘এক নম্বর তুমি আগে পাত্রীর করকোষ্ঠী দেখাবে। ওসব জাল, ভুয়ো, বিয়ের জন্যে আগে থেকে তৈরি করানো ঠিকুজি নয়। জন্মসময় চেয়ে নিয়ে আমাদের নিজেদের লোক দিয়ে আমরা করিয়ে নেবো।’
—‘কেন বলো তো! খোকার বেলা তো তুমি এতো ঠিকুজি-ঠিকুজি করোনি?’ গৃহিণী ডিবে থেকে পানের বোঁটায় করে একটু চুন জিভের ডগায় ছুঁইয়ে বললেন—‘সেটাই তো কথা! ঠিকুজি দেখিনি, ভুল করেছি, ও ভুলের চারা নেই। তা নয়ত কোথাও কিছু নেই অমন জ্বলজ্যান্ত ছেলেটা দুম করে চলে যায়! সেদিন কথায় কথায় বউমার হাতখানা সোজা করে ধরেছিলুম, পষ্ট বৈধব্য রেখা! ওসব মেয়েছেলের কপালে হয় গো, কপালে হয়।’
—‘তুমি আবার এসব দেখতে জানলে কবে?’
—‘আরে বাবা, জানতে হয়! মায়ের প্রাণ, ও তুমি বুঝবে না। খোকা গিয়ে থেকে আমি ওর ঠিকুজি নিয়ে গুরুদেবের কাছে ছোটাছুটি করছি। খোকার আশি-একাশি পর্যন্ত পরিষ্কার আয়ু। অপঘাত নেই, আঘাত নেই, কিচ্ছু নেই। গুরুদেবের কাছ থেকেই রেখা-টেখা দেখতে চিনতে শিখছি। আমার বিদ্যেতে ওইটুকু ধরা পড়ল। তারপর জানি না। বউটারই কি কম খোয়ার হল ভাগ্যের হাতে। আহা এই বয়সে…’ গৃহিণী উদাস হয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন—‘এবার আগে ঠিকুজি, পরে কথাবার্তা। রূপ গুণ ওসব কিছু নয়, স-ব সংসারে মানিয়ে যায়। বড়র তো রূপ মন্দ ছিল না, সে ধুয়ে কি এখন জল খাচ্ছি। আর নগদ দান সামগ্রী নিয়ে তুমি অমন কচলাকচলি করবে নাকো। কোষ্ঠী যেখানে মিলবে, সেখানেই বিয়ে হবে, এই আমার শেষ কথা।’
—‘নগদ না নিলে তোমার ঘরখরচাই উঠবে কোত্থেকে আর মেয়েটা যে গড়গড়িয়ে এম এ পাশ করতে চলেছে তার বিয়েরই বা কি করবে?’
—‘নেবে না তা তো বলিনি। বলেছি কচলাকচলি চলবে না। তারা যা দিতে পারবে তাই নিতে হবে। আর মেয়ের বিয়ে আমি ছেলের দানসামগ্রী, বরপণ দিয়ে দেবো এমন হা-ঘরে আমাকে পাওনি বাপু। তোমাদের ভট্চায্যিদের সে রীত হতে পারে, আদতে চাল-কলার বামুন তো! আমরা মুখুটি। আচায্যি বংশ।’
—কাশীনাথবাবু বললেন—‘এই শুরু হল। তুমি থামাবে এই আমরা আর তোমরার পাঁচালি?’
গিন্নি বললেন—‘তুমি না হয় যা রোজগার করছ সংসারে ঢালছ। ইনসিওরের প্রিমিয়াম দিচ্ছ, কিন্তু আমার সোনার চাঁদ ছেলে? সে তো কিছু কম রোজগার করেনি। আহা সে তো সবটাই তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে সেই থেকে খরচা করবে।’
কাশীনাথ গম্ভীর গলায় বললেন—‘বউমা তো তাঁর টাকা আলাদা অ্যাকাউন্ট করেছেন। সে পাসবইও তাঁর কাছে। তোমার অংশেরটুকু আমার কাছে আছে এই পর্যন্ত। তা দিয়ে আজকালকার দিনে একটা মেয়ের বিয়ে হয় না।’
গৃহিণী মেঝেতে মাদুর পেতে আধশোয়া হয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন —‘বউমার আলাদা ব্যাঙ্ক? বলো কি গো? আগে বলোনি তো?’
কাশীনাথ বললেন—‘এসব গুহ্য কথা। মেয়েমানুষের কানে তোলা মূর্খামি। কথা উঠল তাই বললুম।’
গৃহিণী বললেন—‘দাদার টাকা যদি বোনের বিয়েতে লাগে তো সে তো খুব ভালো কথা, সে আমি বউমাকে বলে ঠিক বার করে নেবোখন। তুমি ছেলের পাত্রী আর মেয়ের পাত্র এক সঙ্গেই দেখ। বউমা কলিকে খুব ভালোবাসে।’
—‘দেখ কদ্দুর কি করতে পারো। আমার তো মনে হয় না বউমা দেবেন। চাইতে গিয়ে ছোট না হতে হয়।’
অধ্যায় ৮
কলির বিয়ে লাগল শ্রাবণ মাসেই। আষাঢ় মাসে বিয়ে হলে কন্যা ধনধান্য ভোগসুখরহিতা হয়, গৃহিণী কোট ধরেছিলেন আষাঢ়ে কোনমতেই বিয়ে চলবে না। শ্রাবণে কন্যা মৃতবৎসা হয় বলেও আপত্তির কারণ ছিল, কিন্তু সবাইকার আগ্রহের আতিশয্য দেখে ঠাকুরমশাই একটা নির্দোষ সর্বশুভংকর লগ্ন বার করেছেন ঠিক খুঁজে। কলির এম এ পরীক্ষা নভেম্বর মাসে। সে রাজি নয় একদম। ভীষণ কান্নাকাটি করছে। এ. কে. বি বলেছেন ভালো করে পড়াশোনা করলে হাই-সেকেন্ড ক্লাস তার বাঁধা। বিয়ের হুজুগে পড়াশোনা ডকে উঠলে সে নিজের মুখ, এ. কে. বি’র মুখ রাখতে পারবে না। তাছাড়াও অন্য একটা কথা আছে। কলি জোর করে নিজের হৃদয় থেকে একটি ভদ্র সুশ্রী মুখের আগ্রহদৃষ্টিকে নির্বাসিত করতে চায়। পারে না। ছাদে পায়চারি করতে করতে, পড়া মুখস্থ করতে করতে হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। পরিমল তাদের স্বজাতি। ঘটক-টটকের মাধ্যমে অনায়াসে ঘটানো যেত জিনিসটা। একটু সময় দিলেই তৈরি হয়ে নিতে পারত ও। কিন্তু এর বেশি কলির সাহস নেই। বিয়ের কথায় তার মুখ বুক শুকিয়ে গেছে। ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু একমাত্র পরীক্ষার দোহাই ছাড়া অন্য কোনও ওজর-আপত্তির কথা কাক-পক্ষীতেও টের পায়নি। মিলি সর্বক্ষণ আঠার মতো লেগে আছে, সে-ও না। খালি বলছে—‘এতো কাঁদছিস কেন? তুই একটা বোকার রাজা। কত শাড়ি পাবি, গয়না পাবি, কত্ত রকম উপহার, কনে সেজে তোকে যা দেখাবে না! তার ওপর বর পাবি। হি, হিঃ আমায় যদি কেউ বিয়ে দিত এক্ষুনি রাজি হয়ে যেতুম। বি এস সি’র রেজাল্টটা বেরোবার আগে হলেই ভালো হত।’ কানের কাছে বকবকবক। কলি বলে—‘তুই চুপ করবি মিলি?’
আত্মীয়স্বজনরাও এক এক করে এসে পড়ছেন। বড় মাসি এসে থাকবেন, পিসিমাও। কাকিমার বউদি, কলিরা রাঙা কাকিমা বলে, তিনি খুব কাজের, যজ্ঞিবাড়ি হলেই তাঁর ডাক পড়ে। তিনিও এসে গেছেন। সবাই মিলে দিবারাত্র আদিরসাত্মক ঠাট্টা করে কলির কান ঝালাপালা করে দিচ্ছেন।
নেমন্তন্ন করতে এ. কে. বি’র বাড়ি গিয়েছিল কলি, স্যার কার্ডটা হাতে নিয়ে বললেন—‘আনন্দিত হলাম, বলতে পারছি না, কলিকা, আশীর্বাদ করছি যদিও।’
—‘কেন স্যার? পরীক্ষা আমি দোবই। সেইরকম কনডিশন করিয়ে নিয়েছি, ভালো রেজাল্টও করবই। আপনি দেখবেন।’
—‘তা আমি জানি। তোমার ওপর সে ভরসা আমার আছে। আমার নিরানন্দ অন্য কারণে।’
কলি মুখ নিচু করল।
এ.কে.বি.বললেন—‘পরিমল মুখার্জি অতো ব্রাইট ছেলে, ও তো ফার্স্ট ক্লাস পাবেই। তারপর হয়ত কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে চলে যাবে। পাত্র হিসেবে তো খারাপ ছিল না, তবু সাহস করতে পারলে না? এতো ব্যক্তিত্বহীন, অব্যবস্থিতচিত্ত তোমরা! তবে ওকে আশা দেওয়াই বা কেন?’
কলির দু চোখ ভরে এসেছে। গুমগুম করে মাদল বাজছে বুকের মধ্যে। ধরা গলায় সে বলেছিল—‘আমি কোনদিন কোনও আশা দিইনি স্যার কাউকে, আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন!’ বলে একরকম ছুট্টে বাইরে চলে এসেছিল।
মা এখন আস্তে আস্তে একটার পর একটা গয়না দিয়ে তাকে সাজাচ্ছে। কলি মেয়ে হয়েও, বিবাহের পাত্রী হয়েও তার কি গয়না হল, শাড়ি হল খোঁজ নেয়নি। মা দু’হাতে পাঁচ গাছা করে চুড়ি পরালেন, তার মুখে কঙ্কন। গলায় সরু পাটি হার। হঠাৎ কলি চমকে বলল—‘মা এরকম বেঁকি চুড়ি, পাটি হার বউমণির ছিল না?’
মা আস্তে বললেন—‘বউমারই তো! তোকে দিয়েছে। ওর আর এসব কোন কাজে লাগবে? আর যা আছে খোকামণির জন্যে যথেষ্ট।’
কলি বলল—‘মা, বউমণি কোথায়? কই সে আমাকে তো বলেনি। এসব গয়না আমাকে দিচ্ছে? বউমণি নিজে হাতে না দিলে এসব আমি পরব না।’ কলির গলায় কান্না উঠে আসছে।
—‘এখানে স্ত্রী-আচার শুরু হচ্ছে। গায়ে-হলুদ দেওয়া হবে। বউমার এখানে আসতে নেই, কলি অসভ্যতা করো না।’
কলি বলল—‘একটু দাঁড়াও, আমি জিজ্ঞেস করে আসছি।’
আজ অনেকদিন পর রূপ স্বেচ্ছায় মায়ের আঁচল ছাড়া হয়েছে। বিয়ে-বাড়িতে অনেক মজা, তার ওপর সমবয়সী বন্ধুবান্ধব। দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা, হঠাৎ চিৎকার করে এ ওকে ভড়কে দেওয়া এই সব হচ্ছে তার উৎসব। বন্দনার তাই আজ বিশেষ কাজ নেই। সকালের দিকে রাশীকৃত পান সেজেছে। এখন একদিকে নান্দীমুখের আয়োজন হচ্ছে। আরেকদিকে এয়োরা সব গায়ে হলুদের আয়োজন করছেন। ছাদনাতলা হচ্ছে নিচের উঠোনে, বন্দনা সেই দৃশ্য থেকে যতদূর পারে সরে নিজের ঘরের দক্ষিণের জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। গরাদ ধরে। ঝমঝম খসখস শব্দে পেছন ফিরে তাকাতেই নতুন হলুদ ডুরে পরা কলি তাকে জড়িয়ে ধরল। অদূরে বড়দি। কলি বলল—‘বউমণি, আমাকে এই সব তোমার গয়না পরানো হচ্ছে দেখ। এসব আমি কেন নেব? মোটেই নেব না।’
বন্দনা বলল—‘নিবি না কেন কলি? এসব আমি তোকেই দিয়েছি তো!’
—‘দিলে আশীর্বাদ করে তুমিই পরিয়ে দিও। আর এতেই বা কেন? এতো তুমি আমাকে দেবে কেন? একটা কিছু দাও। যা হোক একটা কিছু।’
বন্দনা মৃদুস্বরে বলল—‘কলি, একটা গয়নায় তো মেয়ের বিয়ে হয় না রে! গা সাজিয়ে দিতে হয়। তোর দাদা থাকলে যা করতেন, আমি সেটা আমার সাধ্যমতো করেছি। কেন কষ্ট পাচ্ছিস, এই সব আমি তোকে দিয়েছি। মুক্তোর সেট দিয়ে আশীর্বাদ করব।’
—‘আবার মুক্তোর সেট? বউমণি তুমি কি পাগল হলে?’
বন্দনার চোখ ছলছল করছে, বলল—‘গয়নার সার্থকতা কিসে বল? কেউ তাকে পরলে তবে তো? তুই পরলে, আমার ভালো লাগবে, বিশ্বাস কর।’
—‘তাহলে তুমি একবার ওখানে এসো!’
—‘যাব’, একটু ইতস্তত করে বন্দনা বলল, ‘যাব, একটু পরে। তুই যা। আমার হাঁতের ক’টা কাজ আছে। সেরে যাব।’
কলি নিচে চলে গেল। বড়দি বলল—‘দেখলি তো?’
মা বলল—‘দেখলে তো? আমি কি মিছে কথা বলছি, না তোমার বউমণির আঁচল থেকে চাবি খুলে নিয়ে তার আলমারি থেকে গয়না চুরি করেছি? লেখাপড়া শিখলে মেয়েছেলের মতিভ্রম ছাড়া আর কিছু হয় না।’ মার গলায় ভীষণ রাগ।
গায়ে হলুদ হয়ে গেলে হুলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে কলি চার কলাগাছের মধ্যিখানে শিলের ওপর দাঁড়াল। তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। একটা খুরিও সে ভাঙতে পারল না। তার হয়ে বড়দি, বড়মাসি, বড়মাসির বউ, পাশের বাড়ির মাসিমা এঁরা ভেঙে দিলেন। কে কোথায় বলল—‘খোকার বিয়ের পর বাড়িতে এই প্রথম কাজ। কোথায় বন্দনা বউ এয়ো হয়ে দাঁড়াবে, ছিরি হাতে করে ছাদনা তলায় ঘুরবে, তা নয়…।’
বড়দি বলল—‘এই কলি, এখন থেকেই এতো কাঁদতে শুরু করলি, বিয়ের সময়ে মুখ যে ভিমরুলের চাকের মতো হয়ে যাবে রে!’
কাকিমা বললেন—‘চার দাদার এক বোন। তুই তো কোন জন্মেই চলে গেছিস। দিদির কোল-পোঁছা। কত আদর। যা চেয়েছে মুখের কথা খসতে না খসতে হাজির। কাঁদবে না! দিদির কোলের ওই তো ঘর আলো করে ছিল রে!’
কলির চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। একমাত্র কলি ছাড়া কেউ জানে না, বাড়ি-ছাড়ার, মা-বাবার কোল-ছাড়ার কান্না এ নয়। তাকে কাঁদাচ্ছে স্মৃতিতে ওতপ্রোত হয়ে মিশে থাকা একটি বিষণ্ণ তরুণ মুখ, প্রৌঢ় মাস্টারমশাইয়ের র্ভৎসনা, তীব্র এক মৃত্যুদৃশ্য যা সে এখনও ভুলতে পারেনি, এবং নিরাভরণ একটি একদা-শ্ৰীমতী-এখন শ্রীহীন নারীমুখ। কলির বাস্তবিক মনে হচ্ছে বউমণির হাত থেকে, গলা থেকে জোর করে করে গয়নাগুলো উপড়িয়ে নিয়ে তাকে পরানো হল। তারপর একটা অদৃশ্য নারী-কণ্ঠ চেঁচিয়ে বলল—‘যা যা এবার এখান থেকে দূর হয়ে যা শতেকখোয়ারি, হতভাগী!’ নির্জন, নিরানন্দ, তমসাবৃত পথ দিয়ে বউমণি শূন্যহাতে একলা একলা চলে যাচ্ছে। কলির এমন শক্তি নেই, এমন সাহস নেই যে তার জন্য কিছু করে।
কলির উপলব্ধি ঠিকই। শাশুড়ি বন্দনার কাছে প্রথমে টাকাই চেয়েছিলেন। বন্দনা ভয়ানক বিপাকে পড়ে গিয়েছিল। ফিক্স্ড্ ডিপপাজিটের ওই পঁচিশ হাজার টাকাই তার একমাত্র ভরসা। ব্যবহার হয়তো করে না, কিন্তু আছে যে এটাই তার আত্মবিশ্বাসের একমাত্র কারণ। খানিকটা ভেবে নিয়ে সে বলেছিল—‘টাকা তো তেমন কিছু নয় মা, আমি বরং আমার গয়না কিছু দেবো।’ সোনার গয়না দেবার কথা সে আদৌ ভাবেনি। কারণ সোনাও যে টাকা পয়সার মতোই মূল্যবান এটুকু জ্ঞান তার এতদিনে হয়েছে। সে তার মুক্তো-চুনীর জড়োয়া সেটটা বার করে দিয়েছিল।
শাশুড়ি তখনই বলেছিলেন ‘এ তো পোশাকি, তোলা গয়না বউমা। এ দিয়ে তুমি না হয় ওকে আশীর্বাদ করো। টাকাটা পেলে সোনার গয়নাগুলো গড়াতুম। পঁচিশ ভরি মোট লাগবে। আমার মফ চেনটা থেকে সাতভরি বেরোবে, টাকা না দেবে বাকিটুকু না হয় তুমিই দাও। যেমন আছে তেমনি দিয়ে দেবো, বানিটা আর লাগবে না। খোকা থাকলে তো সে-ই ব্যবস্থা করত। দিয়ে-থুয়েও তোমার ছেলের বউয়ের জন্য যথেষ্ট থাকবে।’
গয়নার প্রয়োজন যে শুধু ছেলের বউয়ের জন্য নয়, সেগুলো তার মূল্যবান সম্পত্তি, অনিশ্চিত জীবনের পাথেয়, অসুখ-বিসুখ, ছেলের উচ্চশিক্ষা নানা কারণেই দরকার হতে পারে এ কথা বন্দনা শাশুড়িকে মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারল না। বাবার দেওয়া চুড়ি, হার, কানবালা, এঁদের দেওয়া কঙ্কন, সবই তাকে বার করে দিতে হল।
মনটা সেইদিন থেকে এতো খারাপ, এতো তেতো হয়ে আছে যে বন্দনা ভয় পেয়ে যাচ্ছে—কলির যেন আবার কোনও অমঙ্গল না হয়। কলিকে সে খুবই পছন্দ করে। ভালোও বাসে। ভালোমনে দিতে পারছে না, মাঝ রাত অবধি ওই গয়নার জন্য তাকে কাঁদতে হয়েছে। সেই চোখের জলে ভেজা গয়না পরে কলি শ্বশুরবাড়ি যাবে। বন্দনা মনে মনে বারবার কলির মঙ্গলকামনা করে।
অধ্যায় ৯
বেলা গড়াচ্ছে। বিয়েবাড়ি সেজে উঠছে। বেজে উঠছে। ফুলের গন্ধ, সানাইয়ের আওয়াজ যে এমন অশান্তিকর হতে পারে বন্দনা যেন আগে বোঝেনি। কত সাজসজ্জা, শুধু মানুষ নয়, ঘর, দোর, দালান, ছাদ, উঠোন সব সেজে উঠেছে, নতুন রঙের গন্ধ চারিদিকে। কত অলঙ্কার, প্রসাধনের গন্ধ, রোশনাই। কোথাও নিজেকে লুকোবার এতটুকু ঠাঁই নেই। ছোট্ট ছোট্ট ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে বন্দনা শুকনো মুখে তাড়াতাড়ি একটু ট্যালকম পাউডার ঘষে। গরদের কালোপেড়ে শাড়ি শাশুড়ি রেখে গেছেন। আজকের দিনে বহু আত্মীয়-কুটুম, বন্ধু-বান্ধব আসবে, রঙিন কাপড় পরা চলবে না। শাড়িটা পরে বন্দনা আর আয়নার দিকে ফিরে তাকাল না। কোনক্রমে একটা হাত খোঁপা করে নিয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াল। কেউ না বলে বড় বউ শুভদিনে গোমড়া মুখে নিজের ঘরে বসে সংসারের অকল্যাণ করছে। মহিলামহলের দিকে পা বাড়াতে সে যেন মরমে মরে যায়।
কলি ধরেছিল বউমণি তাকে সাজাবে। কাকিমা বলেছিলেন—‘বেশ তো, তাতে দোষ কিছু নেই।’ কলির মার কিন্তু মত হয়নি। তিনি নিজের ভাইয়ের বউকে কাজটা দিয়েছেন। বউটি খুব পয়া। আসতে না আসতে ভাইয়ের শেয়ার মার্কেটের পয়সা ফুলে উঠতে শুরু করেছে। ভাইয়ের ছেলের পদোন্নতি হয়েছে। দুটি নিখুঁত শিশুর জননীও হয়েছে বউটি। মেয়ের বিয়ের কোনও ব্যাপারে বিধবার ছোঁয়া থাকা তাঁর পছন্দ নয়। শুধু অপছন্দই নয়। আতঙ্ককর। গয়নাগুলো অবশ্য তার ছোঁয়া লাগাই, এবং সেই পরেই সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান হবে। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। অলঙ্কার, বিশেষত সোনা শুদ্ধ জিনিস। ওতে দোষ নেই।
বড়মাসিমা ক’দিন ধরেই আছেন। সন্ধেবেলায় তাঁর মেয়ে বউ এসেছে। দুজনেই পয়সা-অলা ঘরের বউ। কলির মেসোর জমিদারির পয়সা। আর তার মাসতুত দিদির শ্বশুরবাড়ি তিনপুরুষে সরকারি আমলা। তাদের ঠাট-বাটই আলাদা। মাসিমার পুত্রবধূ চন্দ্রার চড়া মেক-আপ। থিয়েটারের অভিনেত্রীর মতো, জমকালো। টিকলি থেকে চন্দ্রহার অবধি সবই পরেছে বউটি। ব্রোকেড শাড়ি। একটু মোটাসোটা সুন্দরী। চোখের কাজলে, ঠোঁটের লিপস্টিকে, গালের রুজে চন্দ্রা বিয়েবাড়ি জমজমাট করে রেখেছে। তার ননদ অর্থাৎ বড় মাসিমার মেয়ের দুটি ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও বেশ আঁটসাঁট। তার বিয়ে হয়েছে আলিপুরের দিকে। নামকরা ফ্যাশন-দুরস্ত পরিবার। পুরো কালো রঙের সাজগোজ তার। কালো পাথরের গয়না, কালোর ওপর সোনালি বুটির জরিদার রেশমি শাড়ি, কালো মিনের চুড়ি, লম্বা সীতাহার। মিনেকরা কাজ। চন্দ্রা আর এই মাসতুত ননদ কাজল দুদিক থেকে বন্দনাকে ঘিরে ধরল।
কাজল বলল—‘দ্যাখ বন্দনা, আমি তোর থেকে সাত বছরের বড়। আমি দু ছেলের মা হয়ে এমন চুটিয়ে সাজতে পেরেছি, আর তুই আমার চোখের সামনে এমনি পাগলির মতো ঘুরবি? তোর কি মার খাবার ইচ্ছে হয়েছে?
চন্দ্রা কোনও মন্তব্য করল না, খালি তার অজস্র গয়নার কিছু কিছু উল্টে-পাল্টে ঠিকঠাক করতে লাগল। হারের খামিগুলো বারে বারে উল্টে যায়। গয়নার ঝুল্লিগুলোও বড্ড শাড়ির জরিতে আটকে আটকে যায়। এইভাবে প্রত্যেক বিয়েবাড়িতে কিছু কিছু ঝুল্লি হারায়। আবার স্যাকরাকে ডাকো, আবার তাকে সারাও। কাজলদি কি বলতে চাইছে সে বুঝতে পারছে না। কি করবে বন্দনা? কি করতে পারে? সে বন্দনার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বন্দনার সম্পর্কে তার তীব্র কৌতূহল। ক মাস আড়াআড়ি বিয়ে হয়েছিল দুজনের। চন্দ্রার আগে। বন্দনার বিয়েতে চন্দ্রা নতুন বউ। ঠিক এইরকম সাজের চূড়ান্ত করে গিয়েছিল। মাথায় সোনার মুকুট, পায়ে নূপুর। কিন্তু সে বরাবরই একটু মোটা, আলগা ধরনের। বন্দনা ছিমছাম। সিংহাসনের ওপর সোজা বসে থাকা নরম-ঢলঢলে মুখের জা’টিকে দেখে সেবার বেশ হিংসে হয় চন্দ্রার। সেই প্রথম ঈর্ষার অনুভূতি কোনদিন যায়নি। অভিমন্যুর মৃত্যুর খবরে সকলকারই মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছিল। চন্দ্রারও খুব খারাপ লাগে। কিন্তু নিয়মভঙ্গের দিন সে লালপাড়, সোনালি জরির বুটি মাইসোর সিল্ক পরে খেতে এসেছিল, এক-গা সোনার গয়না, চওড়া সিঁদুর, লিপস্টিক, গায়ে সুগন্ধ। কাজল এল শ্বশুরবাড়ি থেকে। কালো কাজের সাদা ঢাকাই পরনে। চন্দ্রাকে দেখে তিরস্কারের সুরে বলল ‘কি করেছিস রে চন্দ্রা? আজকের দিনে কেউ এমনি সাজে?’ চন্দ্রার রাগ হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—‘আহা, সবাই তো সেজেছে, আজ এয়োস্ত্রীদের বিশেষ দিন, মা-ই তো বলছিল, নয়তো আমি আর জানছি কোত্থেকে? আমার সিঁদুরের ওপর মা-ই তো আরেক দফা সিঁদুর চড়িয়ে দিল। জানি না বাবা।’
কাজল আহত গলায় বলেছিল—‘মার আর বুদ্ধিশুদ্ধি কোনদিন হবে না।’
চন্দ্রা বাঁকা হেসে বলেছিল—‘তা দিদিভাই, তুমি কিন্তু আমার থেকে কিছু কম সাজোনি। লাল হয়ত পরোনি। সিঁদুরটাও তোমার হেয়ার-স্টাইল না কি বলে, তার চোটে একটু ঢাকা পড়ে গেছে, কিন্তু তোমার শাড়িটা আমারটার চেয়ে অনেক দামী। এটাই সেবার জামাইবাবু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বুনিয়ে আনলেন না? তোমার কানে হীরে, আঙুলে হীরে, লকেটেও হীরে। সবই আসল কমল হীরে। ওসবের দাম কত হতে পারে আমিও ব্যবসাদারের ঘরের মেয়ে ভাই। আমার জানা। তোমাদের মতো ভান-ভড়ং-এর মধ্যে আমি নেই। শ্রাদ্ধবাড়িই হোক আর যা-ই হোক, পাঁচটা মানুষ অসবে তো! ভদ্রলোকের সামনে বেরুবার মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে তো অন্তত।’
কাজল গম্ভীর হয়ে বলেছিল—‘বন্দনাকে দেখতে যাওয়াটা আমাদের প্রথম কর্তব্য। আমি তো আবার আগের দুদিন আসতেই পারিনি। কিন্তু তোকে নিয়ে ওর কাছে যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে।’
চন্দ্রা বলল—‘নাই বা নিয়ে গেলে!’
কাজল একাই চলে গেল রাগ করে। যেতে যেতে দালানের গোল আয়নার সামনে চট করে একবার দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্বটা দেখে নিল। নাঃ, অত্যধিক উগ্র, অশোভন কিছু নেই। চন্দ্রা যা-ই বলুক। সবই সংযত, শোভন, অভিজাত। কিন্তু বন্দনার ঘরে কাজলের জন্য বেশ খানিকটা ধাক্কা অপেক্ষা করে ছিল।
আলনার ওপর একটা আধময়লা ঢাকা চাপা দেওয়া। আলমারি, ড্রেসিং-টেবিলের কাচ মলিন। জলচৌকির ওপর পর পর সুটকেস তার ওপর কেউ একটা ধোপার বাড়ির পাটভাঙা চাদর চাপা দিয়ে গেছে, কারণ তার ওপরেই অভিমন্যু আর বন্দনার যুগল ছবি। বিয়ের। তাতে মালা দেওয়া। সন্দেহ নেই, দুজনেই মৃত। টেবিলের ওপর পাতলা ধুলো। জোড়া খাট, তার একদম ওধারে, দেয়ালের ধার ঘেঁষে অবিশ্বাস্যরকমের শীর্ণ একটি শরীর। চুলগুলো বালিশের এপাশ-ওপাশ ছড়িয়ে পড়েছে পাগলিনীর মতো। চোখ বুজোনো। গাল বসে গেছে। রঙ পাণ্ডুর। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে উঠেছে। গায়ের ওপর একটা গরম কালো চাদর বুক পর্যন্ত টানা। বন্দনা ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছে। এ কে? এ কি? কাজলের স্বামী ফরেন সার্ভিসে আছেন, স্বামীর সঙ্গে তাকে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়। এসেছে মাত্র গতকাল। অভিমন্যুদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে একবারও আসতে পারেনি দেখা করতে। তার মনে হল জানা না থাকলে সে বন্দনাকে চিনতে পারত না। এখনও খুব কষ্টে চিনছে। নিজের গায়ে ফরাসী সেন্টের গন্ধ যেন তার দু গালে চড় মারছে। কাজলের মনে হল এই অনুষ্ঠানের মতো, এই অনুষ্ঠানে তার, চন্দ্রার এবং অন্য অনেকের উপস্থিতির মতো হৃদয়হীন, অশ্লীল ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। ভয় হল বন্দনার যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়! সে যদি দেখতে পেয়ে যায় তাকে, তার এই সযত্ন সংযত নিয়মভঙ্গের সাজখানাকে? তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে কার সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল। ফিরে দেখে চন্দ্রা। ফিসফিস করে চন্দ্রা বলল—‘ও সারাক্ষণ ওষুধ খেয়ে ঘুমোয় দিদিভাই, আধপাগল মতো হয়ে গেছে। ও আমাদের দেখতে পাবে না। দেখবার চোখই নেই। বুঝতে পারবে না কিছু। ওর চোখে আমার লালও যা তোমার কালোও তা।’
চন্দ্রার চোখ ছলছল করছে। দুজনে পা টিপে-টিপে বাইরে বেরিয়ে এল। কাজল রুমাল টানতে ভুলে গেছে, কোমর থেকে, শাড়ির আঁচলে চোখ মুছছে।
আজ কাজলের অনুযোগের জবাবে বন্দনা কি বলে শোনবার জন্য চন্দ্রার উদগ্র কৌতূহল। আজ তো বন্দনা রোগিণীও না, পাগলিনীও না। হঠাৎ শুধু চন্দ্রাদের জাত থেকে অন্য এক জাতে চলে গেছে। ধনী-দরিদ্রে যেমন দুস্তর পার্থক্য, নীল রক্তে আর লাল রক্তে যেমন, সধবা আর বিধবার মাঝখানেও সেইরকম এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। কি বলে ওই জাতের মানুষ?
বন্দনা শুধু বলল—‘কাপড়টা মা দিয়েছেন। কলির বিয়েতে এটাই আমি বাড়ি থেকে পেয়েছি।’
মিলি সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। ভীষণ সেজেগুজে। চন্দ্রা বলল—‘বন্দনা, মিলির গায়ে ওটা তোমার ফুলশয্যের বেনারসীটা না?’ বন্দনা মাথা নাড়ল হ্যাঁ।
নিঃশ্বাস ফেলে কাজল বলল—‘চল বন্দনা, কনের ঘরে যাই।’
হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে বন্দনা বলল—‘আমি? না থাক। আমার যাওয়া চলবে তো!’
—‘সে আবার কি? যাওয়া চলবে না কেন?’
—‘কি জানি, কাজলদি সব নিয়ম তো আমার জানা নেই!’
কাজল বলল—‘কোনও নিয়ম নেই। তুই আয় তো। সকলকার সঙ্গে দেখা করবি তো!’
বন্দনা বিপন্ন মুখে বলল—‘আমি বরং নিচে যাই একবার। মা বলেছিলেন নিরামিষ ঘরে রান্না-বান্না, খাওয়ানো একটু দেখতে। সময়মতো না গেলে রাগ করবেন।’ বলে বন্দনা আর অপেক্ষা করল না। সিঁড়ির দিকে চলে গেল।
চন্দ্রার হৃদয়ে সমবেদনা। দুঃখ। সবই ঠিকঠাক আছে। তা সত্ত্বেও, সব ছাপিয়ে তার বুকের ভেতরটায় কিরকম একটা হালকা ভাব। আর কোনদিন কোনও আত্মীয় সমাবেশে তার মাসতুত জা বন্দনা তার প্রতিদ্বন্দিনী হয়ে উঠবে না। আগে আগে যত বিয়ে, অন্নপ্রাশন, সাধের নেমন্তন্নে দুজনে গেছে। সবার মুখে এক কথা। ফিস ফিস করে অবশ্য। ‘বড়মাসিমার বউটিও সুন্দরী, কিন্তু যাই বলো আর তা-ই বলো মেজমাসিমার বউটির যেন আলাদা একটা শ্ৰী আছে চোখে মুখে গড়নে।’ দেওররা, ভাসুররাও বন্দনা এলেই বেশি মনোযোগী হয়ে উঠত। ধারা পাল্টে যেত সবার। একটা যেন অতিরিক্ত সম্ভ্রম। তার নিজের স্বামী-ই তো বলত ‘বন্দনা ফ্যানটাসটিক’। এই সব কথাবার্তা চন্দ্রার কানে বিষ ঢালত, সে কোনদিন হাসিমুখে এই সব প্রসঙ্গে যোগ দিতে পারত না। স্বামীকে বলত ‘তোমার বুঝি অভিমন্যুদার ভাগ্যের জন্য হিংসে হয়!’ তার স্বামী বলত ‘অভিমন্যু? ওঃ ও তো লগন-চাঁদা ছেলে। হিংসে করে আর কি করব!’ ‘তা দেখে শুনে বন্দনার মতো বউ আনলেই তো পারতে!’ স্বামী হতভম্ব হয়ে বলত ‘যা ব্বাবা। আচ্ছা তো তোমরা মেয়েরা। কোথা থেকে কোথায় সড়াত করে চলে গেলে?’ এই সব অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আর পুনরাবৃত্তি হবে না।
কাজলের মনের ভাবটাও হল বড় বিচিত্র। বন্দনা যেন এক কথায় তাকে বুঝিয়ে দিল সে আর কাজলদের, চন্দ্রাদের কেউ নয়, সে অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গেছে। ক্রমশ আরও যাবে। কাজেই চন্দ্রাদের সাজগোজ, কাজলদের অতি সযত্ন অতি সাবধান প্রসাধন, অলঙ্কার-নির্বাচন এসব আর বন্দনাকে স্পর্শ করে না। বন্দনার কিছু মনে করার প্রশ্ন নেই। কুকুর যদি মাংস খায়, গরু কি তাতে কিছু মনে করে? ওরা নিশ্চিন্তে সাজতে পারে। কাজল মাসিমার বড় ঘরে যেখানে কনে সেজে কলি বসে আছে, আর তার পাশে মিলি উপহার নিচ্ছে সেখানে চলে গেল। পেছন পেছন চন্দ্রা। কাজল অনেকক্ষণ চুপ করে দেখল, তারপর মনের মেঘ কাটাতে বলল—‘কলিকে ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে, না? এই রকম একটু বিষণ্ণ ভাবটা কনের মুখে খুব সুন্দর মানিয়ে যায়, দেখেছিস, চন্দ্রা? বেশি স্মার্ট, বেশি হাসি, অঙ্গভঙ্গি ভালো লাগে না।’
চন্দ্রা বলল—‘যা বলেছ। আজকালকার কনেগুলোকে দেখলে তো কনে বলে বোঝাই যায় না। তবে কলিকে যত ভালোই দেখাক আজকের দিনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর প্রাইজ যদি কাউকে দিতেই হয় তো সে তোমাকে, তোমাকে, তোমাকে।’
কাজল বলল—‘দু ছেলে মেয়ের মা, বড়টা সিনিয়র কেমব্রিজ দিতে চলল, আমার আবার সাজগোজ, আমার আবার রূপ!’
চন্দ্রা বলল—‘বারবার দু ছেলে মেয়ের মা, দু ছেলে মেয়ের মা করো না তো! ওদের পেটে ধরা ছাড়া আর কিছু তোমাকে কোনদিন করতে হয়েছে?’
কাজলের কাঁধে দু হাত দিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে চন্দ্রা আবদেরে গলায় বলল—‘বলো না গো কি করে এমন ফিগার রাখলে? আমি রোজ রোজ বেঢপ হয়ে যাচ্ছি!’
এই সময়ে কলির চোখ পড়ল ওদের দিকে। ইশারায় ডেকে বলল—‘বউমণিকে দেখেছ।’
—‘বউমণি কে? ও, বন্দনা? দেখলাম তো!’
—‘ওকে এখানে একটু আসতে বলো না!’
—‘বলেছিলাম, এল না রে, নিচে চলে গেছে। কাজ আছে।’
কলির চোখ ছাপিয়ে আবার জল এল। বড় মাসিমা ঢুকে বললেন ‘চোখের কাজল ধেবড়ে গেলে কেমন করে শুভদৃষ্টি করবি মা? এই চন্দ্রা বউ, কাজলা ওকে কাঁদাচ্ছিস কেন রে?’
শাশুড়িকে আসতে দেখে চন্দ্রা ঘর থেকে টুক করে সরে গেল। মা কাজলকে বললেন—‘কাজলা, এক খিলি পান এনে দে তো কলিকে। গলাটাও শুকোবে না, ঠোঁট দুটিও টুকটুকে রসালো হয়ে থাকবে। সারা দিনের উপোস, আহা মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে গো!’
অধ্যায় ১০
এ বছর বৃষ্টি হয়নি তেমন। আষাঢ়ে বৃষ্টি হয়েছে নিয়মরক্ষা। শ্রাবণের বৃষ্টি গ্রামের দিকে যত ঝরেছে, শহরে তত ঝরেনি। এক এক দিন মেঘের পরে মেঘ জমে। ঘন শ্রাবণ মেঘ। মাটির ওপর মেঘের ছায়া। তারপর হঠাৎ হু-হু করে হাওয়া দেয়। কিছুক্ষণ পরেই আকাশ ফর্সা। যেন কলির বিয়েতে অসুবিধে হবে বলেই শ্রাবণের গোড়ায় ঝিরঝিরে মতো নামমাত্র হয়ে বৃষ্টি থেমে গেল। আজ সকাল থেকেই মেঘের গুরু গুরু ডাক, কালি-ঢালা আকাশ, তারপর মুষলধার। স্কুলবাস থেকে নেমেই হাঁটু জল। নাতিকে কোলে করে নামালেন দাদু। সে জলে নামবার জন্য ছটফট করছে। দোরগোড়া থেকে ঠাকুমা ধমকাচ্ছেন। বারান্দায় উৎকণ্ঠিত মা আধঘোমটা দিয়ে দেখছে। একটা মস্ত ছাতা দরজার সামনে এসে থামল। ওপরে ছাতা, তলায় জল। মাঝখানে ঢোলা প্যান্ট পরা কোমর, আর তার ওপর ফুলে ওঠা শার্টের অংশ। নাতি-দাদুর দিক থেকে এই দৃশ্যের দিকে চোখ পড়ে গেল। আর কিছু দেখতে হল না। বুকের মধ্যে গুরগুর শুরু হয়েছে। এক দৌড়ে বন্দনা ঘরের মধ্যে চলে গেল। কাকা। দীর্ঘ চার বছরেরও পর।
ক্রমশ ক্রমশ প্যান্ট-গোটানো, ভেরিকোজ-ভেন-অলা শক্ত শক্ত মজবুত কাঠের গুঁড়ির মতো পা দু-খানা দৃশ্য হল। ঠাকুমা মাথায় ঘোমটা টেনে বললেন—‘অ মা, বে-ই মশাই!’ সামান্য লজ্জা পেয়ে ভেতরে যেতে যেতে বললেন—‘আসুন, আসুন। দেখুন দিকি নাতি আমাকে টেনে একেবারে রাস্তায় বার করে ফেলেছে।’
কথা শুনে দাদু পেছন ফিরে তাকালেন—‘আরে আরে সোমনাথবাবু? পথ ভুলে?’ কাশীনাথবাবুর মুখে উল্লাস, বিস্ময়!
—‘দেখ দাদাভাই আজ কে এল!’
বন্দনা ছুটেছে বাথরুমে। চোখ মুখ ভেসে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে একটা বিস্ফোরণের মতো কিছু। তার অশ্রু কি শোকের, না আনন্দের, না অভিমানের? বন্দনা জানে না। সে শুধু দেখছে অনেক দিনের খরার পর বৃষ্টি নামছে। ততক্ষণে ছেলে বাইরে থেকে ডাকাডাকি করছে—‘ও মা। দেখ না আমি কেমন ভিজেছি।’ শাশুড়ি ডাকাডাকি করছেন, ‘অ বউমা, দেখে যাও কে এসেছেন, তোমার আবার অসময়ে বাথরুম কেন গো?’
চোখ মুখ ধুয়ে বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করে বেরিয়ে এল বন্দনা, একতলায় বৈঠকখানা ঘরে যখন পৌঁছল তখন চোখে জল নেই, কিন্তু চোখ ফোলা, লালচে, বুকের সামনের কাপড় ভিজে।
কাকার গলার স্বর গমগম করছে। কোথা থেকে এলেন। কিভাবে হঠাৎ ঠিক করলেন, টিকিট পেতে কি কষ্ট! বন্দনা ঢুকে প্রণাম করতে আর্তনাদ করে উঠলেন—‘এ কি চেহারা করেছিস রে বুড়ি?’
বন্দনা প্রাণপণে নিজেকে সামলায়, ঠোঁট কামড়ে মেঝের দিকে চেয়ে আছে। শাশুড়ি বসেছিলেন, নীরস কণ্ঠে বললেন—‘আর কি চেহারাই বা আশা করেন বে-ই মশাই। সব সাধ-আহ্লাদ তো ঘুচেই গেল এই বয়সে। খায় না, দায় না।’
কাকা মাথা নেড়ে বললেন—‘সে কি? এটা তো ঠিক নয়! এ হতে দেওয়া একেবারেই ঠিক নয়।’
কাশীনাথবাবু বললেন—‘কি ঠিক নয় সোমনাথবাবু?’
—‘এইভাবে জীবনটাকে অপচয় হতে দেওয়া কি ঠিক?’ সখেদে বললেন সোমনাথ। কাশীনাথবাবু বললেন—‘জীবন তো তার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। আর জীবন!’ নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর।
কাকা বললেন—‘এ কি কথা বলছেন? বিধাতার দান জীবন! অমূল্য জীবন, সে কি নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক?’
শাশুড়ি বললেন—‘বউমা, কাকাকে ঘরে নিয়ে যাও মা। শুকনো কাপড় চোপড় দাও। একেবারে কাক-ভেজা ভিজেছেন।’
বন্দনার পেছন পেছন ওপরে উঠলেন কাকা। মুখে কথা নেই। ঘরের মধ্যে রূপ রঙ-তুলি নিয়ে মেঝেতে বসে গেছে। তাকে দেখে কাকার মুখে হাসি ফুটল। খপ করে কোলে তুলে বললেন—‘আমি কে বলো তো?’
রূপ বলল—‘আঃ ছাড়ো না, জানি না!’
—‘আগে বলো আমি কে, তবে ছাড়ব।’
এঁকে বেঁকে মানুষটির খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসাবার চেষ্টা করতে করতে রূপ বলল—‘তোমার নাম আমি জানি। বে-ই মশাই। বিচ্ছিরি নাম। এরম নাম আবার হয় নাকি?’
কাকা হাসতে হাসতে বললেন ‘ঠিক বলেছ নাতিবাবু। নামটা বিচ্ছিরি, বুড়ি আমি তোর কে হই ওকে বলে দে তো!’
বন্দনা শুকনো গলায় বলল—‘সত্যিই কি তুমি আমার কেউ হও? কেউ নয় তুমি আমার।’
—‘যাক, এতক্ষণে তোর গলার আওয়াজ পেলুম’। কাকা একইরকম হাসি-হাসি মুখে বললেন ‘যাক একটা ধুতি-টুতি কিছু দিবি তো? যতই ঠাণ্ডা অভ্যাস থাক, তোদের এই সমতলের বৃষ্টি গায়ে লাগলেই যত বুড়োটে রোগ চেপে ধরবে।’
বন্দনা বলল—‘তুমি তাহলে পাকাপাকি ভাবেই পাহাড়ি হয়ে গেলে?’
—‘পাকাপাকি আমি কিছুই হচ্ছি না, তা যদি বলিস। কাঁচাকাঁচি বললে না হয় মেনে নিতে পারি।’
বন্দনা আলমারি খুলে অভিমন্যুর ধুতি-পাঞ্জাবি-গেঞ্জি বার করে দিল। কাকাকে বাথরুমে নিয়ে গেল।
সোমনাথবাবু স্টেশনে নেমে সেখানে লাগেজ রেখে আগে বুড়ির বাড়ি এসেছেন। এতদিনে এই একবারই মাত্র মনে হয়েছে বড় অন্যায় হয়ে গেছে। বুড়িকে দেখে আসা উচিত ছিল। আসলে সোমনাথবাবুর মনোভাব বড় বিচিত্র। বুড়িকে কোলে-কাঁখে করে মানুষ করেছেন, তার বিয়ে দিয়েছেন উপযুক্ত পাত্র দেখে। তারপর দাদা মারা গেলেন, দাদা ছিলেন তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁরও বালকবয়সে বাবা মা মৃত। মস্ত বড় একান্নবর্তী পরিবারে এই দাদাই তাঁকে পক্ষীমাতার মতো সব ঝড়-ঝঞ্ঝা আড়াল করে মানুষ করেছেন। সংসার করেছেন, বেশি বয়সে। বউদি মারা গেলে মনে হয়েছিল দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হলেন। দাদা বা দাদার মেয়ের চেয়ে তাঁর নিজের কষ্ট কিছুমাত্র কম হয়নি। বিয়ে তো করলেনই না। মনের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতেই কিরকম একটা বৈরাগ্য তৈরি হয়ে গেল। ক্রমশই যেন গিঁট খুলছে। দাদা চলে যেতে শূন্য বাড়িতে মনে হয়েছিল জীবনরজ্জুর সব গ্রন্থিগুলো খুলতে খুলতে জীবন- ব্যাপারটা এবার খুব সোজা সরল দাঁড়িয়ে গেল। আর কোথাও আটকে থাকবার দরকার নেই। মেয়ে ভালো ঘরে-বরে পড়েছে। তার কোনও অভাব-অভিযোগ নেই। সে এতই ব্যস্ত যে কাকার কাছে আর দু-দিন কাটিয়ে যাবারও সময় পায় না। ভালোই তো! যে যার নিজের মতো করে সুখী হোক। সুখে থাকলেই হলো। সুখটাই বড় কথা। ব্যস। তাহলে তো কোনও দায় নেই। পরিণত যৌবনে কেদার বেড়াতে গিয়ে হিমালয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন সোমনাথবাবু। মাঝে মাঝেই ট্রেকিং-এ যেতেন। এবার যেন পাকাপাকিভাবেই পায়ে স্পাইক দেওয়া শু, হাতে লাঠি আর পিঠে রুকস্যাক উঠল। উলিকটের গেঞ্জির ওপর গরম কাপড়ের শার্ট, তার ওপর সোয়েটার, কোট, কম্বল চাপিয়ে সোমনাথবাবু চলেছেন এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে। কেদার-বদরি হল তো গঙ্গোত্রী-গোমুখ, সেটা হল তো যমুনোত্রী, সেটা শেষ হলে অমরনাথ, রূপকুণ্ড, সন্দকফু, ফালুট। আবার নেপাল হয়ে এভারেস্টের পাদমূলে। যতটা যাওয়া যায় একটার পর একটা। সারা বছর অফিস করেন, তারপর মাসখানেকের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। চাকরিটা বড্ডই বাধাস্বরূপ মনে হওয়াতে একটু সকাল-সকাল অবসর নিয়ে নিলেন। ব্যাস তারপর থেকে বাধাবন্ধনহীন হিমালয়যাত্রী। আলমোড়ায় বসে খবর পেলেন অভিমন্যুর মৃত্যুর। পিঠের কাছে তখন গোটা হিমালয়ান রেঞ্জ, চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ, ত্রিশূল কোলে কোলে রোদ এসে পড়েছে। অপূর্ব শোভা। কুয়াশা কেটে ক্রমশ ঝকঝক করছে সব। সবই যেন মানুষের কামনা-বাসনা, আনন্দ-বিষাদের ঊর্ধ্বে। মনে হল, না না অভিমন্যু মোটেই হারায়নি, আছে এই পৃথিবীতেই, এই বায়ুমণ্ডলে, শরীরের বাধা মুক্ত হয়ে সে পরমানন্দে ভ্রমণ করছে। সে-ও বুঝি এবার তাঁর মতো পরিব্রাজক-ভূমিকা বেছে নিল। সব মানুষই শেষ পর্যন্ত তাই নেয়। বুড়ির কিছুদিন খুব কষ্ট হবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলে আর কষ্ট নেই। কিছুদিন, মাত্র কিছুদিন মেয়েটা অপেক্ষা করুক। জীবনের সত্য-রূপ বুঝতে মাত্র ক’টা দিন আর। নানান জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে কনখল হয়ে কাশীতে পৌঁছলেন সোমনাথবাবু। কাশীতে থাকাকালীন, দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁর একদিন একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়।
লাক্সার রোডের ধর্মশালা থেকে রোজই দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে আসতেন তিনি। একদিন ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, দেখলেন সাদা থান পরা এক অশীতিপর বৃদ্ধা গঙ্গাস্নান করে জড়-পুঁটলি হয়ে বহু কষ্টে উঠে আসছেন। উঠতে উঠতে হঠাৎ বসে পড়লেন, সোমনাথবাবু তাড়াতাড়ি তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়ে দেখেন তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। ঘাটের সিঁড়ির ওপর সোমনাথবাবুর কোলে মাথা রেখে, সোমনাথবাবুর হাতের গঙ্গাজল মুখে নিয়ে বৃদ্ধা মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে মনে হল বিড়বিড় করে কি বলছেন।
—‘কিছু বলবেন, মা?’ সোমনাথবাবু তাঁর মুখের কাছে কান নিয়ে গেলেন। ‘কিছু চাই?’
—‘নারায়ণ, নারায়ণ,’ অতি কষ্টে বললেন বৃদ্ধা।
—‘বলুন, কি ইচ্ছে আপনার!’
—অজ্ঞাত পরিচয় প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বললেন, ‘বিশ্বনাথ, পরজন্মে যেন আর বিধবা করো না।’
সোমনাথবাবু একটা ধাক্কা খেলেন। মানুষের কত রকমের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনার বস্তু আছে জীবনে। রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দেহি মে। অথচ আশি বছর অতিক্রান্ত এই বৃদ্ধার মুখ দিয়ে এতো অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনা উচ্চারিত হল! আর কিছু চাওয়ার কথা মনে পড়ল না? ঐশ্বর্য, বুদ্ধি, যশ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঈশ্বর-প্রেম কিছু না। শুদ্ধ নির্বৈধব্য?
মুখ তুলতে নানা বয়সের আরও কয়েকটি মুখ দেখতে পেলেন সোমনাথ। বেশির ভাগই শীর্ণ। নানা অভিজ্ঞতার রেখা আঁকা, হাতে গঙ্গাজলের ঘটি, গায়ে নামাবলী, সব মুখেই যেন এক মুখ।
হঠাৎ সোমনাথবাবু সোজা হয়ে বসলেন—মৃত বৃদ্ধাকে অনেকক্ষণ থেকে চেনা-চেনা লাগছিল। কেন তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাঁর মুখে যেন বুড়ির আদল।
ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বললেন—‘দিদিমা মুক্তি পেলেন। আহা বোধহয় গত পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষটা একা একা এই কাশীতে পড়েছিল গা! কী দুঃখুটাই পেয়েছে।’
আর এক জন কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে বললেন—‘গঙ্গার কোলের ওপর গেলেন। মাসিমার ডাক নিশ্চয়ই শুনবেন বাবা, পরের বারে দেখ। যাবে ভাগ্যিমানি জাজ্বল্য এয়োতি হয়ে পাকা মাথায় সিঁদুর পরে। বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ!’
ব্রাহ্মণ সন্তান, শেষ সময়ে মুখে জল দিয়েছেন, অপরিচিতা বৃদ্ধার মুখাগ্নি সোমনাথবাবুই করলেন। সারা দিনের পর স্নানটান সেরে ধর্মশালার টানা বারান্দায় বসলেন। পাহাড় থেকে সমতলে নামলে কিছুদিনের জন্য শরীরটা বেজুত হয়ে থাকে। হরিদ্বারে মাত্র একদিন কাটিয়ে কাশীতে এসেছেন। কেমন একটা অবসাদ। আগে এমন হলে মনে হত, সমতলের হাওয়া তাঁর সহ্য হচ্ছে না, আরও উঁচুতে থাকা দরকার। চলে যাওয়া দরকার, আবার। আজ মনে হল—না। গ্রন্থিমোচন হয়নি। হয়নি বলেই এই অবসাদ। জীবনের পাকে যে গিঁট পড়েছে, তিনি তাকে খোলবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে চলে গেছেন, যতক্ষণ না খুলছেন যতক্ষণ না ফিরছেন, হিমালয় বৈরাগ্য, আনন্দ সব মায়া। সব মিথ্যা। তিনি একেবারেই মূর্খের স্বর্গে বাস করছিলেন। বুড়িমাকে এক্ষুনি একবার দেখে আসা দরকার।
কাশীনাথবাবু এবং তাঁর স্ত্রী কিছুতেই সোমনাথবাবুকে যেতে দেবেন না।
কাশীনাথ এবং তাঁর ভাই বন্দনার খুড়শ্বশুর দুজনেই বললেন—‘লাগেজটা আপনি স্টেশনে রেখে এলেন কেন, বুঝিয়ে বলুন আগে।’
—‘আরে প্রায় বছরখানেক পরে বাড়ি ফিরছি। বাড়ি তো একটা জঞ্জালের আণ্ডিল হয়ে আছে কি না। তাই ভাবলুম ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। দেরি হয়ে যাবে, আগে বুড়িকে দেখে…’
—‘তা বেশ তো, হাতের সুটকেস, বেডিংটা নিয়ে আসতে কি হয়েছিল? বুড়ির বাড়িতে কি আপনার উঠতে নেই?’
বেয়ান হেসে বললেন—‘তা সুটকেসের জিনিসও বুড়ির বাড়ি আছে, আর শয্যের অভাবও ভগবানের ইচ্ছেয় এখনও হয়নি। তোমরা ওঁকে সুটকেস-বেডিং-এর জন্যে অত হয়রান করছ কেন?’
সোমনাথবাবু উকিলি জেরার মুখে খুবই অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। কিছুতেই তিনি মুখ ফুটে বলতে পারছেন না, কুটুমবাড়িতে ও রকম না বলে-কয়ে হুট করে ওঠা যায় না। অন্তত তিনি পারেন না।
বেয়ান বললেন—‘বেশ তো, যা করেছেন করেছেন। এখন মেয়ের বাড়ি দু-দিন জিরিয়ে তবে জঞ্জালের আণ্ডিলে যাওয়া হবেখন।’
বন্দনা চা দিয়ে গেল কুটুমদের জন্য তুলে রাখা, দামী বোন চায়নার কাপে। সঙ্গে মুড়ি, বেগুনি, ফুলুরি। ইলিশমাছ ভাজা। বেলা চারটে প্রায় বেজে গেছে। সোমনাথবাবু তাঁর নিয়ম ভঙ্গ করে ভাতে কিছুতেই আর বসবেন না। শেষ বেলায় গড়িয়ে নেবার অভ্যাসও সোমনাথবাবুর নেই।
বেয়াই-বেয়ানদের সঙ্গে গল্পগাছা সেরে বন্দনার আয়ত্তের মধ্যে আসতে সোমনাথের সন্ধে প্রায় উতরে গেল।
বন্দনা বলল—‘কাশীতে আমার মতো দেখতে কাকে দেখলে তাইতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল বুড়ি বলে একটা মানুষ আছে, নইলে কাশীর পর কোথায় যেতে?’
কাশীর দৃশ্যটা মনে পড়ে সোমনাথের মুখের ওপর ছায়া নেমে এসেছে। কার মুখে কখন তিনি বন্দনার আদল দেখেছিলেন সে সব খুঁটিনাটি তিনি বলেননি। মনে করতেও চান না আর। তবু তো মন থেকে মোছা যায় না কিছুতেই! অশীতিপর এক মৃত্যুপথযাত্রিণীর মুখে এক যুবতীর মুখের আদল কেউ দেখে? তবু তো দেখেছিলেন! মুখের গাম্ভীর্যটাকে মুহূর্তের মধ্যে মুছে ফেলে সোমনাথ বললেন—‘কোথায় আর যেতুম রে বুড়ি। তোর কাছে যে আমার কান বাঁধা। তবে হ্যাঁ, তোকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল খুব। জানি পুঁচকেটাকে নিয়ে পারবি না, তাই উচ্চবাচ্য করিনি। কিন্তু তোর যে খুব অসুখ গেছে। বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছিস মাসের পর মাস—এ সব কথা তো আমি জানতুম না মা!’
বন্দনার চোখে জল এসে যায়! কাকা বলছেন কি! তিনি কি সত্যিই এ পৃথিবীর নন? নির্মম, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন? এমন করছেন, এমন ভাবে কথা বলছেন যেন বন্দনার কিছুই হয়নি, কোনও পরিবর্তনই হয়নি তার জীবনে, মাসের পর মাস বিছানায় শুয়ে থাকার কোনও কারণ যেন তার ঘটেনি। একবারও অভিমন্যুর নাম মুখে আনলেন না। যেন তিনি জানেন না যে সে নেই। ধরেই নিয়েছেন আপাতত সে কোথাও গেছে, সময় হলেই এসে পড়বে। কিম্বা অভিমন্যু ভট্টাচার্য বলে বন্দনার জীবনে, কাকার জীবনে কেউ কখনও ছিল না। তার শোক দুঃখ ক্ষতির কোনও গুরুত্বই তিনি দিলেন না। নিজের কথাতেই ভরপুর। অমরনাথের পথে কোথায় কবে পিছলে বরফের ফাটলে পড়ে যাচ্ছিলেন। মানস সরোবরে সন্ন্যাসীরা কি রকম অবলীলাক্রমে চান করে অথচ জলে হাত দিলে মনে হয় হাত খসে গেল। এভারেস্টের পথে শেরপারা তাঁকে ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখিয়েছিল। এমনভাবে বলছেন যে এক একটা সময়ে রূপের সঙ্গে সঙ্গে বন্দনাকেও হেসে ফেলতে হচ্ছে।
—‘বুঝলে নাতিবাবু, আমি চলেছি আর কুয়াশা চলেছে। আমি যদি চলি তিন পা তো কুয়াশাটা চলে ছয় পা। শেরপা ব্যাটাও চলেছে, কিন্তু চলছে কি না বুঝতে পারছি না তো। এমন ঘন কুয়াশা যে মনে হচ্ছে সামনে একটা খাড়া সাদা দেয়াল, নিশ্চয়ই মাথা ঠুকে যাবে। এমন সময়ে সেই বিচ্ছিরি কুয়াশার মধ্যে থেকে ভেসে এল এক অদ্ভুত ডাক। কোনও মানুষ কিম্বা পশুর গলারও অমন আওয়াজ কেউ কখনো শোনেনি হলপ করে বলতে পারি। জানিস, আগের দিনই আবার শেরপাটা ইয়েতির টাটকা পায়ের ছাপ দেখিয়েছে। এক হাত লম্বা, তিনটে মর্তমান কলার মতন আঙুল। আমি তো ভাবলুম এই আমার হয়ে গেল। আলভারেজের শেষ হয়েছিল বুনিপের হাতে, আর সোমনাথ বাঁড়ুজ্জেকে শেষ করবে ইয়েতি। ইয়েতিই আমার নিয়তি। প্রাণপণে কুয়াশার সাদা দেয়াল ফুঁড়ে যেদিক থেকে ডাকটা আসছিল তার উল্টো দিকে দৌড় লাগিয়েছি। আর কোথায় যায়! সোজা ইয়েতির খাসখপ্পরে। বিচ্ছিরি-গন্ধঅলা বুক। একেবারে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর শুনলুম ইয়েতিটা ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলছে—‘এ সাব। আপ কঁহা দৌড়কে দৌড়কে যাতা, পহলে বোলা না হুঁয়াপর খাদ হ্যায়। হুঁয়া মৎ যানা!’
ধড়ে প্রাণ এল, শেরপা দ্রিমিং। বললুম—‘দ্রিমিং, ইয়েতির ডাক শুনতে পেয়েছ?’
দ্রিমিং বললে—‘ইয়েতিকা আওয়াজ! হায় রাম, আপ কিধরসে সুনা। কহানী সুনকর আপকো দিমাগ বিলকুল খারাপ হো গয়া। ডরো মৎ সাব।’
আমি বললুম—‘এই তো দু মিনিট আগে একটা গোঙানির মতো আওয়াজ। শুনতে পাওনি?’
দ্রিমিং বললে—‘হায় রাম, সাব উও তো হম খাঁসতা থা—বোঝো নাতিবাবু কোথায় ইয়েতির হাসি আর কোথায় দ্রিমিং-এর কাশি।’
রূপ খুব মজা পায়। হেসে লুটিয়ে পড়ে। বন্দনাও হাসতে থাকে, বলে—‘তুমি পারোও বাবা, সেই একরকম রয়ে গেলে। কোত্থেকে গল্পগুলো বানাচ্ছো বলো তো!’
কাকা বলেন—‘তোর মার কথা শুনেছিস? আচ্ছা, এর মধ্যে গপ্প বানাবার আছেটা কি? তবু যদি বলতুম সত্যি ইয়েতি দেখেছি। হিমালয়ে কত মজা, কত রোমাঞ্চ তা তো আর জানিস না। গল্পের চেয়েও অনেক গুণ আশ্চর্য।’
রূপ এখন আস্তে আস্তে দাদুর কোলে উঠে বসেছে। বিরক্তি নেই। আবদার নেই। দুধ খেয়ে নিল দাদুর কোলে বসেই। বন্দনা বলল—‘কতক্ষণ তুই দাদুর কোলে বসে থাকবি রূপু, পা ব্যথা করবে যে!’
কাকা বললেন—‘আরে এখনই দেখছিস কি? এ তো সবে কোলে চড়িয়েছি, এরপর কাঁধে চড়াব, বলো দাদা? তারপর?’
—‘তাপ্পর হিমালয়!’ রূপ হাততালি দিয়ে বলে উঠল।
—‘ওই দ্যাখ বুড়ি, এরই মধ্যে ওকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছি। দিয়েছি তো?’
রাত্রে সোমনাথবাবু জিদ ধরলেন বুড়ির সঙ্গে খাবেন। মেজ দেওর আজকাল বোম্বাইতে বদলি হয়েছে। কলির বিয়েতেও সে আসতে পারেনি। ছোট দেওর আর মিলি আগে খেয়ে নিয়েছে। এবার বাড়ির কর্তাদের পালা। আজকাল খাওয়ার টেবিলে বসবার লোক কমে যাওয়ায় কর্তারা ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই বসেন। কিন্তু আজ বড় বেয়াই এসেছেন। তিনজনে একত্রে বসবেন। সেইমতোই টেবিল সাজানো হয়েছিল। সোমনাথবাবুর জিদ শুনে দুই গিন্নিই আপত্তি করে উঠলেন। গাঁই গুঁই। অসুবিধে আছে। তাছাড়া, বউমার অভ্যাস নেই, ও লজ্জা পাবে। সোমনাথবাবু হেসে বললেন—‘বুড়ি আমার সঙ্গে খেতে লজ্জা পাবে, এ একটা নতুন কথা শোনালেন বটে, বেয়ান। মা অল্প বয়সে চলে গেল। বুড়ির স্কুলে যাবার সময়ে আমাকেই বউদির মতো গরস পাকিয়ে পাকিয়ে খাইয়ে দিতে শিখতে হয়েছিল। প্রথম-প্রথম এমন থাবা ভরে দিতুম যে ওর সাজ নষ্ট হয়ে যেত। জানেন তো। তবু আমি না খাওয়ালে ওর স্কুলে যাওয়াই হত না। আপনাদের বাড়ির বউমা হতে পারে, কিন্তু আমার যে মেয়েও বটে, মা-ও বটে।’
খাবার টেবিল ডান দিকে। শাশুড়িরা দুজনে মিলে সারাটা সন্ধে ধরে অনেকরকম রান্না করেছেন। রুপোর থালায় সাদা বলের মতো লুচি। লালচে মাছের কালিয়া, পোলাও, দই-ইলিশ, মাংস, ভাপা দই, চাটনি। বাঁ দিকে দেয়াল ঘেঁষে বন্দনার কম্বলের আসন পড়েছে। সামনে পাথরের সেট। ফল, মিষ্টি, গ্লাসে দুধ।
সোমনাথবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন—‘ওকি ওটা কি বুড়ির জায়গা? নিচে কেন?’
দুই শাশুড়ি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। খুড়িমা ঢোঁক গিলে বললেন—‘কাষ্ঠাসনে দোষ নেই অবশ্য। তবু মাছ-মাংস ছিষ্টি আঁশ, ছোঁয়া ন্যাপা।’
কাশীনাথবাবু কাষ্ঠ হেসে বললেন—‘বেয়াইমশাই সত্যি-সত্যিই কাশী থেকে এলেন তো? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে খোদ বিলেত থেকে এসেছেন।’
সোমনাথবাবু সে কথা ভালো করে শুনলেনও না, বললেন—‘এত্তো সব দিয়েছেন আমাদের। বুড়ি-মার যে কিচ্ছু নেই!’
খুড়শাশুড়ি বললেন—‘সকালে একবার ময়দা খেয়েছে, রাত্তিরে আবার খেলে ওর অম্বল হয় কি না!’
—‘তো ভাত দিলেন না কেন? এতো বড় রাতটা ওর কাটবে কি করে? ওই শশা, কলা আর খরমুজা যে পেটের মধ্যে তলিয়ে যাবে? বুঝেছি, ওইজন্যেই ওরকম পেত্নীর মতো চেহারা হয়েছে।’
শাশুড়ি ছেলে ভোলাবার মতো করে একটু কর্তৃত্বভরা কণ্ঠে বললেন—‘নিন নিন আরম্ভ করুন বেইমশাই। মেয়েদের খাওয়ার দিকে নজর দিতে নেই। মেয়েমানুষের গতর লোহার গতর, দুটো খুদ খুঁটে খেলেও গতর ফেটে পড়ে। আজ যে আবার একাদশী!’
সোমনাথবাবু বুঝতে-পারা গলায় স্বস্তির নিঃশ্বাসফেলে বললেন—‘তাই বলুন, আজ আপনাদের সব একাদশী। তাই ফল মূল মিষ্টি। সকড়ি জিনিস খাবেন না কেউ।’
কাশীনাথবাবু তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন—‘আপনি বলছেন কি সোমনাথবাবু! চাঁদ থেকে এসেছেন না কি? আপনার কথার অর্থ জানেন? আপনার বেয়ানরা এয়োস্ত্রী মানুষ, ওঁরা একাদশী করবেন? ছি ছি ছি!’
সোমনাথ ধরা গলায় বললেন—‘শুধু আমার ওই একফোঁটা মা-টাই তাহলে এইভাবে নিশিপালন করতে পারবে, বলছেন? দাদা চাঁদ থেকেও আসিনি, বিলেত থেকেও আসিনি। কিন্তু এ আমি বাস্তবিকই বুঝতে পারলুম না। শিক্ষিত বাড়ি আপনাদের! আমাকে মাপ করবেন। এ সব আর আমার গলা দিয়ে নামবে না।’
ক্ষিপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন কাশীনাথবাবু—‘এ তো আপনি আমাদের অপমান করছেন? কুটুম্ব হয়ে বাড়ি বয়ে এসে অপমান। আপনার মেয়ে আমার বাড়িতে বসে অনাচার করছে, তা জানেন? ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হয়ে পেড়ে শাড়ি, গহনা পরে বিবি সেজে বেড়াচ্ছে, তবু স্নেহের বশে কিচ্ছু বলিনি।’
উত্তপ্ত আবহাওয়ায় কথার পিঠে কঠিন কথা আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। শাশুড়ি যোগ করলেন—‘অলুক্ষুণে বউ। সংসারের অলক্ষণ? আমার অমন ইন্দ্রের মতো ছেলেটাকে পেটে পুরেছে। তারও পর অনাচার? এই তো চারদিকে এতো বাড়ি আছে। এতো সংসার আছে। কোথায় এমন বিয়ের ছ-সাত বছর যেতে-না-যেতে এমন ইন্দ্রপাত হয়। আর কোথায়ই বা সোমত্ত বিধবা মেয়েমানুষ হাতে চুড়ি ঝমঝমিয়ে, রঙিন শাড়ি দলমলিয়ে বেড়াচ্ছে? আমরা দুই জা তো সদাসর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি। কোত্থেকে কি সব্বোনাশ হয়ে যায়।’
ক্রোধ-কম্পিত দুই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার মুখ দিয়ে আজ অনেকদিন পর জমা রাগ, ক্ষোভ, দ্বেষ সব গলগল করে বেরিয়ে এল। তাঁদের দিকে শান্ত চোখে চেয়ে, ততোধিক শান্ত গলায় সোমনাথ বললেন—‘আজই বরঞ্চ আমি বুড়িমাকে নিয়ে যাই। ওকে রেডি হতে বলুন।’
দরজার পিঠে ঠেস দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বন্দনা। শাশুড়ির শেষ কথাগুলো কানে ঢুকতে তার হঠাৎ কি রকম তীব্র গা-বমি করে উঠল। টলতে টলতে সে কোনমতে ওপরে গিয়ে ছেলের পাশে শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত, কালিমাখা চোখে আর জল নেই। জল আসে না। রাগও নেই। সহসাই যেন তার বোধশক্তি চলে গেছে।
কিছুক্ষণ পরে এসে কাকা যখন মাথায় হাত রেখে, কোমল গলায় বললেন—‘বুড়ি, রাগ করেছিস?’ সে উত্তর দিতে পারল না।
কাকা পাশে বসে পড়লেন। বললেন—‘এদিকে ফের বুড়ি, আমার দিকে তাকা! আমার সঙ্গে যাবি না?’
সে একটু কেঁপে উঠল। ক্ষীণ স্বরে বলল—‘আমি বড় দুর্বহ। তুমি কি বইতে পারবে?’
সোমনাথবাবু বললেন—‘বুড়ি, আমি তোকে বইব না তুই আমাকে বইবি, সে-সব পরে ঠিক হবে রে। আগে তো তুই এই আবহাওয়া থেকে বার হ।’
কাশীনাথবাবুর গলা খাঁকারির আওয়াজ পাওয়া গেল বাইরে।
—‘বেয়াইমশাই!’
—‘বলুন দাদা’। সোমনাথবাবু বাইরে বেরিয়ে দাঁড়ালেন।
—‘রাগের মাথায় কি বলতে কি বলেছি, দোষ ধরবেন না। হাত জোড় করছি। আপনি না খেলে এরকমভাবে চলে গেলে গেরস্থের অকল্যাণ হয়, মাথা ঠাণ্ডা করে এবার চলুন।’
সোমনাথবাবু বললেন—‘মাথা গরম তো আমি করিনি দাদা! আপনি আমার বড় দাদার মতন। আপনার ওপর কি আমার রাগ করা সাজে? তাছাড়াও, এই মুমূর্ষু মেয়েটাকে আর ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে এতরাতে পথে বার করা বোধহয় ঠিকও হবে না। বৃষ্টিও পড়ছে বেশ। আমরা কাল সকালেই যাব এখন।’
—‘দু চার দিনের জন্যে বউমা আপনার কাছে কাটিয়ে আসবেন এ আর বেশি কথা কি? কিন্তু এইভাবে যদি নিয়ে যান মনে রাখবেন বরাবরের জন্যেই নিয়ে যেতে হবে। খোরপোষের জন্যেও আমি কিছু দিতে পারব না। খোকা তার সব টাকা তার মাকে উইল করে দিয়ে গেছে। সে আমার বড় ছেলে। অনেক যত্ন করে, খরচ করে তাকে আমি মানুষ করেছি। অত খরচ অন্য কোনও সন্তানের জন্য আর করতে পারিনি। তাদের একরকম বঞ্চিতই করেছি বড়র জন্যে। তার সঞ্চয়ের ওপর আমার ন্যায্য দাবি আছে। বউমা এখানে থাকলে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু এখান থেকে তাঁকে নিয়ে গেলে স্বপ্নেও আশা করবেন না যে তাঁর খোর-পোষের জন্য আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারবেন।’
সোমনাথবাবু মৃদু স্বরে বললেন—‘আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন দাদা। অভিমন্যু যদি তার স্ত্রীর ব্যবস্থা করে গিয়ে না থাকে আমার কোনও খরচ দাবি করবার প্রশ্ন উঠছে না। আমি আমার নিজের সাধ্য অনুযায়ী ওদের দেখাশোনা করব। কতদূর কি করতে পারব জানি না, কিন্তু এমন তিল তিল করে মরতে ওকে দেব না। এটা নিশ্চিত।’
ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব এল —‘বেশ।’ রাগত খড়মের আওয়াজ দালানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বাজতে লাগল।
পরদিন বেলা নটা নাগাদ বন্দনা রূপের হাত ধরে কাকার সঙ্গে ট্যাকসিতে গিয়ে উঠল। সঙ্গে দুটি ট্রাঙ্ক, একটি সুটকেস, একটি হোল্ডল। শ্বশুরবাড়ির দেওয়া গয়না বিশেষ ছিল না। কঙ্কনজোড়াই সবচেয়ে ভালো, সেগুলো কলিকে দিয়েছে। হার, আংটি, কানের ফুল কিছু একটা প্যাকেটে করে কাশীনাথবাবুর টেবিলে নামিয়ে রাখলেন সোমনাথবাবু। বললেন—‘ছেলেতে যা ইনভেস্ট করেছিলেন, সবই লস গেল। আমার বুড়ি-মা যতটুকু পারছে ফিরিয়ে দিচ্ছে।’
ক্ষিপ্তের মতো গয়নার ঠোঙাটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললেন কাশীনাথবাবু। সোমনাথ বললেন—‘আসি। অভিরূপকে আমার যথাসাধ্য মানুষ করার চেষ্টা করব। আপনি ভাববেন না।’
তীব্রস্বরে কাশীনাথ বললেন—‘নাতিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে দরকার হলে আমি কোর্টঘর করব। এখন যাচ্ছেন যান।’
সোমনাথ ক্রমশই বিরূপ হয়ে উঠছিলেন। জিভ কেটে বললেন—‘নিজে আইনজীবী হয়ে এটা কি বললেন দাদা। কোর্টে গেলে অবধারিতভাবে বেরিয়ে পড়বে অভিমন্যুর লাইফ-ইনসিওরেন্সের টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বুড়ির গয়না… সবই আপনারা…’
খ্যাঁশখেঁশে গলায় কাশীনাথবাবু বললেন—‘যান, যান, আর কথা বাড়াবেন না। অলক্ষণ যত শিগগিরই দূর হয়ে যায় ততই ভালো।’
বন্দনা গাড়ির মধ্যে বসে শিউরে উঠে কানে আঙুল দিল। আসার সময়ে সে শাশুড়িদের প্রণাম করে আসতে পারেনি। তাঁদের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। শ্বশুরমশাই পা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, খুড়শ্বশুর বাজার করার ছুতোয় বেরিয়ে গেছেন, তাঁরও সঙ্গে দেখা হয়নি। শুধু খুড়তুত ছোট ননদ মিলি ঘটনা-পরম্পরার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বন্দনা দোতলা থেকে একতলায় নামছে, সিঁড়ির মুখে মিলি কাঁদতে কাঁদতে তার আঁচল চেপে ধরেছিল।—‘বউমণি তুমি যেও না, তুমি আর খোকামণি চলে গেলে আমি কি করে থাকব। কে আমার বোনা দেখিয়ে দেবে!’ বন্দনা ফিসফিস করে বলেছিল—‘কলেজ-ফেরত যাস না আমার কাছে, ঠিকানা তো জানিস!’
শ্রাবণের আকাশ সজল, গম্ভীর কিন্তু ক্ষান্তবর্ষণ। এতটুকু হাওয়া নেই। পথের পাশে পাশে অ্যাসফাল্টের যেখানে একটু ফাটল পেয়েছে গজিয়ে উঠেছে ঘাস, ঘাসফুল। গাছগুলোর পাতা চিকন সবুজ, বৃষ্টির জলে নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সেদিকে তাকালেই সানাইয়ে পূরবীর আলাপ শুনতে পাওয়া যায়। লাল বেনারসী, দুহাতে শাঁখা, বালা, হাতভর্তি সোনার চুড়ি। পথে যে এখনও জল জমে আছে। কালকের বৃষ্টির বাসি জল। তার মধ্যে অনেকদিন আগেকার কোন বধূর ছায়া পড়েছে। মাথায় মৃতমায়ের সোনার সিঁথিপাটি, দুধে-আলতা ভরা পাথরের থালা, আলপনা, হাতের মধ্যে ছটফটে মাছ। উৎসুক মুখগুলো ওড়না ফাঁক করে দেখছে, খুড়শাশুড়ি বললেন—‘ঘর-আলো-করা বউ হয়েছে দিদি। বরণ আরম্ভ করো, দুধ তো উথলে গেল বলে।’ হাসি-ভরা গলার আওয়াজ। দুধে-আলতায় পা ডুবিয়ে পা দু-টি গোলাপি। ভট্চায্যি বাড়ির প্রথম বউ, কৃতী ছেলের জন্যে অনেক খুঁজে পেতে সংগ্রহ করে আনা রূপসী বধূর বধূবরণ হচ্ছে।
অধ্যায় ১১
অষ্টমঙ্গলায় বাড়ি ফিরে কলি শুনল বউমণি কাকার কাছে গেছে। খোকা নেই, বউমণি নেই। বাড়িটা কিরকম খালি-খালি লাগছে। শ্রীহীন। এ ক’দিনের মধ্যেই শ্বশুরবাড়িতে বেশ মানিয়ে নিয়েছে কলি। খুব আমুদে বাড়ি। তাদের বাড়ির মতো গুমোরও নেই। গুমোটও নেই। চার ভাইয়ের পরিবার। সে বড় বউ। শাশুড়ি-শ্বশুর কেউ নেই। আছেন এক অবিবাহিত জাঠশ্বশুর। তিনি দিলদার লোক। ভাইপোদের সঙ্গে একত্রে বসে আড্ডা দ্যান। নিজেদের বাড়িতে মাথার ওপর সব সময়ে একটা চাপ টের পেতো। এটা বলতে নেই, সেটা করতে নেই। ওটা করতেই হবে। এ বাড়িতে ও সবের বালাই-ই নেই।
বিয়ের প্রথম তিনদিন কাটতেই জাঠশ্বশুর সবাইকে সামনে রেখে বললেন—‘দ্যাখো বাপু। আমরা পাঁচটি ছোকরা শাসনের অভাবে একেবারে বখে যাচ্ছি। দু-দিন পর আর কেউ আমাদের বাড়ি পদার্পণ করবে না। কাজে কাজেই আমাদের ইহকাল-পরকালের ভার নেবার জন্যে তোমাকে কষ্ট করে আনা। তুমি নতুন বউটি হয়ে থাকলে আমাদের একদম চলবে না।’
সবচেয়ে ছোট ছোকরাটি চোদ্দ বছরের, টেবিল চাপড়ে বলল—‘হিয়ার, হিয়ার। জেঠু আমরা কি বউদিকে শাসনকার্যে সহায়তা করতে পারি?’
—‘তুই আবার কি সহায়তা করবি রে ব্যাটা।’
—‘বউদি, সবচেয়ে বড় ছোকরাটি নানারকমের নেশা করেন, সিগারেট খান এনতার, সিগারেট লুকোলে সিগার, সিগার লুকোলে নস্যি, নস্যি লোপাট করে দিলে, দোকান থেকে জর্দা পান খেয়ে আসেন, এঁর কিঞ্চিৎ লাঠৌষধির দরকার হয়ে পড়েছে। দ্যাখো তুমি তোমার শাসনদণ্ড ব্যবহার করবে কি না!’
কলি ভীষণ অপ্রস্তুত। কিন্তু জেঠু একটুও টসকালেন না। বললেন—‘আরে বউমা, তোমাকে এখন অনেক কাজ করতে হবে। তুমিও মা একটা নেশা না হলে এতে পেরে উঠবে না, জর্দা পান ধরো, মুস্কিপাতি জর্দা। একটু একটু করে ডোজটা বাড়াবে।’ সবাই হই-হই করে উঠতে জেঠু হাসতে হাসতে চলে গেলেন, মুখ ফিরিয়ে বলে গেলেন—‘আর আমার পেছনে লাগবি তোরা? সর্ষেতে ভূত ধরিয়ে দোব।’ কলির বর সঞ্জয়ও খুব রসিক মানুষ। ফাজিলই বলা চলে। কাউকে দু-মিনিটগম্ভীর থাকতে দেয় না। বাসি-বিয়ের দিন কলি গম্ভীর হয়ে ছিল, মন খারাপ স্বভাবতই। সঞ্জয় তার পরের ভাইকে বললে বিজু, এই বিজু চট করে পান্তুয়া নিয়ে আয় তো ক’টা। ভাই সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করল। সঞ্জয় পান্তুয়াগুলো কলির মুখের পাশে ধরে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, আর মাথা নেড়ে ‘উঁহু’ বলে রেখে দেয়। ঘরশুদ্ধ লোক হাসছে। জিজ্ঞেস করছে, ‘কি হল?’ ‘কি দেখছিস রে সঞ্জয়?’ ‘কি করবি রে দাদা?’ সঞ্জয় বলল, ‘দেখছি কোনটা বেশি গোল, নতুন বউমার চোখ, না ভানু ঠাকুরের পান্তুয়া।’ কলি হেসে ফেলতেই তার মুখের মধ্যে একটা পান্তুয়া গুঁজে দেওয়া হল। পেছন থেকে কে একজন হাত দুটো ধরে রেখেছে। কলিকে পান্তুয়া গলাধঃকরণ করতেই হল। সঞ্জয় বলল, ‘দেয়ার য়ু আর। আমাদের বাড়িতে কাউকে মুখ গোমড়া করে থাকতে দেওয়া হয় না। মুখ গোমড়া করলেই পান্তুয়া খেতে হয়।’
এতো তাড়াতাড়ি, নতুন জামাইয়ের সঙ্গে আলাপ-সালাপ না করেই বউমণি কাকার কাছে চলে গেছে শুনে কলির একটু অভিমান হল। বাড়িতে আর সবাই তো বুড়োবুড়ি। মিলি, ছোড়দা আর বউমণি। মেজদা তো কর্মস্থল থেকে ছুটিই পেল না। বউমণির ঘরেই কলিদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। কলির মনে হল ঘরটা দরকার হবে বলেই কি বউমণি চলে গেল? কেন আর কি ঘর ছিল না? এতো বড় বাড়ি তাদের!
মিলিটাকে একা পাওয়াই যাচ্ছে না। জামাইবাবুর সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে আছে। জামাইবাবুটিও তেমনি। কথায় কথায় ছ্যাবলামির ফোয়ারা। একবার সামনে দিয়ে যেতে-যেতে শুনতে পেল মিলিকে অফার দেওয়া হচ্ছে—‘আরে বাবা, আমার একলারই তো বিয়ে হয়ে গেছে? আমার তো আরও তিনটে ভাই রয়েছে। যাকে ইচ্ছে তুমি গলায় মালা দাও। ব্যাস দিদির কাছেও থাকতে পাবে, জামাইবাবু মানে সঞ্জয়দার কাছেও থাকতে পাবে।’
সঞ্জয়ের পরের ভাই বিজু এবার মিলির সঙ্গেই বি এস সি দিয়েছে। তার পরের জন সবে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে, ছোট জন তো ক্লাস নাইনে পড়ে। যদিও এঁচড়ে পক্ব।
মিলি বলছে— ‘ইঃ, আপনার সব তো-পুঁচকে পুঁচকে ভাই! তাদের বিয়ে করতে হবে আমায়? কেন, আমায় বিয়ে পাগলা ঠাউরেছেন না কি?’
—‘না, না, সে কথা না, আমাকে তোমার খুব পছন্দ হয়েছে কি না, তাই বলছিলুম। আমার প্রোটোটাইপ কিন্তু আর ভূভারতে খুঁজে পাবে না।’
কলি ঘরে ঢুকে বলল—‘এই মিলি। গাছে জল দিয়েছিস?’
—‘এমা একদম ভুলে গেছি।’ মিলি উঠে পড়ল। ছাদের গাছগুলো দুই বোনেরই সমান প্রিয়।
কলি বলল—‘দ্যাখ, মনে হচ্ছে কতদিন তোতে-আমাতে গাছে জল দিইনি। এ ক’দিন দিয়েছিলি তো?’
—‘হ্যাঁ’ মিলি বলল, ‘ওতে আমার ভুল হয় না। তোর ফুলশয্যের দিন তত্ত্ব সাজাতে সাজাতে হাত ভেরে গেছিল, তা-ও দিয়েছি ঠিক।’
কলি বলল—‘হ্যাঁ রে, আমাদের পড়ার ঘরটাতে কিম্বা ছোড়দা-মেজদার ঘরটাতে বুঝি থাকবার ব্যবস্থা করা যেত না!’
—‘কার থাকা?’
—‘এই আমাদের!’
—‘যাঃ। ও ঘরে আবার নতুন জামাইকে থাকতে দেওয়া যায় না কি? তক্তাপোশ গায়ে ফুটবে না?’
—‘তো তাই বুঝি বউমণি কাকার কাছে চলে গেল? বউমণি শেষ কবে বাপের বাড়ি গেছে ভুলেই গেছি। এমনি যাক, যাক। এই কারণে যেতে হলে আমার খুব খারাপ লাগবে।’
—‘তোকে বলেছে!’ মিলি ঠোঁট উল্টোল, ‘কে তোকে বললে নতুন জামাই থাকবে বলে বউমণি বাপের বাড়ি গেছে। তাই জন্যে না আরও কিছু! জ্যাঠামশাই তো বউমণিকে তাড়িয়ে দিয়েছে।’
—‘তাড়িয়ে দিয়েছে মানে?’ কলি ভীষণ অবাক হয়ে বলল।
—‘বউমণিকে, বউমণির কাকাকে। কাকা এসেছিলেন। রাত্তিরে খেতে বসে সেকি ঝগড়া! যদি শুনতিস। আমি শুয়ে পড়েছিলুম। উঠে বসে ঠকঠক করে কাঁপছি। বউমণির শরীর খারাপ হয়ে গেছে, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করে না এই নিয়ে কি বলেছিলেন, বাস আর যায় কোথায়!’
—‘বউমণির শরীর খারাপ হয়ে গেছে, খায় না এতো সত্যি কথা!’
—‘জানি না বাবা, সব খেপে লাল। জেঠিমা বললে অলক্ষণ, জ্যাঠামশাই বললে যত তাড়াতাড়ি যায় তত ভালো।’
—‘বলিস কি রে? কলির চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে, নিঃশ্বাস ঘন, ‘তুই কিছু বললি না?’
মিলি অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল—‘আমি? আমি কি বলব?’
মাত্র সাতদিন বিয়ে হয়েই কলি যেন অনেক বড়, অনেক পরিণত, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠেছে। বলল—‘তুই না হয় চিরকালের খুকুমণি। ছোড়দা? ছোড়দা কোথায় ছিল?’
—‘ছোড়দা? তবেই হয়েছে? আমি যদি খুকুমণি হই তবে ছোড়দাটা কি রে? নবজাত শিশু? গোলমাল শুনে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—‘এই মিলি মিলি, এতো গোলমাল কিসের রে?’ আমি বললুম—‘কি জানি বউমণিকে নিয়ে কি সব হচ্ছে।’ ছোড়দাটা কি বলল জানিস? বলল —‘বুড়োগুলো জ্বালালে। আমি ছাদে যাচ্ছি। গোলমাল থেমে গেলে, কোস্ট ক্লিয়ার দেখলে সাইরেন বাজাবি, আমি নেমে আসব।’ পরদিন বউমণি যখন ন’টা নাগাদ চলে যাচ্ছে, তার আগেই ছোড়দা না-খেয়ে-টেয়ে অফিসে তাড়া আছে বলে পগার পার।’
—‘এ বাড়ির কেউ মানুষ হল না। বড়দাই একমাত্র ছিল, যাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা যায়।’
—‘আর সব মেনিমুখো, না রে?’ মিলি উৎসাহের সঙ্গে বলল।
কলির মনের মধ্যে ব্যথা আর রাগ প্রতিযোগিতা করে বাড়ছে। সে মিলির কথার জবাব দিল না। তরতর করে নেমে এল। মিলি ব্যস্ত হয়ে পেছন পেছন নামতে নামতে বলল—‘এই দিদি। কাউকে বলিসনি আমি বলেছি, প্লীজ, মা আমাকে মেরে ফেলবে।’
কলি একেবারেই দাঁড়াল না। নিচে নেমে এসে রান্নাঘরে মাকে পেয়ে গেল। জামাই খাবে, মা ঘি-ভাত চাপিয়েছে, ডেকচির ঢাকনির ওপর জ্বলন্ত কয়লা সাজাচ্ছে। কাকিমাকে দেখতে পাওয়া গেল না। কলি বিনা ভূমিকায় বলল—‘মা এসব কি শুনছি?’
—‘কি শুনছিস?’
—‘বউমণিকে নাকি তোমরা তাড়িয়ে দিয়েছ?’
—‘কে বললে?’ আঁচলের চাবির গোছা সশব্দে কাঁধে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালেন কলির মা।
—‘যেই বলুক, কথাটা তো সত্যি!’
—‘আমরা তাড়িয়েছি। না সে নিজে তেজ করে গেছে! মটমটে তেজ! কোথায় ছিল অত তেজ। অত আদিখ্যেতার কাকা! মরণকালে তো একবার দেখতেও আসেনি। এল, চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যি শোনাল, বাস অমনি তিনি ধিন ধিন করে নেচে উঠলেন। ভাঙবে, ওই তেজ ভেঙে সে আবার ফিরে আসবে। দাদাভাইটার জন্যে আমার’… গলা ধরে এল শেষের দিকে।
কলি কঠোর গলায় বলল—‘মা সেজদাকে তোমরা তাড়িয়ে দিয়েছিলে সে কি ফিরেছে? বউমণিকেও তাড়ালে? সে-ও ফিরবে না। খোকাও ফিরবে না। তোমাদের এই মহাপবিত্র বাড়িতে শেষ পর্যন্ত তোমরা চার বুড়োবুড়ি ছাড়া কেউই থাকবে না। খোকামণিকে তোমরা ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও করো না। এই আবহাওয়ায় সে মরে যাবে।’
কলির মায়ের কানে তার র্ভৎসনার প্রথম অংশটা লেগে ছিল।
তিনি বললেন—‘সেজদার কথা উঠল কিসে?’
—‘কিসে আর? নিজের ছেলেকে তাড়াচ্ছ, বউকে তাড়াচ্ছ, যে তোমাদের তালে তাল মেলাতে একটু এদিক ওদিক করছে তাকেই তাড়াচ্ছ!’
—‘তালে তাল মেলালে ক্ষেতিটা কি শুনি? আমরা তো বয়সেও বড়, দেখলুম না জীবনে কম। আমাদের কথা শুনলে মন্দটা কি হয়? তোর কিছু মন্দ হয়েছে?’
—‘হয়নি। হতে কতক্ষণ! সংস্কারই যদি মানো তো এটুকু তো মানবে আমার বিয়ের সাতদিনের মধ্যে বাড়ির বউ, একমাত্র বাচ্চা এ বাড়ি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে! এতে আমার ভালো হবে মনে করো?’
কাকিমা এসে দাঁড়িয়েছেন। সংসারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কলি তার মায়ের সঙ্গে রাগারাগি করছে। এটা সম্পূর্ণ নতুন। কিন্তু যতটা নতুন, কাকিমার চোখে ততটা লাগল না। মাথায় একমাথা সিঁদুর পরে, হাতে শাঁখা, সোনাবাঁধানো লোহা, একগা গয়না, কলি যেন ক’দিনেই অনেক বড় হয়ে গেছে। অনেক অধিকার অর্জন করে ফেলেছে। কাকিমা আস্তে আস্তে বললেন—‘কথাটা কিন্তু কলি ঠিকই বলেছে দিদি।’
কলির মা বললেন—‘সে যদি তেজ করে চলে যায়, তার কাকার উশকুনিতে তো আমি কি করব?’
—‘সে তো তেজ করে যায়নি দিদি। তা যদি বলো, তেজ সে বেচারী কোনদিনই দেখায়নি। বটঠাকুর এমন করে বললেন যে তারপর আর বেয়াইয়ের ওকে এখানে রাখা চলে না, মানুষের একটা মান-অপমানও তো আছে। আর যাই বলো দিদি! বউটা কি রোগা হয়ে গেছে! বাড়ি থেকে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেল। আমার ভালো লাগেনিকো।’
কাকিমা চোখে আঁচল দিলেন।
কলির মা বললেন—‘কর্তার যা গোঁ! কথায় কথায় মানের কণা খসে যায়। যত গালাগাল তো উনিই করলেন। ছি, ছি, একশ-বার ছি!’
কলি বলল—‘বুঝছো যদি তো বউমণিকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করো মা। তোমরা নিজেরা যাও। গিয়ে বলো।’
—‘ওরে বাবা। সে কথা কর্তাকে কে বলবে? হুলো বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা! সে আমার দ্বারা হবে না।’
কলি বলল—‘ঠিক আছে। তোমরা না বলো তো আমি বলব। ইয়ার্কি নাকি? বাবা কি চিরকাল যা ইচ্ছে তাই করবেন না কি? বউমণির এটা নিজের বাড়ি না? কাকিমা তুমিই বা কি? কাকাও তো ছিলেন? কেউ একটা কথা বলতে পারলে না?’
কাকিমা বললেন—‘চিরকাল চোখ নিচু করে, মুখ নিচু করে থেকেছি মা। বটঠাকুরকে দেব্তার মতো মান্যি করেছি, দিদিকেও। দিদি সে কথা জানে। মুখের ওপর কথা বলবার অভ্যাস নেই মা, থাকলে কি আর এতো বড় অন্যায়টা চোখের ওপর দিয়ে হতে পারত!’
শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার আগের মুহূর্তে বাবার সঙ্গে কলির তীব্র বচসা হয়ে গেল। কলি শুধু বউমণিকে ফিরিয়ে আনবার কথাই বলেনি। সেজদাদের খোঁজখবর করার কথাও বলেছিল। বিবাহিত না হলে বাবা বোধহয় তাকে তুলে আছাড় দিতেন। ধমক দিলেন প্রচণ্ড। কলি বলল—‘আমি উচিত কথা বলবোই। তোমার নিজের যাওয়া উচিত বউমণিকে ফিরিয়ে আনতে।’
উচিত কথা মেয়ে তাঁকে শেখাচ্ছে বলে কাশীনাথবাবু এমন চিৎকার করলেন যে নতুন জামাই ছুটে এল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বলল—‘বাপরে এমন জাঁদরেল বাড়ির জাঁহাবেজে মেয়েকে বিয়ে করেছি আগে বুঝতে পারিনি তো!’
কলির চোখমুখ থমথম করছিল, বলল—‘আস্তে আস্তে বুঝবে।’
অধ্যায় ১২
সোমনাথবাবু বললেন—‘বুড়ি একটাই মুশকিল মা। আমার পেনশন আর ডিভিডেন্ডের টাকায় আমার একারটা রাজার হালে চলে যেত। দাদার জমা টাকাও বেশ কিছু ছিল। কিন্তু আমি যে ছাই ভ্রমণ করে করে তার অনেকটাই খরচ করে ফেলেছি। সে টাকা তো আসলে তোরই। দাদারও সে জ্ঞান হয়নি, আমারও না।’
বন্দনা রাগ করে বলল—‘তা, বাবার টাকাকড়ি, যা নাকি আসলে আমার, সে সব খরচ করে ফেলেছো বলে কি আর আমাকে খাওয়াবে না? নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে বলছ, না কি বলো তো!’
এতোটা তরল ভঙ্গিতে কথা বলা অনেক দিন বন্দনার অভ্যাস নেই। কিন্তু নন্দন রোডের এই দোতলা সবুজ রঙের বাড়িটার মধ্যে ঢুকে হঠাৎ তার শরীর মনের ওপর থেকে একটা ঘেরাটোপের মতো বিষণ্ণতার আবরণটা খসে পড়েছে। ছেলেকে বলছে—‘দ্যাখ রূপু, এই উঠোনটা আমার সুইমিংপুল হতো ছোটবেলায়। মুষলধারে বৃষ্টি পড়লে নর্দমাটা বন্ধ করে দিতুম। দাওয়া অবধি জল উঠে যেত, তার ভেতর সাঁতার কাটতুম। কাকাও নামত, জানিস তো?’
রূপ বলল—‘আমিও করব মা, আমিও করব। তখন কিন্তু বারণ করতে পারবে না।’
ছাদের লোহার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে অন্তত পাঁচ বার ওঠা-নামা করা হয়ে গেল ছেলের। দু-তিনটে ধাপ দৌড়ে ওঠে। আর ফাঁক দিয়ে হাসি-হাসি মুখ বার করে নিচে তাকায়, সেই মুখে বন্দনা তার নিজের ছেলেবেলার মুখখানা অবিকল দেখতে পায়। ছাদের ওপর সে স্কিপিং করত, পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে চু-কিত-কিত খেলত। কিংবা নাম-পাতাপাতি, কিংবা বুড়ি-বাসন্তী। খেলার নাম শুনে রূপ হেসেই অস্থির। দোতলার দালানে এক কোণে দেয়াল-আলমারি, তাতে মায়ের তোলা বাসন থাকত। তার তলায় দু-ফুট মতো ফাঁক। সেই জায়গাটুকুতে ছিল তার পুতুলের সংসার। মা একটা পর্দা করে দিয়েছিল। পর্দাটা দু পাশে সরিয়ে দিলেই তার পুতুলের সংসার বেরিয়ে পড়ত। বেনে পুতুল, মুড়কি পুতুল, কাচের পুতুল, কাচকড়ার পুতুল এবং সবচেয়ে দামী, সবচেয়ে আদরের আলুর পুতুল। তাকে রোজ ফ্রক পাল্টে, দুধ খাইয়ে তবে তার নিজের খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হত। সে কথা বলতে কাকা বললেন, ‘তোর সেই আলুর পুতুল কিন্তু আলমারিতে এখনও তোলা আছে বুড়ি। তুই তাকে শেষ যে ফ্রকটা পরিয়েছিলি, সেটা পরে। এখন যদি ছেলেকে দিতে চাস তো দিতে পারিস!’
রূপ বলল—‘ধ্যাৎ। আমি কি মেয়ে যে পুতুল নিয়ে খেলব! মেয়েগুলো বোকা তাই আলু-পটলের পুতুল নিয়ে খেলে।’
বন্দনা হেসে ফেলল—‘আলু-পটলের আলু নয় রে, প্লাস্টিকেরই পুতুল, আমাদের ছোটতে তাকে আলুর পুতুল কেন বলতো জানি না।’
সোমনাথবাবু খাতা-কলমে কিসব অঙ্ক কষে বললেন—‘তিনজনের চলে যাবে ঠিকই। কিন্তু একটু কষ্ট করতে হবে। একটু হিসেব করে চলতে হবে—এই আর কি!’
বন্দনা বলল—‘বারে, হিসেব করে চলা বুঝি আমার অভ্যেস নেই? আমার বিয়ের আগেকার কথা ভাবো তো! কে করত হিসেব?’
সোমনাথ বললেন—‘আমাতে আর তোতে। ঠিকই। কিন্তু সে তো হিসেবে চলত না রে, বেহিসেবে চলত। যা ইচ্ছে, যা দরকার, দাও খরচ করে দাও। নেহাৎ খরচা করার নানান উপায় আমাদের খুড়ো-ভাইঝির জানা ছিল না তাই। কিন্তু তোর ছেলে তো বড়মানুষের ছেলে, আজকালকার ছেলেও বটে।’
—‘ওকে মাথায় চড়িয়ে আর আমার সর্বনাশ করো না’, —বন্দনা বলল আমাদের যেমনি আয়, আমরা তেমনিই চলব। ওকে অযথা আদর, প্রশ্রয় একদম নয়। আর তুমি অত ভাবছোই বা কেন? আমার হাজার পঁচিশেক টাকা ফিক্সড আছে।’
সোমনাথ বললেন—‘ওতে তুই হাত দিসনি। ওটা থাকুক। পরে কত খরচ আছে।’
—‘লোকজন রেখ না। কাজকর্ম আমি একাই করে নেব।’ বন্দনা পরামর্শ দিল।
—‘তুই কি পারবি? যা ভূতের মতো চেহারা হয়েছে।’
—‘না কাকা, আমাকেও কিন্তু অযথা আদর দেবে না। কাজ করতে পেলে আমি বেঁচে যাব। তিনটে মানুষের তো কাজ!’
অবশেষে, অনেক বাগবিতণ্ডার পর ঠিক হল বাসন মাজা এবং ঘর-পরিষ্কারের জন্য একজন লোক থাকবে। কিন্তু বাকি সব, অর্থাৎ রান্না এবং তার আনুষঙ্গিক ও কাপড়-কাচা বন্দনা নিজেই করবে।
কার্যকালে অবশ্য দেখা গেল, কাজের লোকটির চেয়ে অনেক বেশি কাজের সোমনাথবাবু নিজে। নিজের গুলো তো বটেই, রূপের জামাকাপড়, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি খুব নিপুণভাবে কেচে ফেলে তিনি চোরের মতো কলঘর থেকে বেরোচ্ছেন এবং বন্দনার হাতে ধরা পড়ে যাচ্ছেন। বন্দনা ঝঙ্কার দিচ্ছে—‘আচ্ছা কাকা, তুমি কি বলো তো? বিছানার চাদর কি কেউ রোজ রোজ কাচে? কালই তো আছড়ে আছড়ে কাচলে।’
সোমনাথবাবু অপরাধীর মতো মুখ করে বলছেন—‘আজকে তোদেরটা কেচে দিলুম।’
—‘বাঃ। তাহলে আমি কাচব কি? রূপুর গুলোও তো তুমিই কেচে দিলে।’
—‘আরে, কত কাচার আছে, ধর, তোর ওই বালিশের ওয়াড় গুলো, তার ঢাকা…।’
এবার বন্দনা হেসে ফেলে। কাকা করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে বলেন—‘তুই আগে বেঁচে ওঠ মা, তারপরে করতে চাইলে অনেক কাজ পাবি।’
ভোরবেলা চা করে তিনি বন্দনাকে ডাকেন। ততক্ষণে তাঁর আনাজপাতি কাটাও সারা। বঁটি দিয়ে পারেন না, টেবিলের ওপর ছুরি দিয়ে সব ফালা-ফালা করে কেটে রেখেছেন।
প্রথম যেদিন ভোরবেলায় চা খেতে ডাকলেন কাকা, তখন পাখিরা সবে তাদের আধো-আধো বুলি কপচানো সেরে ব্যস্ততার সুর ধরতে আরম্ভ করেছে। জানলা দিয়ে সরু ফিতের মতো আবছা আলো এসে পড়েছে, একটু পরেই সেটা রোদ হয়ে উঠবে। —‘বুড়ি বুড়ি, চা হয়ে গেছে রে, ওঠ।’ যেন বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসে এই ডাক।
ঘরের বাইরের দালানেই খাবার ব্যবস্থা। আগে রান্নাঘর, খাবার ঘর, বৈঠকখানা সব নিচে ছিল। সোমনাথবাবু সে সব ব্যবস্থা ওপরে তুলে এনেছেন। ইচ্ছে আছে, নিচেটা ভাড়া দিয়ে দেবেন। বড় চৌকো দালান, তারই একধারে পার্টিশন করে নিয়ে রান্নার ব্যবস্থা। অন্য দিকটাতে টেবিল পাতা; সেই সাবেকি গোল টেবিল, যাতে একসময়ে বন্দনা তার বাবা-কাকার সঙ্গে খেতে বসত।
বন্দনা বিছানা ছাড়তে-ছাড়তে বলল—‘ওকি! আমায় ডাকলে না! এত ভোরে চা-ই বা কেন?’
—‘ভুলে গেছিস? ভুলে মেরে দিয়েছিস সব? আমরা তিনজনে এমনি ভোরে চা খেতুম না বুঝি? শিগ্গিরি আয়। জুড়িয়ে যাবে।’ কাকা নিজের পুরনো র্যাপার ভাঁজ করে চায়ের পট ঢেকে রাখেন।
—‘দাঁড়াও আগে দাঁত মাজি, কাপড় ছাড়ি।’
—‘এ হে হে হে, তুই যে দেখছি সাত গিন্নির এক গিন্নি বড়াইবুড়ি হয়ে উঠেছিস! এ যে বাসি মুখে বাসি কাপড়ে খাবারই চা রে!’
—‘না বাবা, আমার অভ্যেস নেই।’
—‘শোন বুড়ি, মুখটা ধুয়ে আয়। কাপড়-টাপড় ছাড়তে যাসনি। আগে চা, তারপর অন্য সব। চা জুড়িয়ে যাবার মতো প্যাথেটিক ব্যাপার আর হয় না।’
অগত্যা বন্দনা বেডটির অভ্যাস ঝালিয়ে নেয়। প্রথম প্রথম শ্বশুর বাড়িতে খুব অসুবিধে হত। সকালে জলখাবারের সময়ে দুধ খেতে হত। বাবাকে শাশুড়ি জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলেন—‘বেয়াই মশাই, আপনার মেয়ের খাওয়া-দাওয়ার অভ্যেস কি?’
বাবা কিছুই বলতে চান না।—‘যা দেবেন তাই খাবে, ওর কোনও ন্যাটা নেই।’
—‘তবু!’
তখনই বাবা বলেছিলেন—‘মেয়েটি আমার বেড়াল। মাছ আর দুধ ছাড়া চলে না। বাস আর কিছু চাই না।’ সকালে এক কাপ দুধ খাওয়া। কিন্তু ভোরবেলা উঠে যে তার আগেই একবার চা খাওয়া হয়ে যেত, সেটা আর বাবা ভেঙে বলেননি। বললেও অবশ্য বিশেষ কাজ হত না। কারণ এ বাড়িতে, সকালবেলায় শুদ্ধ হয়ে স্নান-টান করে তবে খাবার নিয়ম।
ভোরবেলা ঘুম ভেঙে প্রাণটা চা-চা করত। অভিমন্যু অঘোরে ঘুমোচ্ছ। তাদের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর রয়েছেন। ঠাকুমা এই সেদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তাঁর বেঁধে দেওয়া নিয়ম পালন করেই তারা বড় হয়েছে। বিদেশে বেড়াতে গিয়ে ভোরবেলা বেয়ারা চা নিয়ে ডাকাডাকি করলে অভিমন্যু ভীষণ বিরক্ত হত—‘এঃ, দিলে ঘুমটা মাটি করে।’ বন্দনা কিন্তু ভাবত বাড়িতে না হোক ঘরের মধ্যে যদি চালু করা যায় জিনিসটা। কিন্তু মানিয়ে নেওয়ার অভ্যাস আবার সব অভ্যাসের ওপরে যায়! কবে ভোরের গলা-শুকোনো বন্ধ হয়ে গেছে। বাসি কাপড় না ছেড়ে, স্নান না করে কিছু খাবার চিন্তাও অশুচি মনে হতে আরম্ভ করেছে, সে নিজেই জানে না। সে স্নান করে আসার পর অভিমন্যু বিছানা ছাড়বে, বিশেষত ছুটির দিনে, তখন কত রকম আহ্লাদিপনা, ঢং করবে গায়ে পড়ে। বন্দনা তাড়াতাড়ি দূরে সরে গিয়ে বলত—‘ইস্ দিলে তো ছুঁয়ে! যাই, বদলে আসি কাপড়টা!’
—‘কাছাখোলা বাড়ির মেয়ে। তোমার আবার কবে থেকে এতো ছুঁৎমার্গ হল গো!’
—‘হয়েছে, হানতি পারোনি।’ বন্দনা উত্তর দিত।
এখন আবার সেই অভ্যাসকে জোর করে পাল্টে ফেলা। কাকা তাকে তার কুমারী-জীবনের ছন্দে নিয়ে আসবেনই। নইলে নিজের জীবনটার ছন্দও বোধহয় মেলে না। বেসুরো, বেতালা হয়ে যায়।
রান্নাঘরে গিয়ে বন্দনা দেখল, টেবিল-ময় কুচি-কুচি আলু। কুচি-কুচি লাউ; ফালা-ফালা পেঁয়াজ।
—‘একি! ও কাকা! এগুলো কি হবে গো?’
কাকা মাথা চুলকে বলেন—‘কেনরে আলু রাঁধবি, পেঁয়াজ রাধবি, লাউ রাঁধবি। মাছ সব কাটিয়ে কুটিয়ে এনেছি।’
বন্দনা বলল—‘আলু যে রাঁধব সে তো হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি, লাউও রাঁধব। কিন্তু কি রাঁধব? তোমার প্ল্যানটা কি?’
—‘প্ল্যান আবার কি? রান্নাও আবার একটা কাজ। তারও আবার প্ল্যান? দেনা সব কিছু নুন চিনি আদা হলুদ দিয়ে চড়িয়ে, দেখবি দিব্যি একটা যা-হোক কিছু হয়ে যাবে।’ সোমনাথবাবু একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলেন।
বন্দনা বলল—‘তোমাকে আর আমায় এতো সাহায্য করতে হবে না। আর কত কেটেছো বলো তো! আমরা মানুষ আড়াইটে সে খেয়াল আছে? নাকি আমি রাক্ষসী-টসী হয়ে এসেছি বলে তোমার ধারণা।’
রূপ তার আগের স্কুলেই যাচ্ছে। প্রচণ্ড খরচ স্কুলের, স্কুল বাসও আছে। সোমনাথবাবু তার জন্যে আলাদা খেলার ঘর করে দিয়েছেন। সে ওই ঘরে সমবয়সী ছেলে-মেয়ে জুটিয়ে বিজলি-চালিত এরোপ্লেন, কাঠের দোতলা বাঘ-আঁকা বাস, রবারের সেপাই-বাহিনী। ব্যাগাটেলি ইত্যাদি নিয়ে মহা-আনন্দে সময় কাটায়। বিকেলবেলা মাঠে যায় হাতে ক্রিকেট ব্যাট, ক্যাম্বিসের বল, উইকেট নিয়ে। ও বাড়িতে নজরদারি ছিল খুব বেশি, বাড়িতে অন্য কোনও বাচ্চা সহসা ঢুকতে পেত না। রূপ ছিল সঙ্গীহীন। পার্কে গেলেও মন খুলে খেলাধুলো করার বা সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ পেত না। এখানে শুধু বন্ধুবান্ধবই নয়। খেলার মাঠে তাকে ছেড়ে দিয়ে সোমনাথবাবু কাছাকাছি বেঞ্চে বসে থাকেন। অনেক সময়ে ঘুরে বেড়ান। রূপের সেই প্রচণ্ড মা-মা বাতিক কমতে আরম্ভ করেছে। সকালবেলা তাড়াতাড়ি চান-টান সেরে মাকে গম্ভীর চালে বলে—‘দেখো আবার বেশি দেরি করিয়ে দিও না, যা হয়েছে তাই দিয়ে দাও।’ তারপর কাকার হাত ধরে বড় রাস্তায় স্কুলবাস ধরতে যায়। কিছুতেই সোমনাথবাবুকে সে দাদু বলবে না। দাদু তো শ্যামবাজারে থাকে। ছোড়দাদুও তো শ্যামবাজারে থাকে। এটা কাকা। মায়েরও কাকা, ছেলেরও কাকা। বন্দনা বলেছিল—‘কেন শ্যামবাজারের বাড়িতে তোর কাকা নেই বুঝি? আমার কাকাকে কেন কাকা বলবি রে?’
রূপ মায়ের অজ্ঞতায় অবাক হয়ে যায়—‘সে তো কাকু! মেজকাকু, ছোটকাকু! কাকা কোথায়?’
—‘ঠিক আছে বাবা, যা প্রাণ চায় বল। তুই খুশি থাকলেই হল।’
প্রথমটা ভাবা গিয়েছিল, দাদু-দিদার জন্য রূপ খুবই কান্নাকাটি করবে। কিন্তু দেখা গেল বাচ্চারা খুব স্বার্থপর। নিজের খেলাধুলো, খাওয়া-দাওয়া, বন্ধুবান্ধব এবং মায়ের কোলটি ঠিক থাকলে আর বাদ বাকি সব কিছুই তারা চট করে ভুলে যেতে পারে। এক দাদু স্কুল বাসে তুলে দিতে, নামিয়ে আনতে যেতেন। এখন যাচ্ছেন আরেক জন। রূপের তাতে কিছু এসে যায় না। স্কুল থেকে ফিরে জলখাবার খেতে-খেতে সে মহাউৎসাহে বন্ধু আর টিচারদের গল্প করে। ক্লাসে কিরকম ডিগডিগে রোগা আর হোঁৎকা মোটা দুটো ছেলে আছে। অরিন্দম রোজ-রোজ জোক বলে। সঞ্জয় দত্ত খুব খারাপ ছেলে, রোজ পয়সা চায়। রাজা হাজরা আর অর্ণব শেঠ কিরকম ফাইট করে। তার পরই সে মাঠে যাবার জন্যে হামলাতে থাকে। মাঠ থেকে ফিরে ছেলে ঢুলতে থাকবে। অল্প একটু পড়ান সোমনাথবাবু। স্কুলটা ভালো। হোম-টাস্ক দেয় না। বেশির ভাগ পড়াই স্কুলে হয়ে যায়। পড়তে-পড়তে গল্প শুনতে-শুনতে ঢুল এসে যায়। দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে রূপ।
একটা পুরো সংসারের কর্তৃত্ব। অভ্যাস ছিল না কোনদিনই। প্রথম প্রথম বাধো-বাধো ঠেকত। তারপর নেশা ধরে গেল। শ্যামবাজারের বাড়িতে আজ্ঞাপালন ছাড়া আর কোনও সাংসারিক কর্তব্য পালনের বালাই ছিল না। কোনও-কোনও দিন শখের পোশাকি রান্না শাশুড়িরা রাঁধতে বলতেন। শ্বশুরদের খাওয়ার সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসে থাকতে হত। কিন্তু, নিজের ইচ্ছেমতো, বুদ্ধিমতো চলবার সুযোগ তার কোনদিনই হয়নি। এখন বন্দনা রান্নার বই কেনে কাকাকে ফরমাশ করে। নানারকম পদ রাঁধতে-রাঁধতে, কাকা আর ছেলের উৎসাহে আর উচ্ছ্বাসে সে রীতিমত দক্ষ রাঁধুনি হয়ে উঠেছে। দুপুরবেলা বাসনওয়ালী যাচ্ছে, তাকে ডেকে ছেঁড়া জামাকাপড় দিয়ে একটা সসপ্যান, কি একটা কেটলি কেনা হল তো সে মহা জয়ের আনন্দ। অবসর সময়ে বসে-বসে মায়ের পুরনো সেলাই-কলটা টেনে নিয়ে সেলাইও সে মন্দ করে না। বালিশের ঢাকা, পেটিকোট, পায়জামা, পর্দা, সুটকেসের ঢাকা—কি নয়? টেবলক্লথ তৈরি করে কোনকালে স্কুলে শেখা কার্পেটের স্টিচ দিয়ে। কত কতদিন সে রাস্তায় বেরোয়নি। এখনও বেরোবার দরকার হয় না। বাজার হাট সব কাকাই করেন। কিন্তু মাসে একদিন অন্তত কাকা তাদের নিয়ে বেরোবেনই। যেখানে হোক। কলকাতায় এবং তার আশপাশে যে এতো যাবার জায়গা আছে, দেখবার জিনিস আছে তা-ই তো বন্দনার জানা ছিল না। কলকাতার লোকেরা কলকাতা দেখে সবচেয়ে কম। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরে অতবড় মিউজিয়ামটা সে কোনদিন দেখেনি। সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রালের ভেতরে কোনদিন ঢোকেনি। গান্ধীঘাট বা ব্যান্ডেল চার্চ জায়গাগুলো কী সুন্দর। দমদম এয়ারপোর্টে গিয়ে শুধু প্লেন ওঠা-নামা দেখতে-দেখতেই রূপের মতন তারও মনে ছেলেমানুষি উৎসাহ আসে। ইন্টারন্যাশন্যাল লাইনের প্লেন নামবে তো? রূপের সঙ্গে-সঙ্গে বন্দনাও জিজ্ঞেস করতে থাকে। সেই বিশাল প্লেন ডানা মুড়ে খুব কাছে দাঁড়ায়। অ্যালিট্যালিয়া লুফথানজা রূপ পড়ে। সিঁড়ি লাগে গিয়ে। যাত্রীরা সব আত্মীয়স্বজনদের টাটা করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়। সুন্দরী এয়ার হোস্টেস, সুদর্শন ইউনিফর্ম পরা ক্রুরা সব চলে যায়। প্লেনের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, সিঁড়ি ফিরে আসে। তারপর বিরাট দেহ নিয়ে বাঁক ফিরে একসময় উড়ে চলে যায় প্লেন। বন্দনার বুকের ভেতর হু-হু করে। বুক যেন ফেটে যাচ্ছে শতখান হয়ে। চোখ ফাটে না। মুখে ভাষা ফোটে না। শুকনো আমসির মতো মুখ দেখে, কাকা বলেন—‘বড্ড গরম, চ’ আজ ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরা যাক।’ রূপ উৎসাহিত হয়ে বলে—‘আবার কবে আসব কাকা!’ বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে কাকা বলেন—‘চল্ তো এখন শিগ্গির শিগ্গির।’ রাক্ষসীর প্রাণ যেমন কৌটোর ভোমরাতে, কাকার প্রাণ যেন তেমন বন্দনার সুখ-দুঃখের সঙ্গে প্রাণের অধিক টানে বাঁধা হয়ে গেছে। এতটুকু চোখ ছলছল, মুখের ছায়া তাঁকে বুঝি যম-যন্ত্রণা দেয়। ট্যাক্সিতে বসে চোখ বুজোয় বন্দনা। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও বৃষ্টি বাধা মানে না। ঝরে পড়ে শাড়িতে, কোলের ওপর, পাশে বসা ছেলের গায়ের ওপর। রূপ বলে—‘কাকা, আমার বাবা কি অমনি প্লেনে করেই চলে গেছে? আর কোনদিন আসবে না? যারা চলে গেল ওরা আসবে না? আসে না কেন? বলো না, বলো না, কাকা!’
আজ কতদিন পরে রূপের মুখে বাবার নাম। বন্দনা বাইরে মুখ ফেরায়। রূপ তখন কাকার হাতে ছোট্ট ছোট্ট হাতে, ছোট্ট ছোট্ট কিল মারছে—‘ওদের আমি মারব, মারব, মারব।’
কাকা বলেন,—‘ওদের মারিস। আমাকে মারছিস কেন রে পাগলা?’ তিনি হাসবার চেষ্টা করেন, এই প্রথম কিছুতেই হাসি ফোটে না।
অধ্যায় ১৩
চেহারাটি শান্ত, গভীর অথচ মধুর। যেন অনেক অভিজ্ঞতা পরিপাক করে তবে এই মাধুর্যে পৌঁছতে পেরেছে। পরিপাটি বেশবাস, বেশকে ছাড়িয়ে মানুষটিকেই চোখে পড়ে আগে। কথাবার্তা মৃদু, দৃঢ়, মার্জিত, অথচ সপ্রতিভ। স্কুল-বোর্ডের প্রত্যেকের পছন্দ হয়ে গেল। সরকারি অনুদান এঁরা নেন না। ট্রাস্টের টাকাতেই স্কুল চলে। বহু ধনী লোকের দান রয়েছে। সব সরকারি নিয়মকানুন মেনে চলবার দরকার হয় না তাই। এঁরা মনে করেন শিক্ষয়িত্রীদের সবচেয়ে বড় গুণপনা তাঁদের চরিত্র, এবং সেই চরিত্রকে বাইরে রূপ দেবার উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব। চরিত্র বলতে অবশ্য এঁরা মোটের ওপর আভিজাত্য, ভদ্রতা, নৈতিক পবিত্রতা এই সবই বোঝেন। পোশাকে, কথাবার্তায়, হাব-ভাবে এই জাতীয় চরিত্র প্রকাশ পেলেই এঁরা খুশি। চরিত্র বলতে যদি খুব বেশি আত্মস্বাতন্ত্র্য, নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকবার ক্ষমতা, এই সব বোঝায় তাহলে এঁরা হয়ত একটু অসোয়াস্তি বোধ করবেন। আপাতত প্রার্থিনীর চেহারাটি পলকা, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে স্বভাবটি হালকা নয়। সুতরাং বন্দনার চাকরি প্রায় এককথায় হয়ে গেল।
মিসেস খাসনবিশ সেক্রেটারি। বললেন—‘শী নীড্স ইট ভেরি মাচ, বাট ডাজন্ট মেক এ শো অফ দ্যাট।’ অতুল মুখার্জি চেয়ারম্যান, বললেন—‘একজ্যাক্টলি। এটা আমার মতে ভদ্রমহিলার সবচেয়ে বড় কোয়ালিফিকেশন। আর তাছাড়াও, মেয়েদের প্রোভাইড করবার জন্যেই তো একদিন এ স্কুলের পত্তন হয়েছিল। এই ধরনের মেয়েদের। এডুকেশন দিয়ে ছেড়ে দিলেই তো হবে না, প্রয়োজনে তার অ্যাপ্লিকেশনের ভদ্র ক্ষেত্রও তো দিতে হবে।’
—‘বছরখানেক যাক, বি. এডটা আমরাই করিয়ে নেবো’, আরেকজন সদস্য বললেন।
সংসারের অর্ধেক কাজ করে দ্যান সোমনাথবাবু। তাঁর অবসর রয়েছে, স্বাস্থ্য ভালো, উৎসাহ প্রচুর। বন্দনা আর রূপকে পেয়ে তিনি যেন নতুন জীবন পেয়েছেন। এমন উদ্যমের সঙ্গে নাতির জুতো পালিশ করেন, কেড্সে রঙ লাগান, যে কোনদিন তিনি এগার হাজার থেকে ষোল হাজার ফিটের মধ্যে ট্রেকিং করে বেড়াতেন, কিংবা চার হাজার ফিটের তলায় নামলে অস্বস্তি বোধ করতেন এ কথা কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না। ভীষণ সংসারী এক দাদু-মানুষ। বন্দনার হাতের কাজ অভ্যেস হয়ে যেতে বছরখানেকের বেশি লাগল না। এখন কাজগুলো যান্ত্রিকভাবে হয়ে যায়, সুতরাং মন তার নিজের কাজ আরম্ভ করে দেয়, কি করি, কি করি করে অস্থির তো করে দেয়ই তারপর সোমনাথবাবু দেখেন, স্টোভে ভাত চাপিয়ে বন্দনা গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আনাজ কুটতে- কুটতে আগে কাকাকে যে কারণে বকত এখন নিজেই তাই করছে। অর্থাৎ কুটছে তো কুটছেই।
সোমনাথ বললেন—‘বুড়ি, তুই এম এ-তে ভর্তি হয়ে যা।’
বন্দনা বলল—‘তার চেয়ে আমি একটা চাকরি করি না, কাকা। টাকাকড়িও কিছুটা সুবিধে হয়।’
—‘তোর যা ইচ্ছে, যেমন ইচ্ছে, যাতে তুই ভালো থাকিস তাই কর।’
বাড়ি থেকে স্কুল সামান্য দূরত্ব। হেঁটেই চলে আসতে পারে বন্দনা। পথটুকু যেন মুক্তির আপন পথ। সুখী হবার জন্য পথে বার হওয়া যে তার এতো জরুরি ছিল, সে আগে কখনও বোঝেনি। ঘরের মধ্যে যেন অনেকগুলো আয়না ফিট করা থাকে। প্রত্যেকটি দেয়াল থেকে একটি করে আত্মমুখ চেয়ে থাকে, যেদিকে তাকাও খালি আমি, আমি, আমি। সেই আমির ভাবনা, আমির দুঃখ, আমির দুশ্চিন্তা, মন-খারাপ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দিবাস্বপ্ন দিয়ে ক্রমে ক্রমে বাড়িটার কোণগুলো পর্যন্ত ভর্তি হয়ে যায়। দমবন্ধ হয়ে আসে। কাঁধে নতুন চামড়ার ব্যাগ, পরনে ফিকে সবুজ চিকনের কাজ করা শাড়ি, বন্দনা চলেছে, দুধার দিয়ে বয়ে চলেছে জনস্রোত। বহমান বলে প্রতি মুহূর্তে যেন নতুন হয়ে উঠছে। ব্যস্ত সমস্ত, কর্মস্থলে চলেছে, স্টপে স্টপে অফিসযাত্রী মানুষের উত্তেজিত অপেক্ষা। তারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিতে প্লাস্টিকের ঝুড়ি হাতে দুলিয়ে বাজার করতে চলেছে কোনও সুখী গৃহিণী। বাচ্চা ছেলে বা মেয়ের হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছে কোনও মা। বাচ্চাকে স্কুলে পৌঁছে টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরবে। গাঁজা পার্কে এই কর্মব্যস্ত সকালেও বেশ কিছু লোক এসে গেছে। এরা কি বেকার? না অবসরপ্রাপ্ত? কি সূত্রে এদের এখন এ-পার্কে আসা, এ হেন অসময়ে, তা বোঝা সম্ভব নয়। কোন কোনদিন রিকশায় উঠে পড়ে বন্দনা। এমনিতে তার বেরোনোর সময়ের হেরফের হয় না। কিন্তু এক-এক দিন রূপ স্কুলে চলে যাবার পর কাকা বাড়ি ফিরে খুব গাঁই-গুঁই করতে থাকেন।
—‘তুই চাকরিটা নিলি, আর এখন দ্যাখ আমাকে একা-একা খেতে হবে।’
বন্দনা অপরাধী-অপরাধী মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখলে, কাকা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বলেন, ‘যাঃ, তোর দেরি করিয়ে দিলুম। শিগ্গিরি বেরিয়ে পড়। আমার একা খেতে কোনই অসুবিধে হবে না।’
সামান্য মনখারাপ নিয়ে একটু দেরি করে বাড়ি থেকে বেরোয় বন্দনা। হাঁটতে ভালো লাগে না, ফুটপাতে খুব ভিড় মনে হয়। যদিও সসম্ভ্রমে জায়গা ছেড়ে দিতে থাকে যুবকরা। মানুষ। মানুষ দেখতে-দেখতে আস্তে-আস্তে তার চিত্ত ভরে যায়। হাসি-খুশি, রাগী-রাগী, বিরক্ত, তৃপ্ত দেখতে, অসুখী খিটখিটে দেখতে, ব্যস্ত, ঢিলেঢালা, কত রকমের মানুষ। মানুষের মুখশ্রী এ ক’দিনেই ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেলেছে বন্দনা। তার বুকের মধ্যে কে যেন সদাসর্বদা গুনগুন করতে থাকে—আমি তোমাদের সবার একজন। তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই মতো কাজ করব, ঘুরব, ফিরব, দোহাই তোমাদের আমাকে আলাদা করে রেখ না। ঘর সে যত পবিত্র, যত পরিচ্ছন্ন, যত সজ্জিতই হোক না কেন, তার চেয়ে এই ছায়াচ্ছন্ন বীথিকাপথ, কিংবা ঢং-ঢং ঘণ্টিবাজাননা ট্রামলাইন পাতা, তীব্রগতিতে ভারি দোতলা বাস চলা, বহু মানুষের অবিরাম চলাফেরায় অক্লান্ত রাজপথ অনেক, অনেক গুণে ভালো। অথচ অফ পিরিয়ডে সহকর্মিণীদের সঙ্গে গল্প করতে-করতে একেক সময়ে বন্দনার কাকার জন্যে ভীষণ মন কেমন করে ওঠে। সে সমস্ত রান্না সেরে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে, টেবিলের ওপর কাকার খাবার বাটিতে-বাটিতে বেড়ে থালা চাপা দিয়ে রেখে আসে। কাকা রূপকে স্কুলবাসে তুলে দিয়ে গড়িমসি করে ব্যায়াম করেন, তেল মাখেন, চান করেন, গীতা পড়েন, যে অধ্যায় বন্দনাকে পড়াবেন মনে করেন সেটা দাগ দিয়ে দিয়ে ভালো করে পড়ে রাখেন। তারপর ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে সব নামিয়ে দেন। স্টোভে একটু গরম করে নেওয়া কিছুই না, বন্দনা যখন বাড়ি থাকত তখন সোমনাথবাবু আগ বাড়িয়েই কাজটা করতেন, বলতেন—‘সারা সকাল রেঁধেছিস আর উনুনের ধারে যাসনি।’ কিন্তু এখন যেহেতু তাঁকে একা খেতে হয়, সেহেতু গরম করার হাঙ্গামায় তিনি আর যেতে চান না। বন্দনা বকাবকি করলে হাসেন, বলেন—‘যে মানুষের ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে, একটু গরম-ঠাণ্ডায় তার কি এসে যায় বল তো?’
বাসনমাজার লোক এলে দরজা খুলে দেওয়া, রূপ ফিরলে তাকে মোড়ের মাথা থেকে নিয়ে আসা, খেতে দেওয়া, সমস্ত সামলান কাকা। বন্দনা যখন ফেরে, তখন পরিষ্কার তকতকে বাড়িতে শেষ বেলার আলো, ছেলের ঘুমন্ত মুখে সেই আলো ছড়িয়ে থাকে। পাশে আর্মচেয়ারের হাতল থেকে পা দুটো নামিয়ে নিয়ে কাকা বলেন—‘তুই এখানে একটু শো বুড়ি। আমি চা-টা করি।’
বন্দনা বলে—‘আচ্ছা, তুমি কি বলো তো? সারা দুপুর তো একবার ওপর একবার নিচ করেছো। একটু ঘুমিয়ে ছিলে তো?’
—‘ঘুমোবো কি রে? পাগল হলি নাকি? জীবনের আর ক ঘণ্টা মোটে বাকি বল দিকিনি? ঘুমিয়ে সে সময় কেউ নষ্ট করে? শোন, লুচির ময়দা মেখে রেখেছি, আলু কুটে জলে ভিজিয়ে রেখেছি, চল তোকে গরম-গরম ভেজে দিই।’
—‘আচ্ছা কাকা, তোমাকে আমি সত্যি ভীষণ বকবো। কে তোমাকে বলেছে লুচির ময়দা মাখতে। তুমি খাবে?’
—‘আরে আমি তো খেয়েছি তখন প্রায় দুটো। এখন কি আর খেতে পারি? চা ছাড়া কিচ্ছু না।’
—‘তাহলে রূপু খাবে?’
—‘উঁহুঃ, ওকে কিচ্ছু দিসনি। পেট পুরে ভাত খেয়েছে, মাংসটা গরম করে দিলুম। ব্যাটা গপাগপ এক থালা খেয়ে নিল। এখন পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আর কিচ্ছু দোব না।’
—‘তাহলে কার জন্যে লুচিটা হবে?’
—‘কেন বুড়ি, তুই কি মানুষ না? তুই কি সকাল নটায় সামান্য দুটো খেয়ে সারা দুপুর গলাবাজি করে, এই চারটের সময় এক মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফিরলি না? তোদের খেতে নেই, খিদে পেতে নেই, না? তোদের জন্যে আলাদা করে কিছু করে দেওয়াটা এতই হাস্যকর? আচ্ছা তৈরি হয়েছিস। গরুর জাত নাকি? সকালে যা খেয়েছিলি, চাট্টি গলার কাছে রেখে দিয়েছিস? জাবর কাটবি। এখন?’
কাকার রাগ দেখে বন্দনা অবাক। বলে—‘কি আশ্চর্য, তুমি এতো রাগ করছ কেন? খাবার তো কত রকম জিনিসই আছে। খাব না কেন? লুচিটা হাঙ্গামা নয়?’
—‘খাবার অনেক জিনিস আছে? তোর ভাঁড়ারের খবর আমি রাখি না। কি আছে শুনি? পাঁউরুটি? পাঁউরুটি চিবোতে ভালোবাসিস তুই? সত্যি করে বল।’
—‘ন্না।’
—‘মুড়ি? মুড়ি চিবোতে ভালো লাগবে সারাদিনের পর?’
—‘খেলেও হয়। অসুবিধে কি! চায়ের সঙ্গে একবাটি মুড়ি নিয়ে নিতুম।’
—‘মুড়ি মাখবার কি রেখেছিস? চানাচুর? বাদাম ভাজা? নারকোল?’
—‘উহুঃ।’
—‘তাহলে কি ভাবে খাবি? শুকনো মুড়ি একগাল আর এক চুমুক করে চা!’
—‘ঠিক ধরেছে। আমার খুব ভালো লাগে।’
—‘ভালো লাগাচ্ছি তোকে। আমি এখনও বেঁচে আছি; বুঝলি? তোকে তো আর করতে হচ্ছে না। আমি সারাদিন শুয়ে বসে আছি; আমি তোকে ভেজে খাওয়াব। লুচিগুলো সব হয়ত গোল হবে না। কোনটা কোনটা আফ্রিকার ম্যাপের মতো, অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপের মতো হয়ে যাবে।’ বলতে বলতে কাকা হেসে ফেলেন।
অগত্যা বন্দনা রান্নাঘরে গিয়ে লুচি বেলে দেবে। কাকার কি গোঁ; সেই লুচি ভেজে, আলু ছেঁচকি করে তাকে খাইয়ে তবে ছাড়বেন।
সত্যি কথা, চাকরিটা নিয়ে বন্দনা বেঁচে গেছে। মেয়েদের পড়ানোটা বন্দনার কাছে যত না পড়ানো, তার চেয়ে বেশি পড়া। ওদের ছেলেমানুষি কথাবার্তা, আগ্রহ, কৌতুক, সব মিলিয়ে তরুণ জীবন্ত মনগুলোকে সারা ক্লাস পড়ানোর নাম করে ও শুধু উপভোগ করে। সেভন থেকে এইট, এইট-এ থেকে এইট-বি। তার এই খুশিটা স্টাফরুমের সবার কাছে বেশ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তৃপ্তিদি একদিন বললেন—‘আরে ওই দুষ্টুর শিরোমণি এইট-বির ক্লাস করে তোর এতো খুশি কিসের? অ্যাঁ?’ চিন্তাদি বললেন—‘প্রথম প্রথম তো। দু দিন যেতে দাও না, তারপরই ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশবে।’ কিন্তু বন্দনা জানে সে ক্লান্ত হবে না। আসলে আর্থিক স্বাধীনতার ব্যাপার নয়। কাকার কাছে আসবার পর থেকে টাকাকড়ির ব্যাপারে তার আর নিজেকে পরনির্ভরশীল মনে হয় না। কিন্তু মানসিক নির্ভরতা? সেটা থেকেই গেছে। এখন তার একটা নিজস্ব জীবন হয়েছে যেটা কাকা-নির্ভর নয়, রূপ-নির্ভরও নয়। এতে যে তার চারপাশের গণ্ডিটা কিভাবে দূরে হটতে-হটতে মিলিয়ে গেছে এবং মিলিয়ে গিয়ে কি পরিমাণে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তা একমাত্র সে-ই জানে। কিন্তু কাকা? কাকার জীবনের গণ্ডিটাকে সে কেটে ছেঁটে ছোট করে দিল না তো? তাদের জন্যই তিনি ভ্রমণের নেশা ছাড়লেন। অমন পর্যটক মানুষটা হাতা-খুন্তি বেড়ি-ঝাঁটা- বালতি ধরলেন, তাঁর কর্তব্যবোধে তিনি করছেন, কিন্তু তাঁকে সঙ্গ দিয়ে, তাঁর যত্ন করে, ক্ষতিপূরণ করে দেওয়াটা কি তার উচিত ছিল না? কাকাকে সে একটা আনন্দহীন খাটুনির জীবনের চক্রে বেঁধে দিল না তো!
যেদিন এরকম মনে হয় সেদিন বন্দনা ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ক্লাসে যেতে দেরি করে, কখন ছুটি হবে সে-জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। ফেরবার সময়ে তার প্রিয় জ্যাকারান্ডা কি করবী গাছের ফুলের থোকার দিকে তাকায় না। ধূলিমলিন যে রাস্তা হাঁটতে সে রোজ রোজ বেঁচে থাকার আনন্দস্বাদ পায় আজ তা পায় না, কোনক্রমে ব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে দরজার কড়াটা এমনভাবে নাড়ে যেন ভয় পাছে কেউ দরজা না খোলে। কাকা এসে দরজা খুলে দিয়ে এক মুখ হাসেন। সেই প্রিয় প্রৌঢ় মুখখানাকে দেখে তবে শান্তি। বন্দনার সে সময়ে ইচ্ছে করে ছোটবেলার মতো কাকাকে জড়িয়ে ধরে গালে খুব কষে হামি খায়। কিন্তু সে অভ্যেস চলে গেছে। এখন জিনিসটা পাগলামি বা ন্যাকামি বলে মনে হবে। বিশেষ করে তাদের দু-জনের স্বভাবই খুব সংযত, উচ্ছ্বাসহীন বলে। সে খুব করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—‘কাকা তুমি ভালো আছো তো? ভালো ছিলে?’ —বলতে বলতে চোখ ছলছল করতে থাকে।
সোমনাথবাবু বলেন—‘হঠাৎ—? ভালো থাকব না কেন? ও কি কাঁদছিস নাকি?’
—‘তোমার জন্যে আজ সারাদিন মন কেমন করছিল স্কুলে।’
—‘আচ্ছা পাগল মেয়ে তো। আমি কি তোদের ফেলে কোথাও গেছি?’
বন্দনা মনে মনে বলে—‘তুমি যাওনি কাকা, বরং ফিরে এসেছ, মুক্তজীবন থেকে স্বেচ্ছায় এসে জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়েছ, তুমি মহানুভব। আসলে আমিই চলে গেছি। তোমায় ফেলে চলে গেছি।’
সারা সন্ধে কাজকর্ম করতে-করতে ঘুরে-ঘুরে বন্দনা কাকার কাছে চলে আসে। বাচ্চা মেয়ের মতো। রূপ খেলার মাঠ থেকে ফিরে একটু মাকে চায়, রাত্রে কোনদিন মার কাছে, কোনদিন কাকার কাছে শোয়। বন্দনা ছেলের সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু মন পড়ে থাকে কাকার কোলের কাছটিতে। প্রাণপণে সে খালি বোঝবার চেষ্টা করে কাকার প্রাপ্তির ঝুলিতে কিছু কম হয়ে যাচ্ছে কি না।
অধ্যায় ১৪
আস্তে আস্তে গ্রীষ্ম। প্রচণ্ড আগুনের ফোয়ারা। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। পিচ গলছে। গাছগুলো শুষছে। তা-ও কিরকম একটা অসহ্য সূর্যের এই তাপ। এই তাপ যেন বেঁচে থাকার আসল অনুভূতি তীব্রভাবে এনে দিচ্ছে। জামা-কাপড় ভেদ করে, চামড়া ভেদ করে, পেশীর স্তর, তন্তু সব ভেদ করে যেন হাড়ের কাঠামো পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছচ্ছে এই তেজ। তবে সে সঞ্জীবিত সোনালি, সবুজ হবে। গমের দানার মতো আস্তে আস্তে পরিপুষ্ট, পরিপূর্ণ। স্টাফরুমে এখান থেকে ওখান থেকে রব ওঠে। গলদঘর্ম শান্তিদি বলেন—‘উঃ কি গরম রে বাবা আর পারছি না।’ ঊষাদি বলেন—‘ঘামে শরীরের রক্তগুলো সব এবার জল হয়ে যাবে।’ নমিতাদি জলে লেবু নিংড়ে পান করতে-করতে বলেন—‘লেবুর জল। অনেকবার বলেছি এর রেমিডি হল লেবুর জল। কথা তো শুনবে না। সল্টগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো তো আবার শরীরকে ফিরিয়ে দিতে হবে?’
বন্দনা বলে—‘মুখ চোখ একবার ভালো করে ধুয়ে আসুন না ঊষাদি!’
—‘ওরে বাবা, সাম্প্রতিককালে জলে হাত দিয়ে দেখেছ। ফুটছে! টগবগ করে ফুটছে। নীরুকে আজ আর চা করতে কেটলি হীটারে চাপাতে হবে না।’
ক্লাস এইটের ক্লাস-টীচার বন্দনা। মেয়েগুলো তাকে বড় ভালোবাসে। ওদের ভালোবাসা যেমন হয়, আবেগপ্রবণ, বীরপূজামিশ্রিত। ঊর্মি বলে একটি মেয়ে প্রায়ই ফুল নিয়ে আসে, আজ মেয়েটি ওকে একগুচ্ছ সোনার বরণ চাঁপা উপহার দিল। বন্দনা আদর করে ওর গাল টিপে দিল, মেয়েটিকে ক্লাসের অন্যান্য মেয়েদের চেয়েও ছেলেমানুষ মনে হয়। বলল—‘কোথা থেকে নিয়ে এসেছ ফুল?’
—‘আমাদের বাগানে ফোটে দিদি!’ খুশিতে রাঙা হয়ে ঊর্মি জবাব দিল।
—বেশ, খুব ভালো। কিন্তু সেদিন যে পদ্ম এনেছিলে! সে-ও কি তোমাদের বাগানে ফোটে!’
—‘না দিদি’—ঊর্মিমালার মুখ লাল হয়ে গেছে, ‘ঠাকুমা পুজোর জন্য আনিয়েছিলেন দিদি। আমি বলতে…আমি চাইতে…আমি যখন বললুম আপনাকে…’
—‘আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। কিনে-টিনে আনতে যেও না যেন।’
ছাড়া পেয়ে মেয়েটি ছুটতে-ছুটতে চলে গেল। খুব লজ্জা পেয়েছে। চাঁপার স্তবকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বন্দনা মুগ্ধ চিত্তে ভাবল—সত্যিই চম্পা সূর্যের সৌরভ। সূর্যের স্বরূপ-সম্পদ। সূর্য পিতৃসম। প্রাচীন মিশরীয়দের মতো সূর্যের জন্য ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা টলটল করতে থাকে তার মনে। তুমি ছিলে বলেই তো এই ভূগোলক, এই বায়ুস্তর, এই অম্লজান, উদযান, এই শ্যামশষ্প ভরা ধরিত্রী যার তুলনা নক্ষত্রলোকের কোথাও নেই এবং এই জীবন, যা দ্বিতীয়বার আর মানুষ পাবে কি না সে জানে না। একবার, মাত্র একবারই হয়ত এই দুর্লভ উপভোগে ভরা জীবন।
বিকেলে বাড়ি ফেরবার সময়ে ঝড়ের মতো বাতাস বয়। এ তো বাণিজ্যবায়ু নয়। তবু, মনের মধ্যে গুনগুন করতে থাকে ‘মাইটি ট্রেড উইন্ডস্ ব্লোয়িং, মাইটি ট্রেড উইন্ডস’ …‘গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল।’ গাছগুলো পাতা সমেত পাগলের মতো দুলতে থাকে। ঝুরঝুর করে পথের ওপর ঝরে পড়ে ফুলের পাপড়ি, পরাগ। বেণী ওড়ে। আঁচল লুটোপুটি। সমস্ত শরীরটা বেলুনের মতো, না পাখির মতো উড়ে যেতে চায় যেখানে ছোট-ছোট সাবানের ফেনার মতো মেঘ উড়ে চলেছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে বন্দনা দেখে কবি ঠিকই বলেছিলেন জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা। তারও হৃদয় বুঝি পৃথিবীর বোঁটা ছিঁড়ে উড়ে যাচ্ছে। নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো। স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে শাদা বকের মতো উড়ছে, উড়ে যাচ্ছে।
অধ্যায় ১৫
স্কুল থেকে ফিরে খেলতে যাবার জন্যে ছটফটানি শুরু হয়েছে রূপের। আজকাল খাওয়া শেষ করে আর শোয় না, যদি ঘুমিয়ে পড়ে। বিকেল বয়ে যায়। সারাদিন রপটাচ্ছে। পরিশ্রম হচ্ছে খুব। কিন্তু সোমনাথ বলেন, ‘ও হল বালক, নতুন বড় হচ্ছে, প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তে ওর শক্তি বাড়ছে, ওর শক্তিসামর্থ্যের পরিমাপ আমার মতো বুড়োরা করতে পারবে না। ওর শরীর যখন পারছে, তখন ও বিশ্রাম না নিয়েই খেলতে যাক, খেলুক। না পারলে তখন দেখা যাবে।’ ইতিমধ্যে ওকে দুবেলা দুধ খাওয়ানো হচ্ছে, প্রতিদিন একটি করে মুরগীর ডিম, সপ্তাহে তিন দিন মাংস এবং যথেষ্ট ফল খাওয়ানো হচ্ছে। তার মা চাকরি নেওয়ার পর খাওয়ার মান আরও উন্নত হয়েছে। জামা প্যান্ট পাল্টে, পায়ে ধবধবে কেডস হাতে ব্যাট নিয়ে, দাদুর হাতে উইকেটগুলো ধরিয়ে দিয়ে রূপ খুব বড় সড় মানুষের মতো পায়চারি করছে। মা বাড়ি না ফিরলে সে খেলতে যেতে পারছে না। ভারি উৎকণ্ঠিত। দালানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ব্যাটটাকে শূন্যে হাঁকড়াচ্ছে রূপ—‘দেখলে কাকা, হাতটা কি রকম সট করে উঠে গেল। আমি হবো স্ট্রোক প্লেয়ার। ঠুকে ঠুকে কিষেণের মতো খেলা আমার পোসাবে না। কি বলো?’
সোমনাথ বললেন—‘ঠিক। একেবারে ঠিক।’
—‘আচ্ছা কাকা স্ট্রোক-প্লেয়ার কি বোলার হতে পারে না?’
—‘কেন পারবে না রে?’
—‘তাই ভাবছিলুম কাকা। আমার ডান হাতটা কিরকম ঘোরে না, বল করবার সময় বাঁ-হাতি বোলার। সেদিন সঞ্জুর ক্যাচখানা ধরলুম, দেখেছিলে? মাটিতে ডিগবাজি খেয়ে, একেবারে বাঁ-হাতের আঙুল দিয়ে…’ উৎসাহের চোটে ডিগবাজিটা শানের মেঝের ওপর খেয়েই দেখিয়ে দিল রূপ। তারপর ধুলো ঝেড়ে বলল—‘হাতে স্পিন কি? রাইটহ্যান্ড ব্যাটসম্যান, ন্যাটা স্পিনার, খারাপ, কাকা?’
—‘দারুণ ভালো রে, জব্বর!’
চারদিক চেয়ে ভারিক্কি চালে আবার বলে রূপ—‘মা এখনও কেন এল না বলো তো। বড্ড ভয় হয় কাকা। চারদিকে যা অ্যাকসিডেন্ট! মায়ের আবার কিছু হলো টলো না তো?’
সোমনাথ হাসতে-হাসতে তার পিঠ চাপড়ে বলেন—‘দূর পাগলা উদীয়মান ক্রিকেটারদের মায়েদের কিস্যু হয় না।’
বন্দনার আজকে বাড়ি ফিরতে সত্যিই খুব দেরি হচ্ছে। ছুটির পর সে স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়িমুখো না হয়ে উল্টো দিকে চলে গিয়েছিল। ভিক্টোরিয়ার দিকে। চওড়া রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী গাড়িদের পাশাপাশি সে হেঁটে যাচ্ছিল রেসকোর্সের দিকে। অনেকটা হেঁটে তবে মন বশে এল। পিকনিকের আয়োজন হচ্ছে স্কুলে। ডায়মন্ড হারবারের দিকে যাওয়া হবে, নিজেদের স্কুল-বাস নিয়ে। কি কি রান্না হবে তার একটা তালিকা তৈরি হচ্ছিল। প্রতিমাদি বলে বলে যাচ্ছিলেন, নতুন আসা একটি মেয়ে নাম নন্দা, লিখে নিচ্ছিল। ‘চার কিলো মাংস, পাঁচ কিলো মাছ’…বলতে- বলতে প্রতিমাদি হঠাৎ থেমে বললেন—‘দুজনের মতো নিরামিষের ব্যবস্থা রাখতে হবে নন্দা, ফ্রায়েড রাইসটা নিরামিষ রাখো, কাজু কিসমিস কড়াইশুঁটি দিয়ে হোক মিষ্টি-মিষ্টি, কড়াইশুঁটির কচুরি, আলুর দম, ভেজিটেবল চপ, চাটনিটা কমন।’ বন্দনা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারল না সে সবই খায়, তার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করবার দরকার নেই। কথাটা না বলতে পেরে ভেতরে-ভেতরে কী গভীর লজ্জা! এঁরাও তো জিজ্ঞেস করতে পারতেন। ধরেই নিলেন কেন যে তার খাওয়া নিরামিষ হবে? তাহলে বললে প্রতিক্রিয়া কি হত। ঘৃণা? বিস্ময়? বিদ্রূপ? টিটকিরি? নিজের কাছে লজ্জিত হলেও এদের কাছে যেন তার মানটা বেঁচে গেল। কিন্তু অস্বস্তিতে স্টাফরুমে বসতে পারল না সে। উঠে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ কানে এল নন্দার গলা, আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করছে—‘কেন প্রতিমাদি, বন্দনাদি নিরামিষ খাবেন কেন? উনিও কি প্রিন্সিপ্যালের মতো সৎসঙ্গী?’
নীলিমাদি অনুচ্চস্বরে বললেন—‘জানো না বুঝি? ও তো উইডো। সাজ-পোশাক দেখলে বোঝা যায় না অবশ্য। অনেকেই এ ভুল করে।’
মা বাড়ি ফিরতে রূপ মুরুব্বির মতো বলল—‘তোমার জন্যে আমরা আটকে ছিলুম। রোজ রোজ কিন্তু এতো দেরি করো না। অন্ধকার হয়ে গেলে কি আর বলের সুতো দেখতে পাব?’ ব্যাট কাঁধে বীরপুরুষ বেরিয়ে গেল। বন্দনা দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওপরে উঠল। কোত্থেকে যে আজ এত ক্লান্তি এল! টেবিলের ওপর কাকা ফ্লাসকে চা রেখে দিয়েছেন, পাশে কিছু ঢাকা প্লেট, কিছু খাবার-দাবার আছে। বন্দনা ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে ঢেলে অনেকক্ষণ ধরে খেল। আর কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না। প্লেটের ঢাকা খুলে দেখল—কবিরাজি কাটলেট, স্যালাড। মাঝে মাঝে শখ করে দোকান থেকে আনান কাকা। খেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু পড়ে থাকলে কাকাকে অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে। সে কাটলেটটাকে টুকরো-টুকরো করে জানলা দিয়ে নিচে ফেলে দিল, কয়েকটা কুকুর ছুটে এসে টুকরোগুলো নিয়ে মহা কাড়াকাড়ি চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে দেখে আস্তে-আস্তে জানলা থেকে সরে এল। যাক নিশ্চিন্ত।
অনেক রাতে কোথা থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজে উঠে বসলেন সোমনাথ। তাঁর ঘুম খুব সজাগ। পাশের বাড়ির কার্নিশে পায়রারা রাতে পা বদলায়, তার খসখস আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমটা উঠলেন না। কোথা থেকে আসছে কান্নাটা? সরু একটা বারান্দা আছে রাস্তার দিকে, পরপর তিনটে ঘর তার কোলে। মনে হচ্ছে, বন্দনার ঘরের সংলগ্ন সেই বারান্দার অংশ থেকেই আসছে আওয়াজটা। আজ রূপ মায়ের কাছে শুয়েছে। পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় তাই বারান্দায় উঠে গিয়ে কাঁদছে বন্দনা।
শ্বশুরবাড়িতে যেভাবে ছিল তাতে তিল তিল করে মরে যাচ্ছিল মেয়ে। সেখান থেকে তাকে নিজের কাছে নিয়ে এসে একটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে রেখে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য তিনি খুব সম্ভব ফেরাতে পেরেছেন। কয়েক বছর আগেকার বন্দনার সঙ্গে আজকের বন্দনার আকৃতিতে কোনও মিল নেই। এখন তার বয়স যেন কমে গেছে, দেখলে মনে হয় নবীনা কুমারী মেয়ে। বিবাহিত জীবনেও সে এতো সুন্দর ছিল না বোধহয়। সোমনাথ নিজে থেকে চিরকৌমার্য বেছে নিয়েছেন। কৌমার্যের মধ্যে তিনি একটা অতিরিক্ত সৌন্দর্য দেখতে পান। বিবাহিত রমণীর রূপ যেন সকালের আকাশের মতো, খোলামেলা। তার মধ্যে কোনও রহস্য থাকে না। বন্দনা এখন নিজের মতো একটা জীবন পেয়েছে। নিজের সঙ্গে অনবরত বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সে নিজেকে চিনতে পারছে। স্বনির্ভরতা এবং দায়হীনতা এ দুটো জিনিসের স্বাদ আলাদা। বন্দনা নিজস্ব জীবনবৃত্ত পেয়ে স্ব-নির্ভর এবং একই সঙ্গে তার কাকা মাথার ওপরে থাকায় অনেকটা দায়হীন। এখন সে সুস্থ, স্বাভাবিকও। কিন্তু এ আশা সোমনাথের নেই যে মেয়ে অভিমন্যুর অভাবের দুঃখ, তার অকালমৃত্যুর বেদনা কোনদিন ভুলতে পারবে। ভুলুক—তা তিনি চানও না। এ ব্যথাও যে জীবনের এক দুরূহ দান। যে পায় সেই জানে, এর মূল্য কত! জীবনের কত তুচ্ছতা, জীর্ণতা ঝরে ঝরে যায়, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। মানুষ ভেঙে ভেঙে আবার নতুন হয়ে গড়ে ওঠে গভীর রাতে মৃত প্রিয়জনের জন্য এই সন্তপ্ত কান্না এ বড় নিভৃত, গোপন কান্না, কে জানে কত ফাল্গুনী রাতের বকুলগন্ধ মেশা সুখস্মৃতি মথিত হচ্ছে ওই কান্নায়, সেসব রাতের পুনরাবৃত্তি এ জীবনে আর কখনও হবে না। তারও জন্য এ ব্যাকুল কান্না। গুরুজনদের দেখবারও নয়, শোনবারও নয়। বুক দিয়ে আগলে রাখতে পারেন মেয়েকে, কিন্তু এই স্মৃতির আগ্রাসী কবলের কাছে তিনি ব্যর্থ। সন্তর্পণে পাশ ফিরে শোন সোমনাথ। কাঁদুক। একটু কেঁদে নিক। মাঝে মাঝে এমনি হালকা হয়ে না নিলে গুরুভার বুকে বেঁধে মেয়ে পথ চলবে কি করে? কিন্তু গুমরে গুমরে কান্না চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। যেন বুক নিংড়ে যাচ্ছে বেদনায়, দুঃসহ কষ্টে। অনেকক্ষণ শুনে। শুনে আর থাকতে পারলেন না সোমনাথ। ধীরে ধীরে পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। অঘ্রান মাসের কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদ নেই। কিন্তু অসংখ্য তারার আলো। বাড়িগুলো সে আলোয় ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। বন্দনার ছায়ামূর্তিও যেন ভৌতিক। সান্ত্বনা জানাবার ভাষা নেই। শুধু আলতো করে মাথায় হাতটা রাখলেন সোমনাথ। কান্না স্বভাবতই বেড়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পর সোমনাথ আস্তে আস্তে বললেন, ‘কি হয়েছে বুড়ি? এমনি করে কাঁদছিস কেন? আমায় বলবি না?’ গুমরে গুমরে বন্দনা বলল—‘আমি তাকে ভুলে গেছি কাকা। তার জন্যে আমি আর শোক করি না। সেই দুঃসহ কষ্ট আমায় আজকাল ছেড়ে গেছে। আমি কি রকমের সতী সাধ্বী স্ত্রী বলো! খাচ্ছি-দাচ্ছি, দিব্যি সাজপোশাক করছি, বেঁচে আছি মহা আনন্দে। প্রতিদিন কিভাবে উপভোগ করছি জীবনটাকে তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু সে যে অকালে অত কষ্ট পেয়ে মর্মান্তিকভাবে চলে গেল, তাকে আমি মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দিয়েছি। তুমিই বলো কাকা আমি কি এক নিষ্ঠুর, নির্দয়, পাপিষ্ঠা নই? আমি কি নারী নামের যোগ্য? দেশের পুরাণে লোককথায় মৃত স্বামীর পেছন পেছন স্ত্রীর যমালয়ে গিয়ে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার তপস্যার কথা লেখা আছে, যে দেশের একটি মেয়ে একদিন লর্ড বেন্টিংকের সামনে নিজের আঙুল মোমবাতির শিখায় পুড়তে দিয়ে দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিল যে আগুনে পুড়ে মরা তার কাছে কিছুই নয়, আমিও তো সেই দেশেরই মেয়ে….’
সোমনাথবাবু এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন এইবার আর থাকতে পারলেন না, বললেন, ‘থাম বন্দনা, চুপ কর। তুই স্কুলে-কলেজে পড়া শিক্ষিত মেয়ে হয়ে এ দেশের সবচেয়ে কলঙ্কজনক লজ্জাকর কুসংস্কারের বীভৎস নজির তুলে কিসের সাফাই গাইতে চাইছিস? ছি, ছি। আমি তোকে কিছুই শেখাতে পারিনি। কিচ্ছু দিতে পারিনি। আর আমাকেই বা শেখাতে হবে কেন, তুই নিজেই বা নিজের শক্তিতে শিখবি না কেন?’
কাকাকে এত ক্ষুব্ধ বন্দনা কোনদিন দেখেনি। তিনি তার দিকে তাকিয়ে নেই। তাঁকে ভেদ করে পেছনে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন বন্দনা তাঁর সামনে থেকে মুছে গেছে।
কাকা বলছেন, ‘যে সাবিত্রী বেহুলার গল্পের তুই উল্লেখ করলি, সে তো মানুষের সবচেয়ে বড় আকাঙক্ষা অমৃতত্ব লাভের প্রতীক কাহিনী বলেই আমি জানি। বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ প্রেম দিয়ে অমৃতত্ব লাভ। এত পড়েছিস এটুকু বুঝিসনি? দেখতে পাই তুই রোজ অভিমন্যুর ছবিতে ফুল দিস, ঠাকুরের ছবির পাশাপাশি তার ছবি রেখে দিয়েছিস। ধূপধুনো দিয়ে পুজো করিস। তোর সেন্টিমেন্টে লাগবে বলে কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বাধা দেওয়া উচিত ছিল। এমনি করেই কুসংস্কারের চোরাবালিতে তোরা ডুবিস।’
বন্দনা ব্যথিত গলায় বলল, ‘ফুল দিতেও বারণ করছ?’
‘ফুল দিতে বারণ করিনি বুড়ি, আনুষ্ঠানিক পুজো করতে বারণ করছি। ভালোবাসা মনের ধর্ম। তাকে যে মুহূর্তে অনুষ্ঠানের মধ্যে ফেলবি, সেই মুহূর্ত থেকে সে মরতে আরম্ভ করবে। স্তূপীকৃত হয়ে থাকবে শুধু শুকনো ফুল বেলপাতার জঞ্জাল। মন্দিরে মন্দিরে একটু ঘুরলেই তো এ তথ্য বুঝতে বাকি থাকে না।’
‘আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখ শুদু এক মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অন্তর্গত কিছু গ্রহতারা দেখতে পাচ্ছিস। তাই-ই এতো যে হিসেব হয় না। তোর আমার দৃষ্টির বাইরে। ধারণাশক্তির বাইরে অবাধ অগাধ মহাশূন্য পড়ে আছে, অণুর পরে অণু জমে জমে সৃষ্টি হল জল, মাটি, প্রাণী। এই সব, এই এত আয়োজন কি বৃথা মনে করিস? বিজ্ঞানের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম।’
‘আমি তো মনে করি অভিমন্যু এক অর্থে পুণ্যাত্মা মানুষ ছিল। মাত্র আটত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা তার প্রয়োজন হয়েছিল এ যাত্রায়। তুই কি মনে করিস তোর পুজো নিতে এখনও সে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের মধ্যে গতিহীন প্রেত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! জানিস না মানুষের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ যে আলোকবর্তিকা জ্বলছে, অভিজ্ঞতার সারটুকু নিয়ে তাকে বিশুদ্ধ দীপ্তি হতে হবে বলেই তার বারবার পৃথিবীতে আসা? অভিমন্যুর যে অভিজ্ঞতাটুকুর প্রয়োজন তোকে দিয়ে ছিল, তা নিশ্চিত পূর্ণ হয়ে গেছে, দেহাতীত আত্মা কাউকে মনে রাখে না, সতীত্ব সাধ্বীত্ব ইত্যাদি বাঁধা বুলি কপচে তুই যে জিনিসের ছায়ামাত্র প্রকাশ করতে চাইছিস সেই ভালোবাসা মনে রাখার প্রয়োজনও আর তার নেই।
বন্দনা আর কাঁদছিল না, অবাক হয়ে কাকার উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়েছিল, বলল, ‘বাঃ, যে মুহূর্তে একটা মানুষ চলে গেল, অমনি তাকে ভুলে যাব? তাকে আর মনে রাখার দরকার নেই? পুরনো কাপড়ের মতো ধোবার বাক্সে ফেলে দিয়ে নতুন কাপড়ের পাট ভাঙব? এই তোমার তত্ত্ব কাকা? এ যে বড় হৃদয়হীন দর্শন, তোমার বিজ্ঞান, তোমার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মাথা দিয়ে বুঝলাম, কিন্তু হৃদয় কি তা মানে?’
—‘ভুলে যাওয়া উচিত তা তো বলিনি; প্রিয়জনের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক তার মধ্যে একটা চিটচিটে আসক্তির দিক আছে, সেটা ত্যাগ করার কথা বলছি। সেটা বাদ দিলে যে ভালোবাসা থাকে সেটুকুই তো হল সেই ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। নৈনং ছিন্দান্তি শস্ত্ৰানি নৈনং দহতি পাবকং, ন চৈনং ক্লেদয়ান্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ। সেই ভালোবাসা অনুভূতির মধ্যে সূক্ষ্ম লাইট ওয়েভের মতো মিশে থাকবে, তুই আরও উজ্জ্বল হবি, আরও পরিপূর্ণ। সমৃদ্ধ হবে তার ব্যক্তিত্ব, তোর আত্মা। কারণ তুই শুধু পেয়েছিলি না, পেয়েছিস। যা একবার পাওয়া যায় বুড়ি তা আর হারায় না কখনও, তোর সত্তার ভেতরে তা নিশ্চয় কাজ করে যাচ্ছে, তাকে কাজ করতে দে…’
মাঝরাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে সোমনাথবাবুর গলা গমগম করে উঠল। তিনি তখনও বলছেন—‘এ-ও বলি বুড়ি, শুধু স্বামীর ব্যাপারেই এই ভোলা-না-ভোলার ব্যাকুলতা মেয়েদের এতো বেশি কেন, ভেবে দেখেছিস? আদরের সন্তান গেলে মেয়েরা সে শোক কাটিয়ে উঠে আর একটি সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে দুঃখ বা লজ্জা বোধ করে না, তোর মা তোর দশ বছর বয়সে মারা গেছেন, তুই কখনও মায়ের কাছছাড়া হতিস না, তোর মারও তুই ছিলি প্রাণ, দশ বছর বয়সটার স্মৃতি বেশ ভালোই তৈরি হয়ে যায় বুড়ি, অথচ তোর মায়ের জন্যে মনে কতটুকু জায়গা রেখেছিস! মায়ের ছবিতে কোনদিন ফুল দিয়েছিস, মালা পরিয়েছিস? ধূপ জ্বেলেছিস? জ্বালাসনি বলে বিবেকের কাছে নিজেকে কখনও অপরাধী মনে করেছিস? তিনি গিয়েছিলেন নিতান্ত অল্পবয়সে, চৌত্রিশও বোধহয় পুরো হয়নি, সে-ও তো অকালমৃত্যুই! এই মায়ের কাছে তোর, কিংবা যে কোনও মানুষের ঋণ যত, আর কারও কাছে তো তার কণাও নয়! তবে? শুধু স্বামীকে ভোলা না ভোলা নিয়ে তোদের বিবেকের এতো জ্বালা কেন মা? কিছু না শুধু এইটুকুই। তোকে বোঝাতে চাই যাকে বিবেক বলে মনে করছিস সে শুধু একরকমের আত্মপ্রবঞ্চনা। সত্যকে যে মুহূর্তে চিনতে পারবি, হয়ত ধাক্কা খাবি কিন্তু আস্তে আস্তে মিথ্যে ভয়, মিথ্যে লজ্জা, মিথ্যে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবি। বিপত্নীকদের আরেকটা বিয়ে করার কোনও সামাজিক বাধা নেই, মৃত স্ত্রীর জন্য পালনীয় কোনও কঠোর আচারও নেই, তাই তাদের স্ত্রীর শোক ভুলতে দেরি হয় না। স্বামীহীনাদের বেলায় সব দিক থেকেই নিষেধের দেয়াল ওঠে তাই শোকও যেতে চায় না। না হলে কি হত বলা যায় না।’
বন্দনা কাঁপছে দেখে কাকা তার হাত শক্ত করে ধরে বললেন, ‘আমার কথায় যে সত্য আছে সে তুই পাশ্চাত্য দেশগুলোর দিকে তাকালেই বুঝতে পারবি। যেহেতু স্বামীর মৃত্যুতে স্বাধীনতা খর্ব হয় না, সেহেতু শতকরা নব্বুইজন সেখানে সুবিধে পেলেই পুনর্বিবাহ করে। দশ পার্সেন্টের ক্ষেত্রে মৃতের প্রতি আনুগত্যটা খাঁটি। তা-ও তাদের মধ্যে কতজন বিবাহক্ষম, সন্দেহ আছে।’
বন্দনা বলল, ‘তুমি আজ আমায় এমন কঠিন কঠিন কথা বলছ কেন কাকা, আমি জানি না। আমার ভেতরটা যে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তুমি কি বুঝতে পারছ না?’
—‘তুই যে বললি জীবনটাকে উপভোগ করছিস বলে হঠাৎ তোর ভীষণ বিবেকদংশন হচ্ছে। তাই এত কথা বললুম। সত্যি যদি জীবনটাকে ভালো লাগে তো ভালো লাগতে দে, তার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে স্মৃতি জাগিয়ে জোর করে আজকের ভালোলাগাটাকে বাধা দিস না। তাতে একবারও প্রমাণ হবে না, তুই অভিমন্যুকে ভালোবাসিস না। মা মিথ্যা মোহ, ভ্রান্তি, মায়ার আবরণ আমি তোর ওপর থেকে সরিয়ে নিতে চাইছি।’ সোমনাথবাবুর গলার স্বর কোমল, বললেন, ‘জীবনকে তুই সহজভাবে দেখতে শেখ, কোনও কিছুই নিজের ওপর জুলুম করে, সংস্কারবশে করিস নি। স্বাভাবিক জীবনের ধর্মে যদি মৃত প্রিয়জনের জন্য কষ্ট আর তেমন তীব্র না থাকে তো না-ই থাকল। সত্যকে সহজে নে, এই আমার প্রার্থনা। স্ত্রীর শোকের কতটা যে প্রকৃত ভালোবাসা থেকে আর কতটা বৈধব্যভীতি থেকে তার অনুপাতের একটা ভয়াবহ এবং করুণ গল্প বলি শোন, তারপর তোকে ছেড়ে দেব। আমাদের বাড়িতে ছিলেন বড়পিসিমা—চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়, ষোলতে বিধবা হন। মাথা ন্যাড়া, আধময়লা থান পরনে, বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের সব রান্না একা হাতে করতেন, কাউকে ছাড়তেন না, যেন সংসারকে ওইটুকু না দিলে নিজের অস্তিত্বটার কৈফিয়ত দেওয়া যাবে না এমনই একটা ভাব ছিল তাঁর। কিংবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন যেন। বেলা তিনটের সময়ে খেতেন, সেই একবেলার আহার। বোধহয় আমার মা রাত্রে জোর করে দুধ মিষ্টি কিছু খাওয়াতেন কোনদিন কোনদিন। একসময়ে আমার ছোট পিসেমশাই-এর হল সাঙ্ঘাতিক উদুরি। সে অসুখ তখন ক্যানসারের মতোই দুরারোগ্য ছিল। নিজের বাড়িতে তেমন দেখবার কেউ নেই। ছোট পিসিমা পিসেমশাইকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে উঠলেন। চিকিৎসা চলল কিন্তু অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে হতে অবশেষে এমন হল যে দিন কাটে তো রাত কাটে না। সকাল থেকে ছোটপিসিমা রোগীর শয্যার পাশে। দুপুরবেলা বেচারি দিদির ডাকে সবে উঠে একটু খেয়ে আসতে গেছেন এমন সময়ে পিসেমশাই-এর শেষ সময় উপস্থিত হল। আমাকে পাঠানো হল তাঁকে ডাকতে দেখলুম খাবার ঘর ভেতর থেকে এঁটে বন্ধ। প্রাণপণে দরজা ঠেলছি কোনও সাড়া নেই। শেষে জানলার খড়খড়ি তুলে দেখি আসনে ছোটপিসিমা বসে, সামনে ভাতের থালা, বড়পিসিমা গ্রাস তুলে তুলে ছোটবোনের মুখে দিচ্ছেন। মাছ মাংস ইত্যাদি যে তিনি কখন কাকে দিয়ে আনিয়েছেন অসুখের বাড়িতে, কখন চুপি চুপি রান্না করে রেখেছেন কেউ জানতে পারেনি। মুখে গ্রাস তুলে দিচ্ছেন আর বলছেন—‘আগে খেয়ে নে রে ছুটি, জীবনে আর কোনদিন ছুঁতে পারবি না।’
‘আমি সেখান থেকে ছুট্টে পালিয়ে এলুম। তারপর ছোটপিসিমা যখন মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর পরনে লাল পাড় শান্তিপুরী শাড়ি। মাথায় ডগডগে সিঁদুর, পানের রসে ঠোঁট রাঙা কিন্তু পিসেমশাইয়ের তখন আর জ্ঞান নেই। জ্ঞান হারাবার আগে করুণ চোখে যাকে খুঁজছিলেন তিনি তখন জীবনের শেষ খাওয়া খেতে, শেষ সাজ সাজতে ব্যস্ত।
‘সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনকে মেনে নে বন্দনা। কত স্মৃতি যাবে, কত স্মৃতি আসবে, কত কিছু হারাবি, কত পাবি। এভাবে নিজেকে অতীতে প্রোথিত বাড়বৃদ্ধিহীন গাছের শব করে রাখিসনি। তুই যত চলবি, যে ভালোবাসা মানুষকে অন্য মানুষ করে তোলে সে ততই তোর দু হাতে ধরা দেবে। নইলে নয়।’
অধ্যায় ১৬
পরদিন স্কুলে গেল না বন্দনা। একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ঘোরাফেরা করলেন সোমনাথবাবু কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এখনও বন্দনার চোখ লাল, মুখ ফুলে আছে। নাই বা গেল একদিন। কিন্তু পরদিনও সে গেল না। তার পরদিনও না। তৃতীয়দিন সোমনাথবাবু বুঝতে পারলেন সে কোনদিনই আর স্কুলে যাবে না। সেদিন রাত্রে ঝোঁকের মাথায় অনেক কথা, প্রায় একটা বিরাট বক্তৃতাই দিয়ে ফেলেছেন বন্দনাকে। বিষয় খুবই স্পর্শকাতর। সেইজন্যেই কি সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলল? কিন্তু তিনি তো নিরুৎসাহকর কোনও কথা তাকে বলেননি! বরং যাতে অপরাধবোধ, পাপবোধ থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে সহজ হয়, বাকি জীবনটা মোটের ওপর ভারমুক্ত হয়ে চলতে পারে এমন কথাই তাকে বলেছেন। বন্দনা কি রাগ-অভিমান করল? হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে সব সময় যুক্তি কাজ করে না। তিনি যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন, তত্ত্ব এবং উদাহরণের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাতে কি বন্দনা কোথাও আঘাত পেয়েছে? সে একবার বলেছিল বটে তাকে এত কঠিন কথা তিনি কেন বলছেন! তাহলে কি সে তাঁর ওপর রাগ করে স্কুলের কাজটা ছেড়ে দিল? স্কুলে কাজ নিতে তিনি তাকে কখনও বলেননি। বন্দনার নিজেরই ইচ্ছে সেটা। তিনি দেখে সুখী হয়েছিলেন যে বন্দনা কত স্বচ্ছন্দ হয়ে গেছে। প্রতিদিন এটা তিনি অনুভব করেছেন। তাহলে? তিনচারদিন কেটে গেলে সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলেন; বন্দনা বলল, ‘তুমি কি চাও যেখানে আমাকে সব সময় মিথ্যাচরণ করতে হয়, যেখানে আড়ালে আমাকে লক্ষ্য করে লোকে বক্রোক্তি করে সেখানে আমি যাই?’ কিছুই বুঝতে পারলেন না সোমনাথবাবু। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর আসল ঘটনাটা প্রকাশ পেল। বন্দনা বলল, ‘সামনাসামনি ওরা উদার, আড়ালে আরও কত কি বলে থাকে, কি মনোভাব পোষণ করে আমার সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি থেকেই তো বোঝা যায়।’ সোমনাথ ব্যথিত হয়ে বললেন, ‘কি যে নিষ্ঠুর এই মায়ের জাত। নিজেদের হেয় করতে এদের সত্যিই জুড়ি নেই। কিন্তু বুড়ি এতো ভঙ্গুর হলে তো তোর চলবে না। তুই দুর্বল হলে আঘাত বারবার আসবে। আর এসব আঘাত মনকে শুধু ছোট করে, এ সব আঘাতের কোনও মর্যাদা নেই। তুই যে কোনও সংস্কার মানিস না সেটা লুকোলে চলবে না নিজের মধ্যে জোর না থাকলে লোকে বারবার আঘাত করবেই, অনেক সময়ে না বুঝেই করবে যে।’
বন্দনা চুপ করে রইল। একবারও বলল না জোরের সঙ্গে যে সে এবার থেকে আরও সবল হবে, এত সহজে ভেঙে পড়বে না। আসলে সে মনে মনে বলছিল, ‘আমি পারব না। পারছি না যে কাকা।’ কিন্তু এ কথা বললে কাকা পাছে তাকে আরও জোর করেন, তাই সে চুপ করে রইল।
চুপচাপ গুমোট দিনগুলো কাটে। একমাত্র রূপ বাড়ি ফিরলে তার হাঁকডাক, কলকাকলিতে সে গুমোট কাটে।
সে বাড়ি এসেই সেদিনের স্কুলের মুখ্য ঘটনাটা নাটকীয়ভাবে বলবে—‘ওঃ জানো মা আজকে স্কুলে ফাটাফাটি কাণ্ড।’
—‘কেন রে?’ বন্দনার প্রশ্ন খুব নিরুৎসুক।
—‘আরে দুটো নতুন ছেলে অন্য স্কুল থেকে এসেছে, কথা বলছিল, ব্যস মিস তাদের জামার পেছনে ডঙ্কি আর মঙ্কি লিখে দিয়েছে বড় বড় করে।’
—‘কোন মিস?’ সোমনাথবাবু জিজ্ঞেস করেন।
—‘মিসেস রডরিগ্স। সেই যে গো যার ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ে। স্যামুয়েল। ভীষণ বিচ্ছু!’
—‘তারপর?’
—‘টিফিনের সময়ে তো ছেলে দুটো বাইরে বেরিয়েছে, আর স্কুলশুদ্ধু ছেলে তাদের নিয়ে হেসেছে। তখন কি সাহস! ছেলে দুটো প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে কমপ্লেন করেছে, কেঁদেছে।’
বন্দনা অন্যমনস্ক ছিল, বলল, ‘আচ্ছা! সত্যি খুব সাহসী ছেলে তো?’
রূপ উৎসাহ পেয়ে বলে, ‘তারপর শোনো না, প্রিন্সিপ্যাল মিসকে ডেকে কি বকুনি! চাইল্ড সাইকলজি, নেভার ইনসাল্ট দেম, য়ু আর নট ফিট টু বী আ টিচার, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই শুনেছি। কেন্ নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল একটু পরে এসে আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিলে কি হবে, তার আগেই আমাদের শোনা হয়ে গেছে।’
সোমনাথবাবু বলেন, ‘যাক তবু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মিঃ স্মিথের।’
রূপ বলল, ‘মা তুমি কখনও তোমার স্কুলের মেয়েদের এরকম শাস্তি দাও, পেছনে লিখে!’
বন্দনা মুখে বলে, ‘পাগল হয়েছিস।’ মনে মনে বলে ‘আমি লিখব কি? আমার পেছনেই সবাই নানান কথা লিখে দিচ্ছে, এমন কালি দিয়ে যে সে আর কিছুতেই উঠতে চায় না।’
সোমনাথবাবু খুব চুপচাপ হয়ে গেছেন। মানুষকে সাহায্য করা বড় কঠিন। কথায়, আচরণে, আদরে কোথাও তো চেষ্টার অন্ত নেই। তবু হয় না। তবু হল না। জীবনের ওপর মৃত্যু ক্রমাগত জয়ী হয়ে চলেছে। এতদিন পর তাঁর মনের মধ্যে গভীর আলস্য আসছে। অবসাদ, হতাশা। হতাশা থেকেই আলস্য। বন্দনার মায়ের মৃত্যুর পর, দাদার অবস্থা দেখে তাকে মানুষ করার ভার নিজেই তুলে নিয়েছিলেন যেচে। কোনদিন মনে হয়নি খারাপ করেছেন। একটি বালিকাকে আস্তে আস্তে গড়েপিটে তোলবার মধ্যে তিনি অসীম আনন্দ পেয়েছেন। সেই মেয়ে স্বামীকে হারালো। শ্বশুরবাড়িতে তার অবস্থা দেখে, নিজের মধ্যে সেই পুরনো জেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল আবার। অসীম স্নেহও ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল এই হার-না-মানা জেদ। মুমূর্ষ মেয়েকে আবার জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। এখন তাঁর মনে হচ্ছে স্নেহের চেয়ে কি জেদটাই বেশি ছিল। বেশ তো এগোচ্ছিল। এখন যেন মেয়ে তাঁর সামনে একটা দেয়াল তুলে দিয়েছে। এই পর্যন্ত, আর এগিও না। কিছুদূর পর্যন্ত তোমার চেষ্টা আমি মেনে নেব। কিন্তু স্বপ্নেও ভেব না অনুশাসনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমি স্বীকার করে নেব। হঠাৎ সোমনাথের মনে হল তাঁর আর কোনও কাজ নেই। সত্যি সত্যি তিনি অবসর নিয়েছেন। বুড়ো হয়ে গেছেন। একেবারে বুড়ো। ইজিচেয়ারটায় আধশোয়া হয়ে ভেতরের বিমর্ষতায় কিরকম একটা চুলের মতো আসে। সেটা ঠিক ঘুম নয়। ঘোর। ঘোরের মধ্যে নিজেই নিজেকে বলেন, ‘চলো এবার ফেরো।’
‘কোথায়?’
—‘না, হিমালয় নয়। এবার আরও উঁচু অলটিচ্যুড, আরও উত্তরে। যেখানে সব প্রশ্নের শেষ উত্তর, সব তীর্থের সেরা তীর্থ।’
—‘ওদের কি হবে?’
—‘ওদের আর অত আগলে রাখতে হবে না। তুমি আড়াল করে আছ বলে বাড়তে পাচ্ছে না। সরিয়ে নাও তোমার পক্ষপুট। অভিজ্ঞতার মোকাবিলা নিজেদের করতে শিখতে দাও।’
‘কিন্তু বালকটি?’
—‘ওকে ওর মা দেখবে, মানুষ করবে, তুমি কে?’
ঘোরের মধ্যেই সোমনাথবাবু শুনতে পেলেন বন্দনা বলছে—‘ওমা, তুমি! হঠাৎ! এতকাল পরে!’
অপরিচিত নারী কণ্ঠ বলে উঠল, ‘বউমণি তুমি আবার কবে থেকে আমাকে তুমি বলতে আরম্ভ করলে গো?’
—‘কতদিন দেখা নেই! কিছু মনে করিসনি! সবাই ভালো আছেন?’
—‘ওমা মনে কি করব? কার ভালোর কথা জিজ্ঞাসা করছ?’
—‘সবার। মা, বাবা, কাকা, কাকিমা, মেজদা, ছোড়দা, মিলি।’
—‘সবাই ভালো। মেজদার তো বম্বেতেই বিয়ে হয়েছে। ভটচায্যি বাড়ির থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে একেবারে, জানো তো? বিরাট পয়সা বউদিদের। মেজদা গিয়ে তাদের এক্সপোর্টের ব্যবসার হাল ধরেছে। মেজবৌদি বাঙালি হলে কি হবে? একেবারে বম্বেওয়ালী হয়ে গেছে। বাংলা বলে ভাঙা ভাঙা। মিলিটার বিয়েটা কিছুতেই লাগছে না। আসলে কাকা-কাকিমা বোধহয় স্বপ্নে-দেখা রাজপুত্তুরটি পাচ্ছেন না। যাই হোক, তোমাকে কিন্তু যেতেই হবে।’
সোমনাথবাবু আস্তে আস্তে চোখ মেললেন। একটি বউ, দেখলে মনে হয় বেশ বড়লোকের ঘরের। ঝলমল করছে চেহারাখানা। শাড়ি গয়নার জাঁকজমক ছাড়াই। ঝলমলানিটা কিসের? সোমনাথবাবু নিজেই জিজ্ঞেস করলেন নিজেকে, উত্তর দিলেন—বোধহয় সুখের। সমৃদ্ধিও আছে অন্তরালে। কিন্তু জানান দিচ্ছে না।
বন্দনা বলল, ‘আয় কলি, কাকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। কাকা, এই আমার ননদ কলি, তুমি বোধহয় ওকে চিনতে পারছ না, এত বদলে গেছে!’
কলি বলল, ‘আমি একটুও বদলাইনি বউমণি, বিশ্বাস করো। একটু মোটা হয়েছি শুধু। কোন বাঙালিনী বিয়ের পর মোটা হয় না গো? তুমিও হয়েছিলে!’ বলতে বলতে কলি কাকাকে প্রণাম করল; বলল, ‘কাকু, আমার মেজ দেওরের বিয়ে, বউমণি, আপনি, খোকা সবাই অবশ্যই যাবেন। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমার কর্তা অফিসের কাজে দিল্লি গেছেন। সেই বিয়ের দিন সকালে আসবেন। তাই আসতে পারলেন না।’
সোমনাথবাবু বললেন, ‘ও সব বলতে হবে না। আমি নিশ্চয় যাব মা।’
বন্দনা বলল, ‘কাকা রূপকে নিয়ে যাবেন কলি, আমাকে লক্ষ্মীটি বাদ দে।’
কলির মুখ কালো হয়ে গেল, বলল, ‘বউমণি, ছেলের অন্নপ্রাশনে কিচ্ছু করতে পারিনি। সে সময়ে এদের জেঠু মারা গেলেন। আমাদের এ বাড়িতে এই আমার নিজের হাতে আয়োজন করা প্রথম উৎসব, তুমি যাবে না, এ হতেই পারে না।’
—‘আমি গিয়ে কি করব কলি, আমি একটা মূর্তিমতী ছন্দপতন ছাড়া কি?’
কলি হারবার পাত্রী নয়। বলল, ‘বউমণি, একজনের ওপর রাগ করে আরেকজনকে শাস্তি দেওয়া কি ঠিক? মা, বাবা, কাকা, কাকিমা সবাই এখন তোমার জন্যে দুঃখ করেন, খোকামণির জন্যে ও বাড়ির আলো নিভে গেছে, জীবনে পাশাপাশি থাকতে গেলে কত কি ঘটে, খুবই খারাপ, ভোলা যায় না, তবু ভুলতে হয়। মাফ করাও যায় না তবু একটু মাফ করতেই হয়। আমি নিজে এসে যখন তোমাকে সাধাসাধি করছি, তখন তোমায় কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হবে না নিশ্চিত জেনেই করছি তো!’
বন্দনা বলল, ‘ওসব কিছু নয় কলি। আমি সব ভুলে গেছি। মাফ করবারও প্রশ্ন নেই। ওসব ছাড়। আমার কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে, পাঁচজনের মজলিশে যেতে একেবারে ভালো লাগে না রে, জোর করিস না।’
কলি সোমনাথবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কাকু আপনিই বলুন এটা কি বউমণি ঠিক করছে? এভাবে সরে থাকা, দূরে থাকা এটা কি সুস্থতার লক্ষণ?’
সোমনাথ বললেন, ‘তুমি ঠিকই ধরেছে মা। এইরকম দূরে সরে থাকা ঘোর মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু আমার কিছু করবার নেই। আমি বুড়ো মানুষ। কারো বাবা নই যে জোর করলেই জোর খাটবে। তোমাকে বিফল মনোরথ হয়েই ফিরতে হবে। যদি বলো তো নাতিকে নিয়ে আমি যাবো’খন।’
কলি বলল, ‘সে তো যাবেনই। তবে আমি হার মানছি না। বউমণিকে আমি ঘরের বার করবই। একটা মানুষ দিনের পর দিন নিজেকে এভাবে জ্যান্ত কবর দিয়ে রাখতে পারে তোমাকে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না। আমি আবার আসব। আজ যাই?’
—‘আবার এসো মা’, সোমনাথবাবু বললেন। কলি সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল। বন্দনা পেছন পেছন। একটু পরেই গাড়ি ছাড়ার শব্দ হল।
সোমনাথবাবু চশমাটা খুলে রেখে আবার চোখ বুজলেন।
একটু পরে বন্দনার গলা শুনলেন, ‘তুমি ওভাবে বললে কেন?’ চোখ খুললেন সোমনাথ—‘কি ভাবে?’
—‘বললে তুমি বুড়ো, তুমি কারুর বাবা নয়। তোমার জোর নেই⋯।’
—‘কথাগুলো কি মিথ্যে? আমি বুড়ো হইনি? আমি কি কারুর বাবা?’
বন্দনা কাকার হাতের ওপর মাথা রেখে বলল, ‘কাকা তুমি বুড়ো নও। বুড়ি আসলে আমি। আমি বুড়ো, প্রাচীন, আবর্জনা হয়ে গেছি। আমার মনের মধ্যে শ্যাওলা ধরে আছে। চেষ্টা করছি, আমি কিছুতেই পরিষ্কার হতে পারছি না। তুমি আমার ওপর রাগ করো না। আমি তোমার রাগ-অভিমানের যোগ্য নই। এতো দীনহীন আমি!’
সোমনাথ উঠে বসলেন। বন্দনার চোখে জল থমকে আছে। বলল, ‘তুমি এভাবে নিজেকে সরিয়ে নিও না, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।’
—‘কেন বুড়ি, তোর ছেলে রয়েছে। তার প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য, ভালোবাসা⋯··এ কি তোর যথেষ্ট নয়? স্নেহ নিম্নগামী জানিস তো!’
বন্দনা মাথাটাকে আরও জোর করে কাকার হাতের ওপর চেপে ধরে বলল, ‘রূপের আমি আছি। কিন্তু আমার কে আছে বলো?’
—‘কিন্তু আমি তো তোকে কষ্ট দিই বুড়ি। তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে জেদ করি। কোনও জিনিসই জোর-জুলুম করে হয় না, আমি ভুলে যাই মা।’
—‘ভোলো, ভুলে যাও কাকা। জোর করো। আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গড়ে উঠতে সাহায্য করো। আমার সত্যিকারের ইচ্ছে যে কি তা তো আমি জানি না। তোমার কথাগুলো আমি দিবারাত্র মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করি। বুঝতে পারি একটা শক্ত খোলসের মধ্যে বাস করছি। বিশ্বাসের, শিক্ষার, সংস্কারের অভ্যেসের শক্ত খোলা। সেটা ভেঙে বার হওয়া যে ভীষণ কঠিন কাকা, কত কঠিন, তুমি পুরুষ, তার ওপর বিয়ে করোনি, তুমি মুক্ত, তুমি জ্ঞানীও, তুমি বুঝবে না।’
সোমনাথ মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—‘যদি কলিদের বিয়ে-বাড়িতে যেতে বলি, যাবি?’
—‘প্লীজ কাকা, অন্য একদিন আমি কলির বাড়ি নিশ্চয়ই যাব। ওইদিন যেতে বলো না। অনেক লোকের ভিড়, বিশেষ করে মেয়েদের ভিড় আমার সহ্য হয় না। আমি… আমার ভেতরটা কিরকম কুঁকড়ে যায়। ঘেন্না হয়। সত্যি বলছি কাকা। তাছাড়াও, ওখানে আমার শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে দেখা হবে। ওঁরা যদি ফিরে যেতে বলেন, বলবেনই। তুমি কি চাও আমি চলে যাই?’
এমন করুণ মিনতির সুরে কথাগুলো বলল বন্দনা, যে সোমনাথ আর এ নিয়ে দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ করতে পারলেন না। মনে মনে বুঝলেন বন্দনা ঠিক কথাই বলছে, এই উপলক্ষ করে কলি বোধহয় পঁয়তাল্লিশ নম্বরের সঙ্গে বন্দনাদের মিল-মিশ করিয়ে দিতে চাইছে। হয়ত তাতে এক ভাবে ওদের পায়ের তলার মাটি শক্ত হবে। কিন্তু বন্দনাকে খানিকটা পুনর্মূষিক হতেই হবে। তিনিই বা এই বয়সে আর কি নিয়ে থাকবেন? বন্দনা তাঁকে ছেড়ে যেতে চায় না। তাঁর ভেতরটা গভীর স্নেহে টলটল করছে। তিনি সেইরকম টলটলে গলাতেই বললেন—‘চল বুড়ি, খাবার বেলা বোধহয় পার হয়ে গেল।’
খেতে খেতে বন্দনা বলল—‘একটা কথা বলব? রাগ করবে না?’
—‘আমি কি তোর ওপর শুধু রাগই করি! বলই না কি কথা।’
—‘ওদের অফিসে অমলেন্দু ঘোষাল বলে এক ভদ্রলোকের কাছে একবার যাবে? তখন পার্সোনেল-এ ছিলেন, এখন কি হয়েছেন অবশ্য জানি না।’
—‘কেন রে?’
—‘আমার কিছুদিন থেকেই মনে হচ্ছে ওর স্ত্রী হিসেবে ওখানে একটা কাজের চেষ্টা করলে আমি পেয়ে যেতে পারি। ঘোষালের সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা। ওকে দাদার মতো ভালোবাসতেন।’
—‘কিন্তু তুই তো কাজ করতে গেলে দুঃখ পাস।’
—‘ওখানে পেয়েছি বলে এখানেও পাবো তার কি মানে আছে?’
সোমনাথ হাসলেন—‘বাইরে দুঃখ আছেই, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এখানে পেলে ওখানেও পাবি। তাছাড়া মেয়েদের পক্ষে টিচিং জবটা খুব নিরাপদ। চাকরিটা তোকে সুটও করেছিল ভালো। কত কাছে ছিল বাড়ির!’
বন্দনা থালার ওপর আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে বলল—‘আগের চেয়ে অনেক শক্ত হয়ে গেছি এখন, বিশ্বাস করো। স্কুলে আমি রেজিগনেশন পাঠিয়ে দিয়েছি। ওই পরিবেশটার সঙ্গে আমার কিরকম একটা মন-খারাপের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। কিরকম একটা কমপ্লেক্স। আমি যে এতো দুর্বল আমি নিজেই জানতাম না। তুমি এবারটির মতো আমায় মাফ কর। আর কখনও আমি ওরকম করব না। দেখ!’
অধ্যায় ১৭
অমলেন্দু ঘোষাল অভিমন্যুর থেকে কিছু ছোট। দুজনেই বোধহয় এক স্কুলের ছাত্র, সেই হিসেবে একটা অতিরিক্ত টান, সৌহার্দ্য ছিল। বন্দনাকে দেখবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। লাঞ্চ আওয়ারের পর। অফিসে এখন বেশ খানিকটা শিথিলতা। অনেকেই সিটে নেই। ঘোষালের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে বন্দনা ঘামছে। ঘোষাল অভিমন্যুকে অফিসের বাইরে দাদা বলত, বন্দনাকে বউদি। সামাজিক, মেলামেশা অবশ্য ছিল না। কিন্তু যতবার অফিসের উৎসবে, পার্টিতে এসেছে অমলেন্দু ঘোষাল তাকে বিশেষ খাতির করেছে। ককটেল পার্টির গোলমেলে আবহাওয়ায় তাকে সহজ হতে সাহায্য করেছে। আজ সেই মানুষটির কাছে সে প্রার্থী। প্রথমে সে কাকাকেই পাঠাতে চেয়েছিল। তিনি আগে এসে অবস্থাটা বুঝে যান। কিন্তু কাকার শরীরটা ভালো নেই। বুকে চাপ। মাথা ঘুরছে। ডাক্তার বলছেন ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু বিশ্রাম দরকার। কাকা তা সত্ত্বেও আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল খুব কষ্ট হবে। তাছাড়াও ডাক্তারের বারণ। এ দিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়ে গেছে। তাকে আসতেই হয়েছে।
অমলেন্দু বললেন—‘আপনার তরফ থেকে টেলিফোন পেয়ে আমি খানিকটা অবাকই হয়ে গেছি। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ তো আপনি একেবারেই ছিন্ন করে ফেললেন।’
বন্দনা টেবিলের মাৰ্বল রঙের টপটার দিকে তাকিয়ে বলল—‘আসলে মিঃ ঘোষাল আমি তো এখন ও বাড়িতে নেই।’
—‘ও বাড়িতে নেই? মানে অভিদার বাড়িতে? নেই?’ সামান্য বিস্ময় প্রকাশ করেই নিজেকে সামলে নিলেন ঘোষাল। অযথা কৌতূহল প্রকাশ করবার লোক তিনি নন। তাছাড়া এতে বিস্ময়েরই বা আছে কি?
বন্দনা বলল—‘ছেলেকে নিয়ে কাকার কাছে আছি। আমি ভাবছিলাম এখানে যদি একটা চাকরি পাওয়া যায়।’
ঘোষাল চমকে বললেন—‘চাকরি? আপনি?’ বন্দনা মুখ নিচু করে আছে। মনে মনে দ্রুত ভেবে নিলেন ঘোষাল মিসেস ভট্টাচার্য আর শ্বশুরবাড়িতে থাকেন না। ছেলেকে নিজেই মানুষ করছেন। কাকা বয়স্ক। রিটায়ার্ড। আর্থিক অসুবিধে হওয়া বিচিত্র নয়। বললেন—‘আশ্চর্য! আপনি এতদিন কি করছিলেন? এতদিন আসেননি কেন? আপনাকে এখানে অ্যাবজর্ব করা আমাদের দায়। নৈতিক কর্তব্য। খুব আনন্দের সঙ্গে আমরা সে কর্তব্য পালন করব। আপনি এক কাজ করুন। আপনার সম্মানের উপযুক্ত কাজ তো চাই! পাঁচজনের সঙ্গে বসে কাজ করতেও আপনার অসুবিধে হবে। আপনি তাড়াতাড়ি একটা টাইপরাইটিং স্টেনোগ্রাফির কোর্স নিয়ে আসুন। আমার নিজস্ব অফিসেই আপনাকে আমি নিয়ে নেব। সেক্রেটারিয়াল কোর্স আমরাই পড়িয়ে নেব। আপনি তো আগে জয়েন করুন।’
দারুণ উৎসাহের সঙ্গে বাড়ি ফিরে বন্দনা দেখল সদর খোলা। এখনও রূপের ফেরার সময় হয়নি। তবু এটা নিশ্চয় ওরই কীর্তি। সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে উঠতে জুতোর শব্দ পেলো ওপরে। তাদের নিচের তলার ভাড়াটে অবনীশবাবু এবং একজন ডাক্তার নেমে আসছেন। বন্দনাকে দেখেই অবনীশবাবু বললেন—‘এই তো এসে গেছেন।’
—‘কি ব্যাপার?’ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে বন্দনা জিজ্ঞেস করল।
—‘ভয়ের কিছু নেই মা। —সোমনাথবাবুর শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। একটু অজ্ঞান মতো হয়ে গিয়েছিলেন। ইনি ডক্টর সেন, আমি ডেকে আনলাম।’
—‘কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?’
খুব চিন্তিত মুখে ডাক্তার বললেন—‘হয়েছে তো অনেকরকম। একটা ই· সি· জি· করিয়ে কোনও কার্ডিওলজিস্টকে কনসাল্ট করুন। তাড়াতাড়ি। আমি লিখে দিচ্ছি—ডক্টর চ্যাটার্জি খুব কাছেই বসেন। চলে যান।’
কাকার ঘরে ঢুকে বন্দনা দেখল চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছেন তিনি। কথা না বলে, খাটের পাশে বসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুললেন। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বন্দনা মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে রাখল। ডাক্তার কথা বলতে বারণ করেছেন। কাকাকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। জীবনে যত ঝড় এসেছে সোমনাথবাবুর স্বভাব হল সোজা দাঁড়িয়ে সেই ঝড়কে আটকানো। লম্বা লম্বা নমনীয় গাছের মতো তিনি ঝড়ের সঙ্গে নুয়ে পড়ে নিজেকে বাঁচাতে শেখেননি। প্রথম যখন শরীর খারাপ টের পেলেন, নিজের কাছে যথেষ্ট বই আছে। পড়ে শুনে, ব্যায়াম, হাঁটা, নিয়মমত খাওয়া নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি আরম্ভ করে দিলেন। ডাক্তারের কাছে ভুলেও গেলেন না। কিন্তু এই ঝড় এভাবে আটকানো তাঁর সাধ্যের বাইরে। বন্দনা যোগীন্দর অ্যান্ড যোগীন্দরে কাজে যোগ দেবার পাঁচ মাসের মাথায় সোমনাথবাবু মারা গেলেন। মায়োকার্ডিয়্যাক ইসকিমিয়া।
অধ্যায় ১৮
হেমন্ত এদেশে খুবই ক্ষণস্থায়ী। সামান্য কয়েকটা হিমঝরা মেঘালো গা-শিরশিরে দিন। শহরের বুকের ওপর তখন ধোঁয়াশার দৈত্য অথচ বাতাসে গুমোট। মাত্র ক’টা দিন। তারপরেই ঝকঝকে শীত। ঘষা মাজা আকাশ। তকতকে সোনালি হাওয়া। পাতা ঝরে সমস্ত গাছ আস্তে আস্তে কঙ্কালসার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই নিষ্পত্র আঁকাবাঁকা ডালের কি শোভা! রূপ ময়দানে ছবি আঁকতে যায় ছুটির দুপুরে। এই সব গাছের কঙ্কাল এঁকে ফিরে আসে, ঝুলি নামিয়ে বলে—‘মা দেখো, কত রকমের ফর্ম!’ মুগ্ধ হয়ে স্কেচগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে বন্দনা। রিক্ততা, নিঃস্বতার রূপও এমন অপরূপ হতে পারে! প্রত্যেকটি গাছ যেন তার সমস্ত অলঙ্কার আবরণ, তার যা কিছু অতিরিক্ত সব নিঃশেষে খসিয়ে দিয়ে এক আত্মবিশ্বাসী উদাসীনতার বাতাবরণ তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষমাণ। চিরায়ত অপেক্ষা। যাকে সব বলে মনে করা যায় সেই সব, চলে গেলেও কিছু থাকে। কতটা থাকে তার ওপরই কি মানুষের চরিত্র-শক্তির শেষ বিচার!
খুব ভালো ছবি আঁকছে রূপ। যদিও নকল করার ক্ষমতাটা ওর যত বেশি, নিজস্ব সৃষ্টির দিকে ততটা মন নেই। তবু ওর মাস্টারমশাই বলেন ছবি আঁকাই ওর নিজস্ব লাইন। বন্দনার ভীষণ ইচ্ছে ছিল ছেলে ডাক্তার হবে। পৃথিবীতে যদি ভগবানের কাছাকাছি কিছু কল্পনা করা যায় তো সে হল ডাক্তার। প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেয়। শারীরিক ও মানসিক। রূপের পিসি কলিরও খুব ইচ্ছে তাই। রূপ যখন আরেকটু ছোট ছিল, কলি আর বন্দনা ছুটির দুপুরে বসে অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছে। দুজনের ছেলেই ডাক্তার হবে। রূপ হবে কার্ডিওলজিস্ট, আর কলির ছেলে হবে জেনারল প্র্যাকটিশনার। সবাই যদি স্পেশ্যালাইজ করে তো আর সব রোগের কি হবে? কিন্তু দেখা গেল রূপের এদিকে ঝোঁক নেই। বলল—‘ইসস, তোমরা তাই ভেবে রেখেছ বুঝি? আমি ডাক্তার হব না মা। ডাক্তারের লাইফ বলে কিছু আছে নাকি? সর্বক্ষণ শুধু অসুখ। অসুখ আর অসুখ।’ তাছাড়া ডাক্তার হতে হলে আগে তো বায়োলজি পড়তে হবে। ব্যাঙ বা আরশুলা কাটার কথা ভাবলেই রূপের গা শিউরোয়
কলি বলল—‘তুই কি তাহলে শিল্পী হবি রূপু? সে যে শুনতে পাই ভীষণ স্ট্রাগলের জীবন! এসপ্লানেডে রেলিং-এ ছবির এগজিবিশন করতে হবে, হল পাবি না। দর্শক পাবি না, ক্রেতা পাবি না।’
রূপ বলে—‘লত্রেক, রেমব্রান্ট এঁদের হিসট্রি জানো? ইমপ্রেশনিজম-এর হিসট্রি জানো! ১৮৭৮ সালে রেনোয়ারের যে ছবি চল্লিশ পঞ্চাশ ফ্রাঁতে বিক্রি হয়েছে ১৯২৮ শে সেই ছবিরই দাম হয়েছে ১২৫,০০০ ডলার। ভাবতে পারো?’
কলি হেসে বলে—‘১৮৭৮ থেকে ১৯২৮ মানে পঞ্চাশ বছর। ওরে বাবা, এরকম যদি হয় তো তোর প্রতিষ্ঠা দেখতে আমার আর বউমণির বেঁচে থাকবার কোনও চান্স নেই রে।’
বন্দনা ওকে দমিয়ে দিতে চায় না। এত ভালো আঁকে ও! কাছাকাছি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোথাও কোনরকমের শিল্পী কেউ নেই। ছবি-আঁকা তো দূরের কথা, গান, নাচ, কবিতা লেখা, তাদের দুই পরিবারের মধ্যে কারুর এসব গুণ নেই। তবে কলির কাছে শুনেছে তার সেজ দেওর, সেজদা নাকি বাজনা-পাগল ছিল। দারুণ পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ন বাজাত। রূপু শিল্পী হবে এই কল্পনার মধ্যে বন্দনা রোমাঞ্চ খুঁজে পায়। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে, শিল্পীকে নিজের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল হতে হলে উপোস করতে হবে। শিল্পীর বেশ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থাকা চাই। রূপের মাস্টারমশাই সুদীপ্ত সরকারের শিল্পী হিসেবে মোটামুটি খ্যাতি আছে। কিন্তু তিনি সরকারি চাকরি করেন। আঁকাটা তাঁর নেশা। এই নেশা তিনিই ধরিয়েছেন রূপকে। ছবি-আঁকার জগতের নানান চমকপ্রদ কাহিনী তিনি যখন রূপকে শোনান, বন্দনাও এসে বসে। এই জগতের সঙ্গে তার কোনও পরিচয় ছিল না। রূপের পড়বার জন্যে তিনি ‘লাস্ট ফর লাইফ’ আর ‘মুল্যাঁ রুজ’ বলে দুটো বই এনে দিয়েছিলেন। রূপের সময় হবার আগেই বই দুটো বন্দনা পড়ে ফেলল। সুদীপ্তবাবুকে ফেরত দিয়ে দিল। বলল—এগুলো পড়লে কিন্তু শিল্পী হবার সম্ভাবনাতেও ভয় হয়, যাই বলুন।’
সুদীপ্ত বললেন—‘কেন, ভালো লাগল না?’
—‘লেখা হিসেবে অপূর্ব লেগেছে। কিন্তু জীবন হিসেবে নয়, আপনি বইগুলো রূপুকে পড়াবেন না। ওর পক্ষে ভারি হয়ে যাবে।’
সুদীপ্ত হেসে বললেন—‘আপনার পক্ষেও খুব ভারি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে!’
বন্দনা সংশয়-ভরা চোখে বলে—‘রূপুর জন্যে খুব ভয় পাচ্ছি। এরকম ছন্নছাড়া অসহ্য কষ্টের জীবন নিজের ছেলের জন্যে কোন মা চায় বলুন!’
—‘দিন কাল আস্তে আস্তে পাল্টাচ্ছে মিসেস ভট্টাচার্য।’
—‘কি করে পাল্টাবে? এ দেশের লোক কোনদিন ছবি কিনে ঘরে টাঙাবার মতো বড়লোক হবে? একটু ফুল সাজাতেই সব জিভ বেরিয়ে যায়।’
—‘বড়লোকের খুব প্রয়োজন তো নেই, তা যদি বলেন, দেখবার চোখ এবং রুচির প্রয়োজন। সেদিক থেকে আমরা খুব দীন। এটা স্বীকার করতেই হবে। ধনী লোক এ দেশেও কিছু কম নেই। তবে আপনি ভাবছেন কেন, কমার্শিয়াল আর্ট আছে। বড় বড় পাবলিশিং হাউজ আছে।’
—‘তো আপনি সেসব করলেন না কেন?’
—‘আরে আমাকে বাবা অল্প বয়সেই সরকারি চাকরিতে জুতে দিয়েছিলেন। পরে দেখলাম এটা একটা বেশ নিরাপদ ব্যবস্থা। চাকরিটা যেন চাকরিই নয়। ভালোলাগার জিনিস নিয়ে মেতে থাকবার অবসর ও এনার্জি দুটোই থাকে। আসলে আমি চাকরি করতে করতে আঁকাজোঁকার দিকে এগিয়েছি। কিন্তু অভিরূপের মানসিকতা এখনই একটা নির্দিষ্ট বাঁক নিয়েছে ছবি-আঁকার দিকে। ওর মাস্টারমশাই হিসেবে এটাতে ওকে উৎসাহ দেওয়া সাহায্য করা এ আমার কর্তব্য নয়? বলুন! আর কর্তব্যটা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে, ওকে অসুবিধেয় পড়তে আমি দেব না। আপনি একদম ভাববেন না।’ সুদীপ্ত সরকার এমন ভরসা দিয়ে কথাটা বলেন যে বন্দনার ভয়-ভাবনা কমে যায়।
সুদীপ্তবাবু মাঝে মাঝে ছবির প্রদর্শনী করেন। ক্যাথিড্রাল রোডে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর আলাদা ভবন হয়ে সুবিধে হয়েছে খুব। সুদীপ্ত সরকার এবং তাঁর সহযোগী শিল্পী সমীর গুহর মিলিত প্রদর্শনী। সুদীপ্ত বন্দনার পাঁচ ছটা সিটিং নিলেন প্রতিকৃতি আঁকবার জন্য। বন্দনা প্রথমটা রাজি হয়নি। কিন্তু রূপের ভীষণ আগ্রহ, খাবার টেবিলের ওপর হাত রেখে বন্দনা বসে থাকবে। সুদীপ্ত তাঁর স্কেচবুক নিয়ে উল্টো দিকের চেয়ারে বসে বেহালার ছড় টানার মতো তাঁর পেনসিল চালাবেন। রূপ পাশে বসে বসে দেখবে। কিভাবে মায়ের মুখের আদল দু চার আঁচড়ে ফুটে উঠছে—কাগজের ওপর। সে নিজে ফিগারে ততটা পটু নয়। ল্যান্ডসকেপে যতটা। বিভিন্ন ভঙ্গির কয়েকটা স্কেচ এঁকে নিয়ে বন্দনাকে ছুটি দিয়ে দিলেন সুদীপ্ত। হেসে বললেন—‘ছবি যা আঁকব তাতে যেন নিজের লাইকনেস আশা করবেন না।’
—‘সে কি? কেন?’
লাজুক হেসে তিনি বললেন—‘কেন কি বৃত্তান্ত জানতে হলে তো ছবিটা দেখতে হয়।’
এগজিবিশনটা আজ দেখতে এসেছে বন্দনা কলি আর রূপকে সঙ্গে নিয়ে। সুদীপ্তবাবু সমীর গুহ-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনিই ক্যাটালগ হাতে নিয়ে তাদের ছবি দেখাতে নিয়ে গেলেন। সমীরবাবু তাঁর নিজস্ব প্রদর্শনীর নাম দিয়েছেন ‘সাত সমুদ্র তের নদী।’ ভদ্রলোক জল-পাগল। উট্রাম ঘাটের গঙ্গা, দশাশ্বমেধ ঘাটের গঙ্গা, শীতের অজয়, রূপনারায়ণ আর গঙ্গার সঙ্গম, গোধূলিতে গোদাবরী ট্রেন থেকে দেখা—অন্তত পঁচিশখানা তাঁর নদীর ছবি, সাগরের ছবি সে তুলনায় কম, মাত্র তিনটি। কিন্তু নদীর তুলনায় ছবিগুলো বিরাট। ঝড়ের সমুদ্র, উত্তাল, ভীষণ ভয়ঙ্কর, শান্ত সমুদ্র বালুবেলায় নীল চাদর ছড়িয়ে শুয়ে আছে। রাতের সমুদ্র, ফসফরাস আর দূরে মাছের ট্রলারের আলো জ্বলছে, লাইট হাউজের আলো পড়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে সমুদ্রের বুকে ভৌতিক জ্যোতি।
ছবিগুলো ভীষণ ভালো লাগল বন্দনার। শান্ত সমুদ্রের ছবিটা সে কিনবে কি না কলির সঙ্গে চুপিচুপি আলোচনা করে নিল। কলি বলল—‘একবার সুদীপ্তবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখলে হয়। আমরা তো সত্যি ছবির কিচ্ছু বুঝি না।’ বন্দনা বলল—‘এই ছবিটা ঘরে থাকলে আমার ভালো লাগবে রে কলি, কি সুন্দর মিঠে নীল রঙটা দেখ, হাওয়াতে বালি সরে সরে গেছে সিল্কের শাড়িতে কুঁচির মতো। নাই বুঝলুম ছবি। এটাই আমার সবচেয়ে পছন্দ।’
সুদীপ্ত সরকারের ঘরে ভিড় বেশি। তাঁরও প্রদর্শনীর নাম আছে—‘এক মুখ, নানা মুখ।’ অয়েলে আঁকা। বৃদ্ধার মুখ দিয়ে আরম্ভ, মুখে অজস্র বলিরেখা, নিদন্ত মুখে শুধু মাড়ির হাসি হলুদ, সোনালি খয়েরি দিয়ে আঁকা এই ছবিতে মনে হয় যেন শেষ বিকেলের আলো পড়েছে। বেশ দূর থেকে দেখতে হয় ছবিগুলো। বেশি সামনে গেলে শুধু চাপ চাপ রঙ। কলি বলল—‘বউমণি এদিকে এসো।’ চুপিচুপি বলল—‘তোমার ছবি মনে হচ্ছে! তোমার আদল!’ রূপ বলল—‘হ্যাঁ মা তোমার।’ অন্তত বারোখানা ছবির একটি সিরিজ। পেছন থেকে দেখা মুখের এক দশমাংশ, ডান পাশ, বাঁ পাশ, নিচু হয়ে কোনও জিনিস তোলার ভঙ্গিতে, হাত উঁচু করে কিছু নামানোর ভঙ্গিতে, রঙের আঁচড়ে, কালো, খয়েরি তামাটে গোলাপি রঙের হেরফেরে পুরো দেখা না গেলেও বন্দনার মুখ যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ সব ছবির জন্য কোনও সিটিং বন্দনা দেয়নি। সব শেষ ছবিটি সবচেয়ে বিস্ময়কর। এখানে পুরোপুরি আলোয় মুখ ফেরান। কিন্তু এ যেন অনেক বয়স্ক বন্দনা। অনেক দূরের দিকে চেয়ে আছে। মাথায় পাকা চুল। মুখে বয়সের রেখা। রূপ বলল—‘মা, মাস্টারমশাই তোমাকে এ রকম বুড়ো করে এঁকেছেন কেন?’
বন্দনা বলল—‘তুই-ই তো বেশি বুঝবি, কেন। তুই-ও তো হবু শিল্পী রে? আমি কি বুঝি!’
বেরোবার সময়ে সুদীপ্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁরা মনে হল বারোটি ছবির সিরিজ নিয়ে কিছু দুর্বোধ্য আলোচনা করছিলেন, বন্দনার অপ্রস্তুত লাগল, সে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। সুদীপ্ত এগিয়ে এসে বললেন,—‘কি রূপ, কেমন লাগল।’
—‘ভীষণ ভালো লেগেছে মাস্টারমশাই, মা বলছে সমীরকাকুর একটা ছবি কিনবে।’
—‘খুব ভালো, কোনটা। আমি দাগ দিয়ে রাখি, সমীর, সমীর!’
কলি বলল—‘আপনি আগে দেখুন এ ছবিটাই কেনবার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কিনা, আরও অনেক ছবি তো আছে।’
সুদীপ্ত এ ছবিটার নম্বর দেখে বললেন—‘মিসেস মুখার্জি, আমার কাছে কিন্তু ছবির ভালো-মন্দ নেই। অন্তত এ-সব ছবির। বিভিন্ন রাগ যেমন হয়। এগুলোও তেমনি শিল্পীর বিভিন্ন মেজাজ। যে ছবি মিসেস ভট্টাচার্যর ভালো লেগেছে, সেটাই উনি কিনবেন, এতে আমার গাইড্যান্স দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনি কিছু কিনলেন না?’
কলি রহস্যময় হেসে বলল— ‘আমিও কিনব। আপনার ওই বারো-ছবির সিরিজ যার আপনি নাম দিয়েছেন ‘উওম্যান ইন মাস্ক অ্যান্ড উইদাউট মাস্ক’ ওই থেকে শেষেরটা বাদ দিয়ে যে কোনও দুটো আপনি বেছে দিন।’
সুদীপ্ত বললেন—‘ওঃ, ওগুলো যে আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। পুরো সিরিজটাই। খুব দুঃখিত। আমি আপনাকে অন্য একটা বেছে দেব। কিংবা এঁকে দেব। ফ্রেশ, আপনার পছন্দটা আমি বুঝতে পেরে গেছি। এখন চলুন একটু চা খাওয়া যাক। তারপর আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।’
বন্দনা বলল—‘না, না, কোনও দরকার নেই, আমাদের তো আর বেশিদূর যেতে হচ্ছে না, আপনাকে এখানে দরকার, থাকুন না।’
‘আরে এখানকার সব সমীর সামলে নেবে, বন্ধ হবার সময়ও হয়ে এল। এই তো উল্টোদিকেই একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁ আছে, চলুন একটু বসা যাক।’
রূপ বলল—‘চলো না মা, আমার কত কথা জিজ্ঞেস করার আছে।’
রেস্তোরাঁয় ঢুকে রূপ বলল—‘পিসি তুমি আজ আমাদের বাড়ি থাকো।’
বন্দনা বলল—‘সেই ভালো, রাত হয়ে যাচ্ছে, তুই বরং একটা ফোন করে আয় পিসেকে।’
রেস্তোরাঁর লাল গদি মোড়া চেয়ারে বসে সুদীপ্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ লাজুক হেসে বললেন—‘খুব রাগ করেছেন আমার ওপর, না?’ তাঁর দৃষ্টি বন্দনার দিকে।
বন্দনা বলল—‘রাগ করার কি আছে! তবে অবাক হয়েছি খুব। আপনি আমাকে লাইকনেস আশা করতে তো বারণই করে দিয়েছিলেন।’
—‘তা দিয়েছিলাম। কিন্তু এত যে অমিল, তা বোধহয় ভাবেননি। আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পারছি।’
বন্দনা শুধু বলল—‘এসব ছবির সিটিংও তো আমি দিইনি!’
‘তা দেননি—, আসলে, আমি আপনার চেহারার এবং মুখের কয়েকটা বেসিক স্কেচ নিয়েছিলাম। তলার থেকে যাতে গলা আর চিবুক আগে দেখা যায়। পেছন ফিরে সামান্য মুখ ফেরালে যতটুকু দেখা যায়, এইভাবে, বাকি সব রঙ, সব রেখা, আলো-ছায়া আমার কল্পনা।’
কলি বলল—‘আপনার কল্পনা এরকম বাঁকা পথ ধরে চলে কেন?’
—‘আমার কল্পনা কি আপনার বিকৃত মনে হল?’
কলি অপ্রস্তুত হয়ে বলল—‘বাঁকা পথ বলেছি, বিকৃত বলিনি তো! দুটোয় তফাত নেই?’
—‘তা যদি বলেন মিসেস মুখার্জি, কল্পনা জিনিসটাই বাঁকা।’
রূপ এসে গিয়েছিল। বলল—‘সুদীপ্তকাকু মা’কে অমন বুড়ি করে আঁকলেন কেন?’
সুদীপ্তকে খুব ভাবিত দেখাল, বললেন, ‘রূপ তুমি আরেকটু বড় হও, বুঝবে মায়েরা বৃদ্ধাই হন, সব সময়ে বৃদ্ধা।’
বন্দনা বলল—‘রূপ যদি না-ও বোঝে, আমাকে তো বুঝতে হবে!’
‘সুদীপ্তবাবু, আপনার আঁকার পেছনে উদ্দেশ্যটা কি? কিছু বলতে চাইছেন, সেটা কি!’
কলি বলল—‘সিরিজটার নামটাও আমার দুর্বোধ্য লাগল ‘উওম্যান ইন মাস্ক অ্যান্ড উইদাউট মাস্ক’ খুব আপত্তিকর কিন্তু যাই বলুন। মেয়েরা কি সবসময়ে মুখোশ পরে থাকে?’
—‘থাকে না? মানুষ মাত্রেই থাকে। কিন্তু পুরুষের কাছে পুরুষের মুখোশটা যতটা সহজভেদ্য, নারীরটা ততটা নয়। আমাদের প্রত্যেকটা পরিচয় এক একটা মুখোশ, মা, স্ত্রী, কন্যা এই সমস্ত আরোপিত পরিচয়ের মধ্যে একটা অন্য মানুষ, এসেনশিয়াল বীয়িং আছে যে লুকিয়ে থাকে। একাকিত্বে, নির্জনতায় সে ধরা পড়ে। মিসেস মুখার্জি, ওই সিরিজের যে শেষ ছবি, সেটাই মুখোশপরা নারীর ছবি, যে নিজেকে সমাজের আদর্শ অনুযায়ী কাটছাঁট করে নিয়েছে, অন্য এগারোটি ছবি তার মুখোশবিহীন সত্তার। ভালো করে লক্ষ করলে দেখতে পেতেন ছবিগুলোর বেশির ভাগই প্রায় কিশোরীর। যার কাছে জীবন সবে উন্মোচিত হতে আরম্ভ করেছে।’
কলি বলল—‘ওরে বাব্বা, আপনি বউমণিকে এভাবে স্টাডি করেছেন?’
রূপ বলল—‘কখন করলেন কাকু?’
সুদীপ্ত একটুও না ঘাবড়ে গিয়ে বললেন—শিল্পীরা যে সব সময়ে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে কাগজে ক্ষেত্রফল-টল কষে নিয়ে আঁকতে আরম্ভ করে তা নয়, আমি তো একেবারেই এভাবে কাজ করতে পারি না। প্রথমে মিসেস ভট্টাচার্যের একটা প্রতিকৃতি আঁকবারই আমার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু উনি তিনদিন আমাকে তিনটে সিটিং দেবার পরই বুঝলাম উনি অসম্ভব ভালো সাবজেক্ট, অত মোবাইল ফেস আমি কমই দেখেছি। তিনদিন আমি ওঁর মুখের তিনরকম মেজাজ দেখলাম। রেখা, কন্টুর সব বদলে দিয়ে সেই মেজাজকে ধরতে হয়। বাড়িতে গিয়ে অনেকগুলো ছবি আঁকলাম, স্কেচের ওপর বেস করে, প্রত্যেকটাই এতো এক্সপ্রেসিভ হল যে, এই সিরিজটার কথা আমার মনে এল।’
বন্দনা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। রূপ আইসক্রিম-কফি খাচ্ছে। চোখ গোলগোল করে মুগ্ধ চোখে মাস্টারমশাইকে দেখছে, মুখে স্ট্র, এই বয়সটা ওর বীরপূজার বয়স। রূপ বলল— ‘আমার কথাটার উত্তর দিলেন না তো কাকু?’
‘কোন্ কথা?’
—‘ওই যে মা-কে কেন ওই রকম পাকা চুল, বুড়ো করে আঁকলেন?’
কলি তখন কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে, বলল—‘ওই ছবিটাকে আপনি মুখোশ বলেছেন…’
সুদীপ্তকে খুব দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল, বললেন— ‘এতো কৈফিয়ত দিতে হবে জানলে আরেকটু ভেবে আসতাম, মিসেস মুখার্জি। কাজগুলো বেশির ভাগই ইন্সটিংটিভ। রূপ তোমাকে বললাম মায়েরা তাঁদের রক্ষণশীলতায়, আত্মত্যাগে, মাতৃত্ব-ই তাঁদের একমাত্র পরিচয় এই মনোভাবে খুব বয়স্ক। তরুণী মা-ও।’
কলি বলল— ‘সেটাকে মুখোশ বা ভান বলছেন?’
সুদীপ্ত বললেন—‘সব পরিচয়কেই আমি আমার শিল্পী-ভূমিকায় মুখোশ বলে ভেবেছি বোধহয়, একমাত্র অন্তরতম আত্মপরিচয় ছাড়া।’ তারপর বন্দনার দিকে ফিরে বললেন—‘খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলছি—আপনি যদি আপনার সময়মতো আমাকে আরও কয়েকটা সিটিং দেন…’ বন্দনা হেসে ফেলে বলল—‘তা হলে কি আমার সঠিক প্রতিকৃতিটা আঁকবেন?’
—‘না, না।’ সুদীপ্ত অন্যমনস্কভাবে বললেন— ‘তা হলে হয়ত আরও অনেক মুখ আঁকতে পারতাম। পুরো একটা অ্যালবাম। একই জনের মুখ অথচ লক্ষ মুখ।’
বন্দনা বলল—‘দেখুন সুদীপ্তবাবু, মানুষমাত্রেরই নানান মেজাজ, নানান মানসিক অবস্থা থাকবেই। আপনাকে আরও সিটিং দিলে আপনি ‘স্টাডি অফ এ উইচ’, ‘স্টাডি অফ এ ডেড উওম্যান’স ফেস’ এ-সবও আঁকতে পারতে পারেন। আমি মোটেই আপনাকে সে সুযোগ দিতে রাজি নই।’
সুদীপ্ত হেসে ফেললেন—‘আপনার এতো ভয় হয়েছে ছবিগুলো দেখে? ওগুলো কিন্তু খুব প্রশংসিত হচ্ছে। যাই হোক মডেল হিসেবে আপনার কিন্তু কিছু সম্মান-দক্ষিণ প্রাপ্য হয় মিসেস ভট্টাচার্য, সেটা আপনি না নিলে আমি ভীষণ কষ্ট পাব।’
সাইড ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বার করে রূপের হাতে দিয়ে সুদীপ্ত বললেন—‘দ্যাখো তো রূপ পছন্দ হয় কিনা!’
রূপ তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল প্যাকেটটা— নীলাম্বরী, বালুচরী।
বন্দনা বলল—‘সিটিং দেবার সময়ে তো এ-সব কথা হয়নি সুদীপ্তবাবু!’
—‘আপনার কত সময় নষ্ট করেছি, কত কষ্ট করে একভাবে বসে থেকেছেন।’
—‘হ্যাঁ, কিন্তু সেটা মূল্য দিয়ে কিনে নেবেন, এ-কথা আমি জানতাম না।’
—‘মূল্য দিয়ে তো কিনিনি, এটা উপহার, না নিলে আমি সাঙ্ঘাতিক চোট পাব।’
—‘আপনি শিল্পী মানুষ একটা ছবিই তো দিতে পারতেন আমাকে।’
—‘ছবি না দিলেও আমি আপনাকে শিল্পবস্তুই দিয়েছি। এটাতে যে বালুচরীর কাজ আছে আঁচলে তা ক্র্যাফ্ট-এর পর্যায়ে আছে না আর্ট হয়ে উঠেছে এটা ভাববার বিষয়। এটা ব্যবহার্য জিনিস এই পর্যন্ত। যাই হোক ছবি তো নিশ্চয়ই দেব।’
কলি বলল—‘আমার পছন্দসই ছবিগুলো তো বেচে দিয়েছেন, তাহলে আমি কোন্টে নেব, আমাকে গাইড করুন।’
রূপ বলল—‘মাস্টারমশাই আমাকে একটা দেবেন না?’ রূপ কখনও বলে সুদীপ্তকাকু, কখনও মাস্টারমশাই।
সুদীপ্ত বললেন—‘নিশ্চয়, যেটা তোমার পছন্দ।’
—‘তাহলে আমাকে ওই বৃদ্ধার ছবিটা দেবেন। গোল্ডেন কালার, কত বলিরেখা এঁকেছেন, হাসিটা কি সুন্দর!’
সুদীপ্ত বললেন—‘ঠিক আছে।’
বন্দনা বলল—‘রূপ, যে কোনটা ওরকম চেয়ে নিও না। আগে এগজিবিশন হয়ে যাক…’
‘তার দরকার নেই’, সুদীপ্ত হাত তুলে বললেন, কলির দিকে ফিরে বললেন— ‘সমীরের গঙ্গাস্কেপ একটা নিন না, আর একটা ছবি আমি আপনাকে ফ্রেশ এঁকে দেব। আপনি কোনটা নেবেন মিসেস ভট্টাচার্য।’
—‘রূপ আর আমি কি আলাদা? ওই ছবিটাই থাকবে। শাড়ি আপনি দিতে পারবেন না।’ বন্দনার গলার স্বরে স্থির সিদ্ধান্তের জোর। খুব ক্ষুণ্ণ কালো মুখ করে সুদীপ্ত শাড়ির প্যাকেটটা সাইড-ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলেন।
কলি কথা ঘোরাতে বলল—‘আচ্ছা সুদীপ্তদা, এই দেখুন আমি কিন্তু আপনাকে দাদা বলে ডাকলাম, চার দাদার কোলের বোন, আপনি আজ্ঞে, মিসেস মুখার্জি-টুখার্জি বেশিক্ষণ সহ্য হয় না, তুমি আর কলি বলবেন। ছবির জন্য আপনি বউদিকেই বাছলেন কেন? আমার সঙ্গেও তো আপনার পরিচয় ছিল? আমাকে বাছলেও তো পারতেন!’
সুদীপ্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন—‘হ্যাঁ তা তো পারতামই, তবে তোমার ছবি কখন আঁকব? সব সময়েই তো ঝড়ের মতো আসো, যাও, সঙ্গে স্বামী, পুত্র, লটবহর।’
—‘ও স্বামী-পুত্তুররা লটবহর বুঝি! থাকলে ছবি আঁকার সাবজেক্ট হওয়া যায় না?’ বলেই কলি সাবধান হয়ে গেল, বউমণি আবার কিছু মনে না করে।
সুদীপ্ত বললেন—‘কথাটা তা নয়। তোমাকে তো বসতে হবে, সময় দিতে হবে। রূপকে শেখাতে যাই বলে মিসেস ভট্টাচার্যকে কিছুক্ষণ বসতে বলতে পারি। তা ছাড়াও তোমার স্বামীর অনুমতি নেওয়া উচিত। আলাপ করিয়ে দিও? অনুমতি চেয়ে নেব।’
কলি বলল—‘ওসব অনুমতি-টতির আমি ধার ধারি না। অতসব করতে হলে আমার ছবি আঁকতে হবে না।’
—‘কি আশ্চর্য! এটা একটা ফর্মালিটি, করতেই হয়।’
—‘বউমণির ছবি আঁকবার সময়ে কার অনুমতি নিয়েছিলেন?’
—‘বউমণিরই অনুমতি নিয়েছিলাম।’
—সেটাই যথেষ্ট ছিল তো!’
—‘নিশ্চয়ই!’
—‘আমার বেলাতেও আমার অনুমতিটাই যথেষ্ট হওয়া উচিত।’
সুদীপ্ত কফির কাপ মুখে তুলে কলির দিকে তাকিয়ে রইলেন, বেশ চিন্তিত।
কলি হাসিমুখে বলল—‘ভয় নেই। আমার ছবি আপনাকে আঁকতে হবে না। আমার অনেক ফটো আছে। তাতেই এ যাত্রা কোনরকমে চালিয়ে নেব।’
রূপ হেসে উঠল। বন্দনাও মৃদু মৃদু হাসছে। সুদীপ্ত কাচুমাচু মুখে বললেন—‘এরকম তিরস্কার, এরকম নিন্দে জীবনে কেউ কখনও আমাকে করেনি।’
কিন্তু সুদীপ্ত বন্দনা এবং কলিকেও ছবি দেখার নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন। কলির স্বামী সঞ্জয়ও থাকছে। তবে পাঁচজনে মিলে ছবি দেখার পরে রেস্তোরাঁয় বসে যে আড্ডাটা হয় সেটার প্রতিই বেশি আগ্রহ সঞ্জয়ের। সে সুদীপ্তকে বলে—‘দাদা আঁকিবুঁকি কাটছেন কাটুন, রঙচঙ নিয়ে খেলাধুলো করবার শখ হয়েছে করুন না, লোকের তো মাছ ধরার হবিও থাকে। চোপর দিন পুকুরে চার ছড়িয়ে বঁড়শির আগায় টোপ গেঁথে বসে রইল, সন্ধের মুখে একটি পাঙাস কি সরল পুঁটি নিয়ে বাড়ি ফেরা। তা সে যাক, কিন্তু ব্যাপারটা সিরিয়াস, বিশ্বাস করতে বলবেন না। প্লীজ! আরে বাবা আপনাদের পিকাসো, পাবলো পিকাসো, ওরকম আঁকে কেন বলুন তো? নাক বাঁকা, ঠোঁটের জায়গায় চোখ, চোখের জায়গায় কান, কেন?’
—‘কেন? আপনিই বলুন’—সুদীপ্ত ঝুঁকে বসেন।
—‘সিম্পলেস্ট অফ দা সিম্পল, নিজেকে ইয়ে মানে’, রূপের দিকে আড়চোখে চেয়ে সঞ্জয় সামলে নেয়… ‘নানারকম অত্যাচার করেছে তো শরীরের ওপর! হাতে আর ড্রয়িং আসে না। হাত কাঁপে, দাদা, কাঁপে।’
সুদীপ্ত হো হো করে হাসেন, বলেন—‘আপনিই আর্ট-ক্রিটিক হবার উপযুক্ত লোক। আর্ট-ক্রিটিসিজমে হিউমার নেই, আপনি সেই হিউমার আমদানি করবেন।’
সঞ্জয় বলে—‘হাসছেন? তা হলে আমার ছোটবেলার একটা অভিজ্ঞতা বলি শুনুন, আমিও আর্টিস্ট হিসেবে পুরস্কার পেয়েছিলাম। সেই আমার জীবনের একমাত্র পুরস্কার বলতে গেলে। স্কুলে অ্যানুয়াল এগজিবিশন হচ্ছে, সবাই কিছু না কিছু দিচ্ছে; ছবি, হাতের কাজ, মডেল, চার্ট, নানারকম। আমিই বা দেব না কেন? বাড়িতে জেঠুকে ধরলাম, জেঠু বললেন— “ঠিক হ্যায় গাছ আঁকতে পারিস তো ব্যাটা? আঁক একটার পর একটা গাছ। পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দে।” আমি প্রাণপণে গাছ আঁকছি, কিন্তু ঠিক মনোমত হচ্ছে না। তখন জেঠু বললেন—“দাঁড়া, দেখছি।” আমাদের বাড়ির পেছনে ছিল একটা বুড়ো নিমগাছ। সেই নিমের বাকল নিয়ে এলেন এক টুকরো। বললেন—নে এবার এটাকে তোর কাগজে আচ্ছা করে সাঁট দিকি গঁদ দিয়ে। সাঁটা হলে তার তলায় নামকরণ হল “তুমি বৃক্ষ আদি প্রাণ” বললেন, “যা তোর এগজিবিশনে দিয়ে আয়।” বললে বিশ্বাস করবেন না, মডার্ন আর্ট বলে আমার সেই নিমের ছাল পুরস্কার পেয়ে গেল।’
রূপ খুব হাসছিল, কলি বলল—‘সত্যি তোমাদের এই জেঠুটি যা ছিলেন না, একাধারে চার্লি চ্যাপলিন আর শিশির ভাদুড়ি। বউমণি তোমাকে দেখাতে পারলাম না বলে আফশোস হয়।’
সঞ্জয় বলল—‘জেঠু নিজেকে ‘স্পেসিমেন’ বলে উল্লেখ করতেন। ‘স্পেসিমেন’, ‘সাম্পল’, ‘অজীব চিড়িয়া’ কতরকম।’
সুদীপ্ত বললেন—‘আপনাকে আমি ঠিক দশটা এগজিবিশন দেখাব, আর গোটাকয়েক ইলাস্ট্রেটেড বই পড়তে দেব। তারপর আপনি-ই অন্য কথা বলবেন।’
—‘আমি? অন্য কথা বলব? অসম্ভব। এখনই বোঝান না!’
—‘ছবি দেখবার জিনিস, কথা দিয়ে বোঝাবার হলে নিশ্চয় বোঝাতাম।’
অধ্যায় ১৯
অফিসে যেটা সবচেয়ে স্বস্তির কারণ সেটা হল বন্দনাকে সবার সঙ্গে বসতে হয় না, অমলেন্দুবাবুর ঘরের আগে একটা ছোট্ট ঘর আছে সেখানেই সে বসে, টাইপিস্ট স্যারার সঙ্গে। এই অফিসের তাবৎ কেরানিকুলের গুঞ্জন তার কানে আসে না। কারুর সঙ্গে সামাজিক মেলামেশার দায়ও তার নেই। অফিস যায়, কাজ করে, বাড়ি চলে আসে। আরেকটা জিনিস ভালো লাগে অমলেন্দুবাবু তাকে এতো সম্মান, এতো সমাদরের চোখে দেখেন, যেন সে তাঁর পি. এ. নয়, বয়সে বড় সহকর্মীর স্ত্রীই।
প্রথম দু-চার দিন কাজের পর বললেন—‘আপনার অফিসে আসতে বা বাড়ি ফিরতে খুব কষ্ট হয়, না?’
বন্দনা তখন সদ্য সদ্য অফিসে পৌঁছে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে, বলল—‘না, না, কষ্ট কি? সবারই তো এক অবস্থা!’
—‘না। না। সবার এক অবস্থা কোথায়? আমি তো দিব্যি গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে যাই। আপনার বাড়ি আমার পথে না পড়লেও খুব ঘুরও নয়, আপনাকে তুলে নেওয়া, নামিয়ে দেওয়া আমি অনায়াসেই করতে পারি। কিন্তু…’
—‘না, মোটেই ও কাজ করবেন না।’
—‘করব না। কিন্তু কারণটা আপনি জেনে রাখুন। নিয়মিত এ কাজটি করলেই আপনি অনেকের কোপে পড়বেন। আমি সেটা চাই না। আমি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি আপনি কোম্পানি থেকেই কার-লিফট পান।’
বন্দনা বলল—‘আপনি আমার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে যাবেন না মিঃ ঘোষাল। আমি একেবারে সাধারণ হয়ে থাকলেই স্বস্তি পাব।’
কিন্তু অফিস থেকে বেরিয়ে বেশির ভাগ দিনই সে ট্রাম-বাস চট করে ধরতে পারে না। বাদুড়-ঝোলা ট্রামে-বাসে ওঠবার সাহস বা দক্ষতা কোনটাই তার নেই। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল, তবুও না।
টাইপিস্ট মেয়েটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। সে ধর্মতলায় ব্লকম্যান স্ট্রিটে থাকে। বেশির ভাগ দিনই হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। দিনটা সুন্দর। কিছুক্ষণ ট্রামে ওঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বন্দনা হাঁটতে আরম্ভ করল, পার্ক স্ট্রিটে ঢুকে পড়ল। পর পর গাড়ির সার। চলমান। ভেদ করা দুঃসাধ্য। দু দিক থেকে রেস্তোরাঁর আলো জ্বলছে। বন্দনা ভাবল কোথাও ঢুকে একটু চা-টা খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর বাস পেলে ধরবে, নয়ত আবার হণ্টন। দু দফায় হাঁটলে বেশি কষ্ট হবে না। কলিদের সঙ্গে সাধারণত স্কাইরুমে বসে সে। পরিচিত বলে স্কাইরুমেই ঢুকে একটু উঁচুর দিকে জায়গা নিয়ে বসল। এদের ডিনারের জন্য টেবিল রেডি করা শুরু হয়ে গেছে। বন্দনার অস্বস্তি শুরু হল। ক্লান্তি এবং ঝোঁকের মাথায় আগে খেয়াল হয়নি, দলবেঁধে যেখানে আসতে ভালো লাগে সেখানে একা-একা ভালো না-ও লাগতে পারে। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় কেউ এখানে নিছক একা নেই। বিশেষত মেয়েরা। এবং তারা সকলেই ভীষণ সজ্জিত। উগ্র প্রসাধনে, কেশ এবং বেশবিন্যাসে সবাই-ই প্রায় একরকম। এ-দিকে তার আলগা খোঁপা থেকে চুল ছাড়া পেয়ে কপালের ওপর ঘাড়ের ওপর লেপটে আছে। কচি কলাপাতা রঙের এই টাঙাইলটা সে কাল পাট ভেঙেছে। আজকে একবার ইস্ত্রি চালিয়ে নিয়ে পরেছে। একটা শাড়ি সাধারণত দু দিন চালাবার চেষ্টা করে সে। সকালে মুখে যা সামান্য প্রসাধন হয়েছিল, এখন তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। টিফিন আওয়ারে মেয়েরা মুখ মেরামত করে, টিফিন সেরে যখন আবার সিটে এসে বসে তখন একদম টিপটপ। বন্দনা এসব করে না। সন্ধেবেলায় সে যখন বাড়ি ফেরে, তাকে সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছাত্রী কিংবা রিসার্চ স্কলারের মতো দেখায়। এখন কেউ হয়ত তার দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু বন্দনার মনে হল ডানদিকের টেবিলে পুডল-এর মতো চুল, বড় বড় রিং পরা মেয়েটি তার সঙ্গীকে কিছু বলল, তাকেই লক্ষ্য করে। আচ্ছা, এমন কেন হবে? মানুষ কি একা হতে পারে না? মেয়েদের একা একা কোথাও যেতে ইচ্ছা হতে পারে না? এ ধরনের সংস্কার কেন থাকবে? অন্য কোনও দেশে কি আছে? ব্রিটেন অবশ্য খুব রক্ষণশীল। কিন্তু আমেরিকা? সেখানে হয়ত আবহাওয়া সম্পূর্ণ অন্য রকম। কেউ কারুর তোয়াক্কা করে না। ফর্মালিটির বালাই নেই। এই মুহূর্তে বন্দনার মনে হল তার আমেরিকার নাগরিক হওয়া উচিত ছিল। স্টুয়ার্ড এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে বন্দনা অবাক হয়ে গেল। স্টুয়ার্ড নয়, যোগীন্দরেরই একজন অফিসার। হাতজোড় করে বললেন—‘বসতে পারি?’
—‘নিশ্চয়ই’—বন্দনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল। সামান্যই আলাপ ভদ্রলোকের সঙ্গে, কিন্তু আজ উনি বন্দনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।
—‘আপনি কি কারুর অপেক্ষা করছিলেন?’
—‘উঁহু।’
—‘তা হলে?’
—‘এমনি। ক্লান্ত লাগল, ঢুকে পড়লাম।’
ভরাট গলায় একটি মেয়ে গান ধরেছে। হাঁটু ভেঙে তাল দিচ্ছে, আর গাইছে ‘হোয়েন আই ওয়াজ আ ব্যাচেলর, ব্যাচেলর, ব্যাচেলর গাই।’ অ্যাকর্ডিয়ন বাজছে সঙ্গে সঙ্গে।
ভদ্রলোক বললেন—‘আমার নাম অনুপম সোম, জানেন তো?’
—‘কি আশ্চর্য! জানব না কেন?’
—‘না জানতেও পারেন। লোকে বলে আপনি অমলেন্দু ঘোষাল আর স্যারা মার্শ্যাল ছাড়া আর কাউকে চেনেন না।’
বন্দনা হাসিমুখে চুপ করে রইল। এ সম্বন্ধে তার বক্তব্য কিছু নেই। সত্যিই! মুখ-চেনা, আর সামান্য সৌজন্য বিনিময়—এর বেশি নিকটত্ব তার কারো সঙ্গে হয়নি, হবেও না, কারণ এ ব্যাপারে তার উৎসাহ কম।
অনুপম খুব অল্পবয়স্ক নয়। কিন্তু ধরনটার মধ্যে ভারিক্কি ভাব নেই একেবারেই। সামান্য একটু বিদ্রূপের ভাব সব সময়েই যেন মিশে থাকে তার ব্যবহারে। যেন সে সবাইকার ব্যাপারেই খুব মজা পাচ্ছে।
—‘একলা একলা হঠাৎ স্কাইরুমে?’
বন্দনা বলল—‘আচ্ছা, আমার প্রশ্নটার জবাব দিন আগে— একলা নয়ই বা কেন? আপনি তো একলাই এসেছেন? আমিই বা না আসব কেন?’
অনুপম টানটান হয়ে বসে বলল—‘আমি তা হলে ঠিকই ধরেছি।’
—‘কি ঠিক ধরেছেন?’
—‘আপনি একজন রেবেল, বিদ্রোহিণী।’
বন্দনা মৃদু হেসে বলল— ‘সামান্য এই কারণে কি কেউ বিদ্রোহিণী নাম পেতে পারে?’
—‘সে যাই হোক, আমি নিজেও খুব আনকনভেনশন্যাল।’
এবার সত্যি সত্যিই স্টুয়ার্ড এসে দাঁড়িয়েছে। বন্দনা কিছু বলতে যেতেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অনুপম সোম খাবারের অর্ডার দিয়ে দিল। বন্দনা জোরাজুরি করতে পারে না। বলল— ‘আপনি একটুও আনকনভেনশন্যাল নন।’
—‘না, না। এ ব্যাপারে আমি একদম কনভেনশন্যাল। অন্যান্য ব্যাপারে সৃষ্টিছাড়া। যেমন ধরুন আমি থাকি সম্পূর্ণ একা। আমার মা, ভাই, বোন সবাই থাকেন চেতলায়। আমি রাসেল স্ট্রিটে ফ্ল্যাট নিয়ে একা থাকি। কেন জানেন?’ বন্দনা মাথা নাড়ল। সে জানে না। জানতে চায়ও না খুব। কিন্তু সসামের বলার আগ্রহ খুব বেশি।
সোম বলল—‘আমি বিশ্বাস করি প্রাপ্তবয়স্ক, ম্যাচিওর যুবকের একা থাকাই উচিত। অবশ্য আমার মা মাঝে মাঝে এসে থাকেন কিন্তু টিকতে পারেন না।’
—‘কেন?’
—‘মা বলেন—আমার আট বাই দশ ঘর আর চার ফুটের বারান্দায় নাকি তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ দেখুন মায়ের চেতলার বাড়িতে গেলে, বিরাট উঠোন, বাগান, উঁচু সিলিংওয়ালা ঘর, দালানের মধ্যেই আমার কেমন স্টাফি লাগে।’
—‘আপনি কি কোনও সময়ে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন?’ বন্দনা বলল।
—‘কোনও সময়ে মানে? অল মাই লাইফ। স্কুলে, কলেজে, বরাবর। আপনি খুব ধরেছেন তো!’
বন্দনা বলল—‘হস্টেলে থাকলে ওই রকম একটু…’
—‘স্বার্থপর হয়ে যায় লোকে, না!’
—‘তা ঠিক নয়।’
—‘আরে আমার মা তো তাই বলে থাকেন, আমার বাড়ির ওপর টান নেই, আমি—মা একটা কথা ব্যবহার করেন ‘একালষেঁড়ে।’ আসলে কি জানেন আমি খুব আত্মনির্ভর। বাড়িতে গিয়ে যদি দেখি আমার ছোট ভাই মা-কে বলছে ‘এক গ্লাস জল দাও তো’, বা বোনকে বলছে— ‘আমার শার্টটা কেচে দিস।’ কিংবা সন্ধে পার হলেই দেখি মা বোনকে নিয়ে ঘরে ঘরে বিছানা করছে, মশারি খাটাচ্ছে, আমার, ভাইয়ের সবার, তখন সত্যিই আমার কেমন দমবন্ধ হয়ে আসে।’
—‘এখানে আপনি সব নিজের হাতে করেন?’
—‘এভরিথিং। একজন হেল্পিং হ্যান্ড আছে, কিন্তু সে আমার ব্যক্তিগত কাজ কিছু করে না।’
—‘বাঃ, বন্দনা খুশির সুরে বলল, তারপর বলল নিশ্চয়ই রেস্টুরেন্ট থেকেই রাতের খাওয়া সেরে যাবেন।’
—‘একজ্যাক্টলি।’
—‘এটাও আপনার সেলফ হেল্পের অঙ্গ তো?’
খুব খানিকটা হাসল অনুপম সোম।
—‘ভালো বলেছেন।’
বন্দনার কফি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বলল— ‘এবার আমি উঠি আপনি বসুন। ডিনার সারবেন তো?’
অনুপম সোম বলল—‘আপনারই বা সারতে আপত্তি কি?’
—‘তা হয় না, আমি সামান্য একটু রিল্যাক্স করতে এসেছিলুম। বাড়িতে ফেরার একটা সময় আছে আমার, সেটা পার হয়ে গেলে ছেলে খুব অস্থির হবে।’
—‘ছেলে? কত বড় ছেলে আপনার?’
—‘বছর পনের হবে।’
—‘আর কে আছেন বাড়িতে?’ অনুপম যেমন নিজের বৃত্তান্তও গলগল করে বলে যেতে পারে, অন্যের ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশেও তার কোনও দ্বিধা নেই।
—‘আর কে থাকবেন?’
—‘কিছু মনে করবেন না। আমার কৌতূহল খারাপ লাগলে না হয় না-ই উত্তর দিলেন। আপনার ছেলের পিতৃকুলের বা মাতৃকুলের কেউ, মানে আপনি কোথায় থাকেন? পিত্রালয়ে না শ্বশুরালয়ে?’
বন্দনা একটু বিরক্ত হচ্ছিল, বলল—‘আমি ছেলেকে নিয়ে একাই থাকি।’
—‘ইস্’। অনুপম সোম খুব অপরাধীর মতো উঠে দাঁড়াল। ‘চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।’
—‘আপনাকে পৌঁছতে হবে না। এখন বাস-ট্রামের ভিড় কমে গেছে, আমি অনায়াসেই চলে যেতে পারব।’
—‘তা হয় না, মিসেস ভট্টাচারিয়া। আমার সঙ্গে গাড়ি রয়েছে। এভাবে আপনাকে ছেড়ে দিতে আমি মোটেই রাজি নই।’
—‘আপনার তো খাওয়ার কথা ছিল।’
—‘ওটা কোনও সমস্যা নয় মিসেস ভট্টাচারিয়া। বলছিলাম না আমি খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট! আই ক্যান ফিক্স মাইসেলফ এ স্যান্ডউইচ। ইচ্ছে হলে খিচুড়ি আর ওমলেট বানিয়ে নিতে পারি। ওসব আমার কাছে কিছুই না। আপনি ভাববেন না। চলুন।’
বন্দনা কোনও ব্যাপারে বেশি জোরাজুরি করতে পারে না। অনুপম গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিলে সে উঠে বসল। হরিশ মুখার্জি রোডে বাঁক নিয়ে সোম বলল—‘আপনার পুত্রের সঙ্গে আলাপ করে আসব।’
—‘বেশ তো।’
বন্দনার মনে হল, সেটাই ভালো। ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে তাকে দরজার কাছে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে সেটা কোনরকমেই ভালো দেখাবে না। গোটা পাড়ায় একমাত্র চাকুরে মেয়ে সে-ই। কারো সঙ্গে বিশেষ মেলামেশাও নেই। কি দরকার লোকের মুখে কথা জুগিয়ে।
রূপের সঙ্গে দারুণ আলাপ জমাল অনুপম। দেখা গেল সে ফটোগ্রাফি, ক্রিকেট, টেনিস এবং ছবি-আঁকা সম্পর্কেও কিছু জানে। রূপের ছবিগুলো দেখল একটার পর একটা। বলল—‘তোমার ধরনটা চাইনিজ। তুমি ইমপ্রেশনিজমের দিকে যেও না। ডেকোরেটিভ আর্ট তোমার হাতে ভীষণ ভালো আসবে। মিসেস ভট্টাচারিয়া, আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ দারুণ উজ্জ্বল।’
রূপের মুখ জ্বলজ্বল করছে। অল্প অল্প নরম গোঁফ গজিয়েছে ছেলের। চোখে নবীন চশমা। বন্দনার মনটা হাল্কা লাগল। বলল, ‘যদিও জানি, আপনি একদম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তবু আজ আপনার রান্না যখন করেই ফেলেছি, ব্রত ভেঙে খেয়ে যান।’
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সোম। খুব অপ্রস্তুত। ‘ইস্ নটা বাজছে, খেয়াল করিনি। আমি মোটেই খেয়ে যাব না।’
বন্দনা বলল—‘আপনাকে অত কিন্তু-কিন্তু করতে হবে না, আমি টেবিলে খাবার দিয়েছি। আসুন। রূপু আয়।’
রূপ বলল—‘আসুন কাকু। আপনি বুঝি নিজে রান্না করে খান?’
তিনজনে খেতে খেতে অনুপম খুব খুশি হয়ে বলল—‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট একশবার। তবে মাঝে মাঝে এরকম হয়ে গেলে মন্দ লাগে না, কি বলো অভিরূপ?’
যেন অভিরূপের সঙ্গে তার আজন্মকাল চেনা। বাইরে থেকে দেখতে খুব কেতাদুরস্ত, উন্নাসিক মনে হলেও আসলে মানুষটি খুব ঘরোয়া এবং যতই যা-ই বলুক, এত বকবক করা দেখে মনে হয় ও একলা থাকে কি করে? রূপ অনেকদিন কারো সঙ্গে আলাপ করে এত খুশি হয়নি।
অধ্যায় ২০
—‘এই যে ভাই শুনছেন? এই যে আপনাকেই বলছি।’
বন্দনা ট্রামের জন্য দাঁড়িয়েছিল। শেডের নিচে প্রচণ্ড ভিড়। পেছন থেকে ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল। ভিড়ের কাঁধের মধ্যে দিয়ে চেনা-চেনা মুখ দেখা যাচ্ছে। তাদের অফিসেরই দু’জন মহিলা। একজনের বন্দনার কাছাকাছি বয়স হবে ডেসপ্যাচে আছেন, নাম খুব সম্ভব অণিমা হালদার। অন্যজন বন্দনার থেকে ছোট, সবে এসেছে, নামটা বন্দনা জানে না। অণিমা হালদার বললেন—‘আর ক’দিন পরই আপনি কার-লিফট পেয়ে যাচ্ছেন, জানেন তো? আপনার বসের সাথে সাথে আপনার পদোন্নতি হচ্ছে।’ বন্দনা জানে না এ বিষয়ে কিছুই। তার চোখে বিস্ময়ের ভাব দেখে অণিমা হালদার একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করলেন। আশপাশের লোকেরা কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। কেন যে এঁরা কথাবার্তায় আব্রু মানেন না। সে আস্তে আস্তে পেছন ফিরে ভিড় থেকে বেরিয়ে এল।
অণিমা হালদার তার হাতটা খপ করে ধরে বললেন—‘আর আপনার নাগাল পাচ্ছি না, একটু আলাপ করে নিই।’
বন্দনা হেসে বলল ‘বেশ তো। সে তো খুব ভালো কথা!’ চারদিকে গিসগিস করছে মানুষের ভিড়। উদ্ভ্রান্ত মুখ বেশির ভাগই। বাড়ি ফেরার তাড়ায়।
অণিমা বললেন—‘সত্যিই ভালো কথা তো! আপনি মেয়েদের সাথে মেশেন তো?’
—‘তার মানে?’
অন্য মেয়েটি বলল—‘কি যে বলেন অণিমাদি। বন্দনাদি আপনার সঙ্গে আমাদের অনেকদিন থেকে আলাপ করবার ইচ্ছে। কিন্তু আপনি পিকনিকে আসবেন না, অ্যানুয়াল ফেট-এ যোগ দেবেন না, খালি মুখ নিচু করে ঘোষাল সাহেবের নোট নেবেন। কি করে আলাপ করব?’
অণিমা হালদার বললেন—‘আমাদের প্রথম প্রথম ধারণা ছিল, কিছু মনে করবেন না ভাই আপনি সাহেবের স্ত্রী, সেইজন্যে আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের সাথে মিশবেন না। আমি একটু ঠোঁট কাটা ভাই, মনের কথা পেটে থাকে না।’
বন্দনা বলল—‘ছি ছি এসব কি ভাবছেন? আমি নিজেও তো চুনোপুঁটিই।’
অণিমা বললেন, ‘আমাদের স্ট্যাটাস এক হলে কি হবে, স্বামীদের স্ট্যাটাস দিয়েই এখনও মেয়েদের স্ট্যাটাস ঠিক হয়। আমার স্বামীও কেরানি, আপনার স্বামী ছিলেন অফিসার। কি রে নন্দিতা ঠিক বলিনি?’
—‘আপনি যা বলছেন বলেন না, আমাকে আবার সাক্ষী মানছেন কেন?’ অন্য মেয়েটি বলল।
অণিমা হালদার বললেন—‘বেশ তো তা হলে কেন মেশেন না আমাদের সাথে বলুন।’
বন্দনা ভিড়ের থেকে আরও খানিকটা সরে গিয়ে বলল—‘কোনও কারণ নেই, বিশ্বাস করুন, হয়ে ওঠেনি।’
—‘অনুপম সোমের বেলায় তা হলে হয়ে ওঠে কি করে? সে অফিসার বলে? না পুরুষ বলে?’
বন্দনার কান ঝাঁঝাঁ করছে। ভদ্রমহিলার মুখের কোনও আগল নেই। সে গম্ভীর হয়ে এবার বলল—‘যা বলেন!’
নন্দিতা বলল—‘অনিমাদি, চুপ করেন না। বন্দনাদি, আজ আমি আপনার সাথে আলাপ করবই। আমার বাসা খুব কাছে। বউবাজার, আরপুলি লেন। তিনজনায় যাই, আধঘণ্টার মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেব।’
—‘তখন ফিরব কি করে ট্রাম-বাসের অবস্থা তো দেখছ!’
—‘আমি নিজে আপনাকে সাথে করে ফাঁকা বাসে তুলে দেব।’
বন্দনা বলল— ‘বাড়িতে ভাববে, অন্য দিন হবে।’
অণিমা বললেন—‘কে ভাববে? শাশুড়ি না মা?’
বন্দনা বলল— ‘ছেলে।’
—‘ছেলে ভাববে? ছেলেরা ভাবে মায়েদের কথা? নিজেদের বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা সিনেমা-থিয়েটার এই নিয়েই তো মত্ত। বাসার কথা, মায়ের কথা ওদের মনে থাকে? অবশ্য আপনার ছেলে বোধহয় এখনও অত বড় হয়নি!’
বন্দনা নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বলল— ‘ভবানীপুরের ট্রাম আসছে। উঠে পড়ি। পরে দেখা হবে।’
ময়দানের সবুজের মধ্যে দিয়ে ট্রাম চলে। বেশ ভিড়। পাখার কাছাকাছি যেতে না পারলেও জানলা ঘেঁষে দাঁড়াতে পেরেছে সে। আর একটা দুটো দেখলে বসা যেত। অণিমা হালদারের সঙ্গে এর চেয়ে বেশি কথা বলতে বাধ্য হবার ভয়ে এখনও বুক ঢিপ ঢিপ করছে। তার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কোনও কোনও পিসি-মাসি শ্রেণীর মহিলা ছিলেন এই জাতীয়। বাসি বিয়ের দিন একজন যেমন মন্তব্য করলেন—‘এ যে তালপাতার সেপাই গো। রংটা কটা বটে। তবে কটা না ফ্যাকাশে বলতে পারব না বাপু।’ কিন্তু তাঁদেরও ভব্যতা না থাক একটা মমতা ছিল ধরনধারনে। যিনি তালপাতার সেপাই বলে খুঁত কাড়লেন তিনিই আবার থালাভর্তি খাবারদাবার এনে আদর করে মুখের সামনে ধরলেন—‘একবারে না খেতে পারো, একটু একটু করে খাও মা। নইলে কি সংসারের ধকল সয়!’ কিন্তু এই মহিলা শিক্ষিত, নিশ্চয়ই শিক্ষিত, অথচ ভীষণ অমার্জিত। কথাবার্তার মধ্যে মেয়েলি গ্রাম্যতা দোষ আর পুরুষালি সপ্রতিভতার এমন একটা মিলন হয়েছে যে মিলন একেবারেই সুখের নয়। কাকা ঠিকই বলেছিলেন মেয়েদের পক্ষে স্কুলের চাকরিটাই ভালো। বাড়ির কাছে সেই স্কুলটির কথা মনে করলে এখনও বন্দনার মন কেমন করে। বিশেষ করে ছাত্রীদের কথা ভাবলে। মধুমিতা, আল্পনা, শর্মিষ্ঠা, কি যেন সেই মেয়েটির নাম যে তাকে নিয়মিত ফুল উপহার দিত। চম্পা! পদ্ম! ছাত্রীদের সঙ্গে তার খুব সুন্দর একটা সখ্য জন্মেছিল। সহকর্মিণীদের সঙ্গে ততটা হয়নি। স্টাফরুমে সব সময়ে দলবাজির একটা চোরা স্রোত কাজ করত। নীলিমাদির সঙ্গে গল্প করলে ঊষাদির মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। ঊষাদির সঙ্গে বেশি কথা বললে প্রতিমাদি স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে যেতেন। বেলা, তপতী, রচনা, মায়া তখন তার সমবয়সী ছিল, নিজেদের গ্রুপের মধ্যে আর কাউকে ঢুকতে দিত না। এগুলোর জন্য তার বেশ সুবিধেই হয়েছিল, আলগা ওপর-ওপর মেলামেশা করলেই চলে যেত। কারুর বাড়ি যেতে হত না, কাউকে বাড়িতে ডাকতেও হত না। অবশ্য মাত্রই দু বছর সে ছিল স্কুলে। আর বেশিদিন থাকলে কি হত বলা যায় না।
অন্যদের দিক থেকে দেখলে তার এই মেলামেশার অনিচ্ছাটা উন্নাসিকতা বলে মনে হতেই পারে। বিশেষ করে অন্য মেয়েদের চোখে। উন্নাসিকতা বলতে ঠিক যা বোঝায় এই বিষণ্ণ গাম্ভীর্য, একা-একা থাকা এর সঙ্গে তার খানিকটা তফাত আছে। সেটা যে ওদের চোখে পড়ে না তা নয়, কিন্তু শব্দ ভাণ্ডার বড় সীমাবদ্ধ। ওই শব্দটার বাইরে আর কোনও শব্দ ওদের অভিধানে নেই। বন্দনা বোঝে তার প্রকৃতি এমনিতেই অন্তর্মুখী। মানুষ তার ভালো লাগে। জীবনস্রোত বয়ে চলেছে, সে নিজেও তার সঙ্গে চলেছে এই চিন্তায় তার ভীষণ স্বস্তি। কিন্তু কোনও ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হলে তার প্রতি তাকে খুব বেশি আকৃষ্ট হতে হবে। তার ভালোবাসায় শনির দৃষ্টি আছে। মা মারা গেলেন অল্প বয়সে। দশ বছর মোটে বয়স। বাড়ির আবহাওয়া বদলে গেল। বাবা এমনিতেই তখন উদাসীন, নিস্পৃহ, কাকা যতই মায়ের মতো করে যত্ন করতে চান, তিনি কি পারেন? সেই থেকে বন্দনা গৃহমুখী হয়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে বাবা-কাকার মুখ দেখবার তাগিদে একের পর এক বন্ধু হারাতে লাগল। কেই বা কার জন্যে বসে থাকে? সমবেদনা থেকে যায়। কিন্তু কে আর ওই বয়সে অপরের দুঃখের ভাগ নেবার মতো দরদী হয়! এই সব কারণেই কলেজে পড়ার সময়ে সে এতো কম কলেজে গেছে যে নন-কলেজিয়েট হয়ে গিয়েছিল। টাকাকড়ি দিয়ে আবার সে দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে হয়। তারপর তো ভট্টাচায্যি বাড়িতে বিয়েই হয়ে গেল। ওই কয়েক বছরই বন্দনার মানুষের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশার কাল। শিখছিল জিনিসটা। সম্পূর্ণ হবার আগেই দুম করে সব বদলে গেল। যদিবা কাকার কাছে এসে নিজেকে একটা জীবন্ত মানুষ বলে, একজনের অত্যন্ত প্রিয়জন বলে নিজেকে অনুভব করতে শুরু করেছিল, বিশ্বাসঘাতকের মতো কাকা চলে গেলেন। নিয়তি যেন বারবার তাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছে। অথচ এই সব সহকর্মিণী তাকে উন্নাসিক ভেবে নিচ্ছেন। উন্নাসিকও নয়। অণিমা হালদার সোজাসুজি বলবেন—ঠ্যাকারে। নাক-উঁচু।
এই রকম মনখারাপ করা বিকেলে বাড়ি ফিরে যার জন্য তাড়াতাড়ি ফিরে আসা তাকে দেখতে না পেলে কেমন লাগে? রূপ নেই। নিচের অবনীশবাবুর স্ত্রীর কাছে চাবি দিয়ে গেছে।
বন্দনা জিজ্ঞেস করল—‘কার সঙ্গে বেরোল?’
—‘কি জানি? বেশ কয়েকটি ছেলে এসেছিল। দুড়দাড় করে ওঠার নামার শব্দ পেলুম।’
—‘অনুপ, সন্দীপ, ওরা?’
‘ওরা কেউ নয়। আমি ভালো করে দেখিনি যদিও।’
বন্দনা বিরক্ত হল। দু-চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। তারা ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে রূপ এরকম বাইরে যাক, সে তা চায় না। কাকা চলে যাবার পর থেকে কিভাবে দু’হাতে আগলে ছেলেকে মানুষ করতে হচ্ছে সেই জানে। আবার আগলানো হচ্ছে সেটা বুঝতে দিলে হবে না। ঢালাও স্বাধীনতার আবহাওয়া, খালি কতকগুলো শৃঙ্খলা তুমি মেনে চলে। এইরকম ভাষায় অনুবাদ করা যায় বন্দনার ছেলে মানুষ করার দর্শনটা। তার ধারণা এতেই কাজ হবে। কিন্তু পিতৃহীন ছেলের ওপর বন্ধুদের প্রভাবটা খুব বেশি। যত বড় হয়, তত বেশি। সেটা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা দিয়ে বন্দনা বুঝতে পারে। বাড়িতে এই বাড়ের সময়টা একজন পুরুষের সঙ্গের অভাব যে কী দারুণ অভাব! পিতা বা পিতৃকল্প কেউ। তাঁর জোর, তাঁর চরিত্রের আদর্শ, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ অলক্ষ্যে কাজ করতে থাকে একটি কিশোরের মানসিক বাড়বৃদ্ধির পেছনে। বাড়িতে পায় না। তাই বাইরে খোঁজে। বন্ধু, বন্ধুর বাবা, মাস্টারমশাই। স্কুলের একজন মাস্টারমশাই তো রূপকে রাজনীতিতে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন আর কি! কোনও দরকার নেই, তবু ওই স্যারের কাছে ওর কোচিং নিতে যাওয়া চাই-ই। বারো-তেরো বছরের ছেলের মুখে তখন শোষক-শোষিত, শ্রেণীশত্রু, বুর্জোয়া, সংগ্রাম, চোখে ঘৃণার আগুন জ্বলছে।
ভীষণ ভয় ধরে গিয়েছিল তার। তার বাবার বংশের কত পুরুষ ধরে চব্বিশ পরগনায় বাস সে জানে না। ভবানীপুরের বাড়ি ঠাকুর্দার কাছ থেকে বাবা-কাকা পেয়েছিলেন। ধনী না-হলেও, অভাবের তাড়না কি জিনিস তারা জানেনি। যুদ্ধের বাজারে তাদের নিচের ভাঁড়ার ঘর ভর্তি থাকত চালের বস্তায়। ন্যায্য দামে সেই চাল পাড়া প্রতিবেশীদের দিয়ে বাবা-মা কতজনের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের সময়েও মাকে দেখেছে দু’হাতে ভিখারিদের সাহায্য করতে। সে সময়ে তাদের বাড়িতে ভাতের ফ্যান কখনও ফেলা হত না। কিন্তু শ্রমিক বা চাষী কোনও শ্রেণীর সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। পড়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু তাঁর আঁকা মাস্টারমশাইদের জীবনের ট্রাজেডি যতটা পরিচিত মনে হয়েছে, কুবের মাঝির গল্প ততটা হয়নি কোনদিনই। ‘জাগরী’ সে মোটামুটি ধরতে পারে, কিন্তু ‘ঢোঁড়াই-চরিত-মানস’ কয়েকবার চেষ্টা করে রেখে দিয়েছে। বন্দনার সাহিত্য-জগতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আছেন আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, দুই বিভূতিভূষণ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘তিথিডোর’ আর ছোট গল্পের বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের পরে কিছু কিছু প্রেমেন্দ্র মিত্র আর জীবনানন্দ ছাড়া সে মোটে কবিতাই পড়েনি। বাবা ছিলেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভক্ত। কাকা তাছাড়াও রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, ডি এল রায়, ভালোবাসতেন খুব। রবীন্দ্রসঙ্গীতের খুব চল ছিল না বাড়িতে। উভয়েই রাজনীতির দিক থেকে শ্যামাপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন দাশের ভক্ত। কতটা তাঁদের মতবাদের জন্য আর কতটা তাঁদের চরিত্রগুণে বলা শক্ত।
বন্দনার শ্বশুরবাড়িতে আবার আবহাওয়া ছিল একদম অন্যরকম। ওঁরা বাংলা খবরের কাগজ ছাড়া পড়তেন না। শনিবার রেসের খবরের জন্য বিশেষ ইংরেজি কাগজ দরকার হত। ছেলেমেয়েরা রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব রাখত না। নেহরু যা বলবেন, সারা বাড়ি মোটামুটি দেশ ও বিদেশ সম্পর্কে সেটাই শেষ কথা বলে মেনে নিত। সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গেও তাঁদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ফৈয়জ খাঁ সম্পর্কে তার শ্বশুর একবার খুব বিশ্রী মন্তব্য করায় তার বাবা ও-বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গান-বাজনার জগৎটা ওঁদের কাছে ছিল অচ্ছুৎ। মেয়েদের আমোদ-প্রমোদ বলতে মাঝে মধ্যে সিনেমা যাওয়া, রেডিওর অনুরোধের আসর শোনা, বেড়াতে যাওয়া মানে সাঁওতাল পরগনা। সপরিবারে, বিরাট লটবহর নিয়ে।
অভিমন্যু মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। তার নিজের বিষয় নিয়ে সে প্রচুর পড়াশোনা করত। সাহিত্য-শিল্প- সঙ্গীত এসবের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কম। শ্বশুরমশাই বলতেন, ‘নবেল? ও তো মেয়েরা পড়ে। পড়বেই। শরৎবাবু, রবিবাবু। তুমি আমি ঠেকাতে পারব না।’
অভিমন্যু বলত—‘গল্প কাহিনী উপন্যাসের মধ্যে বন্দনা আমি রস পাই না। জীবনে যা রোজ ঘটছে সেগুলো রেকর্ড করে কি লাভ? একটা পুরো উপন্যাসের জিস্ট কি বলো তো? একজন কি দু’জন জন্মালো, বড় হল, দুজনে প্রেম হল, যে কোনও কারণে মাঝখানটায় গণ্ডগোল। শেষকালে মিলন হল অথবা হল না। এর মধ্যে কে থলে হাতে বাজার করতে গেল, কারা রকে বসে আড্ডা দিল, কোন গিন্নি কার সঙ্গে কি ভাষায় ঝগড়া করল। এসব তো রোজ দেখছি, এ আবার আলাদা করে লেখবার জিনিস নাকি? আর কবিতা? ওরে ব্বাবা, হ্যাঁ রে কলি তুই তো বাংলা-টাংলা পড়িস—
পোড়ে মৌচাক আধিদৈবিক অলাতে
নৈমিত্তিক সব্যসাচীর শলাতে
অপসৃত হয় গুপ্তির জঞ্জাল। মানে কি রে এর?’
কলি বলত, ‘তুমি স্বয়ং কবিকে জিজ্ঞেস করে এস, আমার বিদ্যেতে কুলোবে না।’
বন্দনা বলত—‘তুমি একটু বেরসিক যাই বলো।’
—‘কেন আমি কি হেমন্ত মুখুজ্জের গান ভালোবাসি না! তোমাকে কি আমি সদারঙ্গ মিউজিক কনফারেন্সে নিয়ে যাইনি?’
বালক ছেলের কথাবার্তা শুনে, চাউনি দেখে বন্দনার ভয় ধরে গিয়েছিল। কাকা সবে মারা গেছেন। কেউ নেই যে পরামর্শ করবে। কাকার সঙ্গে যেন পরামর্শ করারও দরকার পড়ত না। তিনি জানতেন এবং বুঝতেন। সব কিছু তাঁর মমতাময় হৃদয় দিয়ে। দুই বাহুর শক্তি দিয়ে ঠিক করে দিতেন। ঈশ্বরের মতন। বন্দনার জগতের ঈশ্বর। ছোট মাপের হতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বর যদি হতেই হয় তবে এইরকম। অন্য কোনরকম ঈশ্বরের অস্তিত্বে ভরসা নেই তার। সে সময়ে অফিস থেকে কলিকে ফোন করেছিল।
—‘কি ব্যাপার বউমণি?’
—‘অনেকদিন আসিসনি, কলি।’
—‘সত্যি? আমার কথা তোমার মনে পড়ে?’
—‘মনে পড়ার সুযোগ দিস কোথায়? তার আগেই তো হই হই করে এসে পড়িস।’
—‘এবার আর আসছি না। এই তো দ্যাখো না, দু-সপ্তাহ হল যাইনি।’
—‘তাই তো ভাবছি।’
—‘আজই যাব বউমণি!’
কলি বউমণিকে না দেখে বেশিদিন থাকতে পারে না। কিশোরী বয়সের মুগ্ধ চোখ দিয়ে দেখা প্রথম বউদি। বড় আদরের, বড় ভালোবাসার। বয়সে বড়, বোঝে বেশি, জানে বেশি, কিন্তু বন্ধু। দিদির মতো। কলির মনের মধ্যে বউমণির জায়গা পাকা। তার মনের মধ্যে একটা ভীষণ অনুশোচনাবোধও কাজ করে যায়। বউমণি যখন বাড়ি ছাড়ল, তখন সে প্রাপ্তবয়স্ক, বিবাহিত। অন্যায়ের প্রতিবাদ অবশ্য করেছিল, কিন্তু আর কিছুই পারেনি। একেক সময়ে মনে হয় পঁয়তাল্লিশ নম্বরের জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে বউমণির ভালোই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। সঞ্জয়েরও তাই মত। সঞ্জয়ের বেশির ভাগ মতই অবশ্য কলির মত। সে যাই হোক, সঞ্জয় বলে, ‘ওরে বাবা তোমাদের পঁয়তাল্লিশ নম্বরে জামাইষষ্ঠী খেতে যেতে হবে ভাবলেও আমার হৃৎকম্প হয়। আমরা দুই কাকপক্ষধর নওলকিশোর খেতে বসেছি দু-পাশ থেকে দুই জাঁদরেল শাশুড়ি হাওয়া করছেন, পাখা চলছে বনবন করে, তবু দুগ্গাঠাকুরের মতো হাওয়া খাচ্ছি। জামাইদের যথেষ্ট আদর হবে না নইলে। আর দু দিক থেকে দুই শ্বশুর শ্যেন দৃষ্টিতে দেখছেন জামাইদের জন্যে যে দমকা খরচাটা হয়ে গেল সেটার ঠিকঠাক সদ্গতি হচ্ছে কি না। উরি ব্বাপ্।’
কলি সঞ্জয় দুজনেই এসে গেল সন্ধেবেলা। বন্দনা উৎকণ্ঠিত মুখে জানাল রূপের সমস্যার কথা। সঞ্জয় মুখ গম্ভীর করে বলল—‘স্কুল পাল্টানো ছাড়া কোনও উপায় নেই বউদি।’
—‘সে কি? এতদিনের স্কুল! সেই ছোট্ট থেকে পড়ছে!’
—‘এই বেলা পাল্টে দিন। পাল্টালেও সুবিধে হবে কি না জানি না অবশ্য। আপনি ছাড়লেও কি কমলি ছোড়বে?’
কলি বলল—‘স্কুল ছাড়ানো কি সম্ভব? ও শুনবে কেন? এক কাজ করো না বউমণি, ও অত ভালো আঁকে একজন আঁকা শেখাবার মাস্টারমশাই রেখে দাও। এনগেজ্ড্ থাকবে, পলিটিকসের ভূত ঘাড় থেকে নেমে যাবে।’
সুদীপ্ত সরকারের সেই সূত্রে আগমন এ বাড়িতে। সত্যিই কলির বুদ্ধি আছে। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ছবি আঁকতে আঁকতে কবে রূপ শ্রেণী সংগ্রামের কথা ভুলে গেছে।
শূন্য বাড়িতে ঢুকতে কিরকম বুক কেঁপে ওঠে। এতদিন একরকম একলা জীবনযাপন করছে, কলিদের বাদ দিলে সঙ্গীহীনই। চাকরি করছে, জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত। একা হাতে ছেলেকে বড় করে তুলছে, তা সত্ত্বেও তার এই ধরনের ব্যক্তিত্বহীন মেয়েলিপনা গেল না। কারুর নির্মম বা অভব্য কথার জবাব দিতে পারে না, সহজে ভেঙে পড়ে, সব সময়েই আশা করতে থাকে বাড়িতে ফিরে কাউকে দেখবে। না দেখলে বুক ভেঙে যায়।
এরকম সাধারণত হয় না। এলেই রূপকে দেখতে পায়। একা কিম্বা বন্ধুদের সঙ্গে। সপ্তাহে দু’দিন সুদীপ্তবাবু আসেন। সোজা অফিস ফেরত চলে আসেন। রূপ যখন বাড়ি ফেরে তখন বন্দনার সবে ধন নীলমণি অন্নপূর্ণাটি থাকেন। সেই রূপকে খেতে দিয়ে বন্দনার চা ফ্লাস্কে রেখে দেয়। রূপকেও বেশিক্ষণ একলা থাকতে হয় না। আজ অনেকদিন পর এরকম শূন্য ঘর। শূন্য ঘর দেখলেই বুক হু-হু করে। দালানে টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা, পাশে চায়ের ফ্লাস্ক। মৃদু আলো জ্বলছে। পুরনো দিনের লাল সিমেন্টের চকচকে মেঝে, তার ওপর যেন কয়েক জোড়া জুতোর দাগ। ওরা তো কিছু মানবে না, শুনবেও না। হুড়মুড় করে এসেছে, চলে গেছে বোঝাই যাচ্ছে। বন্দনার কেমন কান্না পেল। সে পর্দা সরিয়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকল। তার একার খাট, একার টেবিল, আলমারিটা বিরাট। বর্মা টিকের আলমারি মায়ের। ওপর দিকে কারুকার্য করা। দু পাল্লাতেই আয়না বসানো। দেয়ালে ক্যালেন্ডার, এরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন দুর্গ নিয়ে ক্যালেন্ডার করেছে। এটাতে রুক্ষসুক্ষ সিংহগড় দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমের দেয়াল জুড়ে রূপের আঁকা ছবি সাঁওতাল পরগনায় বসন্ত এসেছে। যদিও ছবিতে শিমুল পলাশ তবু সুদীপ্তবাবু ছবির নাম দিয়েছেন ‘মউলের বাস।’ দু ফুট বাই তিন ফুট চটের ওপর তেল রঙে আঁকা এই ছবিতে ফিনিশিং টাচ আছে সুদীপ্ত সরকারের, প্রাইজ পাওয়া ছবি। টেবিলের ওপর দেয়ালে অভিমন্যু-বন্দনার বিয়ের অব্যবহিত পরে তোলা ছবি। কিছু বই টেবিলের ওপর গোছানো রয়েছে। আর কিছু নেই। মাঝখানের দরজা খুলে পাশে রূপের ঘরে ঢুকল বন্দনা। কলির কথায় ছেলের ঘর আলাদা করে দিয়েছে। এটা আগে কাকার ঘর ছিল। বন্দনা ঘুরে ঘুরে দেখল, এ-ও কি রূপের একার ঘর? রূপেরও কি একা-একা লাগে তার মতো! অফিসের বাইরে সব সময়টাই তো সে মনে মনে রূপকে দিয়ে রেখেছে। কিন্তু মায়ের সেই সঙ্গ কি ছেলের সব সময় কাজে লাগে? এ ঘরের দেয়ালে রূপের বাবার একলার ছবি। এটা আগে বন্দনার ঘরে থাকত, ছেলের ঘর আলাদা করে দেবার পর তার বাবার একটা ছবি ঘরে থাকা দরকার মনে করেছিল, তাই এটা এ ঘরে। এক সময়ে এ ছবিতে সব সময়ে টাটকা ফুলের মালা দেওয়া থাকত, আজকাল আর নিত্য হয়ে ওঠে না। আরেক দিককার দেয়ালে সুদীপ্তবাবুর সেই বৃদ্ধার মুখ। টেবিলে ছড়ানো বই, নকশা, অন্য দেয়ালগুলোতে রূপের নিজের আঁকা নানান ছবি। জলরঙের স্টীল লাইফ। জানলা থেকে দেখা গলির দৃশ্য, চারকোণে চারটে সেলোটেপ দিয়ে এঁটে রাখে ও, কিছুদিন পরে নতুন ছবি আঁকে তখন আগেরগুলো টান মেরে ফেলে দেয়। কোনটা কোনটা বন্দনা যত্ন করে তুলে রেখে দেয়, কোনটা কলি আদর করে নিয়ে যায়, বলে ‘কোথা থেকে এ গুণ পেল বলো তো আমাদের বাড়ির ছেলে? কাশীনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ির ছেলে ল্যান্ডস্কেপ আঁকছে। যাই বলো বাবা ভাবা যায় না।’
বন্দনার ঘর যেমন খালি খালি, বর্ণহীন, এ ঘর তেমনি ভর্তি। দেয়াল বোঝাই, টেবিল বোঝাই, খাট বোঝাই। রঙচঙে ঘরখানা। না তেমন একাকিত্ব টের পেল না বন্দনা। রূপের জগৎ, জীবন এখনও অবধি পূর্ণ। সে কোনও অভাব টের পায় না। অন্তত তার মায়ের কাছে তাই মনে হল। যে সময়ে কাকা এই ঘরটাতে থাকতেন, এর সাজসজ্জা অন্যরকম ছিল। ঘরটাতে এলেই পুবের জানলার দিকে পেছন করে রাখা একটা অদৃশ্য আর্মচেয়ার দেখতে পায় বন্দনা। একটি কাঁচা পাকা চুলের মাথা তাতে বিকেলের আলো এসে পড়েছে। দু-টি মসৃণ পা, ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে পা দু-টিকে আয়নার মতো ঝকঝকে রাখতেন কাকা। আর্মচেয়ারের হাতলে পা দু-টি দুপুর বেলায় তোলা থাকত। দক্ষিণের দেয়ালে যেখানে এখন নিদন্ত বৃদ্ধার ছবি ঘটা করে দুলছে সেখানে ছিল একটা ছোট্ট বুক র্যাক, তাতে কাকার নিজস্ব পছন্দের বই থাকত। সে বুক র্যাকটা বই সমেত ওপাশের ঘরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আর্মচেয়ারটা বিক্রি হয়ে গেছে। কি হবে স্মৃতি জমিয়ে রেখে! সে ঠাকুর দেবতার ছবির সঙ্গে মৃত স্বামীর ছবি রাখত, ঠাকুরপুজোর ছল করে তাকেই ধূপ, দীপ, ফুল, ভোগ দিত বলে কাকা একদিন রাতে তাকে বড্ড বকেছিলেন। সেই থেকে বন্দনা ঠাকুরপুজোই বন্ধ করে দিয়েছে। সে তো সত্যিই আসলে কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, বা ভোলা গিরির পট পুজো করত না। অভিমন্যুর দৃপ্ত সুন্দর মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে থাকত। তাকেই মনে করত। যা কিছু দিত, তাকেই দিত। সকালবেলা জল-বাতাসা দেবার সময়ে কৌটোয় রাখা বড় ফেণী বাতাসা থেকে সাবধানে পিঁপড়ে বেছে দিত। সন্ধেবেলায় উৎকৃষ্ট সন্দেশ আনাত, এক এক দিন এক এক রকম। সে কি পটের অলীক-দর্শন পেচক-বাহন লক্ষ্মী ঠাকুরকে খাওয়ানোর জন্য? কক্ষনো না। তার এই স্মৃতিবিলাস কাকা ভালো চোখে দেখেননি। তাঁর কথা নিয়ে বন্দনা অনেকদিন অনেক রাত ক্রমাগত ভেবেছে। পুরোপুরি মানতে পারেনি, তবু মনে হয়েছে কাকা যা বলেছেন তার মধ্যে সত্যি আছে। সে মনে মনে অভিমন্যু-রূপ দেবতাকে মানস গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে বলেছে—‘তুমি যখন ছিলে, মানুষ ছিলে, চলে গেছ বলে তোমাকে আমি দেবতা বানিয়ে ফেলছিলুম, আর বানাব না। তোমার ছবি সামনে না নিয়েও যদি তোমাকে সহজে মনে রাখতে পারি, তোমার এক সময়ের থাকা এবং এখনকার না-থাকাকে যদি এই বিচিত্র জীবনের ছন্দে সুরে মিলিয়ে নিয়ে চলতে পারি তবেই আমার স্মরণ সত্যিকারের স্মরণ হবে। সেই ভালোবাসাই সত্যি ভালোবাসা। নয়ত সবটাই হয়ে উঠবে সংস্কার সন্মোহ। কাকা ঠিকই বলেছেন।’
তৃতীয় ঘরটা, যেটাতে এখন বাড়ির অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জিনিসগুলো আছে, সেই ঘরে এসে বন্দনা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। গলির আলোগুলো জ্বলে উঠেছে শুধু তাদের বাড়ির কাছটা একটা অন্ধকারের বৃত্ত। এখানকার আলোটাই গেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বন্দনার মনে হল তার ভীষণ শরীর খারাপ করছে। আর সে এই একলা জীবন বহন করতে পারছে না। একটা গোটা ছেলের ভার একদম একলা। মেয়ে হলে তবু তাকে চোখে চোখে রাখা যায়। আচ্ছা যেখানেই যাক, অন্তত বলে তো যাবে! নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে গিয়ে খেয়াল হল হাত পা মুখ কিছু ধোয়া হয়নি, মাথা ধরে গেছে, চা খাওয়া দরকার। পেটের মধ্যেটা খিদেয় কুলকুল করছে।
অফিসের জামা-কাপড় পাল্টে, হাত মুখ ধুয়ে চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে বসতেই হল, অন্ন বেশ যত্ন করে আলুর চপ ভেজে রেখে গেছে, সেগুলো এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও খিদের মুখে বেশ ভালোই লাগছে।
সাড়ে আটটা বেজে গেলে বন্দনার মনে হল সে সত্যিই এবার পাগল হয়ে যাবে। কিছু একটা এক্ষুনি করা দরকার। কাকে ফোন করা যায়? রূপের টেবিলের ডায়েরি থেকে ওর বন্ধু সুমনের ফোন নম্বরটা বার হল। পাশের বাড়ি থেকে ফোন করতে হল। সুমনের ফোন বেজেই যাচ্ছে, বেজেই যাচ্ছে। তখন কলিকে ফোন করল, করেই মনে হল কলিরা কাশ্মীরে বেড়াতে গেছে। তারপর মনে পড়ল আরেকটা নম্বর ২৯-২১৭৬, অনুপম সোমের স্বর।
—‘হ্যাল্লো সোম হিয়ার।’
—‘আমি বন্দনা ভট্টাচার্য।’
—‘কে? বন্দনা … মিসেস ভট্টাচার্য ফোন করছেন? কি সৌভাগ্য? কি ব্যাপার?’
সোমের উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে বন্দনা প্রায় বোজা গলায় বলল—‘অফিস থেকে ফিরে অবধি রূপকে দেখছি না, চাবি নিচে দিয়ে গেছে, নটা বাজছে, কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না।’
ওদিকে কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা, তারপর অনুপম বলল, ‘আমি আসছি, চিন্তা করবেন না।’
বন্দনা বাড়ি ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ির ফোনটা বাজল। জানলা দিয়ে ওবাড়ির মেয়েটি ডাকল—‘বন্দনাদি ও বন্দনাদি, রূপ ফোন করছে।’
—‘কোথায়? কোথা থেকে? কি ব্যাপার?’
—‘ওদের স্কুল-হস্টেলের সুপার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ মারা গেছেন। হস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে ও ওখানে রয়েছে ভাববেন না, ওর আসতে দেরি হবে। শ্মশানে যাবে।’
বন্দনা অবাক হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত খানিকটা। কিন্তু ভীষণ অবাক। বছর ষোল বয়স রূপের। সে ক্লাস টেনে পড়ে। জীবনের প্রথম দিকে তার নেশা ছিল ক্রিকেট। তারপরে কিছুদিন রাজনীতি। তারপর আপাতত আঁকা। একটার সঙ্গে আরেকটার কিছুমাত্র মিল নেই। কিন্তু রূপ হঠাৎ শ্মশানে যাবার মতো সিদ্ধান্ত একা-একা নিয়ে নেবে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করেই, এতো রাত অবধি না বলে কয়ে সে বাড়ির বাইরে, এতই কি বড় হয়ে গেল সে?
খুব লজ্জার সঙ্গে হঠাৎ বন্দনা লক্ষ করল সে খুব স্বার্থপর। একজন মানুষ, ছেলেদের হস্টেল-সুপার, তিনি মারা গেছেন হঠাৎ। তাঁর ছাত্র এই দুঃসময়ে তাঁর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, শেষকৃত্যের কর্তব্য করতে যাবে এবং সে ছেলে তারই ছেলে, এ তো খুব আশ্বাসের কথা, গর্বেরও কথা। কিন্তু সে মনে মনে চায় না ছেলে যাক। অন্য ছাত্ররা যাক না। তার রূপ যেন না যায়। যে ছেলের পাঁচ বছর বয়স হতে-না-হতেই বাবাকে পিণ্ডদান করতে হয়েছে সে কেন আবার এসব সংস্রবে যাচ্ছে। গায়ের ভেতরটা শিরশির করছে বন্দনার। রাতে খাওয়া হবে না, কোথায় না কোথায় খাবে, হয়ত কাঁধ দেবে, কাঁধে ব্যথা হবে, কখন ফিরবে, অসময়ে চান …। ছেলে সামাজিক কর্তব্য করছে, পূজনীয় মাস্টারমশাইয়ের জন্যে তার মনে সম্মান, শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ জন্ম নিয়েছে, যার টানে সে মাকে না জানিয়েই শ্মশানে চলেছে—এ তো একদিক থেকে আনন্দের কথা। অথচ বন্দনা ভাবছে হস্টেলের ছেলেগুলো বেছে বেছে ওকেই ডাকতে এল কেন?
অধ্যায় ২১
বাইরে গাড়ি দাঁড়াবার আওয়াজ হল। রূপুকে কি কেউ গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেল! বন্দনার বুকের ভেতরটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। যাক তাহলে আর দুশ্চিন্তায় রাত ভোর করতে হবে না। বন্দনা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিল।
অনুপম সোম বলল—‘ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। আমি দেখছি কি করা যায়।’
বন্দনা বলল—‘ইস্স্ আপনি শুধু শুধু কষ্ট করলেন। এইমাত্র ও পাশের বাড়িতে ফোন করেছিল, খবর পেয়েছি।’
—‘তাই নাকি? দেখছেন তো আপনারা অযথা ভাবেন!’ অনুপমের গলায় স্বস্তি।
—‘আপনার মুখ কিন্তু এখনও খুব শুকনো দেখাচ্ছে। কোথায় গেছে ও?’ ওপরে এসে বসতে বসতে বলল অনুপম।
বন্দনা বলল।
—‘তার মানে ও মিডনাইটের আগে ফিরছে না, নিশ্চয় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে। ততক্ষণ অব্দি আপনি কি হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবেন নাকি?’
বন্দনা হেসে বলল—‘অত কাতর দেখাচ্ছে আমাকে?’
—‘আরও বেশি দেখাচ্ছে। যদিও মুখে হাসি টানার চেষ্টা করছেন। আপনার প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু সফল হচ্ছেন না।’
অনুপম নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। জুতো মোজা খুলে চেয়ারের তলায় ঢুকিয়ে সে টান-টান হয়ে উঠে দাঁড়াল।
বলল—‘এমন অসময়ে ডাকলেন যে সবে রান্নাটা আরম্ভ করেছিলাম, চলে আসতে হল।’
বন্দনা খুব লজ্জিত হয়ে বলল—‘ছি, ছি, রূপের ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনাকে খবরটা দিয়ে দিতুম, আপনার এরকম হয়রানি হত না।’
অনুপম বলল—‘আপনার আক্কেল বলে কিচ্ছু নেই। কাজেই আমার তো হয়রানি হবেই। অফিস থেকে আজ ফাইল বয়ে আনতে হয়েছে একগাদা। প্রচুর কাজ। লিট্র্যালি নাওয়া-খাওয়ার সময় ছিল না। এরই মধ্যে বিচারবিবেচনাহীন আপনার ফোন।’ বলে অনুপম মিটিমিটি হাসতে লাগল।
বন্দনা বলল—‘যতই ঠাট্টা করুন, কথাগুলো সত্যিই বলছেন। আপনার ভীষণ খিদে পেয়েছে আমি বুঝতে পারছি। দাঁড়ান দেখি কি আছে, যা আছে তাই খেতে হবে কিন্তু।’
সোম বলল—‘যেমন কপাল!’
রান্নাঘরে মিটসেফে জলে বসানো আছে রাত্রের খাবার তার আর রূপের মতো। কৌটোতে রুটি। বার করে খুব অপ্রস্তুতে পড়ে গেল বন্দনা। সকালে অন্ন তেলাপিয়া মাছ এনেছিল তাই দিয়ে কি একটা তরকারি রেঁধে রেখেছে। তাদের মা আর ছেলের মতো। তাদের এই দিয়েই খাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু এ কি বাইরের লোককে দেওয়া যায়! বিশেষত অনুপম সোমের মতো সাহেব লোককে, যে স্কাইরুমে ডিনার সারে!
পেছনে ফিরতে সোমের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে গেল বন্দনার।
—‘কি দেখছেন?’ মজার গলায় বলল সোম—‘অতিথিকে এসব দেওয়া যায় কি না?’ বন্দনা খুব চমকে গিয়েছিল। অনুপম সোমের গতি খুব দ্রুত। তার সঙ্গে তাল রাখা শক্ত। ভাবলেশহীন প্রোফেশন্যাল মুখে ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাওয়া থেকে লাফিয়ে স্কাইরুমের আলাপ, সেখান থেকে আরেক লাফে নন্দন রোডের বাড়ি, রূপের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা যে প্রায়ই স্কুল ফেরত ওকে নিয়ে এখানে সেখানে খাওয়াচ্ছে। বাড়িতেও আসে প্রায়ই। রূপকে বলে—‘মাস্টার তুমি পড়াশোনা করো, ততক্ষণ তোমার মায়ের সঙ্গে একটু গল্প করি।’ আর আজ একটা বড় লাফে রান্নাঘর।
বন্দনা আস্তে আস্তে বলল—‘সত্যি তাই ভাবছিলুম। দেখুন তো, এসব কি আপনি খেতে পারবেন? আমি বরং একটু লুচি-টুচি করি।’
সোম বলল—‘কি মাছ? তেলাপিয়া? ওরে বাবা ওই আমেরিকান কই খেলে নির্ঘাত আমার অ্যালার্জি। দেখি তো আপনার ভাঁড়ারে আর কি আছে?’
বন্দনা বলল—‘ঠাট্টা করছেন? আপনি বাইরে গিয়ে বসুন, আমি দেখি কি করতে পারি।’
সোম বলল—‘উঃ কি ফাস্ করতে পারেন আপনারা মেয়েরা। শুনুন এসব আমি খেতে পারব না তা নয়, আমি জেলিফিশ পর্যন্ত খেতে পারি, অক্টোপাস-ভাজা কত খেয়েছি, ওটা কোনও কথা নয়, কিন্তু একটা প্রস্তাব করছি, সেটা যদি রাখেন, তো খাব, নইলে আজ আমার নো মীল ডে।’
—‘কি প্রস্তাব? আপনি আচ্ছা ছেলেমানুষ তো?’
অনুপমের চোখ খুশিতে চকচক করছে। বলল—‘আমার গাড়িতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার আছে। আপনি যখন ফোন করলেন, তখন আসলে আমি রাঁধছিলাম। কি মনে হল যা রেঁধেছি সব পুরে নিয়ে এসেছি। আপনি যদি খান তো আপনার তেলাপিয়া আর আমার সুইটসাওয়ার প্রন আমরা দুজনেই খাব। নানরুটি নিয়ে এসেছি কোয়ালিটি থেকে।’
বন্দনা বলল—‘প্লীজ অনুপমবাবু আমার ছেলে না খেয়ে আছে। আমি কি করে …’
—‘দেখুন মশাই আপনার ছেলে না খেয়ে নেই, শ্মশানযাত্রা আমরাও করেছি, ওরা খুব ভালো করে খেয়ে নিয়ে তবে বেরোবে। আপনার কোনও ভয় নেই। তাছাড়া অভিরূপের ভাগ আমরা রেখে দেব। আমি কিরকম রাঁধুনি একটু চেখেই দেখুন!’
খেতে খেতে বন্দনা বলল—‘এ কক্ষনো আপনি করেননি অনুপমবাবু।’
—‘কেন?’
—‘একেবারে রেস্তোরাঁর মতো হয়েছে যে!’
—‘আরে বাবা আমার কাছে চাইনীজ কুকবুক আছে। এই সব রান্নাগুলো দেশী ঘন্ট চচ্চড়ির চেয়ে অনেক অনেক সোজা। আমি এগুলোই করি। হগ মার্কেট থেকে ছাড়ানো চিংড়ি প্যাকেটে করে নিয়ে এলাম। চটপট সস্ দিয়ে তৈরি হয়ে গেল রান্না। দেখুন বন্দনা ভট্টাচার্য, একবছর হতে চলল আমার সঙ্গে মিশছেন, কিন্তু এখনও বোঝেননি আমি একজন কি দারুণ এলিজিব্ল ব্যাচেলর। এমনকি রেঁধে পর্যন্ত অর্ধাঙ্গিনীকে সাহায্য করতে পারি।’
বন্দনা হেসে বলল—‘কে বললে বুঝিনি! আমার হাতে পাত্রী থাকলে আগেই আপনার দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা করতুম। দুঃখের বিষয় হাতে তেমন এলিজিব্ল কেউ নেই।’
সোম বলল—‘সত্যি নেই? ঠাট্টা করছেন?’
বন্দনার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সোমেরও প্রায় শেষ। বন্দনা আস্তে আস্তে প্লেট তুলতে তুলতে বলল—‘সত্যি নেই। ঘটকালি কখনও করিওনি। তবে আপনার যদি খুব সঙ্গিন অবস্থা হয় তো খোঁজ করতে পারি।’
সোম বলল—‘আমার অবস্থা খুব সঙ্গিন, ঠিকই ধরেছেন। আচ্ছা ক্যামাক স্ট্রিটে নিজস্ব ফ্ল্যাট, কোম্পানি দিয়েছে। আপনি একদিনও গেলেন না। কিন্তু বাসস্থানটা আমার নেহাত খারাপ নয়। গাড়িটা আমার নিজস্ব, কোম্পানি তেলের খরচ দেয়। চেতলার বাড়ি দশ কাঠার ওপর। তাছাড়াও তারকেশ্বরের দিকে জমি-জমা আছে। এ সব কিছুরই হাফ আমার। ইকনমিক্স নিয়ে এম এ পাস করেছি। ফার্স্টক্লাসটা মিস করেছিলাম জনৈক প্রোফেসরের কৃপায়। যাই হোক, লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স ঘুরে এসেছি। ম্যানেজমেন্টের কিছু বিদেশী ট্রেনিংও আছে। বয়স পঁয়ত্রিশ বছর, সাত মাস, তিন দিন, সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। বলুন খারাপ?’
—‘কে বলেছে খারাপ?’
—‘তবু তো আপনার পছন্দ হচ্ছে না।’
—‘বলছি তো এবার দেখব।’
—‘মিসেস ভট্টাচার্য, আপনি আমার সঙ্গে আর কতক্ষণ ঠাট্টা করবেন?’ হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে সোম বলল।
—‘ঠাট্টার কি হল?’
—‘আমি তখন থেকে আপনার কাছে একটা ভদ্র বিধিসম্মত স্টাইলে বিবাহের প্রস্তাব রাখবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর আপনি ক্রমাগত সেটা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন।’
বন্দনা আপাদমস্তক চমকে উঠল। মুখ পাংশুবর্ণ। গলা শুকিয়ে গেছে। সে কোনও কথাই বলতে পারল না।
সোম উঠে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এল। বন্দনা তখনও এঁটো হাতে টেবিলের গোছানো বাসনের সামনে বসে আছে।
—‘ও কি আপনি ওরকম পাথরের মতো হয়ে গেলেন কেন?’ সোম আশ্চর্য হয়ে বলল।
বন্দনা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—‘আপনি বানিয়ে দিলেন বলে।’
—‘আমি বানিয়ে দিলাম! কেন, আপনি কি আপনার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আমাকে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলে বিশ্বাস করেননি? নইলে কি বিপদের সময়ে সর্বাগ্রে আমার কথাই আপনার মনে পড়ত?’
—‘নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেছি, অনুপমবাবু। আপনি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি এ প্রস্তাব আমাকে দিতে পারেন, আমি স্বপ্নেও আশঙ্কা করিনি। এ কি আপনার তামাশা না নাটক করার প্রবৃত্তি আমি এখনও বুঝে উঠতেই পারছি না।’
—‘সত্যি আশ্চর্য! অথচ বন্দনা, আমি এই একবছর ধরে আপনার যতটা কাছে এগিয়েছি, আমার মনে হয়েছে, আপনিও ততটাই এগিয়েছেন।’
—‘কেন আপনার এ কথা মনে হল জানি না। আমরা মেয়েরা কি কোনও অনাত্মীয় পুরুষমানুষের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতেও পারব না! যাই হোক আমি এসব কথা একেবারেই ভাবিনি। আমি বিবাহিত। বিবাহিতের কাছে বিয়ের প্রস্তাব…’
—‘ছিলেন। বিবাহিত ছিলেন। কিন্তু এখন নেই।’
—‘এখনও আছি। এখনও আমি অভিমন্যু ভট্টাচার্যের স্ত্রী।’
—‘বন্দনা, প্লীজ ডোন্ট ডিসীভ ইয়োরসেল্ফ, ইউ ডোন্ট লিভ লাইক এনিবডিজ উইডো। ইউ আর ফ্রি, অ্যান্ড ফ্রি টু রিম্যারি ফর লাভ।’
—‘আপনি এই সিদ্ধান্তে কি করে এলেন?’
—‘কি আশ্চর্য, এটা তো তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়। তোমাকে দেখে অবিবাহিত কুমারী মেয়ে মনে হবে, তোমার অতবড় ছেলে আছে এ কথা পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করবে না। অসম্ভব তোমাকে কারো উইডো ভাবা।’
—‘আপনি আমাকে ক্রমাগত অপমান করে চলেছেন অনুপমবাবু।’
—‘অপমান? কোথায়? কখন?’
‘আপনি তো এটাই বলতে চাইছেন যেহেতু আমি রঙিন শাড়ি পরি, যেহেতু খাওয়া-দাওয়ায় কট্টর বৈধব্য পালন করি না। সেহেতু আমার মৃত স্বামীর প্রতি আমার আর কোনও অনুভূতি থাকতে পারে না। আপনি সোজাসুজিই বলেছেন আমি আপনার দিকে এগিয়েছি। এটা অপমান ছাড়া কি? আপনাকে সহসা তুমি বলবার অধিকারও আমি দিইনি। আপনি কি মনে করেছেন বৈধব্যের কুসংস্কারগুলো পালন করি না বলে, আমি সস্তা হয়ে গেছি, আমার সঙ্গে যা খুশি ব্যবহার করা চলে? সম্পত্তি, ডিগ্রি, চাকরির লোভ দেখিয়ে আমাকে কিনে নেওয়া চলে?’
অনুপম সোমের মুখ দফায় দফায় ফ্যাকাশে হচ্ছে। বন্দনা যত উত্তেজিত, সে তত পাংশু। নিস্তেজ। সে খুব মিনতির সুরে বলল— ‘মিসেস ভট্টাচার্য, আমি আপনাকে অপমান করতে পারি না। পারি না। আপনি এ কথায় এতো আঘাত পাবেন আমি বুঝতে পারিনি। আমি আপনাকে, আমি আপনার… নাঃ…’
‘ঠিক আছে। আপনি দয়া করে এবার চলে যান। আমি আপনার কাছ থেকে আর কোনও কথাই শুনতে চাই না।’
অনুপম বলল, ‘আমি চলে যাচ্ছি নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি দয়া করে আপনার ধারণাটা ফিরিয়ে নিন। আপনাকে আমি সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী বলে জানি। শ্রদ্ধা করি। আপনার সমস্ত আচার আচরণ, ব্যক্তিত্ব আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, আপনি আমায় ভুল বুঝলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।’
নিচ থেকে প্রবল শব্দে কড়া-নাড়ার আওয়াজে দুজনেরই সম্বিত ফিরে এল। অনুপম ব্যস্ত হয়ে নিচে গিয়ে দরজা খুলে দিল, রূপ।
অনুপম বলল—‘এসো মাস্টার! দেখ গিয়ে তোমার মা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে ফোন করেছিলেন, এখনও বোধহয় কান্নাকাটি করছেন। আমি চলি।’
বন্দনা দালানের ওপর একটা পাথরের পুতুলের মতো দাঁড়িয়েছিল। রূপকে আসতে দেখেই তার চোখ গলতে আরম্ভ করল। রূপ বলল—‘আচ্ছা মা, তুমি কি বলো তো? ফোন করে দিয়েছিলাম তো! আবার কান্নাকাটি করছ কেন?’
বন্দনা বোজা গলায় বলল, ‘রূপু, তুই আমার একমাত্র। অন্যদের অনেক আছে। আমার আর কেউ নেই। অন্য যে শ্মশানে যায় যাক। তুই শ্মশানের সংস্রবে যাবি না। আমার বুক ধড়ফড় করে। তুই আমাকে না জিজ্ঞেস করে কক্ষনো এমন করে যাসনি।’
রূপ অসন্তুষ্ট গলায় বলল— ‘সুবীর, আদিনাথ, জীবেশ, তপন সব্বাই এসে ডাকল। মিঃ মল্লিক হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন, আমি যাব না? মাস্টারমশাইয়ের আত্মীয়স্বজন কেউ এখানে নেই। আচ্ছা মা, তুমি এরকম আনরিজিনেবল হলে কি করে চলবে? সব্বাই এখনও কেওড়াতলায় রয়েছে, আমি শেষ পর্যন্ত তোমার কথা ভেবেই এগারোটা বাজছে দেখে ফিরে এলাম। খারাপ লাগল খুব। কিন্তু তোমায় তো জানি। এরকম করো না। ও কি ওরকম কাঁদছ কেন?’
রূপ কাছে এসে দাঁড়াল অপরাধীর মতো। তার মুখে এখনও অসন্তোষ।
বন্দনা চোখের জল মুছে বলল— ‘তুই খাবি তো? শোন আগে জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে আয়, বালতিতে ভিজিয়ে রাখ। স্নান কর, আমি একটু গরমজল করে দিচ্ছি।’
রূপ গোঁজ হয়ে বলল— ‘চান করার কি আছে? ইনফেকশাস ডিজিজ নয় কিছু নয়, স্ট্রোক। আমি জামাকাপড় ছেড়ে নিচ্ছি। খাব না, বন্ধুরা প্রচুর খাইয়ে দিয়েছে। বডি নামিয়ে কতক্ষণ ওয়েট করতে হয় জানো না তো! আমরা তো সব পালা করে গিয়ে রেস্টুরেন্টে খেয়ে এলাম। ওকি! অনুপমকাকুর জুতো মোজা পড়ে রয়েছে যে! কি কাণ্ড। তুমি একেক সময়ে এমন করো না!’
অধ্যায় ২২
কলেজ ছুটি হবার পর সুজিত, অনিল, প্রিয়ব্রত জোর করে অভিরূপকে কফি হাউসে ধরে নিয়ে গেল। বলল— ‘আরে, এখুনি এখুনি বাড়ি গিয়ে করবে কি? কত গরম গরম আলোচনা শুনবে দেখবে কেমন ভালুকজ্বর এসে যাবে গায়ে।’
কলেজে এমনিতেই অভিরূপ একটু একা হয়ে পড়েছে। ওর বন্ধুরা বেশির ভাগই ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিভিন্ন লাইনে চলে গেছে। কয়েকজন খুব ভাল রেজাল্ট করে ফিজিক্স, ম্যাথমেটিকসে অনার্স নিয়েছে, তাদের নাগাল পাওয়া ভার। সুমনের সঙ্গে একদিন দেখা হতে অভিরূপ বলেও ছিল— ‘সুমন আমাদের স্কুলের অমন গ্রুপটা ভেঙে গেল রে!’
সুমন কাঁধ নাচিয়ে বলেছিল— ‘লাইফ’স লাইক দ্যাট।’ অর্থাৎ অভিরূপের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভেঙে যাচ্ছে বলে তার কোনও খেদ নেই। অভিরূপের খুব হতাশাজনক, খুব অপমানকর লাগে সেটা, সেই থেকে সে একলা, খানিকটা মনমরাও। বাড়িতে কোনও জীবন নেই। মার যখন গাড়ি আসে সকালে তখন রূপ চানই করেনি। মা তাড়াহুড়ো করে চলে যায়। একলা একলা খেয়ে নিচে অবনীশবাবুদের ওখানে চাবি রেখে সে কলেজ যায়। কলেজে ক্লাস করতে ভাল লাগে না। স্কুলের কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের পর এই বিশাল কলেজে গরুর গোয়ালের মতো ক্লাসে বসে চশমা-পরা অধ্যাপকের ল’ অফ ডিমিনিশিং রিটার্নস্-এর ওপর লেকচার তার আদৌ ভালো লাগে না। বাড়িতে ফিরে চাবি নিয়ে দরজা খুলে ঢুকতে হয়। আরও ঘণ্টাখানেক পরে মা ফেরে। মায়ের আজকাল পদোন্নতি হয়েছে, দায়িত্ব বেড়েছে। কিন্তু রূপের কি বেড়েছে? নিঃসঙ্গতা, হতাশা! এই ভাবে একটা অনার্স ডিগ্রি নিয়েই বা সে কি করবে? আজ নতুন বন্ধুরা জোরজার করায় কফি-হাউসে এসে তার ভালোই লাগল। বেশ একটা লাইফ আছে।
ডানদিকে ঢুকেই পার্টিশন, সেখানে এক সেট টেবিল চেয়ার। রূপ বসতে যাচ্ছিল, সুজিত বললে, ‘ওটা রিজার্ভড, অভিরূপ, আগে বাঢ়ো!’
—‘কে রিজার্ভ করল? তুমি কি করে জানলে?’
‘আরে বাবা, বসো। একটু পরেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হবে।’
যেতে যেতে শুনল একটি ছেলে টেবিলে ঘুসি মেরে রক্তচক্ষু বলছে— ‘আলবৎ হবে।’ এত জোরে ঘুসি মারল যে টেবিলের খালি কাপ ডিসগুলো ঝনঝন করে উঠল। তার উল্টোদিকের ছেলেটি একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলল, ‘আলবৎ হবে না। তুমিও বেঁচে থাকবে, আমিও মরে যাব না। কি হবে না হবে দুজনেই দেখতে পাব।’
ওরা কয়েকজন মিলে জানলার দিকে একটা টেবিল অধিকার করে বসতেই প্রিয়ব্রত কনুইয়ের ঠেলা মারল রূপকে, পেছন দিকে ইঙ্গিত করল, রূপ সামান্য একটু মাথা হেলিয়ে দেখল একজন ভালো মানুষ চেহারার চুল পাট করা যুবক। প্রোফেসর বলে মনে হয়। আরেকজন তরুণী।
প্রিয়ব্রত বলল— ‘চিনতে পারলে?’
—‘না তো!’
—‘নাঃ। তুমি না! হোপলেস। আরে বাবা গ্রুপ থিয়েটার-টার দেখ না? সুমিতা দে, আর ভদ্রলোকটি ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর। মাস্টারমশাই ছাত্রীর জন্যে ভালো ভালো পালা লিখে দিচ্ছেন, ঐ আর কি। তা জায়গাটা আমরা ওঁদের ড্রামাটিক ডিসকাশনের জন্যে ছেড়ে দিয়েছি। দিস ইজ ডেমোক্র্যাসি ভাই।’
রূপ আজকে বাড়ি ফিরে দেখল উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জানলায়।
—‘কি রে রূপ, আজ ক্লাস হয়েছিল তো?’
—‘হবে না কেন?’
‘স্ট্রাইক-টাইক হাঙ্গামা তো লেগেই আছে, তাই বলছি।’
—‘স্ট্রাইক হলে তো কাগজে দেখতে!’
আসলে মা আজকাল তাকে সোজাসুজি কতকগুলো কথা জিজ্ঞেস করতে ভয় পায়। যেমন— ‘এত দেরি হল কেন?’ বা ‘ক্লাস-টাস ঠিকমতো করছিস তো?’ রেজাল্টটা ভালো হয়নি। অনেক স্বপ্ন ভেঙেছে। মারও যেমন ভেঙেছে, তারও তো তেমন ভেঙেছে! এসব জিজ্ঞেস করলে ভীষণ একটা রাগ এসে যায়। দেরি হল কেন জিজ্ঞেস করলে রূপও বলে—‘তোমার তো রোজ রোজ দেরি হয়, আমাকে কি কৈফিয়ত দাও।’ মা নিভে গিয়ে বলে— ‘জিজ্ঞেস করলেই পারিস! জিজ্ঞেস করলে আমার ভালোই লাগবে।’ ক্লাসের কথা জিজ্ঞেস করতে রূপের ভুরু ভীষণ কুঁচকে যায় বলে—‘আমি কিন্তু আর স্কুলের বাচ্চা নেই মা, আমার পেছনে খবরদারি করাটা ছাড়ো!’
মা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছিল— ‘তুই আমাকে এভাবে বলবি?’
—‘একজন সাকসেসফুল চাকুরের চলাফেরার সঙ্গে একজন আনসাকসেসফুল স্টুডেন্টের চলাফেরার তফাত হয়ে যায় মা, তুমি বুঝেও বোঝ না। তো আমি কি করব?’
বন্দনা আকাশ থেকে পড়ে। এ কি ধরনের জটিলতা রূপের মধ্যে বেড়ে উঠছে। তার সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক সফল চাকুরে আর বিফল ছাত্রের? মা ছেলের নয়? রূপ যত বড় হচ্ছে তার চেহারায় তার ঠাকুমার আদলটা স্পষ্ট হচ্ছে। খানিকটা গোলগাল চেহারা। চকচকে চুল। মসৃণ কপাল। ওকে দেখলে বন্দনার অভিমন্যুর কথা মনে পড়ে না। রূপের জীবনে বাবার স্মৃতি নেই। এখন যেন তার প্রয়োজনও নেই। ছেলের এই বিরক্তি, এই বহির্মুখী মনোভাবের জন্যে কি সে-ই দায়ী? তার খাওয়া-দাওয়া, পড়াশোনার সুব্যবস্থা যতদূর পারে সে করেছে। কিন্তু তা ছাড়া? বন্দনা খুব আত্মগ্লানির সঙ্গে মনে মনে স্বীকার করে চাকরিটা তার অর্থের জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল না। বাড়ি রয়েছে, বাড়ি ভাড়া রয়েছে, কিছু জমা টাকা নিজেরও ছিল, কাকারও ছিল। চাকরিটার জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চয় অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু এর চেয়ে কমেও সে চালিয়ে নিতে পারত। চাকরিটা আসলে টাকার জন্যে নয়, তার নিজের মানসিক প্রয়োজনের জন্যে। শুদ্ধু ছেলেকে নিয়ে, তাকেই জীবনের সর্বস্ব এবং একমাত্র করে সে বাঁচতে পারেনি। শ্যামবাজারের বাড়ি হলে হয়ত পারত। কিন্তু কাকার কাছে এসে কোথা থেকে একটা নিজস্ব জীবনের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা তার ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চাকরির সময়টুকু বাদে বাকি সবটাই সে রূপকে দিতে চেয়েছে। কিন্তু রূপ তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমেই অপরিচিত হয়ে উঠছে। তার আগ্রহের বস্তুগুলো বন্দনার বড় অচেনা। রূপ খেলাধুলো ভালোবাসত, সব ছেলেই বাসে। কিন্তু ওর যেন সবটাই অতিরিক্ত। রানিং কমেন্টারি শুনবে তো এক মিনিটও রেডিও কান ছাড়া করবে না। বাথরুমে যাবে তা-ও ট্রানজিস্টার চৌবাচ্চার পাড়ে বসান। কার সেঞ্চুরি হতে পনের রান বাকি, রূপের চুল উশকো খুশকো। সে খাবে না। খেলেও ফেলে ছড়িয়ে। রাজনীতি যখন আরম্ভ করল, তখন ক্রিকেট একদম ভুলে গেল। খেলাধুলো? ওসব বাজে ব্যাপার, বুর্জোয়া। এসব দিয়ে নাকি মানুষের মধ্যে বেড়ে ওঠা বিপ্লবের প্রবণতাকে ঠেকিয়ে রাখা হচ্ছে। মিছিল, স্লোগান, সে এক কাণ্ড। তারপর সে যখন আঁকতে আরম্ভ করল, বন্দনার খুব ভালো লেগেছিল। তার ছেলে কত রকম রূপ সৃষ্টি করছে, দেখে বন্দনার মনে আনন্দ, শান্তি এসেছিল। কিন্তু এখন যেন সেই ছবি-আঁকার থেকেও রূপ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। বন্দনা ভাবে সে যদি সম্পূর্ণ পুত্র-কেন্দ্রিক জীবনযাপন করত, তাহলেই কি একটি বেড়ে-ওঠা কিশোরের সমস্ত দাবি সে পূরণ করতে পারত! কাকা বেঁচে থাকলে সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম হত। অসময়ে চলে গিয়ে তিনি যেন তাদের একেবারে মেরে রেখে গেলেন। বাবাকে মনে না রাখলেই দাদুকে রূপ মনে রেখেছিল। কথায় কথায় তাঁর প্রসঙ্গ আসত। ইদানীং কলেজে ঢুকে সেই দাদুর স্মৃতিও ওর ফিকে হয়ে এসেছে মনে হয়।
সন্ধেবেলা একা-একা বাড়ি ফিরতে ভালো লাগে না বলে সে প্রায়ই বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফেরে। হই-চই। আড্ডা। মোড়ের দোকান থেকে চা-খাবার আনিয়ে খায়। বন্দনা এলেই, বন্ধুরা বলে, ‘এবার যাই। মাসিমা ভালো আছেন?’
—‘তোরা ভালো আছিস? শুধু আড্ডা মারলি না পড়াশোনাও করলি কিছু!’
—‘ওঃ মাসিমা, আপনাদের যুগে লোকে পড়াশোনা করত। এখন করতে হয় না, হয়ে যায়।’
—‘যায় বুঝি? আপনাআপনি? হলেই ভালো।’
যেদিন বন্ধু নিয়ে না ফেরে সেদিন ও-ই অন্য কারো বাড়ি যায়। বলাই আছে। কলেজ থেকে সন্ধেবেলা না ফিরলে ভেবো না। সুতরাং অফিস থেকে ফিরে সেই তৃতীয় ঘরে জানলার পাশে একা-একা বসে থাকা।
রাত্রে খাওয়ার সময়ে রূপ বই-টই পত্রিকা হাতে নিয়ে খায়। আপাদমস্তক পত্রিকা আর ছবি-ছড়ানো বিছানার মধ্যে এঁকেবেঁকে ঘুমিয়ে পড়ে। বন্দনার ঘুম আসে না। রূপের ঘর গোছায় অনেক রাত পর্যন্ত। খুব সন্তর্পণে। অন্ধকারে, চাঁদের আলোয়। একটি জিনিসও না ফেলে, এদিক ওদিক না করে যথাসম্ভব গুছিয়ে রাখে। তারপর ঢুল আসতে থাকে, তখন গিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে নিঃশ্বাস এমনিতেই দীর্ঘ হয়। বন্দনার গুলো যেন আরও দীর্ঘ।
সুদীপ্তবাবু বলেছিলেন রূপ গ্র্যাজুয়েশনটা করে নিয়ে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে যাক। কিন্তু রূপ কি চাইছে বোঝার ক্ষমতা নেই বন্দনার। ভীষণ অব্যবস্থিতচিত্ত ছেলে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেতে এতদিনের পরিকল্পনাটা যদি ভেস্তে দেয়? কিচ্ছু বলা যায় না।
প্রতি শনিবার সুদীপ্ত সরকার নিয়ম করে আসেন। গল্প করেন, চা খান, কোনও সময়ে রূপ থাকে, কোন সময়ে থাকে না, রূপের ভবিষ্যৎ নিয়ে আগামী শনিবার ওঁর সঙ্গে আলোচনা করতেই হবে ভাবল বন্দনা। রূপ উপস্থিত থাকলেই ভালো, ওর সামনেই তুলবে কথাটা।
শনিবার রূপ কলেজে বেরোবার সময়ে বন্দনা মনে করিয়ে দিল কথাটা— ‘রূপ, গত শনিবারও কিন্তু তুমি ছিলে না। মাস্টারমশাই বলে গেছেন থাকতে।’
রূপ বলল, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ এসে যাব ঠিক।’
কিন্তু বিকেল থেকে ভীষণ বৃষ্টি নামল। সুদীপ্তবাবু এলেন কাকভেজা হয়ে। ছাতাটা খুলে নিচের উঠোনে মেলে দিয়ে বললেন— ‘আর দাঁড়িয়ে লাভ নেই। যা ভেজা ভিজেছি। পত্রপাঠ বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। ওপরে আর উঠব না। সব জলে ভেসে যাবে।’
বন্দনা বলল, ‘আপনার বাড়ি না হলেও এটা একটা বাড়ি তো বটে, এখানেও ভিজে গেলে শুকনো জামাকাপড় পাওয়া যায়। এই বৃষ্টিতে আবার কেউ ফেরত যায় নাকি? এ তো ক্রমশই বাড়ছে!’
সুদীপ্তবাবু বললেন, ‘আমার ছাত্রের জামা আমার গায়ে উঠবে না।’
—‘জানি, আপনাকে ফিটিং জামাকাপড়ই দিচ্ছি। ওপরে আগে আসুন তো!’
আলমারির পাল্লা খুলে তোয়ালে জড়ানো ধুতিগুলো সাবধানে নামাল বন্দনা। ধুতি পাঞ্জাবি চওড়া ধাক্কা দেওয়া শান্তিপুরী জরিপাড়, কাঁচি ধুতি, ফরাসডাঙার নীলচে পাড় দেওয়া ধুতি, সূক্ষ্ম মিলের ধুতি। কিছু কিছু পাটে পাটে কেটে গেছে। হলুদ হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। বেছে নিয়ে পাল্লা বন্ধ করল। এসব তার কাছে ছিল না। যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, নিজের কিছু শাড়ি আর ছেলের জামাকাপড় ট্রাঙ্ক সুটকেসে ভরে নিয়েছিল। কলি এই ক’বছরে দফায় দফায় তার আলমারির জিনিস তাকে এনে দিয়েছে।
সুদীপ্ত বললেন, ‘এ কি আপনার সব রেডি? আপনি কি মন্ত্র জানেন?’ বলেই জামা-কাপড়-তোয়ালে হাতে সুদীপ্ত চুপ করে গেলেন। আস্তে আস্তে কলঘরের দিকে চলে গেলেন। বন্দনা দালানের জল মুছে চায়ের জল চাপালো।
সুদীপ্ত সরকার মাথায় অভিমন্যুর মতো লম্বা না। তবু আজকাল বেশি ঝুলের পাঞ্জাবি পরার চল হয়েছে বলে চোখে লাগে না। চশমাটা খুলে অনেকক্ষণ ধরে অকারণে চশমার কাঁচ মুছলেন সুদীপ্ত। বন্দনা পটশুদ্ধ চা, নিমকি নামিয়ে রাখছে।
সুদীপ্ত বললেন— ‘বালকটি কোথায় গেল এই বাদলার বিকেলে!’
—‘গেছে তো কোন সকালে। ঠনঠনেতে আজ যা জল দাঁড়াবে— আসবে কি করে, তাই ভাবছি’— বন্দনা বলল।
—‘এরকম হলে কি করে?’
‘বেথুন-রো-এ এক বন্ধুর বাড়ি প্রায়ই তো থেকে যায়। হয়ত তাই থাকবে।’
—‘এরকম থেকে যায় নাকি?’
—‘মাঝে মধ্যে!’
—‘বলে না না-বলে?’
—‘বলেও যায় কখনও, কখনও পারলে ফোন করে দেয়।’
—‘আপনি একা থাকেন?’
—‘আমি তো একাই সুদীপ্তবাবু, ও থাকলেও একা-ই।’
—‘মায়ের প্রতি ওর এর চেয়ে বেশি দায়িত্ববোধ হওয়ার কথা ছিল।’
—‘দায়িত্ববোধ দিয়ে কি হয়? কিছু হয় না।’
—‘ও কি বলছেন? এ বয়সে ছেলেরা একটু এরকম হয়ই। তাই বলে…’
—‘আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়ছি।’
—‘সে তো দেখতেই পাচ্ছি।’
—‘ভীষণ আড্ডাবাজ হয়ে উঠেছে, বন্ধু, বন্ধু, আর বন্ধু।’
—‘সংসারের কিছু-কিছু দায়-দায়িত্ব ওকে দেন না কেন?’
—‘দিতে তো চাই। ও এড়িয়ে যায়। আমি বোধহয় ওকে ঠিকমতো তৈরি করতে পারিনি। কিন্তু কোথায় যে আমার ভুল তাও বুঝতে পারি না।’
—‘ও কি বরাবরই এরকম?’
—‘না তো! একেবারেই না। ছোটবেলায় ভীষণ মা-মা ছিল। এখন ঠিক সেই মাত্রায় বন্ধু-বন্ধু হয়েছে। লেখাপড়া তেমন করে করছে না। ও কি করবে সুদীপ্তবাবু, আপনাকে কিছু বলে?’
—‘আপনি বোধহয় ছোট সমস্যাকে বড় করে দেখছেন।’
—‘ভীষণ ভয় করে আমার। মনে হয় ওর যদি কিছু না হয়। যদি দাঁড়াতে না পারে! ও নিজেও আমাকে দোষ দেবে। পাঁচজনেও দেবে। আমি তো নিজেকে মাফ করতে পারবই না।’
—‘কেন আপনার ত্রুটিটা কোথায়?’
—‘সুদীপ্তবাবু আপনি জানেন না, ওর দাদু-ঠাকুমার আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছিলুম একদিন, সে অবশ্য আমার কাকার ভরসায়। কিন্তু তিনি তো দুম করে চলে গেলেন। ও বাড়িতে থাকলে ওর চারপাশে কত লোক, কত শাসন, কত দায়িত্ব আপনা থেকেই থাকত। এখানে কিছু নেই। কিচ্ছু না।’
—‘শুনুন মিসেস ভট্টাচার্য, এসব দ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় দেবেন না। রূপ একেবারেই বোকা ছেলে নয়, ব্রিলিয়ান্ট কি সকলে হয়? কিন্তু ও খুব সহজেই নিজের রাস্তা খুঁজে নেবে। দেখবেন! আপনি ওর জন্যে অত ভাববেন না। আমি কিন্তু ভাবিত হচ্ছি, আপনার জন্যে।’
—‘আমার জন্যে? কেন?’ বন্দনা আকাশ থেকে পড়ল।
‘রূপ এমন একটা বয়সে পৌঁছেছে, নিজের পথ খুঁজে নেবার তাগিদ ওর ভেতর থেকে এখন আপনিই তৈরি হবে। কিছু কিছু ভুলত্রুটি সব মানুষই করে। কিন্তু করে-টরেও ওর দাঁড়িয়ে যাবার অনেক সময় আছে। সমস্যাটা ওকে নিয়ে নয়। আপনাকে নিয়ে। আপনি যে অনেক বেশি অসহায়। এতো একা। এতো বিষণ্ণ, কোথাও যেন আপনার কোনও ভরসা নেই। এভাবে আপনি বেঁচে থাকবেন কি করে? যত দিন যাবে আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন ছেলের ওপর আর ছেলে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমাগত দূরে সরে যেতে থাকবে।’
—‘আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?’ বন্দনার চোখে আতঙ্ক। কাঠ-কাঠ শরীর।
—‘আমি ভয় দেখাচ্ছি? মিসেস ভট্টাচার্য আপনি নিজেই তো ভয় পেতে আরম্ভ করেছেন!’
—‘কি করব? কি করা উচিত তাহলে?’
—‘আচ্ছা মিসেস ভট্টাচার্য, দু’জনকে কিছুতেই মনের মধ্যে স্থান দিতে পারেন না, না?’
—‘দু’জনকে?’
—‘যিনি চলে গেছেন তিনি তো চিরদিনই আপনার অন্তরের মধ্যে পাকা আসনে থাকবেনই। কিন্তু তাঁর পাশে যদি কোনদিন কাউকে অন্তত এই ভয়াবহ একাকিত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যও স্থান দিতে ইচ্ছে হয়, আমাকে ডাকবেন।’
বন্দনার মাথা নিচু। চোখ সজল, সুদীপ্তবাবু দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি বললেন—‘রূপকে আমি নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসি। আমার আত্মীয়পরিজন সবই আছে, তবু কেউ নেই। আপনি তো জানেন! আমি বহুদিন থেকে রূপকে এবং আপনাকে আপনজন বলে ভাবতে শুরু করেছি। আপনি হয়ত জানেন না, আপনারা ছাড়া আমারও সত্যি কেউ নেই।’
সুদীপ্তবাবুর ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো হয়ে চশমার ওপর পড়েছে। চোখগুলো এমনিতে খুব কালো, এখন আরও কৃষ্ণ আরও গভীর মনে হয়। সিগারেটটা উনি ছাইদানির ওপর নামিয়ে রেখেছেন। ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি পরে আজকে যেন অন্য মানুষ। আপনভোলা শিল্পী নয়। জীবন সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তিত, ভাবুক। বন্দনা মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। চারদিকে হাওয়া এলোমেলো, বর্ষার সন্ধ্যা যেন অতীতস্রাবী। সে যেন আবার এসেছে, হাসছে, তার সঙ্গে, রূপের সঙ্গে, রূপ লুটোপুটি খাচ্ছে, তিনজনের রান্না করছে বন্দনা। অন্নপূর্ণা বলছে, দিদি দাদাবাবু বলে গেছেন রেডি হয়ে থাকতে, একটু পরে ফিরেই বেরোবেন তোমাদের নিয়ে। অনেক যেন রাত। তবু সিগারেটের গন্ধ থমথম করছে ঘরগুলোতে। সে চলে যায়নি। যাবে না। বন্দনার একলার ঘর একলার থাকবে না। এই ভয়, এই সর্বক্ষণের মনখারাপ তার দমকা হাসির চোটে কোথায় উবে যাচ্ছে।
অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে থেকে বন্দনার সাদা সিঁথির দিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত বললেন—‘বৃষ্টিটা বোধহয় একটু ধরেছে। আমি এবার যাই। রূপ এলে বলবেন আমি এসেছিলুম, ওকে এক্সপেক্ট করেছিলুম, কাল রবিবার আবার আসব, ও যেন থাকে।’
বন্দনা বলল—‘এখনও বৃষ্টি বেশ পড়ছে, ভেতর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। আপনি আর একটু বসুন না। রূপকে আমি বলে রেখেছি। ও হয়ত ফিরবে। তারপর উঠবেন।’
কোমল গলায় সুদীপ্ত বললেন, ‘আপনার ভয় করছে, না?’
—‘হ্যাঁ। এরকম বিশ্রী ভয় আমার আজকাল কেন করে, জানি না।’
আরও ঘণ্টা দুই পরে রূপ বাড়ি ফিরে দেখল, সুদীপ্তকাকু ছাইদানিতে পোড়া সিগারেটের স্তূপ করে ফেলেছেন, টেবিলের ওপর একগাদা পত্রিকা। মা রান্নাঘরে, খিচুড়ির সুবাস বৃষ্টিভেজা হাওয়ায়।
—‘কতক্ষণ এসেছেন? সুদীপ্তকাকু?’
—‘অনেকক্ষণ। তুই তো জানিসই আমি শনিবার আসব।’
—‘শনিবারেই যে আজকাল আমরা ক’জন—এক বন্ধুর বাড়ি পড়তে যাই। বৃষ্টিতে দেরি হয়ে গেল।’
—‘আমি কি ডেটটা পাল্টে ফেলব?’
—‘কি দরকার?’
—‘তোকে পাব কি করে? এ সপ্তাহে কি আঁকলি?’
—‘কিচ্ছু না।’ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল রূপ, ‘আচ্ছা সুদীপ্তকাকু এঁকে কি হয় বলুন তো? আমাদের মতো মানুষের পক্ষে আঁকাটা হবি থাকাই ভালো না?’
বন্দনা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, পার্টিশন ধরে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল—‘রূপ তুই আর্ট কলেজে যাবি না?’
—‘আচ্ছা মা, আমি যে যামিনী রায় কি অবনীন্দ্রনাথ হব না সেটা কি তুমি এতদিনেও বুঝতে পারনি?’
—‘কিন্তু এতদিনের প্রস্তুতি… এতদিনের আশা…’
সুদীপ্ত বললেন—‘যামিনী রায়, অবনী ঠাকুর, মুকুল দে, কিছুই হবার তোমার দরকার নেই রূপ। আর্টিস্টের এখন অনেক চান্স। আমি নিজেই তোমাকে ইনট্রোডিউস করে দিতে পারব।’
—‘তো আপনি নিজে তো এখনও অন্য চাকরি করছেন, আপনিও তো গেলে পারতেন!’
—‘যাব! হয়ত যাব!’ অন্যমনস্ক গলায় সুদীপ্ত বললেন, ‘তাছাড়াও তো বুঝিস, আমি শিল্পী হিসেবে ফ্রি-লান্স্ থাকতে চাই। তোর ধরনটা অন্যরকম। ডিফিডেন্ট হবার কিছু নেই।’
রূপ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল— ‘ডিফিডেন্ট আমি হইনি। আসলে সুদীপ্তকাকু আমি ঠিক করে ফেলেছি কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসব। আঁকায় আজকাল সেরকম স্যাটিসফ্যাকশন পাই না।’
বন্দনা রান্নাঘরের প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এইভাবেই রূপ কত যত্নে কত আদরে তার স্বপ্নগুলোকে গড়ে, তার পর নির্মমভাবে ভেঙে দেয়। সত্যি যে সে কি বৃত্তি শেষ পর্যন্ত নেবে সে নিজেও জানে না, এ বিষয়ে এখন বন্দনা নিশ্চিত।
সুদীপ্ত একটু পরে বললেন—‘কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিবি সে তো খুব ভাল কথা। বাঃ! তৈরি হচ্ছিস নাকি?’
—‘ওই আর কি। গ্র্যাজুয়েশনটা হয়ে যাক।’
—‘হ্যাঁ, গ্র্যাজুয়েশনটাই তাহলে মন দিয়ে কর।’
বন্দনা বলল— ‘রূপ তুমি জামা-কাপড় বদলে এসো। খাবার দিচ্ছি।’
—‘জামাকাপড় বদলাবার কি আছে? আই অ্যাম অল রাইট। হাত ধুয়ে নিচ্ছি, খাবার দিয়ে দাও।’
সুদীপ্ত উঠছিলেন, বন্দনা বলল—‘আপনি চললেন কোথায়? আপনারও রান্না হয়েছে।’
অধ্যায় ২৩
এ কি সম্ভব? না এ হয় না। এতদিন পর হয় না। নাকি এত দিন পর বলেই হয়? সময়ের দূরত্বটা দরকার একজনকে নামিয়ে আরেকজনকে বসাতে? একজনকে নামিয়ে? হঠাৎ সমস্ত শরীর ব্যথায় শিউরে মুচড়ে ওঠে, বিসর্জনের বাজনা বাজছে কোথায়। বন্দনা তার স্বামীর মূর্তি বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছে। আবার সিঁদুর পরবে বলে। না, এ হয় না। এখনও যে সে অভিমন্যু ভট্টাচার্যের স্ত্রী। দিনান্তে তাকে একবারও মনে পড়ে না এরকম কত দিন চলে গেছে। তার স্পর্শের স্বাদ আর এ দেহে নেই। খুব দূরের এক নিষ্প্রাণ ছবি সে। কিংবা গতজন্মের কোনও সম্পর্ক। সুদীপ্ত সত্যিই তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছেন। কিশোর বয়সে রূপ বিপথে চলে যাচ্ছিল, তাকে শক্ত হাতে ফিরিয়ে এনেছেন। এখনও ওর ওপর মাস্টারমশাইয়ের প্রভাব কাজ করে। সুদীপ্ত ওকে বোঝেন। বন্দনা বরং বোঝে না। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি? তাদের সঙ্গে সম্পর্ক না-ই বা থাকল। তারা কি ভাববে? নির্ঘাৎ বলাবলি করবে এই জন্যেই বন্দনা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। স্বভাব যাদের এই রকম, তারাই বৈধব্যের রীতি-নীতি পালন করে না। অসংযমী। রূপ হয়ত খুশিই হবে, কিন্তু তাকে সে বলবে কি করে? লজ্জা না পেয়ে, প্রতিদিনকার বাজার করতে বলার মতো স্বাভাবিক গলায় বলতে হবে। অথচ ভাবতেও বন্দনার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে, মুখে রক্ত জমছে। কলি? কলি-সঞ্জয় কি বলবে? ওরা তার একমাত্র বন্ধু। বলতে গেলে বোন-ভগিনীপতির মতো। ওরা যদি ঘৃণা করে? দূরে সরে যায়! চোদ্দ বছর কেটে গেছে এইভাবে। এখন জীবনযাত্রায় পরিবর্তনই কি সম্ভব? অথচ সুদীপ্ত এখন তার একমাত্র ভরসা, একমাত্র ভালো লাগা। তিনি এলে বাড়ি-ঘর-দোর, জীবন-সংসার সব পূর্ণ লাগে। আজ সুদীপ্ত মুখ ফুটে কথাটা বললেন, তাই। কিন্তু অকথিত এই বন্ধুতা, এই নির্ভর-এর ইতিহাস তো অনেকদিন হয়ে গেল। রূপ যখন সপ্তাহে তিনদিন মাস্টারমশাইয়ের কাছে দু রকমের আঁকা শিখত—অঙ্ক এবং চিত্রাঙ্কন, তখন সুদীপ্ত একদিন না আসতে পারলেই তার খারাপ লাগত। অভদ্রভাবে কখনও কখনও বলে ফেলেছে —‘শুক্রবার এলেন না?’
—‘আরে একটা কাজ পড়ে গিয়েছিল ভীষণ, আমি আগামী সপ্তাহে চারদিন এসে যাব এখন।’
বন্দনা ভীষণ লজ্জিত হয়ে বলেছে— ‘ছি ছি আমি কি তাই বলেছি? আমি শুধু খোঁজ নিচ্ছিলাম।’
সুদীপ্ত মাঝে মাঝে বাইরে যেতেন। কখনও কাজে, কখনও বেড়াতে। সে সময়গুলো বন্দনার ভেতরে ভেতরে অস্থির লাগত। এতদিনে মাত্র একবারই বন্দনা বেড়াতে গেছে, দীঘা, কলিদের সঙ্গে, ফিরে আসার পর সুদীপ্ত বললেন—‘বেড়াতে কেমন লাগল?’
—‘খুব ভালো।’
—‘আমার আর রূপের সঙ্গে ফুলেশ্বর ঘুরে আসবেন চলুন।’
সে যে কি আনন্দ আর আশ্বাসে পরিপূর্ণ দিন। ইন্সপেকশন বাংলোয় জানলার ধারে ইজেল খাটিয়ে দু’জনে বসে গেছে। কখনও বাইরে, নদীর ধারে। বন্দনা আঁকা দেখছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে একা-একা। অথচ একা লাগছে না। গলা ছেড়ে গান গাইছে।
রূপ ছবি আঁকতে আঁকতে বলছে—‘মা তো বেশ ভালোই গায় সুদীপ্তকাকু, কখনও তো শুনিনি আগে!’
সুদীপ্ত বলছেন, ‘উহু কথা বলো না, গানটা যে শুনছ, সেটা জানতে দিও না। নো কমেন্ট।’
—‘কেন। কাকু?’
—‘আরে তোমার মা লজ্জা পেয়ে যাবেন। গান গায় মানুষ ভেতরের তাগিদে, নিজেকে যখন আর ভেতরে ধরে রাখতে পারে না, তখন। সেই গান জোর করে বন্ধ করে দিলে মানুষের বুক ফেটে যায়।’
রূপ পরে গলগল করে গল্প করেছে এসব মায়ের কাছে। তখন খুব কথা বলতে ভালোবাসত ছেলে। কিছু লুকোত না। দু-চার বছরের মধ্যে কিরকম আমূল পাল্টে গেল! সুদীপ্তর সবচেয়ে বড় গুণ তিনি কাউকে আত্মসচেতন করে দ্যান না। তিনি যেন খুব সুন্দর একটা খুশি এবং আন্তরিকতার পরিমণ্ডল। ক্যানভাস। সে ক্যানভাসে তুমি আপন খেয়ালে ছবি এঁকে যাও। ভালো হল কি মন্দ হল ভাববার দরকার নেই। আসল কথা হল আত্মপ্রকাশ। নিজেকে খুলে মেলে ধরবার অভ্যাস বন্দনার ছিল না বলে বুকটা ফাটত। সুদীপ্ত থাকলে তার আত্মপ্রকাশ সহজ হয়।
কিন্তু অফিস? অণিমা হালদার প্রমুখ সহকর্মিণীরা? কি বলবে? আড়ালে বলবে না, সামনেই বলবে। স্থূল কথাবার্তা, স্থূল আক্রমণ সে যে সইতে পারে না। আসলে সে যত দিনই চাকরি করুক, এই জগতের জন্য এখনও সে তৈরি হতে পারেনি। যে শক্ত খোলসটা নিজের চারপাশে দরকার, যে সপ্রতিভ আচার-আচরণ বাক-চাতুর্য প্রয়োজন তা সে এখনও আয়ত্ত করে উঠতে পারেনি। আরও ভয় আছে। অনুপম সোম? তাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল। গর্ব করে বলেছিল—আমি বিবাহিত, অভিমন্যু ভট্টাচার্যের স্ত্রী। বলেছিল— কট্টর বৈধব্য পালন করি না বলেই কি মনে করেন আমি পুনর্বিবাহের জন্য মুখিয়ে আছি! এই অনুপমের কাছে তার মুখ থাকবে কি করে? সেই দিন থেকে অনুপম তার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলে, ফর্ম্যাল কথাবার্তার বেশি বলে না। বন্দনার মুখোমুখি হলেই তার মুখভাব একটা আহত চেহারা ধারণ করে। বন্দনা যদি আজ সুদীপ্ত সরকারকে বিয়ে করে অনুপমের প্রতিক্রিয়াটা কি হবে? সে কি অপমানের প্রতিশোধ নেবে না? সে কি হিংস্র হেসে বলবে না —‘তাই বলুন। মিসেস ভট্টাচার্য। সোজা সত্যি কথাটা বলতেই পারতেন। আরেকজনের সঙ্গে আপনার মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। অন্য কথা বললেন কেন? কেন বললেন আপনি বিবাহিত, আপনি অভিমন্যু ভট্টাচার্যের স্ত্রী, আর কাউকে বিয়ে করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন আমাকে অপমান করলেন?’
ভেবে দেখলে, অনুপম এ কথা বলতেই পারে! সত্যিই বন্দনা তাকে যেভাবে অপমান করেছিল, সে বেচারা তার মতো কিছুই করেনি। কিছু না। আসলে কতকগুলো কথা ‘উইডো’, ‘ইউ ডোন্ট লিভ লাইক এনিবডিজ উইডো’— এই কথাগুলোই তার মাত্রাছাড়া ক্রোধের কারণ।
কিছুতেই এ কমপ্লেক্স সে কাটিয়ে উঠতে পারল না। কাকা বেঁচে থাকলে হয়ত তাকে ধীরে ধীরে মুক্তমনের নারী, মুক্ত মানুষ করে তুলতেন, তার নিজের হওয়ার সাধ্য নেই।
এক শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদ নিজের টেবিলের ওপর অজ্ঞান হয়ে গেল বন্দনা। অমলেন্দু অন্য কোনও ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলেন। স্যারা টকাটক টাইপ করে যাচ্ছে। অমলেন্দু ফিরে সুইং ডোর খুলে ঢুকতে যাবেন বাঁদিকের টেবিলে স্যারা টাইপ করে যাচ্ছে। দেখলেন ডান দিকের টেবিলে বন্দনার মাথাটা টেবিলের ওপর, আস্তে আস্তে ঝুলে যাচ্ছে।
—‘এ কি, মিসেস ভট্টাচার্য! কি হয়েছে?’ সাড়া নেই। স্যারাকে ডাকলেন। স্যারা এসে দেখে বলল— ‘শী হ্যাজ আ ব্ল্যাক আউট।’
কোম্পানির ডাক্তার এসে দেখলেন, তক্ষুনি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হল। যেতে যেতে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এল বন্দনার। দেখল সব ঘুরছে। সে শুয়ে আছে তবু ঘুরছে। স্বয়ং পৃথিবী মাতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল কি সে? মাথার কাছে স্যারা বসেছিল, নড়াচড়া টের পেয়ে ঝুঁকে পড়ল— ‘বন্ডনা, বন্ডনা, ডোন্ট ওয়ারি য়ু আর আ বিট আনওয়েল। উই আর টেকিং য়ু টু মেট্রোপলিট্যান জাস্ট ফর আ চেক-আপ। হাউ আর য়ু ফীলিং নাউ?’
ঘোষাল উল্টো দিকে বসেছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন— ‘কি কষ্ট হচ্ছে বউদি?’
—‘মাথা ঘুরছে প্রচণ্ড।’
—‘ঠিক আছে কথা বলবেন না, চোখ বুজিয়ে থাকুন।’ ঘোষালের আত্মীয় সম্বোধনে বোজা পাতার তলায় চোখ দুটো ভিজে ভিজে ওঠে।
কোম্পানি তাকে বারো দিন নার্সিং হোমে রাখল। সমস্ত চেক-আপ। ই. সি. জি, ই. ই. জি, ব্রেন-স্ক্যান সব রকম বিশেষজ্ঞ এলেন। কিছুতেই উপশম হয় না। রোগিণী খালি শান্ত হবার ওষুধ, ঘুমের ওষুধ খেয়ে থাকে। ঘোরে থাকে।
শেষে সুদীপ্তবাবু বললেন—‘সঞ্জয়বাবু, ঘোষালসাহেবকে বুঝিয়ে বলুন ওঁকে এবার আমরা বাড়ি নিয়ে যাই। সব কিছু চেক-আপ তো হয়ে গেছে। এখানে চিকিৎসা-বিভ্রাট ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। এতো সিডেশন ভালো না।’
সঞ্জয় বলল, ‘বাড়িতে? সে কি? কে দেখবে?’
কলি বলল, ‘আমি দেখতে পারি। সেটা কোনও কথা না। কিন্তু চিকিৎসার কি হবে?’
একটু চুপ করে থেকে সুদীপ্ত বললেন—‘আমি ডাক্তার জানি। আপনাদের একদম নিশ্চিন্ত থাকতে বলছি। ঠিক হয়ে যাবে সব। এখানে যেভাবে বার্বিচ্যুরেট ব্যবহার করছে একটা স্থায়ী ক্ষতি না হয়ে যায়।’
ঘোষালের সঙ্গে অনেক বাগ-বিতণ্ডা করে সুদীপ্ত একরকম জোর করেই নিয়ে এলেন বন্দনাকে। কলি রইল। কিন্তু কলির থাকার চেয়েও বড় থাকা সুদীপ্তর। হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ঠিক করা, তাঁকে ডেকে এনে দেখানো, নিয়মমতো ওষুধ খাওয়ানো। রূপ যদি ডাক্তারকে রিপোর্ট দেবার ভার নিতে যায়, সুদীপ্ত বলেন ‘থাক। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে। তোর ক্ষতি হবে। আমিই যাব এখন।’
আসলে সুদীপ্তর ভয় রূপ ঠিকমতো রিপোর্ট দিতে পারবে না। রূপ তার মায়ের কিছু জানে না। ডাক্তার সিনহা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পূর্বাপর জিজ্ঞেস করবেন। রূপ সেসব বলতে পারা দূরের কথা, জানেই না।
মাসখানেকের মাথায় একেবারে সুস্থ হয়ে গেল বন্দনা। খাট থেকে উঠে দাঁড়াতে আর মাথা টলটল করছে না। নিজের শরীরটা নিজের মনে হচ্ছে। কলি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করল—‘কি রোগটা হয়েছিল আমার বউদির? ডাক্তারবাবু!’
প্রবীণ ডাক্তার বললেন—‘আমরা তো ডায়াগনসিস করে চিকিৎসা করি না মা, সিমটমের চিকিৎসা করি, রোগীর শরীরের স্বাভাবিক হালচাল বুঝে লক্ষণ মিলিয়ে চিকিৎসা।’
‘—রোগীর হিসট্রি তো আপনি জিজ্ঞেস করেননি। কনস্টিট্যুশন জানলেন কি করে?’
—‘খানিকটা দেহ লক্ষণ মিলিয়েই জানা যায়। হিসট্রি সব সুদীপ্তবাবুর কাছেই জেনেছি। তাঁর রিপোর্ট এতো পুঙ্খানুপুঙ্খ ছিল বলেই এতো তাড়াতাড়ি সারল। নয়তো মাকে আরও কিছুদিন শুয়ে থাকতে হত।’
কলি আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল—‘লক্ষণের চিকিৎসা করলেও একটা না একটা ডায়াগনোসিস তো আছে!’
—‘তা আছে। সুদীপ্তবাবু ঠিকই ধরেছিলেন। নার্ভাস সিসটেমের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়াতেই এমনি হয়েছিল। অ্যাংজাইটি নিউরোসিস।’
—‘তাই? আর কিছু না?’
—‘এটা কি সামান্য জিনিস হল মা? একটা মানুষের ভাবনাচিন্তা সহনশক্তি সব কিছুরই একটা সীমা আছে। সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অতিবড় অঘটন ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। যে যেভাবে রি-অ্যাক্ট করে।’
—‘তাহলে আবার এরকম হতে পারে!’
—‘না হওয়ারই কথা। চিকিৎসা তো একটা হল। সিসটেমটা একটা বুস্ট পেল। তবে অসম্ভব নয়। ওঁকে একটু নিশ্চিন্তে থাকবার ব্যবস্থা করে দিন।’
কলি যেদিন চলে যাবে বন্দনার রোগমুক্তি উপলক্ষে একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করল। সে নিজেই নানারকম রান্না করল, বন্দনাকে কিছু করতে দিল না। সবাইকে খাওয়ালো নিজের হাতে। রূপ আর রঞ্জু রূপের ঘরে, সুদীপ্ত সঞ্জয়ের সঙ্গে গল্পে মত্ত।
কলি বলল—‘বউমণি আমার তো সময় হয়ে গেল।’
বন্দনা তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল—‘আমার তোকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না কলি। তুই চলে গেলে আমি একা কি করে থাকব?’
কলি হেসে বলল—‘এতদিন কি করে চলছিল বউমণি?’
—‘চলছিল না রে কলি, ওকে কি চলা বলে?’
—‘কেন, তোমার ছেলে?’
—‘ছেলে কি কখনও মায়ের সঙ্গী হয়? হয় না।’
—‘তাহলে তোমার সুদীপ্ত?’
বন্দনা যেন আচমকা চড় খেয়েছে। মুখ একবার লাল হয়েই পরক্ষণে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।
কলি বলল—‘সুদীপ্তবাবু তোমাকে সত্যি-সত্যি ভালোবাসেন, তুমি ওঁকে বিয়ে করো।’
—‘কি বলছিস? ছিঃ ছিঃ।’
—‘ছি ছি নয়। না করলেই বরং তোমায় আমি ছি ছি করব বউমণি। এবার উনিই তোমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। তোমার খুঁটিনাটি এতো উনি কি করে। জানলেন বলো তো?’
—‘তোর যুক্তিতে তো তাহলে ডাক্তারদের আগে বিয়ে করে ফেলতে হয় আমাদের।’
—‘ওটা কু-যুক্তি বউমণি, তুমি ঠিকই বুঝেছ আমি কি বলছি। আমার মনে হয় তুমি নিজেও ওঁকে…’
—‘কলি, কি হচ্ছে?’
—‘কেন বলো তো তোমার এতো লোকভয়?’ কলি এবার রেগে উঠল, ‘লোকে তোমার কে কি করবে? কোন সমাজের সঙ্গে মেশো, কার খাও পরো যে গাল শুনতে হবে? তুমি ভীষণ দুর্বল বউমণি। এতো লোকলজ্জা, এতো দুর্বলতা ভালো নয়। সুদীপ্তদার ভালোবাসাকে তুমি স্বীকার করে নাও।’
—‘তুই যা বলছিস তা যদি সত্যি হয় তাহলে স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকবার দরকার হবে না কলি। বিয়ে না করেও ভালোবাসা যায়।’
তিরস্কারের দৃষ্টিতে বন্দনার দিকে তাকিয়ে রইল কলি, বলল— ‘যায়। কিন্তু বিয়েটাই সবচেয়ে শোভন, সুন্দর। ব্যক্তির চোখেও, সমাজের চোখেও। আশা করি তুমি এ বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনঃস্থির করে ফেলবে।’
—‘তুই আমায় জোর করছিস? কলি নিজের তোর খারাপ লাগবে না? কষ্ট হবে না?’
—‘কষ্ট? কার জন্য? দাদার জন্য?’
বন্দনা চুপ করে রইল।
কলি বলল—‘বউমণি দাদা কি স্বর্গে তোমার জন্যে বসে আছে মনে করেছ নাকি? যদি স্বর্গ বলে সত্যিই কিছু থাকে। কোনও একটা মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা, সেখানে দাদার মতো মানুষের খুব শান্তিতে বিচরণ করবার কথা। দাদার জন্য কষ্ট আছে। সে অকালে চলে গেল আমার সবচেয়ে ভালো দাদাটা। কিন্তু সে কষ্ট এখন ফিকে হয়ে এসেছে। মিথ্যে বলে তো লাভ নেই! আর তার সঙ্গে সুদীপ্তদার সঙ্গে তোমার বিয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। বউমণি একটা শূন্যের জন্য তুমি তোমার পুরো জীবনটাকে বরবাদ করে দেবে, কোনদিকে তাকাবে না, কাউকে ভালোবাসবে না, এ আমি কখনই বাঞ্ছনীয় মনে করি না।’
—‘তুই হলে পারতিস? কিছু মনে করিসনি কলি।’
—‘পারতাম কি? পেরে আছি বউমণি। আমার হৃদয় এতো ছোট নয় যে সেখানে একজন মৃতের পাশে একজন জীবিতের জন্য স্থান-সঙ্কুলান হবে না।’
—‘পেরে আছিস? মৃত-জীবিত? কি বলছিস কলি?’
—‘আমার জীবনের, আমার যন্ত্রণার তুমি কতটুকু জানো বউমণি? নিজে যন্ত্রণা না পেলে আমি তোমার কষ্ট বুঝতাম কি না তাই কে জানে! যন্ত্রণা না পেলে কেউ মানুষ হয় না বউমণি!’
কলি আর দাঁড়াল না। চটপট করে সবাইকে চা খাইয়ে চলে গেল।
অধ্যায় ২৪
সুদীপ্ত বললেন—‘আমার একটা উপহার তামাদি হয়ে গেছে যদিও, তবু বড় আনন্দ আর পছন্দ করে কেনা ছিল জিনিসটা। সেটা এখন নিলে আমি খুব খুশি হতাম।’
সন্ধে ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। শাঁখ বাজার শব্দ বাতাসে মিশে আছে। তিনটে ঘরেই ধূপ জ্বালিয়ে দিয়েছে বন্দনা, চন্দন গন্ধে এখন বাড়ি ম ম। সে বলল—‘ঠিক আছে নিই তবে।’
সাইড-ব্যাগ থেকে একটা সযত্নে প্যাক করা বাক্স বেরোল। অর্ধেকটা খুললেন সুদীপ্ত—নীলাম্বরী শাড়ি।
‘মনে পড়ছে?’ সুদীপ্ত বললেন।
—‘সেই থেকে জমিয়ে রেখে দিয়েছেন?’
—‘ইয়েস।’
‘কেন?’
—‘এর আবার কোনও উত্তর হয় নাকি? প্রথমত যাঁকে মনে করে উপহারটা কেনা তিনি যতক্ষণ না গ্রহণ করছেন ততক্ষণ তো আমি জিনিসটার জিম্মেদার। তাছাড়া’… সুদীপ্ত একটু থেমে বললেন—‘উপহারটা দেবার দিন আসবে এ আশা ছিল।’
—‘এত আত্মবিশ্বাস?’
—‘ও ইয়েস। ভালোবাসার আরেক নামই যে আত্মবিশ্বাস!’
—‘এসব ইললিগ্যাল মনোভাব কবে থেকে?’
—‘বলব না।’
—‘কেন?’
—‘ইললিগ্যাল’, শব্দটা তুলে নিতে হবে।
—‘নিলাম।’
—‘প্রথম দিন প্রথম ক্ষণ থেকে বলতে পারলে কবিদের ফাইন্ডিংস্-এর সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু তা নয়। সেই সিরিজ আঁকবার সময় থেকে…’
—‘মডেল হওয়া ব্যাপারটা তো বিপজ্জনক তাহলে?’
—‘আঁকতে গিয়ে যদি মানুষকে আবিষ্কার করা যায়, যদি ভাবে ভাব মেশে তাহলে এক অর্থে বিপজ্জনক, বেদনাদায়ক ঠিকই!’
—‘এরকম হয় নাকি? হয়েছে আগে আর?’
সুদীপ্ত হেসে ফেললেন—‘দুঃখের বিষয়, না।’
—‘আবিষ্কার-টার কি বললেন ভালো বুঝলাম না।’
—‘দেখলাম এক নিষ্পাপ কৈশোর প্রার্থনাময় যৌবনে পৌঁছল, জীবন তার প্রতিশ্রুতি রাখল না। কৈশোরের বিস্ময় ভরা চাহনিতে আস্তে আস্তে গভীর অবসাদযোগ, বিষাদযোগ। অথচ সেই বিষাদযোগের অন্তরালে পরিপূর্ণ বাঁচবার ইচ্ছা, বিপুল কর্মশক্তি, তার চেয়েও বড় ভালোবাসবার শক্তি বাঁধ দেওয়া জোয়ারের জলের মতো আটকে আছে। বাঁধ কেটে দিলে পুষ্পিত প্রান্তরের রূপ কেমন হতে পারে মনশ্চক্ষে তাও দেখতে পেলাম। মনে মনে আঁকলাম।’
বন্দনা ভাবল—‘পুষ্পিত হওয়া অতি সহজ!’ মুখে বলল—‘ঠিক যেমনটি এঁকেছিলেন, বাস্তবের ছবিটা যদি তেমন না হয়!’
—‘হবে না-ই তো!’ সুদীপ্ত জোর দিয়ে বললেন, ‘আমার চেয়ে লক্ষগুণ বড় শিল্পী ছবি আঁকছেন, তাঁর ঝুলি থেকে কি রঙ, কি রেখা বার হয়—দেখবার অপেক্ষায় আছি।’
জীবনশিল্পী তাই তার ঝুলি থেকে প্রথম রঙ বার করেছে। ঘোর নীল, রাত্রির আকাশের মতো। অভিসারের রঙ। নীলাম্বরী পরে বন্দনা অফিস গেছে। সরু পাড়, জমকালো আঁচল, তাইতে রাধাকৃষ্ণর রাসলীলা। কত গোপী মুখ, বাঁশি, বৃক্ষ, লতা, ফিকে গোলাপি রঙের রেশমী সুতো দিয়ে অসাধারণ একটি ছবি তৈরি করেছে বিষ্ণুপুরের বালুচরী শিল্পী। ঘোষাল সাহেব পর্যন্ত চমকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। রোগমুক্তির পর এই প্রথম বন্দনা কাজে যোগ দিল। ঘোষালের মুখে আনন্দের হাসি। স্যারা বলল—‘ফ্যানটাসটিক।’ সোম কাজে এসেছিল ঘোষালের কাছে, ফেরার সময় এক দণ্ড দাঁড়াল, আড়চোখে স্যারার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল—‘কংগ্র্যাচুলেশনস্।’
চমকে উঠল বন্দনা—‘হঠাৎ?’
—‘স্বভাবতই সেরে উঠেছেন বলে। তাছাড়া আপনাকে খুব সুন্দর, খুব জীবন্ত লাগছে। আমি শুধুমাত্র দর্শক। তবু এ দৃশ্যে বড় খুশি লাগছে। কংগ্র্যাচুলেশন এগেইন।’
পেছন ফিরে চলে গেল সোম। ও কি কিছু জানে? জানা তো সম্ভব নয়! কোনক্রমেই নয়। আজই প্রথম সে সুদীপ্তর সঙ্গে একা বেড়াতে যেতে রাজি হয়েছে। রূপ আজ কলেজ-ফেরত বন্ধুর বাড়ি যাবে, ফিরবে না বলে গেছে। বন্দনাও বলেছে—সে-ও আজ একটু বেরোবে। অফিস-বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ফেরার তাড়া নেই। সুদীপ্ত সিনেমায় যেতে ভালোবাসেন না, নাটক ভালোবাসেন, গ্রুপ থিয়েটার। এখন তো তেমন কিছু হচ্ছে না। কোথায় নিয়ে যাবেন কে জানে। বন্দনা কিছু জিজ্ঞেস করেনি। যা করবে ভালো বুঝে করবে। বহুদিনের পর নিজেকে কিছু ভাবতে হবে না, এই ভেবেই সে খুশি।
ছুটির পর অফিসের গাড়িকে সে বলল পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে ছেড়ে দিতে। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি, নিয়ে আকাশবাণী ভবন। সুদীপ্ত বললেন—‘ট্যাক্সিটা ছাড়বার দরকার নেই।’ আবার মুখ ঘুরিয়ে থিয়েটার রোড, লর্ড সিনহা রোড। বিরাট কলেজ হলে গানের আসর বসেছে। পুরিয়ার সিদ্ধ শিল্পী। দেড়ঘণ্টা ধরে পুরিয়ায় ভ্রমণ করে হঠাৎ শুদ্ধ কল্যাণের বিপুল অতিজাগতিক গাম্ভীর্যে পৌঁছলেন। সুরের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে বন্দনা। যতবার তীব্র মধ্যমে পৌঁছচ্ছে সুর ততবার তার শরীরের মধ্যে বালিকা-কালের পাথুরিয়াঘাটার কনফারেন্সের পুরো আবহ সুরবিস্তার করছে। হ্যারিংটন স্ট্রিটের মোড়ে একটা বিরাট ফাঁকা জায়গা ছিল অনেক দিন। সেই জায়গাটা ঘিরে সদারঙ্গ মিউজিক কনফারেন্স বসত। বড়ে গোলাম আলি, আমীর খাঁ, বাহাদুর খাঁ এদের ওখানেই শুনেছে। হীরাবাঈ এবং সরস্বতীরানেকে পাথুরিয়াঘাটায়। সে সব ছিল বড় আনন্দের, রঙ বাহারের দিন। শূন্যে কে যেন রঙ ছড়াতো, রঙ আর সুগন্ধ। মউলের বাস তখন হাওয়া দিলেই বইত হু হু করে। ঘুম-ভাঙানিয়া সে সব রাত। রাতের আকাশ বেয়ে সুরের প্রপাত নেমে আসছে। কখনও সগর্জনে ফৈয়জ খাঁয়ের গলায়, কখনও গম্ভীর মন্দ্র চালে আমীর খাঁয়ের গলায়, কখনও নৃত্যপর ঝরনাধারায় হীরাবাঈ বরোদেকার। বাগেশ্রীতে তারানা ধরেছেন শিল্পী। কীরকম এক গম্ভীর বিষন্ন প্রার্থনা মুক্তি পাচ্ছে, অনন্ত হরিনারায়ণম, যেন তুম তরানা নুম-এর মধ্যে থেকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। আজকের এ আসর স্মৃতিজাগানিয়া, দুখজাগানিয়া, যে স্মৃতি, যে দুঃখ আসলে একরকম নিবিড় সুখ। অনুভূতির খুব গভীর স্তরে তার দুঃখ আজ সুখের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে টের পেল বন্দনা। কেন এত বিবাদ বিতর্ক, কেন ভাবনা, কেন এতো অবসাদ? অনুভূতির তৃতীয় স্তরে সবই এক অখণ্ড সামুদ্রিক বিশালতায় বিরাজ করছে। ভৈরবী ঠুংরি ধরেছেন পণ্ডিতজী। ঠুংরির পরতে পরতে যেন ভজনের দৈবী মূৰ্ছনা মিশিয়ে দিচ্ছেন, চোখের পাতার পেছনে থমকে থাকা জল যেন আর থাকতে চায় না, ওই আকৃতি ওই মোচড়কে অভিষিক্ত করতে চায়। সেই সুরসাগরে, রূপসাগরে, সুগন্ধসায়রে ডুব দিতে দিতে বন্দনার প্রথম ডুবে অপরূপ রূপ-যৌবন সব যেন ফিরে এল এক দিব্য উপহারের মতো, রোমে রোমে আবার সেই হারানো রোমাঞ্চ-তরঙ্গ, ঠোঁট মধুর প্রত্যাশায় কাঁপছে, তার হাত পা সব যেন নরম-ননীর তৈরি, যে কোনও সময়ে এই সুরের উত্তাপে গলে যাবে। দ্বিতীয় ডুবে বন্দনা অলঙ্কার নিয়ে উঠল,বহু-মূল্য আভরণ। অলঙ্কার হল বাহুল্য, সজ্জা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত। যে জীবনে শুধু প্রয়োজনের দায় মেটাবার ব্যবস্থা সেখানে বাঁচবার অনেক উপকরণ সত্ত্বেও একটা কঠিনতা, একটা ফাঁকি থেকে যায়। প্রয়োজন মিটিয়ে যখন অতিরিক্তের প্রকাশ হয়, নানা রূপবন্ধে, নানা ছন্দে, সেই জীবন অলঙ্কারময়, তার আনন্দের উৎস বিচিত্র। বন্দনার চোখে আজ অকারণ অশ্রুর সুখ, বুকের মধ্যে আবেগের জোয়ার যেখানে সে ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত নেই, কণ্ঠ বুঝি যে কোনও মুহূর্তে ওই সুরে সুর যোজনা করতে আছড়ে পড়বে। ছন্দোময় পায়ের পাতা, অদৃশ্য মুদ্রা হাতে, কটিতে ভাঁজ। গান শুনতে শুনতে বন্দনা মনে মনে উঠে দাঁড়ায়, রাশি রাশি ফুল আকাশে ছুঁড়ে দেয়, মুঠো মুঠো আবির ফাগ, তার দু-হাতের মুঠো থেকে ঝরে ঝরে পড়ে পৃথিবী রঙিন করতে থাকে।
ভৈরবী ঠুংরির পর আসর শেষ। রাত বারোটা বেজে গেছে। নির্জন অথচ আলোকময় পথ। ওপরে তারাভরা মধ্যযাম। এত সুন্দর কলকাতা বন্দনা কখনও দেখেনি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের বিশাল সিলুয়েৎ দেখা যাচ্ছে কোনও রহস্যময়, অপার্থিব উপস্থিতির মতো।
সুদীপ্ত বললেন—‘এটুকু তো হেঁটে যেতেই হবে। এখন গাড়ি পাওয়া যাবে না। খুব কষ্ট হবে?’ সুদীপ্তর গলা তখনও সুরে ভারি হয়ে আছে।
বন্দনার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ভেতরটা এতো ভরাট। পা ফেলতে অস্বস্তি পাছে তাল কেটে যায়। দু-পাশের পরিচিত সব সৌধরা আজ এক মায়ানগরীর মায়াপ্রাসাদ। জ্যোৎস্নাময় পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলতে চলতে তার মনে হল—হয়ত মায়া। সত্যিই মায়া। জীবন কখনও কখনও এমন মায়াময় বলেই প্রতিদিনকার তিল তিল খুঁটে খুঁটে বাঁচার উঞ্ছবৃত্তি সত্ত্বেও মানুষ বাঁচবার প্রবল ইচ্ছে নিয়েই বাঁচে। লোয়ার সার্কুলার রোড, হেস্টিংস রোড, হসপিট্যাল রোড সব ছায়া-বৃক্ষে মোড়া। সদর দরজার তালা খুলে বন্দনা ভেতরে ঢুকে গেলে সুদীপ্ত দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। দু’জনে দু’পাশে। একজন দরজার ভেতরে, একজন বাইরে রাস্তায়। ভেতরে ভেতরে দু’জনেই মন্দ্রিত মথিত, কিন্তু বাইরে নিস্পন্দ, নির্বাক। কিছুক্ষণ পরে সুদীপ্ত বললেন—‘আজ তবে চলি!’
বন্দনা কিছু বলল না। শুধু দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। একটু পরে দরজা বন্ধ করল। দোতলায় উঠে ক্যোলাপসিবলের তালা খুলল। শূন্য পুরী। আজ যেন শূন্য নয়। সঙ্গে করে যে গান, যে সুর, যে তালের অলঙ্কার সে আজ দেহমন ভরে নিয়ে এসেছে সেই সব তার অঙ্গে থেকেও কি এক মন্ত্রে ঘরময় দালানময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এ এমন এক অলঙ্কার যা দিয়ে দিলেও ফুরিয়ে যায় না। শুতে গিয়ে বন্দনার মনে হল সে অকূল সুরপাথারে ডুবে যাচ্ছে। এ সমুদ্রে ডুবে গেলেও দম বন্ধ হয় না।
অধ্যায় ২৫
ম্যারেজ রেজিস্টারের কাছে গিয়ে সইসাবুদ করে আসা হবে। কোনও অনুষ্ঠান নয়, হোটেলে খাওয়া হবে, তারপরে সুদীপ্ত বন্দনাকে নিয়ে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যাবেন। সপ্তাহখানেক। সে ক’দিন কলি রঞ্জুকে নিয়ে রূপের কাছে থাকবে। তারপর ফিরে এসে সুদীপ্তর ইচ্ছে তাঁর বাড়িতে বন্দনা-রূপ চলে যাবে। বন্দনার ইচ্ছে সুদীপ্তই এসে তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। এ ব্যাপারটার এখনও মীমাংসা হয়নি। আর বাকি রূপকে বলা। সুদীপ্ত আজকাল মস্ত অ্যাড-এজেন্সিতে বড় চাকরি পেয়েছেন, তিনি বলছিলেন রূপকে নিয়ে একদিন নতুন অফিস দেখাবেন,দু’জনে একটু ঘুরবেন, তারপরে জানাবেন কথাটা। নতুন অফিস দেখা হল, ঘোরা হল, খাওয়া হল, কিন্তু কথাটা বলা হল না। সুদীপ্ত বললেন—‘সামহাউ আই কুড্ন্ট্। আমাদের অন্য উপায় ভাবতে হবে। দু’জনেরই যখন বলতে এত দ্বিধা লাগছে।’
শনিবার রাত্রে কলি ফোন করল—‘রবিবার রঞ্জুর জন্মদিন, রূপু যেন সকাল থেকে যায়।’
রবিবার সারাটা সকাল ফাঁকা। বন্দনা তিনখানা ঘর ভালো করে ঝেড়ে ঝুড়ে গুছোল। পর্দাগুলো কাচতে দিয়েছিল, সব পরালো। পাখা পরিষ্কার করল। গায়ে মাথায়, শাড়িতে ঝুল ময়লা। বেশ করে মাথা ঘষলো। একটা দেড়টার সময়ে বেরিয়ে মনে হল শরীরটা চমৎকার হালকা লাগছে, ভাত-টাত খেয়ে আর এই হালকা অবস্থাটাকে পাল্টে কাজ নেই। একটু দুধ আর পাউরুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল একটা বই নিয়ে। কখন আস্তে আস্তে ঘুম এসে গেছে, দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজতে চটকা ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বন্দনা দেখল রূপের ঘরে পাখা চলছে। রূপ বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে, জামা-কাপড় পরা।
—‘কি রে কখন এলি? কে খুলে দিল?’
—‘নিচের জেঠিমা।’
—‘কি খাওয়ালো পিসি?’
—‘খাওয়ালো!’
—‘চা খাবি তো এখন! আর কিছু?’
—‘নাঃ শোনো মা, একটু তাড়াতাড়ি করো, আমি একবার এক্ষুনি বেরোব।’
—‘বেরোবি কি? এই তো এলি?’
—‘বেরোতে হবে, একবার অনুপের কাছে যাব।’
—‘এখনই? কেন রে?’
—‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা হস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।’
বন্দনা অবাক হয়ে বলল— —‘কেন? কার জন্য?’
—‘ন্যাচার্যালি আমারই জন্য। আমার পক্ষে এখানে আর থাকা সম্ভব নয়। তোমরা আমাকে তাড়িয়ে ছাড়লে!’
—‘রূপ তুই কি বলছিস? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।’
—‘তুমি পিসি আর দ্যাট ম্যান মিলে যা ব্যবস্থা করেছ, তাতে আমার আর এখানে থাকা চলে না। তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা পর্যন্ত চলে না। আই হেট দ্যাট ম্যান।’ —রূপ গলা চড়াল।
—‘রূপ’—বন্দনা কঠিন গলায় বলল—‘কবে থেকে এই মনোভাব তোমার ওঁর সম্বন্ধে?’
—‘আজ থেকে। এই মুহূর্ত থেকে। যখন থেকে তোমাদের ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা শুনেছি তখন থেকে।’
—‘তার আগে তুমি ওঁকে পছন্দ করতে?’
—‘করতাম। ভুল করতাম।’
—‘কমেন্ট না করে, সোজা কথার সোজা উত্তর দাও রূপ। চক্রান্ত কাকে বলছ? আমার পক্ষে এরকম একা-একা থাকা ভীষণ কষ্টকর ভয়াবহ হয়ে উঠছে দিনকে দিন। সুদীপ্তকাকুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক খুব ভালো বলেই এ কথা আমি ভাবতে পেরেছি।’
রূপের মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—‘এতদিন তো তুমি আর আমিই ছিলাম, কোনও অসুবিধে তো হয়নি!’
—‘এখন আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। আমার ভয় করে।’
—‘এখন তো আমিও বড় হয়ে গেছি। আর কিছুদিন পর তোমার ভার পুরোপুরি নিতে পারব। এখন তোমার এ সব মনে হচ্ছে কেন! আর আর…বয়স বেড়ে গেলে কি কেউ বিয়ে করে?’ বিয়ে কথাটা অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় উচ্চারণ করল রূপ।
বন্দনা মৃদু গলায় বলল—‘তাহলেই বোঝো, এ কেমন বিয়ে।’
—‘মা প্লীজ, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি..তুমি এটা করতে পারবে না। করলে আমি চলে যাব। কোথায় যাব জানি না, আমার কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই, উঃ বাবা, বাবাগো, তুমি আমাকে আমার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এলে কেন? এখানে আমার কেউ নেই, কিছু নেই…’ রূপ সর্বহারার মতো দু’হাতে চুল ছিঁড়তে লাগল।
বন্দনা বলল—‘রূপু শান্ত হও। শোনো, ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছিল শুধু আমার জন্য নয়, তোমার জন্যেও বটে। তুমি একজন অভিভাবক পেতে, অভিজ্ঞ বন্ধু পেতে। তুমি যদি না চাও এরকম কষ্ট পাও তো হবে না…’ বলতে বলতে তার গলা বুজে এল।
রূপ বলল ‘উনিশ পার হয়ে কুড়ি বছর বয়স হতে চলল, আমার অভিভাবক? তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে অন্তত নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও।’
—‘তোমার কি মনে হচ্ছে উনি এলে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না? উনি বাধার সৃষ্টি করবেন?’
—‘উঃ মা, আই ডোন্ট নো। আই ডোন্ট কেয়ার, আই জাস্ট হেট দ্যাট ম্যান নাউ, ওঃ আমি পাগল হয়ে যাব!’
—‘আমি তো বলছি তোমার এরকম মনে হলে ঘটনাটা ঘটবে না।’
—‘মা ইউ আর সো কাইন্ড, ইউ আর আ নাইস নাইস গার্ল!’ রূপ অনেকদিন পর মাকে জড়িয়ে ধরল।
—‘ছাড়ো রূপ।’
—‘তুমি কষ্ট পাচ্ছ তাহলে? রাগ করে আছ। ওই লোকটা তোমাকে আমার কাছ থেকে টোট্যালি কেড়ে নিয়েছে?’
—‘কষ্ট পাচ্ছি! রাগ করছি, কারণ তুমি ছেলেমানুষের মতো উল্টোপাল্টা চিন্তা করছ। আমি তোমার মা, আমাকে কেউ তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে? এখন? কিন্তু আমারও তো একটা জীবন আছে। তুমি তোমার নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, আমি একলা-একলা কিভাবে দিন কাটাই, তুমি জানো? জানবার চেষ্টা কর?’
—‘কেন মা, আমার জীবনটা কি তোমার জীবন নয়? আমি কেরিয়ারটা নিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে আছি। একবার করে নিতে দাও না। তারপর দেখবে আমি আর তুমি কিরকম মজাসে থাকি; রূপের গলায় কাকুতি মিনতি।’
—‘সে তো ঘটনাটা ঘটলেও করা যায়। তুমি ঠিকভাবে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে রূপ। প্রথমটা হয়ত একটু আপসেট হয়ে যাচ্ছিস।’
—‘না, না,—’ রূপ চিৎকার করে উঠল।—‘আমি বন্ধু-বান্ধবের কাছে মুখ দেখাব কি করে? বাড়িতেই বা আমি কি করে টিঁকব? দোহাই তোমার মা যা চাও তাই করব, খালি বন্ধ কর বন্ধ কর ব্যাপারটা।’
বন্দনা ধীরে ধীরে অস্ফুট গলায় বলল—‘তাই হবে। ওঁর আসার কথা কিছুক্ষণ পরেই। তোমার সামনেই আমি ওঁকে বলব। তুমিও তোমার যা মনে হয়, যুক্তিটুক্তি সব বলতে পারো।’
রূপ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। ভয় ঘৃণা দুই-ই তার চোখে। বলল—‘আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হ্যাভ টু ফেস দ্যাট ম্যান। মা তুমিই ওকে যা বলার বলে দিও। আমি চললাম। পরে আসব।’ ঝড়ের মতো পায়ে চটি গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল রূপ।
সুদীপ্ত এলেন ঘণ্টাখানেক পরে। ওপরে এসে দেখলেন, বন্দনা দালানের চেয়ারে বসে আছে, গালে হাত। বললেন—‘কি ব্যাপার? নিচের দরজা খোলা। আবহাওয়ায় যেন ঝড়ের পূর্বাভাস।’
—‘পূর্বাভাস নয়। ঝড়টা হয়ে গেছে’—বন্দনা ধীরে ধীরে বলল।
—‘ঝড়? কিসের ঝড়?’
—‘রূপকে ওর পিসি আজ খেতে ডেকেছিল, জানিয়েছে, তারই প্রতিক্রিয়ায় ঝড়।’
—‘ও কি মানতে পারছে না?’—সুদীপ্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন।
—‘না। এখন ও তোমাকে হেট করে। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে গেছে—এ বিয়ে হবে না। ও লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। ওর কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। আর ও তো বড় হয়েই গেছে। মার দেখাশোনার ভার আর কিছুদিন পর থেকে ও-ই তো নিতে পারে।’
—‘তুমি কথা দিলে?’
—‘দিয়েছি। নইলে বলছিল হস্টেলে চলে যাবে। ওর কেউ নেই। আমি ওকে ওর নিজের বাড়ি থেকে উৎপাটিত করে এনেছি, ভুল করেছি। আজ অনেক দিন পর ও বাবাকে ডেকে কাঁদল।’
—সুদীপ্ত বললেন—‘উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে। ছেলেমানুষ তো নয়। একেই একটা জটিল মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এভাবে কথাটা ওকে বলা ঠিক হয়নি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে পারতে।’
—‘তুমি কি করতে?’
—‘আমি তো ভাবছিলাম। ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত ওকে জানাবারই পক্ষপাতী ছিলাম না। আগে রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে যেত। তারপর সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে যেতাম। ইনক্লুডিং রূপ। ইনক্লুডিং রঞ্জু, কলি, সঞ্জয়। তিনটে ঘর নেওয়া হত। সেই সময়ে আস্তে আস্তে ভাঙা হত খবরটা।’
—‘পাগল হয়েছ? সমুদ্রে গেলে ও জলে ঝাঁপ দিত। পাহাড়ে গেলে খাদে। তুমি ওর রকম সকম দেখনি তাই বলছ।’
—‘শোনো বন্দনা, ও যা-ই বলুক, যা-ই মনে করুক, মনে রেখ এটা ওর প্রথম প্রতিক্রিয়া। আইডিয়াটা নিজের মনে যত নাড়াচাড়া করতে থাকবে, পরিচিত হতে থাকবে, ততই আস্তে আস্তে মেনে নিতে সুবিধে হবে। প্রথমটা রেজিস্ট্রেশনের পর আমরা না হয় আলাদাই থাকলাম। তুমি এ বাড়িতে আমি আমার বাড়িতে। তুমি এভাবে ওকে কথা-টথা দিয়ো না।’
—‘দিয়েছি তো। দিয়ে দিয়েছি।’
—‘ও কিছু নয়। রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে যাক। আমরা যেমন আছি তেমনি থাকি। মাঝে মাঝে তুমি ওকে বোঝাবে। মাঝে মাঝে আমি। বুঝে যাবেই। বুঝে যাবার পর খবরটা বলব।’
—‘আর তা সম্ভব নয়। ও আমার কাছ থেকে কথা নিয়ে গেছে। আমি যদি সে কথার মর্যাদা রাখতে না পারি ওর কাছে আমার একটুও মান থাকবে না। ও একদম নষ্ট হয়ে যাবে। আমাকেও শেষ করে দেবে— এ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।’
—‘তুমি এতো ভেঙে পড়ছ কেন বন্দনা!’ সুদীপ্ত বন্দনার ঠাণ্ডা হাতের ওপর হাত রাখলেন—‘আমি বলছি এই বয়সের প্রতিক্রিয়াগুলো, এই রাগ, ঘৃণা অসহায়তা বোধ এ সমস্তই সাময়িক। সময় দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।’
বন্দনা হাসল, বলল—‘আমার ছেলেকে কি তুমি বেশি চেনো! এখনও সময় আছে। এখনও যদি ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি, ওকে বাঁচাতে পারব, নইলে ও একেবারে বিপথে চলে যাবে।’
ঘড়ির টিকটিক আর পাখা চলার মৃদু আওয়াজ ছাড়া পরবর্তী মিনিটগুলোয় প্রায় আর কোনও শব্দই রইল না। সুদীপ্ত সিগারেট ধরাতে ভুলে গেছেন। বন্দনা সেই একই রকম অনড় ভঙ্গিতে বসে। ঢং ঢং করে সাতটার ঘণ্টা বাজলে সুদীপ্ত বললেন—‘আমি তাহলে চলি, বন্দনা!’
বন্দনা উঠে দাঁড়াল, ব্যাকুল গলায় বলল—‘চলে যাবে? এখুনি? আবার কবে আসবে? কখন?’
সুদীপ্ত একটু সময় নিলেন, বন্দনার রুক্ষ মাথার ওপর আলতো করে একবার হাত রাখলেন, ক্লান্ত সুরে বললেন—‘আসব। কিন্তু কি লাভ?’
—‘লাভের কথা ভেবেই কি চিরদিন সব কাজ করেছ?’
—‘না, তা করিনি। কিন্তু এটা যে আলাদা বন্দনা…’ সুদীপ্তর গলা ভেঙে যাচ্ছে… ‘আমিও যে একজন তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ, আমার এভাবে চলতে খুব খুব কষ্ট হবে…তাছাড়াও তোমার ছেলের আমাকে ঘৃণা করাটাই যদি শেষ কথা হয়, তুমি যদি সেটাকেই মেনে নাও, ভয় পাও, তাহলে আমি এলে জটিলতা ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকবে। তুমি যা ভয় করছ তাই-ই হবে তখন। রাগে, ঘৃণায় ও বিপথে চলে যাবে।’
বন্দনা দাঁড়িয়ে রইল। সুদীপ্ত হাতটা একবার তার দিকে বাড়ালেন, তারপর আবার গুটিয়ে নিলেন, খুব মৃদুস্বরে বললেন—‘ভয় পেয়ো না বন্দনা। আসব, আমি আসব।’
সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন সুদীপ্ত। যে সিঁড়ি দিয়ে কয়েকঘণ্টা আগে নেমে গেছে রূপ। দু’জনেই বলে গেল আসব। কিন্তু শূন্য দালানের ওপর একা-একা দাঁড়িয়ে বন্দনার মনে হল ভুল, মিথ্যে। ওরা কেউ আর আসবে না। যতই সে মনকে চোখ ঠারুক, রূপ তাকে অনেকদিন ছেড়ে চলে গেছে। দু’জনের মধ্যে কোনও সখ্য, কোনও সাধারণ আগ্রহ, সাধারণ মূল্যবোধের ভিত্তি নেই। স্বভাবও সম্পূর্ণ বিপরীত। রূপ বহির্মুখী। সে ভীষণই অন্তর্মুখী। রূপ তার আগ্রহের জগৎ, আনন্দের জগৎ খুঁজে নিচ্ছে। মা তার একটা অভ্যাস, একটা সংস্কার, সেটাকে এখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি এই পর্যন্ত। মায়ের একটা প্রতিমা তার মনের মধ্যে গড়া আছে, প্রাণহীন প্রতিমা, যার মুখ চোখের ভাব চিরকালের জন্য স্থির। সে প্রতিমার ঘরে নিত্য পূজা হল কিনা, সেবা হল কিনা, তা নিয়ে রূপের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ওই ধূলিমলিন প্রতিমাটিকে সে বিসর্জন দিতেও পারছে না। আজকের ঘটনা ওর মনে স্থায়ী রেখা এঁকে দিল। ওর প্রতিমায় চিড় খেয়েছে।
সেই খুঁত-যুক্ত প্রতিমা এবার হয়ত ও কোনদিন বিসর্জনই দিয়ে দেবে। সুদীপ্তর পক্ষে এই বেলাশেষের সম্পর্কের কূল থেকে ফেরা খুব মুশকিল। তাঁকে বন্দনা অথই জলে ভাসিয়ে দিল। তার তবু নেই-নেই করেও ছেলে আছে। সুদীপ্তর কেউ নেই। কার কাছে ফিরে যাবেন? যাকে স্ত্রী বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন অনেক দিন থেকে, তাকে কি আর পরিচিত বন্ধুর মতো দেখা সম্ভব? হয়ত তিনি মাঝে মাঝে আসবেন। ক্লান্ত পা টেনে টেনে। নিজের মনকে জোর করে বুঝিয়ে। সেই আসার মধ্যে অভিমান পুঞ্জ হবে, অভিমান থেকে ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে উদাসীনতা, আস্তে আস্তে আনন্দটা কর্তব্য, তারপর কর্তব্যটা ভার মনে হবে। খুব গুরুভার। সুদীপ্ত তখন আর আসবেন না।
অধ্যায় ২৬
প্রদীপ বলল—‘আমি প্রস্তাব করছি, অভিরূপ আজ আমাদের সব্বাইকে পার্ক হোটেলে ডিনার খাওয়াবে।’
—‘আমি এই সাধু প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি,’ অংশু বলল। অঞ্জু একটা ঝটকা দিয়ে বলল—‘এটা তোমাদের খুব অন্যায়। এটা হতে পারে না। অভিরূপ এখন গার্জেনের হোটেলে খায়।’
অংশু বলল—‘কড়া ডোজ দিইছিস অঞ্জু, অভিরূপের জন্যে তোর প্রাণ কেঁদে উঠছে সেটাও অ্যাপ্রিশিয়েট করছি। কিন্তু বললে তো হবে না। অভিরূপ সাঁসালো পার্টি। একমাত্তর নয়নের মণি তার ওপর।’
অঞ্জু বলল—‘ঠিক আছে, আমি সংশোধনী প্রস্তাব আনছি অভিরূপ খাওয়াবে, তবে পার্ক হোটেল নয়, বসন্ত কেবিনে।’
হাত উল্টে প্রদীপ বললে—‘যা শালা। পার্ক হোটেল থেকে বসন্ত কেবিন। ইম্যাজিনেশন আছে অঞ্জুটার। হবে ওর। জীবনে কিছু পারবে।’ প্রস্তাব পাস হয়ে গেল।
অভিরূপ এতক্ষণে বলল—‘লে ল্লেঃ, পার্ক হোটেল! দেখেছিস কখনও ভেতরটা? কি ড্রেস পরে যেতিস যদি সংশোধনী ছাড়া প্রস্তাব পাস হয়ে যেত। আমি না হয় বাড়ি থেকে এনে টাকা ফেলে দিতাম।’
প্রদীপ বললে—‘কি ড্রেস দেখাচ্ছিস তুই বে! জানিস অদূর ভবিষ্যতে এসব হোটেল ফোটেল জনগণের হয়ে যাবে! তুই কি ব্রিটিশ আমল থেকে এলি নাকি? শালা কলোনিয়াল। এই অঞ্জু ওর কান মুলে দে তো!’
জলি বলল—‘এই তোমরা ব্যাকরণে ভুল করবে না একদম। অঞ্জু কি ওর শালী যে কান মুলে দেবে? কানমলার হক বউয়েদের থাকে না, শালীদেরই একমাত্র থাকে। দিই, অভিরূপ দিই!’
অভিরূপ একটু লাল হয়ে জলির বাড়ানো হাতের দিকে তাকিয়ে বলল —‘খবর্দার পকেট নিয়ে টানাটানি করছ কর। কান ফানে হাত দিতে এলে লাশ পড়ে যাবে।’
লাশ পড়ার কথায় সকলেই খুব হাসল। একে তো অভিরূপ এদের চোখে লালটুস, ক্যাবলা, তার ওপর ওদের ভাষা ভালো রপ্ত হয়নি, অথচ বলতে যায়। প্রয়োগে থেকে থেকেই নানারকম ভুল হয়।
আজকে ওদের সবারই আনন্দ মাত্রাছাড়া। কারণ অনেক দিন ঘোরাঘুরি করে অভিরূপ আজ অঞ্জুর ফাইন্যাল মত পেয়েছে। য়ুনিভার্সিটির আলাপ গড়াতে গড়াতে দু-তিন বছর হয়ে গেল, এখনও পুরো দলটার কফি-হাউজ অধিবেশন বন্ধ করার কোনও কারণ ঘটেনি। অংশুর প্রাইভেট টুইশন, প্রদীপ বাড়ির বাজার সরকার, বাজারের কমিশন থেকে খরচ চলে। অঞ্জু-জলি কিভাবে নিজেদের বাড়ি থেকে হাত-খরচ আদায় করে সেটা টপ সিক্রেট, ওরাই জানে।
বসন্ত কেবিনে কবিরাজি এবং ফাউল কারি দিয়ে উৎসব পালন করার পর অংশুরা নেহাত দয়া করে অভিরূপ আর অঞ্জুকে ছেড়ে দিল, বলল—‘যা যা, তোরা একটু ঘুরে ঘেরে আয়।’
অঞ্জুর পরনে কড়া কমলালেবু রঙের ছাপা শাড়ি। সেই একই রঙের লিপস্টিক, টিপ। প্রায় মাঝ-পিঠ অবধি চুল হর্সটেল করে বাঁধা—অঞ্জুর চোয়াল সামান্য উঁচু। নাকবসা। এবং ছড়ানো পৃথুল ঠোঁট। চোখ দুটি প্রতিমার চোখের মতো একটু ওপর দিকে বাঁকানো। চলনে বলনে, ভাষায় ভঙ্গিতে বেপরোয়া বিজয়িনীর প্রত্যয়। লম্বায় অভিরূপ তার থেকে ইঞ্চিখানেকের বেশি নয়। একেবারে গোলগাল, নধর, এক টুকরো কুচকুচে গোঁফ আর চশমায় হঠাৎ দেখলে গাম্ভীর্যটুকু ধরা পড়ে। ভালো করে দেখলে বোঝা যায়, সে যেন ধরা পড়েই আছে।
বাইরে বেরিয়ে সে বলল—‘এই অঞ্জু, উট্রামে যাবে?’
—‘আউটরাম? ধুস! দিলুটা রোজ আমায় আউটরামে নিয়ে যেত। পকেট গড়ের মাঠ! ওসব গঙ্গা-ফঙ্গা আমার ভাল লাগে না।’ দিলু অভিরূপের পূর্বসূরী। সেই আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটের দিনগুলো থেকে দিলুর সঙ্গে অঞ্জুর প্রণয় পর্ব চলছিল। দিলু ওকে একটা আংটিও পরিয়ে দিয়েছিল। নানারকম মনকষাকষির পর অঞ্জু আংটিটা খুলে দিয়েছিল। দিলু বলেছিল—‘ফেরত দিচ্ছ। দাও। আমিও মরে যাচ্ছি না। তুমিও না। দিলুও দেখবে কত ধান থেকে তুমি কতো চাল বের করতে পার।’
দিলুর ব্যাপারটা অভিরূপ জানে। দিলুর পূর্বে যে একটি নওলকিশোর ছিল সে-কথাও। কিন্তু তা সত্ত্বেও দিলুর নাম সে সহ্য করতে পারে না। বলল—‘দিলেটা একেন্নম্বরের বজ্জাত। ওর সঙ্গে তোমার কি?’
অঞ্জু সোজাসুজি বললে—‘আহা ন্যাকা! জানে না যেন।’
অভিরূপ হার মেনে বললে—‘ঠিক আছে, কোথায় যাবে বল।’
—‘সিনেমা! আবার কোথায়।’
—‘এখন? এখন তো ইভনিং শো আরম্ভ হয়ে গেছে! ঘণ্টা কাবার হতে চলল।’
—‘তাতে কি? আমাদের তো এয়ার কণ্ডিশনে বসা নিয়ে কথা! হলে বসে অঞ্জু বলল—‘তুমি ওদের মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন আমার মাথায় আসে না। তোমার মাকে বলো যোগীন্দরে ঢুকিয়ে দেবে!’
কথাটা যে অভিরূপের মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু সে জানে মাকে বলা বৃথা। নিজের কর্মক্ষেত্রে মা ভীষণ ডাঁট নিয়ে থাকে। ছেলের জন্যে উমেদারি করতে মায়ের মাথা-কাটা যাবে। বলল—‘ছাড়ো তো! সীরিয়াসলি লেগেছি যখন, ঠিকই পেয়ে যাব একটা।’
—‘দূর’ অঞ্জু বিরক্ত হয়ে বলল, ‘বছরের পর বছর ওয়েটিং রুমে বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না। দিদির বিয়ে হয়ে গেল, বোনের বিয়ে হয়ে গেল, আমার বেলাই খালি যত বেকার রাঙা মুলো জোটে।’
অভিরূপ আহত হয়ে বলল—‘অঞ্জু প্লীজ, তুমি আর একটু ভদ্রভাবে কথা বলা অভ্যেস করো, নইলে তোমাকে আমি মায়ের কাছে নিয়ে যাব কি করে?’
অঞ্জু অম্লানবদনে বলল—‘যা বলেছ! অংশু-ফংশুর সঙ্গে মিশে আমার একটা পার্মানেন্ট ল্যাঙ্গোয়েজ প্রবলেম হয়ে গেল। কি যে করি। তোমার মা আবার যা, দেখলে ভয় লাগে।’
—‘ভয়? কিসের ভয়!’
—‘কী গম্ভীর। তার ওপরে সিলভার-টনিকে লাল হয়ে আছে। ডাঁটিয়াল। যাই বলো বাবা।’
অভিরূপ বলল—‘অঞ্জু, তুমি একটা ইমপসিবল, মা খুব ভালো লোক। একটু গম্ভীর বরাবরই। কিন্তু সেটা হাই-ব্ৰাণ্ড বলে নয়। অনেক শোক দুঃখ পেয়েছে তো। দেখ তুমি গিয়ে যদি হাসি ফোটাতে পারো।’
অঞ্জু ঘুরে বসে বলল—‘দেখ অভিরূপ, তুমি যদি ভেবে থাক, আমি তোমাকে বিয়ে করব, তোমার মায়ের মুখে হাসি ফোটাবার মিশন নিয়ে, তবে কাটো। এক্ষুনি কাটো।’
হল মোটামুটি ফাঁকা। ওদের সিট রীয়ার স্টলে। তবু অঞ্জুর শেষ কথাটার তীক্ষ্ণতায় দু চার সারি সামনে বসা কয়েকজন ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন। চাপা গলায় বললেন—‘চুপ করবেন?’
অভিরূপ বলল—‘দেখলে তো? সত্যিই কিন্তু তোমার কথাবার্তার ধরন চেঞ্জ করতে হবে আমাদের বাড়ি যেতে হলে।’
অঞ্জু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—‘দেখা যাবে।’
এই দলটার সঙ্গে অভিরূপের আলাপ-পরিচয় হয়েছে ইউনিভার্সিটি থেকে। ওর স্কুলের সঙ্গীসাথীরা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেনি। দু একজন বিদেশে চলে গেছে। কলেজের যে সবচেয়ে বন্ধু, সে-ও কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে এখন ট্রেনিং-এ আছে। অভিরূপের মুশকিল হল সে কিছুতেই একটাতে লেগে থাকতে পারে না। নইলে তার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারেই খারাপ না। কমপিটিটিভ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে গিয়ে অনার্সটা ভালো হল না, অনার্সটা করতে গিয়ে কমপিটিটিভ পরীক্ষাটাও না। তাছাড়া অনার্সের ফল খারাপ হয়ে যাওয়ায় সে এমনি দমে গেল, আর সর্বভারতীয় পরীক্ষার পড়ার জন্য নিজেকে তৈরি করতেই পারল না। ইউনিভার্সিটিতে অনেক কষ্টে সুযোগ পাওয়া গেল পলিটিক্যাল সায়েন্সে। তার কলেজের সহপাঠীরা বরানগরে চলে গেল ইকনমিক্স পড়তে। অভিরূপ একদম একা পড়ে গেল। মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কে আজকাল কেমন একটা আড়ষ্টতা এসে গেছে। খারাপ রেজাল্ট দেখে মা খুব মুষড়ে পড়েছিল। ‘ইসস্, এতো খারাপ হল কেন রে, রূপ? তুই বড্ড দুটো তিনটে জিনিস একসঙ্গে করতে যাস। একূল-ওকূল দুকূল যায়।’
—‘গেছে গেছে, সবাই যদি এখন রঞ্জনলাল মুখার্জি না হতে পারে।’
কলির ছেলে রঞ্জন কলকাতার এক নাম করা স্কুলের নাম করা ভালো ছেলে। মা বলল—‘কারুর সঙ্গে তুলনা করবার দরকার কি?’
—‘তুলনা আমি করিনি, তুমি করছ।’
—‘আমি আবার কখন তুলনা করলুম?’
—‘মনে মনে করেছ। করা অবশ্য স্বাভাবিক। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। আমার লাকটা তো গোড়া থেকেই খারাপ। একদম গোড়া থেকে।’
মা একটু চুপ করে থেকে বলল—‘রূপ, পরীক্ষায় ভালো মন্দ থাকবেই। আমি কথার কথা বলেছি। ও নিয়ে বেশি মন খারাপ করবার দরকার নেই। তুই আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে যা।’
‘—না।’ রূপ তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল।
মা আস্তে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে।
রাত্রে খেতে বসে নরম গলায় রূপ বলল—‘মা দেখ, এম-এতে আমি ভালো করবই।’
মা ভয়ে ভয়ে বলল—‘ইকনমিক্স পাবি তো?’
—‘এই মার্কসে ইকনমিক্স হবে না। আমাকে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়তে হবে। তবে আমার কথা লিখে রাখো যে যুগটা আসছে সেটা পল সায়েন্সের যুগ। তাছাড়া আই এ এসের জন্য তো আবার বসছিই।’
মা উদ্বিগ্নস্বরে বলল—‘এম-এটা করে নে না। তারপর আই এ এস-এর কথা ভাবিস।’
—‘এই জন্যেই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা চলে না। তুমি এতো ওল্ড ফ্যাশনড। এখন আর একেক্কে এক দুয়েক্কে দুই-এর দিন নেই। এখন একসঙ্গে সব করতে হবে। খেলাধুলো, পড়াশোনা, রাজনীতি, স—ব।’
মা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—‘রূপু, তুই সত্যিই এখনও বড় ছেলেমানুষ। একটু আমার কথা মেনেই দেখ না কি হয়। নিজের মতে চলে তো একটা রেজাল্ট…’
রূপ মাংসের বাটিটা ঠেলে দিল, বলল—‘দূর, খাব না, ভাল লাগে না।’
মা বলল—‘না, না তুই খেয়ে নে। আমি আর কিছু বলব না।’
রূপ দেখল পরের দিনই পিসি এল, পিসিতে মায়েতে কিসব গুঞ্জন হল, পিসি যাবার সময়ে বলে গেল—‘রূপু, তোকে তোর পিসে ডেকেছে, কাল পরশুর মধ্যে একবার যাস।’
যাবে না যাবে না করেও অভিরূপ গিয়েছিল। পিসে সে সময়ে একটা খুব লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছিল। ওদের অফিসে সেলস-ট্রেনি নেওয়া হচ্ছে, রূপ যদি দরখাস্ত করে পিসে চেষ্টা করবে। রূপ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেছিল—‘মার্কেন্টাইল ফার্মের চাকরিতে কি সিকিওরিটি আছে পিসে? সম্মানই বা কি? চাকরি হল সরকারি চাকরি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস।’
পিসে হেসে বলেছিল—‘আমার কাছে তো এই চাকরিটাও বেশ সিকিওর আর বেশ প্রেসটিজিয়াসই মনে হচ্ছে রে। এসব চাকরিতে উন্নতির সুযোগ অনেক। ভেবে দেখ, এ সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না। এম-এ পাস করতে করতে বয়স বেড়ে যাবে।’
—‘ভেবে দেখি।’
বাড়িতে ফিরে মায়ের সঙ্গে একচোট হয়ে গেল।
মা বলল—‘সঞ্জয় কি বলল রে?’
—‘জানোই তো সব।’
—‘সত্যি জানি না।’
—‘কেন পিসিতে তোমাতে চুপিচুপি কি যে সব চক্রান্ত করলে আমার বিরুদ্ধে।’
মা গম্ভীর হয়ে বলল—‘পিসে তোমাকে কিছু যুক্তি পরামর্শ দেবে, তাই শুনেছি। বলতে ইচ্ছে হয় বলো, নইলে থাক।’
অভিরূপ বলল—‘আচ্ছা মা, আমাকে বইতে কি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। ইউনিভার্সিটির মাইনে আর বইপত্রের টাকাটা কি খুব বেশি।’
—‘এ কথা কেন?’
—‘কই রঞ্জনলাল মুখুজ্জেকে তো কেউ চাকরির অফার করছে না। সে তো যত খুশি পড়ার চান্স পেয়ে যাচ্ছে। সে কি তার বাবা আছে বলে।’
মা বলল—‘রঞ্জন এখনও স্কুলের গণ্ডিই পেরোয়নি। তবে হ্যাঁ তাকে ডাক্তারি পড়াবার জন্যে তৈরি করা হচ্ছে এটা ঠিক। কিন্তু রূপ তোমার যে বাবা নেই, তোমাকে যে যত শিগগির সম্ভব নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মায়ের পাশে, এটা তোমার জায়গায় অন্য যে কোনও ছেলে নিজেই বুঝে নিত। নিজেই ভাবত। আমার অবস্থাও যেমন অন্য পাঁচজন মায়ের মতো নয়, তোমার অবস্থাও তেমন কখনই অন্য পাঁচজন ছেলের মতো নয়। তোমার বাবা নেই। ইট রিয়্যালি মেক্স ভেরি ভেরি বিগ ডিফারেন্স।’
রূপের কাছে মায়ের উত্তরটা অপ্রত্যাশিত। বাবা না থাকার প্রসঙ্গটা বরাবর মাকে খুব দুর্বল কাঁদো-কাঁদো করে দেয়, সচেতনে না হলেও এটাকে অস্ত্র হিসেবে বহুবার ব্যবহার করে ফল পেয়েছে সে। হঠাৎ সে কিছু জবাব দিতে পারল না। ভুরু কুঁচকে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।
অনেক রাত অবধি ঘুম আসছিল না। মায়ের হাত কপালের ওপর। —‘রূপ।’
রূপ পাশ ফিরে শুল।
মা কোমল গলায় বলল—‘তুই চাকরির কথায় ওরকম ভেঙে পড়ছিস কেন? আমি সঞ্জয়কে ফোন করেছিলুম। চাকরিটা খুব ভালো, তুই ঘুরতে ভালোবাসিস, ঘুরতে পারবি। স্কুটার কিনবি একটা। আর চাকরি করতে করতেও তুই আই এ এস-এর জন্যে তৈরি হতে পারবি। সবাইকার ক্ষমতা কি এক ধরনের হয়। রঞ্জুর একদিকে মাথা খোলে তোর অন্যদিকে মাথা খেলবে। আমার ধারণা হাতে কলমে কাজ করে শিখতে তোর ভালো লাগবে রে রূপ।’
—‘তুমি তাহলে চাও আমি, চাকরিই করি?’
—‘চাই, কিন্তু পড়াশোনায় ইতি করে নয়। রোজগারের ধান্দার জন্যও না। তোর একটা চেঞ্জ দরকার। একঘেয়ে মুখস্থবিদ্যার আবহাওয়ায় তুই ফুটতে পাচ্ছিস না। চাকরি করলে তুই ছোট হয়ে যাবি না। কিছুদিনের মধ্যেই দেখবি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবি।’
—‘ঠিক আছে তুমি যদি তাই চাও, তাই হবে।’
—‘আমি চাই বলে কিছু করিসনি। নিজে ভেবে-চিন্তে ভালো মনে করতে হয় তো কর। নইলে থাক।’
অনেক রাত পর্যন্ত মা রূপের কপালে হাত বুলিয়ে দিল। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল রূপ।
বন্দনা জানলার ধারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে রাতটা কাটিয়ে দিল। সে এতদিনে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে রূপের আর পড়াশোনা হবার নয়। ও সব সময়ে নিরাপত্তাবোধের অভাবে ভুগছে। এক জিনিস থেকে আরেক জিনিসে ওর আগ্রহ বদলে যাচ্ছে। মতি স্থির থাকছে না। সঞ্জয় ঠিকই বুঝেছে। চাকরিটা পেলে, চাকরি করলে, ওর আত্মবিশ্বাস আসবে, ও স্থির হবে, ব্যবস্থিত হবে। হে ঈশ্বর চাকরিটা যেন ও করে।
সকালবেলায় রূপ খুশি মেজাজে বলল, ‘য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তিটা তো হয়ে থাকি। চাকরিটা যদি না-ই হয়।’
সঞ্জয় যেভাবে কথা বলেছিল তাতে বন্দনার সন্দেহ ছিল না যে চাকরিটা ওর হবেই, তবু বলল—‘সে তো ঠিকই, ভর্তি হয়ে থাকতে আপত্তি কি?’
ফর্ম জমা দেবার লাইনে রূপের ঠিক সামনে দাঁড়িয়েছিল অংশু। ওর কলেজেই পড়ত, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। ওকে দেখে বলল—‘এই যে রূপচাঁদ, এসে গেছিস? সব মাল এক ধার থেকে পল সায়েন্সে। ওই দ্যাখ তিনু, আমাদের তিনকড়ি রে, ওই প্রদীপ।’
এই সময়ে অংশু আর রূপের মাঝখানে দুটি মেয়ে এসে ঠেলেঠুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।
অংশু বলল—‘যাশ শালা, এ আবার কি? এই, এই ম্যাডাম কি হচ্ছে, এটা একটা কিউ।’
একটি মেয়ে ঠোঁটের অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল—‘কিউ? তাই বুঝি। এই জলি, এরা বলছে এটা কিউ। কিউ কি রে? শুনেছিস কখনও?’
জলি নামধারিণী হাত নেড়ে বললে—‘ছেলেমানুষ বলছে, ওদের বলতে দে।’ এরকম অদ্ভুত সংলাপ অভিরূপ তো দূরের কথা অংশু পর্যন্ত কখনও শোনেনি। অংশুকে দেখে মনে হল সে হার স্বীকার করে নিয়েছে। বলল—‘কোন কলেজ ম্যাডাম? ’
মেয়েটি বোঁ করে পেছন ফিরে গেল, তারপর আবার সামনে ফিরে বলল—‘হল?’
—‘কি হবে?’
—‘ওই যে কলেজের নাম জিজ্ঞেস করলেন। গায়ে লেখা আছে, দেখলেন?’
অংশু বলল—‘যাঃ শালা।’
জলি হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল—‘ব্যাকরণে ভুল করে ফেললেন দাদা, না ভাই, আচ্ছা দাদাভাই, আ-কারের জায়গায় ঈ-কার হবে।’
দু’জনেই হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল।
অংশু বলল—‘আপনাদের নাম কি?’
জলি বলল—‘মাইরি।’
—‘মাইরি নাম? ধুর।’
—‘নাম কেন হবে। আপনার বাক্যটার পাদপূরণ করে দিলাম।’ অংশু বোকার মত হাসল।
জলি বলল—‘আমার নামটা অলরেডি আউট হয়ে গেছে। জলি, শুধু জলি, পদবী, উপাধি ইত্যাদি ফালতু ব্যাপারে বিশ্বাস করি না। আর উনি হচ্ছেন মিস অঞ্জু সরদার। পুরো নাম অঞ্জলি। কিন্তু অমন আদ্যিকেলে নাম ওকে মানায় না বলে ছেঁটে কেটে ছোট করে নিয়েছি। ফিল্মে চান্স পেয়েছে। যে সে না।’
অভিরূপ এতক্ষণ চুপ করেছিল, লোভ সামলাতে না পেরে বলল—‘একসট্রা না কি?’
জলি বলল—‘একসট্রা? তুমি হও গে ভাই গণেশদাদা। অঞ্জু ভ্যাম্প-এর রোল ছাড়া নেয় না। গড়িয়ে গড়িয়ে নাচতে হয়। চোখ নাচবে, কোমর নাচবে, সব নাচবে, পারবেন? কি গণেশদাদা পারবেন?’
অঞ্জু বললে—‘বাদ দে। বাদ দে।’
ওদের দু’জনকে অনায়াসে টপকে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে অঞ্জু বলতে লাগল—‘লেডিজ ফার্স্ট, লেডিজ ফার্স্ট ।’ সবার আগে ফর্ম জমা দিয়ে রিসিট চোখের ওপর নাচাতে নাচাতে বেরিয়ে গেল।
অংশু বললে—‘বোওল্ড। ক্লীন বোওল্ড। এক্কেবারে তুখোড় ইয়র্কার রে! ব্যাটের তলা দিয়ে গলে গেল।’ তারপর গলা নিচু করে বলল—‘চাবুকের মতো ফিগার, দেখেছিস অভিরূপ?’
এই নতুন ইয়ারদের হুল্লোড়ের জগতে এমন নেশাড়ের মতো জমে গেল রূপ যে ইনটারভিউয়ের দিন সে যখন আড়াই ঘণ্টা লেট করে সঞ্জয় পিসের বিখ্যাত আপিসে পৌঁছল তখন সেটা কতটা ট্র্যাফিক-জ্যামে আটকে পড়া বা রাস্তার আধলা ইঁটে হোঁচট খেয়ে পা কেটে যাওয়ার জন্য আর কতটা ভেতরের অনিচ্ছা থেকে, বলা শক্ত।
এখন সেই চাকরিটার কথা ভেবে তার হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে হয়।
অধ্যায় ২৭
পঁচিশ বছরের জন্মদিন পালনটা রূপের একদম পছন্দ নয়। একে তো একটা ধেড়ে ছেলে, তার ওপরে বেকার। তার আবার জন্মদিন। পনের বছরের জন্মদিনটা খুব ঘটা করে পালন করা হয়েছিল। প্রত্যেক বছরই পিসিরা আসে, সে বছর আরও কেউ কেউ এসেছিলেন। পিকনিক, সিনেমা, গান, কিন্তু সেসব দিনের কথা রূপ মনে আনতে চায় না। জন্মদিন আবার কি! করতেই যদি হয়, তো পায়েস-ফায়েস করে খাইয়ে দিলেই তো হয়। লোককজন ডাকা আবার কি। কিন্তু বন্দনা কিছুতেই শুনবে না। আসলে তাদের জীবনে উৎসবের সুযোগই নেই। অথচ মাঝে মাঝে পাঁচজন অতিথি এসে হই-হল্লা করলে ভালো লাগে। শেষে রূপ বলল,—‘ঠিক আছে আমার কয়েকজন বন্ধুকে বলব, কিন্তু তাদের তুমি বলতে পারবে না অকেশনটা কি।’
বন্দনা বলল—‘তোর বন্ধুরা অনুপ, কিশোর, সন্দীপ, সুমন সবাই জানে।’
রূপ চুপ করে গেল। আসলে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে তার আজকাল আর যোগাযোগ নেই। এই সুযোগে সে অঞ্জু অংশুদের গ্রুপটাকে বাড়িতে আনবার কথা ভাবছে।
কথা ঘোরাবার জন্য সে বলল—‘আমার পঁচিশ বছর বয়স হয়ে গেল? ইসস মা।’
বন্দনা হেসে বলল—‘বয়স তো বেড়ে যাবেই রে। দুঃখ কেন?’
—‘দূর এতো চেষ্টা করছি, এখনও পর্যন্ত একটা চাকরি জোগাড় করতে পারছি না।’
—‘চাকরির বাজার ক্রমশই খারাপ হচ্ছে রে রূপু। টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন না থাকলে খুব মুশকিল। যাই হোক, এম-এটা তো করে ফেলেছিস। একটা ঠিকই পেয়ে যাবি।’
—‘মা, তোমাদের ওখানে হয় না, না?’ রূপ সাহস করে বলেই ফেলল। বন্দনা বলল—‘আমাদের ওখানে ইউনিয়ন এতো স্ট্রং, তাদের বায়নাক্কাও ভীষণ। সেরকম কোনও ওপনিং হলে আমি চেষ্টা করব। তবে সে সম্ভাবনা কম।’
অনুপম সোম এখন পার্সোনেল ম্যানেজার। কোনক্রমেই বন্দনা তাকে। জানাতে পারবে না সে এখানে ছেলের চাকরির চেষ্টা করছে।
—‘মা, পিসেকে একবার বলে দেখবে?’
বন্দনা বিষন্ন হয়ে গেল। বলল—‘দেখ রূপু অন্য লোকেদের যা-যা থাকে আমাদের তার অনেক কিছুই নেই। শুধু সম্মানটা আছে। তোর পিসি পিসে সত্যিকারের ভালো লোক, আমাদের হিতৈষীও। সেবার তুই ইনটারভিউটাতে গিয়ে পৌঁছতে পারলি না, সঞ্জয়কে খুব অপদস্থ হতে হয়েছিল। ও অবশ্য আমায় কিছু বলেনি। কিন্তু এখন যদি চাকরির জন্য ওকে ধরি, ওর সম্মান নষ্ট হবে। আমারও নষ্ট হবে।’
অসন্তুষ্ট মুখে রূপ বলল—‘তোমরা যে কি বলো মা। কোনকালে কি ঘটনা ঘটেছিল, সঞ্জয় পিসের অফিস-অলারা কি সব মনে করে রেখেছে?’
বন্দনা বলল ‘এক কাজ কর না। তুই নিজেই পিসেকে গিয়ে বল না। তাহলে তোর আগ্রহটাও বুঝবে।’
কথাটা রূপের মনে লাগল। সঞ্জয় পিসে খুব মাই-ডিয়ার লোক। সেবার সে কৈফিয়ত দিয়ে এসেছিল পায়ের ব্যাণ্ডেজ দেখিয়ে। পিসেমশাইয়ের মুখ থাকেনি অফিসে, কিন্তু তাকে তেমন কিছু বলেননি। শুধু বলেছিলেন—‘আরে তুমি একটা ইয়ংম্যান, পায়ে ব্যাণ্ডেজ নিয়েই আসতে। কি ক্ষতি ছিল? আর জ্যাম-ট্যাম থাকলে সেরেফ হেঁটে মেরে দেবে, তোমার পা-গাড়ি তো আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। জীবনে উন্নতি করতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হবে মাস্টার।’
সঞ্জয়-পিসের কাছে একবার বোধহয় যাওয়া যায়। বাড়িতে না। অফিসে। যেতে হবে পার্ক সাকাস। এসপ্লানেড থেকে বাস বদল করতে হবে। প্রোসেশন বেরিয়েছে দেখে রূপ বাস থেকে নেমে পড়ল, হ্যারিংটনে ঢুকে পড়ল, চৌরঙ্গি রোডে এখন গাড়ি বহুক্ষণ থেমে থাকবে। হঠাৎ ডান দিকের বিল্ডিংটায় ওর চোখ আটকে গেল, এই বাড়িটার তিন তলায় ‘পেগাসাস অ্যাডভার্টাইজিং’এর অফিস। রূপ ঢুকে পড়ল। তিনতলায় উঠেই চিনতে পারল জায়গাটা। যদিও আরও অনেক সাজ-সজ্জা হয়েছে, চতুর্দিক কাচে মোড়া, দেয়ালে দেয়ালে মুর্যাল। ঠাণ্ডা ঝলক চতুর্দিক থেকে। বদলেছে, তবু চেনা যায়, নির্দিষ্ট ঘরের সামনে গিয়ে পিওনকে চিরকূট দিল। লিখবে নিজের নাম? যদি দেখা না করেন? নাঃ, লিখে ফেলা যাক, যা হয় হবে।
চিরকূট পাঠাবার পর মুহূর্তেই পিওন এসে বলল—‘যান, ডাকছেন।’ ভেতরে ঢুকতে রূপের পা বেধে যাচ্ছে। খানিকটা মোটা কার্পেটের কারণে, খানিকটা অন্য কারণে। টেবিলের ওধারে দেয়াল ভর্তি নানান সাইজের, নানান প্রকারের বিজ্ঞাপনী ছবির পটভূমিকায় সুদীপ্তকাকুর সাদার ছোঁয়া লাগা কালো চুল। ভারি চশমা। সিগারেটের ধোঁয়ায় কালচে ঠোঁট, আঙুল। সেই মুখ সামান্য ভারি।
—‘কি ব্যাপার? বসো।’
রূপ সসঙ্কোচে বলল—“আপনি ভালো আছেন, মাস্টারমশাই।’
—‘কেন তোমার কি সন্দেহ আছে তাতে?’ সুদীপ্ত হেসে বললেন, —‘তারপর কি করছ? আঁকাটা একেবারেই ছেড়ে দিলে?’
—‘আবার ধরব ভাবছি, কিছু কিছু অলরেডি এঁকেছিও। দু-একটা। ধরুন বইয়ের প্রচ্ছদ। কিছু কিছু অ্যাড-এর লে-আউট। জাস্ট ফর ফান…’ রূপ একটু ইতস্তত করে থেমে গেল।
সুদীপ্ত খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন—‘তুমি কি চাকরি খুঁজছ রূপু?’
রূপ চুপচাপ মুখ নিচু করে বসে। কিচ্ছু বলতে পারছে না।
সুদীপ্ত বললেন—‘তুমি পরদিন তোমার কাজগুলো নিয়ে এস, ধরো কাল কি পরশুর মধ্যে। আর এই অ্যালবামটা দিচ্ছি দেখ একটু বসে।’ সুদীপ্ত ড্রয়ারের মধ্যে থেকে একটা বিরাট অ্যালবাম বার করলেন। রূপ দেখতে লাগল। সুদীপ্ত রূপকে দেখতে লাগলেন। একবারও তার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন না।
আজ রূপ মাকে চমকের পর চমক দিচ্ছে। ‘মা, এই হল অংশুমান আমার ইউনিভার্সিটির বন্ধু। এ অঞ্জু, এই প্রদীপ’, মার মুখে সামান্য বিস্ময়। অনুপ, সন্দীপদের যে সে বলেনি একথা রূপ মাকে জানায়নি। বন্ধুদের সঙ্গে বান্ধবীদের সংযোজনের কথাও না।
জলি বলে উঠল ‘মাসিমা, আপনাকে কি সুন্দর কি ইয়ং দেখতে। অভিরূপের দিদি বলে মনে হয়।’
বন্দনা অবাক হয়ে তাকাল। এরকম কথা যে তার মেয়ের বয়সী একটি মেয়ে এভাবে বলতে পারে সেটাই তার কাছে আশ্চর্য। সে কথা ঘোরাবার জন্য বলল—‘তোমাদের কাউকেই আমি আগে দেখিনি। রূপ আগে এদের সঙ্গে পরিচয় করাসনি তো।’
—‘টাইম নিচ্ছিল’ অঞ্জু দাঁতে নখ কাটতে কাটতে জবাব দিল, তারপর বলল—‘অভিরূপ তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করাবে না?’
প্রদীপ বলল—‘এই অঞ্জু, কি বলছিস? জানিস না।’
জলি বলল—‘এ মা!’
বন্দনা একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলল—‘তোমরা গল্প করো আমি আসছি। সে চলে যাবার পর সবাই অঞ্জুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রদীপ বলল—‘কি রে অঞ্জু জানতিস না অভিরূপের বাবা নেই?’
অঞ্জু একইভাবে দাঁতে নখ কাটতে কাটতে বলল—‘না বুঝতে পারলে কি করব?’
রূপ আশ্চর্য হয়ে ভাবল—সবাই জানে, অঞ্জু জানে না? হতে পারে? তাছাড়া অঞ্জুকে যেন সে নিজে একবার বলেছে। কবে কোথায় মনে করতে পারছে না, কিন্তু নিশ্চয়ই বলেছে।
সারা সন্ধে ঝমঝমে বাজনা বাজল রেকর্ডে, সমস্বরে গান তার সঙ্গে অন্যান্যবারের মতো টেবিলে খেতে দেওয়া গেল না। রূপ এক ফাঁকে মাকে এসে বলল—‘মা তুমি আমায় একটা একটা করে প্লেট দিয়ে দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি। ওরা গানে গল্পে এতো মেতে আছে যে টেবিলে এসে খেতে চাইছে না।’
টেবিল ফুল দিয়ে সাজিয়েছে বন্দনা, খাবারগুলো সব বুফের জন্য আলাদা আলাদা প্লেটে রাখা, বলল—‘ঠিক আছে নিয়ে যা।’ ছটা প্লেটই রূপ একে একে বয়ে নিয়ে গেল, দ্বিতীয়বার আরও কিছু নিতে এল রূপ। তৃতীয়বার এল জলি।
—‘মাসিমা রান্না দারুণ হয়েছে। চাটনি আর কাটলেটটা আর একটু দিন না।’ বন্দনা বলল—‘চলো না আমি যাচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি।’
জলি হেসে বলল—‘ওখানে আপনি যেতেই পারবেন না। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার, সাদা কাঠি পেছনে লুকোলেও টের পাবেন।’
বন্দনার নির্দেশমতো হাতটা ধুয়ে নিয়ে জলি কাটলেট আর চাটনি নিয়ে গেল। ছেলের জন্মদিনের আমোদ আহ্লাদ রূপের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল, পরিশ্রমের ভাগটুকু মায়ের। রান্নাঘর আর দালানের মধ্যে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করে বন্দনা তার সেই তৃতীয় ঘরের একলা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আজকেও তার জানলার তলায় অন্ধকারের বৃত্ত। অথচ চার পাশে আলো জ্বলছে। এই বাড়ির সামনের আলোটাই বার বার খারাপ হয়ে যায়। রাস্তার আলো মুখে পড়ে না বলে একরকম স্বস্তিও হয়। রূপের বন্ধুবান্ধবীরা হই হই করে চলে গেল। সদর দরজার কাছে হল্লার শব্দ। ‘ফির মিলেঙ্গে’, ‘রূপচাঁদ চলি।’ ‘অভিরূপ মাসিমাকে বলে দিস ফার্স্টক্লাস খেলাম।’
পাঁচটি ছায়ার পেছন পেছন ষষ্ঠ ছায়া রূপও ওদের এগিয়ে দিতে গেছে। রাত এখন সাড়ে দশটা। মেয়ে দু-টি কোথায় থাকে, কিভাবে পৌঁছবে। বন্দনার একটু ভাবনা হল, এরা নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু কিরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন সৌজন্যহীন ধরন এদের। মেয়ে দু-টিও ছেলেদের সঙ্গে সমানে তাল দিচ্ছে। এরকম ধরনের মেয়ে বন্দনা কোনদিন দেখেওনি, কল্পনাও করেনি।
নিচে খিল তোলার শব্দ হল। দু তিনটে সিঁড়ি টপকে টপকে রূপ ওপরে আসছে। এত খুশি তাকে যেন বহুদিন দেখেনি বন্দনা।
—‘মা, মা।’
—‘কি রে?’ রূপ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।
রূপ ঝলমলে মুখে বলল—‘ওঃ মা যা রেঁধেছিলে আজ। তুলনা হয় না। ওরা সবাই বলল ফাটাফাটি।’
বন্দনার মুখে পাতলা হাসি ভেসে উঠেছে, বলল, ‘তুই খুশি হয়েছিস?’
জবাব না দিয়ে রূপ মাকে জড়িয়ে ধরল। রূপের ঠোঁটের ওপর একটুকরো গোঁফ ছিল ক’দিন আগেও। কামিয়ে ফেলেছে। মুখটা একটু অপরিচিত লাগে। মাথায় ওর অনেক নরম চুল, বোধহয় খুব নেচেছে কুঁদেছে। তাই এলোমেলো হয়ে আছে। রূপের মুখ ওর ঠাকুমার মতো, একটু গোলগাল, দাঁতগুলো হাসলে দেখা যায়। ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল ছিল আগে, এখন বোধহয় সিগারেটের গুণে একটু মেরুন-বেগুনি রং ধরেছে। রূপ তার বাবার মতো লম্বা নয়, মাঝারি দোহারা চেহারা, একটু অসাবধান হলেই থলথলে হয়ে যাবে। বন্দনার মনে হল, রূপ বড় হয়নি। বড় হবেও না কোনদিন। যদিও ও নিজেকে খুব বড়ই মনে করে।
বন্দনার পেছন পেছন ঘরে ঢুকে রূপ ধপাস করে খাটে বসে পড়ল—‘ওরা কেউ অকেশনটা বুঝতে পারেনি মা, পারলে এইসা প্যাঁক দিত।’
—‘প্যাঁক? সে আবার কি?’
রূপ বলল—‘পেছনে লাগা আর কি। আজকালকার এই ভাষাগুলো তোমাদের হয়ত বাজে মনে হবে, কিন্তু দারুণ এক্সপ্রেসিভ। মা ওদের কেমন লাগল তোমার?’
—‘কিছু লাগবার মতো আলাপ আর করালি কই।’
—‘ওরা আসলে তোমাকে একটু সমীহ করছিল। প্রথম দিন তো। জলি আর অঞ্জু আবার আসবে।’
আবার আসবে? বন্দনা চুপ করে রইল। তারপর তাক থেকে একটা বই পেড়ে বলল—‘রূপু তোর জন্মদিনের উপহার। রাসেলের অটোবায়োগ্রাফি। রূপ মোড়ক খুলে দেখল। বন্দনা বলল—‘একটু একটু করে পড়বি। ফিরে ফিরে পড়বি।’
রূপ বলল—‘তা তো বটেই। আচ্ছা মা ওদের মানে জলি আর অঞ্জুকে কেমন লাগল?’
—‘কোনজন জলি? কোনজন অঞ্জু?’
—‘ওই যে ভায়োলেট শাড়ি পরা ওইটে অঞ্জু।’
বন্দনা বুঝতে পেরেছিল, তবু জিজ্ঞেস করল। মেয়েটি চোলি পরেছিল চুমকি দেওয়া। গোছা গোছা বেগুনি কাচের চুড়ি।
মেয়েটি অভিরূপের বাবার সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিল। সে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল—‘ও জানে না তোমার বাবা অনেকদিন চলে গেছেন!’
রূপ অপ্রস্তুত মুখে বলল—‘খুব বেশিদিনের আলাপ তো না, হয়ত বলিনি।’
—‘অনুপদের সঙ্গে কি আজকাল তোমার সম্পর্ক নেই?’
—‘তা থাকবে না কেন? কিন্তু এরা একটা আলাদা গ্রুপ, হয়ত মিশ খাবে না, তাই বলিনি।’
—‘ওদের সঙ্গে মিশ খাবে না, তোর সঙ্গে খেল কি করে?’
রূপ মাথা চুলকে বলল—‘তোমার ওদের পছন্দ হয়নি, না?’
বন্দনা একটু হেসে বলল—‘পছন্দ হবার মতো নয়, সেটা তুই নিজেই বুঝতে পারছিস তাহলে।’
—‘অঞ্জুকেও তোমার ভালো লাগেনি, না?’
বন্দনার ভেতরে এবার ইলেকট্রিক শক। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।
—‘মা কথা বলছ না কেন?’ রূপ ঝুঁকে পড়ে বলল—‘ভালো অবশ্য না-ও লাগতে পারে, বাইরে থেকে ওকে দেখলে একটু উদ্ধত মনে হয়।’
—‘ভেতরটা উদ্ধত নয় বলছিস?’
রূপ আর পারল না—‘মা শী ইমপ্রুভস্ অন অ্যাকোয়েন্ট্যান্স। ওকে যদি বিয়ে করতে চাই?’
—‘এই তো বলছ বেশিদিনের আলাপ নয়, ভালো করে না বুঝে সুজে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিও না রূপ!’
রূপ ঢোক গিলল। বলল—‘না, এক্ষুনি করছি না। চাকরি টাকরি পাই! মা, ওকে অনেকেই বিয়ে করতে চায়, আমি বেশি দেরি করলে…ও রাজি হয়েছে।’
—‘তোর কি বিয়ের কথা ওকে বলা হয়ে গেছে?’
—‘হ্যাঁ, না, মানে একরকম—হয়েই গেছে।’
বন্দনা গম্ভীর গলায় বলল—‘এতো তাড়াতাড়ি কিছু ঠিক করো না রূপ। অনেকে ওকে বিয়ে করতে চায় বলছ, তুমি একটু দেরি করলেও ও যদি তোমার প্রতি অনুগত থাকে তাহলেই বুঝবে…’
—‘মা প্লীজ, ওকে না হলে আমি বাঁচব না। আমাকে তাড়াতাড়ি করতেই হবে।’
বন্দনার একবার মনে হল বলে—কাউকে না হলে কারুর বাঁচা আটকায় না। সাময়িক ভাবাবেগ, উচ্ছ্বাস এসব রূঢ় বাস্তবের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। কিন্তু এসব বলে কোনও লাভ নেই। একদিন ছেলেকে সে প্রায় এইভাবেই মিনতি করেছিল। ছেলে সেখানে রুদ্র প্রলয়ঙ্করের ভূমিকা নিয়েছিল। বন্দনার মনের গহনে সেই ভালোবাসা এখন চোরা নদীর মতো আটকে পড়ে আছে। তাতে স্রোত বয় না। একটা কর্দমাক্ত দহ। কিন্তু চলছে তো জীবন! প্রথম প্রথম যে দারুণ কষ্ট হত, মনে হত সব ছেড়ে-ছুড়ে পাগলিনীর মতো দরজা-জানলা হাট করে খুলে রেখে সে বরাবরের মতো কোথাও বেরিয়ে যায়। এখানে, এই ঘর-কন্নায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে সময়ে দীর্ঘদিন রূপকে দেখলে তার ঘৃণা হত। নিজের মনোভাবে সে নিজেই ভয় পেয়েছে, কষ্ট পেয়েছে। সুদীপ্তকে দেখলে তাকে কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হত। বিরাট একটা প্রশ্ন চিহ্ন নিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে হত। এসব কি ভয়ের কথা নয়! বন্দনা সেই সব বিভীষিকার দিন দাঁতে দাঁত চেপে পার হয়ে এসেছে। কাউকে জানতে দেয়নি। কলিকে পর্যন্ত না। জানতে দিতে প্রচণ্ড লজ্জা। বন্দনা নিজের দুঃখের কথা কাউকে জানাতে লজ্জা পায়। আত্মমর্যাদার মানটা এত উঁচুতে তুলে ফেলেছে যে কারুর কাছে দুর্বল হতে পারে না। সুদীপ্ত অনেক দূরে সরে গেছে। আসে না, কিন্তু দুতিন মাস অন্তর অন্তর একটা করে চিঠি দেয়। সে চিঠি রূপের হাতে পড়লেও কোনও অসুবিধে নেই।
রূপ বলল—‘মা, একটা কথা বলব? রাগ করবে না?’
—‘আমার রাগের কত তোয়াক্কা তুই করিস।’
—‘না আমি সীরিয়াসলি বলছি। আমি অঞ্জুকে বিয়ে করি, তারপর তুমি…’
—‘তারপর আমি কি রে? চলে যাব এখান থেকে? না মরে যাব?’
—‘কি যে বলো! তারপর তুমি সুদীপ্তকাকুকে…’
বন্দনা চমকে উঠল। একটু পরে আস্তে আস্তে বলল—‘এখন আর তা হয় না।’
—‘কেন হয় না?’
—‘অনুভূতির জগতে যা ভেঙে যায়, তাকে সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে আর কাজ চলে না।’
—‘কেন, সুদীপ্তকাকু তো এখনও তোমায় চিঠি দেন। মা আই অ্যাম সরি।’
—‘চিঠি দেন হিতৈষী বন্ধু হিসেবে। কিন্তু রূপ সব কথা তোমাকে বোঝাতে পারব না। তোমার এতদিনে সময় হল বলেই আমার সময় হবে না। আমার আর সে মন নেই। আমি বুড়ো হয়ে গেছি।’
রূপ হেসে বলল—‘আমার বন্ধুরা বলছিল, তোমাকে আমার বড় দিদির মতো দেখতে লাগে, অনায়াসেই বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যায়।’
—‘রূপ, তোমার আগের বন্ধুরা স্বপ্নেও মায়ের সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলা ভাবতে পারত না।’
—‘এরা একটু ঠোঁট কাটা। কিন্তু মনে মুখে এক হওয়াও তো একরকমের ভালো।’
—‘সব কথার, সব ব্যবহারের স্থান-অস্থান, পাত্রপাত্র ভেদ আছে রূপ, সেগুলো অস্বীকার করলে সভ্যতার শর্তগুলোই অস্বীকার করা হয়।’
—‘অঞ্জু উইল চেঞ্জ মা, দেখ।’
—‘না বদলালেই কি তুই আমার কথা শুনবি?’ বন্দনা হাল-ছাড়া গলায় বলল, ‘যা বলি তোর ভালোর কথা ভেবেই বলি, তুই তোর রুচি মতো চলবি, শুধু রুচিটা নষ্ট না হয়ে যায় এটাই ভাবি।’
রূপ বলল—‘ও মাই সুইট মাদার, রুচি যুগে যুগে পাল্টায়। আমাদের যুগটা তোমাদের থেকে এক্কেবারে আলাদা…’
—‘তাহলে আমার মতো সেকেলে রুচির সঙ্গে আর থাকতে পারবি না বলেই কি আমায় বিদায় করতে চাইছিলি?’
রূপ বলল—‘উঃ, তুমি যে কী বলো! আমি তোমার সুখের কথা ভেবেই বলেছি। তুমি যেমন আছ, তেমনি থাকবে। আফটার অল দিস ইজ ইয়োর ফাদার্স হাউজ।’
বন্দনা চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। ছেলেও একই ভাবে তার কোলের ওপর থুতনি দিয়ে। রুচির অমিলটা এখনই স্পষ্ট করে ধরা পড়েছে। বন্দনার বাবার বাড়িতে রূপের বউ যদি থাকতে না পারে, তাহলে কি রূপই চলে যাবে?
ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে বলল—‘রূপু, তোর ছেলেবেলাকার দিনগুলো র কথা মনে পড়ে? স্কুল থেকে এসে মাকে না দেখলে কেমন করতিস?’
—‘মনে পড়ে মানে? ফীলিংগুলো শুদ্ধ মনে আছে।’
—‘দিন কত বদলে যায়!’
—‘মা ডোন্ট বি সিলি। এখনও যদি ওইরকম নেই-আঁকড়েগিরি করি তোমার কি ভালো লাগবে? আই অ্যাম এ গ্রোন আপ ম্যান নাউ।’ বন্দনা হেসে বলল—‘সত্যি! তুই গ্রোন-আপ ম্যান আর আমি গ্র্যান্ড ওল্ড লেডি।’
রূপ বলল—‘ইউ আর এ গ্র্যান্ড অ্যান্ড লাভলি মাদার। আমার প্রস্তাবটার কথা ভেবে দেখলে পারো। আমি সুদীপ্তকাকুর কাছে গিয়েছিলাম। হী ইজ আনচেঞ্জড্।’
বন্দনা চমকে, বলল—‘গিয়েছিলি? এই বলতে?’
—‘না, তা নয়। চাকরির জন্য।’
—‘চাকরির জন্য? ওঁর কাছে? রূপ!’
—‘কেন, কি হয়েছে তাতে?’ রূপ কাঁধ নাচাল। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মায়ের দিকে, পেছন ফিরে। ‘উনি আমাকে চাকরি দিচ্ছেন। হী ইজ এ গুড গাই। নিশ্চয়ই আমার জন্যে দিচ্ছেন না। মা’—রূপ ফিরে দাঁড়াল, —‘আই ফীল ওবলাইজ্ড্ টু হিম। তুমি রাজি হয়ে যাও। নইলে আই’ল ফীল ভেরি ব্যাড অ্যাবাউট ইট।’
—‘সে ক্ষেত্রে চাকরিটা নিও না।’ ঠাণ্ডা গলায় বলে বন্দনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।
হঠাৎ ভীষণ ভয় লাগল বন্দনার। যাকে খুব আপন জন বলে জানি, আদ্যোপান্ত চেনা, হঠাৎ যদি দেখা যায় সে প্রতারক, যাকে ভাই বলে জানি, সে ভাই নয় ভাই সেজে এসে এতদিন ঠকিয়েছে, ছেলে আসলে ছেলে নয়, কোনও অচেনা মানুষ একরকম চেহারার সুযোগ নিয়ে ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে গেছে, তাহলে যেরকম আতঙ্ক হয়, এ সেই ভয়ানক আতঙ্ক। যে রূপ মা বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে ঘৃণায় বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল তাকে সে তবু খানিকটা চেনে। কিন্তু আজ যে নিজের স্বার্থের জন্য মাকে বিয়ে করতে বলছে সেই রূপকে তার একদম অপরিচিত লাগল। তার বুকের ভেতরটা হু হু করছে। খাঁ খাঁ করছে। না না, রূপ নিশ্চয়ই এভাবে বলেনি। এ ভেবে করেনি কাজটা। হয়ত ও সত্যিই এখন অনেক পরিণত হয়েছে। মায়ের সুখের কথা ভেবেই প্রস্তাবটা দিতে পেরেছে। মাস্টারমশাইয়ের ওপর পুরনো শ্রদ্ধা, আস্থা ফিরে এসেছে বলেই তাঁর কাছে চাকরি চাইতে যেতে পেরেছে। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা কতটা নির্লজ্জতা হবে ও বুঝতে পারেনি।
অধ্যায় ২৮
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের বয়স ছিয়াত্তর সাতাত্তর। বেশ শক্ত আছেন। খালি চোখে ছানি পড়েছে। এখনও পাকেনি বলে কাটানো হচ্ছে না। দাঁত প্রায় সবই অক্ষত। মাথার চুলগুলি সব সাদা। গোঁফ দাড়ি পরিষ্কার কামানো। তাঁর দাদা চোমরানো গোঁফ রাখতেন। বিশ্বনাথ যেন দাদার থেকে নিজেকে আলাদা বলে চেনাবার জন্যেই গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন। রাম লক্ষ্মণ বা গৌর নিতাইয়ের সঙ্গে দু-ভাইয়ের তুলনায় কোথায় যেন তিনি গভীরভাবে ক্লান্ত। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন হাফ পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে, পায়ে শুঁড়তোলা চটি। বেশ খটখট করে উঠে এলেন, প্রায় নিঃশব্দে। বন্দনা বাইরের পোশাক পরে বেরোচ্ছিল, কাঁধে ব্যাগ, মুখ নিচু। একেবারে অন্যমনস্ক। সিঁড়ির মোড়ে দু-জনে প্রায় ঠোকাঠুকি। বন্দনা অবাক হয়ে বলল—‘কাকাবাবু!’ বিশ্বনাথ ঘেমে গেছেন, বন্দনা বলল—‘আসুন, পাখার তলায় বসুন।’ অনেক দিন বাদে সে মাথায় কাপড় টেনে দিয়েছে। বিশ্বনাথবাবু বসতে, প্রণাম করেছে অনেকখানি মাথা নিচু করে। একটা অভ্যাসও ভোলেনি। বিশ্বনাথবাবু সেই যুগের মানুষ যাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম নেন। দু হাত মাথায় রেখে আশীর্বাদ করেন।
—‘সুখী হও মা,’ বলতে বলতে বিশ্বনাথবাবুর গলা ভারি হয়ে এল, —‘জীবনের কতগুলো বছর তো কেটেই গেল। বৃদ্ধের এ আশীর্বাদ যেন বাকি জীবনটাতে তোমার কাজে লাগে মা।’
বন্দনা ব্যস্ত হয়ে বলল—‘আপনি বসুন কাকাবাবু, আমি একটু শরবত করে আনি।’ তার মনে আছে বিশ্বনাথবাবু দু’বেলা দু কাপের বেশি চা খেতেন না। গরমকালে শরবত তাঁর খুব প্রিয়। বেশি উপকরণ লাগে না, পাতিলেবু নুন, চিনি দিয়ে ঠাণ্ডা জল। এই-ই তিনি খেতে ভালোবাসতেন, দোকানের বোতলের জিনিস নয়।
‘শোনো মা বসতে আসিনি, তোমার কাছে আর্জি নিয়ে এসেছি। যদি সাহস দাও তো পেশ করি, শরবতের কথা তার পরে ভাবা যাবে।’
বন্দনা বলল—‘কি আশ্চর্য! আর্জি? আমার কাছে আপনার?’
—‘হ্যাঁ মা, তোমার কাছে আমার। একদিন নিজের বাড়ি ছেড়ে দুধের ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছিলে। কোনও সাধ্য ছিল না, তাই রুখতে পারিনি। কৃতী দাদা। সংসার তাঁরই। আমি চিরকাল এটা সেটা বাজে কাজে পৈতৃক টাকা, দাদার টাকা নষ্ট করেছি শুধু। মাথা তোলবার মুখ ছিল না। যা করেছেন চিরকাল মেনে নিয়েছি। আজ তাঁর অবর্তমানে যত অভাজনই হই, আমিই তো ও বাড়ির কর্তা! তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি বউমা।’
বন্দনা মুশকিলে পড়া গলায় বলল—‘আমি তো বেশ আছি কাকাবাবু। জীবনকাল এখানে কেটে গেল। এখন আর যেতে চাইলেই কি পারব?’
—‘দেখ মা, দাদা বউদিদি চলে গেছেন, তাঁদের ওপর আর অভিমান রাখতে নেই।’ বিশ্বনাথবাবু বললেন।
—‘আমার মনে আর কোনও রাগ-অভিমান নেই, কাকাবাবু।’
—‘সে আমি জানি না মা। বাড়ি সেই থেকে খাঁ খাঁ করে। দাদার বড় ছেলে চলে গেল অকালে, সেজ তো বাড়ি ছাড়া সেই কবে থেকে। শুনেছি তারা অস্ট্রেলিয়া গিয়ে সেট্ল করেছে। মেজবাবু থাকে বম্বেতে। সেখানে শহরতলিতে শ্বশুরের বিরাট সম্পত্তি পেয়েছে। তার ছেলেমেয়েরা এখানে আসতেও চায় না। এক রইল ছোটবাবু। তার কোনও ইস্যু নেই। স্বামী-স্ত্রীতে উদয়াস্ত চাকরি করে। অত পরিশ্রম যে ওদের কার জন্য, কিসের জন্য বুঝি না মা। তুমি শুনলুম খোকামণির বিয়ে দিচ্ছ, অত বড় বাড়ি আমাদের। আমার অনুরোধ ওখান থেকেই দাও। ওখানেই ছেলে-বউ নিয়ে থাক। বাড়ি তো তোমার ছেলেরও।’
বন্দনা কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। এই সময়ে কলি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নিচ থেকে উঠে এল। বোধহয় গাড়িতে বসে ছিল। বন্দনার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসল। ভাবটা-কেমন জব্দ করেছি।
—‘কথা হল তোমাদের? কাকু!’
—‘আমি আমার আর্জি পেশ করেছি মা।’
—কলি বলল—‘আর্জি পেশ আবার কি? নিজেদের বাড়ির বউ নিজেরা নিয়ে যাবে। শোনো বউমণি, অত ভেবো না। আগে একবার শ্যামবাজার ঘুরে আসবে চলো তো! আজই চলো!’
—‘সেই ভালো,’ বিশ্বনাথবাবু বললেন—খোকা কোথায়?
—‘খোকা তো অফিস গেছে।’
—‘তুমি!’
—‘আমার শনিবারে ছুটি থাকে। আমি একটু কেনাকাটা করব বলে বেরোচ্ছিলুম।’
—‘মার্কেটিং আজ থাক না বউমণি। আমি সঙ্গে না থাকলে তুমি কি কেনাকাটা করবে শুনি!’ কলি ঝাঁঝিয়ে উঠল। গলা নামিয়ে বলল—‘চলো! কাকু বাড়ি বয়ে এসেছেন!’
বন্দনার দ্বিধা একটা কারণে নয়। শ্বশুর-শাশুড়ি এক এক করে মারা গেছেন। সে যায়নি। শ্বশুরমশাই যেদিন মারা গেলেন সে আর রূপ সুদীপ্ত সরকারের সঙ্গে ফুলেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিল। দিন তিনেকের ব্যাপার। কিন্তু অত পরে যেতে তার কিন্তু-কিন্তু লেগেছিল। শাশুড়ির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবার সাহসই তার হয়নি। আর শাশুড়ি যখন গেছেন তখন সে খুব অসুস্থ, নার্সিং হোমে। কলি তাকে খবরটা জানায়নি। দিনের পর দিন তার সঙ্গে কাটিয়েছে, সেবা করেছে, একবার মুখ ফসকেও বলেনি। অনেকদিন পর জেনেছে, তখন আর যাবার বেলা নেই। সেই সব অপরাধবোধ তার মনের মধ্যে ভারের মতো চেপে রয়েছে। মেজ দেওর, ছোট দেওরের বিয়ের সময়ে, মিলির বিয়ের সময়ে ওঁরা কার্ড পাঠিয়েছিলেন, সে যায়নি। উপহারস্বরূপ কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল শুধু।
বিশ্বনাথবাবু বললেন—‘চলো মা, তালাচাবি যা দিতে হবে, দিয়ে নাও। আমরা আস্তে আস্তে নিচে নামি। তোমার কাকিমা কী খুশি যে হবেন!’
পঁয়তাল্লিশ নং শ্যামবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে কবে শেষ রঙ পড়েছিল বন্দনা জানে না। সে বাড়ি ছাড়ার পর তিন তিনটে বিয়ে হয়েছে, কোনও একটাতে পড়ে থাকা সম্ভব। লাল ইঁটের বাড়ি। সকাল বেলার রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। সিংদরজা দিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই খুড়শাশুড়ি বেরিয়ে এলেন। ছলছলে চোখ। বড্ড যেন বুড়ো হয়ে গেছেন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে গেছেন, এই সব শিরদাঁড়ার রোগ আগেকার দিনে একশ জনের মধ্যে পঞ্চাশ জনেরই হত। এখন কিন্তু আর হয় না ঠিকঠাক চিকিৎসা করালে। বন্দনা প্রণাম করতে আদরে জড়িয়ে ধরলেন।
কাকাবাবু বললেন—‘দাদার সেরেস্তাঘর, এই দামী লাইব্রেরি এসবের কোনও উত্তরাধিকারী নেই। আমি ঝেড়েঝুড়ে এখনও টিঁকিয়ে রেখেছি, তোমরা যা বুঝবে করো।’
সেই কালো পাথরের ঠাণ্ডা সিঁড়ি। দোতলায় ঘরের পর ঘর তালা ঝুলছে। কাকিমা বললেন—‘তুমি চলে যাবার পর থেকে তোমার ঘর তোমার কাকাবাবু তালা দিয়ে রাখেন সমানে। মেজর বিয়ে হল, ছোটর বিয়ে হল কাউকে খুলে দিলেন না। বটঠাকুরও কিছু বললেন না। যতই যাই বলুন, তাঁদের আদরের ছেলের আদরের বউই তো তুমি মা?’ দরজা খুলে দিয়ে বললেন—‘নাও, তোমার নিজের জিনিস বুঝে নাও।’
ডবল-বেড খাটে বন্দনার বিয়েতে বাবার দেওয়া জাজিম পাতা। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাচ অস্বচ্ছ। পড়ার টেবিল, চেয়ার, শূন্য আলনা। কালো সাদা মার্বেলের মেঝে এইমাত্র বুঝি কেউ ধুয়ে মুছে গেছে। দেয়ালে তার স্বামীর ছবি। বহু পুরনো একটি টুরিজমের জমকালো ক্যালেন্ডার, যা বন্দনা অপূর্ব ছবিগুলোর জন্যে ফেলতে পারেনি। বন্দনার মনে হল তাকে কেউ পূর্বজন্মে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আবছা আবছা মনে পড়ছে সব। বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে কাকিমা বললেন—‘তুমি কাকাবাবুর কাছে বসো মা, আমি একটু কাজ সারি।’ কলি গাড়ি নিয়ে কোথায় গেছে। একটু পরে এসে বন্দনাকে তুলে নিয়ে যাবে। বৈঠকখানা ঘরে বসে কাকাবাবু খাটো গলায় বললেন—‘সাত কাঠার ওপরে ভদ্রাসন মা। আরও কাঠা তিনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। আমার অর্ধেক প্রাপ্য হয়। সে অর্ধেক আমি তোমাকে লিখে দেব। বাকিটুকুরও তিনভাগের এক ভাগ তোমার ছেলের। মানে দুয়ের তিন অংশই তোমার । তার ওপরে মেজ আর এখানে আসতে চায় না। তার শ্বশুরের অগাধ বিষয় সেখানে। এদিকে ছোট নিঃসন্তান। এত বড় বাড়ি পড়ে থাকবে মা, এই বেলা ছেলেকে নিয়ে এসে বসো।’
বন্দনা আস্তে আস্তে বলল—‘কাকাবাবু, আমি অত হিসেব বুঝি না। আমার একটা বাস করবার নিজস্ব জায়গা আছে। আমি তো গৃহহীন নই! এখানে এতকাল পরে এভাবে এলে মেজদা কি ছোড়দা যদি ভালো মনে নিতে না পারেন, সে অশান্তি আমি সইতে পারব না।’
বিশ্বনাথবাবু বললেন—‘না মা। তুমি ভুল বুঝছ। ছোট আর বউমা একটা শিশুর মুখের জন্যে হা পিত্যেশ করে থাকে। তোমরা এলে, তোমার বউমা এলে, নাতি নাতনি হলে এ ঘর দুয়োর ভরে যাবে, তাতে তাদের আনন্দের সীমা থাকবে না। আমি জানি।’
বন্দনা মনে মনে হাসল। কাকাবাবু অনেক দূর পর্যন্ত ভেবে ফেলেছেন। বলল—‘আমি রূপুকে বলি। সে যদি রাজি হয় তো ভেবে দেখব।’
রূপের সঙ্গে অঞ্জুও এল সন্ধেবেলায়। স্কুটারের পেছনে চেপে। রাত ন’টায় একসঙ্গে খেয়ে বাড়ি ফিরবে। বন্দনা বাধ্য হয়ে তার সামনেই কাকাবাবুর প্রস্তাবটা পেশ করল। রূপ বলল—‘দূর, শ্যামবাজারের সেই আদ্যিকালের বাড়িতে কে ফিরে যাবে?’
অঞ্জু বলল—‘বাঃ, বাড়িটা তো তোমাদেরই। না গেলে তো বেহাত হয়ে যাবে! গাড়ল আর কাকে বলে!’
বন্দনা সামনে থেকে সরে গেল। অঞ্জুর কথাবার্তার ধরন শুনলে তার বিশ্রী মন খারাপ হয়ে যায়।
বন্দনা সরে যেতে অঞ্জু বলল—‘কোথায় তোমাদের শ্যামবাজারের দরদালান, আর কোথায় এই একরত্তি বাড়ি। ওখান থেকেই বিয়েটা হোক। বাড়িতে সম্পত্তিতে তোমার ভাগ রয়েছে, দখল নেবে না? কোথাকার বুদ্ধু রে!’
অনেক তর্কাতর্কির পর স্থির হল শ্যামবাজারের বাড়িতেই বিয়ে হবে। কিন্তু থাকা হবে আপাতত এখানেই। বন্দনার অফিস ডালহৌসী পাড়া ছেড়ে উঠে এসেছে লোয়ার সার্কুলার রোড। রূপ যায় হ্যারিংটন স্ট্রিট। শ্যামবাজার থেকে যাতায়াতের অসুবিধে।
রূপ বলল—‘তাছাড়া ওরকম যৌথ পরিবারে তুমি থাকতে পারবে?’
—অঞ্জু বলল—‘যৌথ পরিবারেই তো থাকছি।’
—‘কোথায়?’
—‘তোমার মা তো থাকছেন, যৌথ পরিবার ছাড়া কি?’
—‘ওখানে আমার দাদু-দিদা বুড়ো-বুড়ি রয়েছে। কাকা-কাকিমা রয়েছে, তাদের আমিই ভালো করে চিনি না।’
—‘তারা থাকবে তাদের মতো! আমি থাকব আমার মতো!’ রূপ কাঁধ নাচিয়ে বলল—‘কি জানি বাবা, তোমাদের মেয়েদের মতিগতি বোঝা ভার।’
হেসে উঠল অঞ্জু—‘বুঝতে চেষ্টা করো না। একেন্নম্বরের ভূত একটা।’
অধ্যায় ২৯
রাত বারোটা বেজে গেছে। উৎসববাড়ি নিস্তব্ধ। সানাই এতক্ষণে চুপ করল। মাঝের ঘরে ফুলশয্যা। তারপরে ছোট একটু ঘেরা দালান পেরিয়ে কলিদের পুরনো পড়ার ঘর। ওদিকের ঘরে ছোট দেওর। এখনও সে বন্দনার সঙ্গে ব্যবহারে একটু আড়ষ্ট। কিন্তু তার বউটি ধরা-ধরা গলায় সব সময়ে এক কথার জায়গায় একশ কথা বলে। সব সময়ে আলু-থালু, পাগল-পাগল। সে অন্তত আট ন-বার বন্দনাকে জিজ্ঞেস করেছে ‘ও দিদি, এখানে থাকবে তো! না, আবার আমাকে প্রেতপুরীতে একলা ফেলে চলে যাবে?’ বিয়েবাড়িতে শিশু দেখলেই সে তাকে আদরে আদরে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। শিশুটি প্রতিবাদ করলেই কেঁদে ফেলেছে। সুতপার অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হয়। একবার অনেক কষ্টে সংকোচ কাটিয়ে বলেছিল—‘সুতপা, একটা দত্তক নিলে তো হয়!’
বিষন্ন মুখে মাথা নেড়ে সুতপা বলেছিল—‘তুমিও এই কথা বলছ দিদি! কোথাকার কোন বাচ্চা নেব, মল্লিকবাড়ির মেয়ে আমি, বন্ধ্যা হতে পারি, কাঙাল তো নই!’
বন্দনা বুঝেছিল সুতপার সমস্যা যা ভেবেছিল তার চেয়েও জটিল। সুতপা বলেছিল ‘রাগ করলে, দিদিভাই? তার চেয়ে নাতি। না না নাতনি তোক। মনের সাধে মানুষ করব এখন। অনাথ-আশ্রমের বাচ্চা নিয়ে শেষে ফ্যাসাদে পড়ি আর কি!’
এ বন্দনা কি করে তাকে বোঝাবে নাতি বা নাতনিকে মানুষ করতে পাওয়ার অধিকারও ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় না।
পরদিন বউকে রওনা করিয়ে দিয়েই ভবানীপুরে ফিরে এল সে। যে বাড়ি অভিমন্যুর, সে বাড়ি অভিমন্যু বিনা এখনও কী দুঃসহ। বাথরুমের দিকে তাকালেই মনে পড়ে যায় সেই দৃশ্য, সেই বিস্ফারিত দৃষ্টি। সে-সব স্মৃতি তো সে মনে করতে চায় না। তার নিজের ঘর, যে ঘর এখন রূপকে দিয়েছে, সেখানে ঢুকতে মনে হল অভিমন্যুও এক্ষুনি ঢুকল বারান্দার দিকে দরজা দিয়ে।
—‘বন্দনা, আমি আসব ভুলে গিয়েছিলে? আমাকে ছেলের বিয়েতে ডাকলে না তো! আমাকে পর করে দিয়েছ। বন্দনা, তোমরা আমাকে একেবারে ভুলে গেছ?’
বন্দনা দেখে তার বুকের কাপড় ভিজে উঠেছে। দেয়ালে তার ছবি, জুঁইয়ের মালা এক রাত্তিরেই শুকিয়ে এসেছে, বন্দনার স্বামী এখন বন্দনার থেকে বয়সে ছোট আটত্রিশ বছরের এক দুরন্ত যৌবনের যুবক। বন্দনা তাকে বহুকাল পেরিয়ে এসেছে, প্রায় দশ বছর হতে চলল। তবু সে তাকে এখনও, এমনি অনিবার্যভাবে কাঁদায়।
কি করে তাহলে থাকবে সে? তাকে যেতে হবে যেখানে স্মৃতি এমন করে প্রতি কোণে থমকে দাঁড়িয়ে নেই, বাঁচতে যখন হবেই তখন এমন স্মৃতি-পাগল হলে তো চলবে না!
কাকাবাবু কাকিমাকে প্রণাম করে সে বলল—‘আমি আসা যাওয়া করব, কাকিমা, ভাববেন না।’ সুতপাকে বলল—‘তুমি যখনই ইচ্ছে হবে আমার কাছে চলে যাবে। আমিও আসব। থাকব। কান্নাকাটি করো না।’
রূপ ভবানীপুরের পরিবেশে অভ্যস্ত। সে কিছুতেই শ্যামবাজারে থাকতে চাইছে না। সে থাকলেও বন্দনা এ বাড়িতে এসে থাকার কথা ভাবতে পারে না। কিন্তু মনে মনে সে এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। ছোট জায়ের প্রীতি স্বীকার করে নেয়। থাকা হবে না, কিন্তু আসা যাওয়ার যে স্রোত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাকে মুক্ত করতে হবে। কলি একবার ইতস্তত করে বলেছিল—‘বউমণি ওরা ভবানীপুরে থাকে থাকুক না, তুমি এখানে এসে থাক। অঞ্জুকে একলা সংসার করতে দিলে আমার মনে হয় সব দিক থেকেই ভালো হবে।’
সকালবেলার রান্নার খুঁটিনাটি অন্নকে বুঝিয়ে দিতে দিতে সে কথা ভেবে বন্দনার হাসি আসে। সে নিজে আজকাল অফিসে লাঞ্চ খায়। কিন্তু অঞ্জুর জন্য তাদের রান্নার ধরন-ধারন সবই পাল্টে ফেলতে হয়েছে। সেদ্ধ রান্না সে একদম খেতে পারে না, অথচ রাঁধতেও তার কোনও গরজ নেই। একদিন অন্ন আসেনি, বন্দনাও বেরিয়ে গেছে সকাল সকাল। রূপকে সেদিন বাইরের খাবার খেতে হয়েছে, অঞ্জুও পঞ্জাবি দোকানের রুটি-মাংস খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। মা না থাকলে রূপের খাওয়া-দাওয়ার খুব মুশকিল। সে আবার ঝাল খেতে পারে না। একদম।
সুতরাং জীবনযাত্রা আগের মতো চললেও তার চাল-চলন এখন বদলে গেছে। ছোট্ট বাড়িটাতে এখন প্রাণের জোয়ার। দু-টি যুবক-যুবতীর আনন্দ। হাসি-গল্প, খুনসুটিতে সরগরম। রূপ অফিস থেকে এসেই কোনমতে কিছু খেয়ে অঞ্জুকে স্কুটারের পেছনে বসিয়ে বেরিয়ে যায়। অঞ্জু একদম বাড়ি বসে থাকতে পারে না। সারাদিন ধরে সে লম্বা লম্বা নখ রাঙায়, সন্ধে হলেই বেরোবে। ফিরতে ফিরতে ন’টা দশটা এগারটা। হু হু করে হাসতে হাসতে, পরস্পরকে কিল মারতে মারতে ঝড়ের মতো ফেরে। রূপ বলে —‘তুমি খেয়ে নিও মা। আমাদেরটা ঢাকা দিয়ে রাখবে। এ পাগলির কবে কি মতি হবে জানি না তো! খাওয়ার হলে খেয়ে নেব, না হলে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে দেব।’
বন্ধুর দল এলে জমজমাট আড্ডা বসে। বন্দনা চা দিতে গিয়ে দেখে অঞ্জু মধ্যমণি হয়ে বসেছে, তার এক হাত রূপের কাঁধে তোলা, আরেক হাত দিয়ে সে প্রদীপের জামার ভেতরে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ক্ষ্যাপার মতো হাসছে সবাই। বন্দনাকে দেখেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় অঞ্জু। বলে —‘এই দেখ, আমাদের শাশুড়ি বউয়ে কিরকম সমঝোতা। শাশুড়ি চা করে দিচ্ছে, বউ সার্ভ করছে।’ ‘শাশুড়ি’ কথাটা, অঞ্জুর ধরন-ধারন কোনটাই ভালো লাগে না বন্দনার। সে সরে যেতে যেতে শোনে কেউ একজন বলছে, ‘মাসিমার মতো হতে হলে তোকে একজন্ম ঘুরে আসতে হবে অঞ্জু।’
অঞ্জু বলছে—‘যা যা, নিজের নিজের চরকায় তেল দি গে যা।’
কলি মাঝে মাঝে বলে, ‘বউমণি তুমি গোড়ার থেকেই ওদের বড় প্রশ্রয় দিচ্ছ, কিছু বলো না কেন?’
বন্দনা বলে—‘আমি বললে কিছু ফল হবে এ-কথা তোকে কে বলল কলি! আর বলবই বা কি! মাঝখান থেকে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে।’
—‘বাইরের একটি মেয়ে তোমার বাড়ির নীতি-নিয়ম তো বুঝতে না-ও পারে বউমণি!’
—‘না বোঝে না-ই বুঝুক কলি, আমি বোঝাতে পারব না। আমায় মাফ কর। যে ক’টা দিন আছি, কোনরকম সংঘর্ষ ছাড়া কাটিয়ে দিতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করব।’
কলি তখন অঞ্জুকেই বলে—‘হ্যাঁরে অঞ্জু, সারাদিন বসে বসে তোর পা ধরে যায় না!’
—‘যায়ই তো। সন্ধে হলেই তো বেরিয়ে পড়ি।’
—‘সারাদিন বসে বসে কি করিস? ’
—‘পিসি তুমি কি আমাকে রান্না-বান্না করতে বলছ নাকি? আচ্ছা পিসি, আমি আসার আগেও তো এ বাড়িতে রান্না হত, নাকি! আজ আমি একটা মানুষ বাড়তি হয়ে গেছি বলেই কি আমারটা করে নিতে বলছ!’
কলি বলে—‘তুই এমন করে কথা বলিস!’
—‘আমার বাবা ঢাকঢাক-গুড়গুড় নেই। আমাকে যা বলবে সোজাসুজি বলবে। ওসব ঘর-গেরস্থালি, রান্না-টান্না আমার দ্বারা হবে না। আমি এসেছি বলে বেশি ঝঞ্ঝাট হলে বলবে, ওকে বলব স্রেফ দোকান থেকে আমার খাবার এনে দেবে।’
কলি বলে—‘বাবারে বাবা, আমার ঘাট হয়েছে, তুমি যেমন আছ, তেমনি থাক। আমি চললুম। বউমণি, সারাটা দিন ছুঁড়ি কি করে কাটায় একটু উঁকি মেরে দেখ তো!’
বন্দনা হেসে বলে—‘তুই এসে দেখে যাস।’
ওরা যেদিন বাড়ি থাকে সেদিন বন্ধু-বান্ধব আসে। আড্ডা চলতে থাকে দশটা পর্যন্ত। ঘন ঘন চায়ের ফরমাশ আসতে থাকে। চায়ের সঙ্গে কিছু কিছু অনুপানও প্রত্যাশা করে রূপ। তার নতুন চাকরি, নতুন বউ, বন্ধুরা কেউ এখনও তার মতো ভাগ্যবান নয়, আনন্দের আতিশয্যে ঢালাও নেমন্তন্ন, ঢালাও আপ্যায়ন।
এক একদিন বিছানায় ছটফট করে বন্দনা। এতদিনের এত কষ্ট করে অর্জিত স্বাধীনতা, অবসর যাপনের মুক্তি, বাড়ির আবহাওয়ায় এত যত্নের পারিপাট্য, পবিত্রতা নিয়ম সব তাসের প্রাসাদের মতো ভেঙে পড়ছে। এখন মনে হচ্ছে অঞ্জুকে অত সহজে মেনে নেওয়া তার উচিত হয়নি। সে যদি এ বিয়েতে মত না দিত, রূপ এখুনি চাকরি পেত না, সুদীপ্ত দিতেন না। আরও কিছুদিন সময় পাওয়া যেত। হয়ত রূপ বুঝতে পারত অঞ্জু মেয়েটি ঠিক তাদের বাড়ির উপযুক্ত নয়। কিন্তু কবে থেকে যে বন্দনা ছেলেকে ভয় করতে শুরু করেছে, সে জানে না। যত বয়স বাড়ছে, ততই বাড়ছে এই অসহায়তাবোধ। যদি রূপ তাকে ছেড়ে চলে যায়! এই বাড়িতে এখনও একদম একলা সে। দিন রাত। তবু তো রাত্রে সে পাশের ঘরে থাকে। দিনে রাতে দু’বার কি তিনবার সামান্য সময়ের জন্য হলেও তাকে তো দেখা যায়! এখনও রূপের মা মা ডাক এই বাড়িতে বাজে। এখনও অনেক আছে। যত সইবে, নিজের যন্ত্রণাকে যত গ্রাস করে নিতে পারবে, তত সংঘর্ষের সম্ভাবনাও কমবে। সংঘর্ষ নয়, কিছুতেই নয়। একদিন না একদিন রূপের চোখ থেকে পদা খসবেই। তখন অঞ্জলিকে তার এই আলগা গা-ছাড়া স্বার্থপর চরিত্র পাল্টাতে হবেই।
অধ্যায় ৩০
রূপের আজ মেজাজ খুব খুশি। নতুন চাকরি, বিয়ের পরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠেনি। ছুটি পায়নি। এতদিনে ছুটি মিলেছে। অংশু, প্রদীপ, অচিন্ত্য তার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে ঢুকল। ওপরে উঠতে উঠতে সে দরাজ গলায় ডাকল. ‘মা, মা, শিগগির চা দাও। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। অঞ্জু, মা কোথায়?’
অঞ্জু একবার রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে বলল—‘কি জানি! নেই তো এখানে।’
—‘ফিরেছে তো?’
—‘হ্যাঁ। দেখলাম তো!’
—‘যাকগে, চা-টা দাও তো।’
অচিন্ত্য বলল—‘হ্যাঁ ভালো করে চা বানা দেখি।’
অঞ্জু বলল—‘আমার বয়ে গেছে। সারা দুপুর ধরে হাত-পা সমস্ত পরিষ্কার করেছি। আঙুলগুলো বাড়িয়ে দেখাল অঞ্জু, লম্বা লম্বা লাল টুকটুকে নখ।’
অংশু বলল—‘ওসব জানি না। অনেকদিন চালিয়েছিস। লাগা দিকি চা। আর কি কি আছে বার কর।’
রূপ বলল—‘মা নিশ্চয় কিছু না কিছু করে রেখেছে।’
অঞ্জু মুখ গম্ভীর করে উঠে গেল। রান্নাঘরে ঢুকল সসপ্যান নিয়ে চায়ের জল চড়াল। দুধ বার করল। বেশ খানিকটা ঢেলে দিল প্যানে। তারপর প্যান ঢাকা দিয়ে চায়ের কৌটো খুঁজতে লাগল। তার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। মিনিট কয়েক পরেই অঞ্জুর তীব্র চিৎকারে রান্নাঘরে ছুটে গেল সবাই। অঞ্জুর সিনথেটিক শাড়ি ধরে গেছে, আঁচল দিয়ে সে প্যানের হাতল ধরেছিল। রাগের মাথায় শাড়ির কথা খেয়াল ছিল না। হাতের ওপর দুধ জল উথলে উঠে হাতের কজিও পুড়েছে খানিকটা। আগুন নিভল। রূপের মুখে এখনও আতঙ্ক। অংশু বলল—‘চা খাওয়ার বারোটা বাজল আজ।’
রূপ অঞ্জুর কজিতে বার্নল লাগাচ্ছিল, বলল—‘আমার বউটা আরেকটু হলে সীতা হয়ে যাচ্ছিল, আর তোরা চা-চা করছিস!’
অচিন্ত্য বলল—‘তোর বউ সীতা না মায়ামৃগ তা শ্রীরামচন্দ্রই জানেন।’
অঞ্জু পা ছড়িয়ে বসেছিল, হাত বাড়িয়ে চিমটি কাটল একটা। অচিন্ত্য হাসতে হাসতে বলল—‘আসলে তোর বউ কিষ্কিন্ধ্যা-বাসিনী, কিরকম খিমচোয় দেখিস না।’
অংশু বলল—‘কিন্তু মাসিমা কোথায় গেলেন বল তো! প্রাণটা এখন সত্যি মাসিমা-মাসিমা করছে।’
রূপ বলল—‘অঞ্জু ঠিক আছ তো? দাঁড়া এবার মাতৃদেবীকে খুঁজতে যাই।’ ছাদে এসে মা-কে পেল রূপ। মাদুর পেতে চোখ বুজে শুয়ে আছে। —‘মা তুমি এখানে? অঞ্জু যে পুড়ে যাচ্ছিল!’
বুঝতে একটু সময় লাগল বন্দনার। ভীষণ মাথার যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। আজকাল এই আধকপালে মাথা ধরাটা প্রায়ই হচ্ছে। এসে দেখল অন্ন আসেনি। বন্দনা জামাকাপড় বদলে ওষুধ খেয়ে ছাদে চলে গেল। কিছু দরকার নেই। শুধু বিরাম। শুধু ঘুম।
রূপের ডাকে উঠে বসল, বলল—‘বলিস কি রে? কি করে?’
—‘চা করতে গিয়েছিল, আঁচল-টাঁচল ধরে একেককার!’
বন্দনা বলল—‘লাগেনি তো!’
—‘লেগেছে বই কি! বার্নল দিয়েছি। তুমি একটু দেখ যদি আর কিছু লাগে।’
বন্দনা নিচে নেমে এল। অনেকদিন পর ছেলের ঘরে ঢুকল। বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছে অঞ্জু। হাতটা দেখে বন্দনা বলল—‘ঠিক আছে। আর কিছুর দরকার হবে না।’
অচিন্ত্য বলল—‘মাসিমা, আপনার কি শরীর খারাপ?’
—‘বড্ড মাথা ধরেছিল।’
—‘তাই তো ভাবি, আমরা এলাম, মাসিমা কোথায় গেলেন?’ অঞ্জু বলল—‘ওর প্রাণটা মাসিমা মাসিমা করছিল, এক্ষুনি বলছিল। বন্দনা ক্লান্তমুখে জোর করে হাসি টেনে বলল—‘কেন? চায়ের জন্য?’
—‘ঠিক ধরেছেন মাসিমা’, অচিন্ত্য হাউহাউ করে বলল। এরা দুঃখ, অভিমান, বিদ্রূপ কিছুই বোঝে না। এই অনুভূতিহীনতার বিরুদ্ধে কোনও লড়াই চলে না। এদের সঙ্গে লড়াই চালাতে গেলে যে হাতিয়ার দরকার তা বন্দনার নেই। এইরকম অসাড় সন্তানের চেয়ে দুষ্ট ছেলেও ভালো। তার সঙ্গে সামনাসামনি ঝগড়া করা যায়। তাকে তিরস্কার করা চলে। এরকম নির্বোধ ছেলেকে নিয়ে সে কি করবে?
বন্ধুরা চলে গেলে রূপ বলল—‘যাক টিকিটটা হয়ে গেল।’
—‘কিসের?’ বন্দনা, অঞ্জু দু-জনেই জিজ্ঞেস করল।’
—‘কাশ্মীর।’
অঞ্জু বলল—‘ইস্ এতক্ষণ খবরটা চেপে রেখেছিলে?’
বন্দনা বলল—‘যাক, তাহলে ছুটি পেলি?’
—‘পুরো পাইনি। পুজোর চারদিনের সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে নিতে হল। ষষ্ঠীর দিন যাচ্ছি, লক্ষ্মীপুজোর দিন ফেরা।’
—‘ষষ্ঠীর দিনের টিকিট কেটেছিস?’—বন্দনা উদ্বিগ্ন স্বরে বলল।
—‘হ্যাঁ! কেন? ওরকম করছ কেন?’
—‘রূপু, টিকিট ফেরত দিয়ে দাও, চেষ্টা করো পরের দিনে যদি পাও।’
—‘সে কি? কেন? কত কষ্ট করে টিকিট পেয়েছি, এখন লাস্ট মোমেন্টে…’
—‘আরেকটু কষ্ট করে ফিরিয়ে দিবি রূপু, ডেট পাল্টাতে না পারিস, যাওয়া হবে না এখন। বেড়াতে যাবার অনেক সুযোগ জীবনে আসবে, আমার কথা রাখ— ও দিনটাতে যাস না;’ বন্দনার গলা কাঁপছে।
—‘কারণটা বলবে তো!’
অঞ্জু বলল—‘পাগল হয়েছেন নাকি? টিকিট হয়ে গেছে, কবে থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন ফেরত দাও বললেই ফেরত দেবে, ছেলেখেলা নাকি?’
বন্দনা বলল—‘তুমি চুপ কর অঞ্জু। রূপ টিকিট ফেরত দিয়ে আসবে। পরে যেও।’
—‘ছুটিও আর পেয়েছি, যাওয়াও আর হয়েছে।’ রূপ হতাশ গলায় বলল, ‘হঠাৎ এমন খেপে গেলে কেন?’
বন্দনা বলতে পারছে না, রূপের বাবা ষষ্ঠীর দিন যাত্রা করে আর ফেরেননি। সে বলল—‘ষষ্ঠীর দিনটা যাত্রার পক্ষে ভালো নয় রে রূপ, লক্ষ্মীটি আমার কথা শোন।’
অঞ্জু তীক্ষ্ণ গলায় বলল—‘যাত্রার পক্ষে ভালো নয়? বললেই হল? এতো কুসংস্কার আপনার, জানা ছিল না তো? এদিকে তো কিছুই মানেন না। সবই খাচ্ছেন, সবই পরছেন! আমাদের বেড়াতে যাবার কথাতেই পাঁজি পুঁথি সব বেরিয়ে পড়ল।’
বন্দনার হাত-পা কাঁপছে। কি বলছে অঞ্জু? কি অসম্ভব স্পর্ধা? রূপ? রূপু কি কিছু বলছে? শাসন? অনুযোগ? মৃদুতম ভর্ৎসনা? না, রূপ ভুরু কুঁচকে নিজের ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে অঞ্জু। বন্দনা অস্থির পায়ে অভিমন্যুর ছবির সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় খিল তুলে দিল গিয়ে। জানলার পাল্লা বন্ধ করে দিল। আলো নিভিয়ে দিল। আবার ছবির সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—‘সত্যিই তো, আমি ভর্তৃহীনা ধূমাবতী। বেঁচে থাকবার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু শুধু আমার উদাসভাবে গ্রহণ করা উচিত। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার একমাত্র পরিচয় আমার ভাতের থালায় আর আমার পরনের কাপড়ে। সেখানে যদি পরিচয় না রাখতে পারি তাহলে পুত্রবধূর কাছ থেকে এই অপমান আমার প্রাপ্য। নিশ্চয় প্রাপ্য।’
অধ্যায় ৩১
সোমবার দিন সকাল সাড়ে ন’টা নাগাদ যোগীন্দর অ্যান্ড যোগীন্দরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অমলেন্দু ঘোষাল অবাক হয়ে দেখলেন এক অদ্ভুতদর্শন মহিলা তাঁর ঘরে ঢুকছেন। এবড়ো-খেবড়ো চুল কাটা। নতুন মিলের থান পরনে, সাদা ব্লাউজ। নতুন কাপড়ের রঙের সঙ্গে পুরনো ব্লাউজের রঙে মিল খায়নি বলে খুব অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মহিলা সম্পূর্ণ নিরাভরণ। ইনি কে? কি চান? কোনও ভদ্রবংশের মহিলা ভিক্ষা চাইতে এসেছেন? ঢুকলেন কী করে? তাঁর ব্যক্তিগত বেয়ারা রতন কী করছে? মুখ ফসকে কিছু বলে ফেলবার আগেই ঘোষাল আরও অবাক হয়ে দেখলেন ভদ্রমহিলা তাঁর ফাইল ক্যাবিনেটে চাবি লাগাচ্ছেন এবং ঘোষাল তক্ষুনি চিনতে পারলেন মহিলা তাঁরই ব্যক্তিগত সচিব মিসেস বন্দনা ভট্টাচার্য।
আর্তনাদ করে উঠলেন ঘোষাল—‘একি মিসেস ভট্টাচারিয়া! একি করেছেন? এভাবে এখানে একি? চুল কেটেছেন এভাবে?’ একজোড়া কাচের মতো চোখ ঘোষালের মুখের ওপর স্থির হল। বন্দনা ভট্টাচার্য বললেন—‘কেন মিঃ ঘোষাল, জানেন না এই তো আমার ইউনিফর্ম!’
অমলেন্দু দেখলেন বন্দনা বিকারগ্রস্তের মতো ঠকঠক করে কাঁপছেন; ভেতরের কি এক দুরন্ত আবেগে, আক্ষেপে, কান্নায় যা তিনি কিছুতেই প্রকাশও করতে পারছেন না। ঘোষাল তাড়াতাড়ি উঠলেন, দু হাতে বন্দনাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। কলিংবেলের দিকে হাত যাচ্ছিল, বন্দনা প্রাণপণে তাঁর হাত চেপে ধরলেন, অস্ফুটে বললেন—‘এখন কাউকে ডাকতে পারবেন না, আজ আমি আপনার কাছে রেজিগনেশন দিয়ে যাচ্ছি।’
—‘রেজিগনেশন? বউদি! কেন!’ ঘোষাল চমকে উঠেছেন।
—‘আমি পারছি না। এভাবে চাকরি করতে পারব না, দাদা, আমার মাথা আর কাজ করবে না, করছে না…।’
ঘোষাল বললেন—‘শুনুন, আমার কথা শুনুন, বউদি! কি হল? আপনি তো শ্বশুরবাড়িতে থাকেন না! কে, কে তাহলে আপনাকে এতো কষ্ট দিল! ছিঃ!’
বন্দনার মুখচোখ চুরমার হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। সে টেবিলের ওপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে উঠছে।
স্যারা এসে গেছে। তাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে ঘোষাল বন্দনাকে বললেন—‘চলুন, বউদি, আজ আপনাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই।’ স্যারার বিস্মিত চোখ। অফিসে এখনও খুব কম লোক এসেছে, তাদেরও বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে দিয়ে ঘোষাল বন্দনাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।
ভি আই পি রোড দিয়ে তাঁর গাড়ি ছুটছে। অমলেন্দু পেছনে তাকাচ্ছেন না, যেন তিনি জানেন না পেছনে বসা মানুষটি মুখ ঢেকে কাঁদছেন, তিনি কোনমতেই আর নিজের বশে নেই। সমস্ত অভিমান, ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে আজ। ঘোষাল বলছেন—‘অনেকদিন আপনাকে এখানে নিয়ে আসব ভেবেছি। আসা হয়ে ওঠেনি। অফিসের এতো উৎসব, এক্সকার্শন, কোনটাতে আপনি যোগ দেন না, অনেকবার ভেবেছি জিজ্ঞেস করব কেন, অনুরোধ করব আসতে। তারপর ভেবেছি ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ওপর জোর না করাই ভাল। এখন দেখছি ভুল করেছি। আসলে আমার ধারণা ছিল আপনি আপনার অবাঞ্ছিত পরিবেশ থেকে একবার যখন বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, স্ব-নির্ভর হতে পেরেছেন, তখন আপনার অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়েই গেছে। কিন্তু আপনি যে এতো দুর্বল, এতো ছেলেমানুষ কখনও বুঝিনি।’
তাঁর কথা পেছনের মানুষটির কানে যাচ্ছে কিনা বোঝার উপায় নেই।
—‘কি অদ্ভুত কাকতালীয় দেখুন’—অমলেন্দু বললেন, ‘আজ থেকে আঠার বছর আগে আজকের দিনেই আপনি আমার কাছে এসেছিলেন। মনে আছে? আমি বলেছিলাম আপনার দেখাশোনা করবার নৈতিক দায়িত্ব আমাদের। আজকে আসতে আসতে সে কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম আনন্দ করব, সেলিব্রেট করব। আপনার মতো রক্ষণশীল পরিবারের বধূর অফিসে চাকরি নেবার ঘটনা সেই পঞ্চাশের দশকে খুব ঘটত না। আজ অনেকেই আসছেন। আবহাওয়াও অনেক বদলে গেছে। কিন্তু তখন কেউ ভাবতে পারত না। অফিসে মহিলা-কর্মী নেবার রেওয়াজও ছিল না। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা বরাবরই ছিলেন। কিন্তু বাঙালি মহিলা, একেবারেই ছিলেন না। আপনি হয়ত জানেন না আপনি আমাদের অফিসের প্রথম বাঙালি মহিলা। আর দু বছর পূর্ণ হলেই অফিস আপনাকে ফেলিসিটেশন দেবার কথা ভাবছে।’
গাড়ি থামল। ঘোষাল নেমে পেছনের দরজা খুলে বললেন—‘আসুন বউদি, নামুন।’
বন্দনা মুখ ফিরিয়ে বলল—‘আমার কোথাও কারো সামনে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমায় মাফ করুন দাদা।’ ঘোষাল বললেন—‘এখানে সে অর্থে কেউ নেই। যারা আছে তারা আপনাকে পেলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করবে। আমার কথা রাখুন। একবার নেমে দেখুন।’
পাশে বাঁশের গেট। একটি দোলনচাঁপার গাছ। গেট খুলে দু-তিনটি ছেলেমেয়ে ছুটে এল। কারো হাতে শাবল, কারো হাতে খুরপি। মাটিমাখা হাত। অমলেন্দু একজনের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—‘কুণাল! তোদের মা কোথায়?’
কুণাল নামের বালকটি অস্ফুটে কিছু বলল। বন্দনা ততক্ষণে মাথায় ঘোমটা দিয়ে নেমে দাঁড়িয়েছে। অমলেন্দু বললেন—‘ঠিক আছে তোরা বাগান কোপাচ্ছিলি, যা। আমি দেখছি।’ একটি ষোল সতের বছরের ছেলে তার বাঁকা চোখ বাঁকিয়ে বলল—‘দাদা, মা? আমার মা?’
ঘোষাল সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—‘হ্যাঁরে হ্যাঁ তোর মা।’ খুব খুশি হয়ে ছেলেটি এগিয়ে এসে বন্দনার হাত ধরতে গেল। অমলেন্দু বললেন—‘বাঃ, প্রণাম কর।’
ছেলেমেয়ের দলটি কলরব করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। অমলেন্দু বললেন—‘বউদি, এরা জড়বুদ্ধি। কেউ নানারকম রোগে, কেউ জন্মের সময়কার কোনও আঘাতে এমন হয়ে গেছে। বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য সরকারি বেসরকারি অনেক রকম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এদের কেউ দেখে না, এদের কথা কেউ ভাবে না। মানুষের সমস্ত আয়োজন, সমস্ত ভাবনা-চিন্তার বাইরে এরা। যেটুকু ব্যবস্থা আছে প্রয়োজনের তুলনায় তা এতো সামান্য যে সিন্ধুতে বিন্দুবৎ বললেই হয়। অথচ অভিভাবক এদেরই সবচেয়ে বেশি দরকার। জানেন তো বেশিরভাগ এই রকম অভাগা শিশু আমরাই তৈরি করছি। পৃথিবীর কোনও সভ্য উন্নত দেশে এখন ফরসেপ ডেলিভারি হয় না, একমাত্র এই ভারতেই হয়। আর তার ফলে যে কত বাচ্চার ব্রেন অ্যাফেকটেড হয় ভাবতে পারবেন না। নিজেদের বাবা-মা এদের নিয়ে লজ্জাবোধ করে। খুব অসহায় তারাও। সমাজে এদের স্থান নেই। পথের কুকুরের মতো এদের গায়ে ঢিল ছোঁড়ে, খারাপ মন্তব্য করে, নানা রকমভাবে অত্যাচার করে এদেরই সমবয়সী ছেলেরা। এরা বড় হয়ে গেলেও শিশু, কি যে করুণ অবস্থা এদের না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।’
দালান পেরিয়ে সামনের অফিস ঘরে এসে বসলেন অমলেন্দু। কৌতূহলী ছেলেমেয়েগুলি ঘুরছিল। একটি মেয়ে বলল—‘দাদু, তুমি আজ আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবে? তাই সকাল সকাল এসেছ?’
ঘোষাল হেসে বললেন—‘দুর্গাপুজোর জোগাড় করছিস তোরা। এখন কি বেড়াতে যেতে পারবি? আগে দীপু মা-কে ডেকে দে তো!’ বলতে বলতেই একটি মেয়ে এসে ঢুকল। বয়স অল্প, রূপের চেয়েও ছোট। বলল—‘বাবা, আজ এতো সকালে?’
অমলেন্দু বললেন—‘আমাদের বন্দনা বউদির কথা তোকে কতদিন বলেছি। আজ ওঁকে আনলাম। সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা। আগে অবশ্য একটু কফি খাওয়া।’
মেয়েটি তাড়াতাড়ি চলে গেল।
বন্দনা বলল—‘আপনার মেয়ে?’
—‘মেয়েও বলতে পারেন। পুত্রবধূও বলতে পারেন। অনেক দেখেশুনে ছেলের বিয়ে দিলাম। আপনাকে কার্ড দিয়েছিলাম। আপনি হয়ত ভুলে গেছেন। বছরখানেক পর অফিস থেকে ছেলেকে স্টেটসে পাঠাল। বেশি আর বলব কি, কয়েক মাসের মধ্যেই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেল। দীপু ফিরে এল। আমরা স্বামী-স্ত্রী তখন থেকে ওকে মেয়ের মতো করে মানুষ করলাম। ও কলেজে পড়ল, পাশ করল, নিজের ইচ্ছেয় নার্সিং-এর কোর্স নিল। তারপর ওর বিয়ের ব্যবস্থা করলাম। দীপুর বরকে আমি জামাই মনে করি বউদি। ও ডাক্তার। স্পেশালাইজ করেছে এই সব সমাজ-ছাড়া অভাগাদের দেখবার জন্য। প্রধানত ওরা দুজনে মিলেই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। স্বভাবতই আমিও জড়িয়ে পড়েছি। বউদি এরা সমাজের সৃষ্টি, মানুষের দায়, অথচ সমাজ এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমার সাধ্য সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমার যে ছেলে চলে গেছে তার শোক এই শিশুগুলির কান্নায়, অস্বাভাবিক চলাফেরায় রেখে দিয়ে গেছে।’ অমলেন্দু চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললেন, খুব মনোযোগ দিয়ে তিনি চশমার কাচ মুছছেন।
দীপু বলল—‘আমরা এদের কতকগুলো শ্রেণীবিভাগ করে নিয়েছি, প্রথমত তো ছেলে আর মেয়েদের বিভাগ আলাদাই। তাছাড়াও খুব গুরুতর, গুরুতর, অল্প জড়তা এইভাবে এদের আলাদা আলাদা ক্লাস নেওয়া হয়। হাতের কাজ শেখানো, গান-বাজনা শেখানো, শোনানো, এ সমস্তই ডাক্তারদের নির্দেশমতো হয়। এদের পড়াতে, এতটুকু কিছু শেখাতে বিস্তর পরিশ্রম, প্রচুর ধৈর্য আর বিশেষ ট্রেনিং-এর দরকার হয় কাকিমা। এদের স্বাভাবিক বুদ্ধি পাঁচ ছ বছরের শিশুর বেশি এগোয়নি।’
মেয়েদের ওয়ার্ডে একটি বছর বারো তেরর মেয়ে বিছানায় একেবারে বেঁকে পড়ে আছে দেখে শিউরে উঠল বন্দনা, বলল—‘ওর মুখ দিয়ে যে গাঁজলা উঠছে ডাক্তার ডাকবে না দীপু!’
দীপু বলল—‘ও সবসময়েই ডাক্তারের নজরে আছে কাকিমা। ওর অবস্থা আরও অনেক খারাপ ছিল নল দিয়ে ছাড়া খাওয়ানো যেত না। এখন তো তবু মাঝেমধ্যে সলিড খাওয়ানো যায়। সিভিয়ার এপিলেপসি ওর।’
মেয়েদের ওয়ার্ড ছাড়তেই ছেলেটি এসে বন্দনার হাত চেপে ধরল—‘মা, মা, তুমি যেও না।’
দীপু ইংরেজিতে বলল—‘কাকিমা, টুলুর মা মারা যাবার পর ওর বাবা ওকে এখানে রেখে গেছেন। ও সেমি-সিরিয়াস টাইপের পেশেন্ট। আপনাকে দেখে ওর মৃত মায়ের কথা কেন মনে হয়েছে কে জানে। আসলে ওরা স্নেহের জন্য, মায়ের জন্য কাঙাল কাকিমা, শিশু যখন সুন্দর হয়, আকর্ষণীয় হয় তখনই সে ভালোবাসা স্নেহ যত্ন পায়। নইলে আমরা খুব কৃপণ কাকিমা, আমাদের সব দানই এতো সীমাবদ্ধ! এদের দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন, স্নেহ-মমতা নিয়ে আমাদের গর্ব করার কিছু নেই। ওটা একটা রিফ্লেক্স। সুন্দর সুগন্ধ ফুলের জন্য যেমন আমরা আকর্ষণবোধ করি সুন্দর শিশুর জন্যও তেমনি।’
বন্দনা আস্তে আস্তে বলল—‘দীপু তুমি কি তোমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছ? তোমার এতো অল্প বয়স…!’
—‘তবু কেন স্নেহ-ভালোবাসার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি, জিজ্ঞাসা করছেন তো! ওই যে বললাম, এদের অনেকেরই বাবা-মা আছেন, কিন্তু আমাদের হাতে এদের ফেলে দিতে পেরে তাঁরা যেন নিশ্চিন্ত। আর তাঁদেরই বা কি বলব, এই সেদিন একজন মা হাউ-হাউ করে কাঁদছিলেন, বলছিলেন ‘আমার বাড়িতে আত্মীয়স্বজন কেউ আসে না। পাড়া-প্রতিবেশী এড়িয়ে চলে, মেয়ে বাইরে বেরোলেই পাড়ার ছেলেরা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করে, মেয়েও চোদ্দ-পনের বছরের হল। কে জানে কোনদিন এই অল্পবুদ্ধি মেয়েকে কে কিভাবে ব্যবহার করবে!’ দীপুর চোখ ছলছল করছে। এই সময়ে কুণাল নামের ছেলেটি দৌড়তে দৌড়তে এসে বন্দনার আঁচল ধরল—‘তুমি দুর্গাপুজোর সময় আমাদের বাড়ি আসবে, হ্যাঁ!’ তার চোখ-মুখে অকৃত্রিম ভালো বাসা। বন্দনা ডানহাত দিয়ে কুণালকে জড়িয়ে ধরে বলল—‘আসব, নিশ্চয় আসব।’ কুণাল খুশি হয়ে ঘোষালের গায়ে মাথা ঘোষল খানিকটা, তারপর লাফাতে লাফাতে চলে গেল।
বন্দনা বলল—‘একে তো অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না দাদা।’ দীপু হাসল, বলল—‘ও মাইল্ড। আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবু স্বাভাবিক বাচ্চাদের স্কুলে রেখে ওর কি হাল হয়েছিল শুনুন। ক্লাসের ছেলেরা রোজ ওর নামে মিথ্যে কথা বলে বলে ওকে টীচারের হাতে মার খাওয়াতো। রোজ। শুধু মার নয়, বকুনি, ব্যঙ্গ। শেষে একদিন ও ভীষণ রেগে গিয়ে দরজার চৌকাঠে যে ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল এবং সবাই মিলে ওর প্যান্ট খুলে নেবার মতলব করছিল, তার ওপর দরজাটা ঠাস করে বন্ধ করে দেয়। ছেলেটির মাথা ফেটে যায়। ওর স্কুল ওকে “নিষ্ঠুর প্রকৃতির বাচ্চা” বলে সাঙ্ঘাতিক বেত মেরে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়। মৃগী রোগটা ওর তারপর থেকে শুরু হয়েছে।’
ঘোষাল বললেন—‘স্নেহ-মায়া-মমতা-বিবেচনা-বিচক্ষণতা এই সব ভালো ভালো শব্দের বাইরের জীব এরা।’
বন্দনা বুঝতে পারছে তার ঠোঁট কাঁপছে। সে চোখের জল সামলাবার জন্য মুখ নিচু করে হঠাৎ তার কাপড়ের কুঁচির থেকে কম্পিত চোর-কাঁটা বাছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।
ফিরে আসবার সময়ে ছেলেমেয়েগুলি শাবল, খুরপি ফেলে আবার ঘিরে ধরল ওকে। ‘তুমি আসবে, আবার আসবে, কবে আসবে?’ মাতৃস্নেহর জন্য অবুঝ অবোধ অস্পষ্ট চিৎকার! টুলুর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কান্নায় বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তার মুখ। তার ছোট্ট পৃথিবী থেকে মা আবার চলে যাচ্ছে। সেই মানুষ একমাত্র যে স্নেহ-মমতা বলে বস্তুর স্বাদ তাকে দিয়ে গেছে।—‘টুলু কাঁদে না, আমি শিগগির আবার আসব!’ বন্দনা নিচু হয়ে ওকে আদর করে বলল।
গাড়ি ঘুরিয়ে অমলেন্দু এবার শহরের কেন্দ্রের পথ ধরলেন। বললেন—‘বউদি, মাথার চুল কেটেছেন, বেশ করেছেন। অমন পাঁচচুলো থাকলে রাস্তায় বেরোবেন কি করে?’ মেয়েদের একটি সেলুনের সামনে তাঁর গাড়ি থামল। বললেন, ‘চলুন, চুলটা ওরা ঠিক করে দিক।’ বন্দনার কোনও আপত্তিই শুনলেন না। পনের মিনিট পর বন্দনা বেরিয়ে আসতে বললেন—‘চলুন এবার একটু খাওয়াদাওয়া করা যাক। কোথায় যাবেন?’
বন্দনা বলল—‘আপনার যেখানে ইচ্ছে।’
এলিয়ট রোডের এক বাঙালি রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ সারা হল। পরিবেশন করছে মেয়েরা। খাওয়াদাওয়া শেষ করে মুখে পান দিয়ে ঘোষাল বললেন—‘এবার আমি আপনাকে আপনার বোনের বাড়ি পৌঁছে দেব, বউদি। আর পরশুদিন আমার বাড়ি আপনার নেমন্তন্ন, অফিস থেকে নিয়ে যাব। কালকের দিনটা আপনার ছুটি। এখন বোনের বাড়ির ডিরেকশনটা দিন।’
—‘বোনের বাড়ি? কে? কলি?’
—‘হ্যাঁ।’
—‘কেন দাদা?’
—‘আমার বাড়িই নিয়ে যেতাম। কিন্তু একদিনের পক্ষে একটু বেশি হয়ে যাবে আপনার। সেখানে আমার মিসেস রয়েছেন। হাজার হোক তিনি তো বাইরেরই লোক। আজ চলুন বোনের বাড়ি।’
কলি আজকাল ক্যামাক স্ট্রিটে থাকে। রঞ্জন আই. আই. টি। সঞ্জয় এখন অফিস। দরজা খুলে অমলেন্দু এবং তার পেছনে বন্দনাকে দেখে চমকে উঠল কলি। মুখে ভয়ের ছায়া। ‘কিছু হয়েছে?’
অমলেন্দু হেসে বললেন—‘আমাকে দেখলেই কি তোমার ভয় করে?’ চোখের সামান্য ইশারা করলেন। বললেন—‘বউদিকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম।’
বন্দনার মাথায় ঘোমটা। আপাদমস্তক সাদা। ভেতরে ঢুকতে তার মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়ল। কলি প্রথম থেকেই চমকে ছিল, এখন আতঙ্কিত হয়ে বলল—‘একি বউমণি?’
বন্দনার মাথার চুল ঘাড় অবধি। তাতে সাদার ছিট। তার পরনে থান। শ্বেতবর্ণ, কঠিন মূর্তি এক। কলির মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন। কিন্তু বউমণির মুখের ভাব অদ্ভুত, কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না কলির। কিন্তু রাগ হচ্ছে। ভীষণ রাগ। শেষকালে আর থাকতে পারল না, বলল- ‘বউমণি, এবার তো তাহলে আর পঁয়তাল্লিশ নম্বরে ফিরে যেতে কোন বাধা নেই!’
বন্দনা বলল—‘তা নেই। কলি। যাব। ওখানেই যাব। কিন্তু ফিরে যাব না। নতুন করে যাব।’
কলি বসে পড়ে বলল—‘বউমণি, কি হয়েছে?’ তার চোখে ভয়। বউমণিকে এরকম অদ্ভুত সুদূর, শান্ত, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এতো বড় সে কখনও দেখেনি। বন্দনা তেমনি দূর থেকে, কেমন এক রকমের অপার্থিব হাসি হেসে বলল— ‘ভয় পাচ্ছিস কলি! বড় ঘুম পাচ্ছে রে, আজ তোর কাছে একটু ঘুমোতে এসেছি। মনে হচ্ছে ভয়ে, লজ্জায়, শোকে, দুঃখে অনেকদিন ভালো করে ঘুমোইনি। কাল, কাল তোকে সব বলব। কাল শ্যামবাজারে যাব।’
অধ্যায় ৩২
কাঁধ অবধি কাঁচা-পাকা চুল মাথায়। সরু লাল পাড় সাদা শাড়ি পরনে। হঠাৎ দেখলে খুব ফ্যাশনদুরস্ত এক প্রবীণা বলে মনে হয়। বোঝা শক্ত, ছেলের ওপর দুরন্ত অভিমানে, নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায়, জীবনের প্রতি ধিক্কারে একদিন উনি চুল কেটে ফেলেছিলেন। সোনালি ফ্রেমের চশমার পেছনে গভীর আশ্বাস। ভুরুতে যেন অভয়মুদ্রা। আজ ওঁর ফেয়ারওয়েলের দিন। আর কোনও আলাদা দিনে ওঁকে কিছুতেই আনা যাবে না জেনে অফিসে ওঁর কাজের শেষ দিনটিতেই সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন সহকর্মীরা। উদ্যোক্তা জেনারেল ম্যানেজার পার্সোনেল— অনুপম সোমের পরিচালনায় অফিসার্স ক্লাব এবং ইউনিয়ন। টিফিনের পর সোম নিজে এসে যখন ওঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন বন্দনা তখন ভারি অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু কোনও পরিস্থিতির সামনে পড়ে গেলে বিব্রত হবার মানুষ মিসেস ভট্টাচার্য নন। মঞ্চের ওপর প্রশংসাসূচক বক্তৃতামালা তিনি প্রশান্ত মুখেই শুনে গেলেন। চশমার পেছনে চোখের মুদ্রা অপরিজ্ঞাত রইল। যেন বক্তৃতায় উল্লিখিত ব্যক্তি তিনি নন। শেষকালে তাঁকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ জানালেন অনুপম সোম।
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বন্দনা ভট্টাচার্যের গলার স্বরে গাম্ভীর্য এসেছে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন যেন প্রাচীন পাথরের মূর্তি। শূন্যের দিকে দৃষ্টি স্থির। অর্থব্যঞ্জনাময় এক আলোকিত শূন্য। বলছেন: ‘আপনাদের ভালোবাসার উত্তরে আমি আপনাদের আমার অন্তরতম আশীর্বাদ তো দিতে পারিই! কিন্তু কতটুকু মূল্য সেই বিমূর্ত আশীর্বাদের যদি তার সঙ্গে সাকার সাবয়ব আর কিছু না থাকে? জীবনকে কতকগুলো অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতার মালা করে কি লাভ? আনুষ্ঠানিক আশীর্বচনের বদলে যদি দিই এমন বিশ্বাস যা আপনারা জীবনের প্রতিদিন লগ্নি করতে পারবেন প্রতিদিন যার থেকে ফেরত পাবেন আশাতীত লভ্যাংশ? এই বিশ্বাস যদি কেউ জীবন দিয়ে পায়, তবে তাকে গ্রহণ করতেও সারাজীবনই লাগে। বিশ্বাস করুন মানুষের শক্তি শুধু নিজের জন্য, শুধু নিজের পরিবারের জন্য নয়। কণামাত্র হলেও কিছু শক্তি যদি অবশিষ্ট রাখেন, যদি তাকে সমর্পণ করেন দুঃখী, দুর্দশাগ্রস্ত, হতভাগ্য মানুষের জন্য, যদি একটিমাত্র অবোধ শিশুকেও পৃথিবীর আনন্দের শরিক করতে পারেন, একটিমাত্র দীনজনের কাছেও যদি বাঁচবার সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারেন, তবে সেই উৎস থেকেই আপনার জন্য সর্বদুঃখহর আনন্দধারা বইবে। আমাদের আসল শত্রু—রোগ, দারিদ্র্য, অপঘাত। এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার প্রকৃতিদত্ত হাতিয়ার আমাদের রয়েছে। তাকে আমরা পারস্পরিক বিবাদে, ঈর্ষায়, লোভে অপচয় করি। অথচ মানবযাত্রায় আমরা সবাই সমান শরিক। সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বমাপের দুঃখের মুখোমুখি হলেই সত্যিকারের সুখ আমাদের আয়ত্তে আসবে। আসবেই।’
শ্যামবাজারে ফিরতে দেখল কলি এসেছে। মুখে খুবই উদ্বেগের ছায়া। বন্দনা তার অফিসের উপহারগুলো কলির হাতে তুলে দিল। বউমণির সব রকমের প্রাপ্তিতেই কলির আনন্দ সবচেয়ে মুক্তধারা। কিন্তু কলি খুলে দেখল না কাশ্মীরি শালের প্যাকেট, ভালো ভালো বইয়ের বাক্স। শুকনো মুখে বলল—‘বউমণি, তুমি নাকি ইউরোপে যাচ্ছ? সারা ইউরোপ?’ সুতপা বলল—‘যাচ্ছেই তো। ভিসা পেয়ে গেছে।’
বন্দনা তার ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল—‘সবচেয়ে ধনী দেশগুলোয় যাব। বুঝলি কলি! সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, ফ্রান্স। আগে লন্ডনে পৌঁছই, দেখি কি শিডিউল করেছে ওরা। আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে ওরা কিছু করুক! প্রাচুর্যের অনেকটাই তো যার-পরনাই ভালো খেয়ে, ভালো পরে, ভালো শিখে তারপর উদ্দেশ্যহীন স্বেচ্ছাচারে খরচ করে ফেলছে। পৃথিবীতে যারা অপুষ্ট মস্তিষ্ক নিয়ে আসছে, তাদের দায়িত্ব যে ওদেরও, সে কথা ওদের বুঝিয়ে বলার দরকার। শুধু তো টাকা নয়! চাই প্রযুক্তিগত জ্ঞান, গবেষণা, অনেক ধৈর্য, পরিশ্রম, ডেডিকেশন! ওরা বুঝবে!’
কলি বলল—‘সঙ্গে কে যাচ্ছে বউমণি?’
—‘কে আর যাবে! সুতপাকে সঙ্গে নিতাম, কিন্তু এখানকার এই এত বড় রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার গড়ে তোলার মূল দায়িত্ব ওরই, ওদিকে দীপু নির্মাল্য একদম একলা। বাচ্চাগুলোকে সামলাতে কত লোক লাগে বল তো! কাজের লোক যে সত্যিই বড় কম রে কলি! তুই এলে যে আমাদের কত সুবিধে হয়!’
বউমণির ষাট বছর বয়স হল, যে বয়সে কলির মা দুম করে চলে গেছেন। কলি বউমণিকে মায়ের চেয়েও ভালোবাসে। বহুদিনের সুখ-দুঃখে, আত্যন্তিক সহমর্মিতায় গড়া দুর্লভ ভালোবাসা যা মরে তো না-ই, কমেও না, ক্রমাগতই বেড়ে যায়, ক্রমেই গভীর, আরো গভীর হয়। বউমণি এই বয়সে অত দূর যাবে? কখনও সে সমুদ্র পার হয়নি, সমুদ্র দূরের কথা ভারতবর্ষেই সে মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠানের কাজে দিল্লি ছাড়া কোথাও, কখনও যায়নি। বয়সটা ভালো না। কলি ঢোঁক গিলছে। ইতস্তত করে অবশেষে বলল—‘কেন বউমণি! ঘোষালদা তো তোমাদের ‘আত্মদীপ’-এর বড় কর্তা। বড় বড় কাজ করেছেন। বহু দেশ-বিদেশেও ঘুরেছেন। কত অভিজ্ঞতা! অবসরও রয়েছে। উনি যেতে পারেন না তোমার সঙ্গে?’
বন্দনা হেসে বলল—‘পারবেন না কেন? কিন্তু তার তো আর দরকার নেই!
