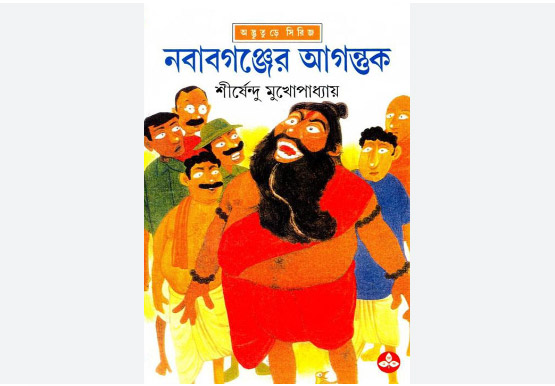১. ঘরে চোর ঢুকেছে
ঘরে চোর ঢুকেছে টের পেয়ে মাঝরাতে গবাক্ষবাবু বিছানায় উঠে বসলেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, “কে ঢুকেছিস রে ঘরে? যোগেন নাকি? নাকি পঞ্চানন! চারু নয় তো! হাবুল নাকি তুই?”
কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর একটা মোলায়েম গলা বলল, “আমি প্রিয়ংবদ।”
“প্রিয়ং… কী বললি?”
“বদ।”
“বদ তো তুই বটেই। বদের হাঁড়ি। কিন্তু নামটা নতুন হলেও গলাটা যে পুরনো! চেনা-চেনা ঠেকছে। তা নাম পালটালি কী করে?”
“কাছারিতে গিয়ে পয়সা খরচ করে মশাই।”
গবাক্ষবাবু মুখে একটা দুঃখসূচক চুক চুক শব্দ করে বললেন, “পয়সাটা বৃথাই গেল রে। গাঁ-গঞ্জের মানুষ কি আর এত ভাল নামের কদর বুঝবে? উচ্চারণই করতে পারবে না।”
কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মোলায়েম গলাটা বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলল, “গাঁয়ের লোকের উশ্চাটনের কথা আর বলবেন না মশাই। উশ্চাটন একেবারে যাচ্ছেতাই। আগে পঞ্চা-পঞ্চা করত, এখন পেড়াপেড়ি করায় বন্দু বন্দু বলে ডাকে। প্রিয়ংবদ উশ্চাটনই করতে পারে না।”
“তাই বল, তুই তা হলে আমাদের পুরনো পঞ্চা চোর! তা আমার বাড়িতে কী মনে করে? আমার বাড়িতে কি তোষাখানা খুলে বসেছি? না কি টাঁকশাল বসিয়েছি?”
“তা জানি মশাই। আপনি হুঁশিয়ার লোক। এ-বাড়িতে চোরের একাদশী।”
গবাক্ষবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, “তা হলে ঢুকলি যে! কী মতলব তোর?”
“টাকাপয়সার ভরসায় আসিনি। একখানা জিনিস খুঁজতে এসেছি।”
“জিনিস! জিনিসটাই বা কী এমন রেখেছি যে চোর ঢুকবে! তোদের কি ধারণা ঘরে দামি-দামি জিনিস রেখে চোরদের নেমন্তন্নের চিঠি পাঠিয়ে বসে আছি। আমি তেমন বান্দা নই।”
পঞ্চা খুক করে একটু হেসে বলল, “তা আর বলতে! ঘরের যা ছিরি করে রেখেছেন তাতে ঢুকতে লজ্জাই হয়। তক্তাগপাশের তো একখানা পায়াই নেই, ইটের ঠেকনো দিয়ে রেখেছেন। রান্নাঘরে কয়েকখানা মেটে হাঁড়িকুড়ি আর কলাই করা থালাবাটি। না মশাই, চোরেরও মান-সম্মান আছে।”
পঞ্চার এই কথায় গবাক্ষবাবুর একটু প্রেস্টিজে লাগল। তিনি অতিশয় গম্ভীর গলায় বললেন, “তা হলে কি তুই বলতে চাস আমি ছ্যাঁচড়া লোক?”
“বললে ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে। তবে সত্যি কথা বলতে হলে বলতেই হবে যে ছ্যাঁচড়া শব্দটা যেন আপনার জন্যই জন্মেছে। অনেক বাড়িতে ঢুকেছি মশাই, কারও বাড়িতে এমন দুর্দশা দেখিনি। চোরদের জন্য কি আপনার একটু মায়াও হয় না?”
গবাক্ষবাবু বেশ অপমান বোধ করছেন, কিন্তু প্রতিবাদ করারও উপায় নেই। পঞ্চা সত্যি কথাই বলছে। তাই গবাক্ষবাবু গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, “ভাল করে খুঁজলে কি আর টাকাটা সিকিটা পেতি না?”
“আজ্ঞে সেকথা ঠিক। খুঁজলে আপনার ঘরে টাকাটা সিকিটা কপালে যে জোটে না তা নয়। বাঁদিকে পায়ের কাছে তোশকের তলায় একখানা সিকি আছে, বালিশের তলায় একটা আধুলি, আলনায় যে ছেঁড়া জামাখানা ঝুলছে তার বাঁ পকেটে একখানা কাঁচা টাকাও আছে বটে, তবে সেটা অচল। আজ বাজারে আলুওলা টাকাটা নিতে চায়নি বলে আপনার খুব মেজাজ চড়ে ছিল।”
“টাকাটা মোটেই অচল নয়। চালালে দিব্যি চলে যাবে।”
“তা যাবে। সাঁঝবাজারে যে-লোকটা ঘানিঘরের পাশে বেগুন বেচতে বসে তার দু চোখে ছানি। তাকে গছাতে পারেন। নইলে ঈশেনপুরের নন্দী মহাজনের হাবাগোবা বাজার সরকার মহেশবাবুকে। নইলে জকপুর বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের অঙ্কের মাস্টার পাগলা কালীবাবুকে। ভারী আনমনা লোক। অঙ্কের পণ্ডিত হলে কী হবে, বাজার করতে গিয়ে সাত টাকা কিলোর সাড়ে তিনশো গ্রাম জিনিসের দাম কষতে গলদঘর্ম হতে হয়।”
ফাঁপরে পড়ে গবাক্ষবাবু বললেন, “এত ফ্যাচফ্যাচ করিস নে তো। টাকাটা অচল হলে কি আমিই নিতুম! বেকুব তো আর নই।”
“নিলেন আবার কোথা, এটা তো পড়ে পাওয়া। কথায় কথায় কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে মশাই। কালীর থানের সামনে যখন কাল বিকেলে আপনি টাকাটা কুড়িয়ে পেলেন তখন তো জগা বটতলায় বাঁধানো বেদিতে বসে পা দোলাচ্ছিল। স্বচক্ষে দেখেছে। টাকাটা পড়ে আছে সেটা জগাও জানত। কুড়িয়েছিল, তবে অচল দেখে ফের ফেলে রাখে।”
গবাক্ষবাবু ফের ফাঁপরে পড়ে বললেন, “একখানা টাকার তো মামলা। তা নিয়ে অত কচলাচ্ছিস কেন?না হয় অচলই হল টাকাটা, তাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হল শুনি।”
“না, টাকাটা সিকিটার কথা বলছিলেন কিনা, তাই বলা। ওসব ছোটখাটো ব্যাপারের জন্য আসা নয় মশাই। অন্য কাজ আছে।”
“সেইটে বলে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যেত। চোরেদের আজকাল যা আস্পর্ধা হয়েছে তা আর কহতব্য নয়। চুরি করতে ঢুকেছিস, কোথায় মিনমিন করবি, ঘাড় হেঁট করে থাকবি, ধরা পড়ে চোখের জল ফেলবি, হাতে পায়ে ধরবি, তা নয় উলটে গলা তুলে ঝগড়া করছিস!”
“ঝগড়া! কস্মিনকালেও কারও সঙ্গে ঝগড়া করিনি মশাই, তবে হ্যাঁ, দরকার হলে উচিত কথা বলতেও ছাড়ি না। আর চোর বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন কেন, চোর কি খেটে খায় না। আপনাদের চেয়ে তাদের খাটুনি বরং অনেক বেশি। আপনারা যখন নাকে তেল দিয়ে রাতে ঘুমোন তখন এই আমাদের রাত জেগে মেহনত করতে হয়। তার ওপর কাজের ঝুঁকিটাই কি কম? ধরা পড়লে গেরস্তের কিল, পুলিশের গুঁতো হজম করতে হয়, বরাত খারাপ হলে কড়া হাকিমের হাতে পড়ে হাজতবাসও আছে। চোর বলে কি মানুষ নই আমরা?”
“তা বটে। কিন্তু আমি তো বাপু তোকে কিলও দিইনি, পুলিশও ডাকার ইচ্ছে নেই। অত চটছিস কেন?”
“আপনি লোক তেমন খারাপ নন জানি। নইলে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুখ-দুঃখের কথা কইতুম নাকি? তবে সজনীবাবুর বাড়ির আড্ডায় গিয়ে গিয়ে আপনার স্বভাবটা খারাপ হচ্ছে।”
“কেন, সজনীবাবু কি লোক খারাপ?”
“তা আর বলতে! একে তো বাড়িখানাকে দুর্গ বানিয়ে রেখেছেন, তার ওপর পাইক বরকন্দাজ, বাঘা কুকুর মিলিয়ে নিচ্ছিদ্র অবস্থা। মাছিটি গলবার জো নেই। তবে তা সত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্মীকান্ত বাজি ফেলে সজনীবাবুর বাড়িতে ঢুকেছিল। যেমন পাকা হাত, তেমনই তার পাকা মাথা। চোরেদের সমাজে তাকে সবাই ওস্তাদ বলে মানত। তা লক্ষ্মীকান্ত পাইক বরকন্দাজকে ধোঁকা দিয়ে, কুকুরগুলোকে ফাঁকি দিয়ে একেবারে সজনীবাবুর শোয়ার ঘর অবধি পৌঁছেও গিয়েছিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে যায়। তারপর তার কী দুর্দশা!”
গবাক্ষবাবু সোৎসাহে বললেন, “কচুয়া ধোলাই খেল বুঝি? সজনীবাবুর পাইক বরকন্দাজ গায়ে গতরে খুব জোয়ান। তাদের রদ্দা খেলে আর দেখতে হচ্ছে না।”
“দুর মশাই! কোথায় রদ্দা! চোরেরা রদ্দার পরোয়া থোড়াই করে। আমাদের হাড় হল পাকা হাড়। কিলিয়ে আপনার হাতে ব্যথা হয়ে যাবে। আমাদের কিছুই হবে না।”
“তা হলে আর লক্ষ্মীকান্তর দুর্দশাটা কী হল? পুলিশের হাতে সোপর্দ হল নাকি?”
“তা হলেও অনেক ভাল ছিল। কিছুদিন ঘানি ঘুরিয়ে ছুটি হয়ে যেত। তা নয় মশাই। তার চেয়ে অনেক খারাপ। সজনীবাবু লক্ষ্মীকান্তকে ক্ষমা করে দিলেন।”
“বাঃ, সে তো মহৎ কাজ!”
“সবটা শুনুন, তারপর ফুট কাটবেন। ক্ষমা করে তারপর তাকে এক বাটি দুধ চিড়ে খাইয়ে বসালেন। তারপর সারারাত ধরে উপদেশ দিলেন। উপদেশ শুনতে শুনতে লক্ষ্মীকান্ত বেচারা হেদিয়ে পড়ল। ভোরবেলা পর্যন্ত উপদেশ গেলার পর সে চি চি করতে লাগল।”
গবাক্ষবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “আহা বেচারা! সত্যিই উপদেশের চেয়ে খারাপ কিছু হয় না রে!”
“তবেই বুঝুন, উপদেশ শুনলে তো আমার মাথা ঘোরে, শরীর ঝিমঝিম করে।”
“আমারও তাই। তারপর কী হল বল।”
“আজ্ঞে সে বড় দুঃখের উপাখ্যান। লক্ষ্মীকান্তর মতো অত বড় মান্যগণ্য চোর শেষে সজনীবাবুর পা দুটো চেপে ধরে বলল, এবার একটু চুপ দেন কর্তা, যা বলেন করতে রাজি আছি। তারপর কী হল জানেন? সজনীবাবু লক্ষ্মীকান্তকে মা কালীর সামনে দিব্যি দিয়ে চুরি ছাড়ালেন। তারপর নিজের গাঁটের কড়ি দিয়ে তাকে শ্যামপুরের বাজারে দোকান খুলে দিলেন।”
“বাঃ! এ তো মহৎ কাজ!”
“সে আপনাদের কাছে। আমাদের কাছে এ হল চূড়ান্ত অধঃপতন। অতবড় ডাকসাইটে চোর এখন নুন, তেল, তেজপাতা, হলুদ, জিরে বিক্রি করে সারাদিন। বসে বসে দু-চার আনা লাভের আঁক কষে। রাত্রিবেলা হাই তুলে তুড়ি মেরে দুর্গা নাম জপ করে পাশবালিশ আঁকড়ে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। কী সাঙ্ঘাতিক অধঃপতন বলুন তো। মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ করতে গেলে হাতজোড় করে কাঁদো কাঁদো মুখে বলে কী জানেন? বলে ভাই রে, আমাকে আর মানুষ বলে গণ্য করিস না তোরা। আমি উচ্ছন্নে গেছি।”
“বুঝলুম।”
“তাই বলছিলাম, সজনীবাবুর সঙ্গে মেলামেশা করাটা আপনার ঠিক হচ্ছে না। কত বড় একটা প্রতিভাকে উনি নষ্ট করে দিলেন বলুন তো!”
“তা অবশ্য ঠিক। তোর কথা শুনে লক্ষ্মীকান্তের জন্য আমার একটু কষ্টও হচ্ছে। কী আর করবি বল, যা হওয়ার হয়ে গেছে। তোরা একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলিস, তা হলেই হবে। সজনীবাবুর বাড়িতে আর কেউ না ঢুকলেই হল।”
“বলেন কী মশাই! ওবাড়িতে চুরি করার প্রেস্টিজই আলাদা। নিখিল নবাবগঞ্জ দলিত তস্কর সমাজে কেঁড়া দিয়েছে, ও-বাড়িতে যে চুরি করতে পারবে তাকে সোনার মেডেল দেওয়া হবে।
“অ্যাঁ। দলিত কী যেন বললি।”
“নিখিল নবাবগঞ্জ দলিত তস্কর সমাজ।”
“দলিত! দলিত মানে কী?”
“তা কে জানে মশাই। তবে কথাটা নাকি আজকাল খুব চালু। আমাদের ফটিক লেখাপড়া জানা লোক, ময়নাগড় বাসবনলিনী বিদ্যাপীঠে ক্লাস টেন অবধি নাকি পড়েছিল। সে-ই কথাটা জোগাড় করেছে।”
গবাক্ষবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “তা না হয় হল, কিন্তু সোনার মেডেলের লোভে ফের বিপদে পড়া কি ভাল? সজনীবাবুর তো শুধু পাইকবরকন্দাজই নেই, শ্যামাপদ তান্ত্রিকও আছে। পিশাচসিদ্ধ কাঁপালিক, দিনকে রাত করতে পারে।”
“তা খুব জানি। আমার তো মনে হয় লক্ষ্মীকান্তকে ভেড়া বানানোর মূলে শ্যামা তান্ত্রিকের হাত আছে। তবে আমাদের হাতেও তারা তান্ত্রিক আছে।”
“তারা তান্ত্রিক! সে আবার কে? নামটা শুনিনি তো!”
“শুনবেন কী করে? নতুন এসেছেন। জটেশ্বরের জঙ্গলে একটা পুরনো শ্মশানে আস্তানা। ভারী দুর্গম জায়গা। শ্যামা তান্ত্রিককে গুলে খেতে পারেন উনি।”
“বটে রে?”
“আজ্ঞে খুব বটে। তারা তান্ত্রিক রাতের বেলা বাদুড়ের মতো উড়তে পারে। উড়ে উড়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক চলে যায়। তার একটা কাজেই তো আপনার বাড়িতে আসা।”
একটু আঁতকে উঠে গবাক্ষবাবু বললেন, “ওরে বাবা, তান্ত্রিকের আবার আমার বাড়িতে কী কাজ?”
“ঘাবড়াবেন না। কাজ সামান্য। উনি একটা জিনিস খুঁজতে পাঠিয়েছেন।”
“ওরে বাবা। আমার বাড়িতে আবার কী জিনিস খুঁজবি? সোনা-দানা-মোহর তো আমার নেই রে বাপু।”
“মোহর কে খুঁজছে? তারাবাবার কি মোহরের অভাব? হাত নেড়ে মোহরের পাহাড় তৈরি করতে পারেন।”
“বটে। তা হলে কী খুঁজছিস?”
“ছুঁচ মশাই, একখানা ছুঁচ।”
“ছুঁচ! ঠিক শুনেছি তো রে! ছুঁচ?”
“ঠিকই শুনেছেন। একটা কাঁচের শিশির মধ্যে একটা ছুঁচ। তারা বাবার সেটা খুব দরকার।”
“ছুঁচ। তা ছুঁচের অভাব কী? ছেঁড়া জামাটামা সেলাই করার জন্য আমার কয়েকটা ছুঁচ আছে।”
“আরে না মশাই, যেমন-তেমন ছুঁচ নয়। এ অন্যরকম ছুঁচ।”
“কীরকম?”
“অতশত জানি না। বলেছেন, একখানা বেশ লম্বা নলের মতো শিশিতে পোরা একখানা ছুঁচ আছে। অনেকটা গুনছুঁচের মতোই।”
একগাল হেসে গবাক্ষবাবু বললেন, “গুনষ্ঠুচ খুঁজছিস সেটা বলবি তো। সেও আমার আছে। তবে শিশিটিশি নেই, সেটা তোকে জোগাড় করে নিতে হবে।”
“দুর মশাই, গুনছুঁচ হলে কি আর রাতবিরেতের মশার কামড় খেয়ে আপনার মতো কঞ্জুষের ঘরে ঢুকি! জিনিসটা মোটা ছুঁচের মতো দেখতে হলেও ঠিক ছুঁচ নয়।”
“তা হলে এই যে বললি ছুঁচ! আবার বলছিস ছুঁচ নয়?”
“না মশাই, আপনাকে বোঝানো আমার কর্ম নয়, ছুঁচের ইতিবৃত্তান্তও জানা নেই। তারাবাবা বলেছেন এই নবাবগঞ্জের কারও বাড়িতেই ছুঁচটা আছে। আমরা পাঁচজন ঘরে ঘরে ঢুকে খুঁজে হয়রান হচ্ছি। মেহনতটা জলেই গেল দেখছি।”
“তা ছুঁচটা দিয়ে তারাবাবা কী করবেন তা বলতে পারিস? চট টট সেলাই করবেন নাকি?”
“তা কে জানে! ছুঁচ দিয়ে বাণও মারতে পারেন। অতশত জানি না। খুঁজতে বলেছেন বলে খুঁজে যাচ্ছি। আপনার বাড়িতে নেই তা হলে?”
“না বাপু, অত কেরানির চুঁচ নেই আমার। খুঁজে দেখতে পারিস।”
একটা তাচ্ছিল্যের “হুঁ“ শব্দ করে পঞ্চানন জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল, গবাক্ষবাবু দেখলেন। তারপর অন্ধকারেই একটু হাসলেন। ব্যাটা কাঁচা চোর। ভাল করে খুঁজলে পেয়ে যেত। জিনিসটা তেমন লুকিয়েও রাখেননি গবাক্ষবাবু। দিন পাঁচেক আগে ভোরবেলা পায়চারি করতে গিয়ে পথেই শিশিটা কুড়িয়ে পান। শিশিটিশি কাজের জিনিস ভেবে কুড়িয়ে নিয়ে দেখেন, তার মধ্যে একটা ষ্টুও রয়েছে। কাজে লাগতে পারে ভেবে সেটা এনে দেরাজে রেখে দিয়েছিলেন। ছুঁচ খুঁজতে যে চোর আসবে তা কে জানত।
গবাক্ষবাবু উঠলেন। বালিশের পাশ থেকে দেশলাই নিয়ে একটা মোমবাতি জ্বালালেন। জানলা বন্ধ করে সাবধানে দেরাজ খুলে দেখলেন কাঁচের শিশিটা ঠিকই আছে। কিন্তু এর জন্য যখন চোর এসেছে তখন আর অসাবধানে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। গবাক্ষবাবু জিনিসটা হাতে নিয়ে একটু ভাবলেন। তারপর বিছানার চাঁদরটা তুলে তোশকটা দেখলেন। তোশকটা তাঁর খুবই পছন্দ হল। ছেঁড়া তোশকের মধ্যে অজস্র ফুটো। তোশকের এক ধারে একখানা পছন্দসই ফুটো পেয়ে তার মধ্যে জিনিসটা ঢুকিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হলেন। রাতবিরেতে ফের ছুঁচের খোঁজে চোর এলে সুবিধে করতে পারবেনা। তাঁর ঘুম খুব সজাগ। তবে ছুঁচটার গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারছিলেন না।
২. সকালবেলাটা আজ বেশ ভালই ছিল
সকালবেলাটা আজ বেশ ভালই ছিল। দিব্যি পুবদিকে হাসি-হাসি মুখ করে সুয্যিঠাকুর উঠি-উঠি করছিলেন। উলটোদিকের বাড়ির গবাক্ষবাবু দাঁতন করতে করতে বাড়ির সামনে পায়চারি করছিলেন। আর গলাখাঁকারি দিচ্ছিলেন। পাশেই তাঁর ভাই অলিন্দবাবু নিজের দোতলা বাড়ির বারান্দায় ডনবৈঠক করছিলেন। নবাবগঞ্জে নবাগত জ্ঞানপাগলা মাথায় একটা রঙিন টুপি পরে নরহরিবাবুর বাড়ির বাইরের সিঁড়িতে বসে গম্ভীর মুখে কী যেন ভাবছিল। আর নরহরিবাবু নিজে বাইরের ঘরে বসে জুত করে তাঁর প্রিয় জলখাবার মুড়ি আর নারকেল কোরা খেতে খেতে ভারী আরাম করছিলেন।
ঠিক এই সময়ে সজনীবাবু প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন দেখে নরহরি ভদ্রতাবশে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে একগাল হেসে বলেছিলেন, “পেন্নাম হই সজনীবাবু, প্রাতর্জমণে বেরিয়েছেন বুঝি!”
সজনীবাবু খুবই রাশভারী মানুষ। কেউ কিছু বললে বা জিজ্ঞেস করলে হুঁ হাঁ দিয়ে জবাব সারেন। বেশি কথা কন না। আজ হঠাৎ কী হল কে জানে। দাঁড়িয়ে একবার অপাঙ্গে নরহরিবাবুর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, “ওঃ নরহরিবাবু। তা কী খবর?”
নরহরিবাবুর হাতে তখনও মুড়ির বাটি, গালের মুড়িক’টা তাড়াতাড়ি চিবোতে চিবোতে বললেন, “আজ্ঞে ভাল। খবর বেশ ভাল।”
“মুড়ি খাচ্ছেন বুঝি? বাঃ, বেশ।”
মুড়ির বাটিটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে এসেছেন দেখে নরহরিবাবু ভারী লজ্জা পেয়ে বললেন, “এই চাট্টি খাচ্ছিলাম আর কি!”
“বেশ, বেশ। তা আপনি তো অভয় বিদ্যাপীঠে বাংলাই পড়ান!?”
“যে আজ্ঞে।”
“আচ্ছা, কাল থেকে একটা শব্দের মানে খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি কি বলতে পারেন কল্যবর্ত’ কথাটার মানে কী?”
বিনা মেঘে বজ্রপাত আর কাকে বলে? কল্যবর্ত শুনেই মুখের মুড়িটা বিস্বাদ ঠেকতে লাগল। ভাবলেন, কলা দিয়ে মুড়িটা মেখে খেতে বলছেন কি না। মুড়িতে কলা মেখে বেশ একটা আবর্তের সৃষ্টি করেই কি কল্যবর্ত হয়?
সজনীবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, “আচ্ছা চলি।” সেই থেকে সকালটাই মাটি। সজনীবাবুর প্রশ্নটা গবাক্ষবাবু শুনতে পেয়েছেন, কারণ তাঁর দাঁতন থেমে গেছে। অলিন্দবাবুও শুনেছেন, কারণ বৈঠকি ছেড়ে তিনি রেলিঙের ওপর দিয়ে বুকে নরহরিবাবুর দুর্দশা দেখছেন। শুধু জ্ঞানপাগলাই যা নির্বিকার।
নরহরিবাবু ঘরে এসে মুড়ির বাটিটা নামিয়ে রেখে বিরস মুখে গিন্নিকে বললেন, “না, চাকরিটা গেল।”
“কেন, চাকরি গেল কেন? এই সাতসকালে কারও চাকরি যায় বলে তো শুনিনি বাপু!”
“আর সকাল-বিকেলের হিসেব করে কী হবে? চাকরিটা নেই বলেই ধরে নাও। এর পরেও কি আর কারও চাকরি থাকে?”
“কী হয়েছে সেটা বলবে তো!”
“সজনীবাবু প্রাতভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, দোষের মধ্যে আমি তাঁকে কুশল প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম। উনি উলটে আমাকে এমন একটা শক্ত শব্দের মানে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি হাঁ হয়ে গেলাম। চাকরিটাও তো করি ওঁরই ইস্কুলে, অভয় বিদ্যাপীঠ সজনীবাবুর বাবার নামে। উনিই সর্বেসর্বা।”
“কীসের মানে বলতে পারোনি শুনি।”
“সে আর শুনে কী করবে। জন্মেও অমন শব্দ শুনিনি। কল্যবর্ত।”
গিন্নি চোখ কপালে তুলে বললেন, “ওমা! এই সোজা শব্দটার মানে বলতে পারোনি! কলাভর্তা মানে তো কলা সেদ্ধ!”
নরহরি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, “কলাভর্তা নয় গো, কল্যবর্ত।” গিন্নি বললেন, “এ তো আরবি ফার্সি শব্দ বলে মনে হচ্ছে। তা অত ভেঙে পড়ার কী আছে! ডিকশনারিতে অমন শক্ত শক্ত শব্দ অনেক থাকে। সবাই কি আর সব কিছুর মানে জেনে বসে আছে? তুমি মুড়ি খাও তো৷”।
গিন্নির কথায় যুক্তি আছে বটে, কিন্তু তাতে নরহরির তাপিত হৃদয় শান্ত হল না। মুড়ি খাওয়ার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু গলা দিয়ে নামতেই চাইল না। আর নামবেই বা কী করে! জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলেন, রাস্তার ওপাশে অলিন্দবাবু তাঁর দোতলার বারান্দা থেকে নীচে তাঁর দাদা গবাক্ষবাবুকে কী যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বলছেন। জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে নরহরি শুনতে পেলেন, অলিন্দবাবু উত্তেজিতভাবে বলছেন, “এঃ, এই ইস্কুলে আর ছেলেটাকে পড়ানো যাবে না দেখছি। বাংলার মাস্টার যখন এমন সোজা শব্দটার অর্থ বলতে পারল না তখন ইস্কুলের অবস্থা তো বুঝতেই পারছ!”
“তা আর বলতে। শব্দটা কী যেন! ওই সময়ে একটা কাক এমন কা করে ডেকে উঠল যে, শুনতে পাইনি।”
“শোনোনি? আরে কল্যবর্ত, কল্যবর্ত।”
“অ। তা এ তো বেশ সোজা জিনিস। আমারই ভারী চেনা-চেনা ঠেকছে। মানেটা পেটে আসছে, মুখে আসছে না।”
“আরে কল্যবর্ত হচ্ছে এক ধরনের মর্তমান কলা। অ্যাই বড়বড় সাইজের হয়। আমার শ্বশুরবাড়ির দিকে তো কল্যবর্তের ঝাড়।”
জ্ঞানপাগলা খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, “পারেনি, পারেনি। মানে বলতে পারেনি।”
পাগলাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী লোক থাকে। বলতে কী, পৃথিবীর অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষকে সাধারণ বিচারে পাগল বলেই মনে হয়। কার ভেতরে কী আছে বলা তো যায় না!নরহরিবাবু তাই চাপা গলায় ডাকলেন, “ওরে জ্ঞানপাগলা! ও জ্ঞানবাবাজি! একটু ইদিকে আয় তো!”
জ্ঞানপাগলা একটু বিরক্তির ভাব করল মুখে, তবে উঠেও এল। জানলার কাছে এসে বলল, “আমার কি খিদে পায় না নাকি? সেই সকাল থেকে বসে বসে কত ভাল-ভাল কথা ভাবছি, কেউ একটু ডেকে একটু জিলিপি কিংবা বোঁদে খেতে বলল না মশাই!”
নরহরিবাবু বললেন, “খাবি বাবা! এই যে, এই যে এক বাটি নারকোল মুড়ি।”
পাগলা গম্ভীর হয়ে বলল, “অন্যের এঁটোকাঁটা খাই না। আমি নয়নগড়ের রাজবাড়ির ছেলে, ভুলে গেলেন নাকি?”
“ওঃ, তাও তো বটে। তুই তো আবার রাজাগজা। তা কী খাবি বাপু বল।”
“পাঁচুর দোকানের কচুরি আর জিলিপি। দুটো টাকা ফেলুন।”
“তা না হয় দিলাম, কিন্তু কল্যবৰ্ত কথাটার অর্থ বলতে পারিস?”
ঠোঁট উলটে জ্ঞানপাগলা বলল, “সেটা আর শক্ত কী? সকালের জলখাবারকেই কল্যবর্ত বলে। দিন, টাকা দুটো দিন।”
ধুস। দুটো টাকাই জলে গেল। জ্ঞানপাগলাকে জিজ্ঞেস করাটাই আহাম্মকি হয়েছে। অত শক্ত শব্দটার কী মানেই না করল ব্যাটা। যাই হোক, দুটো টাকা গচ্চা দিয়ে নরহরি উঠে পড়লেন। বাজারে যেতে হবে।
কিন্তু বাজারে গিয়েও বিপদ। আলুওলা শ্রীদাম তাঁকে দেখেই হাসি-হাসি মুখ করে বলল, “এই যে মাস্টারমশাই, শুনলুম সজনীবাবু নাকি আজ সকালে আপনার পরীক্ষা নিয়েছেন আর আপনি নাকি ফেলুস মেরেছেন।”
নরহরি প্রমাদ গুনলেন। চাকরি তো গেছেই, এবার প্রেস্টিজও গেল। কথাটা যে এত তাড়াতাড়ি চাউর হয়ে গেছে তা দেখে নরহরি তাজ্জব। আলুটা কিনেই তাড়াতাড়ি বাজার থেকে সটকাবার তালে ছিলেন নরহরিবাবু। কিন্তু হঠাৎ বিপিন উকিল এসে পথ আটকাল।
“এই যে নরহরিবাবু! শুনলুম কল্যবর্ত কথাটার মানে বলতে পারেননি! আর শক্তটা কীসের? কল্য মানে কাল, মানে আগামী কালই ধরুন। আর বর্তমানে বেঁচেবর্তে থাকা। সোজা মানেটা দাঁড়াল, যা বাজার পড়েছে, দিনকালের যা অবস্থা, তাতে আগামী কাল অবধি বর্তে থাকলেই বাঁচি। বুঝলেন?”
“যে আজ্ঞে।”
বিপিনবাবু হেঃ হেঃ করে খুব আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। তাঁর পাশে হঠাৎই আবির্ভূত হলেন যোগেনবাবু। দশাসই চেহারা, একসময়ে ব্যায়ামবীর ছিলেন। একবার প্রতিযোগিতায় মিস্টার নবাবগঞ্জ হয়েছিলেন। এখন নবাবগঞ্জ স্বাস্থ্যশ্রী ব্যায়ামাগার খুলে ছেলেদের ব্যায়াম শেখান। বিপিন উকিলকে হাত দিয়ে সরিয়ে যোগেনবাবু বললেন, “ভুল শুনেছেন। ওটা হবে কলাপত্র। মানেও খুব সোজা, কলার পাতা।”
নরহরিবাবু অগাধ জলে। যে যা বলছে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? তার ওপর যোগেনবাবু ব্যায়ামবীর আর বিপিনবাবু উকিল। তিনি ঘাড় কাত করে বললেন, “যে আজ্ঞে।”
ফেরার সময় নরহরিবাবু আর লোকালয় দিয়ে ফিরলেন না। একটু ঘুরে মাঠ-ময়দান ভেঙে, বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে উদাসভাবে হাঁটতে লাগলেন। তারপর একটা বটতলায় বসে পরিস্থিতিটা ভাবতে লাগলেন। চাকরি গেলে কী হবে তা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছেন না। সামনে যেন ধুধু মরুভূমি। তার ওপর লোকলজ্জা। অনেক ভেবেচিন্তে হঠাৎ শ্যামাপদ তান্ত্রিকের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।
সজনীবাবু শ্যামা তান্ত্রিকের কথায় ওঠেন বসেন। ময়না নদীর ধারে একখানা কালীমন্দিরও বানিয়ে দিয়েছেন তাকে। শ্যামা তান্ত্রিক সেখানে সাধনভজন করে, মারণ উচাটন করে। তার নাকি পোষা ভূতও আছে। শ্যামা তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে হত্যে দিলে এ-যাত্রায় বেঁচেও যেতে পারেন নরহরি! অন্ধকারের মধ্যে একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে নরহরি উঠে পড়লেন।
দেদার ঘি-দুধ আর পাঁঠার মাংস খেয়ে শ্যামা তান্ত্রিকের চেহারাটা হয়েছে পেল্লায়। রাগী মানুষ। ভক্তরা ট্যান্ডাইম্যান্ডাই করলে তেড়ে আসে। তল্লাটে তার বেজায় প্রতাপ, সবাই ভয় খায়। নরহরি যখন গুটি গুটি শ্যামা তান্ত্রিকের ডেরায় হাজির হলেন তখন তাঁর পিলে চমকানোর মতো অবস্থা। মন্দিরের বারান্দায় শ্যামা তান্ত্রিক রক্তাম্বর পরে বসা, কপালে কুটি। সামনে বসা দশ-বারোজন ভক্তের দিকে রক্তচক্ষুতে চেয়ে বিকট গলায় চেঁচাচ্ছে, “কাঁচ্চা খেয়ে ফেলব, কাঁচ্চা খেয়ে ফেলব বলে দিলাম! নিয়ে আয় ব্যাটাকে ধরে, দেখি তার ধড়ে ক’টা মুণ্ডু আছে! তন্ত্রমন্ত্র দেখাতে এসেছে নবাবগঞ্জে! এখনও তো চেনেনি এই শর্মাকে! এখনও জানে না, এই দশখানা গাঁ জুড়ে গোটা এলাকার ওপর আমার দখল। হুঁ, তারা তান্ত্রিক! তন্ত্রের ব্যাটা জানেটা কী? কিছু নয়, কিছু নয়। পাছে বিদ্যে ধরা পড়ে যায় সেই ভয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ানোর হিম্মত নেই। ব্যাটা গিয়ে জটেশ্বরের জঙ্গলে পুরনো শ্মশানে থানা গেড়েছে। যতসব চোরচোট্টা বদমাশরা গিয়ে জড়ো হয়েছে সেখানে।” শ্যামা তান্ত্রিকের মেজাজ দেখে সবাই তটস্থ। শ্যামা হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়ল, “তোমরা কেউ যাও নাকি ওখানে?” সবাই সমস্বরে বলে উঠল, “আজ্ঞে না।”
“খবর্দার যাবে না। ও জোচ্চোর লোক, ভুলভাল মন্তর পড়ে তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। বুঝেছ?”
সবাই বলে উঠল, “যে আজ্ঞে।” তারা তান্ত্রিকটা কে তা নরহরি জানেন না। তবে এটা বুঝতে কষ্ট নেই যে, জনৈক তারা তান্ত্রিকের সঙ্গে শ্যামা তান্ত্রিকের একটা অদৃশ্য লড়াই চলছে। কথায় বলে ঠেকায় পড়লে বুদ্ধি খোলে, নরহরির মাথাতেও একটা দুষ্টবুদ্ধি চিড়িক দিয়ে উঠল। তিনি ভক্তদের মধ্যে বসে পড়ে হাতজোড় করে বললেন, “আজ্ঞে আমাকেও লোকে টানাটানি করেছিল বটে তারা তান্ত্রিকের কাছে যাওয়ার জন্য।”
শ্যামা তান্ত্রিক বজ্রপাত ঘটানোর মতো গলায় হুঙ্কার ছাড়ল, “বটে! বটে! কার এত বুকের পাটা?”
“কিছু পাজি লোক। তবে আমি যাইনি। ভাবলুম আমাদের শ্যামা মহারাজ থাকতে তারা তান্ত্রিকের কাছে যাব কেন! ওস্তাদ থাকতে আনাড়ির কাছে কেউ যায়?”
শ্যামা তান্ত্রিক একটু নরম হল। গলা এক পরদা নামিয়ে বলল, “তুই অভয় ইস্কুলের মাস্টার না?”
“যে আজ্ঞে বাবা। বড় বিপদে পড়ে এসেছি।”
“আরে বিপদে পড়েই তো লোকে আমার কাছে আসে। আমি হলুম বিপত্তারণ। তা তোর বিপদটা কীসের?”
“আজ্ঞে চাকরি যায় যায়।”
“কেন, কেন, চাকরি যাবে কেন?”
একজন ভক্ত ফস করে বলে উঠল, “আজ্ঞে, উনি কৈবল্য শব্দের মানে বলতে পারেননি, সেইজন্য সজনীবাবু খুব চটে গেছে।”
“কৈবল্য!” বলে হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসল শ্যামা তান্ত্রিক। তারপর হাসি-হাসি মুখেই বলল, “কৈবল্য, কেবল কৈবল্য। কেবলম, কেবলম। কৈবল্য হচ্ছে ওই করাল কালী। কালী কৈবল্যদায়িনী। বুঝলি।”
হাতজোড় করে নরহরি বললেন, “আজ্ঞে বুঝেছি। তবে কথাটা কৈবল্য নয়, কল্যবর্ত।”
“কী, কী বললি?”
“আজ্ঞে, কল্যবর্ত।”
“কল্যবর্ত।” আবার হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে শ্যামা তান্ত্রিক বলল, “ঘুরছে, ঘুরছে, সব ঘুরছে। বুঝলি? স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে ঘুরছে, বিঘূর্ণিত হচ্ছে মহাকাশ। সত্য-স্রেতা-দ্বাপরকলি সব চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে ওই কাল। মহাকাল। কালের আবর্ত রে, মহাকালের ঘূর্ণিঝড়। আর তাকেই বলে কল্যবর্ত। বুঝেছিস?”
“আজ্ঞে, আপনি মহাজ্ঞানী। এবার জলের মতো বুঝেছি।”
“হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।”
“কিন্তু চাকরিটা গেলে যে মহাকালের ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে যাব মহারাজ।”
শ্যামা তান্ত্রিক দুলে দুলে একটু হেসে বলল, “পারবে ওই তারা জোচ্চোর এর মানে করতে? কেন যে লোকে ঠকবাজটার কাছে যায়। এবার ওকে কাঁচ্চা খেয়ে নেব। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।”
নরহরি কাঁচুমাচু মুখে বললেন, “খুব ভাল হয় তা হলে মহারাজ।”
শ্যামা তান্ত্রিক তাঁর দিকে একটু কুটিল নয়নে চেয়ে বলল, “খবর্দার, ওই তারা জোচ্চোরটার কাছে যাস নে। আমি সজনীকে বলে দেব’খন তোর চাকরিটা যাতে বজায় থাকে।”
পাঁচখানা টাকা প্রণামী দিয়ে নরহরি উঠে পড়লেন। বুকে একটু বল পাচ্ছেন এখন।
মনটা ভাল নেই। কথাটা চারদিকে রটে গেছে। ইস্কুলেও এই নিয়ে কথা হবে, ছাত্ররা দুয়ো দেবে। তবু বাড়ি ফিরে নেয়ে-খেয়ে নরহরি ইস্কুলেও গেলেন। আর যাই হোক, ফাঁসি তো আর হবে না।
যা ভয় করেছিলেন, তাই হল। ইস্কুলে পা দিতে-না-দিতেই দফতরি ফটিক এসে বলল, “হেডমাস্টারমশাই থমথমে মুখ করে আপনার জন্য বসে আছেন। ঘরে মেলা লোক জড়ো হয়েছে। আপনার ফাঁসির হুকুম না হয়ে যায় আজ! যান, শিগগির যান।”
নরহরির পা দুটো কাঁপতে লাগল, বুকে ধড়ফড়ানি। চোখে হলুদ-হলুদ ফুলও দেখতে লাগলেন। তবু মরিয়া হয়ে বুক ঠুকে এগিয়েও গেলেন। মরতেও তো একদিন হবেই।
হেডসারের ঘরে মাস্টারমশাইরা জড়ো হয়েছেন। জনাচারেক অভিভাবক বসে আছেন। সকলের মুখেই আষাঢ়ের মেঘ।
তেজেনবাবু নরহরিকে দেখে বললেন, “বসুন। আপনার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ এসেছে। কয়েকজন অভিভাবক দরখাস্ত করেছেন আপনাকে বরখাস্ত করার জন্য। আপনি নাকি কী একটা শব্দের অর্থ সজনীবাবুকে বলতে পারেননি।”
নরহরি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “হ্যাঁ, কল্যবর্ত।”
তেজেনবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, “পৃথিবীর সেরা পণ্ডিতরাও সব শব্দের অর্থ জানেন না। যাই হোক, অভিভাবকরা কেউ কি শব্দটার অর্থ জানেন?”
অভিভাবকরা একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিলেন। নৃপেন বৈরাগী বললেন, “এর মানে হচ্ছে ইয়ে আর কি। ওই যে–যাকে বলে–”
আর এক অভিভাবক সুধীর বৈষ্ণব বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো–খুব সোজা মানে, ওটা হচ্ছে গিয়ে–”
তৃতীয় অভিভাবক হরিপ্রিয় দাস বললেন, “আরে কলিকালের শেষ যখন হয় তখনই হয় কল্যবর্ত।”
তেজেনবাবু গুরুগম্ভীর গলায় বললেন, “আপনারা বসুন, দক্ষিণাবাবুকে লাইব্রেরি থেকে বাংলা অভিধান আনতে পাঠিয়েছি। তিনি এলেন বলে।”
কথা শেষ হতে না-হতেই হন্তদন্ত হয়ে দক্ষিণাবাবু এসে ঢুকলেন। হাতে মহাভারতের সাইজের অভিধান। ঢুকেই বললেন, “অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!”
তেজেনবাবু বললেন, “অবিশ্বাস্যটা কী?”
“আজ্ঞে, এরকম একটা শক্ত শব্দের অর্থ যে এত সোজা সেটাই অবিশ্বাস্য।”
“মানেটা তো বলবেন।”
“কল্যবর্ত মানে হচ্ছে প্রাতরাশ, অর্থাৎ সকালের জলখাবার। ব্রেকফাস্ট।”
সবাই হাঁ হয়ে থাকলেন।
তেজেনবাবু মুচকি একটু হেসে অভিভাবকদের দিকে চেয়ে বললেন, “শুনলেন তো! আমি নরহরিবাবুর কোনও দোষ দেখছি না। শব্দটার অর্থ আপনাদের মতো আমাদেরও জানা ছিল না। এবার আপনারা আসুন গিয়ে।”
অভিভাবকরা ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে গেলেন। তেজেনবাবু মাস্টারমশাইদের দিকে চেয়ে বললেন, “আপনারা সবাই যে যার ক্লাসে যান। নরহরিবাবুর ব্যাপারটা নিয়ে ছাত্ররা যাতে আলোচনা না করে সেদিকে লক্ষ রাখবেন।”
সবাই চলে গেলেও নরহরিবাবু বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।
তেজেনবাবু বললেন, “আপনি ঘাবড়াবেন না। সজনীবাবু প্রকাশ্যে আপনাকে শব্দটার অর্থ জিজ্ঞেস করে অন্যায় করেছেন। আমরা আপনার পক্ষেই আছি। তবে সজনীবাবু খামখেয়ালি লোক, তাঁর প্রতাপও দোর্দণ্ড। তিনি কী করবেন তা জানি না।”
নরহরিবাবু সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, “তেজেনবাবু একটা কথা।”
“কী কথা?”
“কল্যবর্তমানে যে সকালের জলখাবার, এটা জ্ঞানপাগলা আমাকে বলে দিয়েছিল।”
“অ্যাাঁ, বলেন কী! পাগলাটা জানল কী করে? আমরাই জানতাম না।”
“তাই তো ভাবছি।”
৩. অগ্রহায়ণ মাসের শেষ
অগ্রহায়ণ মাসের শেষ। শীতের শুরুতে বেশ জম্পেশ করে বৃষ্টি নেমেছে সন্ধেবেলা। নবাবগঞ্জের রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে এসেছে। তবু বৃষ্টির মধ্যেই জনাচারেক আড্ডাধারী ছাতা মাথায় দিয়ে এসে সজনীবাবুর বৈঠকখানায় জড়ো হয়েছে। ঘরের এক কোণে একটা জলচৌকির ওপর আসনপিড়ি হয়ে শ্যামা তান্ত্রিকও বসা।
হাতটাত কচলে হেঃ হেঃ করে বিগলিত হাসি হেসে গবাক্ষবাবু বললেন, “ওঃ, আজ সকালে যা একখানা দিলেন না সজনীবাবু, একেবারে গুগলি। নরু মাস্টারের আর বাক্য সরল না।”
সজনীবাবু খুব উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, “নরু মাস্টার কে?”
“আরে আমাদের অভয় বিদ্যাপীঠের বাংলার মাস্টার নরহরি।”
“ওঃ, তা হবে। তা তাকে সকালে কিছু বলেছি নাকি?”
গবাক্ষ অবাক হয়ে বলেন, “বলেননি? সেই যে কল্যবর্ত শব্দের মানে জিজ্ঞেস করলেন আর নরু মাস্টার হাঁ হয়ে গেল! সারা গাঁয়ে তো টি-টি পড়ে গেছে তাই নিয়ে।”
সুধীরবাবু বললেন, “আমরা তো গণ দরখাস্ত নিয়ে ইস্কুলে গিয়ে নরু মাস্টারকে বরখাস্ত করার দাবি পর্যন্ত জানিয়েছি।”
সজনীবাবু উদাস নয়নে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, “আহা, মাস্টার মানুষ, ক’টা পয়সাই বা মাইনে পায়। ও চাকরি তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। বেচারাকে বরখাস্ত করার দরকারটাই বা কী? আছে থাক।”
নৃপেন বৈরাগী হেঁঃ হেঃ করে বলল, “আপনার মতো দয়ার শরীর আর দেখিনি। মহাশত্রুকেও হাসিমুখে ক্ষমা করে দিতে পারেন।”
সজনীবাবু করুণ গলায় বললেন, “এই শ্যামাদাও আমাকে একটু আগে বলছিলেন নরহরি মাস্টারের চাকরিটা যাতে না খাই। আমি ভাবি, চাকরি খাওয়ার মতো পাষণ্ড তো নই রে বাপু।”
গবাক্ষবাবু বিগলিত হয়ে বললেন, “পাষণ্ড! আপনাকে পাষণ্ড বলবে কার ঘাড়ে ক’টা মাথা? সাধারণ মানুষের কথা ছেড়ে দিন, এমনকী চোর-ডাকাতরাও আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই তো কাল রাতেই আমার বাড়িতে একটা চোর ঢুকেছিল–”
হরিপ্রিয়বাবু অবাক হয়ে বললেন, “আপনার বাড়িতে চোর? বলেন কী মশাই? এমন আহাম্মক চোর ভূ-ভারতে আছে নাকি? সবাই জানে আপনি চোর-ডাকাতের ভয়ে আপনার সব টাকা-পয়সা আর দামি জিনিসপত্র নয়াগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতে গচ্ছিত রেখেছেন। চোর তবে কীসের আশায় এসেছিল?”
একথাটায় খোঁচা ছিল বলে একটু লজ্জা পেয়ে গবাক্ষবাবু বললেন, “সেকথা অস্বীকার করছি না। চোরটা যে কেন এসেছিল সেটাও ভেঙে বলেনি। তবে তার সঙ্গে আমার অনেক কথা হল।”
সজনীবাবু মৃদু হেসে বললেন, “চোরের সঙ্গে কথা! আপনি তো তা হলে বেশ আলাপি লোক।”
একটু হেঁ হেঁ করে গবাক্ষ বললেন, “আজ্ঞে আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে ওই গুণটা আমার আছে বটে।”
নৃপেন বৈরাগী বলল, “আহা, কথাটা কী হল সেটাই বলো না! বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে।”
গবাক্ষবাবু বললেন, “হ্যাঁ, চোরটা বলছিল সজনীবাবুকে এ যুগের যুধিষ্ঠির বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিংবা নবাবগঞ্জের গান্ধী। চোরদের এক সর্দার নাকি একবার সজনীবাবুর বাড়িতে ঢুকে ধরা পড়েছিল। তার নাম লক্ষ্মীকান্ত। তা সজনীবাবু তাকে শুধু ক্ষমাই ৩০
করেননি, কোথায় যেন একটা দোকান করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। সত্যি নাকি সজনীবাবু?”
সজনীবাবু উদাস নয়নে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “তা হবে। কত লোককেই তো রোজ ক্ষমা করতে হয়, কে তার হিসেব রাখে বলুন।”
হরিপ্রিয় বলে উঠলেন, “সে তো বটেই, সে তো বটেই।”
গবাক্ষবাবু বললেন, “চোরটা কিন্তু একটা ভয়ের কথাও বলল।”
নৃপেন বৈরাগী বলেন, “ভয়ের কথা। সে আবার কী?”
“চোরেরা নাকি তারা তান্ত্রিক নামে একজন নতুন তান্ত্রিককে পেয়ে গেছে। তার নাকি অনেক ক্ষমতা।”
এতক্ষণ শ্যামা তান্ত্রিক নিশ্চল হয়ে বসে ছিল। একথা শুনেই হঠাৎ ‘ব্যোমকালী’ বলে এমন হুঙ্কার ছাড়ল, সবাই চমকে উঠল। শ্যামা তান্ত্রিক গুরুগম্ভীর গলায় বলল, “কাঁচা খেয়ে নেব তাকে। বাণ মেরে এ-ফোঁড় ওফোঁড় করে দেব। তার মুণ্ডু নিয়ে–”
সজনীবাবু ভারী মোলায়েম গলায় বললেন, “ছাড়ুন তো শ্যামাদা। কোথাকার কে এক চুনোপুটি তারা তান্ত্রিককে নিয়ে খামোখা উত্তেজিত হচ্ছেন। আমরা তো জানি আপনার মতো তন্ত্রসিদ্ধ মানুষ কমই আছে। ক্ষমাই করে দিন না।”
শ্যামা তান্ত্রিক আবার একটু মিইয়ে গেল। মৃদুস্বরে কালী, কালী’ বলতে বলতে চোখ বুজে ফেলল।
সুধীর বৈষ্ণব একটু ফিচেল হাসি হেসে বললেন, “শ্যামাদাদা আগে খুব তারা, তারা’ জপ করতেন, তারা তান্ত্রিকের ওপর খাপ্পা হওয়ার পর থেকে আর ও নাম উচ্চারণও করেন না।”
একথায় শ্যামা তান্ত্রিক চোখ খুলে সুধীরবাবুকে ভস্ম করে দেওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বলল, “সে নির্বংশ হবে, তার চেলারাও নির্বংশ হবে। মাথায় বজ্রাঘাত হবে–”
সজনীবাবু আবার মৃদুস্বরে বললেন, “আহা, শ্যামাদা, মাথা গরম করবেন না। আপনি চটলে যে মহাপ্রলয় হয়ে যাবে।”
শ্যামা আবার মিইয়ে গেল। গবাক্ষবাবু বললেন, “আরও একটা খবর আছে, বলব কি?”
হরিপ্রিয় বললেন, “আহা, খবরটবরের জন্যই তো এখানে আসা। বলে ফেলো, বলে ফেলল।”
“শুনলুম, জ্ঞানপাগলা নাকি কল্যবৰ্ত কথাটার মানে আগেই নরহরিবাবুকে বলে দিয়েছিল। তখন নরহরিবাবুর বিশ্বাস হয়নি বটে, কিন্তু পরে দেখলেন, পাগলা ঠিকই বলেছিল।”
নৃপেনবাবু হঠাৎ খেচিয়ে উঠে বললেন, “এ, জ্ঞানপাগলা বড় পণ্ডিত এসেছেন কিনা। কল্যবর্ত মানে তো আমরাও জানতুম। কী বলল সুধীর, কী বলল হরিপ্রিয়?”
“হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই তো।”
“হেডমাস্টার তেজেনবাবু যখন আমাদের জব্দ করার জন্য উলটে আমাদেরই কল্যবর্ত মানে জিজ্ঞেস করল তখন আমরা তো বুক ফুলিয়েই বলে দিলাম যে, কল্যবর্তমানে সকালের জলখাবার। শুনে তেজেনবাবু চুপসে গেলেন।”
সজনীবাবু ভারী অবাক হয়ে বললেন, “তাই নাকি? তা হলে তো বলতে হয় আপনারা বেশ জ্ঞানী লোক।”
নৃপেনবাবু লজ্জার ভাব করে বললেন, “না, না, এ আর এমন কী!”
সজনীবাবু মৃদু-মৃদু হেসে বললেন, “আমি আরও একটা শব্দ নিয়ে বড় ধন্ধে পড়েছি। তা আপনারা জ্ঞানী মানুষ, বলতে পারেন
এসকলাশি শব্দটার সঠিক অর্থ কী হবে?”
নৃপেনবাবু হঠাৎ শশব্যস্তে উঠে পড়ে বললেন, “এই রে, নাতিটার সকাল থেকে জ্বরভাব, দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে যেতে হবে। একেবারে মনে ছিল না।”
সুধীরবাবুও তড়াক করে উঠে পড়ে বললেন, “গেল বোধ হয় আমার ছাতাটা। ভুল করে ছাতাটা দিনু মুদির দোকানে ফেলে এসেছি।”
উঠি-উঠি ভাব করে হরিবাবু বললেন, “সকাল থেকে মাথাটা ঘুরছে। শশধর ডাক্তারকে একবার প্রেশারটা না দেখালেই নয়।”
তিনজনেই উঠে পড়েছে দেখে সজনীবাবু মৃদু হেসে বললেন, “আরে তাড়া কীসের? শব্দটার অর্থ আজ না বললেও চলবে। বসুন, বসুন, চা আর পাঁপড়ভাজা আসছে।”
তিনজনেই ফের বসে পড়লেন।
সজনীবাবু তাঁর শান্ত চোখে গবাক্ষবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই জ্ঞানপাগলাটা কে বলুন তো! আগে তো নাম শুনিনি!”
গবাক্ষবাবু বললেন, “নাম শোনার কথাও নয়। এই নতুন এসেছে। আজ সকালেই তো নরহরির বারান্দার সিঁড়িতে বসে ছিল, দেখেননি? মাথায় রঙিন টুপি, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল।”
“অ। তা দেখে থাকব হয়তো, ভাল করে খেয়াল করিনি। তা সে কেমন পাগল?”
গবাক্ষবাবু বলার আগেই নৃপেনবাবু বলে উঠলেন, “খুব দেমাকের পাগল মশাই, কারও বাড়িতে এটোকাঁটা খাবে না, ফাঁইফরমাশ খাটবে না।”
হরিপ্রিয় বললেন, “ফিলজফার ফিলজফার ভাব। মুখ গোমড়া করে সবসময়ে কী যেন ভাবে।”
গবাক্ষবাবু বললেন, “একটা মজা আছে, ভিক্ষেটিক্ষে চায় না।”
সজনীবাবু বললেন, “তবে চলে কীসে?”
নৃপেনবাবু বললেন, “লোকে এমনিতেই দেয়। ছদ্মবেশী মহাপুরুষ বলেই ভাবে বোধ হয়।”
গবাক্ষবাবু বললেন, “সে নাকি কোথাকার রাজপুত্তুর। লোকের কাছে পয়সা চাওয়ার সময় বলে, ভিক্ষে নয় বাপু, খাজনা নিচ্ছি।”
সজনীবাবু বলেন, “রাজপুত্তুর! বাঃ বেশ! তা কোথাকার রাজপুত্তুর তা জানেন?”
নৃপেনবাবু মুখোনা বিকৃত করে বললেন, “পাগলের কথার কি মাথামুণ্ডু আছে! সে নাকি নয়নগড়ের রাজপুত্তুর। নয়নগড়ের নাম তো জন্মে শুনিনি বাপু।”
সজনীবাবু হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।
হরিপ্রিয় বললেন, “নবাবগঞ্জে নতুন নতুন চিড়িয়া আসছে কিন্তু। একটা তান্ত্রিক, একটা পাগল, আরও কে আসে কে জানে বাবা।”
সুধীর বৈষ্ণব বললেন, “আসুক, আসুক, যত আসবে ততই খেল জমবে।”
চা আর পাঁপড়ভাজা খেয়ে শুধু শ্যামা তান্ত্রিক ছাড়া সবাই উঠে পড়লেন। রাত প্রায় ন’টা বাজে। বাইরে এখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়াও দিচ্ছে খুব। রাস্তাঘাট খুবই ফাঁকা।
সজনীবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু তফাতে এসেই নৃপেনবাবু খ্যাঁক করে উঠলেন, “সজনীবাবুর আক্কেলটা দেখলে সুধীরভায়া? কথা নেই, বার্তা নেই, দুম করে একটা শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করে বসলেন! কেন বাপু, আমরা কি ওঁর ইস্কুলের পড়ুয়া নাকি? এ তো ঘোর অপমান!”
সুধীরবাবু বললেন, “টাকার গরম, দেমাকের গরম সব মিলিয়ে লোকটা একেবারে টং হয়ে আছে।”
হরিপ্রিয় বললেন, “ওরে বাপু, টাকাটাও তো করেছে বাঁকা পথে। কাজকারবার তো কিছু তেমন দেখছি না, কিন্তু লাখ-লাখো টাকা যে কোত্থেকে আসছে কে জানে। তুমি কী বলল হে গবাক্ষভায়া?”
গবাক্ষবাবু বললেন, “সত্যি কথাই বলেছেন। সজনীবাবুকে নিয়ে একটা রহস্য আছে।”
নৃপেনবাবু বললেন, “আমার তো মনে হয় ওই শ্যামা তান্ত্রিকের সঙ্গে সাঁট করে ভেতরে ভেতরে কোনও কাজকারবার চলছে।”
সুধীরবাবু একমত হয়ে বলেন, “তাও হতে পারে।”
বটতলার গজাননের তেলেভাজার দোকানে ঝাঁপের তলায় গুটিসুটি মেরে বসা জ্ঞানপাগলাকে দেখে নৃপেনবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, “জ্ঞানপাগলা না?”
গবাক্ষবাবু বললেন, “হ্যাঁ, জ্ঞানপাগলাই। গজানন জ্ঞানপাগলাকে রোজ রাতে পরোটা আর আলুর দম খাওয়ায়।”
নৃপেনবাবু অবাক হয়ে বলেন, “বলো কী? কেন, খাওয়ায় কেন?”
“গজানন মনে করে জ্ঞানপাগলা সত্যিই রাজপুত্তুর। শুধু গজানন কেন, নবাবগঞ্জের অনেকেরই ধারণা জ্ঞানপাগলা সাধারণ লোক নয়।”
“হুঁঃ, যত্তসব আহাম্মক। রাজপুত্তুর আজকাল গাছে ফলছে কি না। রাজপুত্তুর হওয়া অত সোজা নয়।”
এত লোককে একসঙ্গে মুখোমুখি দেখে জ্ঞানপাগলা জুলজুল করে চেয়ে মাথার রঙিন টুপিটা খুলে মাথাটা একটু চুলকে নিয়ে বলল, “তোমরা কি খাজনা দিতে এসেছ?”
নৃপেনবাবু পয়সাওলা লোক, ফস করে পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে বললেন, “নিবি? আর একটা শক্ত কথার মানে বলে দে দিকিনি বাবা।”
জ্ঞানপাগলা কুটি করে বলল, “কেন, আমি কি ডিকশনারি নাকি?”
“সবাই বলে তুই জ্ঞানী মানুষ। পাগল সেজে থাকিস বটে, কিন্তু জ্ঞানের নাড়ি টনটনে।”
জ্ঞান চোখ পাকিয়ে বলে, “পাগল! আমি পাগল! আমি হলুম নয়নগড়ের যুবরাজকুমার। খবর্দার ফের ওকথা উচ্চারণ কোরো না।”
জোড়হাত করে নৃপেনবাবু বললেন, “ভুল হয়ে গেছে রে বাপু, মাপ করে দে। বুড়োমানুষ, সবসময়ে সব কথা খেয়াল থাকে না। এই যে আরও পাঁচটা টাকা।”
টাকা পকেটে গুঁজে জ্ঞান বলল, “কী জানতে চাও?”
“এসকলাশি শব্দটার মানে বলতে পারিস বাবা?”
“দুর! এসব তো ইংরিজি শব্দের অপভ্রংশ। পরীক্ষায় ভাল ফল করলে আমার ঠাকুমা বলে বেড়াত, আমার নাতি এসকলাশি পেয়েছে। এর মানে হচ্ছে জলপানি, স্কলারশিপ।”
চারজন একটু মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন। হরিপ্রিয় মৃদু স্বরে বললেন, “মনে হয় ঠিকই বলছে।”
সুধীরবাবুও বললেন, “আমারও তাই মনে হচ্ছে।” নৃপেনবাবু পাঁচ পাঁচ দশ টাকা খসিয়ে শব্দটার মানে জেনেছেন। তিনি শুধু বললেন, “হু।”
জ্ঞানপাগলা বলল, “খাজনার কথা এত ভুলে যাও কেন? ভূস্বামীকে যদি তার পাওনা না দাও তা হলে মাটির অভিশাপ লাগে, জানো?”
নৃপেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “আমরা আবার কবে তোর প্রজা হলুম কে জানে বাবা। তবে তুই জ্ঞানী মানুষ, মাঝে মাঝে খাজনা তোকে দিতে হবে দেখছি।”
জ্ঞানপাগলা একটু ছটাক খানিক হেসে বলল, “খাজনা আদায় করতেই তো আসা।”
.
ওদিকে সজনীবাবু তাঁর ঘরে কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে বসে থেকে হঠাৎ বললেন, “শ্যামাদা, জ্ঞানপাগলটা আসলে কে বলো তো?”
শ্যামা নিমিলিত নেত্রে চেয়ে বলল, “কেন, বাণ টান মারতে হবে নাকি?”
“না, না, ওসব নয়। আগে খোঁজ নাও লোকটা কে, কত বয়স, কোথা থেকে আসছে।”
“কালকেই খোঁজ নিচ্ছি, চিন্তা নেই।”
“ভাল করে খোঁজ নিয়ো। আজেবাজে গুজবে কান দিয়ো না।”
“আরে না, ভাল করেই খোঁজ নেব। দরকার হলে মহেশ দারোগাকে লাগিয়ে দেব। মহেশ আমাকে খুব খাতির করে।”
“আহা, অত হট্টগোল পাকিয়ে দরকার কী? মহেশকে বললে সে হয়তো পাগলকে কোমরে দড়ি দিয়ে থানায় নিয়ে যাবে, তোক জানাজানি হবে। আমি চাইছি গোপনে খবর নিতে, কেউ যেন টের না পায়।”
“তারও ভাবনা নেই। বিশেকে লাগিয়ে দেব’খন। সে চোর ছ্যাঁচড় যাই হোক, খুব চালাক চতুর। পেটের কথা টেনে বের করতে তার জুড়ি নেই। তবে সে মজুরি চাইবে।”
“কত চাইবে?”
“গোটা পঞ্চাশেক টাকায় হয়ে যাবে।”
সজনীবাবু টাকাটা বের করে দিয়ে বললেন, “কালই খবর চাই।”
টাকাটা ট্যাকে গুঁজে শ্যামা তান্ত্রিক উঠে পড়ল। বাইরে তার দু’জন চেলা অপেক্ষা করছিল, শ্যামা বেরোতেই দু’জন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। একজন একটা ছাতা মেলে ধরল শ্যামার মাথার ওপর।
বজ্র গম্ভীর স্বরে দু’বার কালী, কালী’ বলে শ্যামা রাস্তায় নেমে পড়ল। বৃষ্টির তোড় একটু বেড়েছে, বাতাসের জোরও। রাস্তাঘাট যেমন নির্জন তেমনই অন্ধকার।
দ্বিতীয় চেলা একটা টর্চ জ্বেলে বলল, “একটু দেখে চলবেন বাবা। রাস্তায় জল জমে গেছে।”
শ্যামা সবেগে জল ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে বলল, “ওরে, টর্চের আলোতে কি আমি পথ দেখি? আমি দেখি ধ্যানের চোখে, তৃতীয় নয়নে। সামনে মা হাঁটছেন, দেখতে পাচ্ছিস না? ওই দ্যাখ শ্যামা মা কেমন মল বাজাতে বাজাতে চলেছেন। দেখতে পাচ্ছিস?”
“আমাদের পাপী চোখ বাবা, এই চোখে কি দেখা যায়?”
“হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।”
অট্টহাসি শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ দশাসই চেহারা নিয়ে গদাম করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল শ্যামা। তারপরই আর্ত চিৎকার, “বাবা রে!”
চেলা দু’জন পেছনে ছিল। এ ঘটনায় হতচকিত হয়ে টর্চ জ্বালাতেই তারা দেখতে পেল, কোনও বদমাশ রাস্তার দু’ধারে দুটো গাছে আড়াআড়ি একটা দড়ি বেঁধে রেখেছে। তাইতেই পা বেঁধে পড়ে গেছে শ্যামা।
“ওরে, হাঁ করে দেখছিস কী? ধরে তোল!” শ্যামা চেঁচাল। চেলারা গিয়ে তাড়াতাড়ি টেনে তুলল শ্যামাকে। জলে কাদায় দাড়ি গোঁফ রক্তাম্বর সব মাখামাখি। মাজায় চোটও হয়েছে। হাঁফাতে হাঁফাতে শ্যামা বলল, “কোন বদমাশ …?”
সামনের অন্ধকার থেকে কে যেন বলে উঠল, “এটা হল এক নম্বর।”
“কে? কে রে বদমাশ? কে ওখানে?”
কেউ জবাব দিল না।
চেলাদের একজন ভয়-খাওয়া গলায় বলে, “একটু পা চালিয়ে চলুন বাবা, এ তো বেহ্মদত্যির গলা বলে মনে হচ্ছে।”
শ্যামা খচিয়ে উঠে বলে, “নিকুচি করেছি ব্ৰহ্মদত্যির। টর্চের আলোটা ভাল করে ফেল তো, হাঁটু দুটোর ছালবাকল বোধ হয় উঠেই গেছে। গতকাল মাঝরাত্তিরে মা ব্রহ্মময়ী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন বটে, তোর একটা ফাঁড়া আসছে, পথেঘাটে সাবধান। তা কথাটা খেয়াল ছিল না।”
চেলার টর্চের আলোয় দেখা গেল, দুটো হাঁটুরই নুনছাল উঠেছে।
শ্যামা তান্ত্রিক চাপা গলায় বলল, “ঘটনাটার কথা কাউকে বলার দরকার নেই। বুঝলি?”
দু’জনে একসঙ্গেই বলে উঠল, “যে আজ্ঞে।”
আর তৃতীয় নয়নের ওপর ভরসা হল না শ্যামা তান্ত্রিকের। একজন চেলা সামনে টর্চ জ্বেলে পথ দেখাতে লাগল, অন্যজন ছাতা ধরে রইল। শ্যামা তান্ত্রিক ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ডেরার দিকে হাঁটতে লাগল।
টর্চওলা চেলা বলল, “ব্যাপারটা কিন্তু ভয়েরই হয়ে দাঁড়াল বাবা।”
শ্যামা বলল, “কোন ব্যাপারটা?”
“ওই যে কে একজন বলল এটা এক নম্বর। তার মানে এর পর দু’নম্বর, তিন নম্বর, চার নম্বর হতে থাকবে। কোথায় গিয়ে শেষ হবে আন্দাজ করতে পারছে কি?”
মুখটা বিকৃত করে শ্যামা তান্ত্রিক বলল, “ভয়ের কিছু নেই। কোনও বদমাশ ছেলেপুলে কাণ্ডটা করে রেখেছিল। দাঁড়া না, আজ রাতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ধ্যানে বসলেই সব জানতে পারব।”
ছাতা-ধরা লোকটা বলল, “কিন্তু গলাটা তো বাচ্চা ছেলেপুলের বলে মনে হল না। বেশ ভারী গলা।”
“বললুম তো, যে-ই হোক এই শর্মার কাছে তার পরিচয় গোপন থাকবে না। ধ্যানে বসলেই বায়োস্কোপের ছবির মতো সব ভেসে উঠবে চোখের সামনে। তবে একাজ কার তা বুঝতে আমার বাকি নেই।”
টর্চওলা সোৎসাহে বলল, “কে বটে বাবা?”
“কে আবার, ওই তারা তান্ত্রিক। তন্ত্রের তোত-ও জানে না, গুলগাপ্পা দিয়ে কিছু লোকের মাথা খেয়েছে। এখন তন্ত্রের শক্তিতে
পেরে এইসব হীন পন্থায় জব্দ করার চেষ্টা করছে আমাকে। ভীম যেমন দুঃশাসনের রক্ত পান করেছিল, আমারও তেমনই ইচ্ছে যায় ব্যাটাকে বুকে হাঁটু দিয়ে”
ছাতাওলা বলল, “কুপিত হবেন না বাবা, আপনি কুপিত হলে সর্বনাশ।”
“কিন্তু লোকটার কেমন বাড় বেড়েছে দেখেছিস! ওর চেলাচামুণ্ডারা হল সব চোর-চোট্টাবদমাশ। তাদের কাউকে দিয়েই কাণ্ডটা করিয়েছে। দাঁড়া, আমিও দেখাচ্ছি মজা।”
টর্চলা বলল, “তারা তান্ত্রিকের কিন্তু আজকাল খুব নাম হয়েছে বাবা। অনেকে বলে, তারা তান্ত্রিকের অনেক ক্ষমতা।”
শ্যামা হুঙ্কার দিল, “কাঁচ্চা খেয়ে নেব। মা কালীর সামনে হাড়িকাঠে বলি দেব ব্যাটাকে।”
৪. জ্ঞানপাগলা
জ্ঞানপাগলা আজকাল তাঁর বাড়ির বারান্দাতেই রাতে এসে শোয়। তাই আজ নরহরি সজাগ ছিলেন। জ্ঞান যে সোজা লোক নয় তা আজ তিনি ভাল করেই বুঝে গেছেন। গিন্নিকে বললেন, “ওগো, জ্ঞান কিন্তু ছদ্মবেশী লোক। বোধ হয় পাগল হওয়ার আগে প্রফেসর টফেসর কিছু ছিল। হেলাফেলা করা ঠিক হবে না। অমন শক্ত শব্দটার অর্থ কেমন পট করে বলে দিল বলে দিকিনি। এক কাজ করো, আজ রাতে পাগলটাকে ভাল করে ভাতটাত খাওয়াও। আর বাইরের ঘরে একটা বস্তা আর চাঁদর পেতে বিছানাও করে দাও। বাইরে এই বৃষ্টিবাদলায় শুয়ে অসুখ করলে আমাদের পাপ হবে।”
গিন্নি পাপকে ভারী ভয় পান। বললেন, “তার তো আবার বড় দেমাক, এটোকাঁটা খাবে না।”
“এঁটোকাঁটা দেওয়ার দরকার কী? ভাল করেই খাওয়াও।”
নরহরি তক্কে তক্কে ছিলেন। রাত দশটা নাগাদ গজানন একটা ছাতা মাথায় ধরে জ্ঞানকে পৌঁছে দিয়ে যেতেই নরহরি বেরিয়ে এসে বিগলিত হয়ে বললেন, “ওরে জ্ঞান, আজ আর বাইরের বারান্দায় কষ্ট করে শুতে হবে না বাবা, আয় ঘরে তোর বিছানা পেতেছি।”
জ্ঞান তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, “দুর! ঘরে শুলে এতবড় রাজ্যপাট দেখবে কে? চারদিকে নজর রাখতে হবে না?”
“ও বাবা! তাও তো বটে! তুই তো আবার নয়নগড়ের যুবরাজ! তা হলে বারান্দাতেই না হয় কিছু পেতেটেতে দিই।”
“কী দেবে? চট তো! ওসবে আমার সম্মান থাকে না। তার চেয়ে এই মেঝেতে বেশ বসে আছি। ভূমির অধিপতি ভূমিতে বসলে মান যায় না।”
নরহরি একটু অপ্রতিভ হলেন।
তাঁর গিন্নি ভাতের থালা নিয়ে এলে জ্ঞানপাগলা বলল, “দাঁড়াও, দাঁড়াও, আজ তো তোমাদের পালা নয়! আজ গজাননের পালা ছিল। তোমাদের যদি একান্তই ইচ্ছে হয় তা হলে পরশুদিন খাওয়াতে পারো। আর শোনো, ওইসব ঘ্যাঁট ম্যাট হেঁচকি টেচকি আমি খাই না। খাওয়ালে ঘি দিয়ে ভাজা পরোটা আর আলুর দম খাওয়াবে।”
নরহরি আর চাপাচাপি করলেন না। ঘরে দোর দিয়ে শুয়ে পড়লেন। জ্ঞানপাগলা বারান্দায় বসে রইল।
দৃশ্যটা উলটো দিকের বাড়ি থেকে গবাক্ষবাবু দেখছিলেন। ওই যে জ্ঞানপাগলা বসে আছে, এটা তাঁর একটা অস্বস্তির কারণ হচ্ছে আজ। এক কথা হল, জ্ঞানপাগলা যে হাতা ন্যাতা পাগল নয় তা আজ গবাক্ষবাবু বুঝে গেছেন। দ্বিতীয় কথা হল, জ্ঞানপাগলা নয়নগড়ের রাজপুত্তুর শুনে সজনীবাবু যেন হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন আজ। ভয় পেলেন কিনা বোঝা গেল না, তবে যেন একটু চিন্তায় পড়লেন। গবাক্ষবাবু একটু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন। অস্বস্তিটা সেই কারণেও।
জানলার ফাঁক দিয়ে তিনি আবছা অন্ধকারে খানিকক্ষণ জ্ঞানপাগলাকে লক্ষ করলেন। নরহরির ঘরের আলো নিভে যেতেই জমাট অন্ধকারে আর কিছুই দেখা গেল না।
গবাক্ষবাবু বুক ঠুকে আজ শস্তায় একখানা টর্চ কিনেছেন। তাঁর ঘোরতর সন্দেহ, যে-ছুঁচটা তিনি কুড়িয়ে পেয়েছেন সেটা এলেবেলে জিনিস নয়। তন্ত্রমন্ত্রের কোনও বিশেষ প্রক্রিয়ায় বোধ হয় জিনিসটার দরকার হয়। না হলে তারা তান্ত্রিক তার চোর-চেলাদের ঘরে ঘরে পাঠিয়ে জিনিসটা তল্লাশ করত না। গবাক্ষবাবুর অনুমান, তাঁর ঘরে চোরেরা আবার হানা দিতে পারে। সুতরাং টর্চখানা হাতের কাছে থাকলে সুবিধে হয়।
আজ ভাল করে জানলা দরজা এঁটে তবে শুতে গেলেন গবাক্ষবাবু। তবে জানলা দরজার ওপর বিশেষ ভরসা নেই, কারণ সেগুলো খুবই পলকা। তাই শুয়ে সজাগই থাকলেন তিনি।
রাত একটু গম্ভীর হওয়ার পর তিনি উঠে টর্চ জ্বেলে তোশকের ফুটো দিয়ে হাত ঢুকিয়ে কাঁচের শিশিটা বের করলেন। ছুঁচের রহস্যটা কী তা জানার কৌতূহল হচ্ছে খুব। তেমন গুরুতর জিনিস হলে এটা বেচে কিছু টাকাপয়সাও পাওয়া যেতে পারে।
ছুঁচটা শিশি থেকে বের করার আগে তিনি ঘরের চারপাশটা ভাল করে টর্চ জ্বেলে দেখে নিলেন। সামনের জানলার একটা পাট খুলে টর্চের ফোকাস ফেলে দেখলেন, নরহরির বারান্দায় জ্ঞানপাগল দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘাড় কাত করে ঘুমোচ্ছে। বৃষ্টি এখনও পড়ছে। হাওয়াও দিচ্ছে খুব।
জানলাটা বন্ধ করে টর্চের আলোয় শিশিটা ভাল করে দেখলেন গবাক্ষবাবু। শিশিটা ছয় ইঞ্চির মতো লম্বা হবে। তার ভেতরে বেশ মোটাসোটা একটা ছুঁচ। তবে ছুঁচ হলেও মুখ তেমন ছুঁচলো নয়, আর অন্য প্রান্তে সুতো পরানোর ফুটোও নেই। বেশ চকচক করছে জিনিসটা। মরচে টরচে ধরেনি। শিশিটার একটা দিকে কাঁচেরই একটা ছিপি লাগানো। গবাক্ষবাবু সেটা টানা হ্যাঁচড়া করে দেখলেন, বড্ড শক্ত করে আঁটা রয়েছে। একটু নাড়াচাড়া করে দেখলেন, ছুঁচটা নড়ছে না। জিনিসটা শিশির মধ্যে কিছুতে আটকানো আছে।
ধৈর্যশীল গবাক্ষবাবু ছিপিটা একটা ন্যাকড়া দিয়ে চেপে ধরে প্রাণপণে মোচড় দিতে লাগলেন। আর তাই করতে গিয়ে আচমকা শিশিটা হাত থেকে শানের ওপর ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য! শিশিটা ভাঙল না।
এ কীরকম কাঁচ, কে জানে বাবা! শিশিটা তুলে ফের ছিপিটা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। ভয় হল, শিশির মধ্যে তান্ত্রিকের কোনও ভূতপ্রেত আছে কিনা। আর দু নম্বর, ছুঁচটা মন্ত্রপূত কিনা, যদি ছুঁচটা বেরিয়ে এসে পট করে তান্ত্রিকের বাণ হয়ে যায়, তা হলেই বিপদ।
অনেকক্ষণ গলদঘর্ম হওয়ার পর তিনি রান্নাঘর থেকে লোহার সাঁড়াশিটা এনে ন্যাকড়া জড়িয়ে ছিপিটা চেপে ধরে প্যাঁচ কষতে লাগলেন।
হঠাৎ ফট করে একটা শব্দ হয়ে ছিপিটা খুলে গেল। শব্দটা শুনে গবাক্ষ বুঝলেন, শিশিটা বায়ুশূন্য ছিল। ছিপিটা আলগা হওয়ায় হঠাৎ বাতাস ঢুকে শব্দটা হয়েছে। শিশিটা উপুড় করে ছুঁচটা বের করার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু সেটা ভেতরে আটকেই রইল।
তারপর যে কাণ্ডটা হল তাতে গবাক্ষবাবুহাঁ হয়ে গেলেন। শিশির ছিপিটা খোলার কয়েক সেকেন্ড পর হঠাৎ ভেতরকার ছুঁচটা দপ করে জ্বলে উঠল। প্রথমে একটু লালচে, তারপর নীলবর্ণ হয়ে সমস্ত ঘরটা আলোয় ভরে গেল। এ যে ভৌতিক কাণ্ড তাতে গবাক্ষবাবুর সন্দেহ রইল না। কিন্তু তাঁর গলায় স্বর ফুটল না বলে চেঁচাতে পারলেন না, আর ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে পড়ায় ছুটে পালাতেও পারলেন না। বড় বড় চোখ করে শুধু হাতের শিশিটার দিকে চেয়ে রইলেন।
আশ্চর্যের বিষয়, অত উজ্জ্বল আলো সত্ত্বেও শিশিটা তেমন গরম হল না। আলোটা এতই উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে, ঘরটা দিনের আলোর মতো আলো হয়ে গেল।
হাতে পায়ে সাড় ফিরতে একটু সময় লাগল গবাক্ষবাবুর। তিনি তাড়াতাড়ি শিশির মুখে ছিপিটা এঁটে বসিয়ে দিলেন। ভূতের ভয়ের সঙ্গে তাঁর মাথায় একটা মতলবও খেলা করছিল। সন্ধের পর আর মোমবাতি বা কেরোসিনের পয়সা খরচা করতে হবে না। ভূতের আলো হলেও তো আলোই। সন্ধের পর এই আলোতেই সব কাজকর্ম সেরে ফেলা যাবে।
কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এই জিনিসটি তাঁর নয়। তারা তান্ত্রিক জিনিসটা খুঁজে বের করতে তার চোরছ্যাঁচোড় চেলাচামুণ্ডাদের লাগিয়ে দিয়েছে। সুতরাং জিনিসটাকে রক্ষা করতে হলে বুদ্ধি খাটানো দরকার। ছিপিটা বন্ধ করার পর আলোটা ধীরে ধীরে কমে এল, এবং মিনিট তিনেক পর একদম নিভে গেল।
হাঁফ ছেড়ে শিশিটা ফের তোশকের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিয়ে গবাক্ষবাবু ভাবতে বসলেন। মাথাটা গরম। ভয়ে বুকটা একটু ঢিপঢিপও করছে। প্রথম ভয় তারা তান্ত্রিককে। সে কেমন লোক জানেন না। দ্বিতীয় ভয়, ভৌতিক ছুঁচটাকে। কীরকম ভূত ছুঁচটায় ভর করে তাও তাঁর জানা নেই। আদপে ভূত সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতাই গবাক্ষবাবুর ছিল না এতকাল। তারা তান্ত্রিক আর ভূতেরা মিলে কতটা উপদ্রব করবে তাও আন্দাজ করতে পারছেন
গবাক্ষবাবু। এখন উপায় হল জিনিসটা নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে ভিন গাঁয়ে রেখে আসা। সেখানে মেলা লোকলশকর আছে। চট করে বেহাত হওয়ার ভয় নেই।
হঠাৎ শিরশিরে ঠাণ্ডা একটা বাতাস ঘাড়ে মাথায় কানে এসে লাগতেই গবাক্ষবাবু শিউরে উঠলেন। পেছনে তাকিয়ে দেখলেন, জানলাটা দুহাট করে খোলা। কী করে খুলল তা বুঝতে না পেরে গবাক্ষ হাঁ করে চেয়ে রইলেন। একটু শব্দও হয়নি তো! ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। কাঁপতে কাঁপতে টর্চটা তুলে
জানলায় ফেললেন। কেউ নেই।
টর্চটা নিভিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় গবাক্ষবাবু শক্ত হয়ে বসে রইলেন। জানলায় উঁকি দিয়ে কেউ কাণ্ডটা দেখে ফেলল নাকি? সে কি তারা তান্ত্রিকের চর! না কি ছুঁচের ভূত!
অন্ধকার জানলাটার দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইলেন গবাক্ষবাবু। জানলা থেকে চোখ সরাতে চেষ্টা করেও পারলেন না।
আচমকাই অন্ধকার জানলায় একটা আবছা মূর্তি দেখা দিল।
গবাক্ষবাবুর হাত-পা অবশ। তবু প্রাণপণে টর্চটা তুলে আলো ফেলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শস্তার টৰ্চবাতির সুইচটা ঠিক এই সময়েই গণ্ডগোল করল। টর্চ জ্বলল না।
গবাক্ষবাবু গর্জন করার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু গলা চিরে ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ বেরোল। প্রায় ফিসফিস করেই তিনি বললেন, “কে? কে ওখানে?”
জানলার অন্ধকারে হঠাৎ এক জোড়া চোখ বাঘের মতো দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল।
গবাক্ষবাবু প্রাণপণে “রাম রাম রাম রাম” জপ করতে লাগলেন। বুক ঢিপঢিপ করতে করতে দামামার শব্দ হতে লাগল বুকে। গলা শুকিয়ে কাঠ। গবাক্ষবাবুর মনে হল এবার মূর্ছা গেলে ভয়ের হাত থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু মূৰ্ছা যাওয়ার চেষ্টা করে দেখলেন, মুছাটাও কেমন যেন আসতে চাইছে না।
জানলার গা ঘেঁষে বাইরে একটা করবী ফুলের গাছ আর কামিনী ফুলের ঝোঁপ। ডালপালা আর ঝোঁপঝাড়ে হঠাৎ একটা আলোড়ন উঠল। ক্ষীণ হলেও একজোড়া ভারী পায়ের শব্দ দূরে চলে যেতে শুনলেন গবাক্ষবাবু।
হাঁফ ছেড়ে গবাক্ষবাবু বলে উঠলেন, “গেছে!”
একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও বলে উঠল, “গেছে!” গবাক্ষবাবু ফের শোয়ার তোড়জোড় করতে করতে হঠাৎ থমকালেন। প্রতিধ্বনি তো হওয়ার কথা নয়?
গবাক্ষবাবু পরখ করার জন্য ফের বললেন, “গেছে তা হলে!”
সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ একটা গলা বলে উঠল, “আজ্ঞে, গেছে। জোর বেঁচে গেছেন কর্তা।”
গবাক্ষবাবু শুতে যাওয়ার ভঙ্গি থেকে পট করে সোজা হয়ে বললেন, “কে? কে রে?”
জানলার বাইরে থেকে ক্ষীণ সরু গলায় কে বলল, “এই আমি।”
“আমিটা কে?”
“একজন লোক।”
গবাক্ষবাবু বুঝলেন অশরীরী নয়, মানুষই বটে, সাহস পেয়ে বললেন, “লোক মানে? কেমন লোক?”
“আজ্ঞে ভালও বলতে পারেন, মন্দও বলতে পারেন। ভাল মন্দ মিশিয়ে আর কী!”
“কোনদিকের পাল্লা ভারী? ভাল দিকে না মন্দের দিকে?”
“তা এই মন্দের দিকেই বোধ হয় একটু ভারী।”
“চোর নাকি তুই?”
“আহা, প্রথম আলাপেই হুট করে চোরছ্যাঁচোড় বলাটা কি উচিত হচ্ছে মশাই? ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে তারপর হাতের কাজ দেখে না হয় বলবেন।”
“অ। প্রেস্টিজে লাগল বুঝি?”
“আজ্ঞে, পেটের দায়ে দু-একটা অপকর্ম করি বটে, কিন্তু গায়ে তো এখনও মানুষের চামড়াখানা আছে। সত্যি কিনা বলুন।”
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গবাক্ষ বললেন, “তা বটে।”
“তা টর্চটা নতুন কিনলেন বুঝি?”
টর্চটা সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করে ধরে গবাক্ষ বললেন, “কেন, টর্চের কথা উঠছে কেন?”
“না, জিজ্ঞেস করছিলাম, কত দিয়ে কিনলেন। আজকাল টর্চবাতির যা দাম হয়েছে মশাই, তা আর কহতব্য নয়।”
গবাক্ষ সতর্ক হয়ে বললেন, “দামি জিনিস নয় রে বাপু, কেলোর দোকান থেকে শস্তায় কেনা।”
“তাই বলুন, তবে কিনা টর্চবাতির মতিগতির কোনও ঠিক নেই। আমারও একখানা ছিল বটে, কিন্তু কম্মের নয়। যখন ইচ্ছে হল জ্বলল, যখন ইচ্ছে না হল মুখোনা কালো করে রইল। বড্ড নেমকহারাম জিনিস মশাই। অত ভেজাল দেখে আমার বড় সম্বন্ধীকে টর্চখানা দিয়ে দিলুম। এখন ঝাড়া হাত-পা। অন্ধকারেই চোখ বেশ সাবুদ হয়ে গেছে।”
“তা টর্চ নিয়ে এত কথা উঠছে কেন জানতে পারি?”
“আজ্ঞে, সেই কথাটাই বলছি। এই পথ ধরেই একটা বাণিজ্য করতে বেরিয়েছিলুম। দিনটাও ভাল। বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকার রাত, ঘরে ঘরে মানুষজন দিব্যি মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছ। বড্ড ভাল দিন ছিল আজ। তা হঠাৎ দেখলুম আপনার ঘরে এত রাতেও দিব্যি ফটফট করছে আলো। দেখে ভাবলুম, গবাক্ষকর্তা কি বিজলি বাতি জ্বালালেন নাকি ঘরে, না কি হ্যাজাক লণ্ঠন। উঁকি মেরে দেখতে এসে দেখি, আপনি একখানা টর্চবাতি নিয়ে বসে আছেন। ভাবলুম, বাঃ, টর্চবাতির এলেম তো কম নয়? আর তারপরেই কাণ্ডখানা হল।”
“কী কাণ্ড?”
“হুড়মুড়িয়ে তিনি এসে হাজির।”
“তিনিটা কে?”
“আজ্ঞে, তা বলি কী করে? শুধু জানি দশাসই চেহারা। এসে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরপানে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। আমি একটু গা-ঢাকা দিয়ে পেছনেই ছিলুম। দেখলুম ভয়ে আপনার প্রাণ ছাড়ার উপক্রম। আর তখন আপনার নেমকহারাম টর্চবাতিটাও কেমন বেইমানি করল বলুন। জ্বলল না, জ্বললে তেনাকে দেখতে পেতেন।”
“তিনিটা কে জানো?”
“আজ্ঞে না। কস্মিনকালেও দেখিনি।”
“ইনি তারা তান্ত্রিক নন তো?”
“তারা তান্ত্রিক? মানে সেই জটেশ্বরের জঙ্গলের বামাঠাকুরের কথা বলছেন নাকি?”
“হ্যাঁ, হ্যাঁ। তিনি নন তো৷”
“আজ্ঞে, এই পাপচোখে তো তাঁর দর্শন হয়নি এখনও। দিন চারেক গিয়ে ধরনা দিয়ে পড়ে ছিলাম। তা বাবাঠাকুর নাকি সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে সারাক্ষণ দুনিয়া চষে বেড়ান। তাই তাঁকে চোখের দেখাটা হয়ে ওঠেনি। তবে তিনি কি আর ওই শস্তার টর্চবাতির জন্য রাতবিরেতে পঞ্চমুণ্ডির আসন ছেড়ে উঠে আসবেন?”
“তবে লোকটা কে?”
“বলা কঠিন মশাই। নবাবগঞ্জে নতুন নতুন সব জিনিস আসছে। ভয়ের কথাই হল।”
“এখন বলল তো তুমি কে?”
“শুনে কী করবেন? পুলিশে খবর দেবেন নাকি? সে গুড়ে বালি। আমাদেরও যে শ্রীকৃষ্ণের মতো একশো আটটা করে নাম।”
“আহা, পুলিশের কথা উঠছে কেন? নবাবগঞ্জের পুলিশদের আমি ভাল করেই চিনি। চোর ডাকাতের কথা শুনলে তারা সবার আগে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় গিয়ে লুকোয়।”
“যে আজ্ঞে। তারা বুদ্ধিমান। আমার নাম হল গদাই দাস।”
“বাঃ, বেশ নাম।”
ভারী লজ্জার গলায় গদাই বলে, “কী যে বলেন। গদাই আবার একটা নাম হল! তবে কিনা পিতৃদত্ত নাম। তার মর্যাদাই আলাদা। এই পঞ্চার কথাই ধরুন। এমন আহাম্মক দুটি দেখিনি! পিতৃদত্ত নামটা অপছন্দ হওয়ায় কাছারিতে গিয়ে নাম পালটে কী যেন একটা হয়ে এল, তাও আবার পয়সা খরচ করে।”
“হ্যাঁ, জানি। প্রিয়ংবদ।”
“তাই হবে। কোনও মানে হয়? তা আপনি তাকে চেনেন নাকি?”
“তল্লাটের সব চোরকেই চিনি। শুধু গদাই দাসকেই চিনতুম
।”
“আজ্ঞে, নতুন আসা। জামালগঞ্জ গাঁয়ে ছিলুম, তা সেখানে তেমন সুবিধে হচ্ছিল না। ওইটুকু একটা গাঁয়ে আটচল্লিশজন চোর, ভাবতে পারেন? চোরে চোরে একেবারে ধূল পরিমাণ। সরু চোর, মোটা চোর, ট্যারা চোর, কানা চোর, ঢ্যাঙা চোর, বেঁটে চোর, কালো চোর, ধলা চোর, বাঁকা চোর, সিধে চোর–চোরের চিড়িয়াখানা যেন। রাতে পথে বেরোলে চোরে চোরে ধাক্কা লাগত মশাই। শেষে চোরের বাড়িতেও চুরি করতে চোর ঢুকতে শুরু করল। তখন আমার মনে হল, এ তো অধর্ম হয়ে যাচ্ছে। চোরের বাড়িতে চুরি করা তো মহাপাপ।”
“তাই এই গাঁয়ে এসে থানা গাড়লে বুঝি?”
“যে আজ্ঞে। আশীর্বাদ করবেন যেন কাজেকর্মে একটু সুবিধে করে উঠতে পারি। আপনাদের শ্রীচরণই ভরসা।”
“তা তো বটেই। তবে আমাদের শ্রীচরণের চেয়ে নিজের দু’খানা শ্রীহস্তের ওপরেই ভরসা করাই ভাল।”
“কী যে বলেন গবাক্ষকর্তা। আমরা হলাম আপনাদের পায়ের নীচে পড়ে থাকা সব মানুষ। তা ইয়ে টর্চবাতিটা কি আর একবার জ্বালাবেন নাকি কর্তা?”
গবাক্ষ আবাক হয়ে বললেন, “কেন হে, টর্চ জ্বালব কেন?”
“সত্যি কথা বলতে কী গবাক্ষকর্তা, জীবনে অনেক টর্চবাতি দেখেছি বটে, কিন্তু এমন তেজালো আলো আর কোনও টর্চ বাতিতে দেখিনি। তাই আর একবার দেখে চোখটা সার্থক করতে চাই। কেলোর দোকানে পাওয়া যায় বলছেন? আজ রাতেই দোকানটায় হানা দিতে হবে।”
গবাক্ষ প্রমাদ গুনলেন। গদাই দাস যে আলো দেখেছে তা টর্চবাতির আলো নয়। কিন্তু সেটা তো আর কবুল করা যায় না। তাই বললেন, “না হে গদাই, টর্চটা বোধ হয় গেছে। জ্বলতে চাইছে না। টর্চবাতি সম্পর্কে তুমি যা বলেছ সেটা অতি খাঁটি কথা। কখন যে জ্বলবে, কখন যে জ্বলবে না তার কোনও ঠিক নেই। বরং আর একদিন এসো, দেখাব।”
অমায়িক গদাই দাস বলল, “যে আজ্ঞে। তা হলে ওই কথাই রইল।”
গদাই দাস বিদায় নেওয়ার পর গবাক্ষ জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। রাতে আর ঘুম হবে না। মাথাটা গরম।
.
টুং করে একটা মৃদু ঘণ্টার শব্দ হল। মাঝরাত্তিরে সজনীবাবু বিছানা ছেড়ে উঠলেন। দেওয়াল ঘড়িতে রাত দুটো বাজে। ল্যাম্পের আলোটা উসকে দিয়ে তিনি চারদিকটা দেখলেন। না, সব ঠিকঠাক আছে। বেশি ধনসম্পদ থাকার এই এক অসুবিধে। সবসময়ে একটা ভয় থাকে। নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায় না। সজনীবাবুর আজকাল ঘুম বিশেষ হতে চায় না সেই কারণেই। তার ওপর নতুন একটা দুশ্চিন্তা যোগ হয়েছে সন্ধে থেকে। জ্ঞানপাগলা নামে উটকো লোকটা কোত্থেকে এসে জুটল? ভেবে ভেবে মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে।
অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। তাঁর বাড়ি দুর্গের মতোই নিরাপদ। ঘরের দরজা জানলা আঁটা, বাইরে পাইক বরকন্দাজ পাহারায় আছে, আছে পোষা কুকুর। তা সত্ত্বেও নিশ্চিন্তে থাকাটা তাঁর আর হয়ে উঠল না।
ধনসম্পদ তো তাঁর শুধু একটা ঘরেই নয়, বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন কৌশলে সব লুকিয়ে রাখা আছে। সব ঠিকঠাক আছে কি না তা পরখ করে দেখার সবচেয়ে ভাল সময় হল মধ্যরাত।
ল্যাম্পটা উসকে নিয়ে তার আলোয় নিজের ঘরের সিন্দুকটা আগে খুললেন সজনীবাবু। হিরের বাক্সে গোটা পঞ্চাশেক ছোট বড় হিরে, মুক্তোর বাক্সে শতখানেক মুক্তো, মোহরের বাক্সে শ’ পাঁচেক মোহর ইত্যাদি সব ঠিকঠাকই আছে। আলমারি খুলে সোনা আর রুসোর অন্তত শ’দুয়েক থালা বাসন দেখে নিলেন।
ল্যাম্প রেখে দিয়ে একটা বড় টর্চ হাতে বেরিয়ে হলঘরে পা দিলেন। হলঘরের দেওয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং। অনেক পুরনো সব ছবি, সাহেবদের আঁকা। এসব ছবিরও লাখো লাখো টাকা দাম। ছবিগুলোর পেছনে গুপ্ত সব কুলুঙ্গিতে কোনওটাতে গয়না, কোনওটাতে পুরনো পুঁথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, কোনওটাতে পুরনো আমলের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা। ছবিগুলো একটু করে সরিয়ে দেখে নিলেন সজনীবাবু। না, সব কুলুঙ্গিই চাবি দেওয়া রয়েছে।
হল পেরিয়ে পেছন দিকের নির্জন ঠাকুরদালানে এসে পড়লেন সজনীবাবু। নিঃশব্দে তালা খুলে দোতলার মস্ত ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। নিরেট রুপোর মস্ত সিংহাসনে সোনায় বাঁধানো হামা দেওয়া গোপালের মূর্তি। সূক্ষ্ম নেটের মশারিতে ঢাকা।
তিনি দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো চামরটা নামিয়ে আনলেন। চামরটার হাতল রুপোয় বাঁধানো। সজনীবাবু হাতলটা ঘোরাতে লাগলেন। হাতলটার প্যাঁচ খুলে যেতে লাগল।
হাতলটা খুলে ফাঁপা অভ্যন্তরে টর্চের আলো ফেললেন সজনীবাবু। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ফাঁপা হাতলের ভেতরটা আজও ফাঁকা। হাতলটা আবার জুড়ে দিয়ে চামরটা যথাস্থানে রেখে সজনীবাবু বেরিয়ে এলেন। পেছনের দরদালান পার হয়ে একটা অব্যবহৃত সরু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সিঁড়ির তলায় পেছনের একটা ছোট্ট দরজার হুড়কো খুললেন, বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।
সজনীবাবু চাপা গলায় বললেন, “কী খবর রে লক্ষ্মীকান্ত?”
“আজ্ঞে, মনে হচ্ছে সন্ধান পেয়েছি।” সজনীবাবু সিধে হয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, “পেয়েছিস? কোথায় সেটা? কার কাছে?”
“আজ্ঞে, গবাক্ষবাবুর কাছে।”
“কী করে বুঝলি?
“আপনার কথামতো বাড়ি বাড়ি আঁতিপাঁতি করে রোজ খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ মাঝরাতে অলিন্দবাবুর বাড়িতে ঢোকার জন্য জানলার শিক খুলছিলাম, তখন হঠাৎ দেখি গবাক্ষবাবুর বাড়ি থেকে একটা তেজালো আলো বেরোচ্ছে।”
“হ্যাজাক বা টর্চের আলো নয় তো!”
“আজ্ঞে না। ওসব আলো আমরা ভালই চিনি। এ অন্যরকম আলো। খুব তেজি আলো, আর খুব মিঠে।”
সজনীবাবু সোল্লাসে বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরকমই আলো হওয়ার কথা। তারপর কী করলি?”
“তাড়াতাড়ি গবাক্ষবাবুর গবাক্ষে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু আলো ততক্ষণে নিভে গেছে।”
“জিনিসটা হাতিয়ে আনতে পারলি না? একখানা রদ্দা মারলেই তো গবাক্ষর হয়ে যেত।”
“আজ্ঞে, সুবিধে হল না। কারণ সেই সময়ে একটা সা জোয়ান লোক কোথা থেকে হুড়মুড়িয়ে ছুটে এসে জানলার ওপর হামলে পড়ল।”
“কে লোকটা?”
“কস্মিনকালেও দেখিনি, তবে বিরাট চেহারা। আমি গা-ঢাকা দিয়েছিলাম।”
“চিনতে পারলি না! সে কী রে! কী করল লোকটা?”
“আজ্ঞে, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরপানে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর হুড়মুড়িয়ে চলে গেল।”
“এই রে! তা হলে তো অন্যেরও নজর পড়েছে! আর দেরি করা মোটই উচিত হবে না। তা লোকটা চলে যাওয়ার পর তো তুই ঘরে ঢুকে জিনিসটা কেড়ে আনতে পারতিস।”
“তারও অসুবিধে ছিল। উলটোদিকের নরহরিবাবুর বারান্দায় জ্ঞানপাগলা বসে ছিল যে! লোকে বলে সে নাকি ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর আর খুব জ্ঞানী লোক।”
সজনীবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, “জ্ঞানপাগলা লোকটা কে বল তো! গত সন্ধে থেকে তার কথা শুনছি। লোকটা কোথা থেকে এসে উদয় হল?”
“তা জানি না।”
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সজনীবাবু বললেন, “তা তাকেও তো একটা রদ্দা কষাতে পারতিস!”
“আজ্ঞে, সেটাই মতলব ছিল। ভাবলাম, গবাক্ষবাবুর ঘরে ঢোকার আগে পাগলাটার ব্যবস্থা করে নিই। গবাক্ষবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগডুম বাগড়ম কথা কয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নিলাম। মনে হল, গবাক্ষবাবু রাতে সজাগ থাকবেন। আর সজাগ গেরস্তর ঘরে ঢুকতে গেলে একটু সাড়াশব্দ হবেই। পাগলটা ঘুমোচ্ছিল। সোজা গিয়ে তার মাথায় একটা ঘেঁটে লাঠি জোরে বসিয়ে দিলাম।”
“বাঃ বাঃ, পাগলটা চোখ ওলটাল বুঝি?”
“আজ্ঞে না। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। লাঠি বসাতেই পাগল বাঁ হাতে কোন কায়দায় কে জানে– লাঠিটা কপ করে ধরে ফেলল, তারপর ডান হাতে একখানা যা ঘুসি ঝাড়ল, বাপের জন্মে ওরকম ঘুসি খাইনি।”
“বলিস কী!”
“টর্চবাতিটা আমার মুখে ফেলুন। দেখছেন তো বাঁ গালের হনুটা কেমন লাল হয়ে ফুলে আছে। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল।”
“তারপর?”
“ঘুসি খেয়ে ছিটকে বারান্দা থেকে জলকাদায় পড়ে গেলাম। অন্য কেউ হলে মুছা যেত। আমি লক্ষ্মীকান্ত–এককালে বিস্তর পুলিশের গুতো খেয়েছি বলে হাড় পেকে গেছে। কোনওরকমে উঠে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।”
“সর্বনাশ! তা হলে পাগলটাও কি টের পেল?”
“আপনাকে একটা কথা বলি কর্তা। আপনি আমাকে ছিচকে চুরি ছাড়িয়ে আপনার কাজে বহাল করার পর থেকে এ-তল্লাটের চোরেরা আমায় এড়িয়ে চলে। দোকানদার বলেই তারা আমাকে জানে। তাতেই তারা নাক সিঁটকোয়। যদি জানত যে দোকানটা আসলে একটা মুখোশ, তলায় তলায় আমি আপনার হয়ে চোরের ওপর বাটপাড়ি করি তা হলে তারা আমার ছায়াও মাড়াত না।”
“আহা, ওসব কথা উঠছে কেন? তোকে কি আমি খারাপ রেখেছি?”
“আজ্ঞে না, ভালই রেখেছেন। মাস গেলে বাঁধা মাইনে পাই। দোকান থেকেও আয় হয়। কিন্তু বাজারে আমার মানমর্যাদা নেই। সে যাকগে, ওসব দুঃখের কথা বলে কী হবে! আসল কথা হল চোরেরা আমাকে আজকাল আর কোনও গুপ্ত খবরটবর দেয় না। তবু কানাঘুষো শুনছি, ওই বিটকেল ছুঁচটা নাকি তারা তান্ত্রিকও খুঁজছে।”
সজনীবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, “অ্যাঁ।”
“আজ্ঞে হ্যাঁ। তার চেলাচামুণ্ডারা সব বাড়ি বাড়ি ঢুকে ছুঁচ খুঁজে বেড়াচ্ছে।”
“সর্বনাশ! এ তো একেবারে ঢোলশোহরত হয়ে গেছে দেখছি। ছুঁচটা বেহাত হওয়ার আগেই যে ওটা আমার হেফাজতে আসা দরকার।”
“কর্তা, অপরাধ যদি না নেন তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।”
“কী কথা?”
“এই বিটকেল ভুতুড়ে ছুঁচটা আসলে কার? কোথা থেকে এল?”
সজনীবাবু গর্জন করে বলে উঠলেন, “আমার ছুঁচ, আর কার? একজন সাধু আমাকে দিয়েছিল। বলেছিল, যত্ন করে রাখতে। কিছুদিন আগে ওটা চুরি যায়।”
লক্ষ্মীকান্ত একটু করুণ হাসল। “গত দশ বছরের মধ্যে আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও চোর এ বাড়িতে ঢুকেছে বলে শুনিনি। যদি ঢুকতে পারে তা হলে তাকে নিখিল নবাবগঞ্জ দলিত তস্কর সমাজ থেকে সোনার মেডেল দেওয়া হবে।”
“অ্যাঁ! এতদুর আস্পর্ধা তাদের!”
“কোনও চোর আপনার বাড়িতে ঢুকলে সে-খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ত।”
নিজেকে সামলে নিয়ে সজনীবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, “বাইরের চোর নাও হতে পারে। বাড়ির ভেতরকার কারও কাজ হওয়া অসম্ভব নয়। বাড়ি ভর্তি কাজের লোক, পাইক-বরকন্দাজ। সর্ষের মধ্যেই তো ভূত থাকে। কিন্তু জিনিসটা আজ রাতেই উদ্ধার করতে হবে। পারবি? হাজার টাকা বকশিশ। “
করুণ একটু হেসে লক্ষ্মীকান্ত বলল, “পারব কিনা জানি না। তবে শেষ চেষ্টা একটা করে দেখতে পারি।
“দ্যাখ বাবা, দ্যাখ।”
লক্ষ্মীকান্ত বিদায় হলে সজনীবাবু ওপরে উঠে নিজের ঘরে এলেন। লক্ষ্মীকান্ত ভয় খেয়েছে। ভয়-খাওয়া লোককে দিয়ে কার্যোদ্ধারের আশা কম। সজনীবাবু তাড়াতাড়ি বেরোনোর পোশাক পরে নিলেন। বাইরে বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। তবে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে বেশ। একটা বাঁদুরে টুপি পরে হাতে মোটা বেতের লাঠিগাছটা নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সদর দরজা দিয়ে বেরোলে দরোয়ান দেখতে পারে। রাত মোটে দুটো বেজে কুড়ি মিনিট, এসময়ে তো আর কেউ প্রাতভ্রমণে বেরোয় না। সুতরাং দরোয়ানরা যাতে কিছু সন্দেহ না করে সেইজন্য পেছনের দরজা দিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে এলেন। টর্চ জ্বেলে রাস্তাটা দেখে নিলেন একটু। জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। ভাঙাচোরা কাঁচা রাস্তা, দু’ধারে বড় বড় গাছ আর ঝোঁপঝাড়। সজনীবাবু খুশিই হলেন। যে কাজে যাচ্ছেন তার বেশি সাক্ষীসাবুদ না থাকাই ভাল।
বেশ জোরকদমেই এগোচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ভারী বিনয়ী গলায় বলে উঠল, “সজনীবাবু যে! কী সৌভাগ্য! তা প্রাতভ্রমণে বেরোলেন নাকি?”
সজনীবাবু ধাঁ করে ঘুরে টর্চের আলো ফেলে দেখলেন, ধুতি আর জামা পরা, মাথায় গামছা বাঁধা বেঁটেখাটো একটা লোক। মুখে বিগলিত হাসি। হাত দুটো জোড় করে আছে। সজনীবাবু গম্ভীর মুখে শুধু বললেন, “হুম।”
“তা ইয়ে সজনীবাবু, বলছিলাম কী, সুয্যিঠাকুর কি আজ একটু তাড়াতাড়িই উঠে পড়বেন বলে আপনার মনে হয়?”
“কেন বলো তো?”
“এই ভাবছিলাম যে, সজনীবাবু যখন প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন তখন সুয্যিঠাকুরও আজ বুঝি একটু পা চালিয়েই এসে পড়বেন।”
“তাতে কি তোমার সুবিধে হয়?”
“তা একটু হয় বটে। গোরুটা সন্ধেবেলা ঘরে ফেরেনি, সেই কখন থেকে বেটিকে গোরুখোঁজা করে খুঁজছি। অন্ধকারে কোথায় সেঁধিয়ে বসে আছে কে জানে! আলোটা ফুটলে একটু সুবিধেই হবে।”
“তা বটে।” বলে সজনীবাবু হাঁটতে লাগলেন।
লোকটা সঙ্গ ছাড়ল না। পিছু পিছু আসতে আসতে বলল, “তবে কিনা সুয্যিঠাকুরের তো শুধু এই নবাবগঞ্জ নিয়েই কারবার নয়। আরও পাঁচটা গাঁ গঞ্জও তো আছে। সব জায়গায় আলো ফেলতে গেলে পাল্লাটা তো নেহাত কম দাঁড়াবে না। কী বলেন?”
“তা বটে। তা হলে তুমি এবার তোমার গোরু খুঁজতে শুরু করো। দিনকাল ভাল নয়, গোরুচোরেরও খুব উপদ্রব হয়েছে। তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করে ফেলল। আমি বরং এগোই।”
“যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে।”
কিন্তু দশ পা যেতে-না-যেতেই প্যান্ট শার্ট পরা একটা ফচকে চেহারার ছেলের সামনা-সামনি পড়ে গেল। জ একটু কুঁচকে বলল, “মিস্টার চৌধুরী যে! এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! মর্নিং ওয়াকে বেরোলেন নাকি? ভেরি গুড, ভেরি গুড। কিন্তু এই কোল্ড ওয়েদারে আবার সর্দি ক্যাচ করে ফেলবেন না তো? ওয়াকিং স্টিকের বদলে একটা আমব্রেলা নিয়ে বেরোলেই তো পারতেন।”
সজনীবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, “হুম। তা তুমি এত রাতে পথে বেরিয়েছ কেন হে ছোঁকরা?”
“আর বলবেন না। লাইফটাই ডিসগাস্টিং। ঘরে ক্যান্টাং কারাস ওয়াইফ থাকলে যা হয়। ডিফারেন্স অব ওপিনিয়ন থেকে একটা শো-ডাউন হয়ে গেল। তাই মাথাটা ঠাণ্ডা করতে একটু ওপেনিং-এ বেরিয়েছি।”
“বেশ, বেশ, মাথাটা ভাল করে ঠাণ্ডা করো। আমি এগোই।”
“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। বাই মিস্টার চৌধুরী।”
সজনীবাবু তৃতীয় বাধাটা পেলেন আরও বিশ গজ হাঁটার পর। একজন আধবুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিল। তাঁকে দেখেই বিড়িটা ফেলে দিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, “কে যায় রে! আরে এ যে গরিবের মা-বাপ সজনীরাজা। তাই বলি, আমরা কি যার-তার রাজ্যে বাস করি রে রেমোর মা? এ হল সজনীরাজার রাজত্ব। চারদিকে খেয়াল রাখেন। চারদিকে কান, চারদিকে চোখ, চার হাতে আগলান আমাদের, চার পায়েনা না এটা ভুল হয়ে যাচ্ছে।”
সজনীবাবু কটমট করে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, “থাক থাক, আর তেল দিতে হবে না।”
লোকটা অবাক হয়ে বলে, “বলেন কী বাবা। তেল না দিলে কি মেশিন চলে? তাও তেল আর দিতে পারি কই? অত পাইক বরকন্দাজ পেরিয়ে দেউড়িতে ঢুকতে পারলে তো! আর ঢুকলেই কি সুবিধে হবে? ভেতরে মোড়ল মুরুব্বিরা যে রাজাবাবাকে একেবারে ভেঁকে ধরে বসে থাকে। যেন পাকা কাঁঠালে ভোমা মাছি। তা প্রাতঃকৃত্যে বেরিয়েছেন নাকি বাবা?”
“না হে বাপু, প্রাতর্ভ্রমণে।”
“ওই একই হল। যার নাম চালভাজা তারই নাম মুড়ি।”
লোকটার দিকে আর ভ্রুক্ষেপ না করে সজনীবাবু তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন।
“রামজিকি কৃপা। আরে ই তো সোজোনীবাবু আছে। রাম রাম সোজোনীবাবু, শরীর দেমাক সব তন্দুরস্ত আছে তো?”
এ-পর্যন্ত যেক’টা লোকের দেখা পেয়েছেন তাদের একজনকেও সজনীবাবু চেনেন না। নবাবগঞ্জ ছোট জায়গা, এখানে সবাইকে সবাই চেনে। সজনীবাবুও চেনেন। কিন্তু এ লোকগুলোকে চেনা ঠেকছে
কেন, তা ভেবে পাচ্ছেন না। আসলে যে মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তার মাথায় বিড়ের মতো একটা পাগড়ি গোছের, গায়ে গলাবন্ধ কোট, পরনে ধুতি। খুবই বশংবদের মতো হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে।
সজনীবাবু লোকটিকে কাটানোর জন্য বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ভাল।”
“রামজিকি কৃপা, লেকিন হুজুর, কলিযুগ কি খতম হয়ে গেলো নাকি?”
‘কেন বলুন তো?”
“আমি তো ভাবছিলাম কি, কলিযুগ খতম হোতে আউর ভি দু-চার বরষ লাগবে। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কলিযুগ সায়দ খতম হোয়েই গিয়েছে।”
সজনীবাবু ক্রমশ চটছেন। এবার খ্যাঁক করে উঠলেন, “আমার সঙ্গে কলিযুগের সম্পর্ক কী মশাই?”
“আমার বুঢ়া দাদাজি বলত, বুঢ়া দাদাজি সমঝলেন তো? হামার পিতাজি কি পিতাজি, বুঝলেন?”
“বুঝলাম।”
“তো বুঢ়া দাদাজি কহতা থা কি, কলিযুগ যখন খতম হোবে তখন রাত মে দিন হোবে আউর দিন মে রাত। উস লিয়ে বলছিলাম কি সোজোনীবাবু, এখুন কি দিন না রাত। আপনি তো সবেরকা ঘুমনা শুরু কর দিয়া। তাই ভাবলাম, সোজোনীবাবু পণ্ডিত লোক আছে, কলিযুগ খতম হলে উনি ঠিক টের পাবেন।”
সজনীবাবু লোকটার দিকে কটমট করে একবার চেয়ে বললেন, “হুম। যত্তসব।”
বলে আবার জোর কদমে হাঁটতে লাগলেন। না, আর কোনও উদ্ভট লোকের উদয় হল না। তবে মোড়ের কাছ বরাবর যখন। এসেছেন তখন পাশের ঝোঁপের আড়াল থেকে কে যেন মৃদুস্বরে চাপা গলায় ডাকল, “একটা কথা ছিল কর্তা।”
সজনীবাবু বিরক্তিকর সঙ্গে বললেন, “আমার সময় নেই।”
“আমি ওদের দলের লোক নই।”
“তুমি কে?”
একজন মাঝারি মাপের মানুষ ঝোঁপের আড়াল থেকে কুঁজো হয়ে বেরিয়ে এল। গায়ে গেঞ্জি, পরনে হেঁটো ধুতি, চোখে-মুখে একটু ভয়-ভয় ভাব। হাতজোড় করে বলল, “আজ্ঞে, আমি শ্রীদাম।”
এই প্রথম একটা লোককে চেনা ঠেকল সজনীবাবুর। এ লোকটা তাঁর বাগান পরিষ্কার করেছিল গত বছর। বিরক্তির সঙ্গে সজনীবাবু বললেন, “তুই আবার কী চাস? একটা কাজে যাচ্ছি, পদে পদে বাধা পড়ছে।”
“আজ্ঞে, কর্তা, আমাদের ওপর বড় অবিচার হচ্ছে।”
“অবিচার। কীরকম অবিচার?”
“আমরা ভুমিপুত্তুর কিনা বলুন।”
“ভূমিপুত্তর। সে আবার কী রে?”
“আজ্ঞে, এটাই আমাদের জন্মভূমি বটে তো! নবাবগঞ্জেই তো জন্মে ইস্তক এত বড়টি হলাম। তাকেই তো বলে ভূমিপুত্তুর।”
“ভূমিপুত্র নাকি। হ্যাঁ, কথাটা শুনেছি বটে। সন অব দ্য সয়েল।”
“আজ্ঞে, ইংরিজিতে তাই বলে বটে। সং অব্দি সয় লো। তা এই ভূমিপুত্তুরেরও উপায় নেই?”
“তা থাকবে না কেন?”
“আজ্ঞে, সেইটেই তো সমস্যা দাঁড়াচ্ছে। সারাদিন খেটেখুটে যা জোটে তাতে পেট চলে না। তাই রাতের দিকে দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার করতে বেরোতে হয়। সত্যি কথাটা কবুল করলাম বলে অপরাধ নেবেন না কর্তা।”
“হুম। তা সমস্যাটা কোথায়?”
“কিন্তু পয়সা রোজগারের কি জো আছে? কোথা থেকে উটকো সব লোক এসে নবাবগঞ্জ ভরে ফেলল। রাতবিরেতে পথেঘাটে যত্রযত্র তাঁরা দাঁত বের করে দেখা দিচ্ছে।”
“বটে!”
“পরশুদিন হরিপদ সরখেলের বুড়ি পিসির সোনার হারখানা হাতাব বলে খিড়কির দরজাটা সবে আলগা করেছি, অমনই এক ছোঁকরা এসে হাজির। বলে কী, এঃ হেঃ, দরজা কি ওরকম আনাড়ির মতো খুলতে হয়? দেখি তোমার যন্ত্রপাতি। ইস, এইসব মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি নিয়ে তোমরা চুরি করতে বেরোও নাকি? তোমরা খুবই পিছিয়ে আছ হে। এই আধুনিক পৃথিবীতে কত নতুন নতুন যন্ত্র তৈরি হয়েছে। তোমরা কি একটু বিজ্ঞান-টিজ্ঞানও পড়ো
নাকি…বলে সে কী লেকচার। যেন ইস্কুলের ক্লাস নিচ্ছে। চেঁচামেচিতে হরিপদবাবু উঠে, “কে, কে বলে চেঁচাতে পালিয়ে বাঁচি।”
সজনীবাবু হাঁটা বজায় রেখেই বললেন, “ছোঁকরাটা কে?”
“সেই কথাই তো বলছি। ছোঁকরা ভূমিপুত্তুর নয়, উটকো লোক। এই যে আপনার সঙ্গে চার-চারজন মশকরা করছিল, কাউকে চিনলেন?”
সজনীবাবু একটু থমকে গিয়ে বললেন, “না। কারা ওরা?”
“ভূমিপুত্তুর নয় কর্তা, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সব। দিনদিন সংখ্যা বাড়ছে।”
সজনীবাবু এবার সত্যিই থমকালেন এবং একটু চমকালেনও। বললেন, “কবে থেকে দেখছিস এদের?”
“দিন দুই-তিন হল। দিনমানেও দেখবেন বাজারে সড়কে এরা ঘোরাফেরা করছে, জটলা পাকাচ্ছে।”
“কোথা থেকে আসছে এরা! কী চায়?”
“ছোঁকরাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম তার বাড়ি কোথায়। বলল তো নয়নগড় না কী যেন। নয়নগড় কোথায় কে জানে বাবা, জন্মে শুনিনি।”
“নয়নগড়? ঠিক শুনেছিস?”
“সেরকমই তো বলল যেন।”
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সজনীবাবু বললেন, “কী চায় এরা?”
“আমাদের ভাত মারতে চায়, আর কী চাইবে?”
সজনীবাবু পেছন ফিরে টর্চ জ্বেলে পথটা দেখলেন। চারজনের কাউকেই দেখা গেল না। সজনীবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, “আমার দরোয়ান আর পাইকদের একটু হুঁশিয়ার করে দিয়ে আয় তো। ব্যাপারটা আমার সুবিধের ঠেকছে না। যা, দুটো টাকা দেব’খন।”
“যে আজ্ঞে। তবে দু’ টাকায় আজকাল এক পো চালও হয় না কর্তা।”
“যা, পাঁচ টাকাই পাবি।”
“তা হলে চালের সঙ্গে ডালটা হল। কিন্তু বাঙালির যে একটু আঁশটে গন্ধও লাগে কর্তামশাই, না হয় পুঁটিমাছের দামটাই দিলেন।”
“অ। তুই তো ঘঘাড়েল দেখছি। আচ্ছা, দশ টাকাই দেব।”
“ওঃ, অনেকটা ওপরে উঠেছেন কর্তা। আর দু’ ধাপ উঠলে ওইসঙ্গে একটু নুন-লঙ্কাও হয়ে যায়।”
“দু’ ধাপ বলতে?”
“দুটো টাকা মাত্র। ও আপনি টেরও পাবেন না। পানের পিক ফেলার মতো, নাকের সিকনি ঝাড়ার মতো ফেলে দিলেই হবে।”
“হাতি কাদায় পড়লে চামচিকেও লাথি মারে দেখছি।”
“আজ্ঞে, চামচিকের তো ওইটাই মওকা কিনা। তাকেও তো হাতযশ দেখাতে হয়।”
“হুম। তুই বুদ্ধি রাখিস বটে! আচ্ছা যা, বারো টাকাই দেব।”
“তা হলে আগাম ফেলুন, দৌড়ে যাই।”
পকেট থেকে টাকা বার করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লোকটার হাতে দিয়ে বললেন, “কিন্তু কাজটা ঠিকমতো করিস, নইলে কালই পাইক পাঠিয়ে ধরে আনব।”
“প্রাণটা তো আপনার কাছেই গচ্ছিত রয়েছে।”
শ্রীদাম দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর সজনীবাবু খুব জোর পায়ে হেঁটে গবাক্ষর বাড়ি অবধি পৌঁছে গেলেন। চারদিক নিঝঝুম। কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই। টর্চ জ্বেলে দেখলেন, নরহরি মাস্টারের বারান্দায় পাগলাটাকে দেখা যাচ্ছে না। টর্চের আলো যতদূর যায়, জনমনিষ্যি নেই।
লক্ষ্মীকান্ত কি কাজ সেরে চলে গেছে? কিন্তু গবাক্ষর ঘরের দরজা বন্ধ। কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে মনেই হচ্ছে না।
তিনি ধীরে ধীরে গবাক্ষবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরজাটা ঠেলে দেখলেন, ভেতর থেকে বন্ধ। জানলাগুলোও খোলা নেই।
দরজায় টোকা দিয়ে তিনি মৃদুস্বরে ডাকলেন, “গবাক্ষবাবু, ও গবাক্ষবাবু।”
কেউ সাড়া দিল না। সজনীবাবু ঘড়ি দেখেলেন। তিনটে বাজে। এই সময়ে যদি কেউ তাঁকে এখানে দেখে ফেলে তবে সন্দেহ করতে পারে। এ তো ঠিক প্রাতভ্রমণের সময় নয়।
কিন্তু কাজটাও জরুরি। জিনিসটা উদ্ধার হল কি না তা হলে জানাটাও ভীষণ দরকার। অগত্যা সজনীবাবু ঘরের জানলাগুলো বাইরে থেকে ঠেলেঠুলে দেখতে লাগলেন।
পুবদিকের জানলাটা ঠেলতেই খুলে গেল। সজনীবাবু ভেতরে টর্চ ফেলে দেখলেন, গবাক্ষ চাঁদরমুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তিনি চাপা স্বরে ‘গবাক্ষবাবু, গবাক্ষবাবু’ বলে দু’বার ডাকলেন।
তারপরই তাঁর হঠাৎ নজরে পড়ল গবাক্ষবাবুর গায়ে যে চাঁদরটা চাপা দেওয়া রয়েছে তাতে যে লাল রঙের ছোপগুলোকে তিনি চাঁদরের নকশা বলে প্রথমে ভেবেছিলেন তা আসলে রক্তের দাগ। জিনিসটা যে রক্তই তা আরও ভাল করে বুঝলেন মেঝেতে আলো ফেলে। সেখানেই খানিকটা রক্ত পড়ে জমাট বেঁধে আছে।
সর্বনাশ! শেষে লক্ষ্মীকান্ত কি গবাক্ষকে খুন করে গেল নাকি? তো ঘটনা অনেকদূর গড়াবে। অকুস্থলে ধরা পড়লে তাঁরও বিপদ। সজনীবাবু টর্চটা নিভিয়ে তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগের জন্য পা বাড়াতেই ফের বিপদ।
পাশের দোতলা বাড়ির ওপরের বারান্দা থেকে গবাক্ষর ভাই অলিন্দ গদগদ স্বরে বলে উঠল, “সজনীখুড়ো যে। তা আজ কি দাদাকে শব্দার্থ জিজ্ঞেস করতে এসেছেন? খুব ভাল। বেশ কঠিন দেখে শব্দ বেছে এনেছেন তো! একেবারে গুতুলের মতো হওয়া চাই কিন্তু। ঠঙাত করে গিয়ে মাথায় লাগবে আর সঙ্গে সঙ্গে কুপোকাত। ওঃ, কাল নরহরিবাবুকে একখানা যা ঝেড়ে গেছেন, যেন আধলা ইট।”
সজনীবাবু পালানোর মতো মূর্খামি করলেন না। অলিন্দ তাঁকে দেখে ফেলেছে, এখন পালালে সন্দেহ করবে। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখাই হল বুদ্ধিমানের মতো লক্ষণ।
তিনি খুব ভালমানুষের মতো বললেন, “তা তুমি আজ তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছ বুঝি।”
“না খুড়ো, মাঝরাতে ওঠার অভ্যাস নেই। কিন্তু নবাবগঞ্জের যা অবস্থার অবনতি হচ্ছে তাতে ঘুমোয় কার সাধ্যি! রাত হতে-না-হতেই চোর-ছ্যাঁচড়ের যেন হাট বসে যায়। এই কেউ দৌড়ে গেল, এই কেউ দরজায় ঠকাত করে শব্দ করল, এই কেউ ফিসফিস করে কারও সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে লাগল। আড়াইটে পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করে এই বারান্দায় এসে একটু হাওয়া খাচ্ছি। আপনারও কি সেই অবস্থা?”
“আর বলল কেন, একটু আগেই চোর ঢুকেছিল বাড়িতে। শুনছি নয়নগড় না কোথা থেকে একদল খুনে গুণ্ডা আর লুঠেরা নবাবগঞ্জে ঢুকে পড়েছে। তা আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। তাই ঘুরে ঘুরে চেনাজানা লোকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।”
“তা হলে তো খুব ভয়ের কথা হল খুড়ো। সেইজন্যেই আজকাল রাতবিরেতে উৎপাত বেড়েছে। তা নয়নগড় জায়গাটা কোথায়?”
“জানি না। লোকমুখে শোনা কথা।”
“সেই জায়গাটা কি বদমাশদের বীজতলা?”
“তাই তো মনে হয়।”
“আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান, জ্ঞানপাগলা যেন কোথাকার রাজপুত্তুর! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো নয়নগড়ের রাজপুত্তুরই তো বলে নিজেকে।”
সজনীবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, “সাবধানে থেকো। কাউকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কে কোন ভেক ধরে আসছে তার ঠিক কী?”
“তাই তো। এ যে বেশ ভয়-ভয় লাগছে। জ্ঞানপাগলা কি ওই দলের সর্দার?”
“বিচিত্র কী?”
“তা হলে কী করা যায় খুড়ো?”
“রাত পোহালেই মহেশ দারোগাকে একটা খবর দিয়ে রাখো। আর তোমরাও তৈরি থাকো। সবাই মিলে জোট বেঁধে লোকগুলোকে না তাড়ালেই নয়।”
সজনীবাবু আর দাঁড়ালেন না। লক্ষ্মীকান্ত যে ভজঘট্ট পাকিয়েছে তার সুরাহার কথা এখনই গিয়ে ভাবতে হবে। সে কার্যোদ্ধার করেছে কিনা সেটাও দেখা দরকার।
বুড়ো শিবতলার কাছে বাঁধানো বটগাছের কাছে এসে থমকালেন সজনীবাবু। কে একটা বসে আছে। টর্চের আলো ফেলে দেখলেন, দাড়ি গোঁফওয়ালা একটা অল্পবয়সী ছেলে, মাথায় রঙিন টুপি। বসে আপনমনে বিড়বিড় করে কী বকছে। এই কি জ্ঞানপাগলা? তাই হবে। পথেঘাটে একে এক-আধবার দেখেছেন, মনে পড়ল।
সজনীবাবু ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গেলেন, তারপর মোলায়েম গলায় বললেন, “নয়নগড়ের রাজপুত্তুর নাকি?”
ছোঁকরা মিটমিট করে ধাঁধালো টর্চের আলোর ভেতর দিয়ে সজনীবাবুর দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ ঝকঝকে দাঁতে একটু হেসে বলল, “শব্দের মানে জিজ্ঞেস করবেন নাকি?”
সজনীবাবু গলাটা নরম রেখেই বললেন, “না। আমি অন্য কথা জিজ্ঞেস করব।”
“কী কথা?”
“তুমি যদি নয়নগড়ের রাজপুত্তুর তবে এই নবাবগঞ্জে বসে কী করছ?”
ছেলেরা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, “খাজনা আদায় করছি।”
“অ। তা ভাল। তা এখানেই কি থাকার ইচ্ছে?”
“না। এ তো বিচ্ছিরি জায়গা। সময় হলেই চলে যাব।”
“এখানে কোনও কাজ কি বাকি আছে?”
“হ্যাঁ। জরুরি কাজ। আমি একটা ছুঁচ খুঁজছি।”
“ছুঁচ! ছুঁচ খুঁজছ। সে আবার কী কথা?”
ছোঁকরা অকপটে সজনীবাবুর দিকে চেয়ে বলল, “ছুঁচটা আরও অনেকেই খুঁজছে। কিন্তু ওটা আমার জিনিস।”
“অ। তা কীরকম ছুঁচ?”
ছোঁকরা হঠাৎ একটা খাস ফেলে বলল, “সে তুমি বুঝবে না। পৃথিবীর লোভী লোকেরা ওটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। কিন্তু ওটা আমার খুব দরকার।”
“একটু ভেঙে বলবে বাপু? ছুঁচটা তোমার কী কাজে লাগে?”
“ছুঁচটা না পেলে আমার নির্বাসন ঘুচবে না। আমি দেশে ফিরে যেতে পারব না।”
সজনীবাবুর বুক কাঁপছিল উত্তেজনায়। তিনি চুপ করে রইলেন। ছোঁকরা ধীর গলায় বলল, “এক ভোররাতে মাজুম আমাকে তাড়া করেছিল।”
“মাজুম! সে আবার কে?”
“তুমি তাকে জানো না। সে ভয়ংকর এক মানুষ। নয়নগড়েরই লোক, কিন্তু সে আমার শত্রু।”
সজনীবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, “নাঃ, ছোঁকরা সত্যিই পাগল।”
জ্ঞান আপনমনে ধীর স্বরে বলল, “মাজুম আমাকে পেছন থেকে বল্লম ছুঁড়ে মেরেছিল। ঘুমপাড়ানি বল্লম। জটেশ্বরের জঙ্গলের ধারে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। তখনই ছুঁচটা বেহাত হয়ে গিয়েছিল।”
“ছুঁচটা কে নিল? মাজুম?”
ছোঁকরা মাথা নাড়ল, “না। তখন দিনের আলো ফুটে উঠছিল। দিনের আলোয় মাজুম চোখে কিছু দেখতে পায় না।”
“সে তখন কী করে?”
“সে দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে। গুহায়, গর্তে, গভীর জঙ্গলে।”
“এ তো আষাঢ়ে গল্প! আমরা তো দিনের আলোতেই দেখি।”
“তোমরা দেখতে পাও, কিন্তু বাদুড় বা প্যাঁচা দেখতে পায় কি?”
“না, তা পায় না।”
“মাজুমের চোখ ওদের মতো।”
“অ। তা হলে ছুঁচটার কী হল?”
“আমি যখন অজ্ঞান হয়ে যাই তখন ওটা আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ে। তখন কেউ ওটা কুড়িয়ে নিয়েছিল।”
সজনীবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এর পরের ঘটনা তিনি খানিকটা জানেন। বললেন, “কে কুড়িয়ে পেয়েছিল জানো?”
“তোমাদের এখানে কিছু লোক আছে যারা অন্যের জিনিস পেলেই নিয়ে নেয়।”
“তা তো নেই। এখানে মেলা চোর। তোমাদের নয়নগড়ে কি চোরছ্যাঁচড় নেই নাকি?”
“না। সেখানে অন্যের জিনিস কেউ নেয় না।”
“তা হলে মাজুম তোমার ছুঁচ চুরি করতে চায় কেন?”
“তার কারণ অন্য। সে আমাকে নয়নগড়ে ফিরে যেতে দিতে চায় না।”
“অ। তা হলে ছুঁচটা ছাড়া তুমি নয়নগড়ে ফিরবে না?”
“ফেরা সম্ভব নয়।”
সজনীবাবু খানিকক্ষণ ভাবলেন। ছোঁকরা যা বলছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। কোথায় যেন লটঘট আছে গল্পটার মধ্যে।
আবার অবিশ্বাসও করতে পারছেন না। সজনীবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ছোঁকরার পাশেই বসলেন। তারপর বললেন, “ছুঁচটা কুড়িয়ে পেয়েছিল দেড়েল কালী নামে একটা লোক। ছুঁচটা থেকে আলো বেরোয় দেখে সে সেটা দামি কোনও জিনিস মনে করে বেচবার জন্য আমার কাছে নিয়ে যায়। সে দাম চেয়েছিল দশ হাজার টাকা। আমি অচেনা জিনিস পাঁচশো টাকার বেশি দিতে চাইনি বলে সে চলে যায়। জিনিসটা সে আরও কয়েকজনের কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করে। শেষে কিছু লোক তাকে মেরেধরে ওটা কেড়ে নেয়। যারা কেড়ে নিয়েছিল তাদের মধ্যেও আবার লড়াই লাগে। তখনই সেটা কারও হেফাজত থেকে খোয়া যায় আর গবাক্ষবাবু সেটা কুড়িয়ে পান। আমি পরে যখন কালীর কাছে জিনিসটা কিনব বলে খবর পাঠাই তখন সে আমাকে ঘটনাটা জানায়। জিনিসটা নবাবগঞ্জে আছে মনে করে আমি লক্ষ্মীকান্ত নামে আমার একজন চেনা চোরকে লাগাই। সে এই কয়েক ঘণ্টা আগে এসে খবর দিল যে, গবাক্ষবাবুর কাছে জিনিসটা আছে।”
সজনীবাবু থামলেন। বাকিটা বলা উচিত হবে না। ছোঁকরা মাথা নেড়ে বলল, “গবাক্ষবাবুর কাছে নেই। আর তোমার লক্ষ্মীকান্তকে মেরে আধমরা করে রেখে গেছে মাজুম। আর গবাক্ষবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে।”
“অ্যাঁ! গবাক্ষবাবুকে কোথায় ধরে নিয়ে গেল? কেনই বা!”
“গবাক্ষবাবুর ঘরে যখন জান-এর আলো দেখতে পেলাম তখনই বুঝলাম গবাক্ষবাবুর বিপদ আছে। মাজুম যেখানেই থাকুক, জান এর আলো সে দেখতে পাবেই।”
“জান! জানটা কী জিনিস?”
“ওই ছুঁচটার নাম। নয়নগড়ের একজন মানুষ ছিলেন জান। তিনিই সময়ের এই কাঁটাটি আবিষ্কার করেন।”
“সময়ের কাঁটা! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না বাপু।”
“বুঝবে না। ওটাই আমার নয়নগড়ে ফেরার চাবি।”
“নয়নগড়টা কোথায় বাপু?”
“এইখানেই। মাইলখানেকের মধ্যেই।”
“তা হলে যেতে বাধা কী?”
“তুমি জানো কাছাকাছি নয়নগড় বলে একটা জায়গা আছে?”
“না তো!”
“কেন জানো না তা জানো? আসলে নয়নগড় এখানেই আছে, কিন্তু ভিন্ন কম্পাঙ্কে।”
“ও বাবা! মাথা যে ঝিমঝিম করছে।”
“পৃথিবীটা খুব বিচিত্র।”
“তুমি কি সত্যিই পাগল?”
“আমার কথা বুঝতে না পারলে লোকে তো পাগলই ভাববে। গালিলেওকে কি তোমরা পাগল ভাবোনি!”
“তা বটে!”
“আমি সোজা করে তোমাকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটা রেডিয়ো বা টিভি সেটে যেমন অনেক চ্যানেল থাকে, পৃথিবীটাও তেমনই। এর এক-এক চ্যানেলে এক-এক জীবন, এক-এক সমাজ। কেউ কারও মতো নয়। আমরা যেনয়নগড়ে থাকি তোমরা তা কখনও খুঁজে পাবে না, অথচ তা এখানেই আছে।”
রুমাল বের করে সজনীবাবু কপালের ঘাম মুছে বললেন, “ও সব শুনে আমার মাথা ঘুরছে। গবাক্ষর কথাটা শেষ করো।”
“গবাক্ষবাবুর ঘরে জানের আলো জ্বলে উঠতেই মাজুম জটেশ্বরের জঙ্গল থেকে ছুটে চলে আসে।”
“অতদুর থেকে?”
“সে ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে দৌড়তে পারে।”
“ও বাবা!”
“সে এসে হাজির হল এবং বুঝতে পারল জান এখানেই আছে। সে তখনই আমার উপস্থিতি টের পায় এবং আমি পালাই। সে কিছুদুর আমাকে তাড়া করে ফিরে আসে। আমিও ফিরি। সে গবাক্ষবাবুর ঘরে ঢোকে। ঢুকে গবাক্ষবাবুকে হিংস্র চাপা গলায় বলে, ছুঁচটা দে। নইলে মেরে ফেলব। গবাক্ষবাবু ভয় পেয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু ঠিক এই সময় লক্ষ্মীকান্ত এসে ঘরে ঢোকে আর ছুঁচটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। পারবে কেন? মাজুম তাকে মেরে শুইয়ে দেয়।”
“সে কি মরে গেছে?”
“না। ওরা চলে যাওয়ার পর আমি ঘরে ঢুকে দেখে এসেছি। লক্ষ্মীকান্তর খাস চলছে।”
“বাঁচা গেল। তারপর?”
“এই সময়ে গবাক্ষবাবু একটা ভুল করেন। অবশ্য না জেনে। তাঁর হাতে একটা টর্চ ছিল। হঠাৎ তিনি টর্চটা জ্বেলে ফেলেন। আর আলোটা গিয়ে সোজা মাজুমের চোখে পড়ে। চোখে আলো পড়লেই মাজুমের সর্বনাশ। সে সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। গবাক্ষবাবু আলো জ্বালাতেই মাজুম খেপে যায়। বরাবরই সে ওইরকম। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। সে প্রথমে অন্ধের মতো টর্চটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সেটা না পেয়ে সে গবাক্ষবাবুকেই জাপটে ধরে।”
“কেন?”
“পথ দেখানোর জন্য। বলেছি না সে চোখে আলো পড়লে অন্ধ হয়ে যায়? তখন কে তাকে পথ দেখাবে?”
“তুমি কিছু করলে না?”
“হ্যাঁ। আমি সেই সুযোগে একবার চেষ্টা করেছিলাম তার কাছ থেকে জান কেড়ে নিতে। কিন্তু মাজুমের গায়ে এমনিতেই সাতটা হাতির মতো জোর। তার ওপর সে তখন খেপে আছে। একটা ঝটকায় আমাকে দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে চলে যায়।”
সজনীবাবু বললেন, “তোমার গল্পটা রূপকথার মতো। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। শোনো বাপু, তোমার জানের ব্যাপারে আমারও কিছু অপরাধ আছে। ওটা আমিও দখল করার চেষ্টা করেছিলাম।”
“অনেকেই করবে। জান এক আশ্চর্য জিনিস। সঠিক প্রয়োগ করলে সে তোমাকে ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পনে নিয়ে যেতে পারে।”
“না বাপু, ওসব নয়। আমি ভেবেছিলুম, একটা আশ্চর্য আলো ঠাকুরঘরে জ্বালিয়ে রাখব।”
“হ্যাঁ, জানের আলো আশ্চর্য আলো। জ্বালিয়ে রাখলে কয়েক হাজার বছর ধরে জ্বলবে।”
“বলো কী।”
“জান একটি ধাতব জিনিস। তোমরা সেই ধাতুর সন্ধান জানো। অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই তা আলো দিতে থাকে।”
‘তুমি সত্যিই নয়নগড়ের রাজপুত্র?”
“হ্যাঁ। আমি যুবরাজ।”
“আর ওই মাজুম?”
“সে আমার শত্রু। সে আমাকে নয়নগড়ে ফিরে যেতে দেবে না। সেইজন্যই সে জান কেড়ে নিয়ে গেছে।”
“তাতে তার কী লাভ?”
“সে তুমি বুঝবে না। নয়নগড়ে রাত আর দিনের মধ্যেই একটা সংঘর্ষের ব্যাপার আছে। মাজুম এবং তার লোকেরা চায় আমার বাবা দিনের বেলা রাজত্ব করুক, কিন্তু সন্ধের পর থেকে ভোর অবধি রাজত্ব করবে ওই মাজুম। এই প্রস্তাব আমার বাবা মানেননি। তাই একটা লড়াই চলছে। আমাকে তোমাদের কম্পাঙ্কে নির্বাসন দিতে পারলে মাজুম নিষ্কণ্টক হবে। আমার অসহায় বুড়ো বাবা তাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হবেন। কারণ মাজুমরা সংখ্যায় বেশি, তাদের গায়ের এবং অস্ত্রের জোরও বেশি। শুধু দিনের বেলা অন্ধ হয়ে যায় বলে তারা খানিকটা দুর্বল।”
“এখানে যারা নয়নগড়ের লোক বলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা কোন দলের?”
“কিছু আমার দলের, কিছু মাজুমের।”
“এখন আমরা কী করব?”
বিষণ্ণ গলায় জ্ঞানপাগলা বলল, “কিছুই করার নেই। বোধ হয় আমি হেরেই গেলাম।”
৫. কার পাল্লায় পড়েছেন
কার পাল্লায় পড়েছেন তা আদপেই বুঝতে পারছেন না গবাক্ষবাবু। লোকটা তাকে বগলে চেপে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে। এরকম ভয়ংকর গায়ের জোর যে কোনও মানুষের থাকতে পারে তা গবাক্ষবাবুর জানা ছিল না। অপরাধটা কী করেছেন তাও ভেবে পাচ্ছেন না। মাঝরাতে লোকটা হঠাৎ ঘরে ঢুকে যখন বলল, ছুঁচটা দে–তখন তার ভয়ংকর রক্তাম্বর পরা বিশাল চেহারা আর জ্বলন্ত চোখ দেখে দ্বিরুক্তি না করে ছুঁচটা দিয়ে দেন গবাক্ষবাবু। একটা আহাম্মক লোক হঠাৎ কোথা থেকে ঘরে ঢুকে লোকটার সঙ্গে হাতাহাতি করতে গেল। চোখের পলকে লোকটাকে মেরে রক্তাক্ত করে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিল জাম্বুবানটা। সেই সময়ে হঠাৎ হাত পা কেঁপে কেঁপে গবাক্ষবাবুর যখন দাঁতকপাটি লাগার অবস্থা তখনই তাঁর হাতের টর্চটা আচমকা জ্বলে ওঠে। জাম্বুবানটা একটা চিৎকার করে চোখ ঢেকে ফেলল। তারপরই হাত বাড়িয়ে তাকে চেপে ধরে হিঁচড়ে বাইরে এনে বলল, “পথ দেখা। জটেশ্বর জঙ্গলে যাওয়ার পথ দেখা।”
গবাক্ষবাবু ভিরমি খেতে-খেতেও দেখলেন জ্ঞানপাগলা ছুটে আসছে। কিন্তু জাম্বুবানটা তাকেও ডল পুতুলের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তীরবেগে এগোতে লাগল আর বলতে লাগল, “পথ দেখা! পথ দেখা!”
চিঁ চিঁ করতে করতে প্রাণভয়ে গবাক্ষবাবু পথ দেখাতেও লাগলেন। কিন্তু ব্যাপারটা কী হচ্ছে, তা বুঝতে পারলেন না। অন্ধকারে তিনিও যে পথ ভাল দেখতে পাচ্ছেন তা নয়। আন্দাজে আন্দাজে বলছেন, “সোজা চলুন। সোজা। মাইলটাক গিয়ে বাঁয়ে কাঁচা রাস্তা। তারপর …”
জটেশ্বরের জঙ্গল অন্তত মাইলতিনেক পথ। কিন্তু জাম্বুবানটা যেন হাওয়ায় ভর করে লহমায় চলে এল। তারপর গাছপালা ভেঙে তছনছ করতে করতে জঙ্গলে ঢুকতে লাগল। লোকটার গায়ে যেমন জোর, তেমনই সহ্যশক্তি। কিন্তু গবাক্ষবাবু তো তা নন। জঙ্গলের ডালপালার খোঁচায় তাঁর শরীর ছড়ে যেতে লাগল, শপাং শপাং করে ডালপালা চাবুকের মতো পড়ছিল সারা গায়ে। গবাক্ষ আধমরা হয়ে গোঁ গোঁ করছিলেন।
একটা সময়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে থামল নোকটা। তাঁকে ছুঁড়ে জলকাদায় ফেলে দিয়ে বলল, “দে, টর্চটা দে।”
টর্চটা যে হাতে আছে তা ভুলেই গিয়েছিলেন গবাক্ষবাবু। কোনওরকমে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “এই যে! নিন।”
লোকটা নিতে পারছিল না। অন্ধের মতো শুন্যে হাতড়াচ্ছিল। হঠাৎ বিদ্যুতের মতো মাথায় একটা কথা খেলে গেল তাঁর। লোকটা চোখে দেখতে পাচ্ছে না। এমন সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।
লোকটা হিংস্র গলায় বলল, “পালানোর মতলব করছিস! পালাবি?”
বলেই লোকটা খঙ্গের মতো কী একটা জিনিস কোমর থেকে খুলে আনল।
কোপটা যেখানে পড়ল সেখানে গবাক্ষবাবুর পা। তিনি সট করে পা দুটো টেনে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তফাত হলেন খানিকটা।
“কোথায় তুই?”
গবাক্ষ জবাব দিলেন না। কিন্তু বোধ হয় তাঁর শ্বাসের শব্দে টের পেয়ে লোকটা এগিয়ে আসছিল। কী হল কে জানে, গবাক্ষ টর্চটা তুলে সুইচ টিপে ধরলেন।
কেলোর দোকানের শস্তার টর্চ। কখন জ্বলে, কখন জ্বলে না তার কিছু ঠিক নেই।
কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে টর্চটা ধাঁ করে জ্বলে উঠল। আর সোজা ফোকাসটা গিয়ে পড়ল জাম্বুবানটার চোখে। লোকটা খঙ্গ ফেলে দিয়ে চোখ চেপে ‘আ’ করে একটা আর্তনাদ করল।
গবাক্ষবাবু আরও খানিকটা সরে এলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। ভয়ে মরে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু মনে হল টর্চটা থাকলে বোধ হয় বেঁচে যাবেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, টর্চের মতো গুরুতর জিনিস আর দুনিয়ায় নেই। কলকারখানায় সব জিনিস ফেলে শুধু টর্চ তৈরি করা উচিত।
আচমকাই গবাক্ষ শুনতে পেলেন জঙ্গল ভেঙে বাঁদিক থেকে কারা যেন আসছে। জাম্বুবানটার দলবল নাকি? গবাক্ষবাবু তাড়াতাড়ি ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে সরে গেলেন।
চার-পাঁচটা বিশাল চেহারার লোক এসে জাম্বুবানটাকে ঘিরে দাঁড়াল।
কোন ভাষায় যে তারা কথা কইল একবর্ণও বুঝতে পারলেন না গবাক্ষ। কিন্তু তিনি টর্চটা বাগিয়ে ধরে রইলেন।
অন্ধ জাম্বুবানটা কী যেন বলতেই লোকগুলো চটপট চোখে কী যেন পরে নিল। তারপর সোজা এগিয়ে এল তাঁর দিকে।
পট করে টর্চ জ্বালালেন গবাক্ষ। টর্চ জ্বলল বটে, চোখে আলোও গিয়ে পড়ল, কিন্তু ঠুলির মতো কী একটা বস্তু চোখে পরে নেওয়ার ফলে এদের কিছু হল না।
গবাক্ষ আর দেরি করলেন না। পিছু ফিরে ছুটতে লাগলেন। পেছনে লোকগুলো তেড়ে আসছে।
আচমকাই যেন চোখের জ্যোতি বেড়ে গেল গবাক্ষর। তিনি জঙ্গলটা বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন। দিব্যি গাছের ফাঁকে ফাঁকে আঁকাবাঁকা হয়ে পথ করে নিচ্ছিলেন তিনি।
খানিকক্ষণ ছোটার পর মনে হল, পেছনে কেউ আসছে না তো! তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে বেদম হয়ে পড়েছেন। না জিরোলেই নয়। একটা গাছে হেলান দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ বাদে একটা গণ্ডগোল, অনেক লোকের কথাবার্তা আর চেঁচামেচি কানে এল তাঁর। না, এরা জাম্বুবান নয় বোধ হয়। চোখ খুলে তিনি দেখলেন, এতক্ষণ তাঁর খেয়ালই হয়নি যে, ভোরের আলো ফুটেছে। সেইজন্যই জঙ্গলটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন একটু আগে।
কে যেন চেঁচিয়ে ডাকছিল, “গবাক্ষবাবু। গবাক্ষবাবু!” গবাক্ষ সজনীবাবুর গলা চিনতে পেরে সোল্লাসে চেঁচিয়ে বললেন, “এই যে আমি!”
কিন্তু গলা দিয়ে এমন ফ্যাঁসফ্যাঁসে আওয়াজ বেরোল যে তিনি নিজেই তা শুনতে পেলেন না। তবে তিনি এগিয়ে গেলেন। ছুটতে ছুটতে তিনি জঙ্গলের ধারেই চলে এসেছিলেন কখন যেন। একটু এগোতেই দেখেন সজনীবাবুর পিছু পিছু জ্ঞানপাগলা, নরহরি, অলিন্দ, নৃপেনবাবু, তেজেনবাবু, আরও অনেকে দল বেঁধে হাজির।
সজনীবাবু তাঁকে দু’হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, “বেঁচে আছেন তা হলে! অ্যাঁ। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!”
কাতরকণ্ঠে গবাক্ষবাবু বললেন, “আর কয়েকবার ঝাঁকুনি দিলে বেঁচে থাকব না কিন্তু। জাম্বুবানটা আমাকে আধমরা করে রেখেছে।”
সজনীবাবু তাঁকে আরও দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে বললেন, “সেই লোকটা কোথায়?”
গবাক্ষবাবু সভয়ে বললেন, “জঙ্গলের মধ্যে।”
ভিড়ের পেছন থেকে ‘জয় কালী’ বলে এগিয়ে এল শ্যামা তান্ত্রিক। পরনে রক্তাম্বর, হাতে শূল। বলল, “কাল মাঝরাতে ব্যাটাকে বাণ মেরে কানা করে দিয়েছিলাম। এবার ব্যাটার মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলব। বলে কিনা তান্ত্রিক! তন্ত্রের জানে কী ব্যাটা তারা তান্ত্রিক? আসুন আপনারা আমার পিছু পিছু। ব্যাটাকে আমি ঠিক খুঁজে বার করব।”
রোগা চেহারার একটা লোক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, “ও আপনার কর্ম নয় বাবাজি। এ জঙ্গল ঘোর গোলকধাঁধা। পথ আমিই দেখাচ্ছি। দিনমানে তারাবাবা গা-ঢাকা দিয়ে থাকেন। সে জায়গা আমরা কয়েকজন মাত্র চিনি।”
শ্যামা হেঁকে উঠে বলল, “খবর্দার, ওকে বাবা-টাবা বলবি না।”
“যে আজ্ঞে।”
“তুই কে?” লোকটা বলল, “আজ্ঞে প্রিয়ংবদ। কেউ কেউ পঞ্চাও বলে। আসুন।”
পঞ্চা গহিন থেকে গহিনতর জঙ্গলে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। গাছ আর লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যেও একটা সংকীর্ণ শুড়িপথ যে আছে তা বোঝা যাচ্ছিল। পেছনে বিস্তর লোক কথা কইছে। পঞ্চা বলল, “কর্তারা কথা কইবেন না। বাবার ধ্যান ভেঙে গেলে কুপিত হবেন।”
শ্যামা ধমক দিল, “ফের বাবা?”
“আজ্ঞে আর হবে না।”
পঞ্চা যেখানে নিয়ে এল সেটা ঘোর জঙ্গলের মধ্যে একটু পরিষ্কার জায়গা। তবে ওপরে বড় বড় গাছের ডালপালায় বেশ অন্ধকার। সামনে নরকরোটি দিয়ে তৈরি একখানা ঘর। অনেকটা তাঁবুর মতো দেখতে। ঢোকার দরজার পাল্লা বন্ধ। পঞ্চা বলল, “ওই হল বাবার সাধনগৃহ।”
শ্যামা তাকে এবার শুলের খোঁচা দিয়ে চাপা গলায় বলল, “ফের বাবা বললে এ-ফোঁড় ওফোড় করে দেব।”
সবাই ঘরটার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
জ্ঞান এগিয়ে এসে হাত তুলে সবাইকে শান্ত থাকতে ইঙ্গিত করল। চাপা গলায় বলল, “এটা আমার লড়াই। আমি নয়নগড়ের যুবরাজ জ্ঞান, বিদ্রোহ দমনের জন্য আমি মহারাজ প্রণন্দের পাঞ্জা নিয়ে এসেছি।”
সবাই অবাক চোখে চেয়ে রইল। ভিড় ছেড়ে কয়েকজন লোক এগিয়ে গিয়ে জ্ঞানের পাশে দাঁড়াল। তারা কিছুই করল না, শুধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ঘরটার দিকে চেয়ে রইল। তেজেনবাবু মৃদুস্বরে নরহরিকে বললেন, “ওরা বোধ হয় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করছে।”
হঠাৎ একটা করোটি ঘরের মাথা থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। তারপর আরও একটা। আরও একটা। তারপর হঠাৎ হুড়মুড় করে গোটা ঘরটাই ধসে পড়ে গেল। করোটি ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। আর সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে পাঁচটা বিশাল চেহারার ভয়ংকর লোক উঠে দাঁড়াল।
“কে! কে তোরা! এত সাহস! ধ্যান ভাঙলি।”
জ্ঞান অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, “বিদ্রোহী মাজুম, রাজা প্রণন্দের নামে আমি তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদের নির্বাসন দণ্ড ঘোষণা করছি।”
সঙ্গে সঙ্গে মাজুমের মুখ যেন রাগে ফুলে দুনো হয়ে গেল। সে হিসহিস করে বলল, “ওঃ তুমি! তুমি যুবরাজ জ্ঞান! আমার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছ কাপুরুষ!”
বলেই জ্ঞানের গলার শব্দের নিশানা তাক করে সে তেড়ে এল। হাতে খঙ্গ। জ্ঞান সরে গেল বিদ্যুৎগতিতে। তারপর আর হিতাহিতজ্ঞান রইল না মাজুম আর তার স্যাঙাতদের। তারা চারদিকে অন্ধের মতো খঙ্গ চালাতে লাগল। খচাং খচাং করে চারদিকে গাছের ডালপালা কেটে পড়তে লাগল। সভয়ে লোকেরা দূরে সরে গাছগাছালির আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখতে লাগল।
যুদ্ধ অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হল না। হঠাৎ একটা মোটা গাছের আড়াল থেকে সজনীবাবু বেরিয়ে এসে হাতের মোটা বেতের লাঠির বাঁকানো হাতলটা মাজুমের পায়ে ঢুকিয়ে হ্যাঁচকা টান মারতেই সে পাহাড়ের মতো পড়ে গেল মাটিতে। জ্ঞান বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে তার কোমরে হাত দিয়ে দুটো কাঁচের শিশি বের করে নিল।
ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মাজুম। বলল, “কুমার, এটা অন্যায় হচ্ছে। আমার জান ফিরিয়ে দাও। কাপুরুষের মতো কাজ কোরো না।”
“এটা তোমার কাপুরুষতার জবাব। মাজুম, শান্ত হও। মাথা পেতে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করো। নয়নগড়ে তোমাদের আর স্থান নেই। খঙ্গ ফেলে দাও মাজুম, শান্ত হও। তোমাদের এই পৃথিবীতেই বাস করতে হবে। বন্ধুভাবে।”
জ্ঞান সজনীবাবুর দিকে ফিরে বলল, “আপনি সাহসী। অনেক ধন্যবাদ। এবার আমরা চলে যাব।”
জ্ঞান ও তার সঙ্গীরা পাশাপাশি দাঁড়াল। স্থির। জ্ঞান একটা শিশি শূন্যে তুলে কিছুক্ষণ ধরে রইল। তারপর হাতটা সরিয়ে নিল ম্যাজিশিয়ানের মতো। আশ্চর্য! শিশিটা পড়ল না। শুন্যে একটা ঘড়ির কাঁটার মতো ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল। ঠিক এক মিনিটের মাথায় ধীরে ধীরে আবছা হতে লাগল তারা। জ্ঞান হাত তুলে বলল, “বিদায়।” পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। সবাই থ’ হয়ে দৃশ্যটা দেখল।
মাজুম ও তার সঙ্গীরা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সজনীবাবু হঠাৎ নীরবতা ভেঙে বললেন, “ওহে মাজুম, নবাবগঞ্জে থাকতে চাও? তা শত্রু হিসেবে, না বন্ধু হিসেবে?”
মাজুম খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে খড়গটা ফেলে দিল। তারপর দু’হাত ওপরে তুলে স্খলিত কণ্ঠে বলল, “বন্ধু! বন্ধু!”
শ্যামা তান্ত্রিক একগাল হেসে সজনীবাবুকে বলল, “ভাববেন না। ব্যাটাদের আমি আমার চেলা করে নেব’খন।”
(সমাপ্ত)