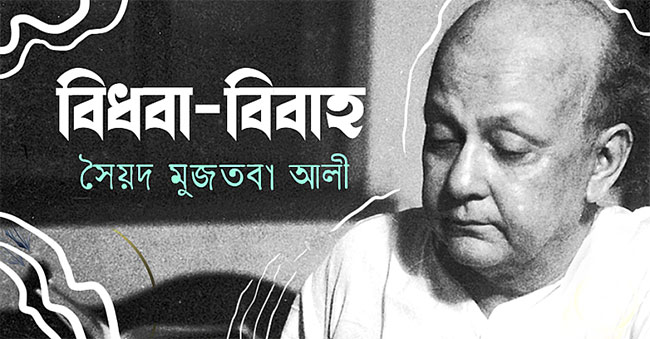আমাদের পুজোসংখ্যা ইংরেজদের ক্রিসমাস স্পেশালের অনুকরণে জন্মলাভ করেছিল কি না সে-কথা পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন, কিন্তু একথা ঠিক যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ইংরিজি স্পেশালের চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রিসমাস সংখ্যাগুলোতে থাকে অসংখ্য ছেলেমানুষি গল্প আর এন্তার গাঁজা-বছরের আর এগারো মাস ইংরেজ হাঁড়িপানা মুখ করে থাকে বলে ঐ একটা মাস সে মুখের সব লাগাম ছিঁড়ে ফেলে যা-খুশি-তাই বকে নেয়। আমাদের পুজোসংখ্যায় এ-সব পাগলামি থাকে না। তাই ভেবে পাইনে সত্যি-মিথ্যেয় মেশানো এদেশের আজগুবি গল্পগুলো ঠাঁই পাবে কোথায়, কোন মোকায়?
এতদিন ইংরেজের নকল করতে বাধো বাধো ঠেকত। ভয় হত পাছে লোকে ভাবে ‘খানবাহাদুরির তালে আছি। এখন পুজোর গাঁজায় দম দিয়ে দু’চারখানা গুল ছাড়তে আর কোনো প্রকারের বাধা না থাকারই কথা। অবশ্য সত্যি-মিথ্যের মেকদার যাচাইয়ের জন্য পাঠক জিম্মাদার।
বরোদার ভূতপূর্ব মহারাজা তৃতীয় সয়াজী রাও-এর কথা এদেশের অনেকেই জানেন। ইনি বিলেত থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, মৌলানা মুহম্মদ আলীকে এবং এদেশ থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্ৰীযুত আম্বেডকরকে বেছে নিয়ে বরোদার উন্নতির জন্য নিয়োগ করেন। এককালে প্রবাসীতে এর সম্বন্ধে অনেক লেখা বেরিয়েছিল। বরোদা রাজ্যের দু-একজন বৃদ্ধের মুখে আমি শুনেছি, অরবিন্দ বাঙলাদেশে যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তাতে নাকি সয়াজী রাও-এর গোপন সাহায্য ছিল।
ইনি আসলে রাখাল-ছেলে। বরোদার শেষ মহারাজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গদিচ্যুত হলে পর, ইনি তার নিকটতম আত্মীয় বলে এঁকে দূর মহারাষ্ট্রের মাঠ থেকে ধরে এনে গুজরাতের বরোদা রাজ্যের গদিতে বসানো হয়। তখন তার বয়স যোলর কাছাকাছি। বরোদার তখন এমনি দুরবস্থা যে দিবা-দ্বিপ্রহরে নেকড়ে বাঘ শহরের আশপাশ থেকে মানুষের বাচ্চা ধরে নিয়ে যেত–সরকারী চাকুরেদের বছরতিনেকের মাইনে বাকি থাকতে বলে দেশটা চলতো ঘুষের উপর, আর তাবৎ বরোদা স্টেটের ঋণ নাকি ছিল ত্রিশ কোটি টাকার মতো।
সয়াজী রাও প্রায় বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। সারদা এ্যাক্ট পাস হবার বহু পূর্বেই তিনি নিজে জোর করে আইন বানিয়ে আপন রাজ্যে বালবিবাহ বন্ধ করেন, খয়রাতি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালান, হিন্দু লগ্নচ্ছেদের (ডিভোর্স) আইন চালু করেন, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি খোলার বন্দোবস্ত করেন ও মরার সময় স্টেটের জন্য ত্রিশ কোটি টাকা রেখে যান। বরোদা শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় কলকাতাকে হার মানায়, সে পাল্লা দেয় বোম্বাই-বাঙ্গাললারের সঙ্গে।
এই মহারাজাই দিল্লীর দবোরে ইংরেজ রাজার দিকে পিছন ফিরে, ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গটগট করে বেরিয়ে এসেছিলেন বলে তাঁর গদি যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অরবিন্দের ব্যাপারে ইংরেজ তার উপর এমনিতেই চটা ছিল, তার উপর এই কাণ্ড— এরকম একটা অজুহাত ইংরেজ খুঁজছিলও বটে। এ-ব্যাপার সম্বন্ধে স্বয়ং সয়াজী রাও লিখেছেন, ‘ইংরেজ আমাকে গদিচ্যুত করতে চেয়েছিল বাই গিভিং দি ডগ এ ব্যাড নেম। তিনি দরবারে হিজ ম্যাজেস্টিকে কতটা অসৌজন্য দেখিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে নানালোকের নানা মত, কিন্তু ফাঁড়াটা কাটাবার জন্য তিনি যে লাখ পনরো ঘুষ দিয়েছিলেন সেসম্বন্ধে সব মুনিই একমত। ব্রিটিশ প্রেসেরও চাপ নাকি ভালো করে তেল ঢাললে ঢিলে হয়ে যায়।
এসব কথা থেকে সাধারণ লোকের ধারণা করা কিছুমাত্র অন্যায় নয় যে সয়াজী রাও খাণ্ডারবিশেষ ছিলেন। তা তিনি ছিলেনও, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তার রসবোধ ছিল অসাধারণ—শুধু রাজারাজড়াদের ভিতরেই নয়, জনসাধারণের পাঁচজন বিদগ্ধ লোককে হিসেবে নিলেও।
সার ভি. টি. কৃষ্ণমাচারীর নাম অনেকেই শুনেছেন। ইনি কিছুদিন পূর্বেও জয়পুরের দেওয়ান (প্রধানমন্ত্রী) ছিলেন ও উপস্থিত কোথায় যেন আরো ডাঙর নোকরি করেন। ইনি যখন বরোদার দেওয়ানরূপে আসেন তখন তিনি উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এবং আর কিছু পারুন আর নাই পারুন, একথা সত্যি, বক্তৃতা দিতে গেলে তার টনসিল আর জিভে প্যাঁচ খেয়ে যেত। এখনো সে উৎপাতটা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।
শুনেছি, তিনি যখন বরোদায় এলেন তখন ‘সয়াজী বিহার ক্লাব’ তাকে একখানা যগ্যির দাওয়াত দিলে। স্বয়ং মহারাজ উপস্থিত। শহরের কুতুবমিনাররা সব বোম্বাইবোম্বাই লেকচর ঝাড়লেন, ভি. টি.’র মতো মানুষ হয় না, এক এ্যাডাম হয়েছিলেন আর তারপর ইনি, মধ্যিখানে স্রেফ সাহারা ইত্যাদি ইত্যাদি।
কুতুবরা ভি. টি’কে সপ্তম-স্বর্গে চড়িয়ে দিয়ে যখন থামলেন তখন—
কৃষ্ণমাচারী-পানে সয়াজী রাও হাসিয়া করে আঁখিপাত।
চোখের পর চোখ রাখিয়া মূক কহিল ওস্তাদজি,
ভাষণ ঝাড়ো এবে উমদা ভাষণ, ভাষণ এরে বলে ছি!
ভি. টি.’র শত্রুরা বলে তার পা নাকি তখন কাঁপতে শুরু করেছিল। অসম্ভব নয়, তবে একথা ঠিক তিনি অতি কষ্টে, নিতান্ত যে ধন্যবাদ না দিলেই নয়, তাই বলে ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন।
সর্বশেষে মহারাজার পালা। বুড়ো বলতেন খাসা ইংরেজি। অতি সরল এবং অত্যন্ত চোস্ত—সর্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার বিবর্জিত।
সামান্য দু-একটা লৌকিকতা শেষ করে সয়াজী রাও বললেন, ‘দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে বরোদা রাজ্য চালনা উপলক্ষে আমি বহু মহাজনের সংস্রবে এসেছি এবং তাদের সকলের কাছ থেকেই আমি কিছু-না-কিছু শিখে আমার জীবন সমৃদ্ধশালী করেছি। এই দিওয়ানের কাছ থেকে শিখলুম বাকসংযম।
শক্তিশেল খেয়ে লক্ষ্মণ কী করেছিলেন রামায়ণে নিশ্চয়ই তার সালঙ্কার বর্ণনা আছে—পাঠক সেটি পড়ে নেবেন।
ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সয়াজী রাও-এর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পাভলোভা এদেশে আসার বিশ বৎসর পূর্বে তিনি ভরতনাট্যম উত্তর ভারতে চালু করবার জন্য একটা আস্ত টুপ নিয়ে বিস্তর জায়গায় নাচ দেখিয়েছিলেন। উত্তর ভারত তখনও তৈরি হয়নি বলে দক্ষিণ কন্যাদের সে-নৃত্যের কথা আজ সবাই ভুলে গিয়েছে।
বরোদার ‘ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট’ দেশ-বিদেশে যে খ্যাতি অর্জন করেছে তার সঙ্গে ভারতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না। এ স্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও বলবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না যে, প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। ইনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র।
সয়াজী রাও-এর অনুরোধেই শিল্পী নন্দলাল বসু বরোদার কীর্তি মন্দিরের চারখানি বিরাট প্রাচীর চিত্র এঁকে দিয়েছেন। নন্দলাল এত বৃহৎ কাজ আর কোথাও করেননি।
নীচের কিংবদন্তিটি পড়ে পাছে কেউ ভাবেন সয়াজী রাও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, তাই তার বহু কীর্তি থেকে এই সামান্য দু-একটি উদাহরণ দিতে বাধ্য হলুম।
গল্পটি আমাকে বলেছিলেন পুব বাঙলার এক মৌলবী সায়েব-খাস বাঙাল ভাষায় বিস্তর আরবী-ফারসী শব্দের বগহার দিয়ে। সে ভাষা অনুকরণ করা আমার অসাধ্য। গ্রামোফান রেকর্ড পর্যন্ত তার হুবহু নকল দিতে পারে না।
নস্যিতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো ব্রহ্মটান দিয়ে বললেন—এই বরোদা শহরে কত আজব রকমের বেশুমার চিড়িয়া ওড়াউড়ি করছে, তার মধ্যিখানে সয়াজী রাও কেন যে চিড়িয়াখানা বানিয়েছেন বলা মুশকিল। তিনি নিজে তো সিঙি, অমুক ব্যাটা গাধা, অমুক শালা শুয়োর, তমুক হারামজাদা বিচ্ছু, আর আমি নিজে তো একটা আস্ত মর্কট, না হলে এদেশে আসবো কেন—এসব মজুদ থাকতে চিড়িয়াখানা বানাবার মতলব বোধ করি জানোয়ারগুলোকে ভয় দেখাবার জন্য, যদি বড্ড বেশি তেড়িমড়ি করে তবে খাঁচা থেকে বের করে বড় বড় নোকরি তাদের দিয়ে দেওয়া হবে।
বাইরের জানোয়ারগুলোর জ্বালায় অস্থির হলে আমি হামেশাই চিড়িয়াখানায় যাই। খুদখেয়ালি অর্থাৎ আত্মচিন্তার জন্য জায়গাটি খুব ভালো। তা সেকথা যাক।
সয়াজী রাও বহু জানোয়ার এনেছেন বহু দেশ ঘুরে। পৃথিবীটা তিনি কবার প্রদক্ষিণ করেছেন, তার হিসেব তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন। একবার বিলেত যাবার সময় তার পরিচয় হল হাবশী দেশের রাজা হাইলে সেলাসিসের সঙ্গে।
আমাদের দেশের লোক সাদা চামড়ার ভক্ত। যে যত কালো সাদা চামড়ার প্রতি তার মোহ তত বেশি, ইয়োরোপে নাকি কালো চামড়ার আদর ঠিক সেই অনুপাতে। একমাত্র হাবশীরাই শুনেছি আপন চামড়ার কদর বোঝে। তাই সায়েবদের দিকে তারা তাকায় অসীম করুণা নিয়ে—আহা, বেচারিদের ও-রকম ধবলকুষ্ঠ হয় কেন?
সয়াজী রাও-এর রঙ কালো। হাবশী রাজা প্রথম দর্শনেই বুঝে ফেললেন, আমাদের মহারাজার খানদান অতিশয় শরীফ। কোনো রকমের বদ-জাত ধলা খুন তার কুলজিঠিকুজিতে কভি-ভী দাখিল হতে পারেনি। এ খুনের জন্য আমীর-ওমরাহ, নোকরখিদমৎগার আপন খুন বহাতে হামেহাল হরবকত হাজির।
হাবশী-রাজ সয়াজী রাও-এর দরাজদিলের নিশানও ঝটপট পেয়ে গেলেন। জাহাজেই রাজার জন্মদিন পড়েছিল-সয়াজী রাও তাকে একখানা খাসা কাশ্মীরি শাল ভেট দিলেন। হাবশীরাজ সে-শাল পেয়ে খুশির তোড়ে বে-এক্তেয়ার। জাহাজময় ঘুরে-ফিরে সবাইকে সে-শাল দেখালেন, লালদরিয়ার গরমিকে একদম পরোয়া না করে সেই লাল শাল গায়ে দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করলেন। চোরচোট্টার ভয়ে শেষতক তিনি শালখানা কাপ্তান সায়েবের হাতে জিম্মা দিলেন।
হাবশী-রাজও কিছু নিকৃষ্টি মনুষ্য নন। সয়াজী রাও-এর দিন-তোড় মহব্বতের বদলে তিনি কী সওগাত দেবেন সে বাবতে বহুৎ আন্দিশা করেও তিনি কোনো ফৈসালা করে উঠতে পারলেন না। তাঁর রাজত্বে আছেই বা কী, দেবেনই বা কী? দুশ্চিন্তায় হাবশী রাজার কালো মুখ আরো কালো হয়ে গেল।
আমি বললুম, অসম্ভব! আমি মিশরে থাকার সময় বিস্তর হাবশী দেখেছি। তারা খানদানী নয়—তাদের মুখই আরো কালো করা যায় না, খুদ হাবশী-রাজের কথা বাদ দিন।
মৌলবীসাহেব রাগ করে বললেন, ঝকমারি! হাজার দফা ঝকমারি তোমাদের মতো বদরসিককে গল্প বলা। পঞ্চম জর্জের রঙ তো ফর্সা, তবে কি ভয় পেলে তার রঙ আরো ফর্সা হয় না?
আমি ‘আলবৎ আলবৎ’ বলে মাপ চাইলাম।
মৌলবীসাহেব বললেন, ‘শেষটায় হাবশীরাজ মহারাজের সেক্রেটারির সঙ্গে ভাব জমিয়ে বহুৎ সওয়াল-জবাব করলেন আর মনে মনে একটা ভেট ঠিক করে নিলেন।
সে বৎসর গরম পড়েছিল বেহদ। লু চলেছিল জাহান্নমের হাওয়া নিয়ে, আর আকাশ থেকে ঝরছিল দোজখের আগুন। সয়াজী সরোবরের বেবাক নিলুফরী পানি খুদাতালা বেহেশত বাসিন্দাদের জন্য দুনিয়ার মাথট হিসেবে তুলে নিয়েছিলেন, আর বরোদার জৈনরা পাখিদের জন্য গাছে গাছে জল রেখেছিল হাজারো রুপিয়া খর্চা করে। শুকনো গরমের জুলুমে আমার দাড়ি-গোঁপ পর্যন্ত যখন পট-পট করে ফেটে যাচ্ছিল এমন সময় শহরময় খবর রটলো, হাবশী বাদশাহ হাইলে সেলাসিস মহারাজা স্যজী রাওকে এক জোড়া সিংহ-সিংহী তোফা পাঠিয়েছেন—তার মুল্লুকের সবচেয়ে বড় জানোয়ার। হিজ হাইনেস সয়াজী রাও মহারাজ, সেনা-খাস-খেল বাহাদুর, ফরজন্দ-ই-দৌলত-ইইনকলিসিয়া, শমশের জঙ্গ বাহাদুরের কদমের ধুলো হবার কিস্মাৎ এদের নেই, তবু যদি মহারাজ মেহেরবাণী করে এদের গ্রহণ করেন, তবে হাবশী বাদশাহ বহুৎ, বহুৎ খুশ হবেন।
সেই গরমের মাঝখানে খবরটা রটল আগুনের মততা। আর গুজোব রটল ধুয়োর মতো বা তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। কেউ বলে, ‘ওরকম জোড়া-সিংগি লন্ডন শহরের চিড়িয়াখানাতেও নেই, কেউ বলে, হাবশী বাদশা খাস ফরমান দিয়ে মানুষের মাংস খাইয়ে খাইয়ে এদের তাগড়া করিয়েছেন, কেউ বলে, এদের গর্জনের চোটে জাহাজের তাবৎ লস্কর-সারেঙ বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েছে। আরো কত আজগুবি কথা যে রটলো তার ঠিক-ঠিকানা নেই।
সয়াজী রাও যে খুশ হয়েছিলেন সে সংবাদটাও শহরে রটলো। চিড়িয়াখানার ম্যানেজারের উপর হুকুম হল হাবশী সিংগির জন্য খাস হাবেলি তৈরি করবাব। কামাররা সব লেগে গেল খাঁচা বানাতে—দিনভর দমাদ্দম লোহা পেটার শব্দ শুনি, আর শহরের ছোঁড়ারা তখন থেকেই খাঁচার চতুর্দিকে ঝামেলা লাগিয়ে মেহমানদের তসবির-সুরৎ নিয়ে খুশ-গল্প জুড়ে দিয়েছে।
ম্যানেজার বোম্বাই গেলেন সিংগিদের আদাব-তসলিমাত করে বরোদা নিয়ে আসার জন্য। সেখান থেকে তারে খবর এল মেহমানরা কোন গাড়িতে বরোদা পৌঁছবেন। সেদিন শহরের ছ’আনা লোক স্টেশনে হাজিরা দিল— হুজুরদের পয়লা নজরে দেখবার জন্য। হাবেলিতে যখন তাদের ঢোকানো হল, তখন শহরের আর বড় কেউ বাদ নেই। সয়াজী মহারাজ শুনলেও গোসা করবেন না বলে বলছি, খুদ তাকে দেখবার জন্যও কখনো এরমধারা ভিড় হয়নি।
আমিও ছিলুম। আর যা দেখলুম তার সামনে দাঁড়াবার মতো আর কোনো চীজ আমি কখনো দেখিনি। আমার বিশ্বাস এ-জোড়া সিংগি দেখার পর আর কেউ খুদাতালায় অবিশ্বাস করবে না। তোমরা কী সব বলল না, নেচার নেচার—সব কিছু নেচার বানিয়েছে—
আমি বাধা দিয়ে বললুম, আমি তো কখনো বলিনি।
মৌলবীসাহেব ট্যারচা হাসি হেসে বললেন, ‘সিংগি দুটোর সামনে কাউকে আমি বলতেও শুনিনি। তোমাদের ঐ নেচার কোন কোন জিনিস পয়দা করেছেন জানিনে, কিন্তু এরকম সিংগি বানানো তার বাপেরও মুরদের বাইরে।
কী চলন, কী বৈঠন, ক্যা পশম, ক্যা গর্দন! পায়ের নখ থেকে দুমের লোম পর্যন্ত সব কুছ গড়া হয়েছে, স্রেফ এক চীজ দিয়ে—তাকৎ! খুদার কেরামতি বুঝবে কে, তাই তাজ্জব মেনে বার বার তাকে জিজ্ঞেস করি, এ রকম মাতব্বরকে তুমি এ-দুনিয়ার রাজা না করে মানুষের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিলে কেন?
‘সিংগি জোড়াকে দেখবার জন্য অহমদাবাদ, আনন্দ, ভরোচ, সুরট এমনকি বোম্বাই থেকে তোক আসতে লাগল। ফুল ফুটলে কেউ লক্ষ্য করে, কেউ করে না, চাঁদ উঠলে কেউ খুশি হয়, কেউ তাকায় না। কিন্তু এ-জোড়া সিংগি দেখে মনে মনে এঁদের পায়ে তসলিম দেয়নি, এ রকম লোক আমি কখনো দেখিনি।
তবে আমি নিজে এঁদের দেখেছি সবচেয়ে বেশি। কেঁচড় ভরে ছোলাভাজা নিয়ে সামনের গাছতলায় বসে আমি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছি এই রাজা-রানীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তাদের ভাষা বুঝিনি এ কথা সত্য, কিন্তু একটা হক বাৎ আমি তাদের ঘোঁতঘোঁতানি থেকে সাফ সাফ বুঝে নিয়েছিলুম, সেটা হচ্ছে এই—হিন্দুস্থান মুলকটা হুজুরদের বিলকুল পছন্দ হয়নি।
তাই যেদিন ফজরের নমাজ পড়ার পর শুনতে পেলুম সিংগিটা মারা গিয়েছে তখন আশ্চর্য হলুম না বটে, কিন্তু পাগলের মতো ছুটে গেলুম চিড়িয়াখানায় আর পাঁচজনেরই মতো। ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি, দেখি এরই মাঝে জলসা জমে গিয়েছে। সবাই মাটিতে বসে গালে হাত দিয়ে খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন এক হাট লোকের সকলেরই বড় ব্যাটা মারা গিয়েছে।
আর সিংহরাজ শুয়ে আছেন পুবদিকে মুখ করে। আহা হা, কী জৌলুস, কী বাহার! দেখে চোখ ফেরাতে পারলুম না। জ্যান্ত অবস্থায় চলাফেরার দরুনই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক তার সম্পূর্ণ শরীরের পরিমাণটা যেন আমার চোখে ঠিক ধরা দেয়নি, আজ স্পষ্ট দেখতে পেলুম কতখানি জায়গা নিয়ে হুজুর শেষ-শয্যা পেতেছেন। মনে মনে বললুম, আলবৎ আলবৎ। এই শেষশয্যা দেখেই কবি ফিরদৌসী তার শাহনামা কাব্যে সোহরাবের মৃত্যুশয্যার বর্ণনা করেছেন।
আর সিংগিনী! সে বোধ হয় তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। সিংহের চতুর্দিকে চক্কর লাগাচ্ছে, তার গা শুকছে আর আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কোন মহারানী ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রীকে সওয়াল করছেন।
বিহানের পয়লা সোনালি রোদ এসে পড়ল সিংহের কেশরে। শাহানশাহ বাদশার সোনার তাজে যেন খুদাতালা আপন হাতে গলা-সোনা ঢেলে দিলেন। সে তসবিরে চোখ ভরে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলুম।
বরোদা শহর শশাকে যেন নুয়ে পড়ল। যেখানে যাও, ঐ এক কথা, আমাদের সিংহ গত হয়েছেন।
সেদিন স্কুল-কলেজ বসলো না, ছেলে-ছোকরারা খাঁচার সামনে বসে আছে-চুপ করে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে কারো মুখে কথাটি নেই। আপিস-আদালত পর্যন্ত সেদিন নিমকাম করলো।
সিংগির লাশ বের করতে গিয়ে ম্যানেজারের জিভ বেরিয়ে গেল। সিংগিনী খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। খাবার লোভ দিয়ে যে তাকে পাশের খাঁচায় নিয়ে এখাঁচা থেকে লাশ বের করা হবে তারো উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত কী কৌশলে মুশকিল ফৈসালা হল জানিনে, আমি দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম।
তারপর আরম্ভ হল সিংগিনীর গর্জন আর দাবড়াননা। সমস্ত দিন খাঁচার ভিতর মতিচ্ছন্নের মতো চক্কর খায় আর মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে খাঁচার দেয়ালে দেয় ধাক্কা। এরকম খাঁচা ভাঙবার মতলব আগে কখনো সিংহ-সিংহী কারো ভিতরেই দেখা যায়নি। এখন সিংগিনী খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু ‘বেড়ে গেছে খাঁচাটাকে ভাঙবার চেষ্টা। সেই দুর্বল শরীর নিয়ে কখনো সমস্ত তাগদ দিয়ে খাঁচায় দেয় ধাক্কা, কখনো শিকগুলোকে খামচায়, আর কখনো লাফ দিয়ে তেড়ে এসে মারে জোর গোত্তা। সে কী নিদারুণ দৃশ্য!
সয়াজী রাও খবর পেয়ে হুকুম দিলেন, ‘বাঢ়িয়া, উমদা হাবশী সিংহ যোগাড় করার জন্য আদিস আব্বাবার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনা করো। কিন্তু সাবধান, হাবশীরাজ যেন খবর না পান তার দেওয়া সিংহ মারা গিয়েছে। আর ততদিনের জন্য কাঠিয়াওয়াড় থেকে একটা দিশী সিংহ আনাবার ব্যবস্থা করো। সেও যেন উমদাসে উমদা হয়, রুপেয়া কা কুচ্ছ পরোয়া নাহী।।
সয়াজী রাও বাদশার দয়ার শরীর, তার ললামে ললামে মেহেরবানি। খুদাতালা তার জিন্দেগী দরাজ করুন, হরেক মুশকিল আসান করুন—বরোদার সিংহই বুঝতে পাবে হাবশী সিংগিনীর দর্দ।
এক মাস বাদে বর এলেন কাঠিয়াওয়াড় থেকে। এ এক মাস আমি চিড়িয়াখানায় যাইনি। পাঁচজনের মুখে শুনলুম, সিংগিনীর দিকে তাকানো যায় না—তার চোখমুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরচ্ছে।
মৌলবী সায়েব গল্প বন্ধ করে জানলার দিকে কান পেতে বললেন, আজান পড়লো। তাড়াতাড়ি শেষ করি।
দুলহাকে যখন খাঁচায় পোরা হবে তখন ‘চার আঁখে’ মিলবার তসবির দেখার জন্য আমি আগেভাগেই খাঁচার সামনে গিয়ে হাজির হলুম। সিংগিনীর চেহারা দেখে আমার চোখে জল এল। অসম্ভব রোগা দুবলা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তেজ কমেনি এক রত্তিও।
কাঠিয়াওয়াড়ের দামাদ এলেন হাতি-টানা গাড়িতে করে। তিনিও কিছু কম না। কিন্তু হাবশী সিংগির যে তসবির আমার মনের ভিতর আঁকা ছিল তার তুলনায় বে-তাগদ, বেজৌলুস বে-রৌশন। সিংহ হিসেবে খুবসুরৎ, কিন্তু দুলহা হিসাবে না-পাস।
খাঁচার দরজা দিয়ে দামাদ ঢুকলেন আস্তে আস্তে। সিংগিনী এক কোণে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এমন এক অদ্ভুত চেহারা নিয়ে যে আমি তার কোনো মানেই করতে পারলুম না।
তারপর যা ঘটলো তার জন্যে আমরা কেউ তৈরি ছিলুম না। হঠাৎ সিংগিনী এক হনুমানী লম্ফ দিয়ে, খাঁচা ইসপার উস-পার হয়ে পড়লো এসে সিংগির ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিন কিম্বা চার-খানা বিরাশী শিক্কার থাবড়া! কঠিয়াওয়াড়ি দামাদ ফৌত! বিলকুল ঠাণ্ডা!’
আমি অবাক হয়ে বললুম, সে কী কথা?
মৌলবী সায়েব বললেন, এক লহমায় কাণ্ডটা ঘটলো। কেউ দেখলো, কেউ না।
আমি বললুম, একটা লড়াই পর্যন্ত দিলে না?
মৌলবী সায়েব বললেন, না।
আমি বললুম, তারপর?
মৌলবী সায়েব বললেন, তারপর আর কিছু না। আমি এখন চললুম, গল্পে মেতে গেলে আমার আর কোনো হুঁশ থাকে না!
দরজার কাছে গিয়ে মৌলবী সায়েব থামলেন। বললেন, হু, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।
খবরটা সয়াজী রাও-এর কাছে পৌঁছে দিতে কেউই সাহস পান না। শেষটায় তার খাস পেয়ারা শহর-কাজী আর ধর্মাধিকারী নাডকর্ণিকে ধরা হল। তারা যখন খবরটা দিলেন তখন মহারাজ নাকি একদম কোনো রকমেরই চোটপাট করলেন না। উল্টে নাকি মুচকি হাসি হেসে বললেন, আমি যখন বিধবা-বিবাহের জন্য একটা নয়া আন্দোলন আরম্ভ করতে চেয়েছিলুম, তখন তোমরাই না গর্ব করে বলেছিলে, এদেশের খানদানী বিধবা—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—নতুন বিয়ে করতে চায় না? হাবশী সিংগিনী এদেরও হার মানাল যে!