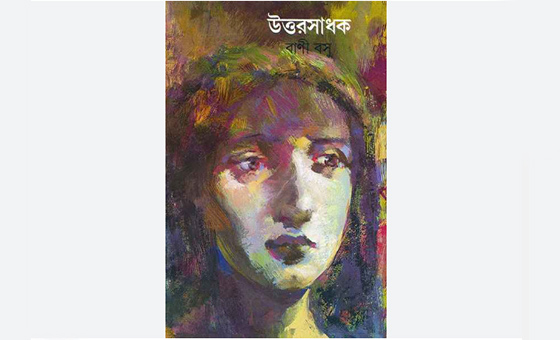মেধা ভাটনগর একটা দুর্দান্ত পাটকিলে রঙের শাড়ি পরছিলেন। পাটকিলের সঙ্গে বোধহয় সবুজ সুতো মেলানো আছে। হেলিকপ্টার থেকে দেখলে ঋতু পরিবর্তনের কোনও কোনও বিশেষ সময়ে ফসলের খেত বা গুল্ম-জাতীয় গাছের জঙ্গলে এই মিশ্রিত বর্ণ ধর্ম দেখতে পাওয়া যায়। লম্বা দিকে সরু-সরু ডোরা। আঁচলের দিকে যত এগিয়েছে ডোরাগুলো ততই আরও চওড়া আরও অলঙ্কৃত হয়ে গেছে। কালো, মেটে লাল আর গাঢ় সবুজ। কলাক্ষেত্র শাড়ি। শাড়ি বিষয়ে মেধার একটা অদ্ভুত আগ্রহ ও বিস্ময় আছে। তাঁর আলমারিতে হ্যাঙারে ঝুলছে এই রকম বিভিন্ন স্থানের বাছাই করা শাড়ি। সংখ্যায় কুড়ি একুশটার বেশি নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি আলাদা করে বিস্ময় জাগাবার মতো। এর মধ্যে যে কোনও শাড়িই তিনি যখন পরে বেরোন, তাঁর নিজের কিরকম একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব হয়। তিনি শুধু পোশাক পরেন নি, যেন এক টুকরো ভারতীয় সংস্কৃতি অঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই কলাক্ষেত্র শাড়ি তাঁকে উপহার দিয়েছে এক মার্কিন ছাত্র। মেধার উৎসাহে যে তার থিসিসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য ভারত দর্শনে আসে। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভেতর যখন সে পলিথিনের মোড়ক খুলে ভারতীয় শাড়ি-বাক্স এবং তার ভেতর থেকে এই অসাধারণ উপহারটি বার করে, তখন মেধা চমৎকৃত, রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। শুধু ছাত্রের দেওয়া উপহার বলে নয়। ভারতীয় ইতিহাসের মেরুদণ্ড যে একাধারে তার গতিশীল গ্রহিষ্ণু ধ্রুপদী শিল্প এবং লোকসংস্কৃতি এই কথাটি টেডকে এবং টেডের মতো অনেককে বোঝাতে পেরেছেন বলে।
মেধা আশা করছেন এখন, ভারতে ফেরবার পর তাঁর শাড়ি কেনার এবং পাওয়ার গতি বেড়ে যাবে, তাঁর সংগ্রহের লাইব্রেরিটা যদি এশিয়াটিক সোসাইটিকে দিয়ে যান, শাড়িগুলো তিনি মিউজিয়ামকে দিতে পারেন, কিন্তু না। তার পরেও এগুলো পরা হবে, তাঁর ছাত্রীদের দিয়ে যাবেন। সযত্নে সংরক্ষিত সুরভিত শাড়িগুলো যাঁরা তাঁকে ভালোবাসে তাদের পরতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না। এই ভাবে তাঁর সংগৃহীত তথ্য পরবর্তী প্রজন্মের কাজে লাগবে। কারণ ব্যক্তি মানুষ আসে, ব্যক্তিমানুষ যায়, কিন্তু বহু ব্যক্তিমানুষের প্রতিভা ও একাগ্র সাধনার ফল যে সংস্কৃতি তা প্রবাহিত হতে থাকে চিরকাল। সেই প্রবাহ যখন পঙ্কিল, সংকীর্ণ, অগভীর হয়ে ওঠে তখনই দেশ আর দেশ থাকে না ভূখণ্ড হয়ে যায়।
মেধার সব শাড়িই যে উপহার তা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটার পেছনে একটা না একটা ইতিহাস আছে। যেমন, গোলাপি-নীলের বমকাই শাড়িটা। এটা তিনি এক ওড়িশি নর্তকীর অঙ্গে দেখেছিলেন। মাছরাঙা উড়ে যাচ্ছে যেন গোলাপি পদ্মবনের ওপর দিয়ে। শাড়িটার সঙ্গে ওড়িশি নৃত্যের সব অসাধারণ ত্রিভঙ্গগুলি মিলে-মিশে আছে। এটা যেদিন পরেন ত্রয়োদশ শতকের নরসিংহদেবের সময়কার কোনও অসামান্য ছন্দোময়ী দেবনর্তকী তাঁর পাশে পাশে ছায়ার মতো ঘোরে। অনেক খুঁজেও যখন কুমকুম সৎপথী নামে ওই নৃত্যশিল্পীটির শাড়ির জোড়া পাওয়া গেল না, মেধা তাকে লেখেন। ফেরৎ ডাকে ভি পি-তে অবিকল ওই শাড়িটি পেয়ে যান। কুমকুম একটা চিরকুটে জানায় এসব শাড়ির জোড়া পাওয়া খুবই মুশকিলের ব্যাপার। সবই অর্ডারি মাল। মেধা আজও জানেন না কুমকুম তাঁর জন্য অত কষ্ট কেন করতে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুমকুমকে আনা হয়েছিল। অভ্যর্থনা-সমিতিতে তিনি ছিলেন। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে গিয়ে যেটুকু আলাপ।
বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েই মেধা প্রথম শাড়ির মূল্য বুঝতে পারেন। সেখানে সুবিধের জন্য অনেক সময়েই প্যান্ট পরতে হত। শাড়ি ধোয়া ইস্ত্রি করার অনেক হাঙ্গাম। আইওয়াতে একটা সেমিনার ছিল। ওদেশে যাবার দু চার মাসের মধ্যেই। মেধা পেপার পড়তে উঠলেন, ঘি-ঘি রঙের ওপর বহুবর্ণ বুটির-ফুলিয়া টাঙাইল। লাঞ্চ ব্রেকের সময়ে দুতিন জন ওদেশী মহিলা প্রতিনিধি তাঁকে এসে বললেন—অসাধারণ, অসামান্য, তুলনাহীন। ভেতরে ভেতরে খুবই আনন্দ মেধার, তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছেন মহিলাদের একজন বললেন—‘সত্যি অসাধারণ, তোমার শাড়ি, তোমার এই পোশাক। এ পোশাক তোমাকেও তুলনাহীন, অপূর্ব করেছে। পরার ভঙ্গিটাই বা কি আর্টিস্টিক। দা সুঈপিং এণ্ড, দা গ্রেসফুল প্লীটস ইন দা স্কার্ট।’ অপর দুজন অবশ্য তখন বলতে শুরু করেছেন—‘ইয়োর পেপার টূ-ইজ ফ্যানটাসটিক…’
ওদেশে এখন বহু বাঙালি, ভারতীয়, বাংলাদেশী রয়েছেন। কিন্তু কাজ-কর্মের জায়গায় প্রায় কেউই শাড়ি পরেন না। কোথাও কোথাও নিষিদ্ধ। অন্যত্র অসুবিধাজনক। কিন্তু মেধা তাঁর ক্লাসগুলো নিতেন শাড়ি পরেই। ক্রমশই তিনি এবং তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা শাড়ি-সৌন্দর্য-সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। একবার একটি ক্লাসে লেকচার আরম্ভ করতে যাচ্ছেন। একটি ফরাসী ছেলে বলে উঠল—‘মাদমোয়াজেল, এক মিনিট অপেক্ষা করুন লক্ষ্মীটি, আমাদের এখনও আপনার শাড়িটা দেখা শেষ হয় নি।’
জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন সন্ধে হয়ে আসছে। আর বেশি দেরি না করাই ভালো। মৈথিলী ভীষণ ক্ষুন্ন হবে। মেধা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, ঘরের জানলা বন্ধ করলেন, দরজায় তালা লাগালেন। সম্প্রতি ছোড়দা এসে জোর করে দোতলায় একটা কোল্যাপসিব্ল করিয়ে দিয়ে গেছে। সিঁড়ির সৌন্দর্য নষ্ট করে দিচ্ছে বলে কোনও লাভ হয়নি। পরের বারে এসে নাকি বার্গলার অ্যালার্মও লাগাবে। কোল্যাপসিব্লটা বন্ধ করতে হবে। তারপর নিচের দরজা, বাইরের গেট। ছোট্ট একটু লন মতো আছে, ধারে ধারে কিছু গুল্ম, কিছু ফুল।
ডাঃ অশোক ভাটনগরের এই বাড়িতে অবশেষে মেধা একলা। তিনি ডাঃ ভাটনগরের তৃতীয় সন্তান। তাঁর বাবার দেশ মীরাট, মায়ের বাংলা। ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ পিতার নাম এবং মাতার সংস্কৃতি গ্রহণ করে। বিশেষত যদি মাতৃভূমিতে থাকে। অশোক ভাটনগর এবং লীলা দত্তের আলাপ-পরিচয়-পরিণয় সব পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে হলেও তাঁরা যখন কলকাতায় কর্মজীবন শুরু করলেন অশোক আস্তে আস্তে কলকাতার উপান্তে এই বাড়ি করেন। লীলা কি ভেবে তাঁর বাড়ির নাম ‘অলম্’ দিয়েছিলেন জানা যায় না। কারণ বাড়ি করলেও অশোক-লীলার জীবনে শেকড় বলতে কিছু ছিল না। অশোক ভুলে গিয়েছিলেন তিনি উত্তর প্রদেশের, লীলাও ভুলে গিয়েছিলেন তিনি বাংলার। যতদিন বেঁচে ছিলেন পৃথিবীর এখানে ওখানে অতিথি-অধ্যাপক, ফেলো ইত্যাদি হয়ে থেকেছেন, ভারতবর্ষের আদ্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন কর্ম উপলক্ষ্যে। ছেলে মেয়েরা কলকাতার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। তাদের বলতেন—‘পালা, পালা। কোথাও শেকড় গাড়বি না। আগ্রহ আর সুযোগ তোদের যেখানে টেনে নিয়ে যায়, চলে যাবি।’ জ্যেষ্ঠ কীর্তি ভাটনগর তাই লণ্ডনে ডাক্তারি করেন। ডাক্তারদের পেশা নামেই স্বাধীন। তাদের কোথাও না কোথাও শেকড় গাড়তেই হয়। মেজ মুক্তি সরকারি চাকুরে। সম্রান্ত বুরোক্র্যাট। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে ঘোরাফেরা করছেন—চাকরি জীবনের এই পর্বে। তাঁরও এক হিসেবে শেকড় নেই। কিন্তু নিজের তাগিদে তো নয়! সবই কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ছোট প্রজ্ঞা অবশ্য প্রচণ্ড শেকড় ছিঁড়েছে। গুজরাতি ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে তার পার্টনার হিসেবে সে সিঙ্গাপুর, হংকং, টোকিও, ইংল্যাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। কখন তাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানতে হলে তার কলকাতার সেক্রেটারিকে ফোন করতে হয়, সে হংকং-এর সেক্রেটারিকে ফোন করে জেনে দেয়। একমাত্র মেধাই শেকড় ছিঁড়তে পারলেন না। ভাটনগর নামের শেকড়, ফার্ন প্লেসের বাড়ির শেকড়, কলকাতার শেকড়। স্টেট য়ুনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রশস্ত করিডরে যে লম্বা মেয়েটি ছেলেদের মতো বড় বড় পা ফেলে হেঁটে যেত, তার চেতনার অভ্যন্তরে বসে বসে বিনুনি নিয়ে খেলা করত আশুতোষ বিল্ডিং-এর দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে উপচোনো কলেজ স্ট্রিট দেখতে থাকা একটি উনিশ কুড়ির মেয়ের ইতিহাস। বোম ফাটছে, টিয়ার শেল…মেধা সরে আয়…লাঠি চার্জ…অসীমাভ পায়ে গুলি খেয়েছে, মেধা চলে আয়…লেট মী বি…প্যাকিং কেসের ওপর চড়ে রোকেয়া বক্তৃতা দিচ্ছে…বন্দুকের গুলির চেয়েও তীব্র, অগ্নিময়..য়ুনিভার্সিটি লনে ছাত্রসভা…ইনকিলাব জিন্দাবাদ…মেধা ওদিকে নয়…যেদিকে ইচ্ছে যাবো… ইস্স্ চোখের জলে নাকের জলে করে ছেড়েছে। ছোট কমনরুম, মুখে-চোখে জল দে, জলের ঝাপটা, চোখের মণির ওপর জল আছড়ে পড়ছে, আলো চম্কে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, আলো অমন টুকরো টুকরো কেন? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলেকট্রনের কণার মতো। অ্যাটমিক বৃত্ত থেকে ছিটকে যাচ্ছে ইলেকট্রন। অ্যাটম বিশেষিত হবে। হয়ে যাচ্ছে ভেতরের প্রচণ্ড জোরালো তাগিদে। মেধা ভাটনগর এইরকম এক বিশেষ তড়িৎকণা বা মানুষ নামধারী সচেতন মৌলের এক ইতিহাসময় আইসোটোপ।
মেধা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা শক্তপোক্ত কাঠামো। দু দফায় সাত বছর সাত বছর চোদ্দ বছর, বেশিটাই যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে কাটাবার ফলে এখন ভারতীয়, বিশেষত বাঙালি মানদণ্ডে বেশ ফর্সাই। সোজা ভুরু, বসা লম্বা চোখ, চোখের মণি গাঢ় বাদামি। মেধার ঠোঁটও লম্বাটে, বিবর্ণ গোলাপি। চুল সোজা, চকচকে। মধ্যিখানে সিঁথি করে একটা বেঁটে বিনুনি, কিম্বা ছোট্ট হাত খোঁপা। চিবুকে একটি টোল। মেধা এই টোলটি ভয়ানক অপছন্দ করেন। টোল, কোঁকড়া চুল, তিল বা বিউটি স্পট এইসব বিখ্যাত সৌন্দর্য লক্ষণ তাঁর ঘোর অপছন্দ। তাঁর ধারণা এগুলো মেয়েদের ন্যাকা করে দেবার ষড়যন্ত্র। তাঁর মতে বেশির ভাগ মেয়ে তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে, হয় ন্যকা, নয় বোকা, নয় তো দুইই। অ্যাফেকটেশন বা ন্যাকামি এক ধরনের স্ত্রীরোগ, জরায়ুর ব্যাধির মতোই। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা এবং ব্যায়াম করে সারানো দরকার। নইলে মনের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়বে। এর বাইরেও আরও নারী-প্রজাতি তিনি শনাক্ত করেছেন যাঁরা সচেতনভাবে পুরুষদের নকল করেন। এঁদের থেকেও মেধা শত হস্ত দূরে থাকার পক্ষপাতী। নিজের চিবুকের টোলটি তিনি রীতিমতো ঘৃণা করেন। ছাত্রজীবনে এর দরুণ তাঁর নাম হয়ে যায় ডিম্পল ভাটনগর। সে সময়ে এবং পরবর্তীকালেও অনেকেই তাঁর এই মারাত্মক টোলের প্রেমে পড়েন। শোনা যায় এরকম একটি নাছোড়বান্দা প্রেমিককে তিনি একবার তাঁর টোলটি উপড়ে নিয়ে তাঁকে অব্যাহতি দেবার প্রস্তাব দেন। একবার প্লাস্টিক সার্জনের কাছেও ঘুরে এসেছেন। টোলের সার্জারির প্রস্তাব সম্ভবত ভদ্রলোক জীবনে এই প্রথম পেলেন। বলেন—‘হোয়াটস রং উইথ ইট?
মেধা নিজের মনের কথা ডাক্তারকে বলবেন কেন। তিনি ডাক্তারের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, নিজের প্রশ্নটাই আবারও করলেন। টোলটার কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি না।
মেধার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারের টোলটা বেশ পছন্দ হয়ে যায়। তবে তিনি চালাক লোক। মনের ভাব চেপে গম্ভীরভাবে বলেন—‘ইমপসিব্ল। হয়ত স্ক্রেপ করে গ্র্যাফ্ট্ করে ঠিক করে দিলাম, তারপরেও ইয়োর চিন মে গ্রো অ্যানাদার ডিম্পল।’
এখন মেধা টোলের সঙ্গে সহবাস করতে শিখে গেছেন। ছোটখাটো ব্যাপারে আপস করা যায়। কিন্তু জীবনে আরও অনেক সমস্যা আছে, আরও বৃহৎ, আরও গম্ভীর, গভীর, ব্যাপক, আরও অনেক ভাবে অনিষ্টকর। সমাজের পক্ষে, মানুষের পক্ষে। মেধা সেখানে একেবারে আপসহীন। তবে তিনি আর অসহিষ্ণু নেই। এই সব অনিষ্টের নিরাকরণে তিনি অস্ত্র ধারণ করেন না। কোনও প্রসাধন, প্রহরণ, বাগ-যুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধ এসব ছাড়াই তিনি কেল্লাফতে করতে চান। তাঁর হৃদয়ের গভীরে আশা তিনি সোজাসুজি ঠিক সড়কটা দিয়ে হেঁটে চলবেন, সমস্যাগুলো আপনা থেকেই কোনও চৌম্বক শক্তিতে হতাহত হয়ে তাঁর পথের দুপাশে লুটিয়ে লুটিয়ে পরবে। মেধা জানেন তিনি কোনও গড়-উওম্যান নন। এরকম ধারণা করা স্বপ্ন দেখার শামিল। তবু কিছু কিছু মানুষের স্বপ্ন মরতে চায় না। মেধার নিজের অমর হবার সাধ নেই। তিনি চান তাঁর স্বপ্নগুলো অমর হোক, সত্য হোক।
দাদা ছিল কীর্তিশরণ, সে কারো, কোনও কিছুর শরণ নিতে চায় না। বড়ই স্বরাট। মেজদা ছিল মুক্তিনাথ, সে নাথ ত্যাগ করেছে। ছোট বোন ছিল প্রজ্ঞাপারমিতা, সে প্রজ্ঞার পারে যেতে ইচ্ছুক নয়। শুধুই প্রজ্ঞা দেশাই। মেধারও আদি নাম ছিল মেধাশ্রী। তিনিও শ্রীটুকু ত্যাগ করতে চাইলেন। শ্রীহীন হবার ইচ্ছেয় নয়। শ্ৰী-এর সঙ্গে যে হতাশা, অত্যাচার, অবিচার এবং আত্মতুষ্টির অনুষঙ্গ এতকাল ধরে চলে এসেছে তার প্রতি তাঁর তীব্র অনীহা। শ্রী থাকুক, কিন্তু কারো দৈন্যের ওপর ভর করে নয়। সৌন্দর্য থাকুক, কিন্তু কখনোই কুশ্রীতাকে আড়াল করবার জন্য নয়।
কাজেই মেধা সুন্দর, অথচ সুন্দর নন। পৃথিবী যদি সত্যিই কোনদিন বিমুক্ত মনের মানুষের বসতি হয়, যেখানে সৌন্দর্য কোনও পরিমাপগত ধারণা নয়, মুখ যেখানে সত্যি-সত্যিই মনের আয়না, সেখানে মেধা ভাটনগর আরও অনেক স্বাধীন-ছন্দ মানুষের ভিড়ে সানন্দে মিশে যাবেন। সবাই রাজা, সবাই সুন্দর, কারণ সবাই ছন্দোময়, শুভময়। সসাগরা ধরিত্রীর আপন সন্তানের মতো। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন মেধা তাঁর অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক দৈর্ঘ্য নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে থাকবেন। অনেকে বলবে—‘কেমন কাঠ-কাঠ’, ‘ফেমিনিন নয়’ কিম্বা ‘বাপ রে, এতো মেয়ে মেয়ে নয়’ আবার কেউ-কেউ আর কোনও বিশেষণ খুঁজে না পেয়ে বলবে—‘কী চমৎকার! কী অনন্য!’ ভিন্নরুচিৰ্হি লোক:।
খুবই কৌতূহল হয় জানতে মেধা বিয়ে করেন নি কেন। তিনি কি নারীমুক্তিতে বিশ্বাসী উগ্ৰক্ষত্রিয়া? কাউকে পতিত্বে বরণ করবেন না পাছে বিন্দুমাত্র দাসীত্ব করতে হয়। না কি তাঁর কোনও যৌন অক্ষমতা আছে? না কি তেমন কেউ তাঁকে কোনদিনও ডাক দেয় নি। মেধার জীবনে একটা গোপন খবর আছে। তিনি সবার অজ্ঞাতে বিয়ে করেছিলেন। এখনকার তুলনায় সে শৈশবকাল। মাত্র উনিশ বছর বয়সে এক বিশ বছরের বড় রাজনৈতিক দাদাকে। ভদ্রলোক যখন পর্যায়ক্রমে অজ্ঞাতবাসে এবং জেলে, তখন তাঁর আরব্ধ কর্মের কিছু কিছু ভার মেধার ওপর পড়েছিল। তখন তিনি ছাত্রী। ছাত্রফ্রন্টে কাজ করার দায় তাঁর। খুব সম্ভব ছাত্রীর স্বভাববশেই প্রচুর প্রশ্ন করতেন। প্রথম প্রথম জবাব পেতেন, তারপর নিরুত্তর কঠিন দেয়াল। জেল থেকে স্বামীর আদেশ এলো পার্টিপতিদের নির্দেশ নির্বিচারে মেনে চলার। বিস্মিত, ব্যথিত পত্নী প্রবল জেহাদ লিখে পাঠালেন, ক্রমশ চিঠির ধারা ক্ষীণ হয়ে এলো। জেলের মধ্যেই বছর দেড়েকের মধ্যে স্বামী যখন মারা গেলেন তখন মেধার সঙ্গে তাঁর আর কোনও সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কাজেই মেধা নিজেও ঠিক জানেন না, তিনি বিধবা না বিবাহ-বিচ্ছিন্ন। তিনি বোধহয় যযাতি-কন্যা মাধবীর মতো। বিবাহিত কিন্তু কুমারী।
মা মারা যাবার পর ফার্ণ প্লেসের বাড়িতে বাবা আর মেধা। বাবা বলতেন—‘কি রে মেধা, সেট্ল্ কর এবার? ত্রিপাঠী বার বার বলছে। ছেলেটা তো ভালোই। মুক্তি খুব সার্টিফিকেট দিচ্ছে।’
মেধার কি খেয়াল চাপল, বললেন—‘ঠিক আছে করব, কিন্তু ওকে এখানে এসে থাকতে হবে। মেয়েরাই বা কেন খালি শ্বশুর-বাড়ি যাবে, বাবা?’
অশোক বললেন—‘যুক্তির দিক দিয়ে তো কথাটা ঠিকই বলেছিস মা। কিন্তু সমাজের কতকগুলো বহুদিনের তৈরি অভ্যাস আছে তো! তাছাড়াও কথাটা কি জানিস? ছেলেরাই শ্বশুরবাড়ি যায়। মেয়েদের মতো ঘটাপটা করে কন্যাবিদায় হয় না বটে, কিন্তু ছেলেরাই যায়। দেখ না, আমিই তো সারাজীবন শ্বশুরবাড়ি পড়ে রইলাম, মীরাট ফিরে গেলাম কি! এখন আমাকে বাঙালি ছাড়া লোকে কি বলবে?
বাবা বাংলা বলেন চমৎকার। শব্দচয়ন, প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার লক্ষ্য করবার মতো। কিন্তু কথায় একটু হিন্দি টান আছে। মেধা হাসল, বলল—‘মীরাটে যে তুমি ফিরে যাবে, কে আছে সেখানে তোমার?’
—‘কেউ না থাক মেধা মাটি আছে?’
—‘হ্যাঁ যে মাটি থেকে উৎখাত হয়েছ মাত্র পনের বছর বয়সে। তাছাড়া বাবা, মাটিটা দেশ, তোমাদের এই পুরনো ধারণাটা ছাড়ো তো! ছাড়ো। মাটিটা দেশ নয়, মানুষগুলো দেশ। দেশের মাটি বলে মাটিতে মাথা ঠেকাও, বিশ্বমায়ের আঁচল-টাঁচলও পাতা থাকতে দেখো কিন্তু দেশের মানুষগুলোই দেশের রূপটা তৈরি করে।’
—‘আমারও তো তাই ধারণা ছিল রে! যত বুড়ো হচ্ছি মনে হচ্ছে মাটিটাই দেশ। মানুষ বদলে যায়, মাটি বদলায় না। হাওয়া, জল, মাটি এসব বদলায় না কখনও। কখনও মিথ্যে বলে না।’
মেধা দেখল বাবা আবেগপ্রবণ হয়ে যাচ্ছেন। শরিকি বিবাদে উত্যক্ত হয়ে একসময়ে অতি অল্প বয়সে বাবা-মার সঙ্গে তাঁদের কর্মস্থল কলকাতায় চলে আসেন। আর কখনও তেমনভাবে ফিরে যান নি। মীরাটের শুকনো হাওয়া, গরম কালের লু, হাড়ের ভেতর ঢুকে যাওয়া শীতের কামড় এমন কি ভয়ানক দিগ-দিগন্ত অন্ধকার-করা দম-বন্ধ আঁধি পর্যন্ত এখন স্মৃতির আদুরে বেরাল হয়ে গেছে। আবেগপ্রবণ সে নিজেও কম না। সেইসঙ্গে দুঃসাহসী। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। নইলে বিশ বছরের বড় মানুষটিকে অমন গোপনে বিয়ে করতে যাবে কেন? বাবা-মাকে বললে কি করতেন? একটু বোঝাবার চেষ্টা করতেন হয়ত—‘দ্যাখ, ম্যাচটা ঠিক হচ্ছে না, একটু ভাব্।’ কিন্তু সে জেদী মেয়ে, সেরকমভাবে জেদ করলে আপত্তি করতেন না। বরং তার দুঃখের সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন স্তম্ভের মতো। কিন্তু কিরকম একটা রোমাঞ্চকর অভিযানের মতো করে তখন নিয়েছিলেন ব্যাপারটা। ভেলায় করে একা আটলান্টিক পেরোনোর মতো। প্রজ্ঞা ছাড়া কেউ জানত না। এখনও জানে না।
বাবা বললেন—‘ত্রিপাঠী যদি এক কথায় এসে থাকতে রাজী হয়ে যায় তোরই কি ভালো লাগবে? তার চেয়ে বিয়ে হোক। শ্বশুরবাড়ি যা। তারপর তুই তো তোর বাবার কাছে বেশিটা থাকবিই। কান টানলে মাথা আপনি এসে যাবে।’
মেধার এক গোঁ—‘না। ত্রিপাঠীকে শর্ত করতে হবে।’
বাবা বললেন—‘ঠিক আছে। ওকেই বল কথাটা।’
মজার কথা রঘুনন্দনও প্রস্তাব শুনে ওই একই মন্তব্য করেছিল—‘আমি যদি এ শর্তে রাজি হয়ে যাই তুমি কি আমাকে সম্মান করতে পারবে?’
—‘কেন পারবো না?’ বললেও কিন্তু মেধার এই প্রশ্নের-উত্তরে-প্রশ্নে দুর্বলতা ছিল। প্রশ্নটা সে নিজেকেও করছিল—‘কেন পারবো না?’ এবং জবাবে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ‘না’ শুনে মরমে মরে যাচ্ছিল। প্রচলিত সংস্কার ভাঙা অত সহজ না। তখনই মেধার ক্ষীণভাবে মনে হয় পুরুষ সম্পর্কে মেয়েদের যেমন একটা সংস্কার আছে, সে স্বনির্ভর, শক্তিমান হবে, কোনও কোনও জিনিস মেনে নেওয়া তার চরিত্রকে দুর্বল করে, মেয়েদের সম্পর্কেও পুরুষদের সংস্কার থাকাটা স্বাভাবিক। মেয়েরা ধীর-স্থির অথবা লোভনীয় ভাবে চঞ্চল হবে, সিরিয়াস বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না, অকারণে হাসবে ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা ভাঙবো না। অথচ অন্যটা ভাঙতে বলব—এটা সুবিচার নয়। মেধা অত্যন্ত সৎ মেয়ে। নিজে নিজেই এই আবিষ্কারটা করার পর থেকে তার বিদ্রোহিণী ভাবটাতে একটু চিড় খায়। অস্বস্তি ছিল, ব্যাপারটা সে মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু তখন থেকেই সে তার প্রহরণগুলো একে একে বর্জন করছে। তবু, প্রহরণ বর্জন করলেও মহাবিদ্যা মহাবিদ্যাই থাকে। মেধা ভাটনগর শক্তিরূপা। যে ভুঁড়োপেটা বুড়ো শিবটিকে সে বরণ করেছিল, সে তার শক্তির স্বরূপ বোঝে নি। সে উপলক্ষ্য। তাকে উপলক্ষ্য করেই মেধার মধ্যে শক্তির খেলা আরম্ভ হয়। এখন কোনও উপলক্ষ্যের দরকার আর নেই, সমস্ত পৃথিবী, গোটা সিসটেমটাই তার শিব, তাকে অবলা অনিমন্ত্রিতা বলে দক্ষযজ্ঞে যেতে দিচ্ছে না। মেধাও একটার পর একটা রূপের খোলস মোচন করে নতুন নতুনতর শক্তিরূপ দেখাচ্ছে, দেখিয়ে চলেছে। কিন্তু হায়, একদম একলা-একলা বুঝি সতিই কিছু হয় না।
ত্রিপাঠীর সঙ্গে বিয়েটা হল না। বাবা মারা গেলেন, মেধা ফেলোশিপ নিয়ে বস্টন গেল। সেখানে থাকাকালীন একটি ব্রিলিয়ান্ট ডিভোর্সীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। অলয় মুখার্জি। ছেলেটির কেরিয়ার সোনার জলে লেখা। অ্যাকাডেমিক মহলে সুনামও খুব। মেধা যখন প্রায় ঠিকই করে ফেলেছে তার প্রস্তাবে মত দেবে, সেই সময়ে তার পূর্বর্তন স্ত্রী তনিমা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সাক্ষাৎকারটা পুরোপুরি অনুধাবন করবার মতো। ডিসেম্বর মাস। জানলার বাইরে তাকালে সব শুধু সাদা দেখাবে। হাওয়া আছে বেশ। বরফের ঝুরোগুলো তাই হিসহিসিয়ে দিক পরিবর্তন করছে ঘন ঘন। এই শব্দ ভীষণ ভালো লাগে বলে টয়লেটের স্কাইলাইটটা মেধা খুলে রেখেছে। বসবার ঘরে জানলার দু’ পাশে পর্দা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। কোলের ওপর লাল পাতলা কম্বল। একটা বিখ্যাত রুশ নভেল পড়ছে মেধা। ‘ডেড সোলস।’ প্রথম খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে এসে গেছে সে, পেঙ্গুইন এডিশনের ২৫৯ পাতা, এখনও মনে আছে—‘ইজ ইট নট লাইক দ্যাট দ্যাট য়ু টূ রাশিয়া, আর স্পীডিং অ্যালং লাইক আ স্পিরিটেড এয়কা দ্যাট নাথিং ক্যান ওভারটেক?…’ ড্রাইভ ওয়ে দিয়ে একটা ওল্ডসমোবিল ঢুকে এলো, ওয়াইপারের কাঁটাগুলো প্রাণপণে উইণ্ড স্ক্রীন থেকে বরফ সরাচ্ছে। দুদিকে দুটো অ্যাপার্টমেন্ট। ডানদিকেরটা ওর। মাঝখানে ড্রাইভ ওয়ে, ভায়োলেট রঙের মনে হল গাড়িটা, খুব অদ্ভুত রং, গাড়িতে চট করে দেখা যায় না। তবে না-ও হতে পারে। একে ঘন তুষারপাত, তার ওপর আধা-অন্ধকার। ভুল হতে পারে। ভায়োলেট গ্রেটকোট, টুপি নেমে এলো, গাড়ি লক করল। মেধা দেখছে। তার অ্যাপার্টমেন্টে রিং হল। দরজা খুলে দিয়েছে, সামনে ভায়োলেট ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে পুতুলের মতো একটি মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।
—‘আসতে পারি?
—‘নিশ্চয়ই! আপনি!’
—‘আমি তনিমা ভট্টাচার্য। এক্স মিসেস অলয় মুখার্জী।
—‘আসুন।’
মেয়েটিকে বসিয়ে মেধা রান্নাঘরে গেল। দুটো লম্বাটে বিয়ার মগে কফি নিয়ে ফিরে এলো। বলল—‘আমি বড় বড় কাপে বেশি-বেশি কফি খেতে ভালোবাসি। তোমার অসুবিধে হচ্ছে না তো!’
—‘না না। খুব ভালো হয়েছে। তাছাড়া কফি ইজ দি থিং। আমিও প্রচুর কফি খাই।’ কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর তনিমা বললে—‘তোমার ক্র্যাকার্স নেই;
—‘ওহ্ হো, ভুলে গেছি। মনে করো না কিছু। আনি।’
ক্র্যাকার্স-এ কামড় দিয়ে সে বিনা ভূমিকায় বলল—‘তোমাকে সাবধান করে দিতে এলুম। আমার যা অভিজ্ঞতা সেটা তোমাকে না বলা বিশ্বাসঘাতকতা হবে। আফট্রল আমরা দুজনেই ইন্ডিয়ান। শুনে তুমি নিজে ঠিক করো কি করবে।’
আর এক চুমুক কফি পান হল, তনিমা বলল—‘অলয় মুখার্জি ইজ আ ফার্স্ট ক্লাস স্কাউন্ডেল। হ্যাণ্ডসম চেহারা। বিতিকিচ্ছিরি রকমের ভালো কেরিয়ার। সাংঘাতিক ভালো চাকরি। দেখেশুনে আমার বাবা মা আমি স-ব গলে বাটি বাটি জল হয়ে গেলুম। পাত্রপক্ষের চাহিদা কি? কিচ্ছু না, বনেদী ঘরের সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। দেখো আমি তাই কি না।’
তনিমা উঠে দাঁড়িয়ে তার টুপি খুলে সোফায় রাখল, চুল থেকে কি একটা খুলে নিল। কালো প্রপাতের মতো চুলের স্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ল, সে চুলের, শুধু চুলেরই কী শোভা! মায়াপ্রপঞ্চময়। টুকটুকে ফর্সা। এরকম গোলাপি ইংরেজরা যাকে মিল্ক অ্যাণ্ড ক্রিম, বাঙালিরা যাকে দুধে-আলতা রঙ বলে এ জিনিস বনেদী আরব্য কি পারস্য ঘরানার মুসলমানী মেয়ে ছাড়া চট করে দেখা যায় না। কুচকুচে কালো চোখ, কালো ভ্রূ। ছোট্ট নাক। চিবুকটা যেন কাট্ গ্লাসের, নিখুঁত তার কাটিং, ছোট ছোট ঝিনুকের মতো আভাময় কান।
তনিমা বলল—‘হয়েছে?’
—‘কি হবে?
—‘দেখা হয়েছে আমি সুন্দরী কি না?’
—‘হয়েছে। তুমি পুতুলের মতো সুন্দর।’
—‘এটা কি একটা কমপ্লিমেন্ট হল?’
মেধা সতর্ক হয়ে গেছে, বলল—‘হল না?’
—‘কি জানি! ডল’স হাউজের অলুক্ষুণে অ্যাসোসিয়েশনটা পুতুল-টুতুল বললেই মনে এসে যায়। এনি ওয়ে আই টূ হ্যাভ ব্যাংগ্ড্ আ ডোর, দো ইট হ্যাজ ফেইলড্ টু রিজাউন্ড নাইক নোরা’জ। যাই হোক, এখানে এসে চমৎকার সাজানো সংসার পেয়ে গেলুম। সংসার করতেই আমি ভালোবাসুতুম। বি এটা পাশ করে কোনমতে বা্বাঃ বলে নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলুম। ম্যাগাজিন পড়ে পড়ে আর টি ভি দেখে দেখে শিখে নিলুম কত কিছু যা বাগবাজারের চক মিলোনা বাড়িতে কল্পনাও করতে পারতুম না। ফুল পাতা গাছ। পর্ক, বেকন, ক্র্যাব, লবস্টার, কত রকম, কত কিছু। ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি রূপবান গুণবান বরখানাকে। একবার এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। অনেকে আসবে। খুব সেজেছি, অলয় গাড়ি চালাচ্ছে আমি পাশে বসে। গাড়ি স্পীড নিয়েছে ভীষণ, আমার মনে হচ্ছে দুজনে মিলে আকাশে উড়ে যাচ্ছি। পেছন থেকে যমদূতের মতো ট্রাফিক সার্জেন্ট এসে ধরল। এ দেখাও, সে দেখাও, ট্রাফিক রুল ভেঙেছ, অমুক কোর্টে তমুক দিন জবাবদিহি করতে হবে। জানোই তো এখানকার ব্যাপার-স্যাপার। যমদূত চলে গেল। হঠাৎ আমার গালে একটা ঠাস করে চড় এসে পড়ল। অবাক হয়ে ফিরে দেখি অলয় লাল চোখে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। বলল—‘পেছনে সার্জেন্ট ধেয়ে আসছে, দেখোনি কেন? আমায় বলে নি কেন?’ চোখ দিয়ে ব্যথায় জল ঝরছে, আমি বললুম—‘এই জন্য তুমি আমায় মারলে?’
অলয় বলল—‘সী হোয়াট আই ডু নেক্সট্।’
আরেকটা ঘটনা। রবিবার। আমার শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। অলয়ও বিছানায় শুয়ে মুখে সিগারেট নিয়ে আয়েস করছে। বলল—‘চা নিয়ে এসো।’ আনতে যাচ্ছি, টেলিফোনটা বেজে উঠল, হঠাৎ পেছন থেকে আমার চুলে হ্যাঁচকা টান। অবাক হয়ে দেখি অলয় ডান পায়ের বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা দিয়ে আমার চুলের তলার দিকটা সাঁড়াশির মতো ধরেছে, মুখটা আমার আপনি উল্টে ওদিকে ফিরে গেছে। মুখের সিগারেট দাঁত দিয়ে চেপে বলল—‘টেলিফোনটা না ধরে কোথায় যাচ্ছো মহারাণী! হু ডু য়ু থিংক য়ু আর?’
আরও অনেক আছে। বলবার দরকার নেই। মনে হয় দুটোই যথেষ্ট। দেশেও অ্যাড দিয়েছে—ব্রিলিয়ান্ট ডিভোর্সী আমেরিকান গ্রীন কার্ড-হোল্ডার ওয়ান্ট্স্ সুটেব্ল্ ম্যাচ। রেস, কাস্ট, নো বার। ভালো মন্দ খেতে ভালোবাসে। রান্না বা গৃহস্থলীর কাজ করতে ঘেন্না করে। এখন তুমি ভেবে দেখো।’
তনিমা উঠে দাঁড়াল, চলে যাচ্ছে। মেধা বলল—‘দাঁড়াও দাঁড়াও, এ যে অদ্ভুত উপন্যাস শোনালে। এসব কথা তো গুজব হিসেবেও রটে। কাউকে তো কখনও বলতে শুনিনি।’
—‘কি করে বলবে? চড় মেরে যখন গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—‘আজ আর শেঠীর বাড়ি যাবো না। যদ্দিন না গালের দাগ মেলায় শপিং-এ পর্যন্ত বার হবে না।’ লোকের সামনে ডার্লিং-ডার্লিং করে আদিখ্যেতা করত তো সব সময়ে। ডিভোর্সের সময় অনেককে বলেছি। কেউ বিশ্বাস করে নি। তুমিও করতে না চাও করো না, মরো, আমি আমার কর্তব্য করে গেলুম। দু বছরের কনট্রাক্টে একটা কাজ করছিলুম, এপ্রিলে শেষ হয়ে যাবে। দেশে মা-বাবার কাছে ফিরে যাবো। আবার বিয়ে করবো। তবে আমেরিকায় আর আসছি না। আমার কাছে আমেরিকা ইজ ইকোয়াল টু অলয় মুখার্জি।
আই হেট দিস কানট্রি।’
মেধার আর অলয় মুখার্জিকে বিয়ে করা হল না। বেশ কিছুদিন ঘুরঘুর করেছিল ভদ্রলোক। কিন্তু দেখলেই তার হাতের দিকে চোখ চলে যেত মেধার। ধ্যাবড়া হাতটা। টকটকে লাল। আঙুলগুলো খুব ক্ষিপ্র মনে হয়। তনিমার গলায় কে যেন বলতে থাকত—‘আই হেট দিস কানট্রি, আই হেট দিস ম্যান।’
গ্যারাজ থেকে স্কুটারটা বার করলেন মেধা। মাথায় হেলমেট চাপিয়ে নিলেন। মৈথিলীর অনুষ্ঠান যখন তখন কাঁটায় কাঁটায় ছ’টায় আরম্ভ এখন পাঁচটা বেজে একত্রিশ মিনিট, যেতে হবে মধ্য কলকাতা। সময়মতো পৌঁছতে পারবেন তো?
অধ্যায় : ২
য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট। লম্বা চওড়া মেরুন রঙের ব্যানার। মেরুনের ওপর সোনালি। রঙগুলো খুঁজে বার করতে মেলা ঝামেলা হয়েছে। গড়পড়তা ডেকোরেটরের কাছে গড়পড়তা রঙই পাওয়া যায়। যেখানে সেখানে সেই একই জিনিস ঝোলে। অথচ বর্ণছায়ের সামান্য এদিক-ওদিক হলেই ফলাফল কত আলাদা! আমরা আলাদা কিছু বলতে চাই। এই সমাজ, এই সংসার, এই-ই জীবনযাপন তবু ঠিক এই নয়। কোথাও একটা আলাদা উদ্দেশ্য, আলাদা বক্তব্য আছে। রঙে সেটা প্রকাশ না হলে চলে? বাজার উজাড় করে ফেলেছে ওরা ঠিক পছন্দসই মেরুনের শেডের জন্য। সঠিক, বিশুদ্ধ সোনালির জন্য। তা সত্ত্বেও গুঞ্জনের পছন্দ হতে চায় না। সে বলে, ‘মেরুন-সোনালি একেবারে প্রিহিসটরিক কম্বিনেশন। তোরা প্লীজ আর কিছু খোঁজ।’ অতঃপর মেরুন-সাদা, নীল-সোনালি প্রস্তাব আসে। যতীনবাবু ডেকোরেটর অনেক দিনের অভিজ্ঞ লোক, তিনি হাত উল্টে বলেন—‘তোমরা চাও আমি করে দিচ্ছি। কিন্তু খুলবে না। দূর থেকে চোখে পড়া চাই তো!’ অতএব মেরুন-সোনালিই বহাল। গুঞ্জনের আপত্তি সত্ত্বেও। গুঞ্জনের গুঁইগাঁই অগ্রাহ্য করে। গুঞ্জন সিং-এর অবশ্য ব্যাপারই আলাদা। ও সন্ধেবেলায় ইনটিরিয়র ডেকোরেশনের কোর্স নিচ্ছে। ক্রোম ইয়লো, সের্যুলিয়ান ব্লু, সানসেট অরেঞ্জ এইসব ওর রঙের নাম। উইলিয়ম মরিস, চিপেনডেল এইসব বুকনি সে যখন তখনই ঝাড়ে। আরে বাবা ব্ল্যাক মানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে এমনি তো সব তোর হবু-ক্লায়েন্ট। টাকাটা তাদের খরচ করতে পারলেই ভালো। হাজার হাজার টাকা দিয়ে নটরাজ কিনবে, শঙ্খ কিনবে, গণেশ-টণেশ কিনবে। আর এ হল ছাত্রসঙেঘর ব্যাপার, ছাত্রদের হাতখরচের টাকা দিয়েই যা-কিছু সব। মৈথিলী বার বার বলেছে : ‘ফান্ডের অবস্থা আমাদের ভালোই। কিন্তু বাইরের জাঁকজমক করতে গিয়ে টাকাটা আমরা খরচ করছি না। আসল উদ্দেশ্যটার কথা কেউ এক মিনিটের জন্যেও ভুলিব না। সেখানে কমপ্রোমাইজ নয়।’
‘লোকোৎসব, চ্যারিটি শো, আয়োজক ছাত্রসংঘ।’ মাঝে মাঝেই লাউড স্পীকারে একটা গম্ভীর গলা ভেসে আসছে—‘আমরা সামগ্রিক উন্নয়ন চাই। শিক্ষা যদিও যে কোনও উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত, আমরা জানি আর্থিক উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষাও কতদূর ব্যর্থ হতে পারে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ এই তিনটে আমাদের প্রথম লক্ষ্য। আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য একটি অনুন্নত, সহায়হীন গ্রামকে এই তিন স্তরেই সমর্থ করে তোলা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কেওড়াখালি গ্রাম….’
ইনস্টিট্যুটের গেটের বাইরে জটলা করছিল পাঁচ ছ’জন ছেলে মেয়ে। শান্তনু বলল—‘কি দিচ্ছে রে উজান! জ্ঞানকুম্ভ উজাড় করে দিলে যে!’
সুমেরু শান্তনুর সাক্ষাৎ সহপাঠিনী এবং খুড়তুতো বোন। সে মন দিয়ে তার আইসক্যান্ডির শেষাংশটুকু চাটছিল। সবুজ জিভ বার করে বলল—‘তুইও তোর কুম্ভ উজাড় করে দে না। দে! কে তোকে বারণ করছে।’
‘মাইকের ধারে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না যে উজোটা! দেখলেই বলছে—‘শান্ত, প্লীজ তফাৎ যা।’
—‘তাই সেই থেকে ঝুট হ্যায় ঝুট হ্যায় স্লোগান দিচ্ছিস?’ পুলকেশ সিগারেটের ছাই টোকা দিয়ে ফেলে বেশ কায়দা করে দাঁড়িয়ে বলল।
সুমেরু মন্তব্য করল ‘ওকেও একটু মাইকটা ছাড়লে পারত। ফাটা কাঁসির আওয়াজও তো একটা বিশিষ্ট আওয়াজ! ফর এ চেঞ্জ ভালো লাগতে পারে।’
শান্তনু বললে- ‘যা যা বাজে বকিস না, আইস-ক্রিম আর কোল্ড ড্রিংক খেয়ে খেয়ে তো নিজের গলাকে ট্রাঙ্কে পুরেছিল। গান করতে বসিস গাধা ছুটে আসে।’
সুমেরু হারবার পাত্রী নয়। সে হেসে বলল- ‘তাই সেদিন যখন মারোয়া সাধছিলুম, তুই ছুটে এলি!’
পুলকেশ বলল—‘ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি। তোরা তোদের লাঠালাঠি থামাবি? আসলে কি জানিস শান্তনু, কেউ কেউ নিজের গলা শুনতে বড্ড ভালবাসে।’
শান্তনু বলল—‘ভবিষ্যতে তারাই অব্যর্থ পলিটিক্যাল লীডার এবং ব্যর্থ অভিনেতা হয়। উজোটার নেতা হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।’
—‘সে তো হতেই পারে, বাড়ির ট্রাডিশন ফলো করতেই পারে।’ পুলকেশ বলল।
—‘বাড়ির ট্রাডিশন ফলো করবে উজান আফতাব? তবেই তোরা খুব বুঝেছিস,’ সুমেরু কাঠির সঙ্গে লেগে-থাকা অংশগুলো চেটে পুটে নিতে নিতে বলল।
—‘তবে কি ও রেভেলিউশন করবে?’-পুলকেশ জিজ্ঞেস করল।
—‘ও রেভিলিউশনের এককাঠি বাড়া কিছু করবে।’ সুমেরু বলল, ‘না করে আমার নাক কান কেটে নিস।’
শান্তনু বলল—‘নাক কান দুটোই দিয়ে দিলি? ব্যালান্স রাখবি কি দিয়ে?’
শুভব্রত এই সময়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল—‘হ্যাঁরে, ক্লাসে তো সব ভালো ভালো পাত্তর দেখেই টিকিট-বই ধরিয়েছিলি। তো সিনিয়ার কেউ আসছে না কেন বল তো!’
ছাত্র সংঘের সদস্যরা স্থানীয় ও বৃহত্তর কলকাতার কলেজ ও যুনিভার্সিটিতে ছড়িয়ে আছে এটা সত্যি। যে যার শিক্ষায়তনে টিকিট বিক্রি করছে। গোটা গোটা টিকিট-বই বাইরেও বিক্রি হয়েছে। আশা ছিল অনেক অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিরা টিকিট কিনেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে গেট দিয়ে যারা দলে দলে ঢুকছে তাদের কেউই বাইশ পেরোয় নি। এরাই ঢুকছে প্রচুর, হই-হল্লা করতে করতে।
শান্তনুদের পাশ দিয়েই চার পাঁচ জন হাত ওপরে ছুড়ে হাসতে হাসতে ঢুকছে। একজন বলল—‘এই, টিকিট বিক্রির সময়ে যে বলল—‘ছাত্রমেলা, এ কেমন ছাত্রমেলা রে! তাহলে তো কলেজর কেলাসগুলোও ছাত্রমেলা!’
আরেকজন বলল—‘আহা হা হা, এটা ওদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বুঝছিস না? মেয়েলি গলায় জবাব হল—‘সেটা পরিষ্কার করে বললেই তো পারত! মেলা ইজ ফাইন, অল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানস আর বোর্স। গোড়ায় স্পীচ, মাঝে স্পীচ, শেষে স্পীচ। মালা ফালা পরানো। বোগাস।’
—‘যা বলেছিস। কিছু লেখা টেকাও তত নেই। ইংরেজিতে একেই বলে চিটিংবাজি।’
—‘জার্মানে কি কয় জানিস?—চীটাগং-।’
আরেক জন সরু গলায় বলল—‘এবং ফ্রেঞ্চে ইহাকেই বলিয়া থাকে সাঁজেলিজে।’
দলটা হাসতে হাসতে ঢুকে গেল।
শান্তনু বলল—‘দিস ইস হিউমিলিয়েটিং। ছাত্রমেলা-ফেলা কি বলছে রে?’
—‘ওসব থ্যাচার সাহেবার ব্রেনওয়েভ’ সুমেরু বলল—‘সারা বছর ধরে ছাত্রমেলা করবে, এই লোকোৎসব দিয়ে শুরু…প্রদর্শনী..সেমিনার..কর্মশালা..অল অন নিরক্ষরতা দূরীকরণ..এই সব সেদিন ক্যানটিনে এসে বলছিল না! ওর সেলসম্যানরা কেউ কেউ নিশ্চয় সে সব বুকনি তুলে নিয়ে ওদিকে নামিয়ে দিয়ে এসেছে।’
কোরা রংএর শাড়ির ওপর নীল গোলাপি ব্যাজ লাগিয়ে গুঞ্জন এদিকে আসছে দেখা গেল। হাতে এক গোছা ব্যাজ।
—‘এই তোমরা এখনও ব্যাজ পরো নি। শো তো শুরু হতে চলল।’
শান্তনু বলল—‘আমরা ভলান্টিয়ার নই। সুমেরু বা পুলকেশ হতে পারে। আমি নই।’
—‘কী তবে তুই? আর কোন কাজে লাগবি?’
—‘কেন? ঘোষক, পরিবেশক, প্রতিবেদক।’
—‘ওরে বাবা রে থামলি কেন? বলে যা.. প্রচারক, প্রসারক, প্রতারক…’ সুমেরু বলল—‘আমাকে একটা দিতে পারিস গুঞ্জন। বেশ স্মার্ট লুকিং রে তোর ব্যাজগুলো।’
গুঞ্জন ব্যাজের গোছাশুদ্ধ হাতটা শট করে সরিয়ে ফেলল—‘ও সব চলবে না। গজল্লা ছাড়ো। আইসক্রিমও ছাড়ো। ছেড়ে ভেতরে যাও, হলের সামনে লোক আছে। টর্চ নিয়ে ভেতরে যাও। নইলে পাচ্ছে না। স্পেশাল ডিজাইন, অর্ডার দিয়ে করিয়েছি ঠিকই। তাবলে এগুলো গয়না নয়।’
হলের ভেতর এই সময়ে আলো নিভতে শুরু করল। নিভন্ত আলোয় বোঝা যায় হল প্রায় ভর্তি। ব্যস্ত-সমস্ত কর্মীরা মাথা নিচু করে স্টেজের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। হলময় একটা মৃদু গুম গুম ধ্বনি। জমাটি আসরের লক্ষণ। এবং যেহেতু সবাই তরুণ-তরুণী, অনুষ্ঠান দেখা বা শোনার আগ্রহের চেয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ ও মত বিনিময়ের ইচ্ছেটা বেশি প্রবল।
সামনের সারিতে মউমিতা তার পাশে-বসা চিত্রলেখাকে বলল—‘এখনও দেখতে পাচ্ছিস না? ওই তো থার্ড রোয়ের ডান দিকের কোণে!’
মউমিতা ও চিত্রলেখা প্রতিবেশী। এক হাইরাইজে থাকে। কিন্তু দুজনের কলেজ, বিষয় সবই আলাদা। মউমিতার চিত্রলেখাকে ছাত্র সংঘের সদস্য করার ইচ্ছে। চিত্রলেখার কৌতূহল খুব। ছাত্র সংঘ গড়েছে কলকাতার কিছু নামকরা ছেলে মেয়ে যাদের অনেককেই ছাত্রমহলে এক ডাকে চেনে।
চিত্রলেখা বলল—‘কোন জন?’
—‘পেছন ফিরে কথা বলছে। ঘাড় ফেরালেই মুখটা পুরো দেখতে পাবি। চেক শার্ট।’
—‘ঢেউ খেলানো চুল মাথায়? শামলা?’
—‘উঃ। ওকে আমি চিনি না। ওর পাশে। বেশ ফর্সা। ঝাঁকড়া চুল। সেকেন্ড ফ্রম রাইট!’
—‘দাঁড়া দাঁড়া বুঝেছি। ও-ই দেবপ্রিয় চৌধুরী?
—‘ও-ই দেবপ্রিয় চৌধুরী। কৌতুহল মিটল তো? এবার নাচটা দেখতে দে।’
—‘আহা কি নাচ। বিহু নাচ, চালি নৃত্য একটা যা হোক বলে দিলেই তো লোকনৃত্য হয়ে যায় না! মেয়েগুলো তাদের এক সাথে পা ফেলাটাও প্র্যাাকটিস করেনি মনে হচ্ছে। স্টেজের এদিকটাই বেশি ইনটারেস্টিং।’
—‘বাবা, এরই মধ্যে এতো? তবু তো এখনও উজানকে দেখিস নি!’
—‘উজান! উজান কে!
—‘উজানকে আমরা টি. ডি. এইচ বলি নিজেদের মধ্যে। টল, ডার্ক, হ্যান্ডসম, মেয়েদের হার্ট থ্রব। তুই উজান আফতাবের নাম শুনিস নি?’
—‘শুনেছি শুনেছি মনে হচ্ছে! ক্রিকেট, না?’
—‘টেনিসও।’
—‘কোনটা রে উজান?’
—‘আগে দেবপ্রিয় চৌধুরীকে গলাধঃকরণ কর। কোন কাল থেকে নাম শুনছিস, আজই তো প্রথম চক্ষু সার্থক করলি?’
—আচ্ছা মউ, সত্যি সত্যি দেবপ্রিয় গাঁয়ের ছেলে!’
—‘সেন্ট পার্সেন্ট সত্যি। রেকর্ড মার্কস পেয়েছিল জানিস তো?’
—‘জানি বলেই তো বলছি, গ্রীন রেভোলিউশন না কি রে?’
—‘বলতে পারিস।’
—‘আলাপ করাবি তো আজ?’
—‘কথা দিতে পারছি না। ওকে ধরা মুশকিল।’
এই সময় রঙ্গশালায় দেবপ্রিয় পাশের ছেলেটিকে কি যেন বলে উঠে দাঁড়াল। পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে, মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে অন্যমনস্কভাবে সে চলে যাচ্ছে। সামনের চুলগুলো কপালের ওপর এলোমেলোভাবে এসে পড়েছে। যতটা লম্বা তার চেয়েও বেশি দেখায় দেবপ্রিয়কে। কারণ পাগুলো ওর বেশি লম্বা। হাঁটার ধরণটাও কেমন আলগা আলগা। বড় বড় পা ফেলে খুব কম সময়ের মধ্যে সে পার হয়ে গেল অডিটোরিয়ামটা। প্রথমটা স্টেজের আলো ছিটকে পড়েছিল তার মুখে। অল্পস্বল্প দাড়ির ওপর। খয়েরি চেক শার্টটার কাঁধের ওপর। তারপর তার মুখ অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে চলে গেল।
আসলে দেবপ্রিয়কে নিয়ে ছাত্রমহলে, বিশেষত ছাত্রীদের মধ্যে খুব কৌতূহল। ছেলেটি অতিমাত্রায় চুপচাপ। অহংকারী তো নয়ই। বিনয়ীও নয় আদৌ। কেউ বলে অজ পাড়া-গাঁ থেকে এসেছে। কেউ বলে মফঃস্বল শহর থেকে, কেউ আবার বলে ওর পরিবার ভিন্ন রাজ্যে থাকে, ও বরাবর বোর্ডিঙে মানুষ। এরকম কথাও প্রচলিত আছে যে অভিভাবক বলতে ওর কেউ নেই। দূর সম্পর্কের আত্মীয়-পরিবারে টিউটর হিসেবে থাকে। যেহেতু দেবপ্রিয় মিশুক নয়, কারও কোনরকম কৌতূহলকে তৃপ্ত করবার পাত্রই নয়, তাই কৌতুহল বেড়েই চলে। কিছু মেয়ে চটপট তার জন্য পাগল হতে থাকে। কিন্তু বেশিদিন এ অবস্থা থাকে না। কারণ দেবপ্রিয় না রাম না গঙ্গা। সে যেন নিজের ভেতরে কোথাও ডুব গেলে বসে আছে। আবহমান কাল থেকে সে যেন কোথাও থেকে অন্য কোথাও উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে যাচ্ছে। তার চোখ নেই পথের দুপাশে, মাথার ওপর আকাশে, অথবা চারপাশের বাতাবরণে কি ঘটছে দেখার। এই উদাসীনতা তার এক ধরণের আবরণ। এমন এক মোহ-আবরণ যা চট করে ছিন্ন হতে চায় না, কষ্ট দেয়। এই উদ্দেশ্যহীনতা তার আকর্ষণও। কারণ, আপাততঃ জগতে তো বটেই, এমন। কি এই ছাত্র-জগতেও এমন বিশেষ কেউ নেই, যে উদ্দেশ্যহীন, কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে হিসেব-পত্র করে এগোচ্ছে না। এত মন্থর, এতো আনমনা, অথচ এতো আত্মস্থ ঠিক কাউকে চোখে পড়ে না আজকাল। যদিও জানা যায় না দেবপ্রিয় সত্যি সত্যিই উদাসীন, লক্ষ্যহীন, না কি এটা শুধুই তার সম্পর্কে একটা ধারণা। তার চারপাশে সেই অজানারও আবরণ। অজানা মানেই রহস্য, রহস্য মানেই মোহ।
স্টেজের ওপর এখন ঘোষক। ঠিকঠাক বলতে গেলে ঘোষিকা। মাইক হাতে ভাঙা-ভাঙা মিষ্টি গলায় বলল—‘এইবার আরম্ভ হবে আমাদের আজকের আসল অনুষ্ঠান। নাচ সহযোগে বাউলগান। আপনারা শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় বা কেঁদুলিতে জয়দেবের মেলায় বাউল গান শুনেছেন। আমাদের বাউল-বন্ধুদের প্রথম বৈশিষ্ট্য এঁরা কেউই কোনদিন মাইক্রোফোনের সামনে, শহর বাজারের পরিবেশে গান করেন নি। এঁদের গানে পাবেন সহজিয়া শ্রেণীর সরলতা ও বিশুদ্ধতা। এঁদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য…’
মউমিতার সঙ্গিনী চিত্রলেখা বলল—‘কে রে মেয়েটা! জঘন্য দেখতে। মউমিতা একটু বিরক্ত হয়ে বলল—‘শুধু দেখিসনি। শোনও। ইচ্ছে হয় চোখ বুজে শোন। গলা, ডেলিভারি, থ্রো এগুলো শোনবার জিনিস।’
চিত্রলেখা বলল—‘তা অবশ্য। গলাটা সত্যি দারুণ!’
—‘স্বীকার করছিস তাহলে? এ হল মৈথিলী ত্রিপাঠী।’
—‘এ-ইতোদের মৈথিলী?’ চিত্রলেখা উত্তেজনায়, সোজা হয়ে বসল, ‘তোদের বিশ্ববিখ্যাত স্কুলের বিশ্ববিখ্যাত ফার্স্টনন্দিনী? যে এইচ-এস-এ স্ট্যান্ড করবে বলে তোদের হোল স্কুল বাজি ধরে হেরেছিল? এখন কি করছে রে?’
—‘ডাক্তারি পড়ছে। জয়েন্টে ফার্স্ট এসেছিল। জয়েন্টের রেজাল্ট নিয়ে তো আর হই-হই হয় না।’
—‘বাব বাঃ। কি করে পারে রে?’
মউমিতা বলল—‘কপাল!’
—‘সবই কপাল বলছিস?’
—‘কপালের ভেতরেও কিছু আছে ডেফিনিট।’
ঘোষণাটা শেষ হয়ে গেছে। মৈথিলী ত্রিপাঠী মাইক ছেড়ে বাঁ-উইঙ্স্-এর দিকে ঢুকে গেল। একটু পরেই দেখা গেল পাশের দরজা দিয়ে সে রঙ্গশালায় ঢুকছে। মৈথিলী বেশি লম্বা নয়। বেশ বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, মুখটা চওড়া। নাক একটু চ্যাপটা ধরনের, ফলে চেহারায় মধ্যে একটা চৌকো ভাব এসে গেছে। বেশ কালো রং কিন্তু খুব চকচকে। ঠোঁটদুটি বেশ স্কুল এবং ঢেউ খেলানো। তার চোখের মণি খয়েরি। একটু মোটা সংক্ষিপ্ত ভ্রু। চুল ঈষৎ লালচে। কপালের ওপর কয়েক গুচ্ছ, কানের লতির তলা থেকে ফণার মতো কিছু চুল বেরিয়ে আছে, বাকিটা পিঠের ওপর। মৈথিলী ব্যাগিজ ছাড়া কিছু পরে না।। ওপরের শার্টটা মেটে লাল, তাতে সাদা চক্র চক্র ছাপ। ছোট চাকা, বড় চাকা।
মউমিতা চাপা গলায় ডাকল—‘মৈথিলী, এখানে জায়গা আছে, বসবে?’ তার গলায় সম্ভ্রম, আগ্রহ। সে যে মৈথিলীকে একটা উঁচু বেদীর ওপর বসিয়ে রেখেছে সেটা তার প্রশ্নের ধরনেই স্পষ্ট।
মৈথিলী চট করে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, মুখে মৃদু অন্যমনস্ক হাসি। বলল—‘আমি মাঝের রোয়ে একটা জায়গা রাখতে বলেছি লুকুকে। মাঝখান থেকে দেখব, ডোন্ট মাইন্ড।’ বলতে বলতেই সে সামান্য নিচু হয়ে স্টেজের সামনেটা পার হয়ে গেল।
চিত্রলেখা বলল—‘ডাঁটিয়াল? না রে?’
মউমীতা বলল—‘ডাঁটিয়াল? কই না তো। মাঝখান থেকে দেখবে বলল শুনলি না! লোকগীতি নিয়ে মেতেছে এখন ওর কোনদিকে খেয়াল নেই। এই যে বাউল ছেলেগুলো গাইছে ওদের দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব ও নিয়েছে। নিজেই খুঁজে বার করেছে ওদের, ট্যাঁকে করে করে ঘুরছে চব্বিশ ঘণ্টা। রাম পাগল একটা।’
—‘তোর সঙ্গে আলাপ কেমন?’
—‘আছে। তবে ওদের গ্রুপ আলাদা, ওরা ছাত্রসংঘের একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বার। সমস্ত প্ল্যানিং, পলিসি মেকিং ওরা করে, আমরা সাধারণ সদস্য। চাঁদা দিই। প্ল্যান, পলিসির কথা শুনি। বাইরে থেকে কাজ করি। ওই যে লুকু শুনলি না? লুকু ওর ফাস্ট ফ্রেন্ড, স্কুল ডেজ থেকে। একেবারে ল্যাং বোট, লুকুটা স্লাইট ডাঁটিয়াল। মৈথিলী কিন্তু ভীষণ ভদ্র মেয়ে, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে আলাপ করে, ডেকে ডেকে, প্রথম যে ছাত্রসংঘের সভ্য হবে তাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সবার সঙ্গে বসতে হবে। রীতিমত ইনটারভিউ, কেন সদস্য হচ্ছে, কি আশা করে, দেশ সম্পর্কে ভাবে কি না, রাজনীতি করে কি না।’
‘ছাত্রসংঘের রাজনীতি কি রে? নিশ্চয়ই মার্কসিস্ট।’
‘একেবারেই না। কোনও দলীয় রাজনীতি করে এমন ছাত্র-ছাত্রীকে আমরা সদস্যই করি না। মৈথিলী বলে, যারা রাজনীতি করে তারা একভাবে চেষ্টা করছে, আশা করি দেশের জন্যই করছে। এ নিয়ে বেশি তর্ক-বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু ছাত্রসংঘ এদের সমান্তরালে চলবে। আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক। আমরা কি স্টাডি করি জানিস তো? পশ্চিমবঙ্গ-ভিত্তিক সোস্যাল সায়েন্স বলতে পারিস।’
‘দারুণ পার্সন্যালিটি, না?’
‘ওরে ব্বাবা দারুণ। নইলে এত বড় প্রতিষ্ঠান চালাতে পারে? একে আই এ এস এর মেয়ে তার ওপর লেখাপড়ায় ওইরকম। যতটা করা উচিত ততটা ভালো রেজাল্ট অবশ্য সেই এইচ এস থেকেই করছে না। করবেই বা কি করে? সারাক্ষণই তো কোনও না কোনও কাজ নিয়ে রয়েছে। চিন্তা কর মেডিক্যাল কলেজের সিলেবাস সামলে সারাক্ষণ ছাত্রসংঘ করছে। ওর সঙ্গে কাজ করতে কত বস্তিতে গেছি। সাক্ষরতা-অভিযানে যাবে আমাদের সবাইকে নিয়ে। মাসি, পিসি, চাচা করে এমন গল্প জুড়ে দেবে না! বর্ণ-লীডার রে মেয়েটা। ওই যে ওই দ্যাখ লুকু…’
‘কই?’
‘ওঃ তুই তালকানা আছিস। পেছন থেকে এগিয়ে আসছে, দ্যাখ না!’
—‘সাদা চুড়িদার, পিংক ওড়না?’
—‘হ্যাঁ।’
—‘ফ্যানটাসটিক দেখতে যে রে!’
—“ও তো স্কুল ডেজ থেকে মডলিং করছে টুথ পেস্টের, চা-এর।’
—‘তাই কেমন চেনা-চেনা লাগছিল।’
—‘এখন আর করে না অবশ্য। ওর যা পীয়ার গ্রুপ, তাল রাখতে হলে সীরিয়াস হতেই হবে। ও তো দেখছি মৈথিলীর জায়গা রাখে নি, নিজেই বসতে পাচ্ছে না বোধহয়। গেল কোথায় মৈথিলীটা।’
—‘তুই যে বললি ও মৈথিলীর ল্যাং-বোট!’
—‘শুধু আমি কেন! সবাই বলে।’
—‘বিউটি অ্যান্ড দা বীস্ট যে রে।’
—‘যা বলিস।’ মউমিতা কথা বাড়াতে চাইল না। স্পষ্টই বোঝা যায় যে মৈথিলী ত্রিপাঠীর গুণমুগ্ধ। চিত্রলেখার কথা শুনতে তার একটুও ভালো লাগছে না। মউমিতা ও চিত্রলেখা এবার মঞ্চের বাউল গানে মন দিল। ঘুরে ঘুরে নাচছিল যে ছেলেটি তার মুখটা খুবই কচি-কাঁচা, বয়স এদের থেকে কম বই বেশি হবে না। এখনও গোঁফ ওঠে নি। কোমল চামড়া। মঞ্চের পেছনের অংশে তার সঙ্গে কোনাকুনি দাঁড়িয়ে গাইছে আর একটি ছেলে। সে গানের বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিশিষ্ট বাউল ভঙ্গিতে পাক খাচ্ছিল। এ ছেলেটির বয়স সামান্য বেশি। মৈথিলী এর নাম ঘোষণা করে কেষ্টপদ দাস। সামনের ছেলেটি নিরুপাধিক পালান।
মৈথিলী জায়গা পায়নি। লুকুকে সে মোটে দেখতেই পায়নি। মঞ্চের ওপরকার ব্যবস্থা মৈথিলীর, সে তার গ্রামীণ অতিথিদের সাজ পোশাক, স্টেজে তাদের দাঁড়াবার জায়গা, আলোকসম্পাত ইত্যাদি নিয়ে গোড়া থেকেই ব্যস্ত আছে। লুকু খাওয়া-দাওয়ার দিকে। ইনস্টিট্যুটে এসেছিল দুজনে এক সঙ্গে। কিন্তু তারপর থেকে আর সম্পর্ক নেই। ভেবেছিল দুজনে বসে দেখবে এক সঙ্গে। অবশ্য একটা রুমাল ফেলে বা ব্যাগ রেখে ‘জায়গা রাখা’ তাদের কারোই পছন্দ নয়। এক যদি স্বেচ্ছাসেবকদের কাউকে বসিয়ে রাখা যেত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, লুকু এ ব্যবস্থাটা করতে সমর্থ হয়নি। কিছুক্ষণ জায়গা পাবার আশায় বৃথা ঘুরে, বিরক্ত হয়ে সে মঞ্চের দিকে যাচ্ছিল, উইংস-এর আড়াল থেকে একটা টুল পেতে বসে শুনবে, পালান হয়ত তাকে দেখলে উৎসাহিত হতে পারে। ছেলেটা কখনও এত লোককে গান শোনায়নি। তার ওপর সামনে মাইক যন্ত্র। ভিতু ভিতু চোখে তাকিয়ে বলেছিল, —“বাব্রে, কুয়োর মধ্যে এ যে দেখি অনেক নোক গো দিদি, মাইক যন্তরে গলা বসে যায় না তো।
এই সময়ে মৈথিলী রঙ্গশালার বাইরের করিডর দিয়ে প্রোফেসর মেধা ভাটনগরকে ঢুকতে দেখল। মৈথিলী তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে মিস ভাটনগর বললেন—‘মৈথিলী, আমি কিন্তু অনেকক্ষণ এসেছি। একদম পেছনে বসেছি। তোমাকে খুঁজতেই এদিকে এলাম।
মৈথিলী বলল—‘সে কি আপনি সামনের দিকে জায়গা পান নি? ভলান্টিয়াররা কি করছে?’
—‘শোনো, ওরা বলেছিল, প্রমিত সামনের সারিতে জায়গা করে দিতে চাইছিল। আমি ইচ্ছে করে সামনের দিকে আসিনি। কাউকে উঠিয়ে বসতে আমার একদম ভালো লাগে না। তাছাড়াও, তোমাদের মঞ্চটাই তো সব নয়, প্রেক্ষাগৃহটাও আমার দ্রষ্টব্য ছিল, আই ওয়ান্টেড টু সি দা এনটায়ার প্রজেক্ট ইন ইটস রাইট পার্সপেকটিভ। রূপাদের গ্রুপের নাচটা কিন্তু একদম লোকনৃত্য হয়নি। ওদের অনেক অভ্যেস করে তবে নাবা উচিত ছিল। বাউল গানটা তোমরা একদম খাঁটি জিনিস দিচ্ছো, লোকনৃত্যের বেলায় সিউডো ফোক ডান্স দিচ্ছো এটা ঠিক না। কসটিউম যদিও খুবই ভালো হয়েছে।’
মৈথিলী বলল—কসট্যুম গুঞ্জনের এলাকা। নাচের পরিকল্পনা রূপা নিজেই করেছে। মধুচ্ছন্দাদি তো এখন ট্রুপ নিয়ে উত্তরভারত ট্যুর করতে গেছেন। পরের বারে ওঁকে ধরব।’
—‘রূপা অবশ্য খুব খারাপ করে নি। কিন্তু টিকিট বিক্রি করেছে যখন, এর থেকে ভালো স্ট্যান্ডার্ড লোকে আশা করবে। যাই হোক পালান অসাধারণ। কেষ্ট দাসও ভালো। কিন্তু পালান একটা আবিষ্কার। এমন বাঁশের বাঁশির সুর অথচ এতো জোরালো আমি শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। তবে ও বড্ড বাচ্চা। ওর গলা পাল্টাবে।’
মেধা ভাটনগরের কথায় মৈথিলী মনে মনে খুব উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তার কিশোর-বন্ধু পালানের গলা সোনালি জরির সুতোর মতো, চকচকে, টানটান, ধারালো। একেক সময়ে যেন তারার সা ছুঁয়ে আসছে। কেষ্টপদ আর পালানের এই দ্বৈত সঙ্গীত তারই পরিকল্পনা। যে পটভূমিতে বাউলগান সবচেয়ে মানানসই, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানে নেই। মৈথিলীর মনে হয়েছিল তার কিছু একটা বিকল্প চাই। তাই এই দ্বৈত সঙ্গীত। পালানের চিকণ গলার সঙ্গে কেষ্টপদর ভারি খসখসে তসরের মতো গলার বুনোট সত্যি একটা অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নাচের পুরো এফেক্টটা সে দেখতে পাচ্ছে না। পালান প্রায় সর্বক্ষণই নেচে নেচে গাইছে, তার হাত পা মুখ সবই খুব কচি। ঠিক একটা সতেজ লাউডগার মতো তার নড়ন-চড়ন, খুব হালকা ফুরফুরে। কেষ্টপদ নাচছে তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে, খুব মাঝে মাঝে, এ যদি ডাইনে পাক দেয় তো ও দেয় বাঁদিকে।
মেধা বললেন, ‘আরও হাফ-ডজন বাউল ছেলেকে গানের অন্তরায় সঞ্চারীতে ঢুকিয়ে দিতে পারো এর পর। মুখটা পালান একা আরম্ভ করল, তারপর ধরো ওই ছেলেটি কেষ্টপদ, তারপর একে একে বাকিরা। তাতে তোমার ভিশুয়ালটা আরও জমবে।’
মৈথিলী বলল—‘আর কিন্তু যোগাড় করতে পারি নি, দিদি।’
—‘আহা পারো নি, এর পরে পারবে। পালানদের যদি ভালো পাবলিসিটি দিতে পারো তো ওরাই যোগাড় করে আনবে।’
মৈথিলী একটু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল, ‘এই অনুষ্ঠানটা কিম্বা বাউলদের পাবলিসিটি দেওয়া কিন্তু আমাদের সঙেঘর আসল উদ্দেশ্য নয় দিদি। আমাদের সব কথা এখনও আপনাকে বোঝানো হয় নি।’
মেধাদি আশ্চর্য হয়ে তাকালেন—‘তোমরা অবশ্য খুব বেশি কথা আমায় বলো নি, মৈথিলী। কিন্তু আমি যতদূর বুঝেছি তোমাদের প্রজেক্ট ঠিকঠাক চালাতে হলে এরকম অনুষ্ঠান আরও করতে হবে। তাছাড়া একটা গ্রামের উন্নয়ন যখন করছ, তখন সেটা করতে গিয়ে অন্যান্য যাদের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে তাদেরও অটোমেটিক্যালি কিছু না কিছু ফললাভ হবেই। উন্নয়নও হবে। কোনও কাজই স্বতন্ত্র, আইসোলেটেড নয়। নদী যখন পাহাড় থেকে নামছে তখন তাঁর লক্ষ্য সমুদ্র, কিন্তু পুরো অববাহিকাটা সে সবুজ করে দিয়ে যাচ্ছে। তোমরা একটা সচেতন, চিন্ময় নদী, তোমাদের অববাহিকা তোমরা কনশাসলি সবুজ, মরুহীন, সমৃদ্ধ করবে। উজান কোথায়?’
—‘উজান বাইরের মাইকটা কনট্রোল করছে, তাছাড়াও আরও অনেক কাজ। কি জানি কোথায়।’
—‘দেবপ্রিয়কে কোনও কাজ দাও নি? মনে হল ও বেরিয়ে গেল।’
—‘জানেন তো মেধাদি, ও পেছন থেকে অনেক কিছু করে দেয়, সামনে কিছুতেই আসবে না।’
মেধা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দেবপ্রিয়র এই কূর্মস্বভাব কিছুতেই কাটানো যাচ্ছে না। বললেন—‘যাক তোমাদের টাকা কেমন উঠেছে?’
—‘আমাদের ফাণ্ডের টাকা সামান্যই খরচ হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের জন্য সামান্য যেটুকু হয়েছে ইলেকট্রিসিটি, টিকিট-ছাপানো আর পালানদের দক্ষিণাবাবদ কিছু গিয়ে ব্যালান্স ভালোই আছে। আর শো থেকে মোট কত উঠল সেটা এখনও গোনা গাঁথা হয়নি। ওটা দেব করবে।’
—‘ঠিক আছে। আমি কিন্তু একটু পরেই চলে যাবো। আমার কাজ আছে জরুরি।
—‘গানগুলো পুরো শুনবেন না?’
—‘কিছুটা তো শুনবোই। শেষ অবধি থাকতে পারছি না। তুমি হিসেবপত্র সেরে কাল-পরশুর মধ্যে একবার এসো, তোমরা সকলেই এসো। নিরঞ্জনকেও আমি জানিয়ে রাখবো। ঠিক আছে তো?’
মেধা আর না দাঁড়িয়ে রঙ্গশালার দিকে চলে গেলেন।
লুকু অডিটোরিয়ামে ঢুকেছিল আগে একবার। জায়গা ছিল না, তাকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল, তাছাড়াও সে বড় অন্যমনস্ক ছিল, যেন কাউকে খুঁজছে, না পেয়ে হতাশ, বিভ্রান্ত বোধ করছে। এই সময়ে সে পেছন দিক থেকে এসে আরেকবার ঢুকল। মেধা তখন নিজের জায়গায় বসছেন। তাঁকে দেখেই লুকু চট করে বেরিয়ে গেল একেবারে বাইরের গেটের কাছে। সেখানে তখন প্রচুর ভলান্টিয়ার জড়ো হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরু হবার পর প্রথম আধঘণ্টা পর্যন্ত ভলান্টিয়ারদের খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। এখন সে ব্যস্ততা কমে এসেছে। অনেকেই হলের ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ-কেউ বা জায়গা পেয়ে বসে গান শুনছে। প্রমিত, বুল্টু, শুভব্রত, শান্তনু সবাই একে একে প্রমিতের লাইটারের সাহায্যে সিগারেট ধরাচ্ছিল গেটের কাছে। লুকুকে আসতে দেখে প্রমিত বলল—‘হয়ে গেল। কে জি বি আ গয়া।’
লুকু আঙুল তুলে চোখ পাকিয়ে বলল—‘দেখো কে জি বিই বলো আর পেন্টাগনই বলো তোমরা তোমাদের অ্যালটেড ডিউটি ঠিক মতো না করলেই হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করতে বাধ্য হবো। প্রমিত, তোমার ওপর খাওয়া-দাওয়ার ভার ছিল না? তুমি এখানে স্মোক করছো!’
প্রমিত বলল—‘একটু রেসপাইট দাও মাদমোয়াজেল। কতগুলো প্যাকেট বাঁধা যে সুপারভাইজ করেছি যদি জানতে! নইলে বাকি ভাণ্ডারাটার ভার না হয় ইয়োর হাইনেসেই নিলেন। শ্রীমান পালান এবং সম্প্রদায় ও বেলা যা টেনেছে, এ বেলায় আমি আর এগোতে সাহস পাচ্ছি না। ওই যে হাঁড়ি বাজায় যে ছেলেটা। উরি ত্তারা!’
বুল্টু বললে—‘খগেন। আচ্ছা এইটুকু একটা ছেলের নাম খগেন্দ্রনাথ। কোনও মানে হয়? এদিকে দেখবি বুড়ো জ্যাঠামশায়ের নাম হয়ত খোকা। পাকা চুল, পাকা গোঁফ, পাকা ব্রেন, খোকাবাবু আসছেন।’
শান্তনু বলল, ‘যা বলেছিস, তবে এ ছেলেটা যেরকম সাঁটাচ্ছে, তাতে খুব কুইক ও খগেন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে পারবে। মানিয়ে যাবে নামটা দেখিস।’
—‘কি মেনাস রে এ বেলা! এই লুকু! ওবেলা তো খিচুড়ি আর লাড়া ঢালালি।’ বুল্টু সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল।
প্রমিত বলল—‘লুচি, আলুর দম আর মোহন ভোগ। লুচি ডালদার। মোহনভোগে নাকি রিয়্যাল ঘি আছে। থ্যাচার সাহেবার নিজের করা মেনু। লুকু কি কাউকে খুঁজতে এদিকে এলে? এনিবডি ইন পার্টিকুলার?’
লুকু জবাব দিল না। সে সুমেরুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে।
বুল্টু বলল—‘এরকম পিকিউলিয়ার মেনু কোথেকে পায় রে?
প্রমিত বলল—‘মেনুর সম্বন্ধে তুই কি বুঝিস রে? থ্যাচারের বিশেষ হুকুম আছে ওদের সরল, গ্রামীণ জিহ্বা যেন কোনমতেই শহুরে জটিলতায় নষ্ট না হয়, মোহন ভোগ বাড়ি থেকে করিয়ে এনেছে।’
—‘বলিস কি রে? গ্র্যান্ড মা থ্যাচারের নিমন্ত্রিতদের স্টম্যাকের ক্যাপাসিটি সম্পর্কে কনসেপশন আছে তো? আমাদের বোধ হয় আর জুটবে না।’
লুকু বলল—‘ওদের ক্যাপাসিটি সম্পর্কে তুই না-ই ভাবলি বুল্টু। অয়েল ইয়োর ওন মেশিন। তাছাড়া মোহনভোগ তোদের জন্য নয়। এমনিতেই পচ্ছিস না। ওদের স্পেশাল।’
—‘কেন রে, ওরা কি বরযাত্রী নাকি?’
লাউড স্পিকারে উচ্চস্বরে পালানের গান শোনা যাচ্ছিল। একটু আগেই কেষ্টদাস একটা ভাটিয়ালি শেষ করেছে। পালানের এটা দ্বিতীয় গান।
প্রমিত বলল—‘শুনতে দে। শুনতে দে। বড় ভালো গাইছে রে ছেলেটা আহা হা হা।’
অধ্যায় : ৩
কলেজ স্কোয়্যারের দক্ষিণমুখী একটা বেঞ্চে বসেছিল দেবপ্রিয়। বসেছিল এমনভাবে যেন য়ুনিভার্সিটি ইনসটিট্যুটের উচ্চ-কণ্ঠ বাউল-আলাপ তার কানে যাচ্ছে না। বাঁ হাঁটুর ওপর ডান হাঁটুটা তুলে হাত দুটো আলগাভাবে বেঞ্চির পিঠে দুদিকে ছড়িয়ে সে বসেছিল বহু দূরের দিকে চেয়ে।
অনেকেই জানে না দেবপ্রিয় এই কাছেই হুগলি জেলার ছেলে। তার বাবা বলেন আদিতে তাদের পূর্বপুরুষ সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করতেন তারপর চতুর্ধুরিণ উপাধি নামে জমিদার হয়ে বসেন। বণিকদের সঙ্গে সদাসর্বদাই কিছু লেঠেল থাকত, তীরধনুক, বর্শা ছোট লাঠি বা পাবড়া সব চালাতেই তারা ওস্তাদ। জমিদার হওয়ার পরও এদের জমি দিয়ে বসত করাতে হয়, মাঝে মধ্যেই নানা ছলে ছুতোয় এদের ব্যবহার করা চলতেই থাকে। চতুর্ধুরিণদের একটি শাখা এতে বিরক্ত হয়ে কিছু দূরে শ্বশুরবাড়ির গ্রাম দায়পুরে বসবাস করতে থাকেন। বৈঁচি স্টেশনে নেমে ভেতর দিকে যেতে হয়। একটাই ত্রুটি গ্রামখানার। কোনও নদী নেই। নদী না থাকলে যেন কোনও জায়গার স্বয়ম্ভরত্ব থাকে না, তার আত্মপরিচয় স্ফুট হয় না। কিন্তু নদীর অভাব গত সাত আট বছর থেকেই পুষিয়ে যাচ্ছে পৃথ্বীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি নামে এক মানুষ নদী আসায়। কোন বিস্মৃত অতীতে পৃথ্বীন্দ্রনাথের ভিটে ছিল দায়পুরে। তাঁর ঠাকুর্দার বাবা ঠাকুর্দা নিশ্চয়ই জমিদার শ্রেণীরই ছিলেন। কিন্তু পুরুষানুক্রমে শহরে বাস করায় গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। বছরে একবার কি দুবার এসে জমির ফসল বিক্রির টাকাকড়ি বুঝে নেওয়া ছাড়া আসা যাওয়া ছিল না। জঙ্গল হয়ে যাওয়া বাগান এবং ভাঙাচোরা বাস্তুর মুখ চলতি নাম ছিল গাঙ্গুলি বাগান। দু তিনখানা বাগান, বিরাট দোতলা কোঠা বাড়ি এবং সংলগ্ন চাষ জমি নিয়ে বিশাল এলাকা। পৃথ্বীন্দ্রনাথ কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে একদিন একলা একলা গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। গাঙ্গুলি বাগান সাফ হতে থাকল, দোতলা কোঠার অধিকাংশ ফেলে দিয়ে বাকি সারিয়ে স্কুল হল, তাঁর নিজের জন্য টালি ছাওয়া বাংলো হল। জঙ্গল কেটে ডেয়ারি, পোলট্রি, বিরাট কিচেন গার্ডেন হল। স্কুলটি দিনে ছোটদের, সন্ধ্যায় বয়স্কদের। প্রথমে দায়পুরের লোক প্রবলভাবে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে এসব, বিশেষত পৃথ্বীন্দ্রনাথের এসে বসাটা। তাঁর তিনটি বাগানের গাছপালা ছিল গ্রামের বহু লোকের রুজির উপায়। কিন্তু তিনি এই সব লোকেদের দিয়েই তাঁর কাজকর্ম করাতে লাগলেন ভালো পারিশ্রমিক দিয়ে। দুটি স্কুলই এখন রমরম করে চলছে। এই পৃথ্বীন্দ্রনাথকেই দেবপ্রিয় গ্রাম সুবাদে মেজজেঠু বলে ডাকে, এবং তিনিই তার যাবতীয় উন্নতির মূলে। দেবপ্রিয়র বাবা গ্রামের বহুদিনের বাসিন্দা। জমিজমাও বেশ কিছু আছে, কিন্তু জ্ঞাতি-গুষ্টি এতো এবং গ্রাম পলিটিক্স এত সাংঘাতিক যে এই জমি জমার পুরো স্বত্ব ভোগ করতে পাওয়া এখন দেখা যাচ্ছে দুরাশা। পুকুরের মাছ রাতারাতি বেপাত্তা হয়ে যায়, ভাগের বাগানের ফলফুলুরি ঠিকঠাক পাওয়া যায় না। বড় বড় গাছ লোপাট হয়ে যায়। বাবার ইচ্ছে দেবপ্রিয় আইন পড়ুক। সদরে প্র্যাকটিস করতেও পারবে, নিজেদের সম্পত্তি উদ্ধারের কাজটাও করবে।
মেজজেঠু সরকারি চাকরি করতেন। ঠিক কি চাকরি দেবপ্রিয় জানে না, খুব বড় চাকরি এই পর্যন্ত সবাই জানে। তবে খুব সিগার খান, এই বয়সেও বুশ শার্ট আর প্যান্ট ছাড়া পরেন না। রাত্রে স্লিপিং স্যুট পরে শোন। মানুষটির হাবেভাবে কিছু সাহেবি ব্যাপার আছে। শৃঙ্খলাবোধটাও হয়তো তারই অন্তর্গত। কিন্তু কথাবার্তায় এবং গ্রামের সবার প্রতি দরদে তিনি খাঁটি এদেশি।
মেজজেঠুই তার দেবব্রত নামটাকে দেবপ্রিয় বানালেন। যত্ন করে পড়ালেন। তার মধ্যে ইংরেজি, ভূগোল, ইতিহাস পড়ালেন যেন তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে। জেলা স্কুলে দেবপ্রিয় আগে ভালোই রেজাল্ট করত। সে জানে গ্র্যাজুয়েশনটা করেই তাকে কোর্টে ছুটতে হবে। মেজজেঠু তার মধ্যে অন্য আগ্রহ জাগালেন। সে যখন মাধ্যমিকে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেল মেজজেই তার সম্মানে একটা ছোট্ট ভোজ দিলেন। ভোজে নিমন্ত্রিত মাত্র দুজন—তিনি স্বয়ং আর দেবপ্রিয়। বললেন ‘তুই পাশ করলেই এ ভোজটা হত। এটা শুধু পাশের ভোজ, স্কলারশিপ পাওয়ার ভোজ নয়। এতে প্রমাণ হয় না তুই হৃদয়বান মানুষ কিনা, তোর স্বকীয়তা আছে কি না, তোর নেতৃত্ব গুণ, উদ্ভাবকের মেজাজ আছে কি না, আত্মপ্রত্যয় কতটা, সহনশক্তি, টলারেন্স কতটা, কল্পনা আছে কি না। কিছুই বোঝা যায় না। শুধু বোঝা যায় তোর স্মৃতিশক্তিটা ভালো। হয়ত তোর চেয়ে অনেক খারাপ করেছে এমন একটি ছাত্র বা ছাত্রীর এসব গুণ তোর চেয়ে অনেক বেশি। কিছু বলা যায় না। সুতরাং তুই পাশ করেছিস ভালোভাবে পড়াশোনা করে এটাই যথেষ্ট।
মেজজেঠু খাওয়ালেন তাঁর নিজের ক্ষেতের দুধের সর চালের ভাত, ঢেঁকি-ছাঁটা। হাত রুটি, কয়েকরকম সবজি সেদ্ধ তার ওপর দুরকম সস ঢেলে, নিজের পোলট্রির লেগহর্ন মুরগীর ডিমের ডালনা। নিজের ডেয়ারির ছানা ও দুধ দিয়ে ছানার পায়েস। প্রত্যেকটি নিজের হাতে করা। জেঠিমা মারা যাবার পর থেকেই জেঠু নিজের হাতে রাঁধতে অভ্যস্ত। তাঁর ভেতরে বোধহয় একটা চাপা অভিমানও যে তাঁর একমাত্র ছেলে মার্কিন নাগরিকত্ব নিয়েছে।
খাওয়ার শেষে হাতমুখ ধুয়ে অনেকক্ষণ দাবা খেলা হল। তারপর জেঠু আসল কথাটা বললেন। তাঁর আশা তাঁর এই স্কুল কলেজ হবে, সব থাকবে এক ক্যাম্পাসের ভেতর। কলেজের নিজস্ব ক্ষেত, খামার, বাগান, পোলট্রি, ডেয়ারি থাকবে বলে এই স্কুল-কলেজ অনেকটাই স্ব-নির্ভর হবে। সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হবে না বলে নিজেদের পাঠ্য তালিকা ও পরীক্ষা-পদ্ধতি তৈরি করার স্বাধীনতা থাকবে। এই প্রতিষ্ঠানের ভার দেবপ্রিয়কে নিতে হবে। খুব আনন্দের সঙ্গে এ প্রস্তাবে তখনই রাজি হয়েছিল দেবপ্রিয়। মেজজেঠু বলেন— ‘বহুদিন ধরে গ্রাম থেকে শহরের দিকে একটা বর্হিযাত্রা শুরু হয়েছে। ফলে গ্রাম শুধু দরিদ্র নয়, দীন হয়ে পড়ছে, প্রতিভাবাদীন, কল্পনাদীন। এই ব্যবস্থা পাল্টানো দরকার। গ্রামকে করতে হবে এতো শান্তিময়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ, অথচ জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধাসম্পন্ন যে শহরের লোক ক্রমে গ্রামের দিকে মুখ ফেরাবে।’
উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম হয়ে তার হয়ে গেল মহা মুশকিলে। মেজ জেঠু বা তার পরিবারের কেউ তো ভাবেনই নি, সে স্বয়ংও ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে জেলাস্কুলের ফার্স্ট বয় উচ্চ মাধ্যমিকে রেকর্ড মার্কস পেয়ে প্রথম হবে। লক্ষ্য বদলে গেল। দেবপ্রিয়র নিজেরই ইচ্ছে হল সে ডাক্তারি পড়বে। পঞ্চায়েত প্রধান হাবু জ্যাঠা এবং গ্রামের অন্য পাঁচজন মাতব্বর ব্যক্তিও তাকে জয়েন্টের ফলাফল অনুযায়ী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার জন্য চাপাচাপি করতে লাগলেন। মেজ জেঠুকে একটু চিন্তিত দেখাল। কিন্তু তিনিও পরে বললেন ‘গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসঙ্কট ও শিক্ষাসঙ্কট—কোনটা যে বেশি ভয়াবহ ঠিক করা মুশকিল।’ তাঁর আগের পরিকল্পনাটাকে তিনি সামান্য পাল্টালেন। দায়পুর গ্রামে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলেও চলবে। বরং স্কুলের সঙ্গে একটি বৃত্তিমূলক কলেজ থাক। সেই সঙ্গে থাক স্বাস্থ্যকেন্দ্র যা ক্রমে একটি বড় আধুনিক হাসপাতালে পরিণত হবে। কলকাতা এবং আশপাশের হাসপাতালগুলোয় এই চূড়ান্ত অরাজকতা ও অব্যবস্থার দিনে জেলায় জেলায় উন্নত মানের হাসপাতাল গড়ে ওঠা আশু প্রয়োজন। দেবপ্রিয় নিজেকে এই হাসপাতালের কর্ণধার হিসেবেই তৈরি করুক। মেজ জেঠুর চিন্তাধারার মধ্যে না আছে কোনও গোঁড়ামি, না আছে অহমিকা, তিনি এইভাবে নিজের আশাকে দেবপ্রিয়র আশার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন।
দেবপ্রিয় সেই থেকে কলকাতায় পড়াশোনা করছে। মামার বন্ধুর বাড়িতে থাকে সে পেয়িং গেস্ট হিসেবে। একতলায় তার নিজস্ব একটি ঘর আছে, দালান পার হয়ে বাথরুম। বাকি বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না রাখলেও চলে। গোয়াবাগান অঞ্চলের বহু-শরিকি বাড়ি। এক বৃদ্ধ শরিক তাঁর নিজের অংশের একটি ঘর তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। দেবপ্রিয়র উচ্চাশার রকম সকম এখন ক্রমশই পাল্টে যাচ্ছে। তার মা বাবার আশা ছেলে তাঁদের বিষয় রক্ষা করবে, মেজ জেঠুর আশা সে তাঁর সমাজকল্যাণকেন্দ্রের অধ্যক্ষ হবে, তার প্রোফেসররা ইতিমধ্যেই মনে করতে শুরু করেছেন তার বিদেশ চলে যাওয়া ভালো। এদেশে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। দেবপ্রিয় অন্ধকারে পথ খুঁজছে। তার নিজের ধরনে। এই অন্ধকার বহু তরুণ-তরুণীর মধ্যে ভয়াবহ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য এক প্রতিযোগিতার অন্ধকার। ছাত্রের উচ্চাশার সঙ্গে সমাজের উচ্চাশার প্রচণ্ড ফারাকের অন্ধকার। দেবপ্রিয় এই ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। সে কিছু করবে কিন্তু তা তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের আশা পূর্ণ নাও করতে পারে। দেবপ্রিয় এখনও জানে না সে ঠিক কি করবে। ইতিমধ্যে তার ভালো লাগে সহপাঠী সহপাঠিনীদের প্রাণ-চাঞ্চল্য, কলকাতার নানারকম সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ, ভালো লাগে কলম ছোঁওয়াতেই শ্রেষ্ঠ উত্তরের মর্যাদা পাওয়া, মানবদেহের অন্ধিসন্ধির বিস্ময়, ভালো লাগে কোনও কোনও অধ্যাপকের সস্নেহ মনোযোগ, কারুর প্রতিভার পরিমণ্ডল, মামার বন্ধুর বাড়ির মামা-মামীদের উঁকিঝুঁকি স্নেহ-কৌতূহল। অথচ, এই সমস্ত ভালো লাগার অন্তরালে নির্ভুলভাবে কাজ করে যায় এক নাম না জানা বিষাদ। কেন, কি বৃত্তান্ত তা যেন দেবপ্রিয় জানে অথচ পুরোপুরি জানে না।
লোকগীতির অনুষ্ঠানের শেষে শান্তনু, বুল্টু, প্রমিত সবাই কলেজ স্কোয়্যারের মধ্য দিয়ে শর্ট কাট করছিল। তারা দেবপ্রিয়কে ওই ভাবেই বসে থাকতে দেখে।
—‘কি রে, এখানে?’ শান্তনু বলল।
—‘এমনি!’
—‘এমনি মানে? গান শুনিস নি। থ্যাচারের থাপ্পড় খাবার ইচ্ছে হয়েছে?’
দেবপ্রিয় বলল—‘শুনেছি। অফ অ্যান্ড অন। ঘরের মধ্যে বেশিক্ষণ আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। জানোই তো গ্রামের ছেলে।
—‘পালানকে তো তুই-ই যোগাড় করে দিলি। কিরকম পার্ফর্ম্যান্স দ্যায় দেখলি না! দারুণ গেয়েছে কিন্তু। হাঁড়ি বাজানো ছেলেটা কি যেন নাম? খগেন না? দুর্দান্ত।’
—‘জানি। ইনস্টিট্যুটে আর কি শুনলে? খোলামেলায় আরও ভাললা খুলত। আমি তো বলেই ছিলুম প্রেসিডেন্সির মাঠে শুদ্ধু একটা তক্তা পেতে হোক।’
—‘ও, তাই রাগ হয়েছে? রীগনস অবজেকশন ওভাররুল্ড্ বাই থ্যাচার? চলি। দেবপ্রিয় বাড়ি যাবি না।’
—‘তোমরা যাও। আমার তো এখান থেকে দু পা। আর শোনো, ওসব রাগটাগের কোনও ব্যাপার নেই।’
শান্তনু বলল—‘আহা হা হা, পার্সন্যালিটি থাকলেই পার্সন্যালিটি ক্ল্যাশ হবে। আমাদের নেই তাই হয় না।’
প্রমিত, বুল্টু, পুলকেশ আগেই এগিয়ে গিয়েছিল। শান্তনুও এবার পা বাড়াল। দেবপ্রিয় গলা তুলে জিজ্ঞেস করল—‘উজান যায়নি?’
—‘উজান? উজান এখনও পালান অ্যান্ড কোং-এর সুবন্দোবস্তর কাজে ব্যস্ত।’ ম্যাডামের আদেশ। লুকুও আছে। আরও দু এক জন তোদের নর্থের দিকের রয়েছে।’
দেবপ্রিয় কেন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। প্রমিতরা চলে যাবার পরও সে একই ভাবে বসে রইল। ঘণ্টাখানেক পরে, অর্থাৎ রাত প্রায় সোয়া নটায় উজান, মৈথিলী এবং লুকু যখন ওই একই জায়গা দিয়ে কলেজ স্ট্রিট যাবার জন্য শর্ট কাট করে তখনও তাকে বসে থাকতে দেখে। উজান বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে চটপটে। একে সে খেলোয়াড়, তার ওপরে আজকাল যোগাসন ধরেছে। স্পোর্টস শার্ট আর জিন্স পরে আছে। রঙ কালো। নাক চোখ মুখ খুব কাটা-কাটা, সমস্ত মুখটাই খুব সচল, সপ্রতিভ, তীক্ষ্ণ এবং মিষ্টি। উজান চলে প্রায় সব সময়েই কুইক মার্চের ভঙ্গিতে। সে আগে আগে আসছিল প্রায় লাফাতে লাফাতে, শূন্যে বল ছোঁড়ার ভঙ্গি করতে করতে মাঝে মাঝে। লুকু একবার বলল ‘উজান, কবে রণ্জিতে ফোর্টিন্থ্ সিলেক্টেড হয়েছিলি ভুলতে পারছিস না, না?’
উজান বলল—‘হাত পাগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি।
মৈথিলী আর লুকু একটু পেছিয়ে পড়েছে। দুজনেই নিজেদের কথায় মগ্ন। মৈথিলী বলছিল ‘তুই প্রবলেমটা ধরতে পেরেছিস? কেষ্ট চায় পাবলিসিটি। ও আমাকে ওর পাবলিসিটি ম্যানেজার বানাতে চাইছে। পালান কিন্তু অতশত বোঝে না।’
লক্ষ্মীশ্রী বলল—‘বোঝে না তুই বুঝলি কি করে?’
—‘বাঃ, সমানে কদিন ওদের সঙ্গে ঘুরছি, এটুকু বুঝব না? পালানটাকে ও আলটিমেটলি ঠকাবে।’
উজান থেমে গিয়েছিল, ওদের শেষ কথাটা কানে যেতে হেসে বলল —‘তুই যে বলছিলি ওরা সহজ সরল। তুই-ই বোধহয় শহরে নিয়ে এসে ওদের মায়ামৃগ দেখালি তাহলে?’
মৈথিলীকে চিন্তিত দেখাল। সে বলল—‘ওরা গান করুক, পয়সা রোজগার করুক এটা আমিও চাই। সেই সঙ্গে ওদের সরলতটাও টিকে থাকুক! এই চাওয়ায় কি খুব অসঙ্গতি আছে?’
—‘আছে বই কি’ উজান বলল, ‘সেটা তুই নিজেই এখন বুঝতে পারছিস।’
—‘আচ্ছা উজান, সরলতা আর বোকামি কি এক? ইজ্নট্ সিম্পলিসিটি আ ভার্চু?
এই সময়ে দেবপ্রিয়কে ওদের চোখে পরল। উজান বলে উঠল—‘আরে দেব, তুই এখনও রয়েছিস?’
—‘হুঁ।’
‘লুকু বলল— ‘মৈথিল, তোর প্রশ্নের উত্তর কিন্তু সামনে বসে রয়েছে। দেব সরল, কিন্তু দেবকে কি কেউ বোকা বলবে?’
উজান আশ্চর্য হয়ে বলল—‘দেব সরল? লুকু তুই দেবকে সরল বললি কি হিসেবে? মৈথিলী তোর মত কি? দেব কি সরল?’
লুকু বলল—‘ওর চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায় ও কত ইনোসেন্ট।’
মৈথিলী বলল—‘তুই ভুল করছিস লুকু, সরল না হলেও কিন্তু নিস্পাপ হওয়া আটকায় না।’
উজান বলল—‘কি জানি, আই থিংক দেব ইজ আ ভেরি কমপ্লেক্স ক্যারেক্টার। দেব, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড।’
দেব উঠে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ বসে বসে তার কোমর ধরে গেছে। এই সমস্ত কথাবার্তায় যোগ দেবার মেজাজ তার নেই। ভেতরে ভেতরে সে যেন প্রতীক্ষা ক্লান্ত। আড়মোড়া ভাঙ্গার ভঙ্গিতে দু হাত ছড়িয়ে সে শুধু বলল—‘আই ডোন্ট মাইন্ড।’
—‘যাবি না?’ উজান বলল।
—‘যাবো।’
ওদের সঙ্গে লম্বা লম্বা শিথিল পায়ে হাঁটতে লাগল দেবপ্রিয়। ওরা তিনজনে একই বাসে উঠবে, তিনজনেই দক্ষিণে থাকে। দক্ষিণের নানান বিন্দুতে, কিন্তু গড়িয়াহাট যাবার বাস পেয়ে তিনজনেই উঠে পড়ল। উজান দাঁড়িয়ে ছিল। মৈথিলী জানলার পাশে, লুকু খুব সম্ভব উল্টো দিকে জায়গা পেয়েছে। দেবপ্রিয় হাঁটছে। খুব মন্থর গতিতে। গোলদিঘির ঘুরন গেটের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল যেন ভেতরে যাবে না বাইরে থাকবে স্থির করতে পারছে না। একটি চেনা ফুচকাঅলা তার জিনিসপত্র গুটিয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। বই পাড়া বহুক্ষণ বন্ধ। দেবপ্রিয় খুব সন্তর্পণে এক প্যাকেট সিগারেট বার করল, অনভ্যস্ত শ্লথ কাঁপা কাঁপা আঙুলে সে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেই বাসস্টপের দিকেই ফিরে গেল। তার সিগারেটের ধোঁয়া এলোমেলোভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।
অধ্যায় : ৪
স্কুটারটাকে গ্যারাজে তুলে গেটের তালা খুলতে খুলতেই মেধা শুনতে পেলেন ভেতরে টেলিফোনটা বাজছে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হয়ে তিনি গিয়েছিলেন সংস্কৃত বিভাগের নন্দিতার বাড়ি। নন্দিতার কাছে কিছু প্রাচীন পুঁথি এসেছে। অনুবাদ করছে ও। মেধাদির কাছে সাহায্য চেয়েছিল। মেধার নিজেরও উপকার। এইসব পুঁথি প্রাচীন ভারতের নানান সময়ের সমাজ-ব্যবস্থা, প্রশাসন, অভিজাতদের জীবন-যাপন, অর্থনীতি, ইত্যাদির ওপর অনেক সময়েই তির্যক আলো ফেলে। গভীর রাত্রে রাত্রির সঙ্গে রঙ-মেলানো বসন পরে অভিসারিকারা পথে বার হত। খুবই পারমিসিভ সোসাইটি সন্দেহ নেই, কিন্তু মেয়েগুলো অক্ষত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসত। মেয়েদের ওপর যখন-তখন অত্যাচার, হালের ভারতবর্ষে যা হচ্ছে, তার বিন্দুমাত্রও যে তখন ছিল না, অভিসারিকা-সিসটেমটা তো তারই প্রমাণ? সেটা কি শাসকের গুণে না সামাজিক শিক্ষার গুণে? এই যে বারাঙ্গনা শ্রেণী যাঁরা চৌষট্টি কলায় শিক্ষিত হতেন, যাঁদের গৃহে নগরের বিদগ্ধ ব্যক্তিরাও এসে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতেন তাঁরা কি জাপানের গেইশাদের সঙ্গে তুলনীয়? না প্যারিসে যাঁরা সালোঁ বসাতেন শিল্পী-সাহিত্যিক এদের খাতির করে তাঁদের মতো? ব্যাপারটা প্রিমিটিভ না অতি-আধুনিক?
সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠে মাঝের ল্যান্ডিংটা বড় মাপের। বিরাট পেতলের আধারে একটা রবার গাছ। বাবার জিনিস। তারই কোলে আবলুশ কাঠের ছোট্ট স্ট্যান্ডে টেলিফোনটা বাজছে। ধরতে ধরতেই রিংটা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলেন মেধা। কিন্তু ফোনটা আর বাজল না। অগত্যা ওপরে উঠে কোল্যাপসিব্লের তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন, আলো জ্বাললেন, ব্যাগটা টেবিলের ওপর নামিয়েছেন এমন সময়ে টেলিফোনটা আবার বাজল। এক রকম দৌড়ে গিয়েই ধরলেন মেধা। বহুদূর থেকে ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে আসছে ‘ম্যাডাম। ম্যাডাম আপনার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে, আমায় একটু সময় দেবেন?’
—‘তুমি কে সেটা আগে বলবে তো!’ মেধা বললেন।
—“আমি…’ ফোনটা আবার কেটে গেল।
মেধা বিরক্ত, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইচ্ছে করে কলকাতার প্রত্যেকটি টেলিফোন-যন্ত্রকে গুলি করে মেরে ফেলতে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও আর রিং হল না। লাইন পাওয়া একেই কঠিন। ক্ষীণস্বর শুনেই বোঝা যায় ঠিকমতো কাজও করছে না। ফিরে আসতে আসতে মেধা ভাবতে লাগলেন কে হতে পারে? ম্যাডাম বলে তাঁকে কে কে ডাকে? ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে বলে এম. ভি। প্রয়োজন হলে মেধাদি বলে। ঘরে এসে শাড়ি বদলাতে বদলাতে তাঁর মনে হল এ নিশ্চয়ই ছাত্রসঙেঘর কেউ। ছাত্রসঙ্ঘ ব্যাপারটা মৈথিলীর উদ্ভাবন না মেধার বলা শক্ত। মেধা যখন বস্টন থেকে ফিরে এলেন, তখন শিক্ষাজগতের আবহাওয়ায় একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখলেন। চিত্রটা খুব হতাশাজনক। ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর থেকে সততা ও নীতির চাপটা একেবারে উঠে গেছে। তারা বিশৃঙ্খল, অরাজক। ক্লাসে অসম্ভব হল্লা করে সুবিধে পেলেই। আরও ভয়াবহ চিত্র অধ্যাপক মহলের। তাঁদের বেশির ভাগই কোনও না কোনও দলীয় রাজনীতি করেন। এবং পড়ানোর সময়ে সুকৌশলে সেই রাজনীতি বক্তৃতায় ঢুকিয়ে দ্যান। এর ওপর, তাঁদের ক্লাশে যাওয়াটাই একটা ব্যতিক্রম। অল্পবয়স্করা সব থিসিস, পেপার, এম. ফিল করতে ব্যস্ত। নাহলে তাঁদের ইনক্রিমেন্ট হবে না। কয়েকজন আন্তরিক স্বভাবের মানুষ আছেন। ছাত্রদরদী না হন, যে কাজের জন্য নিযুক্ত আছেন সেটা যথাসাধ্য ভালোভাবে করা দরকার এটা তাঁরা মনে করেন। অধ্যাপকদের মধ্যে এই শৈথিল্য যে আগেও ছিল না, তা নয়। কিন্তু এঁরা ছিলেন মুষ্টিমেয়। এঁদের নাম-ডাক, প্রশাসনিক কাজকর্মের দায়, অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ এঁদের দুর্ভেদ্য করে রাখত। সরকারি কলেজে ছাত্রদরদ জিনিসটা চিরকালই কম। বদলি এবং প্রোমোশন এই দুটো জিনিসই সাধারণত সেখানে বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কিন্তু যান্ত্রিক ভাবে হলেও পঠন পাঠনের কাজটা চলত। এবার এসে মেধা দেখলেন বেশিরভাগ অধ্যাপকই ক্লাসে যাচ্ছেন না, বা গেলেও ফিরে আসছেন। কারণ ক্লাসে ছাত্র নেই। ছাত্রদের মধ্যে নাকি একটা নতুন কথা চালু হয়েছে পাস-কোর্সের ক্লাস গাধারাই করে। হঠাৎ এই প্রজন্মের ছাত্ররা কি করে এতো স্বাবলম্বী হয়ে গেল মেধা ভেবে পেলেন না। পরে দেখলেন তারা আদৌ স্বাবলম্বী নয়, প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য তারা কোচিং ক্লাসে যায়, সেখানে তৈরি নোট পায়, পরীক্ষাটা ছাত্রদের হয় না, হয় অধ্যাপক-টিউটরদের। আরও অনেক জিনিস তাঁর দৃষ্টিগোচর হল, খাতা দেখার সময়ে কলেজ এবং এলাকা ধরে ধরে বাছ-বিচার হয়। এবং কোচিং ক্লাসগুলোর সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফলের কোথাও একটা সূক্ষ্ম অসাধু যোগাযোগ আছে। মেধা তাঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে জানেন সোজাসুজি প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহ বিশেষত : তিনি একলা করে কিছু করতে পারবেন না। সৎ এবং আন্তরিক ছাত্রও আছে অধ্যাপকও আছেন, কিন্তু তাদেরও একটা বড় অংশ ভীরু, অনেকে পরিকাঠামোর এই শৈথিল্যের সুযোগ নেন। যদিও নিজেরা সোজাসুজি অসৎ নন। এই অন্যায়ের প্রতিকারের ভাব ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। কারণ সাধারণ ছাত্রসমাজ মুণ্ডহীন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-দানবের মতো। তারা যত সহজে ভাঙতে পারে তত সহজে গড়তে পারে না, বিধ্বংসী তাদের প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তিকে খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলছে কেউ এদের যথাযথ ব্যবহার করেননি। স্বাধীনতা-পূর্ব দিনগুলি থেকে নকশাল আন্দোলন পর্যন্ত এই বিপুল প্রাণশক্তি আত্মধ্বংসী বন্যার কাজে ব্যবহার হয়েছে, যে বন্যা কোনও পলির প্রলেপ রেখে যায় না, রেখে যায় শুধু ধূ-ধূ বালির উষর চড়া।
মনের অবস্থা যখন ভীষণ অশান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, মেধা সরকারি কলেজ ত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন সেই সময়ে একদিন তাঁর মেজদার বন্ধু রঘুনন্দন ত্রিপাঠীর মেয়ে মৈথিলী তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে আসে। মৈথিলী মেয়েটি অত্যন্ত গুণী, চৌখস, ইচ্ছে করলেই সে দেশে কিম্বা বিদেশে অনেক উঁচুতে উঠতে পারবে। পরিবারও প্রভাবশালী। কিন্তু মৈথিলী খুব আন্তরিকভাবে তাঁকে জানাল যে ছাত্রদের নিয়ে সে এবং তার কয়েকজন বন্ধু একটা প্রতিষ্ঠান গড়তে চায়। সে স্কুলে, কলেজে, সবরকম প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করেছে, এতে সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, এর মধ্যে ছাত্রদের কোনও মঙ্গল নেই এই তার ধারণা। তাদের প্রতিষ্ঠান হবে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত, সমাজ-কল্যাণই হবে তাদের প্রধান লক্ষ্য। সব কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা এর সদস্য। মৈথিলী মেধাকে উপদেষ্টা হিসেবে চায়। এবং এই প্রসঙ্গেই জানায় যে সমস্ত অধ্যাপকের সৎ, আন্তরিক, কর্মী এবং নির্ভীক বলে সুনাম আছে তাঁদের অনেককেই তারা এই উপদেষ্টা মণ্ডলীতে থাকবার অনুরোধ জানাচ্ছে। মেধা প্রথমে রাজি হননি। কিন্তু মৈথিলী যখন বার বার করে জানালো তাদের রাজনীতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, এবং তারা শুধু অলস সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটা গড়ছে না, গড়ছে মৈথিলীর ভাষায় ‘উইথ ডেড সীরিয়াসনেস’, তখন মেধা রাজি হয়েছিলেন। এরা ইতিমন্ন্যে বেশ কিছু সাক্ষরতা-অভিযান করেছে, ‘স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন’ এটাও ছিল এদের কয়েকটা অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সংগ্রহ করেছে প্রচুর ছাত্র সদস্য। সাধারণ সদস্যদের সংস্পর্শে খুব বেশি না এলেও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য মেডিক্যাল কলেজের মৈথিলী ত্রিপাঠী ও দেবপ্রিয় চৌধুরী, এঞ্জিনিয়ারিং-এর উজান আফতাব, তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ ছাত্রী লক্ষ্মীশ্রী মজুমদার ও গুঞ্জন সিং, এবং সায়েন্স কলেজের প্রমিত গুপ্ত তাঁর সঙ্গে অধিবেশনে মাঝে মাঝেই বসে। এদের মধ্যে প্রথম তিনজন যে অসাধারণ তাদের সংকল্পে, কল্পনাশক্তিতে ও চরিত্রবলে তা তিনি টের পেয়েছেন। উপদেষ্টাদের মধ্যে প্রধানত আছেন নন্দিতা সাহা, ডঃ প্রভাস সোম, সূর্য দাস, মধুচ্ছন্দা দাশগুপ্ত। মুশকিল হচ্ছে এঁরা সকলেই সংসারী মানুষ। নিজের নিজের বৃত্তিতেও আকণ্ঠ নিমজ্জিত। নন্দিতা লেখে, ডঃ সোম রিসার্চ প্রজেক্ট পরিচালনা করেন, সূর্য ভীষণ ভালো ছেলে, কিন্তু বিরাট যৌথ পরিবারের দায় তার কাঁধে, মধুচ্ছন্দার নাচের কেরিয়ার রয়েছে। সংসার-জীবনেও তার নানা গোলমাল। অনেক অধিবেশনেই মেধা দেখেন এদের ‘উপদেশ’ দিতে তিনি একাই এসেছেন। এবং সে ‘উপদেশে’র জন্য ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সমিতির আগ্রহ ও শ্রদ্ধা অসীম। যদিও তারা প্রত্যেকটি পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করে, সময়ে সময়ে সেটাকে আংশিক বদলায়ও। এদের সঙ্গ মেধার উজ্জীবন, উদ্দীপন।
রাত্রের খাবার তৈরি করতে করতে হঠাৎ একটা নাম মেধার মনে এলো। দেবপ্রিয়। খুব সম্ভব ফোনটা করেছিল দেবপ্রিয়। স্যুপটা গরম করতে বসিয়েছেন, রুটি দুটো হয়ে গেছে মেধার ইচ্ছে হল মোটা মোটা আলুভাজা খাবেন। আলুগুলো কাটতে কাটতে ক্ষীণ টেলিফোন-স্বরটা স্মৃতিতে মৃদু ধাক্কা দিচ্ছিল। গরম তেলের মধ্যে আলুগুলো চড়াৎ করে ছেড়েছেন এমন সময় নামটা মনে এলো। দেবপ্রিয়র গলা চট করে শোনা যায় না। এগজিকিউটিভ কমিটির মীটিং-এ থাকলেও সে বেশির ভাগ কথাই মৈথিলী ও উজানকে বলতে দেয়। মাঝে মাঝে, খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময়ে তার বক্তব্য একবার দুবার শোনা যায়, এবং তখনই বোঝা যায় সে কোনক্রমেই ঘুমন্ত সদস্য নয়। সম্পূর্ণ সজাগ, কাজে আগ্রহী। কিন্তু সবাইকার সঙ্গেই দেবপ্রিয় একটা দূরত্ব রেখে চলে। ছেলেটি গ্রাম থেকে এসেছে। মেয়েদের সঙ্গে খুব সহজ হতে পারে না। এটা অবশ্য একটা অনুমান। কিন্তু উপদেষ্টা কমিটিতে যেসব পুরুষ অধ্যাপক আছেন তাঁদের সঙ্গেও তো সে খুব ঘনিষ্ঠ নয়। মেধার সহজাত বোধ বলে দেবপ্রিয় ছেলেটি আরও একটু সক্রিয় হলে ভালো হত। তার নিজের পক্ষে তো বটেই। ছাত্রসঙেঘর পক্ষেও। কারণ মৈথিলী সমাজ-কল্যাণ বা গ্রাম-কল্যাণ করতে চাইলেও তার সঙ্গে মাটির যোগ খুব কম। দেবপ্রিয় যখন মতামত দেয় বোঝা যায় সে সমস্যার সঙ্গে আরও অনেক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। লাজুক, মুখচোরা দেবপ্রিয় আজ কেন তাঁকে ফোন করেছিল জানতে মেধা খুব কৌতূহল বোধ করছিলেন। কিন্তু কলকাতার টেলিফোন সিসটেম যদি কোনও ব্যাপারে বাধা দেবে মনে করে তো সে বাধা অতিক্রম করে কার সাধ্য!
খাওয়া শেষ করে মেধা-অন্যমনস্কভাবে মুখ ধুলেন। এখন তিনি অনেকক্ষণ পড়াশোনা করবেন। গবেষণার কাজ মেধা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। যে বছরগুলো মার্কিন দেশে ছিলেন ওরা তাঁর মস্তিষ্ক, অন্তরাত্মা নিংড়ে একটার পর একটা পেপার করিয়ে নিয়েছে। স্প্যানিশ ইমিগ্র্যান্টসদের ইতিহাস, ইজরায়েল-মার্কিনি সম্পর্কের প্রথম দশ বছরের তাৎপর্য, বেশির ভাগই আন্তজাতিক সম্পর্কের ওপরে। এসব পেপার লেখার কোন প্রয়োজন তাঁর ছিল না। কোনকালে তিনি নিছক পাণ্ডিত্যের জন্য পড়াশোনা করেননি। এখনও তিনি মনে করেন ইতিহাসে গবেষণার চেয়ে জীবন্ত ইতিহাস গড়ে তোলা আরও অনেক জরুরি, অনেক রোমাঞ্চকর কাজ।
রাতের পোশাক পরে আলোটা নিভিয়ে দিতে যাচ্ছেন এমন সময়ে বাইরের দরজার বেলটা বাজল। ড্রেসিং গাউন পরতে এক মিনিট। বড় বড় পায়ে জানালার কাছে এগিয়ে নিচে টর্চ ফেললেন মেধা—‘কে?’
নিচ থেকে সাড়া এলো—‘আমি দেবপ্রিয়।’
‘এত রাতে?’
—‘কলেজ স্ট্রিট থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি। অনেকবার ফোন করবার চেষ্টা করলুম! বেশিক্ষণ সময় নেবো না।’
দরজা খুলে দিয়ে মেধা বললেন—‘ওপরে এসো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না।’ দোতলার দালানে সোফার ওপর খুব আত্মসচেতন সঙ্কুচিতভাবে বসল দেবপ্রিয়। মেধা বললেন—‘কটা বেজেছে জানো?’
—‘জানি। সাড়ে এগারটা।… আসলে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলুম।… ফিরে এসে ফোন করলুম। লাগল না ঠিকমতো।… বাস পেলুম না…
—‘তার মানে তোমার খাওয়া-দাওয়াও হয় নি?’
—‘ও হ্যাঁ, মানে না… খাওয়া-দাওয়ার কথা আমার মনে ছিল না।
মেধা কথা বলতে বলতেই ফ্রিজ খুলছিলেন। বললেন—‘রাত্রে ভাত খাও?’
দেবপ্রিয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল—‘খাওয়া-দাওয়ার সময় আমার নেই ম্যাডাম। আমি শুধু বলতে এলুম পরবর্তী প্রজেক্টগুলোয় আমি থাকতে পারছি না।’
—‘হঠাৎ?’ মেধা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।
—‘হয়ত আমি ছাত্রসংঘও ছেড়ে দেবো?’
—‘ছেড়ে দেবে? তো সে কথা ছাত্রসঙ্ঘের সেক্রেটারিকে প্রেসিডেন্টকে জানাও, আমাকে কেন?’
—‘ম্যাডাম, বাইরে থেকে ছাত্রসঙেঘর কাজ-কর্ম আমি সবই করব, শুধু কোনও সম্মেলনে যাবো না। এর কারণটা খুব সিরীয়স, এক্ষুণি জানাবার সময় আসেনি।
কিন্তু কেউ যেন বুঝতে না পারে আমার এই সিদ্ধান্তের কথা। শুধু আপনি জানবেন।’
—‘তুমি যে কী বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।’
‘এখন আপনাকে বোঝাতে পারবো না। বোঝাবার বিপদ আছে। উজান, বা কেউ যেন জানতে না পারে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।’ দেবপ্রিয় বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল। মেধা পেছন থেকে গিয়ে তার বাহু ধরলেন—‘এতরাতে কোথায় যাবে? খেয়ে নিয়ে এখানেই শুয়ে পড়ো। আমার কোনও অসুবিধে নেই।’
দেবপ্রিয়র চোখে রীতিমতো আতঙ্ক। বলল—‘ম্যাডাম, প্লীজ আমাকে মাপ করুন।’ মেরুন রঙের ড্রেসিংগাউন পরা দীর্ঘাঙ্গী মেধা ভাটনগর রাত সাড়ে এগারটার ভুতুড়ে আলোয় যেন কোনও অতিপ্রাকৃত লোকের অধিবাসী। দেবী না অপদেবী বোঝা যায় না।
—‘তুমি কি হোস্টেলে থাকো?’
—‘না। আমি একটা ফ্যামিলিতে থাকি। রাতে বাড়ি না ফিরলে কালকে আর ঢুকতে পাবো না।’
মেধা হেসে বললেন ‘রাত দুটোয় ফিরেলে ঢুকতে পাবে?’
দেবপ্রিয় হাসল, বলল—‘একটু অশান্তি হবে। কিন্তু পাবো।’
মেধা বললেন—‘তাহলে অন্তত খেয়ে নাও। নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ো। মধ্যরাতের কলকাতার দুঃসাহসিক অভিযান রোমাঞ্চকর হতে পারে, কিন্তু কুকুর, পুলিস, মাতাল, গুণ্ডাদের পাশ কাটিয়ে বেরোতে হলে খালি পেটে পারা সম্ভব নয়।’
দেবপ্রিয় নিতান্ত নাচারের মতো খেলো। রুটি মাখন, দুধ আর কিছুটা স্টু ছিল তাই-ই দিলেন মেধা। ওর খাওয়া দেখতে দেখতে তিনি অনুমান করবার চেষ্টা করতে লাগলেন ছেলেটা কেন ছাত্রসংঘ ছেড়ে দিতে চায়। ছাত্রসংঘের জন্মের পেছনে কোনও নির্দিষ্ট মতবাদ নেই, যেমন তাঁদের সময়ে ছিল। কেউ বিপ্লবে বিশ্বাসী, কেউ শোধনবাদে—এইসব প্রশ্নে চৌষট্টি সালে পার্টি ভাগ হয়েছিল। সাতষট্টির নির্বাচন পর্যন্ত একই নামে দুটি পার্টি চালু রইল। তারপর দুজনেই যখন নির্বাচন নামল, নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিল। এসবের নাড়িনক্ষত্র জানত রোকেয়া, সে-ই তাঁকে ওয়াকিবহাল করে, এত কথা সান্যালদা জানাতে চাইতেন না। কিন্তু এদের মধ্যে তো সে সব প্রশ্ন নেই। এদের কাজের ধরন হল সরাসরি একটা পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা। তবে কি কোনও মনোমালিন্য? অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, মন কষাকষি, জিনিসগুলো একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। সেটাই যদি কারণ হয় তবে দেবপ্রিয়কে তিনি দ্বিতীয়বার ফিরে ডাকবেন না। অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার আবহাওয়া ধ্বংস হয়ে সহযোগিতার যুগ আরম্ভ হোক এদের মধ্যে এই তাঁর মনের গোপন সংকল্প। কিন্তু দেবপ্রিয় একটা রহস্যময় গোপনতাও রাখতে চাইছে। বলতে চাইছে না যখন নিশ্চয় সঙ্গত কারণ আছে। মেধা জোর করতে চান না। কিন্তু কারণটা তাঁকে জানতেই হবে, নিজের চেষ্টায়।
অধ্যায় : ৫
বহুবার খড়ি দিয়ে লেখা এবং মোছার পর শ্লেটের যেরকম রং হয়, হেমন্তর আকাশ অনেকটা সেইরকম। একটা ময়লাটে আলো যেন নোংরা ন্যাতা হাত বুলিয়ে দিয়েছে শহরটার গায়ে। রঘুনন্দন সাত সকালেই খবর পেলেন অফিসের রাস্তায় বিশাল জ্যাম। গতকাল শেষ রাতে নাকি বড়বাজারে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। তাঁকে যেতে হবে নিউ সেক্রেটারিয়েট। ওদিকে যখন এতো জ্যাম, তখন তিনি মেয়েকে মেডিক্যাল কলেজে নামিয়ে ধীরে সুস্থে যেতে পারেন। দাড়ি কামাচ্ছিলেন বাথরুমের বেসিনে, গালের ওপর দিয়ে রেজারটা টানতে টানতে চেঁচিয়ে বললেন,—‘অরু, মুন্নিকে রেডি হতে বলো। আমার সঙ্গে বেরুবে।’ কোনও উত্তর পেলেন না। চানটান সেরে ঘরে এসে দেখেলেন তাঁর গ্রে রঙের সুট, ব্রাউন টাই সব বিছানার ওপর চিৎপটাং হয়ে আছে। অরুণা ধারে কাছে কোথাও নেই। রান্নাঘরের দিক থেকে অবশ্য ছ্যাঁক ছোঁক শব্দ আসছে। কিন্তু ছ্যাঁক ছোঁক শব্দ তোলবার জন্যে তো বৈজুই রয়েছে। অরুণাকে সেখানে থাকতেই হবে এমন ব্যবস্থা রঘুনন্দনের বাড়ির নয়।
খাবার টেবিলে এসে অবশ্য অরুণাকে পাওয়া গেল। হাতে উল কাঁটা। নীরবে খুব মনোযোগের সঙ্গে দুটো তিনটে রং-এর মিশেলে কিছু একটা বুনে চলেছে। টেবিলের ওপর রঘুনন্দনের খাবার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। রান্নাঘরের দিক থেকে কফির খুশবু। রঘুনন্দন টাইয়ের গিটটা ধরে দু-একটা ঝাঁকি দিয়ে তাকে জায়গামতো বসিয়ে দিতে দিতে বললেন—‘মুন্নিকে দিলে না? বললাম যে মুন্নিকে নামিয়ে দিয়ে যাবো।’
অরুণা বুনতে বুনতেই জবাব দিলেন—‘মুন্নি কোথায়, যে তাকে দোব? সে আজ চার পাঁচ দিন বাড়িই ফেরেনি।’
—সে কি?’ রঘুনন্দন পরোটার প্লেট থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন।
—‘কালও ফেরেনি?’ রঘুনন্দনের ভ্রু কুঁচকে উঠেছে।
বললেন—‘কোথায় আছে ও? খবর পেয়েছ?’
—‘খবর পেয়েছি,’ অরুণা তাড়াতাড়ি বললেন, ‘লুকুর বাড়িতে খুব সম্ভব।’
—‘ঠিক আছে। লুকুর বাড়ি থেকেই ওকে পিক্আপ করব। এতদিন ধরে কলেজ কামাই করছে! ডাক্তারি জিনিসটা ফাঁকি দিয়ে পাস করা যায় না। গেলেও উচিত নয়।’
—‘আমি ঠিক জানি না ও লুকুর বাড়িতেই আছে কি না। আন্দাজে বললুম। ও তো শুধু “ফিরছি না” বলেই ফোন রেখে দিল।’
রঘুনন্দন খুব গম্ভীর মুখে বললেন —‘আই ডোন্ট লাইক ইট অরুণা।’ ভালো করে খেলেন না, মুখ মুছে গরম কফিটা কয়েক চুমুকে শেষ করে উঠে পড়লেন।
অরুণা বুনতে বুনতেই রঘুনন্দনের গাড়ির চলে যাওয়ার শব্দ পেলেন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বোনার সরঞ্জাম সব থলিতে ভরে বারান্দার চেয়ারে এসে বসলেন। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে বলে গেলেন —‘বৈজু আমার কফিটা বারান্দায় দিও।’
খবর পেয়েছেন, মেয়ে ফোন করেছে বললেন বটে, কিন্তু অরুণা কোনও খবর, কোনও ফোনই পান নি। মাত্র দুদিনের কড়ারে কোন গ্রামে মেয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে গ্রাম-উদ্ধারের কাজে গেছে। এই জানেন। বেরোবার সময়ে বলে গিয়েছিল —‘সময়মত না ফিরলে ভেবো না। বেশি দেরি হলে ফোন করে দেবো।’ কিন্তু গত পরশু থেকে ফোনের জন্যে হা-পিত্যেশ করে করে তাঁর কপাল ব্যথা হয়ে গেছে। রঘুনন্দন দিল্লি থেকে ফিরেছেন কাল অনেকরাতে। ফিরেই চান করে শুয়ে পড়েছেন। অরুণা সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেননি। মেয়ে তাঁর খুবই ভালো। নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারে। কিন্তু নিজের কাজ ছাড়া আর সব কাজে যেন ওর মন। কিসের জাল যে বুনে যাচ্ছে। এতো রকম ব্যাপারে ওর মাথা দেবার দরকারটাই বা কি? অরুণার জীবনে স্বামী এবং মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। শ্বশুরকুল নেই। পিতৃকুল মাতৃকুল কিছু নেই। মুন্নির বাবা চাকরির সুবাদে জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, দিল্লি-কলকাতা করছেন তাও বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। মেয়ের পড়াশোনার যাতে অসুবিধে না হয় তাই কলকাতায় এই ছোট বাংলো বানালেন অরুণাকেও ছেড়ে দিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল মেয়েও বাপের মতো আই. এ. এস হোক, আর সত্যি তিনি তা চাইতেই পারেন। বৃত্তি পরম্পরাগত হলে মানুষের সামর্থ্য বাড়ে, স্বাভাবিক ভাবেই সে অন্যদের থেকে পিতৃপিতামহের বৃত্তিতে কুশলী হয়ে ওঠে, এই ধারণা রঘুনন্দনের। উপরন্তু মুন্নি ছোট থেকেই খুব ধীর, স্থির, বিচক্ষণ। কিন্তু মুন্নি নিজের পড়াশোনার ব্যাপারে বাবা-মার ইচ্ছেকে আমল দিল না। সে ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছে, খুব ভালো কথা, কিন্তু সেটাকেও যেন খুব গুরুত্ব দেয় না। অরুণা বরাবরই তাঁর সময় রঘুনন্দন আর মুন্নির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। যখন কলকাতার বাইরে যান মুন্নি থাকে বৈজুর তত্ত্বাবধানে একা। কদিন বাইরে কাটিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসেন তিনি। অথচ মজার কথা এই যে তাদের দুজনকে নিয়ে তাঁর এই হাঁসফাসানি তারা দুজনেই অতিমাত্রায় স্বনির্ভর। রঘুনন্দন চিরকাল হোস্টেলে মানুষ। নিজের জামাকাপড় নিজে কাচা, জুতোয় পালিশ লাগানো, ইস্ত্রি করা এসবে চিরকাল অভ্যস্ত। এখন সরকারি আমলা হয়ে এগোতে আর্দালি, পেছোতে আর্দালি, অরুণার কিছু করবার দরকার হয় না। সেখানে যে শক্তিটা খরচ করতে পারতেন সেটাশুদ্ধ অরুণা মেয়ের সেবায় লাগিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুন্নি স্বনির্ভর। ইদানীং দিন সাত আট দিল্লি কাটিয়ে অরুণা যখন ধড়ফড় করতে করতে ফিরে আসেন মুন্নি শান্তমুখে দরজা খুলে দেয়।
—‘ঠিক আছিস তো, মুন্নি?’
মুন্নি হেসে ফেলে। কোনও জবাব দেয় না।
—‘কি করছিলি?’
—‘পড়ছিলুম।’
—‘কি পড়ছিলি?’
—‘হাইডেগার।’
—‘কি ডেগার?’
—হাইডেগার’
—‘খুব অসুবিধে হয়েছিল?
—‘অসুবিধে হবে কেন?’
পরে বৈজুর কাছ থেকে শুনলেন তার নাকি তিনদিন জ্বর ছিল। মুন্নিই তার সেবা যত্ন করেছে, নিজেও বেশ রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করেছে। বৈজু বলে দিয়েছে সে বৈজুর জন্য বার্লি তৈরি করে দিয়েছে। বন্ধুরা এসেছে তিন চার দিন। সবাই মিলে বাড়িতে ফীস্ট করেছে। দিদি এক দিনও দেরি করে ফেরেনি। রেণু আসেনি বলে একদিন ঘর ঝাঁটপাটও দিয়েছে। আর নিজের জামাকাপড় তো সে বরাবর নিজেই কাচে।
অরুণা বলেছেন—‘মাকে তাহলে তো তোর কোনোও দরকারই নেই!’
—‘কি যে বলো মা, কত যে অসুবিধে!’
—‘এই যে বললি, কোনও অসুবিধে নেই। তাছাড়া এই তো নিজে নিজে রান্না-টান্না, বৈজুর সেবা-পথ্য সবই তো করতে পেরেছিস!’
—‘করলেই বা।’
—‘এসব ভালোও তো লাগে তোর। কেমন সব বন্ধুবান্ধব মিলে হই-চই করলি। আমি থাকলে তো বাড়িটাকে এমনিভাবে ব্যবহার করতে পারিস না।’
—‘তাই বলে মা না থাকলে অসুবিধে হবে না?’
—‘কি জানি।’
—‘শোনো মা। কে তোমাকে এই ইউটিলিটেরিয়ানিজম্ শিখিয়েছে? তুমি না থাকলে আমার বুকের মধ্যে টেনিস বলের মতো একটা ভ্যাকুয়াম থাকে। একদম মধ্যিখানে। কিছুটা হার্ট কিছুটা লাং। এই ভ্যাকুয়ামটা ভরবার জন্যে আমি খুব লম্ফঝম্প করি। যদিও একটা ভাল্ভ আমার কিছুতেই কাজ করে না। নিঃশ্বাসে বায়ু থাকে মা, প্রাণ থাকে না।’
—যা যা চুপ কর তো!’
প্রথমটা খুব হাসতে থাকে মুন্নি, তার থাক কাটা কাটা চুল দুলিয়ে। তারপর হাসি থামিয়ে বলে—‘মা বিশ্বাস করো!’ মুন্নি যখন বিশ্বাস করতে বলে, তখন অবিশ্বাস করার থাকা শুধু অরুণা কেন, মুন্নির বাবাও ভাবতে পারেন না।
রাস্তার দিকে চোখ পেতে থাকতে থাকতে অরুণার আধ-কপালে মাথা-ধরাটা আরম্ভ হল। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। একটা চিন্তা নিয়ে থাকতে থাকতে যখন মাথাটা পাগল-পাগল লাগে তখন ভাবনা করার যন্ত্রটা বিকল হয়ে গেলে বড় শান্তি। তিনি নিজের ঘরে এসে ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ডটা নামিয়ে দিলেন। কপালে ঘষলেন একটা সবুজ ওষুধ। ও ডি-কলোনের জলে রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে চোখে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। মাথার ঠাণ্ডা অনুভূতির ওপর মনটা পড়ে রইল। ঠাণ্ডা, খুব ঠাণ্ডা। আস্তে আস্তে মাথার নানান অলিগলিতে, ফাঁকে ফোকরে ঢুকে পড়ছে ঠাণ্ডাটা।
কেন যে নিজের কেরিয়ারটা ছাড়লেন। রঘুনন্দন মুখে বলেন নি ছাড়তে। কিন্তু তাঁর যখন অন্যত্র পোস্টিং হল অরুণা নিজেই থাকতে পারলেন না। বাপের বাড়ির সবাইকে চটালেন। তাদের সঙ্গে আজ আর কোনও সম্পর্ক নেই। শ্বশুর বাড়ি তো কোনদিনই তাঁকে গ্রহণ করেনি। রঘুনন্দনের তাতে কিছু আসে যায়নি। যতদিন তাঁর মা বেঁচে ছিলেন, মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন। কর্তব্য করেছেন, কিন্তু স্ত্রীকে কোনদিন অবহেলা করেননি। প্রথমটা অরুণা বড় সুখী হয়েছিলেন। বাপের বাড়ির পছন্দের কাউকে বিয়ে করলে এভাবে সুখী হতে আর পারতেন না। এখন মনে হয় যৌবন বড় স্বার্থপর। দায়-দায়িত্ব মাথায় নিতেও যতক্ষণ, আত্মসুখের জন্য সব নামিয়ে দিতেও ততক্ষণ। এখন নিজেকে খুব একলাও লাগে। রঘুনন্দন নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একজন সিনিয়র আমলার নিজস্ব বলতে সময় খুব কমই থাকে। মেয়েও এখন নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, মগ্ন। তিনজনে একত্রে থাকতে তো পারছেনই না এখন। রঘুনন্দন রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের চাকরিটা নিলে এমন হত না। যে যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে এক চুলও নড়বে না… ফলে সুখ যা হবার চূড়ান্ত হয়েছে। মান সম্মানও প্রচুর, কিন্তু অরুণার নিজের জীবন ক্রমশ কিরকম অর্থহীন আনন্দহীন হয়ে যাচ্ছে। রঘুনন্দন তাঁর কর্মজীবনের নানান খুঁটিনাটির কথা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা আজকাল একরকম ছেড়ে দিয়েছেন। মুন্নি অবশ্য তার বন্ধু-বান্ধব, পড়াশোনা, সোশ্যাল ওয়ার্কের নানান কথা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে, মতামতও চায়। কিন্তু কেমন আলগা-আলগা, যেন বুড়ি ধুঁয়ে যাওয়া। নিজের কাজ, নিজের জীবন, নিজের লক্ষ্য কিছু চাই-ই। না হলে এই মাথা-ব্যথা এই প্রতীক্ষার কষ্ট… এই টানাপোড়েন… এ চলবেই।…
মৈথিলী যখন বাড়ি ফিরল, বাড়িটা এই সকালেই নিঝুম। বৈজুদা বলল—‘মায়ের দরদ হচ্ছে মাথায়, দেখো হয়ত এখন ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছেন। বাবা খুব চিন্তা নিয়ে অফিস গেছেন।’
মৈথিলী তার ঝোল্লা ব্যাগটা বসবার ঘরের টেবিলে রেখে, জুতো খুলে পা টিপে টিপে মায়ের ঘরে ঢুকল। অঘোরে ঘুমোচ্ছে মা, চোখ থেকে রুমাল সরে গেছে। ওডিকলোনের মৃদু গন্ধ হাওয়ায়। মায়ের চোখের তলায় কালি। মৈথিলীর মাকে একটা চুমু খাবার ইচ্ছে হল, কিন্তু সে ইচ্ছে সংবরণ করে সে আবার পা টিপে টিপে বসবার ঘরে চলে এলো। ফোনের বোতাম টিপল …‘মিঃ ত্রিপাঠী আছেন? —বাবা আমি মুন্নি কথা বলছি। হ্যাঁ বাবা, অ্যাডাল্ট লিটরেসি প্রোগ্রামে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভেতরে যেতে হয়েছিল। অনেক কাজ। ফিরতে পারিনি। না কেউ না। লুকু?… লুকু যায় নি। আমি এসে গেছি, তুমি দুপুরে ভালো করে খেও।… কি করে জানলাম? বৈজুদা দেখালো, তোমার আধধাওয়া প্লেটটা এখনও রেখে দিয়েছে।’
বৈজু রান্নাঘরের দুয়োর থেকে চোখ পাকাচ্ছে—‘ঝুট বলবে না মুন্নি, ফোন রেখে মুন্নি বলল— ‘মিথ্যে কথা! তুমি যেভাবে বর্ণনা দিলে তাতে আমি ওই বিষন্ন, বিদীর্ণ প্লেটটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে বৈজুদা!’ তার মুখে হাসি।
বৈজু মুন্নির কথাবার্তার ধরনে অভ্যস্ত। সে-ও হাসছে। কিছু না বুঝে। কিন্তু মুন্নি এসে গেছে। আবার ওইভাবে হাত নেড়ে শক্ত শক্ত শব্দ দিয়ে কথা বলছে তার ভারি আনন্দ।
মায়ের ঘর থেকে চাপা আওয়াজ ভেসে এলো—‘মুন্নি এলি!’ মৈথিলী প্রায় এক লাফে মার ঘরে ঢুকে গেল। মায়ের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়তেই মা বললেন —‘তোর জামাকাপড়ে কি বিটকেল গন্ধরে!’
—‘গন্ধ হবে না? সারাদিন রোদে রোদে ঘোরা, না জামা-কাপড় বদলানো, না ভালো করে চান, সেই এক ধড়াচুড়ো। এতদিন থাকতে হবে, এত অসুবিধেয় পড়ব, তা কি আগে জানতাম? মা, কোথায় শুয়েছি জানো?’
—‘কোথায়?’
—‘খড়ের বিছানায়।’
——‘সে কি রে?’
—‘সে এক অজ পাড়া গাঁ মা। মাটির ঘর খড়ের চাল, এ ছাড়া কিছু নেই। ওদের এক জনদের একটা বাড়তি ঘর খালি করে দিল, চারচালা ঘর। মেঝেতে আঁটি আঁটি খড় বিছিয়ে দিল, তার ওপর যে যার চাদর পেতে ধড়াচুড়ো পরে শুয়ে পড়লাম।’
—‘কে কে ছিল?’
—‘প্রমিত, শান্তনু, বুল্টু আর উজান।’
—‘সে কি লুকু ছিল না? আর কোন মেয়ে না?’
—‘লুকু শেষ পর্যন্ত যেতে পারল না। ওর বোধহয় মাম্পস হয়েছে মা।’
—‘তুই একা মেয়ে?’
—‘হ্যাঁ। তাতে কি?’
—‘তুই আর ওই চারটে ছেলে এক ঘরে?’
—‘হ্যাঁ! আর কোথায় জায়গা পাবো?
—‘মুন্নি, তুমি এভাবে আর যেও না। এগুলো ঠিক হচ্ছে না। বড়দের মধ্যে কেউ ছিলেন না?’
—‘প্রোফেসর সোম ছিলেন।
—‘তিনিও ওই একই ঘরে?’
—‘বাঃ, তাছাড়া কি?’
—‘তোর অস্বস্তি হল না! আচ্ছা মেয়ে তো!’
—‘অস্বস্তি হলেই বা কি করবো? উজানের অবস্থা যদি দেখতে! আঁট জিন্স্ পরে শুয়েছে মাঝ রাত্তিরে উঠে বসে বলল—‘আমার কোমর, পা সব হাঙরে কেটে নিয়ে যাচ্ছে।’ গ্রোফেসর সোম বললেন—‘তুমি একটু আলগা করো, আলগা হও, মৈথিলী দেয়ালের দিকে মুখ করুক। তাছাড়া এই লণ্ঠনের আলোয় কাউকেই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না,’ গলাটাকে অনুপস্থিত ডঃ সোমের মতো ভারী করে মৈথিলী বলল।
অরুণার রাগ হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি হেসে ফেলতে বাধ্য হলেন, বললেন —‘তোরা কি রে? লাজ-লজ্জা সব বিসর্জন দিয়েছিস?’
—‘লাজ-লজ্জা আবার কোথায় বিসর্জন দিতে দেখলে মা! কাজ করতে গেলে অতো পুতুপুতু চলে না, অ্যান্ড কাজ ইজ আ হান্ড্রেড টাইমস মোর ইমপর্ট্যান্ট দ্যান অল দ্যাট ন্যাম্বি-প্যাম্বি অ্যাবাউট মডেস্টি।’
অরুণা বললেন—‘যত কাজ কি তোর একারই মুন্নি? আর কেউ নেই?’
—‘কাজ করবার লোক সত্যিই খুব কম, মা। এই দ্যাখো না, লুকুটা অসুখ বাধিয়ে বসল। দেবপ্রিয় টার্ন আপ করল না, গুঞ্জন তো কি সব পরীক্ষা দিচ্ছে। আসলে আমরা সবাই ভাবি ওরা তো আছে ওরা করবে। লোক এমনি করে করে কমে যায়। যাক, তোমার মাথার যন্ত্রণা গেছে তো?’
অরুণা বললেন—‘এক ঘুম তো দিয়ে নিলুম। এরকম ভাবে কি কারো যন্ত্রণা যায় মুন্নি? অন্য সংসারে দেখো কর্ত্রী হাল ধরে থাকে, তার কথামতো, তার সুবিধে মতো সবাই চলে। আমার হয়েছে তোমাদের দুজনের মধ্যে তাঁতের মাকুর মতো ঘোরা। আর ভালো লাগছে না।’
—‘মা, তুমি আজ একদম খাঁটি সত্যি কথাটা বুঝেছ। তোমার নিজস্ব কিছু কাজ দরকার। যদি করতে চাও মা তোমাকে আমি অনেক কাজ দিতে পারি।
—‘রক্ষা করো! অরুণা গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘আমার কাজ আমি খুঁজে নেবো। তোমায় আর আমার কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তবে মনে রেখো মুন্নি, আমার নিজস্ব কাজ হলে আর তোমরা আমায় এরকম এক পায়ে খাড়া পাবে না। আমিও ব্যস্ত হতে, অন্যমনস্ক হতে জানি।’
মৈথিলী বলল—‘মা, তুমি দেখছি সত্যি-সত্যিই খুব রাগ করেছে। রাগ হলেই তুমি ভালো ভালো লাগসই ইডিয়ম ব্যবহার করো। ‘এক পায়ে খাড়া’টা রাগ হলেই তুমি বলো।’
মায়ের কাছে মৈথিলী একটু তরল, বাবার কাছে তরলতর। কিন্তু একই মিশ্রণের গাঢ়তা যেমন তাপের তারতম্যে বাড়ে কমে, তার স্বভাবের ব্যাপারেও তাই। মা বাবার উত্তাপে সে খানিকটা গলে থাকে। বাইরের পৃথিবী যত শীতল, যত নৈর্ব্যক্তিক সে ততই ঘন, ততই ঋজু, সংকল্প কঠিন, ওজনদার ও তার নেতৃত্ব তখন মেনে নেয় সবাই। উজান পর্যন্ত যে উজান শতকরা নব্বই ভাগ পুরুষ, দেব পর্যন্ত জীবন সম্পর্কে যার ধারণা মৈথিলীর চেয়ে অনেক প্রত্যক্ষ।
ছাত্রসঙ্ঘের প্রথম প্রোগ্রাম হয় বয়স্ক শিক্ষা। মেধাদি এবং ডাঃ সোমের সঙ্গে আলোচনা করতে ওঁরা মৈথিলীর ওপরেই সব ভার দিলেন। সূর্যদা বয়স্কশিক্ষার পাঠক্রম ঠিক করে দিলেন। সে সব ঠিকভাবে সাজানো মেধাদি সূর্যদা আর নন্দিতাদির সাহায্য নিয়ে প্রধানত মৈথিলীই করল। সেই পরিকল্পনা মতো তারা শালকিয়ার পিলখানা বস্তিতে, কাঁকুলিয়ার বস্তিতে কাজ করল। কিন্তু মৈথিলীর একেক সময়ে সন্দেহ হয় সে এই ধরনের নেতৃত্বের যোগ্য কি না, সে বড্ড শহুরে, বড্ড বেশি উচ্চবিত্ত। শুভ-সংকল্প আর সমবেদনা ছাড়া এই স্তরের মানুষের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। যখন তারা শহরের আশপাশের শ্রমিক-বসতিগুলোয় অভিযান চালানোর কথা আলোচনা করছে, পুলকেশ, প্রমিত, উজান সবাই-ই এতে সায় দিচ্ছে, সে সময়ে দেব একদিন বলল মফঃস্বলের লোকেরা যত দরিদ্রই হোক, কিছু-না-কিছু সুযোগ-সুবিধে তারা পায়ই। কিন্তু শহর থেকে বহু দূরে যেসব গণ্ডগ্রাম আছে সেখানকার অবস্থা সত্যিই ভয়াবহ। আগে এরা মহাজনের ওপর নির্ভর করে মার খেতো। এখন খাচ্ছে পঞ্চায়েত আর জেলা-বোর্ডের হাতে। এদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সর্বপ্রথম দরকার। উজান তখন দেবদের গ্রামটাকেই কর্মকেন্দ্র করবার প্রস্তাব দেয়। দেব বলে হুগলি জেলায় এমনিতে লিটরেসি লেভেল হাই। তার ওপর ওদের গ্রামে পৃথ্বীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বলে একজন আছেন, তিনি নিজেই বয়স্ক শিক্ষার প্রোগ্রাম নিয়েছেন। ওদিকে না গেলেও চলবে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ঠিক হল দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এই কেওড়া বা কেওড়াখালি গ্রাম। ওই গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার নিরঞ্জন খাঁড়া মশাইয়ের সঙ্গে এম ভি’র কিভাবে যেন যোগাযোগ হয়। খুব সম্ভব খরার সময়ে নিরঞ্জনবাবু নানান জায়গায় সাহায্য প্রার্থনা করে করে ঘুরতেন। এম ভি-ই প্রথম সূর্যদা আর নন্দিতাদিকে নিয়ে কেওড়াখালি গ্রাম দেখে আসেন। প্রোগ্রাম ছকা হল। মা বাবাকে অ্যাডাল্ট লিটরেসি বলে বুঝিয়ে দিলেও মৈথিলীদের পরিকল্পনা আরও ব্যাপক। তারা এর জন্য চ্যারিটি শো করে করে টাকা তুলেছে, ছাত্রসঙ্ঘের চাঁদার টাকা, এবং কিছু কিছু ডোনেশনও আছে।
স্টেশনের নাম কি অদ্ভুত অদ্ভুত— বহড়ু, তালদী, ধপধপি। অন্য স্টেশনে নেমেও যাওয়া যায়। ওরা ধপধপিতে নেমেছিল। বাসের রাস্তা শেষ হয়ে গেল। তারপর কুলতলির মাঠ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ধরে এই তেপান্তর পার হতে হয়। ভীষণ গর্ত, জায়গায় জায়গায় কাদার দঁক, বালি। এখানে ওই গ্রামের উৎসাহী হেডমাস্টারমশাই নিরঞ্জন খাঁড়া একটা ভ্যানগাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সেই ভ্যানগাড়িতে তারা ছজন কিছুটা বসে কিছুটা ঠেলে গ্রামে পৌঁছল। ছেলেরা সবাই কিছুটা করে ঠেলেছে। ডঃ সোম, কিছুতেই ভ্যানগাড়িতে উঠবেন না, হাঁটছেন, আর কপালের ঘাম মুছছেন। সাইকেলের চাকা মাঝে মাঝেই বসে যাচ্ছিল ময়াল সাপের মতো কাদার ফালে। এদিকে বৃষ্টি হয়নি, কিন্তু ওদিকে, শহরের ছেলে মেয়েরা যাবে জেনে তাদের বিপদে ফেলবার জন্যেই যেন বেশ কয়েক দফা হৈমন্তী বৃষ্টি হয়ে গেল। শীতও বাড়ল। রাস্তার কষ্টও। ডঃ সোম বারণ করা সত্ত্বেও মৈথিলীও কিছুটা ঠেলেছে। মেয়ে বলে সে আলাদা সুবিধে নিতে চায় না। যদিও উজান বলেছিল—‘মৈথিল, বাড়াবাড়ি করিসনি। ডাক্তারি পড়ছিস, নিশ্চয় জানিস ছেলে হবো বললেই হওয়া যায় না।’
গ্রামটা এলোমেলো গাছ পালায় ভরা। শীতের গোড়ায় বহু গাছের পাতা ঝরে গেছে। রাস্তাঘাট, বসতবাড়ি, পুকুরঘাট ইত্যাদির শোচনীয় অবস্থা। কুটিরগুলো মোটামুটি পরিষ্কার। কিন্তু এদের পরিচ্ছন্নতার একমাত্র ধারণা গোবর। গ্রামটাতে নদী নেই। কিছু দূরে মাতলা নদী থেকে খালের মতো খানিকটা ঢুকে এসেছে। বাঁয়ে পিয়ালীরও এরকম দু-একটা খাল আছে। এগুলোকে ওরা কানা মজা আর বোজা নাম দিয়েছে। একটিমাত্র পুকুর। তাতেই গ্রামসুদ্ধু লোকের চান, বাসনমাজা, কাপড় কাচা, পানীয় জল সংগ্রহ সব চলে। দেখে শুনে বুল্টু বলল—‘এরা বেঁচে আছে কি করে বল তো? আন্ত্রিক আর কলেরায় এখনও উজাড় হয়ে যায় নি এটাই আশ্চর্য।’
নিরঞ্জন খাঁড়া জানালেন এবছর গরমকালেই প্রচণ্ড আন্ত্রিকের মড়ক লেগেছিল। প্রথমে ওদের দু দিন থাকার কথা ছিল। অবস্থা দেখে ঠিক হল পাঁচদিনের কমে কিছু হবে না। কোন্ কোন্ ব্যাপারে সংস্কার চাই, কোথায় নতুন উদ্যোগ দরকার সেগুলো সরেজমিনে ছকে ফেলা চাই। কুয়ো এবং নলকূপ খোঁড়া হবে। স্পটগুলো উজান ঘুরে ঘুরে ঠিক করল। ওরা থাকতে থাকতেই তো একটা পাতকুয়ো খোঁড়া হয়ে গেল। কিন্তু টিউবওয়েলের জন্যে তো শহরে এসে বিলিব্যবস্থা করতে হবে! খালগুলো থেকে কচুরিপানা পরিষ্কার করাতে হবে। বেশ কিছু জলা জায়গা আছে সেগুলোরও সংস্কার চাই। চারদিনই বিকেলবেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনা করেছে মৈথিলী আর প্রমিত। সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়মপালন, পানীয় জল সম্পর্কে কড়াকড়ি। সাপের কামড়ে এখানে প্রায়ই লোক মরে, সর্পাঘাত, আগুন, জলে ডোবা ইত্যাদির ব্যাপারে ফার্স্ট এইড এবং পরবর্তী করণীয় পরিবার পরিকল্পনা। তালিকায় তো রয়েছে প্রচুর, চার দিনে আর কতটুকু হয়। বয়স্ক শিক্ষার ক্লাসও নিয়েছে বাকিরা, সন্ধেবেলায়। হেড মাস্টার নিরঞ্জনবাবুকেই বয়স্ক-শিক্ষার ট্রেনিং এবং দায়িত্ব দিয়ে এসেছে ওরা। তিনি প্রতি সন্ধেবেলায় তাঁর স্কুলঘরেই বড়দের পড়াবেন। দরকারি বইপত্র, স্লেট পেনসিল, বোর্ড চক প্রভৃতি প্রথম দফায় যা লাগবে তা সবই ওরা দিয়ে এসেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে ওরা শুধু ক্লাসই নেয়নি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সরেজমিনে দেখে শুনে হাতে কলমে কিছু কিছু আচরণবিধি শিখিয়ে দিয়ে এসেছে।
দেব যে কেন গেল না! শেষ মুহূর্তে টার্ন আপ করল না। ওরও কি লুকুর মতো কিছু অসুধ-বিসুখ করেছে? মনে হয় না। চেহারার ধরণটা একটু পলকা হলেও দেব রীতিমতো ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী। এতদিনের মধ্যে একদিনও তার কোনও শারীরিক গণ্ডগোল হতে দেখা যায়নি। ওদের যাবার আগে, কি কি প্রয়োজন হতে পারে, বইপত্র ইত্যাদি কোথায় পাওয়া যাবে, আন্দাজ কতো নেওয়া হবে এ সবই ব্যবস্থা ও করেছিল। কারণ ওর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। ও-ই বলেছিল স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা দুটো বক্তৃতায় বা ফার্স্টএইড শিখিয়ে এলেই কাজ হবে না। স্থানীয় দুচার জনকে রীতিমতো ট্রেনিং দিয়ে, প্রাথমিক কিছু ওষুধ পত্র ব্যান্ডেজ, গজ, অ্যানটিসেপটিক ইত্যাদি দিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলে দিয়ে আসতে হবে।
নিরঞ্জন খাঁড়া ছাড়া লেখাপড়া বলতে কেউ কিছু জানে না। একদম চাষীগাঁ। কিন্তু নিরঞ্জনবাবু সকালে ছোটদের স্কুল চালান। সন্ধেয় এখন থেকে বড়দের ক্লাস নেবেন, এর পরে যদি স্বাস্থ্যকেন্দ্রও চালাতে হয় তো তাঁর পক্ষে বড্ড বেশি হয়ে যায়। প্রাথমিক কিছু ওষুধপত্র তাঁর কাছেই রেখে এসেছে ওরা। তাঁর স্কুলের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলেটির নাম নীলমণি, তাকে তৈরি করে দিতে পারবেন আশ্বাস দিচ্ছেন নিরঞ্জনবাবু।
ইতিমধ্যে গ্রামের মেয়েরা পাতকুয়ো এবং টিউবওয়েল খোঁড়া হবে শুনে খুব উৎসাহী। পঞ্চায়েতে বলে বলে ওরা হার মেনে গেছে। এ গ্রাম তো পুরোপুরি গ্রামের মর্যাদাও পায় না, মৌজা মাত্র। গ্রাম সেবকদের এ গ্রামের কথা মনে থাকে না। বড় বড় বর্গাদার আছে পাশের গ্রামে, তাদের গায়ের জোর, গলার জোর, ট্যাঁকের জোর সব বেশি। মনোযোগ সবটুকু তারাই কেড়ে রেখেছে। সেচের তো কথাই নেই, পানীয় জলের জন্যও শুখার দিনে ওদের বহুদূর যেতে হয়, সেই কষ্ট কমবে। বয়স্ক-শিক্ষার ব্যাপারে আবার এদের উৎসাহ কম। দু একজন গিন্নিবান্নি বলল—‘কি হবে গো দিদি! মেয়ে তো তোমার মতো পেন্টুল পরে শহরে বাজারে ঘুরবে না! ষোল পার হলেই বিয়ে দিয়ে দুব। নাউয়ের শাক রাঁধবার জন্যে কি গোবরছড়া দেবার জন্যে নেকাপড়া না শিখলেও চলবে।’
প্রমিত বলল আপনার মেয়ের ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবেন তো!
—‘সে শক তো মানুষের থাকেই দাদাবাবু।’
—‘তবে? নাতির বেলায় চাইছেন, মেয়ের বেলায় চাইছেন না কেন? মেয়ে লেখাপড়া শিখলে নাতির তো ঘরে বসেই অক্ষরপরিচয় হয়ে যাবে। ইস্কুলে যাবার আগেই। লেখাপড়া শিখলে কেউ ঠকাতে পারবে না, কাগজ পড়বেন, ইস্তাহার পড়বেন, সই কিসে দিচ্ছেন জানতে পারবেন।’
গিন্নি-মানুষটির মুখ তবু গোঁজ রইল। সন্ধেবেলায় মেয়ে ঘরে পিদিম দেখায় জল ছড়া দেয়, রান্না করে, সে সময়টা তাকে ছাড়তে হলে তার ক্ষেতি।
আসবার সময়ে আবার খাঁড়া মশাই হাত কচলে বললেন ‘এদের একটা ভীষণ অভাব পরনের বস্ত্রের। অনেকেরই একটি বই দুটি নেই। আপনারা যদি আপনাদের পুরনো জামাকাপড় কিছু দ্যান, ছেলেমেয়েগুলো পরে বাঁচে।
শান্তনু, প্রমিত, উজান নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করল ওরা এবার কলকাতা ফিরে গিয়ে পুরনো জামাকাপড় সংগ্রহ করবে। নিরঞ্জনবাবু কয়েক দফায় নিয়ে আসবেন।
মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পর মৈথিলী ভালো করে চান করল, বেশ করে সাবান মেখে। তাররপর নিজের ঘরে ঢুকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ডায়েরি লেখায় মগ্ন হয়ে গেল। এটা তার নিত্যকর্ম।
অধ্যায় : ৬
গলার ব্যথায় লুকু ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। লুকুর যে কত ব্যথা! কখনও হাত-পা ব্যথা। কখনও মাথা ব্যথা, কখনও বুকের মধ্যেটা ভারি হয়ে থাকে। এ সব সে কাউকে বলে না। বাবাকে তো নয়ই। বন্ধু-বান্ধবদেরও নয়। তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুন্নি, মৈথিলী। কিন্তু ছোটবেলায় তারা যেমন অবিচ্ছেদ্য ছিল, এর পুতুল ওকে দিত, জামাকাপড় বদলি করত, এখন আর তেমন নেই। মৈথিলীর দৈত্যের মতো স্বাস্থ্য, একেক সময়ে তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন ব্যাসল্ট কি গ্রানাইট পাথর দিয়ে গড়া। দেশ, সমাজ আর মানুষ নিয়ে সে এখন এমন মেতেছে যে আপনজনদের কথা শোনবার, ভাববার ফুরসৎ পায় না। লুকুর মনে হচ্ছে মৈথিলীর পথ এবার ক্রমশই তার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। মৈথিলী কাজে মগ্ন, এই বিচ্ছেদ সে বুঝতে পারছে না, লুকু বুঝতে পারছে, বুঝে তার ভেতরের ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে আরও। সারাজীবনটা কি শুধু হারাবারই খেলা! কিছুই কি তার প্রপ্তিযোগ নেই! মুন্নিকে একদিনই সে তার স্বাস্থ্যের অবনতির কথা বলেছিল, সে বলল—‘ওই যেগুলো বলছিস লুকু, এগুলো কাদের হয় জানিস?’
‘কাদের?’
—‘একদম অলস, নিষ্কর্মাদের। তুই আরও বেশি কাজ কর লুকু। আর একদম ব্রুড করবি না। ব্রুড করাটা তোর একটা বিলাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে।’
লুকু যেখানে সমর্থন পায় না, সেখানে আর মুখ খোলে না। ব্যাস। আর কোনদিন সে এ সব কথা মৈথিলীকে বলেনি।
আপাতত তার যা কষ্ট তা ডাক্তারসিদ্ধ। অর্থাৎ স্বয়ং পাস-করা ডাক্তার এসে দেখে, পরীক্ষা করে বিধান দিয়ে গেছেন, এ কোনও অস্পষ্ট শরীর খারাপ নয়, যে ভোক্তা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না, সাইকোসোম্যাটিক বলে যেগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া সহজ। তার বাঁ কানের তলা ফুলেছে। খেতে পারছে না। গলা গলা ভাত তাও গিলতে পারছে না। উপরন্তু গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে রাখতে হয়েছে। নভেম্বরের মাঝামাঝি হওয়া সত্ত্বেও শীত এখনও তেমন পড়েনি। গরম লাগছে তাই। নিজেকে দিনে অন্তত দুবার আপাদমস্তক পরিষ্কার না করলে, লক্ষ্মীশ্রীর নিজের শরীরটাকে কেমন ঘেন্না করে। এখন যেন মনে হচ্ছে গায়ে ইদুঁর-পচা গন্ধ। ডিওডোরান্টটা ভালো করে স্প্রে করে একটু ট্যালকম পাউডার হাতে পায়ে ঘষে নিল সে। চুলগুলো ভালো করে ব্রাশ করল। মা বলত হান্ড্রেড স্ট্রোকস আ ডে। এখন সে ক্ষমতা নেই। একটু যেন ফ্রেশ লাগছে এবার। নিজের ঘরে থাকতে ভালো লাগছে না। ঘরটা যেন তার নিঃশ্বাসে নিঃস্বাসে ভর্তি হয়ে গেছে। নিজের ওপর কি রকম রাগ হচ্ছে। গ্ল্যান্ড হবার আর সময় পেল না! ওরা সকলে কি সুন্দর গ্রামে ঘুরে এলো। নিশ্চয়ই অনেক মজা করেছে। চ্যারিটি শো করতে গিয়েই যা মজা!
আচ্ছা…আমার বদলে কি কেউ গিয়েছিল? কে যেতে পারে? মেয়েদের পক্ষে বাড়ি থেকে পারমিশন যোগাড় করা একটু মুশকিল। কলেজ থেকে এক্সকার্শন যাওয়া হচ্ছে সে এক রকম, বন্ধুরা মিলে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে সে-ও চলে, কিন্তু কয়েকজন ছেলে-মেয়ে মিলে জনৈক অধ্যাপকের নেতৃত্বে গ্রাম সংস্কার! হরি বলো! কথাগুলো বুল্টুর। সে এইভাবে অভিভাবকদের নকল করে। গুঞ্জনের কি পরীক্ষা আছে। আগেই বলে দিয়েছিল যেতে পারবে না। মউমিতা, সর্বাণী কি বাড়ি থেকে অনুমতি পাবে? তবে কি মৈঘিল একাই গেল? একবার ফোন করে দেখলে হত। কিন্তু গলা খুলতে বড় কষ্ট। তার চেয়ে একটা বই নিয়ে ড্রয়িংরুমে সোফায় গিয়ে বসি। বাবা অফিস থেকে কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। ভাইয়ের স্কুল থেকে ফিরতেও বেশ দেরি।
বাড়িটা একদম ফাঁকা। ড্রয়ার থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করি। ধরাই, হ্যাঁ? দিস ইজ ফান, জাস্ট ফান। আচ্ছা তোমরাই বলো ছেলেরা যত খুশি স্মোক করবে, মেয়েরা কেন করবে না? দুজনেরই যদি কাজকর্ম এক হয়, টেনশন এক প্রকৃতির হয়, সব দিক থেকে সমান… শুধু শরীরের গঠন আলাদা! শান্তনু, প্রমিত, উজান সবাই স্মোক করতে পারে। দেব, হ্যাঁ দেবও টানে লুকিয়ে লুকিয়ে। দেব সব ব্যাপারে শহরের ছেলেদের টেক্কা দিতে পারে, খালি চালচলনে পারে না। এ জন্য ওর একটা কমপ্লেক্স আছে। নির্ঘাৎ তাই ও লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খায়। যখন কেউ থাকে না, তখন। কোন মামার বাড়িতে থাকে সেখানে পারে না, নিজের দেশের বাড়িতে পারে না। ওর মেজ জেঠু শকড্ হবেন, অন্যদের সামনে সেজে থাকে গুডি বয়। কিন্তু আড়ালে আবডালে ও স্মোক করা ভালোমতো অভ্যেস করছে। হঠাৎ একদিন পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রিং টিং ছেড়ে সব্বাইকে চমকে দেবার ধান্দা। আমার স্মোক করতে দারুণ লাগে। কি রকম একটা অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব আসে। খুব ভালো করে তখন বুঝতে পারি ছেলেরা কেন এতো স্মোক করে। ব্যক্তিত্বের অভাব, শক্তি সামর্থ্যে স্মার্টনেসে ঘাটতি সবই পুষিয়ে যায় ধোঁয়ায়। যে ছেলেকে এমনিতে কেউ পাত্তা দেয় না, সে-ই যখন ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে, চোখ আধরোজা করে একটু একটু করে ধোঁয়া ছাড়ে, তার চেহারায় একটা আলাদা ডাইমেনশন আসে। লোকে বলবে তুমি মেয়ে, তোমার তো পুরুষত্বের দরকার নেই, তুমি কেন স্মোক করবে, বাজে অভ্যাস ধরবে একটা! পুরুষত্ব মানে কি? বায়োলজিক্যাল পুরুষত্ব একটা হাস্যকর প্রত্যঙ্গ। ওটার জন্যে কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু আদেশ করবার ক্ষমতা, যে কোনও কাজে একটা অনায়াস সামর্থ্য এইগুলোর জন্য ভেতরে ভেতরে একটা ভীষণ তাগিদ আছে, বুঝতে পারি এগুলো মুন্নির আছে। জীবনে যদি কিছু করতে হয় তো ওটা চাই। মৈথিল, মৌমিতা, আমি, উজান, গুঞ্জন, প্রমিত সব এক স্কুলের ছাত্রছাত্রী। কেউ এক বছর আগে, কেউ পরে। এইচ. এসের পর একেক জন একেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমার ইচ্ছে ছিল আর্কিটেকচার পড়ি। কিন্তু জয়েন্টে পারলাম না। বাবা বলল, ‘হিসট্রিতে তো তোমার বরাবর ভালো মার্ক্স। হিসট্রি নিয়ে পড়াশোনা করো। একেবারেই আর সায়েন্স নয়।’ মৈথিলও তাই বলল। কিন্তু আমরা পুরনো স্কুলের বন্ধুরা সবাই ছাত্রসঙ্খে আছি। নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ হয়। নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা আমরা বলাবলি করি।
এমনিতেই আমাকে সুন্দর দেখতে বলে, নরম বলে, অনেকে অনেক সুযোগ নেয়। লোকের হাবভাব দেখে মনে হয় রূপ দেখানো আর রূপ দেখিয়ে পাঁচজনকে এনটারটেইন করা ছাড়া আমার আর কোনও কাজ নেই। মউমিতা খালি বলবে—‘তোর আর কি? তোর যা রূপ, মুণ্ডু ঘুরে যাবে, যেখানেই যাবি।’
—‘আই অবজেক্ট।’ আমি চেঁচাই ‘রূপ আছে আছে, তাই বলে সব কিছুর সাবস্টিট্যুট সেটা নয়।’
—‘তাহলে অত সাজিস কেন?’
—চুলের যত্ন, গাত্রত্বকের যত্ন, ম্যাচ করে ড্রেস করাটা সাজ হল? এ সব সে জন্মে থেকে মায়ের কাছে শিখেছে। তার মা লিপস্টিক, ব্লাশার ছাড়া বেরোত না। মাসে দু বার বিউটি সেলুনে গিয়ে চুল সেট করে আসতো। ছোট্ট লুকু সে সব সময়ে ধৈর্য ধরে মায়ের ভ্যানিটি ব্যাগ ধরে সেলুনের উঁচু চেয়ারে বসে থাকত। যে সময়ের যা, তা ছাড়া অন্য কিছু মাকে পরাও তো! সন্ধের শাড়ি আলাদা, রাত্রের শাড়ি আলাদা, সকালের আলাদা, বিকেলের আলাদা। লুকুকেও মা ডজন ডজন, ফ্রক করিয়ে দিত, একটু বড় হতে কত রকম ড্রেস। মায়ের তুলনায় লুকু তো কিছুই করে না। মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেছে তার সাজগোজ। আসলে তার গায়ের চামড়াটা শুধু মাখনের মতো নরমই নয়, স্বচ্ছও। ভেতরে সূক্ষ্ম লাল রক্তবহা নালীগুলোর লালিমা যেন দেখা যায়। মনে হয় সে খুব প্রসাধন করেছে। লুকুর চোখের জমি নীল, মণিগুলো গাঢ় নীল, কাচের মতো একটা স্বচ্ছতা সেখানেও। যেন মণির ছিদ্রপথ ধরে বহুদূরে তার শরীর মনের অভ্যন্তরে রোমাঞ্চকর এক যাত্রায় নেমে যাওয়া চলে। শ্যাম্পু করলেই লুকুর চুলে ঢেউয়ের ওঠানামা শুরু হয়। অন্য সময়ে নরম সুগন্ধ, সামান্য সোনালি আভার দ্যুতিময় একঢাল চুল। তার চোখের পাতা মস্ত লম্বা, বাঁকানো। মায়ের একটা কথা লুকুর প্রায়ই মনে পড়ে— ‘লুকু, চেহারাটা তোমার একটা অ্যাসেট। তাকে কোনমতেই নষ্ট করো না। শুধু চেহারার জন্য জীবনে অনেক সুযোগ, অনেক ভক্তি, ভালোবাসা পাবে তুমি, যেগুলো অন্যরা পাবে না।’
কিন্তু শুধু রূপের জোরে কোথাও পৌঁছতে লুকুর ঘৃণা হয়। এমন কোনও দেবপাদপীঠ সে আরোহণ করতে চায় না, যেখানে মানুষের রূপজ-মোহ তাকে অন্ধের মতো তুলে দেবে। গা ঘিনঘিন করে তার যখন বয়স্ক মানুষেরা মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাসের সীট ছেড়ে দেয়। লেডিজ সীটের কাছে লেপটে থাকে মাঝবয়সীরা। দেখুক না, সৌন্দর্য দেখবারই জিনিস। উজানকেও একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে করে লুকুর। কিন্তু অমন লোভ থাকবে কেন দৃষ্টিতে! সেদিন এসপ্লানেডে নেমেছে, মেট্রোয় বাড়ি ফিরবে। একজন ভদ্রলোক মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন—‘আহা হা হা, মে গড ব্লেস ইউ।’ এই প্রতিক্রিয়াটা ভারি অদ্ভুত, ভারি নতুন লেগেছে লুকুর। সুন্দর চেহারার জন্যে যদি লোকের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আশীর্বাদ পাওয়া যায় তো মন্দ কি? কিন্তু তারপর? রূপ তো প্রথম দর্শন। তার পরও তো অনেক দর্শন আছে, তখন? তখন নিজের মূল্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অন্য কিছুও তো চাই। পরীক্ষার মার্ক্সটা পর্যন্ত আশানুরূপ না হলে ওরা বলে ‘তোর আর দরকার কি?’
এ রকম যখন বলে কেউ, তখন রাগে তার শরীরের ভেতরটা কেমন করতে থাকে। কিন্তু ভাবমূর্তি তৈরি করেছে ভদ্র, নরম মেয়ের, চট করে তার থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না। মৈথিলী যে বুদ্ধিতে, অন্যান্য গুণে তার থেকে শ্রেষ্ঠ সেটা সে মেনে নিয়েছে। যা সূর্যের মতো স্বতঃপ্রকাশ তাকে মেনে না নেওয়ার কোনও মানে হয়? তার সঙ্গে লুকুর প্রতিযোগিতা নেই। ছিল না। কিন্তু গুঞ্জন, মৌমিতা, উজান তাকে ছাড়িয়ে গেলে তার ভীষণ অপমান বোধ হত। উজানের সঙ্গে এক ব্র্যাকেটে থেকে তার স্বস্তি হত। আর উজান তো এখন ভিন্ন পথের যাত্রী হয়ে গেছে।
পুরো সিগারেটটা শেষ করে খানিকটা আরাম পাওয়া গেল। সকাল থেকে মনটা খারাপ হয়ে ছিল। এখন অনেকটা হালকা লাগছে। ফ্রাস্ট্রেশন বড় বিশ্রী জিনিস।…
এক এক সময় ভাবি কি দরকার আমার এই দৌড়বাজির! আমি যা, যতটুকু মেনে নিই না কেন? কিন্তু ভেতর থেকে কিসে যেন আমায় কামড়ায়। আমি না দৌড়ে পারি না। সাধে কি আর আমার বাবা অত স্মোক করে। খুব রিল্যাক্সড লাগে। মনটা এখন কত হালকা লাগছে। নিশ্চয়ই পারবো। এম. ভির মতো আমি উড়ে যাচ্ছি দেশে দেশে। উনি সমস্ত ইয়োরোপ ঘুরেছেন, ইউ. এস. এ. তো বটেই। এখন থেকেই ওঁকে আমার অ্যামবিশনের কথাটা বলা উচিত। যাবো স্টেটস, সেখানে এম. এস করব, পি. এইচ. ডি। তারপর ওখানকার য়ুনিভার্সিটিতে পড়াবো। গ্রেটকোট পরা এম. ভির একটা ছবি আছে মার্কিন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে…ওই রকম একটা ছবি…ঘরে চলে যাই… ঘুম পাচ্ছে। ভাবল বটে কিন্তু এতো ঘোর আলস্য লাগছিল যে লুকু সোফার ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল। মাথাটা তার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে; চুলগুলো গোছা গোছা হয়ে ঝুলছে মাথার দু পাশ থেকে। হাতটা সোফার হাতলেরর ওপর। পাশে চৌকোণা টেবিলে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের স্টাব। তার আঙুলে এখনও সিগারেট ধরার ভঙ্গি।
পাখির ডাকে তাদের বাড়ির বেল বাজল। লক্ষ্মীশ্ৰী শুনতে পেল না। তাদের বাড়িতে একটি অল্পবয়সী ছেলে কাজ করে, বুদ্ধিশুদ্ধি কাঁচা, সে সাহেবের নির্দেশমতো ফুটো দিয়ে দেখল লুকুদিদির বন্ধু। দরজা খুলে দিল। দেবপ্রিয়র চোখ দুটো ঈষৎ লাল, চুলটা ভালো করে আঁচড়ায়নি। সে তার স্বভাবের বিপরীত দ্রুত ভঙ্গিতে ঢুকে এলো। ঢুকেই লুকুকে অদ্ভুত একটা ট্যাবলোর মতো ঘুমন্ত দেখতে পেলো। দেবপ্রিয় ছেলেটিকে বলল—চা করতে পারবে? শুধু লিকর হলেই হবে। আমাদের দুজনেরই।
—‘দিদি বেশি দুধ চিনি ছাড়া চা খায় না।’
—‘আচ্ছা আজ খাবে। তুমি নিয়ে তো এসো।’
ছেলেটি রান্নাঘরে চলে গেল। দেবপ্রিয় লম্বা লম্বা পায়ে ঘরটা পার হলো, যেখানে লুকু ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেখানে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে কার্পেটের ওপর বসে পড়ল, তার ঠিক সামনে। পাশের অ্যাশট্রেটা ভালো করে দেখল। আস্তে করে লুকুর আঙুল দুটো ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। নাকের কাছে ধরলো, হঠাৎ কারো দেখলে মনে হতে পারে সুন্দরী লক্ষ্মীশ্রীর আঙুলে সে চুমো খাচ্ছে। তারপর দেবপ্রিয় লুকুর মাথাটা আস্তে আস্তে সোফার পিঠে রেখে দিল। ডাকলো ‘লুকু, লুকু চোখটা খোলো।’
বেশ কিছুক্ষণ ডাকবার পর লুকু সামান্য একটু চোখ খুলল। বেশ লাল।
দেবপ্রিয় বলল—‘লুকু সোজা হয়ে বসো। এতে ঘুমোচ্ছ কেন? ওষুধ খেয়েছে কিছু?’
লুকু সোজা হতে চেষ্টা করছিল, পারছিল না। চা এসে গিয়েছিল। দেবপ্রিয় বলল—‘একটু চা খাও লুকু।’
লুকু এবার কথা বলল—‘চা খাব না।’
—‘হ্যাঁ খাবে। তোমার গ্ল্যান্ড ফুলেছে, গলায় ব্যথা, না? ভালো লাগবে খাও। আমি ধরছি।’ দেবপ্রিয়র হাতে ধরা কাপ থেকে এক চুমুক খেয়ে লুকু মুখ বিকৃত করল।
—‘খাও, আরও একটু খাও।’ একটু একটু করে পুরো দু পেয়ালা চা-ই তাকে ধৈর্য ধরে খাওয়ালো দেবপ্রিয়। তার পরে বলল—‘লুকু, আমার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা কে সরিয়েছে? তুমি? না?’
লুকু অস্পষ্টভাবে হাসছে—‘কেন দেব, আমার খাবার ইচ্ছে হলে কি আমি এক প্যাকেট কিনে নিতে পারি না?’
—‘পারোই তো! আমারটা নিলে কেন?’
—‘পারি না। সিগারেটের দোকানদারগুলো যা বিশ্রী। তা ছাড়া, তুমি? তুমিই বা কেন খাবে? তোমার কিসের কমপ্লেক্স দেব…’ লুকু জড়িয়ে বলল।
—‘কি আবোল-তাবোল বকছ? আমি খাই না খাই সেটা আমার ব্যাপার। তুমি কেন আমার প্যাকেটটা নিতে গেলে? শোনো, প্যাকেটটা আমাকে দাও।’
লুকু উঠতে পারছিল না, কোনমতে উঠতে গিয়ে একবার ধপাস করে বসে পড়ল। তারপর বলল—‘দেব, আমায় একটু ধরবে?’
দেবপ্রিয় সারাক্ষণ ওকে খুব চিন্তিতভাবে লক্ষ্য করছিল। বলল—‘নিশ্চয়ই ধরবো। কোথায় যেতে চাও?’
—‘বাপীর ঘরে।’
ধরে ধরে লুকুকে তার বাবার ঘরে নিয়ে যাবার পর বাবার টেবিল-ড্রয়ার থেকে ‘লুকু এক প্যাকেট সিগারেট বার করল, দেবপ্রিয়র দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আলগা-আলগা গলায় বলল—‘তোমার প্যাকেটটা আমি শেষ করে ফেলেছি দেব, বাপীরটা থেকে তোমাকে গোট্টা একটা দিয়ে দিলাম। আই মে হ্যাভ টু গিভ হিম অ্যান এক্সপ্ল্যানেশন। মাই বাপী ইজ সো পার্টিকুলার। স-ব গোনা গাঁথা। আই নেভার থট ইউ আর সো স্টিঞ্জি। একটা প্যাকেটের জন্যে এ তো!’ বলতে বলতে লুকুর চোখ মুখ কেমন হয়ে যাচ্ছিল। দেবপ্রিয় তাকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বাইরের বেসিনের কাছে নিয়ে গেল। সব বমি করে দিল লুকু। পাতলা সাবুর খিচুড়ি খেয়েছিল, পায়েস, লেবুর রস, কিছুক্ষণ আগেকার চা-স-ব। দেবপ্রিয় বলল—থ্যাংক গড। মুখে-চোখে জল দিয়ে, লুকুকে তার ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সে পাখাটা চালিয়ে দিল। লুকুর গলাটা ভালো করে ঢেকে দিল, পরে বলল—‘লুকু তোমার বাবার প্যাকেটটা কিন্তু আমার চাই না। আমার প্যাকেটটা চাই।’
—‘হারিয়ে গেছে যে!’ লুকু এখন খানিকটা শান্ত, ‘শেষ করে ফেলেছি তো!’
—‘সবগুলো খেয়ে ফেলেছো? আটটাই?’ আতঙ্কিত গলায় দেবপ্রিয় বলল।
—‘আটটা নয়, সাতটা। উঃ দেব তুমি কী কিপটে? একদম শাইলক একটা! সুদ দিতে হবে না কি আরেকটা প্যাকেট, কিংবা আ পাউণ্ড অফ ফ্লেশ?’
—‘শোনো লুকু, কি ভাবে-খেয়েছে?’
—‘অফ অ্যান্ড অন! একলা হতে পারলেই খেয়েছি।’
—‘ভালো লেগেছে…নিশ্চয়!’
—‘ওহ শিওর!’
—‘তুমি খালি প্যাকেটটাই আমাকে দাও।’
—‘খালি প্যাকেট?’ লুকুর চোখে বিস্ময়।
—‘লুকু, প্লীজ!’
—‘দেখো টেবিলের তলায় গার্বেজ বিন আছে। ওখানে থাকতে পারে।’
দেবপ্রিয় টেবিলের তলা থেকে কাগজের ঝুড়িটা টেনে আনছে, হাঁটকাচ্ছে, লুকু অবাক হয়ে দেখছে। ওটা পেল শেষ পর্যন্ত। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল—‘লুকু তুমি যতক্ষণ না সুস্থ বোধ করছ, চুপচাপ শুয়ে থাকো, আমি চলি।’
—‘সে কি বসবে না? গল্প করবে না? কেওড়াখালির গল্প!’
—‘কেওড়াখালি আমি যাইনি। ওরা এখনও ফেরেনি যদ্দূর জানি। আমার বড্ড জরুরি কাজ আছে’ আরেক দিন এসে আড্ডা মারা যাবে।’
লুকুর এতো ক্লান্ত লাগছে যে সে তার হতাশাটাকেও ভালো করে প্রকাশ করতে পারছে না। দেবপ্রিয় ঘর থেকে বেরোতে ফিরে তাকাল, বলল—‘লুকু, তুমি আর সিগারেট খেয়ো না।’
—‘হোয়াই? হু আর ইউ টু সে সো?’
—‘আমি ডাক্তার। লুকু, আমি বন্ধুও। তুমি স্মোক করবে না। কেউ খেলাচ্ছলে, গল্পচ্ছলে দিলেও না। কথাটা শুনো।’
দেবপ্রিয় ঘর থেকে বেরিয়ে সামান্য গলা তুলে ডাকল—‘ঝড়ু!’
ঝড়ু রান্নাঘরের পাশের স্টোর রুম থেকে বেরিয়ে এলো। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল দেবপ্রিয়র দিকে। তারপর পেছন পেছন গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।
অধ্যায় : ৭
…‘সেদিন আপনাকে বলা হয়নি ছাত্রসংঘ থেকে আমার তফাত থাকার কারণ। সব কথা আজও বলতে পারছি না। সময় আসেনি। শুধু এইটুকু বলছি আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল করে দেবার একটা ষড়যন্ত্র কোথাও খুব গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। আপনারা সতর্ক থাকবেন। আমি দরকার হলে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই ষড়যন্ত্র আটকাবো। ওখানে কাজ করার লোক এখন অনেক। কিন্তু ডিফেন্স ফ্রন্ট-এ কেউ নেই। চট করে কাউকে বিশ্বাসও করতে পারছি না। ঝড়ু ওঠার আগে প্রকৃতির চেহারা এমনি হয়। আমার দেখা আছে। সে সময়ে মাঝিরা নদী থেকে ডিঙি তুলে ফেলে। আমি এখন ডিঙি তুলে ফেলার পক্ষপাতী…।’
ছেলেটা এতো ভাবুক-প্রকৃতির, কবি-কবি তা তো জানা ছিল না? কথা বলে কম। এখনকার ছেলেমেয়েরা ঠিক এই ভাষা, এই সব তুলনা, চিত্রকল্প ব্যবহার করে না। চিঠিটা আদ্যোপান্ত দুবার পড়লেন মেধা। হঠাৎ মনে হল দেবপ্রিয় ছেলেটি কোনও মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে না তো? প্যারানয়েড যাকে বলে! মফস্বল শহরের অপেক্ষাকৃত সরল পরিবেশ থেকে সে অতি জটিল শহুরে সভ্যতার আবর্তে পড়েছে, অনেকেই মানিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু ছেলেটি অতি বুদ্ধিমান, উপরন্তু অন্তর্মুখী প্রকৃতির। সে তো সহজে তাঁর এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে চাইবে না! ওকে অন্যভাবে সুস্থ করতে হবে। ও খুব অস্পষ্টভাবে ওর ভয়ের একটা ধারণা দিয়েছে। ওকে সাহস দিতে হবে যাতে ও স্পষ্ট করে ওর ধারণার কথা বলতে পারে। বড় বড় কাজের সামনে দাঁড়িয়ে এ রকম ভেঙে পড়তে তিনি অনেক বিপ্লবীকে দেখেছেন। মেধা তাঁর ঠিকানা ও ফোন নম্বরের নোটবইটা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন। ফোন নম্বর রয়েছে মৈথিলীর, লুকুর, উজানের, গুঞ্জনের…। দেবপ্রিয়র কিছু নেই। কোনও ঠিকানা সে চিঠিতেও দেয়নি। কি করে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তিনি?
উজানকে ফোন করলেন মেধা। উজানের দাদু ফোন ধরেছেন বোধ হয়। ভাঙা গলা। কথাগুলো ফস্কে ফস্কে যাচ্ছে বোঝা যায়। দাঁত পরেনি বোধ হয়। উজান নাকি সবে ফিরেছে কেওড়াখালি থেকে। একটু যেন অসন্তুষ্ট ভদ্রলোক। মেধা নিজের পরিচয় দিয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।
সারা পৃথিবী একভাবে চলছে। ভারতবর্ষ চলবে অন্যভাবে। এখানে এখনও পণ দিয়ে বিয়ে হচ্ছে আইন করে তা বন্ধ করে দেওয়ার পরেও, এখনও এখানে পণের প্রশ্নে বউ পিটিয়ে হত্যা করা হয়, এখনও বিধবা মেয়ে বিয়ে করার অপরাধে নিজের মা মেয়েকে খুন করে ফেলে। কলকাতার বুকে কোনও ছেলেকে কোনও মেয়ে ফোন করলে অভিভাবকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বোধ হয় এই সামাজিক পরিবেশে ভালোই খাপ খেয়ে যায়। ঢং ঢং করে ন’টা বাজল। হঠাৎ মেধার মনে হল যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি ক্রমাগতই জড়িয়ে পড়ছেন, তাদের সঙ্গে মেলামেশাটা যেন বড্ড বেশি তত্ত্বগত স্তরে হচ্ছে, তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তিনি কিছু জানেনও না, জানার চেষ্টাও করেন না তেমনভাবে। নিজেদের পরিবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি, তাদের বাবা মা দাদু এঁরা কে কিভাবে এদের গ্রহণ করেন এগুলো জানা দরকার। কারণ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু স্বার্থের তো নয়ই, শুধু অন্ধ ভালোবাসারও হওয়া উচিত নয়। বাবা-মার আদর্শ আর ছেলে-মেয়ে কী করতে চায়, এ দুটো জিনিসের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য, খানিকটা আপস থাকা দরকার। নইলে পরিবার ভেঙে যেতে থাকবে। পরিবারের কোনও বিকল্প নেই। মুক্ত মানুষের যৌথ সমাজব্যবস্থা, সরকারের হাতে সন্তানের নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ কোনও কিছুই পারিবারিক সম্পর্কের মাধুর্য ও সৌন্দর্যের জায়গা নিতে পারবে না। গাছপালা, ফুল পাখি, আকাশ, মেঘ, বাতাস মিলিয়ে প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব যেমন সুস্থ সুন্দর জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, ঠিক তেমনি অপরিহার্য মায়ের টান, বাবার দায়িত্বশীল স্নেহ, ভাইবোনের পারস্পরিক মমতা। যান্ত্রিক এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও অগ্রগতি যদি পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে তো সে মূল্যে যন্ত্র সভ্যতা, এমনকি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিও কেনার কোনও অর্থ হয় না।
কেওড়াখালিতে ওদের সঙ্গে তাঁর যাওয়া উচিত ছিল। আসলে নন্দিতা ও সূর্যর সঙ্গে ঘুরে এসে তিনি একটা খসড়া করে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রথম পর্বটায় ডাঃ সোম যান, দ্বিতীয় পর্বে তিনি যাবেন। এখন মনে হচ্ছে তাঁরই যাওয়া উচিত ছিল। ছেলেমেয়েদের একলা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। এর থেকে সত্যিই অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। ডাঃ সোম একেবারে বোমভোলা ধরনের মানুষ। আর মৈথিলী তো একটা কুড়ি-একুশ বছরের বাচ্চা মেয়ে। খুব পরিণত, বিচক্ষণ,। কিন্তু বয়সটা তো অল্পই। তাঁকে যখন উপদেষ্টা হিসেবে চেয়েছে এবং তিনিও রাজি হয়েছেন তখন তাঁকে আরও ভেতরে ঢুকতে হবে, আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। আসলে বহুবছর আমেরিকায় থেকে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখে দেখে তাঁর অভ্যাসটা এই রকম হয়ে গেছে। কিন্তু এটা ভারতবর্ষ। এখনও এখানে উপমন্যু-উদ্দালক, এখনও এখানে গার্গী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী ছেলে-মেয়েদের রক্তে মিশে আছে। ওরা অনেকেই গুরুর আশীর্বচনের ওপর নির্ভর করে, শুধু আচার্য বলেই তাঁর নেতৃত্ব, অনেক অন্যায়ও মেনে নেয়। নিয়ে থাকে। এ তিনি প্রতিনিয়ত দেখছেন।
দরজায় বেল বাজল। নিশ্চয় উজান। বেচারি বোধ হয় চান-টান সারছিল, মিস ভাটনগরের ফোন এসেছিল, তাকে ডেকে দেওয়া হয়নি বলে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে। কোনও মানে হয়! দরজা খুলে দিয়ে মেধা দেখলেন রঘুনন্দন।
—‘আরে?’
–‘এলাম। বড়ই প্রাণের দায়ে মেধা…’ রঘুনন্দন ভারি পায়ে ভেতরে ঢুকলেন।
—‘বসো, কফি আনি।’
—‘আনো। আর কিছু না।’
মেধা কফি নিয়ে এসে বসলেন। রঘুনন্দন আপনমনে একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। চোখ আরামে বুজে আসছে। মেধা কফিটা নামালেন একটু শব্দ করে। চোখ মেলে রঘুনন্দন বিনা ভূমিকায় বললেন—‘আমার মেয়েটা ভাবালে। রাতে বাড়ি ফিরছে না। কি সব আউল-বাউল ট্যাঁকে করে ঘোরে, হিপি-টিপি হয়ে যাবে না কি বলো তো? জানো কিছু?’
আজকে মেধার অভিজ্ঞতায় এটা দ্বিতীয় অভিভাবকীয় প্রতিক্রিয়া। তিনি বললেন—‘আমি জানি এ কথা কেন মনে হল তোমার?’
রঘুনন্দনের পরনে গ্রে রঙের স্যুট। ব্রাউন টাই। চুলগুলো পরিষ্কার পাট পাট আঁচড়ানো। তা সত্ত্বেও মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। খুব সম্ভব অফিস থেকে এখনও বাড়ি ফেরেননি। তিনি বললেন—‘কি জানি! মেধাদি মেধাদি করে তো ক্ষেপে যাচ্ছে মেয়েটা। তিনি বললেন—তার মা মেয়ের কথা ভেবে ভেবে দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে এদিকে। —‘আমি জানি এই যদি তোমার ধারণা হয়, তবে আমার ওপর ভরসাটাও রাখা উচিত ছিল।’
—‘দেয়ার য়ু আর। তোমাকে যদ্দূর জানি ভয়ঙ্কর উত্তেজক বিস্ফোরক তুমি মেধা, দায়িত্বশীল একেবারে নয়। অন্তত ছিলে না। আজ যে হয়েছে এ ধারণা করার কোনও কারণ দেখি না।’
মেধা ঠিক করে নিয়েছেন রাগ করবেন না, অন্তত দেখাবেন না। তিনি স্মিত মুখেই জিজ্ঞাসা করলেন—‘এ ধারণার কারণ দেখাও। শুধু শুধু কতকগুলো অভিযোগ তুললেই তো হবে না!’
—‘কারণ আমায় বলতে হবে?’ রঘুনন্দন কি ঈষৎ উত্তেজিত? ‘ডাঃ ভাটনগরের মেয়ে হয়ে কীর্তিদা মুক্তির বোন হয়ে ঊনসত্তর সালে তুমি প্রায় জেলে চলে যাচ্ছিলে? যাচ্ছিলে না? তখন তুমি কতটুকু? মুন্নির চেয়েও বোধ হয় ছোট। বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে তোমার আরও একবার জেলে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। প্রজ্ঞা সেবার বুদ্ধি করে তোমাকে হংকং-এ আটকে, তারপরে য়ুরোপ বেড়াতে নিয়ে না গেলে তুমি হয়ত ঠিক এই মেধা হয়ে আর জেল থেকে বেরোতে না।’ …রঘুনন্দন আবার দেশলাইয়ের কাঠিটা কানে ঢোকালেন। গাঢ় নীল শাড়ির অন্তরালে মেধা নিজেও যেন নীল, সেই সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠছেন, গলার স্বর থেকে রস উবে যাচ্ছে একটু একটু করে, বললেন—‘বলো, বলো রঘুদা, থামলে কেন? এই তোমার অভিযোগ? চুরি ডাকাতি কি হত্যার অপরাধে নিশ্চয়ই জেলে যাচ্ছিলাম না। আর দেশসুদ্ধ বয়স্ক লোক যখন নিজেরা ভাত পেয়েছে এই আত্মপ্রসাদে মগ্ন হয়ে হাই তোলে আর ভাত-ঘুম দেয় তখন ছোটদের ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া উপায় কি? নীলকমল না জাগুক, লালকমলকে তো জাগতেই হয়! সে হয়ত অতটা প্রাজ্ঞ নয়, তাই রাক্ষসের কবলে পড়াও তার ভবিতব্য। যাই হোক, এসব বারবার বলে তো লাভ নেই! সে অধ্যায় পুরনো হয়ে গেছে। সে আমার একার সিদ্ধান্ত নয়। একার সাফারিংও নয়। আমার নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণ তুমি কোথায় পেলে?’
চোখটা আধখোলা করে রঘুনন্দন বললেন, ‘অমিয় সান্যালকে বিয়ে করে তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কোনও সম্পর্ক রাখলে না।’
—‘তুমি কি করে জানলে?’ মেধা অবাক হয়ে গেছেন।
—‘কেন? তুমি কি নিজের কার্যকলাপ গোপন রাখতে চাও?’
—‘যতটা দরকার তার বেশি কখনোই নয়। তখন প্রয়োজনে চেয়েছিলাম। জেলবন্দী একটা মানুষ যদি ক্রমেই চিঠিপত্র দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তার ঘনিষ্ঠরা যদি ক্রমশই তোমাকে এড়িয়ে চলতে চায়, কিভাবে তুমি সম্পর্ক কনটিনিউ করবে?’
—‘কাজটা শক্ত, খুবই শক্ত। কিন্তু মেধা তুমি চেষ্টাও করোনি। এটা ঠিক দায়িত্বশীল নারীর বা মানুষের কাজ নয়।’
মেধার মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে, রঘুনন্দন আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে বললেন—‘রাগ করো না মেধা আমার প্রতিও তুমি দায়িত্ব পালন করোনি।’
—‘অন্যায় কথা বলো না রঘুদা’, মেধার স্বর এখন আড়ষ্ট’, ‘আমি তোমায় কখনও কোনভাবে প্রশ্রয় দিইনি।’
—তোমাদের মনে হচ্ছে দাওনি। আমার মনে হচ্ছে দিয়েছ। যাই হোক ওটা না হয় কনট্রোভার্শিয়াল, ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু এদের মাথায় কী ঢুকিয়েছ বলো তো? মুন্নি বাম রাজনীতি করলে আমার ঘোর বিপদ। বুড়ো বয়সে কি শেষে ডিমোটেড হবো? জানি, তুমি আমার বিপদের কথা ভেবে আমার মেয়েকে সাবধান করবে না, তবু না জানিয়ে পারছি না।’
মেধা বললেন—‘রাজনীতি আমি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি রঘুদা। কোনদিন করেছি বলেও পুলিশের খাতায় প্রমাণ করতে পারবে না। নইলে সরকারি কলেজে চাকরি নিয়ে ফিরে আসতে পারতাম না। এসব কথা তোমার মতো সরকারী লোকের কেন জানা নেই তা জানি না। আর তোমার মেয়ে যেটা করবে মনে করে সেটা করে তবে ছাড়ে, আমার কাছে মাঝে-মধ্যে শুধু একটু পরামর্শ নেয়। তুমি কি বলছো পরামর্শটাও ওকে দেবো না?’
—‘ওকে একটু হোম-এর দিকে চালিত করো। যদি পারো। “চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম””—এই সোজা কথাটা মেয়েটাকে বোঝাতে পারি না মেধা। ও অনেকটা তোমার মতোই। আমার মেয়ে অথচ তোমার মতো। কী সাংঘাতিক বলো তো?’
রঘুনন্দন উঠে পড়লেন; বললেন—‘মনে রেখো প্লীজ।’
—‘ও বাম ডান কোনও রাজনীতিই করে না।’
—‘করে না?’—অবিশ্বাসের সুরে বললেন রঘুনন্দন।
—‘ও দেশের সচেতন, দায়িত্বশীল নাগরিক। শুধু নিজের কেরিয়ার নিয়ে মত্ত থাকতে তোমার মেয়ের ঘৃণা হয়, অবশ্য ইফ শী ইজ কেপেবল অফ হেট্রেড।’
—‘এগুলো তোমার অ্যানালিসিস?’
—‘আমারই। কিন্তু এগুলো স্বপ্রকাশ। ওকে সিরিয়াসলি নিলেই বোঝ যায়। ও তো খুব জটিল মানুষ নয়!’
—‘বাঁচালে, রঘুনন্দন দরজার ওপারে যেতে যেতে বললেন, ‘আমার ধারণা ছিল ও খুব জটিল, গোপনতাপ্রিয়… আসলে বসা হয় না। যদি বা হয় এতো দীর্ঘ সময় পরে পরে যে এসব প্রসঙ্গ তুলতে ইচ্ছে করে না।’
—‘অথচ এগুলোই আসল। সন্তানকে জানাটা বাবা-মার সবচেয়ে বড় কাজ, বাবা-মা হিসেবে। এনি ওয়ে, আমি তোমার প্রতি দায়িত্বশীল না হওয়ায় তোমার কিন্তু লাভই হয়েছে’, মেধা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন।
—‘আর তোমার? তুমি কি লাভ-ক্ষতির ঊর্ধ্বে না কি?’
—‘ঠিক তাই…। এতক্ষণে একটা ঠিক কথা বললে।’
মেধা হাসিমুখে বললেন, যদিও তাঁর ভেতরটা জ্বলছিল। রঘুনন্দন ত্রিপাঠীর গাড়ির আলো বাঁক ফেরবার আগেই তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন।
দোতলায় এসে কোল্যাপসিবলটা টেনে দিলেন অভ্যাসমতো। তালা লাগাবার সময়ে একবার মনে হল উজান যদি আসে। ঘড়ির দিকে তাকালেন, না উজানের আসবার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই। ফোনও করল না। ছোড়দারা অনেক দিন আসেনি। হঠাৎ একা-একা লাগল। প্রজ্ঞা যেখানেই থাকুক, দু-তিন মাস অন্তর একবার অন্তত দীর্ঘক্ষণ ধরে ফোন করে। ফোনে কি ওকে বকা যায়? বকার জন্য দু চার দিনের অন্তত অবসর পাওয়া দরকার। তাঁর গোপন কথাটা প্রজ্ঞার ফাঁস করে দেওয়া উচিত হয়নি। বিশেষত, রঘুনন্দন ত্রিপাঠীর কাছে। তিনি বিয়ে করেছিলেন আঠার উনিশ বছর বয়সে সে বয়সটা বীরপূজার, আত্মনিবেদনের, বিদ্রোহের বয়স। বন্ধু রোকেয়া রোদ, জল, ঝড়ু উপেক্ষা করে মিছিল করত, বক্তৃতা করত। এইভাবে একটি সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে যার কিছুর অভাব নেই সে মার্কসিজমের জন্য জীবনপাত করে দিচ্ছে, এতে একটা অসামান্য বিস্ময় এবং রোমাঞ্চ ছিল। আত্মগ্লানি হত একেক সময়ে। রোকেয়া কথা বলত অত্যন্ত মধুরভাবে, কখনও তর্কাতর্কির সময়ে মেজাজ খারাপ করত না। উল্টোনো ড্রাম কি প্ল্যাটফর্মের ওপর তার বক্তৃতা ছিল এক রকম—ধারাল, জ্বলন্ত, কিন্তু মুখোমুখি বা পাশাপাশি বসে সে যখন শ্রেণীসংগ্রাম, সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করে বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থান, প্রোলেতারিয়েতদের আবির্ভাব, উৎপাদন-উৎপাদকের সম্পর্ক, সংঘবদ্ধ প্রোলেতারিয়েতের শাসনযন্ত্র দখল এবং কমিউনিজমের প্রথমাবস্থায় সব কিছুর সরকারি মালিকানার তত্ত্বের কথা বোঝাতো তখন সেটা প্রায় প্রেমালাপের মতো মধুর এবং রোমাঞ্চকর শোনাতো!
মাথার ওপর চিকন সবুজ পাতার মধ্যে দিয়ে হলুদঝুরি ফুল নেমেছে। কেউই তার নাম জানে না। মেধা সেগুলো নিয়ে কবিতা রচনা করত ‘কুমারী লতার ডালে ডালে/কত মৃত আকাঙক্ষার কর্ণভূষা দোলে,/ হায়, ধু ধু অগ্নি জ্বলে।’ রোকেয়া হেসে বলত এই রোমান্টিক কবিতা তোকে কোথায় কতদূরে নিয়ে যেতে পারবে মেধা! আর তোকে যদি ব্যক্তিগতভাবে একটা মূর্খের স্বর্গে নিয়ে যায়ও শত সহস্র লক্ষ কোটি মেহনতি মানুষ বুর্জোয়া শিল্পের যন্ত্রের হাতে যাদের শ্রমের আনন্দ ও মর্যাদাটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়েছে, যাদের শুধু শ্রমের প্রয়োজনে অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখার জন্য যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে এক কড়াও বেশি দেওয়া হয় না, তাদের কোথায় নিয়ে যাবে?
মেধাকে স্বীকার করতেই হত এই সব কাব্যচর্চা তাকে জীবনের গভীরতর স্তর যাকে রোকেয়া মূর্খের স্বর্গ বলছে, সেখানে নিয়ে যেতে হয়ত পারবে। কিন্তু চাষী, চটকলের শ্রমিক এদের সেখানে পৌঁছবার কোনও আশা নেই। এবং যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই রকম নিরন্ন, নিরক্ষর, নিঃসহায়, সেখানে সমর্থ মানুষের পক্ষে কাব্য-চৰ্চা, এমন কি নিছক বিদ্যা-চর্চাও স্বার্থপরতার শামিল।
—‘হ্যা, তুই ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে পাশ করবি, তারপর কোনও কলেজে, কি য়ুনিভার্সিটিতে লেকচারার হয়ে ঢুকবি, লেকচারার, রীডার, প্রোফেসর…। ভালো ভালো শাড়ি পরবি। খুব পদস্থ কাউকে বিয়ে করবি, দুটি তিনটি ব্রিলিয়ান্ট সন্তান, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটবে, হয়ত বা এ দেশে থাকবিই না। তোর বাড়ির যা ব্যাকগ্রাউন্ড, তাতে সেটাই স্বাভাবিক। যা মেধা, তাই যা। ইন দা মীন টাইম…এই সব ইশাক, রজ্জব, হরিপদ, রামহরি, শিবু, কেষ্টা, রানী খালেদা, লক্ষ্মীমণি, অন্নদা, এরা মুখে রক্ত উঠে মরে যাবে। জেনারেশনের পর জেনারেশন একভাবে মরবে। আল্লার দোয়া চাইবে, দেবমন্দিরে দণ্ডি কাটবে, পীরের দরগায় শিরনি চড়াবে, আর মরে যাবে। আমি রোকেয়া, আমার মতো আরও অনেকে যেমন অমিয়দা, সুন্দরলাল অসীমাভ আমরা যারা প্রতিবাদ করবো, ওদের মুখে ভাষা দিতে চাইবো, ওদের গর্জে উঠতে শেখাবো, তারা জেলে পচব।’
মেধা বলতো—‘কিন্তু উপায়ই বা কি? রোকেয়া আমি যদি আজ আমার জীবনটা স্যাক্রিফাইসও করি, তাতেই কি জেনারেশনের পর জেনারেশন মানুষের মুখে রক্ত উঠে এইভাবে মরা থামবে? থামবে কি? বল তুই?’
রোকেয়ার চোখ জ্বলজ্বল করত—‘যদি বলি থামবে?’
‘আমার একার চেষ্টায়? থামবে? তুই বলছিস কি?’
—‘তুই মনে করছিস তুই একা। কিন্তু আসলে তো তুই একা নয়। তোর মতো আরও অনেক বুদ্ধিজীবী পরিবারের সমর্থ ছেলেমেয়ে আছে যারা শক্তিটা নিজেদের কেরিয়ার গড়বার কাজে পুরোপুরি খরচ করে। তারা যদি বোঝে। বুঝছেও, সারা পৃথিবী জুড়ে বুঝছে। দলে দলে যোগ দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে তো তুই একা থাকছিস না।’
—‘ঠিক আছে, দশ, বিশ, ত্রিশ জন আমার মতো যোগ দিল। তাতেই বা এই কোটির দেশে কি হবে?’
—‘কি করলে কিছু হবে তুই-ই বল।’
একটু ভেবে নিয়ে মেধা বলল—‘সরকারকে সচেতন হতে হবে, সরকারি লেভল থেকে যদি কতকগুলো সঠিক নীতি নেওয়া হয়, একমাত্র তবেই…’
—‘বাস, বাস। তুই তাই মনে করিস তো?’ রোকেয়া উৎসাহে টগবগ করছে।
‘সরকারকে সচেতন করাটাই আপাতত আমাদের কাজ। আপাতত।
প্রধানত রোকেয়ার উৎসাহেই অমিয়নাথ সান্যালের ক্লাসে যাওয়া। নকশাল আন্দোলনের শুরুতে যখন চারদিকে গরম হাওয়া বইছে, সেই সময়ে পার্টি অফিসে অমিয়নাথ সান্যাল নামজাদা মার্কসিস্ট নেতার সঙ্গে মেধা ভাটনগরের বিবাহ। সান্যালদা বললেন—‘মেধা তোমার পদবী পাল্টানো না পাল্টানো তোমার ইচ্ছে। বিবাহ মানে আমি বুঝি দুটি স্বাধীনতার সমন্বয়।’ মেধা পদবী পাল্টালো না। ঠিক হয়েছিল আস্তে আস্তে খবরটা ভাঙা হবে বাবা-মার কাছে। সাতদিনের মধ্যে সান্যালদা অজ্ঞাতবাসে চলে গেলেন।
ওঁর কিন্তু আসল ইচ্ছে ছিল রোকেয়াকেই বিয়ে করা। রোকেয়া প্রায় শিশুকাল থেকে মার্ক্সসিস্ট বুলি কপচে মানুষ। অক্লান্ত কর্মী। কতজনকে যে সে দলে নিয়ে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। পার্টির নেতারা তার কাছে কৃতজ্ঞ। তার জ্বলন্ত আত্মপ্রত্যয়ের মূর্তি নিশ্চয় অনেকের মনে আগুন জ্বালাত। অমিয় সান্যালের সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করছে সে একেবারে গোড়ার থেকে। এই বালিকার টিউটর ছিলেন অমিয়দা।
ওকেই খুব সম্ভব বিবাহের প্রস্তাবটা প্রথম দিয়েছিলেন সান্যালদা। রোকেয়া কিছুতেই রাজি হয়নি। ব্যাপারটা আন্দাজ করে মেধা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—‘কেন তুই অমিয়দাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিস না?’
রোকেয়া বড় অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিল, একেবারেই রোকেয়ার মতো নয়, বলেছিল —‘আমাদের পরিবারে আমি একটা প্রচণ্ড প্রবলেম মনে করে সব্বাই। আমাকে, দাদাকে পড়াবার জন্য অমিয়দাকে টিউটর রাখলেন বাবা, পড়ালেখা তো শিখলাম ভালোই, সেই সঙ্গে বাবার উল্টো রাজনীতি। বাবা গোঁড়া কংগ্রেস, এত বছর ধরে এম. পি। দাদা আমি মার্ক্সসিজম করি বলে বাড়িতে ভীষণ অশান্তি। মাকে এর জন্য বাবার কাছে ভীষণ লাঞ্ছনা খেতে হয়। এগুলো আমি যথেষ্ট স্যাক্রিফাইস বলে মনে করি। ফ্যামিলির প্রতি কর্তব্য আমি পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারি না। বাবার আশ্রয়ে আছি, মায়ের স্নেহ ভালোবাসা পাচ্ছি এতো সত্ত্বেও, না হলে কি আমি এতো নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারতাম? কিন্তু বাবাকে আমি ফারদার আঘাত দিতে পারব না। কাউকে বলিসনি, আমি অমিয়দা এবং অন্যান্যদের সবাইকে বলেছি—‘আমি বিয়েতে বিশ্বাস করি না। বিয়ে করবই না।’
—‘বাবাকে খুশি করতে কি তা হলে কংগ্রেসী বিয়ে করবি তুই?’
—‘বাবাকে খুশি করতে আমি বাবার দেখে ঠিক করে দেওয়া পাত্রকে চোখ বুজে বিয়ে করে ফেলব। খুব সম্ভব সে নন-পলিটিক্যাল হবে।’
মেধা রোকেয়াকে বুঝতে পারছিল না। রাজনৈতিক জীবন সে অরাজনৈতিক গার্হস্থ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াবে কি করে? মুখে যার মার্ক্সসিজম-লেনিনিজম ছাড়া অন্য বুলি নেই, সাহিত্য শিল্পকলা সব কিছুকেই সে মার্ক্সের নিরিখে পরীক্ষা করে তবে ছাড়পত্র দেয়, বেশির ভাগ সময়েই দেয় না, কি করে সে বাবার নির্বাচিত বিবাহ করে দিন কাটাবে? কী চায় ও?
অমিয় সান্যাল যখন তারপর তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন তার বিভ্রান্তি আরও গভীর হল। সে সাহস করে বলেছিল—‘কিন্তু আপনি তো রোকেয়াকে ভালোবাসেন, সান্যালদা, আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন?’
অমিয় সান্যাল জ্বলজ্বলে চোখে দূরের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—‘ভালোবাসা কথাটা তুমি যে অর্থে ব্যবহার করছ, সে-অর্থে সান্যালদা কাউকে ভালোবাসে না। বাসতে পারে না। রোকেয়া শক্তিমতী মেয়ে, ওই শক্তি আমার প্রয়োজন, তুমিও তাই, তুমি আমার পাশে এলে আমার হাত আরও শক্ত হবে।’
—‘বিয়ে না করলেও তো তা করা যায়।’
—‘যায়। অতটা নিশ্চিন্ত থাকা যায় না মেধা। বিবাহের বন্ধনটা দরকার। এখনও।’
—‘আপনি বিবাহ-বন্ধনে বিশ্বাস করেন অমিয়দা? আপনি?’ মেধার বিস্ময় বুঝি আজ আর ফুরোবে না।’
—‘হ্যাঁ করি, পুরোপুরি মুক্তির আগে কিছুদিনের বন্ধন। পুরোপুরি কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার আগে যেমন সরকারি নিয়ন্ত্রণ।’
সান্যালদার চোখ দূরমনস্ক। কিসের একটা দ্যুতি সেখানে। মেধার এতোসব জিজ্ঞাসার দরকার ছিল না। কারণ অমিয় সান্যালকে সে তখন দেবতার সগোত্র মনে করে। অমিয়দা তাঁর আদর্শবাদের প্রয়োজনে বিয়ে করলেও মেধা বিয়ে করল তার নিজের প্রয়োজনে। রেজিস্ট্রি করে, সকলকে মিষ্টি খাইয়ে দুজনে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। পর দিন থেকে অমিয় সান্যাল পার্টির অনেক গোপন কথা, অনেক নতুন পথ খোঁজার বিবরণ তাকে দিতে থাকলেন। যার বিন্দু বিসর্গ মেধা আগে জানত না। অমিয় বললেন,—শিগ্গীরই হয়ত আমাকে দার্জিলিঙের ওদিকে গিয়ে থাকতে হবে দীর্ঘ দিন। তোমাকে বেজিং যাবার জন্য তৈরি হতে হবে।’
সাতদিনের মধ্যে বিবাহটা সম্পূর্ণ করার সুযোগ এলো না। তারপর দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস পর্ব। দিন দুপুরে যখন জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা থেকে অমিয় সান্যালকে অ্যারেস্ট করল পুলিস, মেধা তখন এম. এর ছাত্রী, বেণী দুলিয়ে য়ুনিভার্সিটিতে ক্লাস লেকচর শুনছে। খবরটা পেতে যেন একবার বুকের মধ্যে সাপে ছোবল দিল। সেই তীক্ষ্ণ কষ্টের স্মৃতি এখনও চেষ্টা করলেই মনে পড়ে। স্মৃতি তার অত্যন্ত শক্তিশালী।
এগুলো ইতিহাসের পাতা। কালের অমোঘ নিয়মে উল্টে যাবেই। মেধা এটা জেনে গেছেন। অমিয় সান্যাল তাকে বুঝতে পারেন নি, তিনি রোকেয়াকেও বুঝতে পারেন নি। আটষট্টি সালের বারোই ফেব্রুয়ারি দুটি ভিন্ন গ্রহের মানুষে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। অমিয়নাথ যে কারণে এই চুক্তি করেন, তা সফল হয়নি। মেধার পরবর্তী কার্যকলাপ, তার সব কিছুর ভেতর ঢাকবার, প্রশ্ন করবার, সংশোধন করবার, পরিকল্পনার চোরা গর্তগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবার বাতুল ইচ্ছেগুলোকে দমন করতে করতে অমিয়নাথ নিশ্চয়ই জেলের ভেতর থেকেই বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন বন্ধনের সূত্রগুলো কাজ করছে না। প্রথম প্রথম চিঠি চালাচালি হত লোক মারফৎ। অনেক সাবধানতা অবলম্বন করে। জেলে যাবার পর তিনি সোজাসুজিই লিখতে লাগলেন, জেলকর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে, মেধাও লিখতেন, গোপন নামে। সেই চিঠি পত্রের তর্কাতর্কি ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠল। তারপর বন্যা সরে গেল। মেধার মুক্তি ভেতর থেকেই এসে গেল।
রঘুনন্দন ত্রিপাঠী এই ইতিহাসের আদি-মধ্য-অন্ত কিচ্ছু জানে না, সে দিব্যি জাজমেন্ট সীটে বসে গেল। বাঃ! তিনি অমিয় সান্যালের প্রতি কর্তব্য করেননি, রঘুনন্দন ত্রিপাঠীর প্রতি কর্তব্য করেননি! অধিকার কি তার? এক সময়ে সে মেধার পাণিপ্রার্থী হয়েছিল এবং তাঁর ছোড়দা মুক্তিনাথের প্রাণের বন্ধু ছিল—এই। ভারি চমৎকার। মেধা নিজের মধ্যেকার জ্বলুনি কমাবার জন্যে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। দিতেই লাগলেন। জ্বলুনি কমছে না। বাবা নেই যে দৌড়ে গিয়ে বলবেন—‘বাবা দেখো না, ওই লোকটা আমাকে কিভাবে অপমান করছে!’ মা নেই যে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে চোখের জল ফেলবেন। এটা মেধা খুব মাঝে মাঝে করতেন। মা প্রথমটা জিজ্ঞেস করতেন—‘কি হয়েছে কেন কাঁদচ্ছিস?’ মেধা কোনও সঙ্গত কারণ দেখাতে পারতো না। হয়ত একটি নিম্নবিত্ত বান্ধবীর শুকনো মুখ, হয়ত ফুটপাতের ওপর ভিখারি শিশুর ফোলা পেট নিয়ে চিতপাত হয়ে শুয়ে থাকা, কিম্বা সদ্য গোঁফ ওঠা কোনও কিশোরকে কোনও বয়স্ক পদস্থ ভদ্রলোকের অপমান….এগুলো কি বলা যায়।
—‘কেঁদে নে খুকু, কেঁদে নে। মনটা মাঝে মাঝে বড্ড ভারি হয়ে যায়।’ মা বলতেন।
অনেক দিন পর্যন্ত মনটা বড্ড খচখচ করত। মা চলে গেলেন, বলা হলো না, বাবা চলে গেলেন বলা হল না। বিয়ে করেছেন এতো বড় খবরটা মা-বাবার কাছে চেপে রাখা, এতো সোজা কাজ নয়। এখন মনে হয় খবরটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল না পুরো জীবনের, পুরো সময়ের প্রেক্ষিতে। শিশুকালের খেলা। তাই তাঁর সহজাত বোধই তাঁকে নীরব রেখেছিল। প্রজ্ঞারও কোনও অধিকার ছিল না এ কথা রঘুনন্দনের কানে তোলবার। ও কি ভেবেছিল কথাটা গোপনে রেখেই দিদি বিয়ে করবে? রঘুনন্দনকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলে তাকে নিশ্চয়ই বলতেন ব্যাপারটা। অমিয় সান্যাল একজন অতবড় সংগঠক, নেতা, পার্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেলেন, তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে বিপ্লব হল, পার্টি আরও ভাগ হল। জেলের মধ্যে তাঁর মৃত্যুটা কোনও কাজে লাগল না। জেলের মধ্যে পুলিসি অত্যাচারের একটা নথিবদ্ধ প্রমাণ হয়ে রইল শুধু। বাস ওই নথি ছাড়া-আর কেউ তাঁকে মনে রাখেনি। সাতদিনের স্ত্রী পর্যন্ত না।
অধ্যায় : ৮
‘মেধা ভাটনগর’ নামটা অনেক দিন পর শুনলেন ইদ্রিস আমেদ। বয়স আশির ওপরে গিয়েছে। স্মৃতি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে বড্ড লুকোচুরি খেলে। হিন্দি নিউজের সময় নাগাদ ফোন করেছিল মেয়েটি। ‘উজান আছে? একবার ডেকে দেবেন!’ খুব কচি-কাঁচা গলা না হলেও গলাটা নরম। অল্প বয়সের মেয়ে মনে হয়। আফতাবের মেয়ে-বন্ধুর কিছু কমতি নেই। ফোন আসছে আকচার। হই-হই করে পেন্টুলুন পরা ফ্রক-পরা মেয়েরা চলে আসে। হাউ হাউ করে কথা বলে। আমেদ সায়েব পছন্দ করছেন কি করছেন না তাদের ভারি বয়েই গেল। আস্তে চলন, আস্তে বলন দেখা যাবে না। সব ধেই ধেই করছে চব্বিশ ঘণ্টা। আজকাল সর্বত্র এই। বলে কিছু লাভ নেই। কিন্তু নাতি ফিরছে সকাল বেলায়, দুপুরবেলা বাড়ির ভাত ধ্বংস করে আবার বেরিয়েছিল, কিছুক্ষণ আগেই মৈথিলী ত্রিপাঠী ফোন করেছিল। ঘড়ি ধরে দেখেছেন আমেদ সায়েব টানা দশ মিনিট কথা বলল। আবারও মেয়ে গলার ফোন! তার ওপর যেন তেরিয়া—‘উজানকে একবার ডেকে দেবেন।’ তু করলেই যেন উজান এসে পড়তে বাধ্য। ইদ্রিস আমেদ বাহান্ন সাল থেকে এম পি। একটি দিনের জন্যও তাঁকে ক্ষমতার আসন থেকে সরে দাঁড়াতে হয়নি। কমান্ড কাকে বলে তাঁর জানা আছে। মেয়েটির কমান্ডিং টোন। স্বভাব-গম্ভীর গলাকে আরও গম্ভীর করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি—‘উজান এইমাত্র ফিরেছে গ্রাম সফর সেরে।’ দেখি তোর দায়িত্ব বোধ কি বলে! বিবেচনা বলেও তো একটা জিনিস আছে! প্রতিক্রিয়া অবশ্য ভালোই। ‘এইমাত্র ফিরল? ও আচ্ছা।’ ওকে বলে দেবেন যেন আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করে। আমি মেধা ভাটনগর।’
ওপক্ষ ফোনটা রেখে দেবার পরও আমেদ সাহেবের হাতে রিসিভারটা ধরা। মাথার মধ্যে ক্রিং ক্রিং করে কি বাজছে।
‘সাবেরা! সাবেরা!’—উজানের মা এসে মুখ বাড়ায়।
‘আব্বা কিছু বললেন?’
‘মেধা ভাটনগরটি কে? জানো?’
বউ ঠোঁট উল্টোলো, জানে না।
‘অঞ্জুরে ডাক তো?’
অঞ্জু এলো বেশ খানিকটা পরে, একটু যেন বিরক্ত।
‘মেধা ভাটনগর মেয়েটি কে?’
‘মেধা ভাটনগর?’ ওহো, সে তো রোকেয়ার এক নম্বর বন্ধু ছিল। আমাদের বৈঠকখানার বাড়িতে কত আসত!
‘তাই তো বলি! ব্রাইট ছিল খুব, স্কলার না?’
‘বোধ হয়। হঠাৎ তার কথা?’
‘মেধার সাথে আফতাবের যোগাযোগ কিসের?’
‘আফতাবের? মেধার সঙ্গে?’ অঞ্জুমন অবাক হয়ে তাকালেন—‘আমি তো যদ্দূর জানি মেধা বস্টনে থাকে।’
‘রুকুর সাথে তার দহরম-মহরম আছে!’
‘তুমি জানবে। রোকেয়া তো আজকাল আমাকে চিঠি দেয় না। যাই হোক, উজানকে জিজ্ঞাসা করলেই তো চুকে যায়। উজান!’
উজান সবে চান সেরে বেরিয়েছে। চানের পর তার অভ্যাস হল, একটা মাঝারি তোয়ালে দু হাতে দুপ্রান্ত ধরে পিঠ কোমর ইত্যাদি ঘষা। সে আস্তে আস্তে খেলা ছেড়ে দিচ্ছে। টেনিসটা এখনও ছাড়েনি। ক্রিকেট প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। খেলাধুলোর জগতের নোংরা রাজনীতি তাকে ছাড়তে বাধ্য করেছে। কলেজের হয়ে একটু আধটু খেলা। বাস। কিন্তু শরীর ঠিক রাখতে ব্যায়াম দৌড়নো এগুলো সে নিয়মিত করে যায়। তোয়ালে দিয়ে টানাটানি করে ডাইনে বাঁয়ে চামড়াটাকে ঘষে সে শরীরে রক্ত চলাচল ঠিক রাখে। বাবার ডাক শুনে তোয়ালে কাঁধে খালি গায়ে সে বেরিয়ে এলো।
মেধা ভাটনগর কি এখন এখানে?’ অঞ্জুমন জিজ্ঞেস করলেন।
‘হ্যাঁ, কেন?’
‘কেন তা জানি না। আব্বা জিজ্ঞেস করছিলেন।’
উজান দাদুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কিন্তু দাদুর মুখ দু হাঁটুর মধ্যে নেমে পড়ছে। যত রাত হয় দাদু ততই এইরকম হয়ে যান।
‘মিস ভাটনগর সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করছিলেন দাদু।’ উজান কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল।
‘মেধা ভাটনগর তোমাকে কি করে চিনল?’ উজানের দাদুর মামাবাড়ি বাংলাদেশে। সেখানেই তিনি বাল্য কাটিয়েছেন। তাঁর বাচনে প্রায়ই বঙ্গজ ভঙ্গি মিশে যায়।
উজান বলল ‘উনি তো আমাদের প্রোফেসর।’
‘তোমাদের? মেধা তো রুকুর সাথে পড়ত। আর্টস!’
‘উনি আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে সোশ্যাল সায়েন্স পড়িয়েছেন।’
‘অ। তোমারে ফোন করে ক্যানো?’
উজান ব্যস্ত হয়ে বলল—‘এম ভি ফোন করেছিলেন? আমাকে? এতক্ষণ বলোনি কেন?’ সে তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে যাচ্ছিল।
‘শোন, শোন, এত রাতে কোথায় যাস?’
‘ফোন করি একটা অন্তত।’
‘এতো রাতে ভদ্দরলোক ভদ্দরলোককে ফোন করে না।’
উজান বিরক্ত হয়ে বলল—‘আমি ভদ্রলোক নই।’
সে চলে যেতে অঞ্জুমন বললেন—‘কতবার তোমায় বলেছি ওকে ঘাঁটাবে না। আজকালের ছেলে। তোমাদের যুগ আর নেই। আমাদের ওপর যা লাঠি ঘোরাবার ঘুরিয়েছ।’
‘আমি লাঠি ঘুরাইছি তোদের ওপর?’ বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ইদ্রিস আমেদ। কিন্তু এখন বেশ রাত। কিরকম ঝিম ধরে গেছে শরীরটাতে। মনের ওপরও তার প্রতিক্রিয়া হয়।
ঝিমন্ত বৃদ্ধটির ফোকলা দাঁত। বাঁধানো দাঁতের পাটি পাশে কাচের বাটিতে ডোবানো। স্তিমিত চোখের দৃষ্টি। দেখতে দেখতে অঞ্জুমনের মনে হল এই আমাদের মেমবার অফ পারলামেন্ট। দেশের হর্তা-কর্তা ভাগ্যনিয়ন্তা। পরিবারেরও। লোচচর্ম, ক্ষীণদৃষ্টি, স্থবির, কিন্তু হাতে অপার ক্ষমতার শাসনদণ্ড।
উজান বারবার চেষ্টা করেও ফোনটা লাগাতে পারল না। হতাশ হয়ে বাবাকে বলল—‘আমাকে সময় মতো বলবে তো?’
বাবা বললেন—‘আমি জানলে তো! শী ওয়াজ এ জেম অফ এ গার্ল। আমাদের সময়ে। এখন কি হয়েছে জানি না।’
‘এখনও জেম’, উজান বলল, ‘তুমি ওঁকে চিনতে বাবা?’
উদাস চোখে শূন্যের দিকে তাকিয়ে অঞ্জুমন বললেন,—‘চিনতাম মানে? তোর পিসির ফ্রেন্ড ছিল। আমাদের বাড়ি কত আসত।’
‘আমাদের বাড়ি!’
‘এ বাড়ি নয়। বৈঠকখানা রোডের যেটা আব্বা বিক্রি করে দিলেন। রোকেয়ার সঙ্গে কত এসেছে, খেয়েছে, রাত কাটিয়েছে!’
উজান এই প্রথম এ কথা শুনল, সে বলল—‘রিয়ালি!’
‘রিয়্যাল না তো কি! আমাদের অতীতের তুই কি জানিস! মেধা এখনও পার্টি করে?’
‘না তো!’
‘আমারই ভুল। এখন কমিউনিস্ট রাজ। পার্টি করলে মেধা এখন কতো ইনফ্লুয়েনশ্যাল হয়ে যেত। রোকেয়ার মতো ও-ও ছেড়ে দিল। সাদী করেনি এখনও?’
‘সাদী করা না করাটা তোমাদের খুব ভাবায়, না বাবা?’
অঞ্জুমন ছেলের কথায় কেন কে জানে একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন—‘তোরা এতো জ্যাঠা তোদের সঙ্গে কথা বলাই দায়।’
উজান হাসছিল, বলল—‘সত্যি বাবা, তোমাদের জেনারেশনে কিছু লোক বিয়ে শাদী না করলে দেশের অবস্থাটা আজ টিক এমনি হত না। নৌকো টলমল করছে একেবারে। ক্যাওড়াখালি বলে যে গ্রামটাতে কাজ করে এলাম একেবারে ছোট্ট চাষী গাঁ। কিন্তু গত সীজনে মানে গরম কালে আন্ত্রিকে মারাই গেছে পনেরটা বাচ্চা। ভাবতে পারো?’
‘বলিস কি রে? সেখানকার জল তোরা খেলি?’
‘ফোটানো হল। ওষুধ দেওয়া হল। ওদেরও ব্যপারটা শেখানো হল। মুশকিল হচ্ছে গ্রামটাতে একটাও বহতা নদী নেই। অথচ মাতলা পিয়ালী, কুমড়ো নাকি একটা নদী—সবই ওই অঞ্চল দিয়ে বইছে। মাতলা থেকে কয়েকটা খালমতো এসে ঢুকেছে, তা সে কচুরীপানায় সর্বদা ভর্তি থাকে, কাদায়, বালিতে আধবোজা হয়ে রয়েছে। জোয়ারের সাময়েও সেখানে জল ঢোকে না। বড় গোছের পুকুর একটা মাত্র। আমরা পাতকুয়া আর টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করছি। দাদুকে বলো না কিছু ডোনেশন দিতে। অনেক টাকা লাগবে। অত তুলতে পারছি না আমরা।’
সরকারি সাহায্যের জন্যে চেষ্টা কর না, আব্বা তদ্বির করতে পারেন।’
উজানের মুখের রেখা কঠিন হয়ে গেল। বলল—‘না।’
‘কেন?’
‘না।’ দ্বিতীয়বার না’টা বলে উজান আর কথা বাড়াল না, সে সেখান থেকে চলে গেল।
এম ভির কড়া নির্দেশ আছে সরকারি সাহায্য কোথাও চাওয়া হবে না। কেন তিনি পরিষ্কার করে বলেননি, কিন্তু কেওড়াখালিতে প্রথম পর্বে গিয়ে ওরা যে সার্ভে করল তাতেই তারা বুঝতে পেরেছে সরকারি সাহায্য চাওয়া কেন অর্থহীন। সরকারের কাজ করার প্রশাসনিক বন্দোবস্ত তো রয়েছেই, পঞ্চায়েত থেকে জেলা বোর্ড পর্যন্ত ত্রিস্তর বিন্যাস। তা সত্ত্বেও তো কিছু হয়নি! সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে কে কি করবে? সরকার গ্রামসেবকের ব্যবস্থা করে, টাকা কড়ি দিয়ে খালাস। এখন সেই অনুদানের টাকাকড়ি, ঋণের অধিকার সবই যদি পঞ্চায়েত তার ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে, গরিব মূর্খ গ্রামবাসী কি করতে পারে! কেওড়াখালিতে পঞ্চায়েতের অফিস নয়। নখানা ওইরকম গ্রাম নিয়ে তবে ওদের পঞ্চায়েতের এলাকা। গতবার ভোটের আগে কোনক্রমে একটা শ্যালো টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। মাস দুয়েকের মধ্যে সেটা অকেজো হয়ে যায়; বহুবার বলা-কওয়া সত্ত্বেও তাকে সারানোর ব্যবস্থা করা যায়নি। পাশের গ্রাম ফলসার অবস্থাও এমন কিছু ভালো নয়, তবে এদের থেকে ভালো। ভোটের ঠিক আগেটায়, কি পঞ্চায়েত, কি সাধারণ নির্বাচন, ওরা ঢালাও কেরোসিন তেল পায়, রাস্তাঘাটে হাত পড়ে। তারপর সব ভোজবাজির মতো উবে যায়। ওদের সবচেয়ে কাছের সম্পন্ন গ্রাম সুযযিপুর। সেখানেই পঞ্চ-এর অফিস। বি ডি ও সাহেব আসেন। মোটর গাড়ি চলার মতো রাস্তা আছে। চাইলেই কৃষিঋণ মিলছে। সে ঋণ থেকে থেকেই মকুব হয়ে যাচ্ছে। বড় বড় বর্গাদার। কাঁড়ি কাঁড়ি ফসল ঘরে তুলছে। রাজশরিক আঙুল চোষে আর জলকর গোণে।
রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর উজান ছাদে চলে গেল। যোধপুর পার্কের একেবারে প্রথম দিকে বাড়িগুলোর মধ্যে তাদেরটা একটা। দুতলা ছিল, তিনতলা হয়ে গেছে ইদানীং। দাদু বলেন, ‘আমি যদ্দিন আছি বাড়িয়ে যাই।’ দালান, সিঁড়ি সব পেল্লায় মাপের। ছাদের ওপর উঠলে ঢাকুরিয়া ব্রিজটা অনেকটা দেখা যায়। চকচক করছে আলোয়। সে এখন ঘণ্টাখানেক পায়চারি করবে। একটা দুটো সিগারেট খাবে। তারপর ছাদেরই ঘরে শোবে। নিচে যথেষ্ট ঘর থাকা সত্ত্বেও সে ছাদের এই ঘরখানাকে তার আসল আস্তানা করেছে। নিচের ঘরটাতে বন্দু-বান্ধব এলে বসে। বসবার ঘর। এখানে উঠে এলে নিচের সঙ্গে আর কোনও সংস্রব থাকে না। সম্পূর্ণটাই তার নিজের জগৎ। ক্যাওড়াখালি সফর করে সে দুজনকে নতুন করে চিনল। মৈথিলী আর দেবপ্রিয়। মৈথিলী যে কতটা সরল, কাজ পাগল, আন্তরিক স্বভাবের মেয়ে তা যেন নতুন করে জানা হল। স্কুল থেকেই সে মৈথিলীকে জানে। বাবার আগ্রহে সে এই কো-এডুকেশন স্কুলে ভর্তি হয়। দাদুর ভীষণ অমত ছিল। মায়েরও পছন্দ ছিল না। বাড়িতে এলেই স্কুল সম্পর্কে এই বিরূপ হাওয়াটা সে অনুভব করতে পারত।
দাদু বলতেন, ‘কি চান্দু, ইয়ার দোস্ত হচ্ছে?’
মা বলত—‘হবে না? আপনি দেখেন না কত কিসিমের ইয়ার? চুননি ওড়না ঘাঘরা। ওর বাপের ইচ্ছে-সাধ মতোই সব আসে আব্বা।’
তা সে সময়ে মৈথিলী লুকুর সঙ্গেই বেশি মিশত। আরও অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল তার। মৈথিলী বরাবরই খুব মিশুক। উজানের তখন খেলা মন, খেলা প্রাণ। ইদানীং, ছত্রসংঘ হয়ে মৈথিলী উজানের ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে। খেলাধুলোয় শরীর মনের স্ফুর্তিটা আসল কথা, তার জন্য যতটা অনুশীলন, যতটা প্রতিযোগিতা দরকার, অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু অনুশীলন যদি জীবনের সময়টুকুকে খেয়ে নেয়, প্রতিযোগিতা যদি ক্রমশই যোগ্যতার প্রশ্ন থেকে অন্যান্য পক্ষপাত বিশেষত টাকা চালাচালির নোংরা দলাদলিতে গিয়ে পৌঁছয়, খেলার আনন্দটা আর থাকে না। উজান আফতাব উদীয়মান অল-রাউন্ডার হিসেবে ক্রমশই খ্যাতি পাচ্ছিল এমন সময় সে ক্লাব-পলিটিকসের জঘন্য আবর্তে পড়ে গেল। অন্যান্য প্রতিযোগীদের কাউকে দেখল হিংস্র, কাউকে দেখল নিরাশ। আর যেসব কর্তা ব্যক্তিদের ক্রীড়াপ্রেমী বলে শ্রদ্ধা করত তাঁদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে লোভী পক্ষপাতদুষ্ট, কখনও বা নিজের জালে নিজে জড়ানো নির্বোধকে প্রত্যক্ষ করল সে। এই ছাতের ঘরে একদিন চলে এসেছিল আরমান। পার্ক সার্কাসে থাকে। মিডিয়াম পেস বল করে। ব্যাটও ভালো। আরমান বললে—‘উজান আমি খবর পেয়েছি, ওরা আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে রাখবে। তুই থাকলে আমার চান্স কম। সত্যেনদা আমার জন্যে চেষ্টা করছেন, কিন্তু বোর্ড শেষ পর্যন্ত কি করবে….।’
‘সত্যেনদা তোর জন্যে চেষ্টা করছেন? কি ভাবে?’
‘আগরওয়ালার সঙ্গে তো ওঁর খুবই আঁতাত। আগরওয়ালা যদি আমার পক্ষে থাকে…’
সত্যেনদা উজানকে কিছুদিন আগেই বলেছিলেন—‘উজান তুমি থাকছোই, তোমাকে এবার রণ্জীতে ডিসপ্লে করা হবে।
উজান বললে—‘তুই কি বলতে চাস আরমান।’
আরমান প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—‘উজান খেলাটা তোর প্যাসটাইম। আমার কেরিয়ার। সমস্ত জীবনটা খেলায় দিয়ে দিয়েছি। জানিস তো আমাদের অবস্থা। এক পাল ভাইবোন, দুই মা, বাবা হাই-ভোল্টেজ নিয়ে কাজ-কারবার করেন। সব সময়েই রিস্ক্। খেলার সূত্রেও যদি একটা চাকরি পাই…। তাছাড়া তোর তো টেনিসও রয়েছে।’
উজান ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিল। সত্যেন ঘোষ কয়েক দিন এসে ফিরে গেলেন। বাবা জানতে পেরে খুব রাগারাগি করল। ওরা কিন্তু তা সত্ত্বেও উজান, আরমান দুজনকেই রেখেছিল। উজানের ভাগ্যক্রমে টীমের দুজন বসে গেল। এক জনের বুড়ো আঙুল জখম, আরেকজনের রক্ত আমাশা। সে খেলল, দারুণ খেলছিল, আরমানের নিরাশ মুখটা মনে পড়ে, কনসেনট্রেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল শেষটায়। তারপর একটা সাধারণ বলে আউট হয়ে গেল। বোল্ড্। পরে শুনেছিল, বোদ্ধারা বলেছিলেন, খেলছে ভালো, টেমপারামেন্ট নেই। আরমান আলি জান লড়িয়ে দেয়। দিক। আনন্দই যদি না থাকল তাহলে খেলার আর রইল কি!
উজান এখন অন্য খেলা খেলতে চায়। খেলা নয় কাজ। সীরিয়াস কাজ, যাতে সত্যি-সত্যি জান লড়িয়ে দেওয়ার মানে হয়। মৈথিলীই তাকে এ খেলায় এ কাজে নামিয়েছে ঠিক। কিন্তু এখন তার মনে হয় বহুকাল আগে থেকে এই কাজের জন্য সে চিহ্নিত ছিল। যে নির্বাচনী বোর্ড তাকে এখানে নামিয়েছে, তারা তার যোগ্যতা, প্রবণতা, টেম্পারামেন্ট সব বিচার করে নিঃসংশয় হয়ে একটা গুরুদায়িত্ব তার হাতে তুলে দিয়েছে অসীম আস্থাভরে।
ক্যাওড়াখালিতে হেন অসুবিধে নেই যার সঙ্গে ওরা নিজেদের মানিয়ে নেয়নি। জল নেই, জল ফোটাও, ছাঁকো, এর বাড়ি ওর বাড়ি খাও, বড়দের, ছোটদের দফায় দফায় জড়ো করো। চিৎকার করে বক্তৃতা দাও, কাছে ডেকে বোঝাও, প্রশ্নের জবাব দাও, ঘর নেই, আলুর ঘরে শোও। খড়ের গাদায়। সে এক কেলো! কিন্তু এরই মধ্যে সবচেয়ে মজার হল মৈথিলী। যেখানেই হোক ও ডায়েরি লিখবেই। ভোর বেলায়, আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে দাওয়ায় খড়ের গাদার ওপর বসে মৈথিলী ডায়েরি লিখে যাচ্ছে। পাখি ডেকে যাচ্ছে চার দিকে আধো আধো স্বরে, ছানার জলের মতো ভোরের আলো, কুয়াশা-কুয়াশা শীত, তার মধ্যে আপাদমস্তক খড়ের কুচি লাগা মৈথিলী ডায়েরি লিখে যাচ্ছে।
উজানের ভোরবেলায় ওঠা অভ্যাস। যত রাত করেই শোয়া হোক, তাকে ভোর-ভোর উঠতেই হবে। সে চলে যেত মাঠ-ঘাট বন বাঁদাড় পেরিয়ে অনেক দূরে কুলতলির মাঠ বরাবর, ভোরের টাটকা হাওয়ায় জগিংটা অন্তত করতেই হবে। গ্রামের রাস্তা দিয়ে হঠাৎ যদি সে তার ট্র্যাক সুট পরে দৌড়তে আরম্ভ করে, তাহলে হয়ত, পাগলদের কারবার বলে অপারেশন ক্যাওড়াখালির ওইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে! ওর দ্যাখাদেখি কিছু কিছু স্থানীয় ছেলে অনন্ত, মুচিরাম, সমু, প্রদীপ, এরসাদ বা খোকা জগিং করতে শুরু করেছিল। উজানও সঙ্গে সঙ্গে লেকচার আরম্ভ করে দেয়।
‘হ্যাঁ এই ভাবে এক জায়গায় দৌড়ও। পায়ের পেশী শক্ত হবে। কোমর, শিরদাঁড়া সব নরম থকবে। শরীরটাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারা চাই। জানো তো শরীরমাদ্যং। আগে স্বাস্থ্য ভালো করো, তবে অন্য সব।’
সমু বলল—‘নিরঞ্জনদা এক লপ্তে দশ মাইল হাঁটতে পারে।’
অনন্ত বলল—‘কুড়ি কুড়ি চল্লিশ কেজি মাল দু কাঁধে বইতে পারবে।’ অর্থাৎ নিরঞ্জন খাঁড়া হেড মাস্টারমশাই ওদের স্থানীয় হিরো। ওরা আশা করছিল উজান বলবে—‘আমিও পারি।’ উজান মনে মনে হাসল, বলল ‘তোমরাও চেষ্টা করো।’
‘নিরঞ্জনদা এক কাঠা চালের ভাত খেয়ে নেবে একটা গোটা পাঁঠা দিয়ে। আবার উপোস থাকবে তিনদিন চারদিন।’
‘তাজ্জব কি বাত! বাঃ।’
এরসাদ বলল—‘আপনে মুসল্মান?’
উজান হেসে বলল—‘হ্যাঁ, কেন?’
‘পাঁচ ওয়ক্ত নেমাজ পরেন?’
‘এ কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?’
‘কাল শুককুরবার ছিল মসজিদে গেলেন না তো!’
‘কাল সারাদিন তোমাদের খাবার জলের ব্যবস্থা করার জন্যে ঘুরেছি এরসাদ। দেখোনি! কোথায় কুয়ো হবে কোথায় টিউবওয়েল, হাতল ঠেলবে আর মাটির ভেতর থেকে জল এসে তোমাদের মুখে পড়বে’, মজা করে জিনিসটা করে দেখাল উজান।
‘অর্জুনের বাণে যেমন ভীষ্মের মুখে জল পড়েছিল?’ সমু বলল।
‘ঠিক ঠিক।’ উজান উৎসাহের সঙ্গে বাহবা দেয়। ব্রাঞ্চ লাইনে চলে গেল আলোচনা। স্বাস্থ্য থেকে ধর্মাচরণ, ধর্ম থেকে পুরাণ। তা সত্ত্বেও উজান গ্রামের বালক বালিকাদের কিছু যোগাসন, কিছু ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম দেখিয়ে দিয়ে এসেছে। ওরা ফুটবল চায়, ক্রিকেটের ব্যাট বল, উইকেট চায়, সেগুলোর প্রতিশ্রুতি দিতে হল। খাদ্য সম্বন্ধে ওদের বলবার কিছু নেই। যা পায় তাই খায়। সঙ্ঘের পরবর্তী প্রোগ্রামে আছে গ্রামে একটা ডেয়ারি এবং পোলট্রি স্থাপন করা। আশেপাশে জলায় মাছ জন্মায়, কিন্তু চারদিকের যত ক্ষেত ভাসা জল সেখানে এসে পড়ে, তাতে পোকামারা ওষুধ থাকে, ফলে ওই জলার মাছ খেলে তখন এদের সাংঘাতিক পেটের গোলমাল হয়ে যায়। নদীর মাছ ওরা খাবার জন্য পায় না কখনোই। এ বিষয়টা নিয়েও ওরা অলোচনা করেছে। কুয়ো এবং নলকূপের সংখ্যা যদি পরিকল্পনামাফিক বাড়ানো যায় তাহলে স্নান খাওয়া এবং অন্যান্য কাজের জলের অভাব থাকবে না। সেচের সমস্যারও সমাধান হবে। মাঝের পুকুর, মাতলা-পিয়ালির মজা খাল আর জলাগুলো সম্পর্কে কিছু করা যায় কিনা, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে। প্রমিত আর বুল্টু শিগগীরই বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। কিন্তু খোঁজখবরগুলো আসলে নেবার কথা ছিল দেবপ্রিয়র।
‘ব্রাইটেস্ট ইয়ংম্যান অফ দা ইয়ার’ বলে মৈথিলী তার সহপাঠী দেবপ্রিয় চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করায় উজানের।
উজান বলে, ‘প্রাউড টু মিট ইউ।’
দেবপ্রিয় বলল—‘খেলো? তোমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল।’ কিন্তু ইচ্ছেটা খুব বলবান বলে কখনও মনে হয়নি উজানের। কেমন একটু আলগা ভাব। সুইচ লুস কনট্যাক্ট্ হয়ে গেলে যেমন আলো কখনও জ্বলে, কখনও জ্বলে না, দেবপ্রিয়র সঙ্গে সম্পর্কও তাই। এই একগাদা কাজ করে ফেলল। যা বলা হল তাও, যা না বলা হল তা ও, তারপরই হঠাৎ ফিউজ। হঠৎ ওকে লক্ষ্য করলে মনে হবে খেয়ালী। কিন্তু তা নয়, ওর ভিতরে কিছু গণ্ডগোল আছে। একে অত্যন্ত সিক্রেটিভ টাইপ। তার ওপরে এইরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন। আসব বলে শেষ মুহূর্তে এলো না কেওড়াখালিতে। স্টেশনে বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছে তারা ওর জন্য। সেদিন দেরি হয়ে গেলেও পরে নিজে নিজেই আসতে পারত। কিন্তু একদম ডুব গেলে আছে। বেশ কিছুদিন থেকেই সে লক্ষ্য করছে দেবপ্রিয় কারো সঙ্গে বিশেষ মিশছে না, ছাত্রসংঘের ব্যাপারে গা করছে না। এমন কি একটা কাজ করব বলেও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কি, ওদের কারোই জানা নেই। মৈথিলী খুব চিন্তিত। কিন্তু উজানের চিন্তা আরও বেশি। দেবপ্রিয় গোপনে গোপনে কোনও রাজনীতি করে কি না তা-ই কে জানে! সে গ্রাম-ট্রামের ব্যাপারে বেশি জানে বলেই তার ওপর ওরা নির্ভর করছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে হল উজানের। দেবপ্রিয়, ব্রাইটেস্ট ইয়ংম্যান অফ দা ইয়ার কি উজান আফতাবের প্রাধান্য চায় না! গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে, ওর কি উজান মুসলিম বলে কোনও সংস্কার আছে? তা যদি থাকে তো দেবপ্রিয় চৌধুরী ছাত্র সংঘে একেবারেই থাকবার যোগ্য নয়। তাদের প্রতিষ্ঠানে উপায় এবং লক্ষ্য, এন্ড মীনস শতকরা শতভাগ শুদ্ধ হতে হবে। যেমন তেমন করে সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হল, রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় থাকবার জন্য যা করছে, কে সুযোগসন্ধানী, কে সমাজবিরোধী, কে অতি রক্ষণশীল, কে ধর্মান্ধ এসব চিন্তা না করেই, এ জিনিস যে কখনো মঙ্গল আনতে পারে না, তা দেশের বর্তমান অবস্থা দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। উজান আফতাব ছাত্রসঙঘর সেক্রেটারির পদ দেবপ্রিয়কে দিয়ে দিতে পারে কিন্তু দেবপ্রিয় বৃথা ঈর্ষা করলেও না, আর মুসলিম বলে তার সঙ্গে সহজ হতে পারছে না বলেও না। দেবপ্রিয়কে প্রমাণ করতে হবে সে উজানের চেয়ে বেশি যোগ্য, বেশি উদারচেতা। এগুলোর কোনটাই সে এখনও প্রমাণ করতে পারেনি। এ নিয়ে মৈথিলীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। খুবই অপ্রিয় প্রসঙ্গ। তবু। এম ভির সঙ্গেও। সম্ভব হলে। এম ভি কেন ফোন করেছিলেন জানা হল না, কাল সকালে চলে যাওয়া যেত। কিন্তু তখন উনি ব্যস্ত থাকবেন। বরং সন্ধের দিকটায় গেলে হয়ত অসুবিধে হবে না। ফোনটা ভালো বলছে না, ডেড মনে হচ্ছে।
অধ্যায় : ৯
লুকুর যখন সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে এলো, তার মনে হল একটা অদ্ভুত অর্থহীন স্বপ্ন দেখেছে সে। চোখ বড় বড় করে ঘরটা দেখতে থাকল লুকু। এখন যেটা দেখছে সেটাও স্বপ্নের অঙ্গ নয় তো? সীলিংএর ফ্যানটা এখন বন্ধ তার ওপর একটা চড়ুইপাখি বসে। কিরকম একটা হলদেটে রঙ ঘরের ভেতরে, পর্দাগুলো কমলা রঙের বলে আলোটাও কিরকম অদ্ভূত হয়ে যায় এ সময়ে। অর্থাৎ এখন বিকেল, সূর্য এদিকে, পশ্চিমের দিকে চলে এসেছে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে টেবিলের ওপর টাইম-পীসটা দেখবার চেষ্টা করল, পারল না। শরীরটা কি রকম ভারি হয়ে আছে। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল, ‘ঝড়ু’, দু তিনবার ডাকের পর ঝড়ু এলো। মা মারা যাবার পর বাবা তাদের দারুণ ভালো রাঁধুনি মহেশদাকে রাখতে চাইলেন না। একটি বয়স্ক মহিলা দু বেলা রান্না করে দিয়ে যান। বাকি কাজ ঝড়ুই করে।
‘কটা বাজে রে?’
বেশ কিছুক্ষণ ঘড়িটা নিরীক্ষণ করে ঝড়ু উত্তর দিল—‘বড় কাঁটা পাঁচের ঘরে, ছোট কাঁটা চারের ঘরে’
‘এখনও তুই বড় কাঁটা ছোট কাঁটা করবি? শিখবি না?
ঝড়ু সন্ত্রস্তভাবে হাসল।
‘হ্যাঁ কেউ এসেছিল?’
‘তোমার বন্ধু দাদাবাবুর পর আর কেউ আসেনি।’
লুকুর ঝপ করে স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। ওটা তাহলে স্বপ্ন নয়! শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে। লুকু বলল—‘এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে আয় তো, চকলেট দিতে ভুলবি না।’
ঝড়ু অন্তর্হিত হলো। দেব তাহলে কেওড়াখালি যায়নি? কেন? দেব কি জানত লুকু যাচ্ছে না! জানাই সম্ভব। দেব কেন এসেছিল? লিকর খাওয়ালো খানিকটা, কি যত্ন করে, লুকুর গলা-ব্যথা অনেক কমে গেছে, এভাবে খাওয়ানো মায়ের পরে, মা-ও নয় ঠিক, দিদার পরে আর কেউ কখনও করেনি। বাবা-মা পার্টিতে বেরিয়ে গেলে, লুকু মুখ গোঁজ করে থাকত, দিদা তখন গল্প বলতে বলতে একটু একটু করে তাকে খাইয়ে দিতেন। দিদার ঘরে ঠাকুর ছিল, ভীষণ শুচিবাই ছিল দিদার। তা-ও। লুকুর মাছ-ভাতের থালা নিয়ে সে দিদার কাছে চলে যেত। দিদাই তার নাম রেখেছিলেন লক্ষ্মীশ্রী। সেকেলে নাম বলে, সবার কত আপত্তি। শেষকালে ডাকতে ডাকতে লুকু হয়ে গেল। লুকুর গলার কাছে এখন একটা পিণ্ড আটকে যাচ্ছে। দিদা, মা। দিদার ডাক ‘লক্ষ্মীশ্রী’ই’। পুরোটা উচ্চারণ করে ডাক দিতেন দিদা! ‘লুকু!’ ছোট্ট করে ডাকত মা! কেউ আর সেভাবে ডাকবে না। শুধু লিকর কেন? ঝড়ু কি জানে না বেশি দুধ দিয়ে চা খেতে লুকু ভালোবাসে! বেশ ক্ষীরের মতো চা, তাতে একটু তেজপাতা, দারচিনি দিলে আরও ভালো। লুকু বমি করে ফেলেছিল। মুখে-চোখে জল দিয়ে দিল দেব। একটুও ঘেন্না করল না তো! অবশ্য দেব ডাক্তার। দেব তাকে ধরে ধরে এনে এখানে শুইয়ে দিয়েছে। কি যেন একটা চাইছিল! লুকুর হঠাৎ সবটা একসঙ্গে মনে পড়ে গেল। দেব তার সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে গেল, গার্বেজ বিনটা হাঁটকে। স্ট্রেঞ্জ! যাবার সময় বলে গেল লুকু স্মোক করো না, কেউ দিলেও নেবে না, অ্যাজ এ ডকটর অ্যাজ এ ফ্রেন্ড বলছি। যতই ভাবে দেবের হাবভাব, কার্যকলাপ খুব আশ্চর্য লাগে লুকুর। দেব ছেলেটাই আশ্চর্য। মৈথিলী বলে দেবের শ্রেষ্ঠত্ব মেডিক্যাল কলেজের প্রতিটি ক্লাসে, ডিসেকশন রুমে, বারবার প্রমাণ হয়ে যায়। সঠিক উত্তরগুলো ওর মুখ থেকে এমন গড় গড় করে বেরিয়ে আসে যেন মন্ত্র, ভেতরে কোথাও রেকর্ড করা আছে। ওর ডিসেকশনও দেখবার মতো। সরু সরু আঙুলগুলো চলে নিখুঁত সাবলীলভাবে, ও যেন শল্য চিকিৎসক হবার জন্যই জন্মেছে। ডক্টর বাগচি একদিন বলছিলেন ‘তোমরা নিশ্চয়ই অন্তত তিন পুরুষ ডাক্তার।’ নয় শুনে আশ্চর্য হয়েছিলেন ডাঃ বাগচি। ওরা বন্ধুরা বলাবলি করে দেবের বংশে কোথাও সার্জনের জিনটা রিসেসিভ থেকে যাচ্ছিল অনেক দিন থেকে, দেবের মধ্যে প্রকাশিত হল। দেব ছাত্রসংঘের একটা স্তম্ভ। উজান, মৈথিলীও করে। কিন্তু লুকুর কি রকম একটা মনে হয়। আড়াল থেকে দেব সবার ওপরে ছাতটা ধরে আছে। কেন এরকম মনে হয় সে অবশ্য জানে না। ওকে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হয় তার, তার মায়ের কথা, নিজের আশা-আকাঙক্ষার কথা। ছাত্রসঙ্ঘে যোগ সে দিয়েছে ঠিকই। মৈথিলীর কথায় আর মেধা ভাটনগরের জন্য। যতটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়, ততটা সমাজসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়। মেধাদি বলেন ইতিহাসের সাক্ষ্য বলছে মেয়েরা বারবার যুদ্ধবিগ্রহ, ও রাজনৈতিক জটিলতার উপলক্ষ্য এবং শিকার হয়েছে, যেমন দেবলাদেবী ও কমলা, যেমন পদ্মিনী ও নূরজাহান। রণ ও রাজনীতিতে তারা প্রায় কখনও সফল হয়নি যেমন রাজিয়া, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাই এবং ক্ষমতা হাতে পেলে তারা প্রায়শই ক্রূর নিষ্ঠুর স্বার্থপর হয়ে দেখা দিয়েছে যেমন ব্লাডি মেরি, ক্যাথরিন দা গ্রেট, মারি আঁতোয়ানেৎ। হয় তারা পুরুষদের ষড়যন্ত্রের কাছে হেরে যাচ্ছে, নয় তো অত্যাচারী পুরুষ শাসকের আদলে নিজেদের গড়ে নিচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীর রাণী এলিজাবেথও কিছু কম স্বার্থপর, কম অত্যাচারী ছিলেন না। এখন মেয়েদের একাংশের ওপর থেকে সমাজের চাপ, পুরুষের চাপ ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। গঠনশীল, সৃষ্টিশীল কাজ করে মেয়েরা ইতিহাসের এই কঠোর সাক্ষ্য পাল্টে দিক। মেয়েরা আগে মানুষ পরে মেয়ে এটা যেন সর্বদা মনে রাখে।
একথাগুলো মেধাদি সাধারণ ক্লাসে বলেননি। বলেছিলেন তাদের তিনজন মেয়েকে একত্রে। সে গুঞ্জন আর মউমিতা। খুব লজ্জাকর একটা ঘটনা ছিল উপলক্ষ্য। ঘটনাটা লুকুকে নিয়ে। ক্লাসের একটি ছেলে সারা বছর ধরে লুকুকে বিরক্ত করছিল। এ ধরনের উপদ্রব ছোট থেকেই লুকুর অভ্যেস আছে। ওরা অর্পণকে নিয়ে একটু মজাই করত। অর্পণ একদিন একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলল। লুকুকে তো একটা সাংঘাতিক প্রেমপত্র লিখলই, লুকুর বাবাকেও লিখে জানাল সে লুকুকে বিয়ে করতে চায়।
বাপী ভীষণ গম্ভীর মানুষ, লুকুরা দু ভাই বোন বাপীকে বরাবর খুব সমীহ করে এসেছে। যদিও বাপীর আদরও ছিল অতিরিক্ত এবং মা মারা যাবার পর বাপী ক্রমশই নরম হয়ে যাচ্ছিল। রাতে বাপী ঘরে ডেকে বলল—‘কে এ ছেলেটা? অর্পণ দেব না কি নাম? এমন কায়দা করে নাম সই করেছে যে নামটাও ভালো করে উদ্ধার করতে পারছি না। কি সব উল্টোপাল্টা লিখেছে রে? একটা সেকেন্ড ইয়ার হিসট্রি অনার্সের ছেলেকে তুই বিয়ে করবি? তুই, তোরা এতো ইমম্যাচিওর! লুকু, শেষ পর্যন্ত তুই…তোর মার কতো আশা ছিল!’
‘ব্যাস ব্যাস!’ লুকুর চোখ জ্বলছে, সে প্রায় বাঘিনীর মতো বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল; আঁচড়ে কামড়ে একসা করে দিচ্ছে।’
‘কি করছিস! কি করছিস?’
‘তুমি আগে কেন জিজ্ঞেস করলে না, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই কি না। সব কিছু ধরে নাও কেন?’
লুকুর মা মারা যাবার পর লুকু এইরকম হিস্টিরিক হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তার বাপী ভয় পান, বললেন, ‘ঠিক আছে। আমি ভুল করেছি। ভুল ভেবেছি। কিন্তু তা বলে তুই এভাবে রি-অ্যাক্ট করবি কেন? আমাকে বললেই তো হয়…।’
কাঁদতে কাঁদতে লুকুর সেই এক কথা—‘তুমি সব কিছু ধরে নিলে কেন?’
পরের দিন লুকু কলেজ গেল না। তারপর দিন ক্লাসে ঢোকবার মুখে অর্পণ এক গোছা রক্তগোলাপ নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে দেখা গেল। লুকু ঢুকে যাচ্ছিল, মাথা উঁচু করে কোনদিকে না তাকিয়ে, অর্পণ গোলাপের গুচ্ছ তার দিকে বাড়িয়ে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের উল্টো পিঠের ঝটকায় লুকু সেটা ফেলে দিয়েছে। অর্পণের মুখ ফ্যাকাশে। সে আস্তে আস্তে ওখান থেকে চলে গেল। সহপাঠীদের অনেকেই হাসছিল। লুকুর রাগ দেখে কেউ কেউ তাকে শান্ত করবার জন্যও এগিয়ে আসে। অর্পণ এর কিছুদিন পর আত্মহত্যার চেষ্টা করে, হাসপাতালে সময় মতো নিয়ে যাওয়া গিয়েছিল বলে অনেক চেষ্টা চরিত্র করে তাকে বাঁচানো যায়। এখন তাকে কলেজ ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। সহপাঠীরা বলে অর্পণকে ওর দিদির কাছে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মানসিক অবস্থা ভালো নয়।
এই ঘটনায় গোটা য়ুনিভার্সিটি তোলপাড়। করিডরে করিডরে, কমনরুমে, স্টাফরুমে ওই এক আলোচনা। এম ভি সেই সময়ে একদিন ওদের তিনজনকে ডেকে পাঠান।
মউমিতা স্বীকার করে ছেলেটিকে নিয়ে ওরা মজা করত; স্রেফ মজা দেখবার জন্যে ওরা ব্যাপারটা বাড়তে দিয়েছিল। অর্পণ এতো বোকা যে সে ওদের ইয়ার্কিগুলো সত্যি বলে ধরে নিত।
গুঞ্জন খুব তেরিয়া ধরনের মেয়ে, সে বরাবরই লুকুকে খানিকটা আড়াল দিয়ে চলে। সে বলে—‘আমি হলে অনেক দিন আগেই ওকে বেশ করে কষে একটি চড় মারতাম। লুকুর কোনও দোষ নেই।’
মিস ভাটনগর বললেন, ‘এটা তুমি কি বললে গুঞ্জন? ছেলেটির জীবনটা নষ্ট হতে চলেছে, তোমাদের কোনও অনুতাপ নেই?’
‘হোয়াট কুড উই ডু? বলুন মিস তাহলে ও যখন লুকুর জন্য পাগল, লুকুর ওকে পছন্দ না হলেও, ওকে বিয়ে করতে হবে?’
‘তা একেবারেই নয়। কিন্তু ফুলটা ওইভাবে ফেলে দেওয়া ওর উচিত হয়নি। ফুলটা একটা সিম্বল, ভালোবাসার, আত্মার। সে আত্মা যারই হোক, যেমনই হোক, ওভাবে তাকে অপমানিত করা উচিত হয়নি। এটার দায়িত্ব তোমাদের সবার। লুকুর একার নয়। নেভার ট্রাইফ্ল্ উইথ এনিবডিজ লাভ। গোড়ার থেকেই খুব সাফ কথায় জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তুমি এ মনোভাব পছন্দ করছ না। বরং ওকে সহজ হতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল তোমাদের।’
মেধাদির কথা শুনে লুকু কাঁদতে আরম্ভ করে। একেবারে সান্ত্বনাহীন কান্না। অর্পণের অবস্থার জন্য সে তো তখন মরমে মরে যাচ্ছিল। গুঞ্জন বললে—‘ও কে লুকু, নাউ সে সরি।’
মেধাদি বললেন—‘না, গুঞ্জন না। সরি বললেই সব কিছু ঠিক হয়ে যায় না। লুকু তুমি যদি সাবধান না হও, সীরিয়াস না হও, এরকম ঘটনা আবার ঘটবে। কে বলতে পারে তোমার নিজেরও ক্ষতি হতে পারে।’
গুঞ্জন, মউমিতা চলে গেল, উনি বললেন—‘তোমরা যাও, আমি ওকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।’
লুকু কাঁদছিল তখনও। উনি তার মুখটাকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মেধা ভাটনগরের কোলে একটা মৃদু সুন্দুর সুগন্ধ। একটু পরে বললেন, ‘লুকু একটু কফি খাও।’ লুকু দু হাত দিয়ে মেধাদির কোল চেপে ধরেছে, কিছুতেই উঠতে দেবে না। কান্নাবিকৃত স্বরে বলছে ‘অর্পণের কি হবে মিস।’ দিদি বললেন—‘এত সেন্টিমেন্টাল বোকা ছেলেদের কিছু হওয়া খুব শক্ত। ওকে আরও অনেক শক্ত হতে হবে। এতো ভালনারেবল হলে কি চলে? এই ধাক্কাটায় ওর চোখ খুলে যেতে পারে। ও আরও অনেক শক্তধাতের হয়ে যেতেও পারে, বলা তো যায় না। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা জীবনটাকে আরও গভীরভাবে ভালোবাসতে শেখাতে পারে ওকে। সেটাই আমরা আশা করতে থাকি। দেখি আমি খোঁজ নেবো। তবে তুমি যেন শুদ্ধু এই অন্যায়টা করেছ বলে ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ো না।’
সেদিন রাতে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ালেন উনি লুকুকে। উনি মাছ মাংস খান না। ছানার একটা তরকারি, চিলি চিকেনের মতো খেতে, রুটি, আর ফ্রুট স্যালাড। স্কুটারের পেছনে চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। গুঞ্জনরা বাপীকে খবর দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাপী পায়চারি করছিল। দরজা খুলে হেলমেট পরা দিদিকে আর লুকুকে দেখে অবাক। ভীষণ বিচলিত।
‘আপনি এভাবে এতো রাতে, আমাকে একটা খবর দিলেই আমি নিয়ে আসতাম।’
সেসব কথার কোনও জবাব না দিয়ে মিস বললেন—‘এখন থেকে লুকুকে মাঝে মাঝে আমার বাড়ি রেখে দেবো মিঃ মজুমদার।
বাপী যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে—‘প্লীজ ডু প্রোফেসর ভাটনগর, শী ইজ আ মাদারলেস চাইল্ড। ওর ভাই ওর থেকে অনেক শক্ত। মেয়েটার আমার কি যে হবে!’
‘কী যে হবে বলে ছেড়ে দিলে চলবে? একটু বেশি সময় তো ওদের দিতেই হবে আপনার। দ্বিতীয় কেউ নেই যখন। আমি তো পুরা দায়িত্ব নিতে পারবো না।’
‘না না সে কি!’ বাপী খুব লজ্জা পেয়ে গেল। সব কিছু অবশ্য লুকুর শোনার কথা না। বাড়ি পৌঁছেই সে ভেতরে চলে গিয়েছিল। ভাইয়া খেয়েছে কি না, বাপীকে ঝড়ু কি দিয়েছে খোঁজ করতে। কিছুটা লুকু লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছে। সেই থেকে মেধা ভাটনগরকে দেখলেই ও পালায়। মুখ নিচু করে ফেলে। যেন তার গোপন সত্তার একটা চেহারা উনি ঢাকনা সরিয়ে দেখে ফেলেছেন, দেখে ফেলেছেন কোথায় সে নগ্ন। লজ্জা করে। অথচ রাতে শুয়ে শুয়ে মেধা ভাটনগরকেই স্বপ্ন দেখে লুকু। মেধাদির কোমর ধরে সে স্কুটারে করে অনেক দূর চলেছে। মেধাদির কোলে তার মুখ, তিনি ওকে আদর করছেন। মেধাদির মতোই সে হতে চায়। আসলে প্রথম থেকেই সে মেধা ভাটনগরের ভীষণ ভক্ত। গুঞ্জনকে একদিন বলেছিল, ‘আই অ্যাম ক্রেজি অ্যাবাউট হার। এম ভি ক্লাসে এলেই আমার গা শিরশির করে। মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে দিই। ওই ডিম্পলটা! ডিম্পলটা যে কী পাগল করে দ্যায় আমাকে ধারণা করতে পারবি না।’
গুঞ্জন বললে—‘তোর মধ্যে লেসবিয়ান টেনডেনসি দেখা দিচ্ছে লুকু সাবধান হ। ইটস নট হোলসাম।’
লুকু মনে মনে জিভ কামড়ায়। কেন কথাটা গুঞ্জনকে বলতে গেল! এই হোস্টেলাইটগুলো জীবনযাপনের অনন্ত স্বাধীনতা পায়। যা খুশি করে, যা খুশি ভাবে।
প্রথমবার কেওড়াখালি যেতে পারল না সে। মেধাদিও যাননি। দেবও দেখা যাচ্ছে যায়নি। দ্বিতীয়বার যাবে। যাবেই। অশত্থ গাছের ছায়ায় বয়স্ক মহিলাদের অক্ষরপরিচয় করাচ্ছে লুকু। সই করতে শেখাচ্ছে। ফার্স্ট এডের ট্রেনিং দিচ্ছে মৈথিলীর সঙ্গে। দেবের সঙ্গে। তার হাতে ট্রায়াংগুলার ব্যান্ডেছ। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন মেধা ভাটনগর। চোখে তারিফের দৃষ্টি। উনি কি করছেন? কি করবেন? কিছু না করে শুধু তদারকি করবার পাত্র তো উনি নন! সেবার ডিপার্টমেন্টাল পিকনিকে সব্বাইকে পরিবেশন করে খাওয়ালেন অত্তখানি লম্বা মানুষটা নুয়ে নুয়ে। লুকুর হঠাৎ মনে হল সে একটা ছবি দেখছে। সিনেমার মতো। মেধাদি গ্রামের ঠিক মধ্যিখানে একটা চত্বরে দাঁড়িয়ে আছেন। যদিও এরকম কোনও চত্বর সত্যি-সত্যি আছে কি না সে জানে না। সেই সাদা রঙের কমলাবুটির সরু পাড় টাঙাইলটা পরেছেন। ব্লাউজের হাত কনুই পর্যন্ত। সাদা একটা হাত উঁচু দিকে উঠে আছে। সোজা লম্বা। কোথা থেকে অনেক গাছের পাতা মাথার ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে। দেবপ্রিয় অনেক সাদা ফুল নিয়ে এসে পায়ে অঞ্জলি দিল। কে যেন কোথায় বলে উঠল—‘মেধা ভাটনগর’, অমনি চারদিকে রব উঠল ‘অমর রহে।’ কান-ফাটানো চিৎকার। কিন্তু খোলা জায়গায় বলে সে ভাবে কান ফাটায় না। লুকুর বড্ড গলা ব্যথা করছে এখন। কানটা যেন তালা লেগে গেছে।
ঝড়ু সদর দরজা খুলছে। বাপী ঢুকছে, ভাইকে নিয়ে।
‘লুকু, কেমন আছো মা!’
‘ভালো না বাপী’, লুকু কোনমতে বলল।
‘বিকেলবেলার ডোজগুলো খেয়েছ?’
‘এখনও খাইনি।’
‘আচ্ছা আমি দিচ্ছি। আগে কিছু খাও। ঝড়ু…’ বাপী ডাকতে ডাকতে ওদিকে চলে গেল।
ভাইয়া কাছে এসে বলল—‘দিদি আজ বাবা কাউবয় থেকে মাটন চপ এনেছে। গরম একেবারে। তুই খেতে পারবি?
বাপী ঘরে ঢুকছিল, বলল—‘ঠিক পারবে, ‘কাউবয়ে’র মাটন চপ একেবারে মাখনের মতো। আজকে থার্ড ডে ওষুধ পড়ে গেছে। দেখি লুকু গলাটা।’
লুকু অনুভব করল তার গলার ব্যথা ব্যথা ভাবটা অনেক কমে গেছে। আসলে এতক্ষণ যে ব্যথাটা করছিল সেটা গ্ল্যান্ডের ব্যথাই নয়। গলার কাছে ভাবাবেগের পিণ্ড আটকে থাকার ব্যথা। হয়ত সে চেষ্টা করবে খেতে পারবে না, কিন্তু বাপী যে তাকে মনে করে মাখনের মতো নরম মাটন চপ নিয়ে এসেছে এতেই তার মুখের মধ্যেটা স্বাদে ভরে যাচ্ছে।
অধ্যায় : ১০
গ্রীষ্ম আসতে আসতে কেওড়াখালির পাতকুয়োগুলো সব হয়ে গেল। নলকূপ পাঁচটা। একটি যৌথ পোলট্রি ও ডেয়ারি। লেগহর্নের ছানা এসেছে দেবপ্রিয়র মেজ জেঠুর ফার্ম থেকে। পুরোটাই ফ্রি। ডেয়ারি আরম্ভ হয়েছে আপাতত দুটো মহিষ এবং দুটি মাত্র গরু দিয়ে। এগুলিও পৃথ্বীন্দ্রনাথ অনেক কমদামে দিয়েছেন। মুরগী প্রতিপালন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য তিনি স্বয়ং একটি কর্মী নিয়ে এসে কদিন থেকে গেছেন। ছাত্রসংঘের কড়া নির্দেশ এই দুধ এবং ডিম গ্রামের সব পরিবারকে প্রয়োজন অনুসারে বিতরণ করা হবে। যৌথ মালিকানা ছাত্রসংঘের এবং গ্রামের। আপাতত যা হচ্ছে তাতে ওরা পেটে খাক। ব্যবসার কথা পরে ভাবা যাবে। লোকগুলো যেমনি গরীব, তেমনি অলস। চাষবাসের কাজ ছাড়া আর কিছু করতে চায় না। মেয়েরা যত সহজে লেখাপড়া শিখে গেল, বয়স্ক পুরুষদের তত সহজে শেখানো যাচ্ছে না। যাই হোক সার্ভের রেজাল্ট ভালোই। গণস্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করতে শিখেছে মোটামুটি। অল্পবয়সীরা সবাই ব্যায়াম ও খেলাধুলো করে, দুধ ডিম খাচ্ছে সবাই এবং প্রত্যেকটি লোকের প্রাথমিক বর্ণপরিচয় হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাচ্ছে নীলমণি ও রতন নামে দুটি ঊনিশ কুড়ি বছরের ছেলে। নিরঞ্জন খাঁড়া হেড মাস্টারমশাই বয়স্ক শিক্ষার স্কুলের জন্য খুব পরিশ্রম করছেন। মাথায় ঘোমটা টেনে শ্রদ্ধাশীলা চাষী-বউরা পড়তে আসছে, নিরঞ্জনবাবু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে পড়িয়ে চলেছেন। গ্রামের মেয়েদের জলের জন্য অত সময় ও শ্রম ব্যয় হচ্ছে না, সে সময়টুকু তারা খুশী হয়ে লেখাপড়া শিখছে। মেধার পরিকল্পনা মেয়েদের স্বাবলম্বী করার জন্য তাদের কিছু শেখানো দরকার। তিনি পরামর্শ নিচ্ছেন কি করা যায়।
এই সময়ে, অপারেশন কেওড়াখালির তৃতীয় পর্যায়ের শুরুতে মৈথিলী ঠিক করল একটা মস্ত দল কেওড়খালি যাবে। ডাঃ দাশগুপ্তর ফার্মাকোলজি ক্লাসেই সে দেবপ্রিয়কে ধরল। ওকে চট করে ধরা যাচ্ছে না আজকাল। পড়াশোনা নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত বলেও তো মনে হয় না। ওর মেজজেঠুকে বলে মুরগী ও গরু মহিষের ব্যবস্থা করে দিল। মেজজেঠু ট্রেনিং-এর জন্য স্বয়ং কেওড়াখালি গেলেন পর্যন্ত। কিন্তু সেই চ্যারিটি শোর পর থেকেই দেবপ্রিয় ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ হয়ে আছে। ক্লাসের শেষে পেছন থেকে এগিয়ে গিয়ে দেবের কনুইটা শক্ত করে ধরল মৈথিলী। দেবপ্রিয় চমকে পেছন ফিরে তাকাল। এক লহমার জন্য তার চোখে যেন কেমন একটা ধরা-পড়ে-যাওয়ার দৃষ্টি দেখল মৈথিলী। সে বলল—‘দেব, আজ আমাদের বাড়ি চলো, দরকার আছে।’
—‘কি দরকার?’
‘সে যাই-ই হোক না কেন, জরুরি দরকার, এখানে বলা যাবে না।’
বাসে দুজনে আলাদা আলাদা বসেছে। চুপচাপ আসতে হল। মৈথিলীর বাড়ি চ্যাপেল রোডে, খুব ছায়াময় রাস্তাটা। পাশাপাশি চলতে চলতে দেবপ্রিয় হঠাৎ বলল—‘আমিই আসতুম। দরকারটা তোমার চেয়ে আমারই বেশি। কিন্তু সময় পাচ্ছিলুম না।’
বৈজু দরজা খুলে দিল। এখন মৈথিলীর বাবা-মা দুজনেই দিল্লি। দেবপ্রিয়কে নিজের ঘরে বসিয়ে মৈথিলী মায়ের ঘরে জামাকাপড় বদলাতে গেল। বৈজুকে বলতে হবে ভালো কিছু জলখাবার তৈরি করতে। দেব অনেক দিন পর এলো।
নিজের ঘরে ঢুকে সে অবাক হয়ে গেল, দেবপ্রিয় স্মোক করছে। মৈথিলীর কাছ থেকে একটা ছাইদান চাইল।
—‘দেব, তুমি সিগারেট ধরলে কবে?’
—‘অনেক দিন। ধরো, যতদিন তুমি তোমার খবরটা আমার কাছে চেপে রেখেছ।’
—‘কি খবর?’ মৈথিলী হালকা সুরে বলল।
দেবপ্রিয় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল—‘কি খবর তুমি জানো না? তোমার রেজাল্টের সঙ্গে আমার রেজাল্ট অদল-বদল হয়ে গেছে এই সাংঘাতিক জরুরি খবরটা!’
মৈথিলী বসে পড়ে বলল—‘দেব, ইট মাস্ট হ্যাভ বিন অ্যানাদার মিসটেক। দেখো এইচ.এস.-এ আমার রেজাল্ট দেখে স্কুলের কেউ বা আমি নিজে বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই রিভিউ করতে দিয়েছিলুম। দুবছর পর রেজাল্ট যখন এলো খুলে দেখলুম তারা কৈফিয়ত দিচ্ছে অন্য কার সঙ্গে নাকি আমার রেজাল্ট অদল-বদল হয়ে গিয়েছিল। মার্ক্সগুলো হুবহু তোমার। আমি বিশ্বাস করিনি। এই নিয়ে কী অসম্ভব হই-চই হবে জেনে আমি নিজে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করি। ওঁরা তখনও তোমাকে জানাননি। বুঝতেই পারছ, ওদেরও কী ভয়াবহ অবস্থা। চেয়ারম্যানের কাছে তখনই আমি জানিয়ে আসি আমি আমার আগের রেজাল্টটাই অ্যাকসেপ্ট করব। কারণ দেব, এবারের রেজাল্টটাও আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিলাম না। অঙ্কে আমি সিম্পলি দুশর মধ্যে দুশ পেতে পারি না। সেকেন্ড পেপারে দশ নম্বর আমি উত্তরই করিনি। আমার ধারণা আমার স্কুল, বাবার নাম, হোম সেক্রেটারির চিঠি ইত্যাদিতে ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ওরা আরও একটা সাঙ্ঘাতিক ভুল করেছে। কোথাও একটা গণ্ডগোল ঠিকই আছে, সেটা লোকেট করতে পারেনি, শুধু শুধু তোমার মার্কশীটটা নিয়ে টানাটানি করছে শুদ্দু তোমাদের সেন্টারের কোড নং ওয়ান এইট এইট আর আমাদেরটা সেভন ফোর ফোর বলে। সেভন আর ওয়ানে লেখবার দোষে গোলমাল হয়, আর ইংরেজি এইট আর বাংলা ফোর এক। আমি প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলাম। বলে এসেছি উনি যদি ফারদার এ নিয়ে আর কিছু করেন আমি কেস করব। তখন স্টেট এবং সেন্টারের মন্ত্রীদের কাছ থেকে পর্যন্ত চাপ আসবে। খাতাগুলো নিয়ে ছেলেখেলা করবার দুবছর বাদে এসব সংশোধন করা যায় না।
দেবপ্রিয় বলল—‘শুনেছি। উনি আমার স্কুলে ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে আমায় ডেকে পাঠান। সমস্ত ঘটনা জানান। মৈথিলী আমি কি তোমার চ্যারিটির ওপর আমার কেরিয়ার গড়ব?’
মৈথিলী বলল—‘দেব, য়ু হ্যাভ প্রুভড্ ইয়োর সেল্ফ্ এগেইন অ্যান্ড এগেইন। মেডিক্যাল কলেজের টার্মিনাল পরীক্ষাগুলো তো আর এইচ-এস-এর প্রহসন নয়।’
—‘হয়ত প্রোফেসররা আমার রেজাল্টের কথা জানেন বলে বায়াজ্ড্ হয়ে মার্কগুলো দ্যান।
—‘ক্লাসগুলো? ক্লাসে তোমার উত্তরগুলো? আমরা যেগুলো কেউ পারি না, তুমি তো সেগুলো…’
—দেবপ্রিয় বলল—‘আমার ধারণা মৈথিলী, তারপর থেকে তুমি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছ। পড়াশোনা সীরিয়াসলি নিচ্ছো না, যে জন্য নিজেকে ভোলাতে তুমি ছাত্রসংঘও নিয়ে মেতেছে।’
মৈথিলী বলল—‘বিশ্বাস করো দেব, আমি আমার যা পড়ার পড়ছিই। এর চেয়ে বেশি মনোযোগ আমি একটা জিনিসে দিতে পারি না। আর পড়াশোনার চেয়ে এইসব কাজে আমার আগ্রহ অনেক বেশি। ডাক্তারি পড়া মানে এতো সময়, এত ডিভোশন যদি আমি আগে জানতাম ফিজিওলজি কি বায়ো-কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়তাম। এদিকে আসতামই না। আমি বিশ্বাস করি ওরা আমারটা ঠিক করতে গিয়ে আরেকটা মারাত্মক ভুল করেছে। না হলে অঙ্কের ব্যাপারটা কি করে এক্সপ্লেন করবে?’
—‘ওটা তুমি বানাচ্ছো, মৈথিলী!’
—‘কী! বানাচ্ছি! আমি…দেব তুমি আমাকে জানো না। আমি সত্যি বলছি—সেকেন্ড পেপারে দশ নম্বর আমি সল্ভ্ করিনি। সময় পাইনি। কিন্তু আমি শিওর ছিলাম একশ নব্বই আমি পাবোই। ঠিক আছে অনেস্টলি বলো—তুমি কত উত্তর করেছিলে?’
দেবপ্রিয় বলল—‘উত্তর দুশই করেছি। কিন্তু তোমার মতো শিওর ছিলুম না যে দুশয় দুশই পাবো।’
‘এনি ওয়ে তুমি দেখছ তো। তোমার দুশ আসতে পারে। আমার আসতে পারে না। অথচ রিভিউ করে ওই অদ্ভুত চারশ বিশ রেজাল্টটা ওরা আমায় পাঠালো। আমি নিশ্চিত ওরা জানে তোমাদের মফঃস্বলের স্কুল বা তুমি ক্যানডিডেট এ নিয়ে বিশেষ কিছু করতে পারবে না। অপর পক্ষে, আমি হয়ত সব তোলপাড় করে ফেলব। ভয়ের চোটে ওরা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছে। দেব, প্লীজ এ নিয়ে তুমি একদম ভাববে না। তোমার ওপর অন্যায় অবিচারটা আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে বন্ধ করেছি। আই অ্যাম সরি দ্যাট আই এভার স্টার্টেড ইট। দীজ পীপ্ল আর অল সো ইনকমপিটেন্ট, সো ক্যালাস অ্যান্ড সো করাপ্ট্।’
দেবপ্রিয় ভাবিত গলায় বলল—‘আমি খুব ভালো পরীক্ষাই দিয়েছিলুম। কিন্তু স্বপ্নেও ওই রেজাল্ট আশা করিনি মৈথিলী।’
—‘আশা করো নি, কারণ মফঃস্বলে তোমাদের মাস্টারমশাইরা আমাদের এদিকের মতন চুলচেরা বিচার করেন না। ওঁদের অ্যাসেসমেন্টে হয়ত একটা কমপ্লেক্সও কাজ করে। তাছাড়াও প্রতিযোগিতা কম। কলকাতার মতো শহরে, আমাদের মতো স্কুলে কমপিটিশন কি চেহারা নেয় তুমি ধারণাই করতে পারবে না। ধর কোনও কম্পোজিশনের টাস্ক আছে। এক্স-এর সঙ্গে ওয়াই-এর এক নম্বরের তফাৎ। আমাদের ক্লাসে বোঝানো হত এক্স একটা চমৎকার ইডিয়মেটিক ফ্রেজ ব্যবহার করেছে, বড় বড় মনীষীদের ব্যবহার করা বাক্যবন্ধ। সুতরাং, ওয়াই তোমাকে ওইরকম দুটো ব্যবহার করতে হবে বেশি মার্কস পেতে গেলে। একদম পরীক্ষা-মুখী পড়াশোনা, কোচিং। কী বিশ্রী তুমি ভাবতে পারবে না দেব। তোমরা যা করো স্বাধীনভাবে নিজেরা করো, তোমাদের কাজে স্বকীয়তা থাকে, আনন্দও থাকে। কবে যে এই কোচিং সিসটেম, পরীক্ষার এই পদ্ধতি ভেঙে পড়বে, চুরমার হয়ে যাবে আমি সেইদিনের অপেক্ষায় আছি। আমার নিজের ধারণা প্রথম একশ কি দুশ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে গুণগত কোনও তফাৎ নেই। এদের মধ্যে যে কেউ প্রথম আসতে পারে। সবটাই নির্ভর করছে সেই অজানা এক্স-ফ্যাকটার-এর ওপরে। যাকে অবৈজ্ঞানিক মনের লোকেরা লাক নাম দিয়েছে। তার উপরে আছে ভুল, গাফিলতি। পর্বতপ্রমাণ। ওদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ওরা করুক। আমরা কেন করতে যাবো!’
—‘তুমি তো করছো। তোমাকে করতে হচ্ছে। জয়েন্টে তুমিই সর্বপ্রথম ছিলে মৈথিলী!’
—উঃ আবার সেই এক কথা। তুমি কি বিশ্বাস করো জয়েন্টটা সত্যি-সত্যি ট্যালেন্টের পরীক্ষা?’ প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক সংক্ষিপ্ত জবাব তোমার আগে থেকে জানা চাই, নইলে তুমি পারবে না।’
—‘তোমার জানা ছিল?’
—‘প্রত্যেকটি জানা ছিল। আমাকে যিনি কোচ করতেন তিনি প্রত্যেকটা ঘড়ি ধরে করিয়েছিলেন। সেখানে তুমি নিভর্র করছে তোমার স্বাভাবিক স্মৃতি, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও স্পীডের ওপরে। আমাদের সঙ্গে তুমি পারবে কি করে?’
—‘তুমি কি বলতে চাও তোমার কোচ সব প্রশ্ন জানতেন? এই রকম করাপ্ট্ সবাই?’
—‘আমি জানি না। আপাততঃ আমি জানতে চাই না। আই অ্যাম নাউ এ হানড্রেড টাইম্স্ মোর ইন্টারেস্টেড ইন হেল্পিং বিল্ড অ্যান আইডিয়্যাল ভিলেজ।’
দেবপ্রিয় উঠে দাঁড়াল। বলল—‘কিন্তু আমি যে জানতে চাই! শিক্ষাব্যবস্থা যদি এভাবে আমাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তবে ছাত্র হিসেবে আমার প্রথম কর্তব্য কি নয় এই দুর্নীতি আর গাফিলতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। এই করাপশন তো সর্বত্র ছড়াবে। যার যেখানে পৌঁছবার কথা সে সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তোমার আদর্শ গ্রামই কি এর থেকে বাঁচবে? মৈথিলী, আমার মনে হয় তোমার শক্তি তুমি ভুল খরচ করছ। বলব না তুমি স্বার্থপর, তুমি আমার জন্য যে স্যাক্রিফাইস করলে তার ম্যাগনিচুড আমি এখনও কল্পনা করতে পারছি না। কিন্তু প্রোগ্রাম নির্বাচনে তোমার কোথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে। হয়ত তোমার এতো পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত বৃথা প্রমাণিত হবে।’
—‘হোক দেব। তুমি বসো তো! আমরা যে যার সাধ্যমতো চেষ্টা করি। পুরোপুরি সফল হবার আশা যে দুরাশা তা আমার জানা আছে। তুমি কি জানো, পালানকে আমি আর ধরতে পারছি না! উত্তর কলকাতায় একটা দক্ষিণ কলকাতায় একটা আসর করলাম, ইচ্ছে ছিল—জেলায় জেলায় করব। কিন্তু ওকে দূরদর্শনে সুযোগ করে দেওয়ার পর ও নানা জায়গায় আমন্ত্রণ পাচ্ছে। আমার কাছে খবর আছে ভারত সরকার লোকোৎসব করবে আবারও। দলবল নিয়ে রাশিয়া যাবে। এখন ছাত্রসংঘের জন্য গান করতে হলে ওকে অনেক কম টাকায় করতে হবে। কেষ্ট পালান খগেন কাউকে আমরা ধরতে পারছি না। এটা আমাদের একটা ব্যর্থতা। কিন্তু দুতিনজন সত্যিকারের শিল্পী এই যে পরিচিতি পেল, মান পেল, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারল-এটাও তো খানিকটা সাফল্য!’
‘সাফল্য নয়, জীবনযাত্রার মাপকাঠি হবে সততা, আন্তরিকতা, দক্ষতা, মৈথিলী, অন্য কিছু নয়। আমাদের নিজেদের মধ্যে যেন অন্তত পক্ষে এই মূল্যবোধ নিয়ে বিভ্রান্তি না থাকে। সাফল্যের চাকচিক্য দেখে যদি ভুলে যাই এর ভেতরে অনেক স্বার্থপরতা, গৃধ্নুতার অন্ধকার আছে তবে আমাদের সংঘ টংঘ গড়ে কোনও লাভ নেই। এরকম প্রতিষ্ঠান তো চারদিকে প্রচুর আছে। তাদের সংখ্যায় আর একটা যোগ করাই কি আমাদের উদ্দেশ্য! পালান গ্রামে গ্রামান্তরে গান গেয়ে সাধারণ চাষীভুষো গরিব লোককে অনাবিল আনন্দ দিচ্ছে, পরিবর্তে সে পরিশ্রমের অন্ন খাচ্ছে তার গ্রামের মাটির বাড়ির দাওয়ায় বসে, এ দৃশ্যটা সুন্দর। সুটবুট পরে ভি. আই. পি. সুটকেস হাতে রাশিয়ায় যাবে বলে সে প্লেনে উঠছে এবং তোমাকে এড়াবার জন্য যথাসম্ভব কৌশল অবলম্বন করছে এ দৃশ্যটা কল্পনা করতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না।’
বৈজু অনেক খাবার-দাবার করে এনেছে, সে হাসিমুখে এসে বললে—‘দেবুদাদা, খাও। অনেকক্ষণ পড়া লেখা করেছ দুজনে। বাব্বাঃ আমারই গলা শুকিয়ে গেল।’
বৈজু চলে গেলে মৈথিলী বলল—‘দেব তুমি আমাকে কথা দাও, ওই পরীক্ষার রেজাল্টটার ব্যাপার নিয়ে তুমি তোমার মনের মধ্যে কোনওরকম কমপ্লেক্স রাখবে না!’ দেবপ্রিয় উত্তর দিল না।
—‘কথা দাও দেব। আমি তোমাকে যথেষ্ট কারণ দেখিয়েছি আমার সিদ্ধান্তের।’
—‘যদি কথা-টথা না-ই দিই, তো তুমি কি করবে?’—দেবপ্রিয়র মুখে দুর্লভ হাসি। মৈথিলীর মনে হল দেবপ্রিয় সহসা হাসে না, খুব গম্ভীর প্রকৃতির। তার হাসি দুর্লভ বলেও এত অসামান্য সুন্দর। যেন গম্ভীর নিশীথ আকাশের বুক হাসিয়ে হঠাৎ ত্রয়োদর্শীর ফালি চাঁদ ওঠা।
মৈথিলী হেসে বলল—‘ইন দ্যাট কেস আমি বোর্ডের যতজন পারি কর্মীর চাকরি খাওয়ার জন্যে চেষ্টা করব। এনকোয়ারি কমিশন বসবে, বার করবে আমার অঙ্কের খাতা কে দেখেছিল। পরীক্ষক, স্ক্রুটিনিয়ার যে যেখানে আছে সবাইকে খাবো। শুধু হোম সেক্রেটারি নয়, ডেপুটি কমিশনার ক্যালকাটা পুলিস আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মন্ত্রী শান্ত্রী মহলেও কিছু কিছু চেনাশোনা আছে।’
দেবপ্রিয়র হাসিটা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। বললে—‘বাজে কথা বলছো।’
—‘কোনটা, চাকরি খাওয়ার কথাটা? না চেনাশোনা থাকার কথাটা?’
—‘প্রথমটা।’
—মৈথিলী বলল—‘হায় দেবপ্রিয় তুমি জানোই না আমি হোয়াইট লাই ছাড়া মিথ্যে কথা বলি না।’
দেবপ্রিয় মিটিমিটি হেসে বলল—‘জানি। তা এটা সেইসব সাদা মিথ্যের একটা নয় তো?’
—‘ন্ নো! নেভার!’ মৈথিলী জোরে জোরে হেসে উঠল।
দেবপ্রিয় বলল—‘মৈথিলী তোমাকে আমি যতই আবিষ্কার করছি ততই ভালোবেসে ফেলছি। নিশ্চয় বুঝতে পারছ কি বলতে চাইছি!’
মৈথিলী চেয়ারটা দোলাতে দোলাতে বলল ‘শিওর! তোমাকেও আমি যে পর্যন্ত প্রীতি করি, তাহা বোধ করি মনুষ্যে সম্ভবে না।’
দুজনেই খেতে খেতে হাসছে। হঠাৎ চেয়ারটা থামিয়ে মৈথিলী বললে—‘ভুলেই গিয়েছিলাম। দেব, তুমি সিগারেট খাওয়া কবে থেকে ধরলে!’
দেবপ্রিয় বলল—‘যেদিন বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে ইন্টারভিউটা সেরে এলুম সেইদিন থেকে। কিন্তু সেটা ছিল সাময়িক। সিগারেটের নেশাটা জমে উঠেছে যেদিন থেকে একজন আমার পকেটের নির্দোষ প্যাকেটটা বার করে নিয়ে সেখানে অন্য একটা প্যাকেট ভরে রাখে। একই রকম দেখতে, খালি সিগারেটগুলো আলাদা।’
—‘মানে?’
—‘মানে খুব জটিল মৈথিলী। ছাত্রসংঘের কেউ আমাকে ড্রাগ ধরাতে চাইছে।’
—‘হো-য়াট!’ মৈথিলীর হাত থেকে টুং করে চামচ পড়ে গেল—‘কি বলছো? কে?’
—‘এখনও শিওর হতে পারি নি। কিন্তু প্রায় ধরে ফেলেছি। আমি প্যাকেট থেকে দুটো খেয়েই বুঝতে পারি, কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। আগে কখনো খাইনি বলে ধরতে দেরি হল। ভেবেছিলুম অ্যানালিসিস করবো, কিন্তু লুকু সব মাটি করে দিল।’
—‘লুকু?’
—‘হ্যাঁ। ও আবার হয়ত মজা করেই আমার প্যাকেট থেকে বাক্সটা চুরি করে, না পেয়ে প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি, ভেবেছি যে দিয়েছিল সেই নিয়ে নিয়েছে। তারপর কেমন সন্দেহ হয়। লুকু সেদিন চ্যারিটি শো-এ থেকে থেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছিল—‘কার কি হারিয়েছে, মদনমোহন পালিয়েছে।’ তোমরা চলে গেলে কেওড়াখালি, শুনলুম লুকু যায়নি, অসুস্থ। কেমন মনে হল, ওর বাড়ি গেলুম দুপুরবেলায়। যা ভেবেছি ঠিক। একটু আগেই সিগারেট খেয়েছে। গন্ধ পেলুম। ভীষণ বমি করল। স্বীকারও করল। ও অবশ্য বুঝতে পারেনি সিগারেটে ড্রাগ ছিল। ও নিশ্চয়ই আমার কার্যকলাপ খুব রহস্যজনক মনে করেছে। কিন্তু খালি প্যাকেটটা পেলুম, আটটা সিগারেট ফুঁকে দিয়েছে। অ্যানালিসিস করানো হল না। যাই হোক আমার ধারণা—ওটা হেরোইন।
—‘বলো কি? সেইজন্যে তুমি কেওড়াখালি যাচ্ছো না?’
‘সেটা একটা কারণ। কিন্তু আমি প্রবলেমটাকে এড়াতে চাইছি না। আমি ওই ছেলেটিকে খুঁজে বার করবই। মৈথিলী তোমরা কিন্তু সাবধান। আমি একাই যে ওর লক্ষ্য তা না-ও হতে পারে। প্রথমে আমার তাই মনে হয়েছিল, এখন আমি শিওর ও সব্বাইকে ড্রাগ ধরাতে চাইবে। যারা যারা স্মোক করে, তাদের সবাইকে সাবধান করে দেওয়া দরকার।’
—‘কেন এর উদ্দেশ্য কি? নিজে লেজ কাটা শেয়াল, তাই সবাইকার লেজ কাটতে চাইছে?’
—‘উঁহু তাহলে তো সোজাসুজি অফার করতে পারত। কলকাতায় এসে আমি বেশ কয়েকটা নেশাড়ে গ্রুপের সংস্পর্শে এসেছি যারা আমাকে সোজাসুজি ‘গুরু গুরু’ বলে নেশা ধরাতে চেয়েছে। এরা নিজেরা নেশাড়ে, এখন ড্রাগ-পেডলারও হয়ে গেছে। এটা অন্য কিছু। কি আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারি নি। বোঝবার চেষ্টা করছি।’ বলতে বলতে দেবপ্রিয় অস্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করল। ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—‘মৈথিলী তোমরা বারবার রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছো, মনে আছে সেদিন দুদলের দুজন তোমাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে বললে তুমি কিভাবে ওদের এড়িয়ে গেলে! এই রাজনৈতিক দলগুলো সব একেকটা বড় বড় ক্ষমতালোভী চক্র। এরা যেমন তেমন করে নিজেদের দল বাড়াতে চায়। যে কোনও মূল্যে। বয়স্ক ভোটাধিকারের দেশে এটাই ওদের একমাত্র উপায়। কোনও নীতি নয়, আদর্শবাদ নয়, শুদ্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ফলে হু হু করে বেনোজল ঢুকছে সর্বত্র। এ যদি রামা গুণ্ডাকে তোষণ করে তো আরেকজন করে শামা গুণ্ডাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা কোনও রাজনৈতিক দল ছাড়াই শুধু সোশ্যাল ওয়ার্কের জন্য সংঘবদ্ধ হচ্ছে এটা কোনও পার্টিরই ভালো লাগবার কথা নয়। আবার দেখো, দেশের যুবশক্তিতে ঘুণ ধরিয়ে দেবার জন্যও একটা চক্র আছে। স্বদেশী কি বিদেশী জানি না। তাছাড়াও আছে সিম্পলি টাকা। মাদকের ব্যবসা করে যারা কোটি কোটিপতি হচ্ছে তাদের জাল ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর সর্বত্র। এখন কি মোটিভ এখানে কাজ করছে বলা শক্ত। তবে তুমি সতর্ক হয়ে তোমার কাজ করে যাও, আমি এর শেষ দেখবই।’
মৈথিলী উদ্বিগ্ন হয়ে বলল—‘আমায় বলবে না দেব, ঠিক কাকে তোমার সন্দেহ?’
—‘সন্দেহের কথা বলতে নেই। মৈথিলী, তোমার ঘনিষ্ঠদের মধ্যেই কেউ। বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল।’
—‘তুমি একা এই সব চক্রের পিছনে ঘুরো না দেব। এগুলো হঠকারিতা। মেধাদিকেই বা বলছ না কেন?’
দেবপ্রিয় চেয়ারে বসে পড়ল, বলল—‘মৈথিলী মিস ভাটনগরের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমায় বলতে পারো? উনি দু দফায় দশ বছরের ওপর স্টেটসে কাটিয়ে হঠাৎ ফিরে এলেন কেন? ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গেই বা ওঁর দহরম মহরম কেন? সহকর্মীদের সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নেই। একা-একা থাকেন। ভদ্রমহিলা খুব রহস্যময়!’
মৈথিলী হেসে বলল—‘সি আই এর জুজু দেখছ না কি? তুমি মেধাদির সঙ্গে একটু মেলামেশা করো। অত রহস্যময় ওঁকে আর লাগবে না। আসলে তুমি রজ্জুতে সর্পভ্রম করছ। দেবপ্রিয় বলল—‘তুমি কি জানো মৈথিলী, মেধা ভাটনগর ছাত্র-জীবনে বিপ্লবী মার্কসিস্ট ছিলেন পরে হঠাৎ উধাও হয়ে যান। ওর নেকস্ট ট্রেস পাওয়া যায় বস্টনে। এখন আবার উনি হঠাৎ কলকাতায় এসে বসেছেন।’
মৈথিলী বলল—‘মার্কসিস্ট হওয়াটা কি অপরাধ?’
—‘একেবারেই না। মৈথিলী দেখো, আজকালকার যুগে এমন কে আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছে যে মার্কসিজমের কতকগুলো বেসিক টেনেট অস্বীকার করে! কে সাম্য চায় না? আমাদের ছাত্রদের মধ্যে এমন কে আছে যে পুঁজিবাদের সপক্ষে কথা বলবে? কেউ না। আমরা সবাই চাই এ এসট্যাবলিশমেন্ট ভেঙে গুঁড়িয়ে যাক। অন্য কিছু আসুক। কিন্তু আমরা যা চাই সেই দুর্নীতিমুক্ত কুসংস্কারমুক্ত, ভয়হীন, ন্যায়পরায়ণ খোলা আবহাওয়া যেখানে মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন—খাদ্যের, স্বাস্থ্যের, বস্ত্রের, শিক্ষার, প্রয়োজন মিটবে সে কি মার্কসিজমের পথেই কোথাও এসেছে? বিপ্লবের পথ দিয়েই কি তা এলো? বরং ঘোলা জলকে আরও ঘুলিয়ে দিয়ে গেল সব।’
—‘ঠিক আছে আসেনি। তুমি তার জন্য মেধাদিকে একা দায়ী করছ কেন?’
—‘প্রথমত এই জন্য যে এঁরা অল্প বয়সে মার্কসিজমে দীক্ষিত হয়েছিলেন, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন। কোনও মতবাদই বাস্তব অবস্থা নিরপেক্ষ তো হতে পারে না। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসিস্ট থিয়োরিতে কোথায় কোথায় পরিবর্তন দরকার সেটা তাঁদের বুঝতে পারার সময় ও সুযোগ ছিল, সেটা তাঁদেরই দেখবার কথা, মার্কসের ভূত তো সেটা দেখবেন না! কোনকালে ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে গেছে সাতদিনে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল, ক্রিশ্চানরা আজ কি তা মানে? কোন কালে টলেমি বলে গিয়েছিলেন সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে আজ কি আমরা তা মানি? তবে? তাঁরা ভাবলেন না। কিচ্ছু করলেন না, স-ব পশ্চাদপসরণ করলেন। কেন? ঊনিশ শতকের য়ুরোপে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশনের পটভূমিকায় যে থিয়োরি গড়ে উঠেছিল ভারতের অর্থনৈতিক বিন্যাসে তার কতটা রদবদল করা দরকার তাঁরা ভাবলেন না। কিচছু করলেন না, স-ব পশ্চাদপসরণ করলেন। কেন? যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তার রূপায়ণে যেই অসুবিধে দেখা দিল, অমনি মোহভঙ্গ হল, অমনি পলায়ন করলেন? যাই বলো, এটাও সুবিধাবাদ। একবার প্রমাণ হয়ে গেছে উনি কিচ্ছু করতে পারেন নি। এখন আবার ফীল্ডে নেমেছেন, কেন? দুনিয়ার বহু ইনটেলেকচ্যুয়ালকে আমি এইভাবে পালাতে দেখছি। প্রথমে মার্কসিজম লেনিনিজম মাওইজম তাঁদের ভীষণ আকর্ষণ করে, তাঁরা বড় বড় কবিতা লিখে ফেলেন। পরে মোহভঙ্গ হয়, গালাগাল বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁদের খেয়াল হয় না, ভুলটা দেখতে পেয়েও তাকে না শুধরে পালিয়ে যাবার জন্য তাঁরা আরও বেশি সমালোচনার যোগ্য।’
—মৈথিলী তর্কে যোগ দিল না। শুধু বলল—‘দ্বিতীয় কারণ?’
—‘দ্বিতীয় কারণ এই যে মিস ভাটনগর তাঁর পূর্ব পরিচয় আমাদের কাছে গোপন রেখেছেন। আমি তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানতে পেরেছি মেজজেঠুর কাছ থেকে। মেজ জেঠু সে সময়ে সরকারি চাকরি করতেন। অনেক কিছু জানেন। মেধা ভাটনগর নাম শুনেই চিনতে পেরেছিলেন, আমাকে পরে বলেছিলেন এরা ভাঙার দলে। খালি ভাঙতে চায়।’
—‘দেব, মানুষ কি বদলায় না? যিনি এক সময় ভাঙার পক্ষে ছিলেন, তিনি কি এখন গড়ার দলে আসতে পারেন না?’
—‘মানুষ বদলায় মৈথিলী, কিন্তু যখন কেউ কোনও তত্ত্বকে গভীরভাবে জীবনে গ্রহণ করে তখন সেই তত্ত্বটা সম্পর্কেও তার দায়িত্ব থাকা দরকার। ধরলুম আর ছাড়লুম, ছাড়লুম আর আমেরিকা উড়ে গেলুম আমার সুবিধে আছে বলে—এ আমি সমর্থন করতে পারি না।’ মৈথিলী স্পষ্টই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, সে বলল—‘দেব, তুমি মেধাদিকে এমন কঠোরভাবে বিচার করার আগে ওঁর সঙ্গে মেশো। ওঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা জানো। জেনারালাইজ করো না। মেধাদির ভিতরে কোথাও একটা তীব্র জ্বালা আছে, দুঃখ আছে। সেটা ঠিক ব্যক্তিগত কারণে নয় বলে আমার মনে হয়। আমরা শুধু শুধু ওঁকে আমাদের চেয়ার পার্সন করিনি।’
দেবপ্রিয় এখন অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছিল, আস্তে আস্তে বলল—‘আমার আশঙ্কাগুলো সম্পর্কে ওঁকে আমি কিছুদিন আগে একটা চিঠি দিয়েছিলুম মৈথিলী। তখন আমারও ওঁর ওপর আস্থা তোমার মতোই। উনি সেই জরুরি চিঠিটার কোনও উত্তর তো দিলেনই না। মাঝে মধ্যে যখন দেখা হয় সেটার উল্লেখও করেন না। উপরন্তু আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন আমি একটা বাচ্চা ছেলে, আমার অসুখ করেছে, উনি আমাকে লজেন্স দিয়ে ভোলাবেন। মৈথিলী আমি তোমাদের প্রত্যেককেই স্টাডি করছি। তুমি এই পরীক্ষায় পাশ করে গেছ তাই তোমায় এতো কথা বললুম। অন্য অ্যানালিসিসগুলোর রিপোর্ট-এর জন্য অপেক্ষা করছি। ইন দা মিন টাইম তুমি গোপনতা রক্ষা করবে।’
মৈথিলী হেসে বলল—‘তোমার কি সন্দেহ আছে, তাতে?
অধ্যায় : ১১
ফুলতলির মাঠ এখন ঘাসে ঘাসে সবুজ, খানা ডোবা গর্ত বুজে গেছে, মাঝখান দিয়ে চওড়া সড়ক চলে গেছে, যা গ্রামের লোকেদের নিজেদের তৈরি। এ রাস্তাটা ওদের খুব দরকার হয়। পার হতে এবার আর ভ্যানগাড়ির দরকার হল না। দুটো জিপ যোগাড় করেছে প্রমিত। কলকাতা থেকে ধপধপি এসে, তারপর সোজা জিপেই আসা হল হই হই করতে করতে। গ্রামে ঢুকতেই একটা ঘন জঙ্গুলে জায়গা। মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ। সুঁড়িপথ ধরে কোয়ার্টার মাইলটাক পথ গেলে তবে গ্রাম পড়বে। জঙ্গলটা প্রধানত বাঁশঝাড় বাবলা, গরান, নিম, আম ইত্যাদি গাছে ভর্তি। দু চারটে মহাকায় শিরিষ আছে, কেওড়া বা কেয়া একেবারেই নেই। হয়ত বহুকাল আগে যখন সমুদ্রের লোনা জল মাতলা পিয়ালি বেয়ে এসে সব প্লাবিত করে দিত, তখন কেওড়া গাছে ভর্তি ছিল এসব অঞ্চল। এখন এসব মৃত বদ্বীপ অঞ্চল। বিশুদ্ধ ম্যানগ্রোভ প্রকৃতির গাছ বিশেষ নেই। হোগলা, হেঁতাল, শোলা এগুলো অবশ্য খুব দেখা যায়। এই জঙ্গলটা নোংরা।সুঁড়িপথ ধরে গেলে অসুবিধে নেই। কিন্তু পথ থেকে খুব ভেতর দিকে যাওয়া যায় না। ওরা এবার না বলে এসেছে। দলে অনেকে আছে। অনেকেই আগে আসে নি। বাঁশের সরু সরু নরম ডগাগুলো দু হাতে সরাতে সরাতে প্রথমে চলেছিল উজান, পেছনে মেধা। মেধার পাশে লুকু। পেছনে দেবপ্রিয় ও মৈথিলী। বাকিরা আসছে আস্তে আস্তে। জীপগুলো এখন ধপধপির দিকে ফিরে যাবে। সেখানে প্রমিতদের কোনও চেনাশোনা আছেন। সন্ধের দিকে আসবে আবার।
সুঁড়ি পথটা পেরোতেই গ্রামটা যেন হঠাৎ ঘোমটা তুলে বেরিয়ে পড়ে। মেঠো রাস্তা। পরিষ্কার। দুপাশে এলোমেলো ঝোপের বিস্তার। মাঝে মাঝে এদের কুটির। খানিকটা এগোতেই ডানদিকে রাস্তার পাশে একটা বড় হোর্ডিং। গাঢ় সবুজের ওপর সাদা দিয়ে লেখা :
“অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু;
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।”
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এটা করেছে গুঞ্জন সিং।
একটি বুড়ি মানুষ রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছিল। ঝুড়িতে জড়ো করছে শুকনো পাতা, কাটি কুটি। এখন সকাল আটটা নটা বাজে। মাহিষ্যপাড়া শুনশান। উজান বলল—‘সমুর দিদা। গতবারে ওদের বলে দিয়েছিলাম যে যার বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার রাখতে। তা কাজটা করছে দেখছি।’
ওদের পায়ের শব্দে বুড়ি মুখ তুলে তাকাল। ফোকলা মুখ সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভরে গেল। —‘ও নারাণীর মা, ও সমুর মা, দেখে যা কারা এয়েচে।’ বুড়ি কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ‘হ্যাঁ গো উজান বাবা, মিলিদিদি ভালো আচো।’ সমুর দিদা মৈথিলী উচ্চারণ করতে পারে না।
ঘরের আগড় ঠেলে দুটি মহিলা বেরিয়ে এলো। একজনের পরনে লাল কালো নীল হলুদে কটকি শাড়ি ঝকমক করছে, আরেক জন পরেছে একটা কমলা রঙের অর্গ্যানজা শাড়ি, ভিজে গেছে শাড়িটা, মধ্যে ফ্যাব্রিকের কাজ। দুজনেরই হাসি মুখ।
—‘আসুন, আসুন,’ দাওয়ার ওপর সঙ্গে সঙ্গে মাদুর বিছিয়ে দিল ওরা।
—‘ভালো আছো পদ্ম?’ মেধা জিজ্ঞেস করলেন।
—‘থাকবো না? এমন সব কাপড় দিছেন, কত দেখাশুনো করছেন, যুক্তবন্ন পড়তে শিকে গেচি।’
—‘তাই? ক্লাসেই শিখলে?’
—‘না। সমুর ঠেঁয়ে।’
—‘বাঃ। সমুকে তো একটা প্রাইজ দিতে হবে দেখছি। সুবচনী তুমি?’
—‘তোমাদের সুবচুনী পোয়াতি হয়চে গো!’ সমুর মা ওদিক থেকে হেসে বলল।
সুবচনীর প্রতি বছর একটা করে মেয়ে হয়। এ গ্রামে পরিবার-পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজ মৈথিলী অবশ্য করে গেছে। কিন্তু গ্রামের কাউকে ঠিকমতো পরিচালনা করবার জন্য এখনও পাওয়া যায় নি। মৈথিলী আড়চোখে দেখল মেধাদির মুখ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। এ গ্রামে জন্মহার খুব বেশি। সমুর দিদার রেকর্ড আছে ষোলটি সন্তান। তার থেকে নানান বয়সে মরে মরে এখন পাঁচটিতে দাঁড়িয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—‘পদ্মকাকী, তুমি সুবচনী কাকীর খাওয়া-দাওয়াটা ঠিকমতো দেখছো তো? দুধ-ডিম ঠিকঠাক পাচ্ছো? বড্ড ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কিন্তু!’ সমুরা নিতান্ত ছোট চাষী। তাদের জমি বংশ পরম্পরায় ভাগ হতে হতে এখন সমুর বাবা ও দুই কাকার ভাগে যা এসে দাঁড়িয়েছে তাতে তাদের সারা বছরের অন্ন জোটা মুশকিল। কিন্তু সমু বা সমরকুমার হাজরা খুব বুদ্ধিমান ছেলে।
সমুর মা পদ্ম বললে—‘সুবচনীর পাঁচটা মেয়ে, আমার দুটো ছেলে দুটো মেয়ে। নোকে বলচে তাবৎ ডিম দুধ তো সেকালে একজনের বাড়িতেই ঢালতে হয়। যা আসচে ওরই মধ্যে চালাতে হবে, তা মুখপুড়ি মেয়েদের না দিয়ে, ঠাকুরপোকে না দিয়ে খেতে চায় না, এদিকে ভীষণ অরুচি। দুধসাবু ছাড়া পেটে কিছু থাকচেও না দিদি।’
—‘আচ্ছা, আমি দেখছি’—মেধা বললেন। গ্রামে সকলেই সমুদের মত গরিব নয়। যাদের নিজস্ব গরু ছাগল আছে, ঘরপোষা হাঁস মুরগী আছে, তাদের যৌথ ডেয়ারি পোলট্রির জিনিস পাবার ততটা অধিকার নেই যতটা এদের আছে। এখন উৎপাদন ঠিক কতটা, কত জনের মধ্যে বিলি হচ্ছে এ হিসেবটা পাওয়া দরকার।
সমুদের দাওয়া থেকে ওরা উঠে পড়ল। পদ্ম বলল—‘তাহলে আপনাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করি, এখন একটু মুড়ি খান। নারকোল কুরে দিচ্চি।’ আগে যতবার এসেছেন এরাই উদ্যোগী হয়ে পাড়া প্রতিবেশী জড়ো করে তাঁদের খাবার ব্যবস্থা করেছে।’ মেধা বললেন—‘এবার আমরা খবর না দিয়ে এসেছি পদ্ম, আজ আমাদের চড়ুই ভাতি। নিজেরা রান্না করে খাবো। তোমরা ভেবো না। আমি সুবচনীর সঙ্গে একটু কথা বলি। তোরা স্কুলের দিকে এগো।’
সুবচনীকে নিয়ে মেধা ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে চলতে চলতে বললেন—‘দেব, কলকাতায় ফিরে গিয়েই তোমাকে কিছু ওষুধপত্র টনিক কিনতে হবে। কারুর হাতে নয়, নিজে এদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবে। হয় সদর হাসপাতালে, নয় মেডিক্যাল কলেজেই এর ব্যবস্থা করতে হবে। পুত্র সন্তান না হওয়া পর্যন্ত এই অ্যানিমিক মেয়েটাকে এরা রেহাই দেবে না মনে হচ্ছে।’
পাতকুয়োগুলো শুকোতে আরম্ভ করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই নলকূপগুলো হবে একমাত্র ভরসা। মাতলা পিয়ালির মজা খালগুলো এরা সংস্কার করতে আরম্ভ করেছে। মহিষ দুটো জলার মধ্যে নেমে গেছে। ধারে ভিজে ঘাস মাটির ওপর কয়েকটা গরু শুয়ে শুয়ে আধবোজা চোখে জাবর কাটছে।
স্কুলের ছেলেরা এদিকে মুখ করে পড়ছে। ওরাই দেখতে পেয়েছে আগে। হই-হই করে উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই। নিরঞ্জন খাঁড়া ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে নেমে এলেন। গুঞ্জন, লুকু আর মৈথিলীকে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে ছেলেমেয়েগুলো। ওদের লজেন্স-টফি-পিপারমিন্ট বিতরণ করছে ওরা। খাঁড়া বললেন—‘হয়েছে। হয়েছে। এবার সব যে যার জায়গায় গিয়ে বসো।’
মেধা এসে বললেন—‘এরা এরকম সং সাজলো কোত্থেকে রে?’
ছেলেদের পরনে সাদা নীল সেলর স্যুট, নিকার বোকার, একটু বড় ছেলেরা পরেছে জিনস। তিনকড়ি, সমু এগিয়ে এলো পেছনে আরও দু চার জন, প্রত্যেকের গায়ে স্পোর্টস শার্ট। তার ওপর বড় বড় করে নানারকম লেখা। সমুর বুকে লেখা ‘হাই মারাদোনা’, তিনকড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে লাল গেঞ্জি পরে তাতে নীল দিয়ে লেখা ‘বেট, য়ু লাভ মি’, ঝলমলে ব্যাগিজ পরেছে অনেকেই।
মেধা আবার বললেন—‘হ্যাঁরে, গ্রামে ঢুকে থেকে দেখিছ এরা ছেলে-বুড়ো সব্বাই সঙ সেজেছে। নিরঞ্জনই বা ওর ওই জামাটা কোত্থেকে পেল? গোটা শার্টটায় নিউজ পেপার ক্লিপিং-এর ছাপ! খুবই দামী জামা, একটু রঙ জ্বলে গেছে, কিন্তু একেবারে অত্যাধুনিক কাপড়। এই গরমে ওরা পরছেই বা কি করে এসব?’
মৈথিলী বলল—‘নিরঞ্জনদা আপনি পড়ান। আমরা একটু ঘুরে আসি। স্কুল ঘরেই রান্না-টান্না করব।’
পথে নেমে উজান বলল—‘নিরঞ্জনদা বলছিল গ্রামে অন্ন আর ওষুধ-পথ্যেরর অভাব অনেকটাই ঘুচেছে। কিন্তু ওদের এমন অবস্থা নেই যে জামাকাপড় কেনে। পুরনো জামা-কাপড় চেয়েছিল। আইডিয়াটা আমাকেও স্ট্রাইক করে। সত্যিই তো আমাদের সবার বাড়িতেই খুঁজলে নানা সাইজের পুরনো জামা-কাপড় পাওয়া যাবে। সেগুলো জড়ো করে রেখেছিলাম, নিরঞ্জনদা দু তিনবার এসে এসে নিয়ে গেছে। মৈথিলীর বাড়ি থেকে মউমিতার বাড়ি থেকে, আমার বাড়ি থেকেও। আমার বাড়ি অবশ্য জলগ্রহণ করেনি।’
মেধা বললেন—‘ওদের যে ভিখারির মতো দেখতে লাগছে রে! মৈথিলী লক্ষ্য করেছিস? ওই গোলাপি সিনথেটিক শাড়ি সুবচনীকে কে দিল রে?’
গুঞ্জন অপরাধীর মতো বলল—‘ওটা আমার শাড়ি মিস।’
মেধা বললেন—‘কি যাচ্ছেতাই দেখাচ্ছে ওদের! উজান তোরা ওদের ভিখারি বানিয়ে দিলি? আমরা গড়তে চাইলাম একটা স্বাবলম্বী গ্রাম—আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, কুসংস্কার মুক্ত,—তোর বাড়িতে নিরঞ্জন জল খায়নি বলছিস? জামা-কাপড় নিয়েছে তোর?’
উজান হাসছিল। কিছু বলল না।
মেধা বললেন—‘যা করেছিস, করেছিস। এটা বন্ধ কর। শীতকালে ওদের সস্তায় চাদর-টাদর কেনার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। গুঞ্জন তোর উলবোনার মেশিন কদ্দুর?’
গুঞ্জন বিপন্নমুখে বলল—‘দুটো যোগাড় হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমি এসে শেখাতে পারব না মিস। সন্ধেবেলায় লণ্ঠন জ্বলে উঠলেই আমার বাজে লাগে।’
—‘একটা রাত হয়ত থাকতে হবে। তুই একা থাকবি কেন? আর কাউকে সঙ্গে নিবি। দুজনে মিলে থাকবি। ভয় কি! ছেলেও একটা থাক। প্রমিত থাকবে এখন। মেশিনগুলো চালু করে দে। দার্জিলিং থেকে আমি সস্তায় উল আনিয়ে দিচ্ছি। ওরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে বুনতে পারে তো উলের দামটাও উঠে আসছে। দুটো মেশিনে পালা করে গ্রামের দশটা মেয়েও যদি দু ঘন্টা করে বসে…পাঁচ ঘন্টায় বোধহয় একটা করে প্রমাণ সাইজ সোয়েটার হয়, দিনে তিনটে, কম কি? গঞ্জের বাজারে হু হু করে বিক্রি হয়ে যাবে।’
দুপুর বেলা স্কুল-ঘরে খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা রান্না হল। চাটনি কিনে আনা হয়েছিল।
খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলের দিকে অনেকেই জড়ো হয়েছে স্কুলের আটচালায়। অল্প কয়েক ঘর মুসলমান গ্রামটায়। এরা প্রায় সকলেই রাজমিস্ত্রি কিম্বা কাঠপালিশের কাজ করে। শহরে-গঞ্জে যায় ভারি সীজন পড়লে। সপ্তাহ শেষে বাড়ি আসে। আজকের সভায় একমাত্র আনোয়ার শেখ যোগ দিতে পেরেছে। খক খক করে কাশছে আনোয়ার। নীলমণি বলল—‘আনোয়ারকাকা গত কয়েকমাস ধরে এইভাবে কেশে যাচ্ছে।’ দেবপ্রিয় পরীক্ষা করে বলল বুকের ছবি এবং স্পুটাম পরীক্ষা করা দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওকে কলকাতায় যেতে হবে।’
আনোয়ারের দুটি বিবি। একপাল ছেলে মেয়ে। বড় ছেলেটি সবে রাজের যোগাড়ের কাজে নেমেছে। কপালে চড় মেরে আনোয়ার বলল—‘ডাঙার থেকে সবগুনোকে নামাই দিব। নিশ্চিন্দে ঘুমাতে দেয় না। দূরদূর। এগুনোকে খাওয়াতে পারচি না, দেখেন দিদি, ছুটকিটা আবার বাধাইচে।’
মেধা বললেন—‘ছুটকিটা আবার বাধাইচে’ বললে পার পাবেন আনোয়ার! পরিবার-পরিকল্পনার ক্লাস হল শুনেছিলেন?’
—‘তওবা, তওবা, আনোয়ার বলল, ‘কোরাণে নিষেধ আছে দিদি। ও আমাদের ধম্মে বাধে। যা বলেন সব আনোয়ার মানবে। ধম্মে হাত পড়লে মানতে পারবেনে।’ বলতে বলতে আনোয়ারের নিশ্বাস ঘন হয়ে এলো, সে খকখক করে কাশতে লেগে গেল। উজান পেছন থেকে মেধার কনুই ছুঁয়ে ইশারা করল। মেধা চুপ করে গেলেন।
এবারে ওদের ফলন খুব ভালো। আমগাছগুলো ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। থোকা থোকা জাম, লিচু, লেবু। পটল খুব ভালো হয়েছে। উদ্বৃত্ত টাকা থেকে ওরা আরও দুধেল গাই কিনবে। সস্তায় পাওয়া যাবে দায়পুর ডেয়ারি থেকে। মুরগীর চাষ চলছে খুব ভালো। পুরো একটা আটচালা মুরগীর ঘর। পোলট্রি থেকে গৃহপালনের জন্য কিছু কিছু মুরগী ছাড়া হয়েছিল। নিতাই দাস পোলট্রি পরিচালক, জানাল সেগুলো বাঁচছে না। দেশি মুরগী যেভাবে বাঁচে, এসব শৌখীন মুরগী সেভাবে বাঁচে না। বাড়ি বাড়ি মুরগী দেওয়া বন্ধ হোক।
বিকেলের দিকে খানিকটা গান-বাজনা হল। লুকু রজনীকান্তর গান গাইল। সবাই মিলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হল। কেউ কেউ খোল, করতাল, এসরাজ নিয়ে এলো। মৈথিলী বলল—‘পালানরা থাকলে কত ভালো হত বল তো!’ স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিরঞ্জনবাবুর পরিচালনায় তাদের প্রার্থনা সঙ্গীত ‘হও ধরমেতে ধীর’ শুনিয়ে দিল। নিতাই বাঁশি বাজাল। আনোয়ারের একটা পুঁচকে মেয়ে, এই বয়সেই তার মাথায় কাপড়, মিঠে সুরে ভারি সুন্দর গাইল তাদের ছাত পিটোনোর গান।
‘অল্পর বইসে পীরিতি করিয়া ছাড়ি গেলা নিজ দেশ
না লইলা চুড়ি না লইলা শাড়ি না লইলা আপন বেশ।’
সন্ধের মুখে ছাত্র সংঘের ছেলেমেয়েরা বেড়াতে বেরোল। মেধা নিরঞ্জনের সঙ্গে স্কুল ঘরের সিঁড়িতে বসে রইলেন।
মেধা বললেন—‘কী নিরঞ্জন? ছেলেমেয়েরা কি রকম কাজ করছে।’
নিরঞ্জন হাত কচলে বলল—‘কী সুক্ষণেই আপনার কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলুম দিদি। ছেলেমেয়েরা যা করছে তা আমি স্বপ্নেও আশা করিনি।’
—‘তুমি হাত দুটোকে নিয়ে কি করছো, নিরঞ্জন?’
—‘আজ্ঞে!’ নিরঞ্জন থতমত খেয়ে যায়।
—‘হাত দুটোকে অমন করে চটকাচ্ছ কেন?’
—‘আজ্ঞে, অভ্যেস হয়ে গেছে।’
—‘অভ্যেস? কেন?’ মেধা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।
—‘আজ্ঞে আমরা গরিব গুরবো লোক, এই ধরুন প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে হয়, জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হয়। এ গ্রাম তো একেবারে মুখ্যু গরিব গাঁ ছিল কি না, আমাকেই তো বরাবর সব করতে হয়। কারবাড়ি ঝগড়া, কাজিয়া। কে পাশের জমির ধানের জট কেটে নিল…বিনীত, নম্র না হলে চলে না কিনা!’
—‘বিনীত, নম্র, ভদ্র তো নিশ্চয় হবে। কিন্তু তার জন্য হাত দুটো অমন কচলাবার দরকার হয় না। ওরকম ঘাড় নিচু করেই বা থাকবে কেন! তুমি তো গ্র্যাজুয়েট!’
—‘বিদ্যা বিনয়ং দদাতি।’
—‘বিনয় তো নিশ্চয় দেবে। ঘাড় হেঁট করে থাকাটা কিম্বা হাত কচলানোটা কিন্তু বিনয়ের লক্ষণ নয়। নিরঞ্জন তোমার থেকে আমি এর চেয়ে বেশি কাণ্ডজ্ঞান আশা করি। তুমি ঘাড়টা তোল! হ্যাঁ, হাতের ওপর থেকে হাত সরাও! হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে।’
নিরঞ্জন বলল—‘একটা কথা বলার ছিল দিদি।’
—‘বলো।’
—‘গাঁয়ের সবাই বলছিল এবারটা গরু না কিনে আমরা যদি একটা ব্যাটারি সেট টিভি কিনতুম সবাই মিলে একটু আনন্দ করা যেত।’
মেধা সামান্য এলিয়ে বসেছিলেন। সোজা হয়ে গেলেন। বললেন—‘টিভি? গরুর বদলে টিভি? নিরঞ্জন তুমি এদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত, স্কুলের মাস্টারমশাই হয়ে এই কথা বললে? টিভি হলে তোমার ছাত্র-ছাত্রীরা আর কেউ বই পড়তে চাইবে! তুমি জানো না এই ভিশুয়ালের অত্যধিক বাড়বাড়ির ফলে পশ্চিম দেশেও লেখা এবং পড়ার ব্যাপারে লোকে পিছিয়ে যাচ্ছে!
—‘খবরাখবরও তো জানা যায়!’
—‘খবরাখবর জানবার জন্য তোমরা দু-একটা কাগজ রাখছ। কাগজটা বোর্ডে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে এখানে, তা ছাড়াও কয়েক জনের ট্রানজিস্টর রেডিও সেট রয়েছে। সেটাই তো যথেষ্ট। আপাতত। আনন্দ করবার জন্য তোমরা সবাই মিলে গান বাজনা করতে পারো আজ যেমন হল। পুজোর সময়ে যাত্রা তো হয়ই আশেপাশে। মেলাও তো বসে! কিন্তু এতো দরিদ্র গ্রাম। এখনও তোমাদের উদবৃত্ত বলে বিশেষ কিছু নেই। নিজেরাই তো বলো সবজি চালান দেবার ভ্যানগাড়ি দরকার, মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে এত কষ্ট! এর মধ্যে টিভির কথা তোমাদের মনে আসে কি করে?’
নিরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে পড়ল, বলল—‘আজ্ঞে দিদি, আমি একটু ঘুরে আসি।’
—‘এসো। এখানে বসে থাকবার দরকার নেই।’
নিরঞ্জন চলে যাবার পর মেধার মনে হল তিনি কি একটু বেশি খিটখিটে হয়ে যাচ্ছেন? বলার ভঙ্গিতে ধমক, তিক্ততা এসে যাচ্ছে? এই কড়া নির্দেশের সুর তিনি ওদের মধ্যে যে আত্মমর্যাদা জাগাতে চাইছেন, তাকেই যদি আঘাত করে? কিন্তু লোকগুলো কি বেহায়া! কি স্পর্ধা তাদের! এতগুলো অল্পবয়সী ছাত্র-ছাত্রী তাদের সময়, শক্তি ব্যয় করে চ্যারিটি শো করে, চাঁদা তুলে, এভাবে তাদের স্বনির্ভর করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছে। ওষুধপথ্য বইপত্র অন্ন-বস্ত্র কিছুর অভাব রাখছে না। ইতিমধ্যেই গ্রামের চেহারায় একটা স্বাস্থ্যের সর পড়তে আরম্ভ করেছে, পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে, জলা, দিঘি, রাস্তাঘাট। ওদের এই সমস্ত উন্নয়নের উপকরণ একটাও চাইতে ইচ্ছে হল না, না চায় দেশ বিদেশের জ্ঞান, না চায় বইপত্র, না চায় ভ্রমণ করতে। শেষ পর্যন্ত চাহিদা হল কি না একটা টিভি সেট? তা-ও গরুর বদলে?
দেবপ্রিয় প্রমিতকে জঙ্গলের মধ্যে ধরেছিল। সঁড়িপথ দিয়ে যেতে যেতে মরা বিকেলের আলোয় গন্ধটা কোনদিক থেকে আসছে ঠিক করে নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়েছিল। কয়েকটা বাবলা গাছ, ঝোপের মতো। প্রমিত একলা শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। আর কেউ কাছাকাছির মধ্যে নেই। পেছন থেকে এসে দেবপ্রিয় সাবধানে ওর পাশে বসে পড়ল। বলল—‘সাবধান, প্রমিত, এ সব ঝোপে ভীষণ কাঁটা থাকে।’
—‘দেবপ্রিয় তুই?’ প্রমিত চমকে তাকাল।
দেবপ্রিয়ও তার পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করল। আস্তে আস্তে নিপুণ ভঙ্গিতে ধরালো। তারপর খুব হালকা গলায় বলল—‘আমার প্যাকেটটা বদলে দিয়েছিলে কেন প্রমিত?’
—‘আমি? আমি তোর প্যাকেট বদলে দিয়েছি?’
—‘হ্যাঁ আমি দেখতে পেয়ে গেছি। যখন আমার পাশে বসে আজ খাচ্ছিলে, তখনই।’
প্রমিত হা হা করে হেসে বলল—‘এগুলো কত মজাদার বলো?’
—‘সে তো বটেই! আর কাকে কাকে দিয়েছ?’
—‘আর কাউকে নয়। আপাতত তোমাকেই!’
—‘পরে আরও কাউকে কাউকে দেবে তো?’
প্রমিত হঠাৎ একটু চুপ হয়ে গেল, একটু তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল—‘এ কথা বলছিস কেন? তারপরে বলল—‘তোর সঙ্গে জমবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের।’
—‘এভাবে চুপিচুপি না দিয়ে সোজাসুজিও তো দিতে পারতে!’
প্রমিত বলল, ‘ছাড় ছাড়, ঠিক আছে। এবার থেকে সোজাসুজিই দেবো।’
—‘কোথা থেকে এগুলো পাও?’
—‘আছে সোর্স। কেন?’
—‘আমি ভাবছিলুম অরিজিন্যাল সোর্স থেকে আমিও সংগ্রহ করব।’
কটুগন্ধে জঙ্গলের অভ্যন্তর ভরে উঠছিল। দেবপ্রিয় হঠাৎ তার সিগারেটটা মাটিতে ঘষে ঘষে নিবিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল। বলল—‘প্রমিত তুমি আমাকে সুবিধমতো দেখিয়ে দিও তোমার সোর্সটা।’
—‘অফ কোর্স। তুই যদি চাস। তোর কি এতোই দরকার?’
দেবপ্রিয় বলল—‘একবার যখন ধরেছি, দরকার হবেই।’
পেছন থেকে শুকনো পাতার শব্দ হল। লুকু। লুকু বসে পড়ে বলল—‘প্রমিত, দেব, তোরা স্মোক করছিস, আমায় একটা দে, প্লিজ।’
প্রমিত অপ্রস্তুতের মতো হাসল। দেবপ্রিয় বলল—‘লুকু, আমরা এখানে কাজ করতে এসেছি। মডেল গ্রাম হবে এটা একটা। যদি গ্রামের কেউ এসে দেখে আদর্শস্থাপনকারীদের মধ্যে একটি মেয়ে এখানে স্মোক করছে…’
লুকু বলল—‘তোমরা তবে খাচ্ছিলে কেন?’
দেবপ্রিয় বলল—‘অন্যায় করেছি, স্বীকার করছি। চলো, ওদিকে ওরা কি করছে দেখা যাক।’
প্রমিত বলে উঠল—‘হোয়াটস দা হার্ম? লেট হার হ্যাভ আ স্মোক দেব।
দেবপ্রিয় বলল— ‘অল রাইট। আমি কিন্তু চললুম। লুকু তোমার যা ইচ্ছে করতে পারো।’
কয়েক গজ চলে আসার পর দেবপ্রিয় বুঝতে পারল লুকু পেছন পেছন আসছে, দেবপ্রিয় বলল—‘তোমাকে স্মোক করা ছেড়ে দিতে হবে এই কথা বলতে আমি তোমার বাড়ি গিয়েছিলুম লুকু। মনে রাখোনি?’
লুকু অসহায়ের মতো বলল—‘কি করব আমি থাকতে পারি না যে! ভেতরে কি রকম একটা টেনশন বিল্ড করে…আর তোমার ব্র্যান্ডটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।’
দেবপ্রিয় চলতে চলতে থেমে গেল। বলল—‘লুকু, ওই ব্র্যান্ডটার কথা তুমি ভুলে যাও। ওটা তুমি বাজারে পাবে না। তুমি এখনও বুঝতে পারছে না ওটাতে হেরোইন ছিল?
লুকু প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল—‘দেব, তুমি…?’
দেবপ্রিয় ঝট করে লুকুর মুখ চেপে ধরল। বলল—‘আমি খাই না। আমাকে খাওয়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। হয়ত তোমাকেও, অনেককেই। চুপ করে যাও। সাবধানে থাকো।’
দুজনে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। দেবপ্রিয় বলল—‘লুকু তোমরা তো সকলেই এক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী! সবাইকার সম্পর্কেই কি তোমার ধারণা স্পষ্ট?
লুকু বলল—‘তুমি যদি ডি খাওয়ার কথা বলতে চাও তো উজান, মৈথিলী, প্রমিত এরা খায় না, খাবেও না—এটা আমি নিশ্চিত জানি। আমি খেতে পারি, ওরা পারে না।
—‘কেন?’
—‘ওদের কোনও ফ্রাস্ট্রেশন নেই।’
‘নেই কেন? মৈথিলী আশানুরূপ রেজাল্ট করেনি। উজানকে খেলাধুলো ছাড়তে হয়েছে।’
—‘দে জাস্ট ডোন্ট বদার। ওরা এখন নিজেদের পছন্দসই কাজ পেয়ে গেছে। মৈথিলী সামহাউ ম্যানেজেস টু বাব্ল্ উইথ হ্যাপিনেস। অলওয়েজ। আর উজান খেলা ছেড়ে দিলেও স্টিল খেলোয়াড়। ওর বডি দেখেছ? একফোঁটা এক্সট্রা মেদ নেই। খুব ডিসিপ্লিনড লাইফ লীড করে ও। উজানের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত মাপা।’
—‘কেন লুকু অনেক খেলোয়াড়ই তো ভেতরে ভেতরে নেশা করছে, ধরা পড়ছে।’
—‘তারা কোনও প্রতিযোগিতায় কমপিট করার জন্য আর্টিফিসিয়াল এনার্জির জন্য খাচ্ছে অ্যাডিকট হয়ে গেলে কেরিয়ার শেষ। তা ছাড়াও উজান খুব স্ট্রেট ফরোয়ার্ড ছেলে।’
—‘প্রমিত?’
—‘প্রমিতের মাথার ওপর কত বড় দায়িত্ব জানো! ওদের বিরাট ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশনের বিজনেস। তা ছাড়াও আরও কি কি আছে আমি সব জানি না। এম এসসি করেই ও পুরোপুরি চার্জ নেবে। এখন ওর মা সামলাচ্ছেন বেশির ভাগ।’
—‘বাবা!’
—‘ইস, বাবা তো আমরা যখন নাইনে পড়ি মারা গেছেন! প্রমিতের মা রঞ্জুমাসী কিভাবে সেই থেকে সব সামলাচ্ছেন! এখন অবশ্য প্রমিতও যথেষ্ট করে।’
—‘তোমারই বা কি অসুবিধে? তুমি ফ্রাস্ট্রেটেড কেন তা হলে?’
লুকু মুখ নিচু করে ফেলল। তার চোখ ভারি হয়ে আসছে। একটু পরে বলল—‘আই ডোন্ট নো। কিন্তু আমার ভালো লাগে না। কিছু ভালো লাগে না।’ দেবপ্রিয় একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল—‘লুকু আমি ডাক্তারি পড়ছি বটে। কিন্তু শুধু ফিজিওলজি, অ্যানাটমি, ফার্মাকোলজি পড়ে আমি তেমন রস পাই না। আমি ইতিহাস জানতে চাই। বিশেষত আমাদের ইতিহাস। য়ুরোপও বটে। তুমি আমাকে একটু গাইড করতে পারবে?’
লুকু বলল—‘আমাদের তো এনশেন্ট ইন্ডিয়ান হিসট্রি বেশি পড়ানো হয় না। আমরা যেটুকু জানি, সেটুকু তুমিও জানো। ফার্দার স্টাডি করতে হলে তোমাকে আমি একটা বিব্লিওগ্রাফি তৈরি করে দিতে পারি। তোমার অত সময় হবে?’
—‘সেটাই ভাবছিলুম। তুমি যদি একটু জিস্ট করে পড়িয়ে দাও। তোমার কি সময়ের অভাব আছে?’
—‘নাঃ পার্ট ওয়ানে তো সবগুলো হয়ে গেল, পার্ট টু-তে দিলাম মাত্র চারটে অনার্স পেপার। আমি তো তখন থেকেই বসেই আছি। এখনও রেজাল্টও বেরোল না, এম এ-টা আরম্ভ হল না। কিন্তু তোমাকে পড়ানো আমার সাহসে কুলোবে না দেব।’ তা ছাড়া শুধু প্রাচীন ভারত নিয়ে পড়তে গেলে আরও অনেক পড়াশোনার দরকার হবে। অত কি আমি পারবো!’
—‘ঠিক আছে। তোমাদের কোর্সে যা পড়েছ, তাই দিয়েই শুরু করো। আমি প্রতি শনিবার তোমাদের বাড়ি যাবো। ধরো তিনটে থেকে চারটের মধ্যে। অসুবিধে আছে?’
—‘উঃহু। তবে শনিবার ভাইয়ার ছুটি। সে কিন্তু ভীষণ বিরক্ত করবে।’
—‘করুক।’
—‘ঠিক আসবে? প্রমিস।’
—‘প্রমিস! দেবপ্রিয় বাঁশের ডগা সরাতে সরাতে বলল, —‘ইন দা মীন টাইম, তুমি তোমার বাপীর প্যাকেটগুলো সদ্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে।’
লুকু হেসে উঠল। বলল—‘বাপীর থেকে নেওয়া খুব রিসকি। ধরে ফেলবে। আমাকে খুব সাবধানে সংগ্রহ করতে হয়। এটার থেকে একটা, ওটার থেকে একটা…।’
জঙ্গলটা পেরিয়ে ওরা গ্রামের রাস্তার ওপর এসে পড়েছিল। ওদিক থেকে মৈথিলী, গুঞ্জন, উজান, বুল্টু আসছিল, উজান বলল—‘কি রে তোরা এই সন্ধের ঝোঁকে জঙ্গলে কি করছিলি? খুব সন্দেহজনক!’
দেবপ্রিয় বলল—‘আমরা কিছু করিনি। —কে কি করছে দেখতে বেরিয়ে ছিলুম। তবে প্রমিত বোধহয় কিছু করছে।’
মৈথিলী বলল—‘আমরাও এক্সপ্লোর করছিলুম। পুলকেশরা গেছে ফলসার দিকে।
উজান বলল—‘প্রমিত কি করছে দেখে আসতে হয়। দেখবার মতো তো রে দেব?’
দেবপ্রিয় বলল—‘দেখো। দেখে বিচার করো। সবাই মিলে হই-হই করে গেলে হয়ত দেখতেও পাবে না।’
উজান বলল—‘আচ্ছা! ভেরি মিস্টিরিয়াস!’
এই সময়ে দু হাতে বাঁশ ঝাড় সরাতে সরাতে প্রমিত এসে উপস্থিত হল। উজান কিছু বলতে যাচ্ছিল। দেবপ্রিয়র চোখের দিকে তাকিয়ে মৈথিলী হঠাৎ তাকে একটা চিমটি কাটল। জোর গলায় বলল—‘একটি ঘোষণা। ছাত্রসংঘের কেওড়া সফর শেষ হয়েছে। প্রোফেসর ভাটনগর সবাইকে জানাতে বলছেন। রথ ওদিকে প্রস্তুত। এবার আমাদের নগরজননীর জঠরে ফিরে যেতে হবে।’
অধ্যায় : ১২
এবার অরুণা দিল্লি থেকে ফিরলেন বড় অন্যমনস্ক হয়ে। মৈথিলী এখন এতো ব্যস্ত যে সে মায়ের এই ভাবান্তর লক্ষ্যই করল না। রাতে দুজনে খেতে বসে, মৈথিলী খেতে খেতে পড়ে, অনেক সময়ে কয়েক গ্রাস খেয়ে নিয়ে বলে—‘মা উঠব?’
—‘ওঠ।’
—‘তোমার দেরি আছে?’
—‘না, হয়ে এলো।’ মা যে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, ভালো করে খাচ্ছে না বা খেতে পারছে না, মৈথিলীর নজরে পড়ে না।
খাওয়ার পরে সে নিজের ঘরে চলে যায়, হয় পড়তে থাকে, নয় ছাত্রসংঘের কিছু-কিছু হিসেব-পত্র করে। অনেক সময়ে অরুণা ঘরে ঢোকেন।
—‘কি করছিস, মুন্নি?’
—‘পড়ছি মা, তোমার ঘুম পায়নি।’
—কিরকম একটা চাপা অভিমানের সঙ্গে অরুণা বলেন—‘হ্যাঁ, এইবার ঘুমোব, যাই।’
মাঝে মাঝে সামান্য একটু গল্প করে মৈথিলী। বেশির ভাগই তার কাজের গল্প। মা ফিকে হেসে বলে—‘বাঃ, তা হলে তো তোরা সত্যিই ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জন্ম দিচ্ছিস!’
মৈথিলী বলে—‘মা, আমি অত বড় করে ভাবি না। একেবারে সামনে, এক্ষুনি যে কাজটা রয়েছে সেটাকেই করে ফেলতে চাই। আমার যেটুকু সামর্থ্য আছে সেটুকু দিয়ে। কেওড়াখালির একটা ম্যাপ দেখিয়ে মাকে সব কিছু বোঝাতে থাকে সে।
কয়েকদিন পর সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে বসবার ঘরে একজন অস্বাভাবিক কালো গ্রাম্য মানুষকে বসে থাকতে দেখল সে। ধপধপে শার্ট আর প্যান্ট পরে ভদ্রলোককে আরও কালো দেখাচ্ছে। চওড়া চোয়াল। মাথায় ঘন চুল। মার সঙ্গে কথা বলছেন। মৈথিলী ভেতরে চলে যাচ্ছিল। মা ডাকল—‘মুন্নি, এদিকে এসো একবার।’ সে কাছে আসতে বললো—‘ইনি মহাদেব সোরেন, তোমার বড় মামা।’
মৈথিলী তার সমস্ত বিস্ময় চেপে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক খুব সঙ্কুচিত হয়ে তাঁর ধূলিধূসরিত চটি-পরা পা দুখানা সরিয়ে নিলেন। বললেন—‘বাস, বাস, তুমার কন্যা তুমারই মতো স্কলার হচ্ছে তো! আয়ে এস হবেক?’
মা বললে—‘না, ও ডাক্তার হচ্ছে।’
—‘ডাক্তার! উ ডাক্তার! বা! বা! বা! একটা কম্মের মতো কম্ম হইচে। বাঃ ডাক্তার?’
মা বললে—‘ভেতরে যা মুন্নি, বৈজু খাবার দেবে।’
কথাটা বলার দরকার ছিল না। মৈথিলী চলেই যেত। এ ঘরটা তাদের সম্পূর্ণ বাইরের লোকেদের বসবার ঘর। বাবার অফিস-সংক্রান্ত অতিথিরা এখানে বসেন। ভেতরে রয়েছে মস্ত বড় হল। তার একদিকে বসবার আয়োজন, আরেক দিকে খাওয়ার টেবিল, ফ্রিজ, সাইড বোর্ড। ঘনিষ্ঠ জনেরা ভেতরের এই ঘরে বসেন। সে ভেতরে যেতে বৈজুদা খুব গম্ভীর ভাবে টেবিলে জলখাবার রেখে বলল—‘মড়া কেটেছো মুন্নি, জামাকাপড় ছাড়ো আগে!’
—‘কি আশ্চর্য! মড়া কাটিনি! ওসব অনেক দিন হয়ে গেছে। বিশ্বাস করো!’
—‘তোমাদের আর কি! ঘেন্না-পিত্তি নেই।’
মৈথিলী সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসে বসল। তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। হঠাৎ বৈজু বলল—‘এবার বাড়িতে এতো সাঁওতাল আসে কেন মুন্নি! জানো?’
—‘একদম না’, মৈথিলী বলল, বোঝাই যাচ্ছে এই ভদ্রলোকের পরিচয় এখনও বৈজুদা জানে না, সে হেসে বলল—‘এলে তোমার আপত্তি আছে না কি?’
বৈজু মুখটাকে গোমড়া করে রেখেছে। সে বিহারী ব্রাহ্মণ! তার অনেক বাহানা আছে। বহু দিন ধরে সে সাহেব-মেমসাহেবদের সঙ্গে থেকে থেকে একরকম বাঙালিই হয়ে গেছে। কিন্তু তার জাত্যভিমান যায়নি।
মৈথিলীর মনে হল মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে, তার বয়স্ক-শিক্ষার তালিকার সর্বপ্রথমে বৈজুদার নাম থাকা উচিত ছিল। বৈজুদা অবশ্য সাক্ষর। সে নিয়মিত পোস্ট-অফিসে টাকা রাখতে যায়, টাকা তোলে, মনি-অর্ডারের ফর্ম ভর্তি করে, তুলসীদাসও পড়ে, কিন্তু মৈথিলীদের লক্ষ্য সাক্ষরতা নয়, শিক্ষা। প্রথম-প্রথম ওরা ব্যাপারটা অতটা বোঝে নি। কিন্তু একটা মাত্র প্রোগ্রামে গিয়েই ওদের চোখ ফুটে যায়। অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন ওরা কুসংস্কারের ভিতটা ধরে আস্তে আস্তে টান দেয়। চুপচাপ খাওয়া-দাওয়া সেরে সে বাথরুমে ঢুকল। চান করল বেশ অনেকক্ষণ ধরে। ঠিক এই সময়টায় সে সাধারণত বাড়ি ফেরে না। আজকাল ছাত্রসঙেঘর একটা স্থায়ী অফিসের দরকার হচ্ছে। এতদিন কখনো উজানের বাড়ি, কখনো প্রমিতের বাড়ি, এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে তারা দরকারি ফাইলপত্র রাখত। এখন একটা ফাইল ক্যাবিনেট কেনা হয়েছে। মেধাদির বাড়ির নিচের তলাটা ফাঁকা থাকে, একখানা ঘর উনি ছেড়ে দিয়েছেন সেক্রেটারিয়েট টেবিল, পুরনো দিনের সিন্দুক এইসব ব্যবহার করতে দিচ্ছেন। কলেজ ফেরত প্রায়ই ওখানে গিয়ে কাজ করতে হয় দুজন কি তিনজন মিলে কাজ সারে। এক-এক দিন ফিরতে বেশ রাতই হয়ে যায়। গত ক’দিন ধরেই তার ভীষণ খাটুনি যাচ্ছিল, মেধাদি বলে দিয়েছিলেন এ সপ্তাহের বাকি দিন কটা লুকু, গুঞ্জন আর বুল্টু কাজ করবে। মৈথিলীর ছুটি। কলেজ থেকে আজ সোজা বাড়ি এসেছে সে।
এই সাঁওতাল ভদ্রলোকটি তার মামা? জীবনে এ কথা মৈথিলী এই প্রথম শুনল। সে চিরকালই সরকারি বাংলোর আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তার মা-বাবার সম্পর্ক কম। বাবার বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই। তাঁরা তাদের পারিবারিক বন্ধু, কিন্তু বাবার দিকে তার বিশেষ কেউ নেই। ঠাকুমা যতদিন ছিলেন, বাবা যাতায়াত করতেন ভাগলপুরে। কিন্তু ঠাকুমা তার খুব অল্প বয়সে মারা গেছেন। মাকে সে চিরকালই খুব নিবিড়ভাবে পেয়েছে, কিন্তু কখনও বিশেষ মামার বাড়ির কথা বলতে শোনেনি। নীতামাসি বলে একজনই মাসি আছে তার, তাঁর বাবা-মা, মায়ের জ্যাঠামশাই, জেঠিমা। তবে একেবারে নিজের নয় এটাই তার জানা ছিল। এই দাদু-দিদা এখন থাকেন পণ্ডিচেরির আশ্রমে, নীতামাসি থাকেন মাদ্রাজে। দাদু-দিদা তো কখনোই আসেন না। নীতামাসিকেও সে বড় হবার পর মাত্র দুবার দেখেছে।
আজ চান করতে করতে সে ভাবতে লাগল তাহলে তার মার আপন জনেরা ছিলেনই নীতামাসিরা ছাড়াও? তার বড়মামা সাঁওতাল? কিন্তু নীতামাসিরা তো ঘোষ, সোরেন পদবীর সঙ্গে ঘোষ পদবীর তো কোনও সম্পর্ক নেই? সবই কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ টয়লেটের আয়নায় নিজের মুখের ছায়ার দিকে তার নজর পড়ল। মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল মৈথিলী। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই। এই চোখ মুখ নাক সব আদিবাসী ফীচার্স। তার মা চকচকে কালো, মহাদেব সোরেনের মতো কাজল কালো নয়। তামাটে কালো, মায়ের ফিগার অসাধারণ।
মায়ের ঠোট অবিকল তার মতো। তবে মা তার চেয়ে খানিকটা লম্বা, সুন্দরও বটে। মায়ের চেহারার মধ্যে একটা অদ্ভুত অভিনবত্ব আছে, নীতামাসি, রঞ্জুমাসি এদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একটা স্বতন্ত্র চটক। মায়ের চেহারার কথা কোনও সন্তান ঠিক এভাবে কখনও ভাবে না। কথাগুলো শুধু মনের তলায় থাকে। এখন নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাতৃরূপকে এইরকম সচেতনভাবে বিশ্লেষণ করল মৈথিলী। জলের ধারাগুলো তার বাহু বেয়ে কনুইয়ে, গলা বেয়ে বুক ছাপিয়ে নাভিতে নেমে যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে, মৈথিলীর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। সে তাহলে অস্ট্রো-দ্রাবিড়, নাকি আরও সহজভাবে বলতে গেলে নিষাদ! এই ভারতবর্ষের সবচেয়ে আদিম অধিবাসী। যারা ক্রমশ কোণঠাসা হতে হতে অবশেষে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। কিংবা বরাবরই অরণ্যবাসী। অরণ্যের আশ্রয় কোনদিন ছাড়তে চায়নি। অমিশ্র ‘নিষাদ’ জাতির সঙ্গে মিশ্র আর্যরক্তের মিলনে তবে সে তৈরি হয়েছে? একদিক থেকে দেখতে গেলে সে তো অন্যান্য অনেকের চেয়েও বিশুদ্ধ ভারতবাসী।
ভালো করে গা মাথা মুছে, বাথরোবটা গায়ে জড়িয়ে সে যখন হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে সবে তার চুলগুলোকে শুকোতে আরম্ভ করেছে তখন তার মা ঘরে ঢুকল। মা কি রকম অন্যলোকের মতো তার দিকে তাকাল। কেমন ব্যস্তভাবে বলল, ‘মুন্নি, আমাকে শিগগিরই তোমার মামাদের ওখানে যেতে হবে। হয়ত বেশ কিছুদিন আসতে পারব না। তুমি বাবা এলে কথাটা বলবে। চালিয়ে নিতে তো নিশ্চয় পারবে।’
মৈথিলী গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল ‘মা, এমন তুমি তুমি করে কথা বলছ কেন আমার সঙ্গে? কোথায় যাবে? ঠিক কোন জায়গায় আমার মামার বাড়ি? হঠাৎ এতদিন বদে কেন সেখানে যেতে চাইছ? আমায় বলবে না। আমি তোমাকে আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষা প্ল্যান প্রোগ্রামের কথা বলি না?’
অরুণার স্তিমিত চোখ। তিনি ম্লান হাসি হাসলেন, বললেন—‘আমার অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। আমি খুব ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। তোমাদের কথা ভেবে করেছি। যাইহোক এখন তুমি বড় হয়ে গেছো, তোমার বাবার তো কাউকেই আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আর আমার অতটা দায়িত্ব নেই। তোমাদের প্রতি কর্তব্যের ছুতো করে এখন আর আমি আমার নিজের লোকেদের দায়িত্ব এড়াতে পারি না।’
মৈথিলী অনুভব করল মা হঠাৎ যেন অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছে। মায়ের শরীরে মনে একটা অসম্ভব কঠিনতা, যার মুখোমুখি তাকে কখনও হতে হয়নি। টেলিফোনেও মাকে কখনও এত সহস্র যোজন দূর মনে হয়নি। তার আগে কখনও ভয় করেনি, কিন্তু এখন তার সারা শরীর ভয়ে শির শির করতে লাগল। সে প্রায় বোবা স্বরে বলল—‘মা, তুমি এমন মিস্টিরিয়াসলি কথা বলছ কেন?
আমায় পরিষ্কার করে সব খুলে বল। বিশ্বাস করো, আমি ঠিক বুঝব।’
অরুণা মৈথিলীর চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, ‘মুন্নি আমি কি কখনও তোকে অযত্ন করেছি? তোর বাবার প্রতি কর্তব্যপালনে কখনও গাফিলতি দেখেছিস?’
‘না তো মা। এসব প্রশ্ন উঠছে কেন?’
দূরের দিকে চেয়ে আছেন অরুণা। যেন মুন্নির কোনও প্রশ্নই তিনি ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছেন না। বললেন—‘অথচ এই আমিই আরও অনেক গুরুদায়িত্ব ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে এসেছি। সে কি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য টাকা পয়সার লোভে?’
শেষের প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করলেন অরুণা!
‘মা, তুমি যে কি বলছ, কেন বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।’ মৈথিলী ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।
—‘তোর মামা। তোর মামার বাড়ির দিকের সবাই খালি এই একই কথা বলে।’
‘কেন, কী দায়িত্ব, আমায় বুঝিয়ে বলল।’
অরুণা বললেন—‘খাতা কলমে আমার নাম রাধিকা সোরেন, মুন্নি, যদি চাকরিটা করতুম এখনও এই নামটাই চালু থাকত। গৃহবধূ হয়ে গেছি বলে তোর আর জানার দরকার পড়ল না। আমি লোধাসুলির সাঁওতাল পল্লীর মেয়ে। আমার বাবা মা যতদিন বেঁচে ছিলেন আমাকে রাধি বলে ডাকতেন। ক্রিশ্চান মিশনারিরা আমাদের পড়াতো। তা ছাড়াও দিত দুধ, মুরগীর ডিম। পল্লীর সব ছেলেমেয়েকে ডেকে ডেকে দিত, তার সঙ্গে খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার করত। আমাদের মধ্যে অনেকেই এভাবে ক্রিশ্চান হয়ে গেছে। আমার সম্পর্কে ওদের আশা ছিল আমি ওদের সিস্টার্স অফ চ্যারিটিতে যোগ দেবো। সেভাবেই আমাকে গড়ছিল ওরা। কিন্তু আমার পরিবারের লোকেরা ধর্মান্তরিত হতে চাইত না। ওদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। আমি য়ুনিভার্সিটিতে পড়ব, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমার নিজের লোকেদের জন্য কাজ করব এই চাইত আমার মা বাবা এমনকি পল্লীর অনেক মাতব্বর লোকেরাও। মিশনারিরা যেদিন জানল আমাকে কিছুতেই ক্রিশ্চান সন্ন্যাসিনী বানাতে পারবে না, ওরা আমার পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করা ছেড়ে দিল। আমার তখন আরও শেখবার অদম্য ইচ্ছে। মিশনারি বোডিং ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেলাম। আমার বাবা আন্নু সোরেন পল্লীর প্রধানদের সঙ্গে কথা বললেন, সবাই একবাক্যে বলল স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় জলপানি পাওয়া মেয়ে একদিন বড় আরও বড় হয়ে পুরো পল্লীর মানুষকে বাঁচাবে। কেউ কেউ অন্য কথা বলেছিল, কিন্তু যারা দেশের হালচাল বোঝে, আমার বাবা বা দাদার মতো খবরের কাগজ পড়তে শিখেছে তারা সবাই বলল—‘আমাদের শিডিউলড ট্রাইবস বলে অনেক বিশেষ সুযোগ সুবিধে দিচ্ছে সরকার, সে সব আমরা সব বুঝিও না। অন্য লোকে ট্রাইব্যাল সেজে সে সব নিয়ে নিচ্ছে। আমরা পড়ে আছি অন্ধকারে।’ আমাকে ওরা লেখাপড়া শেখাতে চাইল। ঝাড়গ্রাম কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হলাম। সে সময়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন একটি বাঙালি পরিবার। নীতার বাবা সৌরীন ঘোষ আর মা রাণী ঘোষ।’
মৈথিলী বলল—‘দাদু দিদা তোমার কেউ নন? আশ্চর্য। আমি তো কখনও বুঝি নি।’
—‘আশ্চর্যই। উনি তখন ছিলেন মেদিনীপুরের ডি এম। বাবা ওঁর বাংলোয় আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন যদি ওঁর বাড়িতে কাজকর্ম করে আমি পড়াশোনা করতে পারি। তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমাকে দেখে ওঁদের কি রকম খটকা লাগে। ওঁরা জেরা করে করে বাবার কাছ থেকে আমার কাছ থেকে সব শোনেন। তারপর বলেন—‘পরীক্ষায় জলপানি পাওয়া মেয়েকে দিয়ে আমরা তো দাসীবৃত্তি করাতে পারব না। আপনার যদি এতোই দরকার হয়, ওকে এখানে রেখে যান, আমার মেয়েও যেমন সংসারের কাজ দরকার পড়লেই করে ও ও তেমনি করবে। এখানে ও নিঃসঙ্কোচে থাকুক।’
মৈথিলী উত্তরোত্তর আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। বলল—‘মা, তুমি যে এ রূপকথা শোনাচ্ছো।’
অরুণা আস্তে আস্তে বললেন—‘তোর কি লজ্জা হচ্ছে মুন্নি।’
—‘লজ্জা? কেন?’
‘এই তোর মা জঙ্গলের অসভ্য আদিবাসীদের মেয়ে শিক্ষিত সভ্যসমাজ থেকে যারা বহুদূরে বাস করে। তোর মা লোকের চ্যারিটিতে বড় হয়েছে, দাসীবৃত্তি করতে গিয়েছিল। ধর, দাসীই।’
‘মা!!!’ মৈথিলী মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কোলে মাথা গুঁজল। অনেকক্ষণ পর রুদ্ধ কণ্ঠে বলল—‘মা, তোমার এ কথার উত্তর নিশ্চয়ই আমায় দিতে হবে না।’
অরুণা বললেন, ‘রাণী জেঠিমা, সৌরীন জেঠু অবশ্য আমাকে দাসী হতে দ্যাননি। মস্ত ঘরে নীতার পাশের খাটে আমি শুতাম। লোকজনে মশারিটা পর্যন্ত গুঁজে দিয়ে যেত। নীতার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হল। ওদের ভালোবাসতে শুরু করলাম। সরকারি আমলাদের বাংলোর কাজকর্ম, বাঙালি রান্না, রুচি, কথা, ভাষা, সাহিত্য সবই আমার নিজের হয়ে গেল। আমাদের লোধাসুলির মানুষজনের আশা আমি সরকারি পরীক্ষা দিয়ে ভেতরে ঢুকব, তাদের প্রতিনিধি হবো, তাদের শিক্ষা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের বিশেষ সুযোগসুবিধা এই সবের জন্যে কাজ করব। ডাবলু বি সি এস পরীক্ষা দিলাম। প্রথম পোস্টিং হল বরশুল, বি ডি ও অফিসে। বর্ধমানের ডি এম তখন তোমার বাবা। তাঁকে বিয়ে করলাম। তুমি এলে তোমার বাবা বদলি হয়ে গেলেন দার্জিলিংএ। এই বিয়ে উপলক্ষ্যেই আমার নিজের লোকেদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ। ওরা সবাই আমাকে ত্যাগ করল। কমিউনিটির বাইরে বাঙালি ব্রাহ্মণকে বিয়ে করেছি। ওরা আমার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।
কেউ কোথাও নেই, নিজের লোকেরা ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছে, তোমার বাবা দার্জিলিঙে। আমি ঝট করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিলাম। নিজের ট্রাইবের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যেই আমার পড়াশোনা, এই আশাতেই ওঁরা আমাকে তৈরি করেছিলেন, আমি কিছু করি নি। ওরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিল। ঠিকই করেছিল। আজ আবার ওরা আমায় ডাকছে।’
—‘কেন? মা তুমি তো বলোনি ওঁদের জন্যে কিছু করবে না। ওঁরা তো তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন। তুমি নিজেই বলছো ওঁরা হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন। সে সময়ে তো তোমার চাকরি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। পুরো জিনিসটাই বানচাল হয়ে গেল। আমার তো মনে হচ্ছে এটা ওঁদেরই ভুল। তোমার দোষ কোথায়? আর আজ হঠাৎ তুমি এমন কি করলে যাতে ওঁদের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলে?’
অরুণা বললেন, আমি সাহস করে দাদাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। তাতেই ওঁরা আবার আমায় কাজ করার সুযোগ দিতে চান।’
—‘বেশ তো, করো না কাজ। আমরা যে গ্রাম উন্নয়নের কাজ করছি, তেমনিভাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুমি তোমার বাপের বাড়ির গ্রামের উন্নতি করো না মা।’
অরুণা হাসলেন—‘জিনিসটা অত সোজা নয়। পূর্ব ভারতের আদিবাসীরা এখন একত্র হয়েছে। মৈথিলী, আমার যে পিতৃভূমি সেই ছোটনাগপুরের মালভূমি এবং তার আশপাশের এলাকা পৃথিবীর সবচেয়ে খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোর একটা তো জানিস। ওখানকার মতো মাইকা পৃথিবীতে আর কোথাও মেলে না। এই সব খনিজ কয়লা, অভ্র, তামা বক্সাইট লোহা, সমস্ত আমার দেশের মাটির তলায় ছিল। আছে। আর ওপরে আছে লাল মাটির ওপর অফুরন্ত শাল পলাশ মহুয়ার জঙ্গল, সেই জঙ্গলও আমাদের রুজি, আমাদের জীবন। জঙ্গলগুলোকে এরা একটার পর একটা কেটেছে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, যাযাবরের মতো আমরা ঘুরেছি। এক একটা খনি খুঁড়েছে, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে উৎখাত হয়েছি আমরাই। আর হয়েছি কুলি। আমাদের ভোগে কখনও কিচ্ছু আসেনি। আমরা এই সব অধিকার ফিরে পেতে চাই। ওরা আমাকে ওদের মধ্যে চায়। এই আন্দোলনকে শক্তি দেবার জন্য।’
—‘ঝাড়খণ্ড মুক্তি আন্দোলন! মা? রাজনীতি?’
—‘মুন্নি শাসনযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে নিজের লোকেদের স্বার্থে কাজ করার সুযোগ আমার এসেছিল। সে সুযোগ আমি স্বেচ্ছায় হারিয়েছি। আজকের এই ডাক উপেক্ষা করবার সাধ্য আমার নেই।’
—‘কিন্তু জি. এন. এল. এফ, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এসব সাংঘাতিক সেশেসসনিষ্ট রাজনৈতিক ব্যাপার। তুমি, তোমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তারপর এতদিন একেবারে অন্যরকম জীবন কাটিয়ে গেছো। মা ওরা যদি তোমাকে নিজেদের লোক বলে বিশ্বাস করতে না পারে।’
—‘এ সমস্ত রিসক্ আছেই। আমাকে তবু আমার কথা রাখতে হবে মুন্নি। না হলে হয়ত ওরাও আর সইবে না। চরম কিছু করে ফেলবে।’
মৈথিলী চমকে উঠল। তারপর মাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। বলল—‘মা, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।’
—‘যাবি? অরুণা মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, চোখ টলটল করছে। বললেন —‘তোকে তো আমি গড়ে দিয়েছি মুন্নি। আমি নয়, আসলে আমার ভাগ্যই তোকে গড়ে দিয়েছে। যা হতে যাচ্ছিস সেটা সম্পূর্ণ কর। না হলে আবার অসম্পূর্ণ অতীত তোকে এমনি করে পেছু টানে টেনে নেবে। মুন্নি তোর বাবাকে কথাগুলো বলবার দায়িত্ব তোর।
তাকে দেখাশোনা বিশেষ করতে হয় না, তবু যেটুকু করতে হয়, সেটুকুও এখন থেকে তোকে করতে হবে। উনি আসবার আগেই আমি চলে যাবো ঠিক করেছি।’
—‘মা, তুমি ভেবেচিন্তে কাজ করো। ডোন্ট বি সো র্যাশ।’
—‘খুব ভেবেচিন্তেই করছি। তোকে একদিন বলেছিলাম নিজের কাজ আরম্ভ করলে আর তোরা আমায় পাবি না মনে আছে।’
মৈথিলী বলল—‘আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে তোমার অসুবিধে কোথায়?’
—‘আছে আছে। তবে আমি সময় সুযোগমতো আসব। লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে তো আমার কাজ হয়েই যাবে। তখন আর আমার ফিরে আসতে কোনও বাধা থাকবে না।’
ক্রমশ রাত হয়ে আসছে। চ্যাপেল রোডের এই বাংলো নির্জন। বৈজু একবার রাতের খাবার খেতে ডেকে গেছে। মা মেয়ের কারোই যেন গা নেই। বৈজু আবার ঘরের বাইরে টোকা দিল।
অরুণা বললেন—‘খেতে যা মুন্নি।’
—‘তুমি যাবে না।?’
—‘আমার ইচ্ছে করছে না।’
—‘আমি তো এসে অনেক খেলাম। বৈজুদা।’ একটু গলা তুলে বলল মুন্নি।
—‘তুমি খেয়ে নাও।’
‘তোমরা কেউ খাবে না, আমি আগে।’
অরুণা বললেন—‘আমার খিদে নেই। মুন্নিরও পেটভরা। তুমি খাবে না কেন বৈজু?’
দরজার বাইরে টোকা থেমে গেল। বৈজু চলে গেছে। মুন্নি মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রয়েছে। যেতে দেয়নি পাশের ঘরে। চিড়িয়াখানা থেকে সিংহের ডাক ভেসে আসছে নির্জন রাতে। মৈথিলী বলল—‘মা আমি অনেক ভাবলাম। তোমাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি অন্তত একুশ বছর তোমার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ওদের বেশির ভাগ তোমাকে চেনে না। তুমি ব্যুরোক্র্যাটের স্ত্রী। সরকারি লোক। ওদের শত্রুপক্ষ। মা তোমার বয়স বেড়ে গেছে, তুমি কি করে নতুন জায়গায় মানিয়ে নেবে, কোথাও হয়ত তোমার কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে যাবে। তখন ওরা যদি তোমায় কিছু করে?’
অরুণা বললেন—‘আমরা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি না। দাদা যখন আমাকে এভাবে ডাকতে এসেছেন, বুঝেই তো এসেছেন! এখন আর বাবা-মা বেঁচে নেই। দাদা শুধু পল্লীর প্রধানই নন, একজন নেতাও বটে। দাদার ইচ্ছে আমি যাই, ওদের সব অভিমান মিটিয়ে দিই। মনে কর না আমি এতদিন পর বাপের বাড়ি যাচ্ছি।’
মৈথিলী বলল—‘ঠিক আছে, আমিও এতদিন পর মামার বাড়ি যাচ্ছি। আচ্ছা মা কোথায় তুমি যাবে এখন? ওই লোধাসুলি বলে জায়গাটাতে?’
অরুণা বললেন—‘ঠিক বলতে পারছি না।’
—‘এখান থেকেই যদি কাজ করো, অসুবিধে কি?’
—‘এখান থেকে? সরকারি আমলার বাড়ি থেকে? তাও কি হয়?’
—‘বাবাকে তুমি জানাচ্ছো না কেন?’
—‘তোমার বাবা আমাকে যেতে দেবেন না। আমাদের বিয়ের সময় ওরা তো মত দেয়ই নি, ওঁকে প্রচণ্ড শাসিয়ে ছিল। সে-সব তো তোমার বাবা ভুলে যেতে পারে না!’
অরুণা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। মৈথিলী আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। সে সাধারণত বিছানায় পড়ে আর স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোয়। আজ তার ঘুমের সঙ্গে চিড়িয়াখানার বন্দী বাঘ-সিংহ-শেয়ালের ডাক মিশে যেতে লাগল। নির্ভীক মৈথিলী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বুক-চাপা ভয়ের স্বপ্ন দেখতে লাগল। মাথার ওপর পদস্থ বাবা, স্নেহশীলা মা। সচ্ছল, শান্ত জীবনের নিরাপত্তা এক জিনিস। আর হঠাৎ মাথার ওপর থেকে সেই নিরাপত্তার আবরণ সরে যাওয়া, ভ্রূকুটিময় আকাশ অনাবৃত হয়ে যাওয়া আর এক জিনিস! তার স্বপ্নের মধ্যে কেওড়াখালি, পদ্মকাকী, দেবপ্রিয়, ডাঃ সোম, লুকু এবং মহাদেব সোরেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। তার সঙ্গে মেটিরিয়া মেডিকার গুরুত্বপূর্ণ পাতাগুলো। ঘুমের মধ্যে কোথায় যেন ট্রাকের ভটভট আওয়াজ, হুহু করে গাড়ি ছুটে গেল, মৈথিলী পাশ ফিরে ঘুমোতে লাগল।
ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। এত দেরি করে সে সাধারণত ওঠে না। কদিন খুব খাটুনি যাচ্ছে বলেই বুঝি এত ঘুম! চোখ মেলে দেখল মা উঠে গেছে, দরজা খোলা। বাইরে বেরিয়ে দেখল, ডাইনিং টেবিলের একদিকে মোড়ার ওপর বৈজুদা গালে হাত দিয়ে বসে আছে। মৈথিলীকে বেরোতে দেখে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল—‘মুন্নি, ভোর রাত্তিরে সেই সাঁওতাল মোড়লটা এসেছিল, মা একটা পাতলা সুটকেস নিয়ে তার সঙ্গে কোথায় গেল, তোমাকে জাগাতে বারণ করল। একটা চিঠি রেখে গেছে তোমাকে দেবার জন্য। দেখো, দেখে বলো সায়েবকে আগে ট্রাঙ্ককল করবে না আগে পুলিসে ফোন করবে।’
মৈথিলীর হাত একটু একটু কাঁপছে, সে চিঠিটা নিল। মা লিখেছে : ‘মুন্নি, তোর পক্ষে এখনই মামার বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। যখন যাবার মতো অবস্থা হবে, আমি নিজে এসে তোকে নিয়ে যাবো। ভাবিসনি। আমি ভালো থাকবো। মনে রাখিস, তোর মায়ের বংশ কখনও বিশ্বাসের অমর্যাদা করে না। আমিও যতক্ষণ না তাদের বিশ্বাসের ঋণ চুকিয়ে দিতে পারছি ততক্ষণ নিজেকে মানুষ বলে মনে করতে পারছি না। ভালো থাকিস, বাবাকে বোঝাস।’
মৈথিলীর ঠোঁট ভীষণ কাঁপছে, বৈজু তার তিন চার বছর বয়সের পর আর কখনও এভাবে ঠোঁট কাঁপতে দেখেনি। মুন্নি টেলিফোনটার ওপর একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল—‘হ্যালো, কাকু! আমি মুন্নি বলছি, লুকুকে একটু দিন না।’
বৈজু ভেবেছিল মুন্নি বাবাকে ফোন করছে।
—‘লুকু? তুই আজ এক্ষুণি আমাদের বাড়ি চলে আসতে পারবি? …লুকু প্লীজ আয়…আমার মা চলে গেছে…।’
ফোনের অপর প্রান্তে লুকু বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করছে—‘কি বলছিস? মৈথিল? মাসি কোথায়? কাকুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?’
মৈথিলী কিচ্ছু বলতে পারছে না। রিসিভারটা হাতে নিয়ে থরথর করে কাঁপছে, কাঁদছে, জীবনে এই প্রথম।
লুকুর বাবা বললেন—‘কি হয়েছে লুকু?’
লুকু কাঁদতে কাঁদতে বলল—‘মাসি বোধহয় মরে গেছে বাপী, আমার মায়ের মতো মাসিও মরে গেল। এখন মুন্নি আর আমি এক।’
কিছুক্ষণের মধ্যেই মৈথিলীদের চ্যাপেল রোডের বাংলো তার বন্ধুবান্ধবে ভরে গেল। যাকে যাকে যোগাযোগ করতে পেরেছে খবর দিয়েছে লুকু। উজান, প্রমিত, গুঞ্জন, লুকুর বাবা, ভাইয়া, মেধাদি সব্বাই।
অধ্যায় : ১৩
কেউ হারায় কেউ পায়। একজন বঞ্চিত না হলে আরেকজন লাভবান হয় না, এই কি জগতের নিয়ম? যে কোনও লাভেরই উল্টোপিঠে চাঁদের অন্ধকার পিঠের মতো একটা ক্ষতির দিক থেকেই যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতির সম্পদের ভাঁড়ার শূন্য করে। জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাচ্ছে, সৌহার্দ্য কমে যাচ্ছে। জীবনের সঙ্গে দর্শন, তত্ত্বের সঙ্গে অভিজ্ঞতা এমনভাবে তাল পাকিয়ে যেতে থাকে যে মনে হয় বিশুদ্ধ চিন্তার পেছনে এতো সময় দেওয়া, তত্ত্বের জন্য, দর্শনের জন্য সারা জীবন উৎসর্গ করার কোনও মানে হয় না। জীবন, জীবনের ঘটনা নিয়ে সমস্ত তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অনেক সময়ে এড়িয়ে অবস্থান করে। মেধার শূন্য ঘর ক্রমশ ভরে উঠছে। নিচেটা প্রায় বন্ধই থাকতো। ওপরের দালানের একদিকে সামান্য একটু রান্নার আয়োজন তাঁর। ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের সঙ্গে তিনি নিচেই দেখা করেন। কিন্তু বাকিরা সবাই ওপরেই আসে। সকালবেলা যতক্ষণ না য়ুনিভার্সিটি যাবার বেলা হচ্ছে তিনি একা। খুব ভোরবেলা উঠে গাছগুলোর পরিচর্যা করে চান করে নেন। তারপর চা, তারপর পড়াশোনা, বেরোবার এক ঘন্টা আগে ভাতে ভাত চাপিয়ে দেন, জামাকাপড় বদলাতে বদলাতে সেটা হয়ে যায়। খেয়ে পাঁচ মিনিট বজ্ৰাসন, তারপরই স্কুটারে চেপে কর্মস্থল। পনের মিনিটের মধ্যে য়ুনিভার্সিটিতে। নিজের ঘরে বসে বসে ডিপার্টমেন্টাল কাজ কিছু করতে হয়, ঘড়ি দেখে ক্লাসগুলোয় হাজিরা দেন। আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট পোস্টগ্র্যাজুয়েট দুরকম ক্লাসই আছে। এম ফিলের ক্লাসও থাকে কোন কোনদিন। কলেজের সময়টুকু তিনি পড়াশোনা করেই কাটান, সহকর্মীদের মধ্যে হাতে গোনা যায় এমন কয়েকটি মানুষ মেধার ঘরে আসেন। প্রথমেই তো তাঁর প্রোফেসরশিপ পাওয়া নিয়ে বেশ আপত্তি ওঠে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জনা দুই ক্যানডিডেট ছিলেন। কিন্তু মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, গুটিকয় প্রকাশিত পেপার, পড়ানো ও গবেষণার অভিজ্ঞতা এ সমস্ত অগ্রাহ্য করবার সাধ্য বোর্ডের ছিল না। অনেকেই অত্যুজ্জ্বল ভাটনগর পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সেই শুরুর থেকেই নিজের বিভাগের সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর আলগা-আলগা সম্পর্ক। এঁরা হয়ত আশা করেছিলেন এঁদের তিক্ত ব্যবহার, এবং অসহযোগিতা তাঁকে খেপিয়ে তুলবে, কোণ ঠাসা হয়ে তিনি নানারকম বাজে ব্যবহার করবেন, ফলে এঁরা তাঁকে অপমান করবার সুযোগ পেয়ে যাবে। কিন্তু এ সুযোগ তিনি তাদের একেবারেই দ্যাননি। তিনি একেবারে উদাসীন। ভাগ্যে এঁরা প্রোফেসরদের একটা করে ঘর দ্যান। নিজেকে তিনি সেই ঘরে বন্দী রাখেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক খুব ভালো। এম ফিলের ছেলেমেয়েরা যাদের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য কলেজের লেকচারার, তাঁর কাছে ঘন ঘন আসে। মেধা যদিও বিদ্যার জন্য বিদ্যার তত্ত্বতে আস্থা হারিয়েছেন, বিদ্যার সুপ্রয়োগ বলতেও যে ঠিক কি বোঝায় কতখানি বোঝায় তা-ও তাঁর মস্তিষ্কে এবং জীবনে এখনও গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে, তবু ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি মেটানোর মতো পড়াশোনা তিনি এখনও করে থাকেন। সংস্কৃতিবিভাগের এক সহকর্মী তাঁর খুব গুণমুগ্ধ। তিনি মেধার নাম দিয়েছেন ‘তেজোময়ী বাক’। তাঁর বক্তৃতায় নাকি, তেজ, যাকে বলে ওজস্ তা সবসময়ে থাকে। তুলনামূলক সাহিত্য-বিভাগের আরেকজন সহকর্মিণী তাঁকে বলেন ক্লাইটেমনেস্ট্রা। তিনি নাকি কোনও সন্তানতুল্য মতবাদের অপমৃত্যুতে ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। বাইরে যতই শান্ত দেখাক, ভেতরে কোথাও ধূমল, আগ্নেয় তিনি। য়ুনিভার্সিটিতে আরেকজন কাছের মানুষ ডাঃ সোম। ডাঃ সোমের সম্পর্কে মেধা যতটা জানেন, মেধার সম্পর্কে ডাঃ সোম জানেন অনেক বেশি। তিনি অবশ্য এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির। ছাত্রসংঘের সৌজন্যে আলাপ। ডাঃ সোম খুব মজার মানুষ। মেধার সম্পর্কে নানান রটনা, নামকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব হল—‘বলছে বলুক, ওদের বলতে দাও।’
ফার্ন প্লেসের বাড়ি ভরে উঠছে। একেই তো একতলার দুটো ঘর এখন ছাত্রসংঘের কাজে ব্যবহার হচ্ছে। বিকেলের দিকে ছেলেমেয়েরা অনেকেই আসে। তার ওপর মৈথিলী এখন মেধার কাছেই থাকছে। মৈথিলীর মা ওরকম হঠাৎ চলে যাবার পর মেধা তাকে নিজের কাছেই এনে রাখেন। রঘুনন্দনকে ট্রাঙ্ক কল করা হয়। কিন্তু তিনি তখন দিল্লিতে নেই। যাই হোক, দিন তিনেক পরে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। মৈথিলী তখন কলেজে। মেধার তিনটের সময়ে ক্লাস। তিনি সবে খাওয়া শেষ করে মুখ ধুচ্ছেন। গাড়ির শব্দ পেলেন। ওপরের জানলা দিয়েই দেখতে পেলেন রঘুনন্দনের গাড়ি। বেল বাজবার আগে তিনি পৌঁছে গেছেন।
—‘মুন্নি কোথায়?’ —রঘুনন্দন ঢুকতে ঢুকতে বললেন।
—‘কলেজ গেছে।’
—‘কবে থেকে কলেজ পাঠাচ্ছো!’
—‘গতকাল থেকেই।’
—‘ও যদি কলেজ থেকে পালায়?’
—‘সে কি? কোথায় পালাবে?—মেধা অবাক।
—‘ধরো, ওর মার খোঁজে।’
—‘গেলে আমায় বলে যাবে, পালাবে কেন? যেতে তো আমি বাধা দিচ্ছি না!’
—‘বাধা দিচ্ছো না? তাতো দেবেই না। নিজের তো সন্তান নেই। খুব সহজে এ কথাগুলো বলা যায়।’
—‘ওর মা যখন নিষেধ করে গেছেন তখন তার কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল না পেলে যাবে না। তাছাড়া মুন্নি বরাবর খুব র্যাশন্যাল, ধীর-স্থির।’
—‘বৈজুর কাছে যতদূর শুনেছি শী ইজ ডিসট্রাক্টেড। শী ওয়াজ হার মাদার্স চাইল্ড। ভেরি ভেরি মাচ।’
—‘একটু তো ডিস্ট্র্যাক্টেড় হবেই। কিন্তু এখনও অনেক শান্ত হয়ে গেছে। বুঝেছে। ওর মাকে বুঝতে পেরেছে। আর না বোঝা জিনিস বুঝতে পারলেই শান্তি।
—‘কি বুঝেছে? ওর মাকে বোঝবার কি আছে? শী ইজ অ্যাবসল্যুটলি ম্যাড।’
—‘কি করে তুমি এই সিদ্ধান্তে এলে?’
—‘এ সিদ্ধান্তে আসি নি। দেয়ার ইজ নাইনটি পার্সেন্ট চান্স দ্যাট শী হ্যাজ বিন কিডন্যাপড্।’
—‘একি বলছো? উনি চিঠিপত্র লিখেছেন। যথেষ্ট দিন আলাপ আলোচনা করেছেন, নিজের মনকে বুঝিয়েছেন, মৈথিলীকে বুঝিয়েছেন, তবে গেছেন।
—‘শী হ্যাজ বিন ফোর্সড্, পারহ্যাপস্ ব্ল্যাকমেইলড। তুমি ব্যাকগ্রাউন্ড জানো না মেধা তাই এতো কথা বলছো। মৈথিলী কেম ফার্স্ট, দা ওয়েডিং আফটারওয়ার্ডস। ওরা বুনো কুকুরের পালের মতো ক্ষেপে গিয়েছিল, আমার জন্য বিষাক্ত তীর শানিয়ে দিনের পর দিন পেছন পেছন ঘুরেছে।’
মেধা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—‘রঘুদা, এটা আমি তোমার থেকে আশা করি নি। এ তুমি কি বললে?’
—‘কেন? এক যুগ আমেরিকায় থাকবার পরও তোমার এই সামান্য কথা শুনলে এমন রি-অ্যাকশন হয় কেন?’
—‘আমেরিকায় থাকা, আমেরিকায় থাকা শুনতে শুনতে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি রঘুদা। তোমরা এটা বন্ধ করো। দশ বছর কেন সারাজীবন আমেরিকায় বা অন্য কোথাও থাকলেও আমার মূল্যবোধ বদলাবে না।
—‘সেক্ষেত্রে বলব তুমি কনজারভেটিভ, রিজিড, এনিওয়ে, তুমি এ ব্যাপারে আমাকেই শুধু দায়ী করছ কেন? রাধিকা সোরেন নামে নব্য ডাবলু বি সি এস অফিসারটি তখন পরিণত ছাব্বিশ বছরের যুবতী। অমি তো তার ওপর বলাৎকার করি নি। সে স্বেচ্ছায় এসেছিল। তার আদিবাসী ইনস্টিংট তাকে টেনে এনেছিল। তুমি জানো না মেধা সেক্সের ব্যাপারে আদিবাসী মেয়েরা তোমাদের চেয়ে অনেক অ্যাগ্রেসিভ, অনেক খোলামেলা। ওদের সিসটেমটাই তো অনেক ন্যাচারাল। আজ তথাকথিত সভ্যসমাজ বিশেষত হিন্দু ও ক্রিশ্চান সমাজের সঙ্গে মিশে ওরা এই প্রথাগুলোকে লজ্জা পেতে শুরু করেছে। কিন্তু এ জিনিস ওদের রক্তে আছে।’
—‘তা-ই যদি হয়, সে যদি স্বেচ্ছায় এসে থাকে, তাহলে এতো কথা কেন? তুমি তো তাকে ভালোবেসেছিলে! তুমি তো তাকে, তার সন্তানকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিলে?’
—‘ন্যাচারলি। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ওরা অরুণাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছিল। আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে সেটা আর হবে না এটাই ওদের ধারণা হয়। খুব সম্ভব ওদের মধ্যে অরুণার কিছু অ্যাডমায়ারারও থেকে থাকবে। ওরা প্রাণপণে বিয়েটাতে বাধা দেয়। বলতে থাকে আমি ওদের রাধিকে নষ্ট করেছি। ওরা আমার রক্ত চায়। ওর বাবা দাদা যত নয়, আরও কিছু সাঁওতাল যুবক একেবারে লাঠি সোঁটা নিয়ে তৈরি ছিল। তাদের মধ্যেই কেউ হয়ত ওর প্রণয়ী ছিল।
‘থাকতেই পারে। অবস্থা তো দেখছি খুবই জটিল’, মেধা চিন্তিত স্বরে বললেন।
—‘এখন মৈথিলী যদি ওদের মধ্যে যায়, তাকে ওরা আমার প্রতিনিধি বলে দেখবে। আমার ওপর ওদের এতদিনের রাগ মেয়েটার ওপর ঢালবে। তুমি কি তাই চাও?’
—‘না। কিন্তু এসব কথা মৈথিলীকে বলা দরকার।’
—‘বলবেটা কি? ওর মা বাবার বিবাহপূর্ব সম্পর্কের কথা? ওর জন্মের কথা? তুমি পাগল হয়েছো মেধা? তোমাকে বলাই আমার ভুল হয়েছে। আমি একটার পর একটা ভুল করে যাচ্ছি, দেখছি। চমৎকার! অতি চমৎকার!’ রঘুনন্দন উঠে পড়ে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে থাকলেন।
মেধা বললেন—‘না। ওর মায়ের বিপদ নেই, অথচ ওর বিপদ আছে এই কথাটা ওকে বোঝানো দরকার। তবে আমার ধারণা ও যাবে না।’
—‘তোমার কাছে ওকে রেখে কি আমি সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?’ রঘুনন্দন বললেন।
—‘সেটা তুমি বোঝ। তুমি যদি জোর করে ওকে নিয়ে যাও, যেতে পারো। কিন্তু অতবড় বাংলোয় শুধু বৈজুলাল আর ও, জায়গাটাও নির্জন, তুমি যদি কলকাতায় থাকোও, সবসময়ে তো বাইরে বাইরেই থাকবে। আমি ওর শারীরিক নিরাপত্তার কথা ভাবছি না। মনের কথাটাই ভাবছি।’
—‘ও তোমার কাছে ভালো আছে?’
—‘আছে। কিন্তু তাই বলে তোমার দায়িত্ব কমছে না। তুমি যতদিন আছো ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে, কথা বলতে হবে এবং অরুণাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এই বিশ্বাসে ওখানে পুলিস নামানো চলবে না।’
রঘুনন্দন চমকে উঠলেন।
মেধা বললেন—‘হ্যাঁ। ওরা অরুণাকে সত্যি-সত্যিই নিজেদের মধ্যে চায় বলে নিয়ে গেছে। ওদের এখন অরুণার মতো মানুষ খুব দরকার। যারা সরকারের এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির হাড়-হদ্দ জানে, নিজেদের কথা গুছিয়ে বলতে পারে, লিখতে পারে। বছর কুড়ি আগেও যেমনি স্বেচ্ছায় তোমার কাছে এসেছিল, আজ ঠিক তেমনি স্বেচ্ছায় চলে গেছে। আদিবাসী ইনস্টিংট বলতে পারো।’
রঘুনন্দন দুপা ঈষৎ ফাঁক করে বসেছিলেন। তাঁর শাদা পলিয়েস্টারের ট্রাউজার্সে ছুরির ধার। এখন দুই হাঁটুর ওপর কনুই রেখে তিনি মুখটাকে নানাভাবে রগড়াতে থাকলেন। অবশেষে বললেন—‘তোমার কি মনে হয়, হ্যাভ আই লস্ট হার ফর এভার?’
—‘মেয়েকে যা লিখেছেন তাতে তো মনে হয় অবশ্যই ফিরে আসবেন, কিন্তু তুমি পারলে এখনই মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করো। দাঁড়াও ও কোথায় থাকতে পারে আমি ওর টেব্ল্টা দেখে তোমায় বলে দিচ্ছি।’
মেধা ঘরে চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে একটুকরো কাগজ রঘুনন্দনের হাতে দিলেন। বললেন—‘নিশ্চয় পেয়ে যাবে। ওকে আশ্বস্ত করো যে ওর মা ভালো আছেন। তুমি ব্যাপারটাতে ঘাবড়াচ্ছো না। তুমি এখন ওর আমার কাছে থাকাটাই ভালো মনে করছ। এগুলো দরকার।’
রঘুনন্দন খুব বিচলিত হয়ে বললেন, ‘তুমি অনেস্টলি ওর ভার নিচ্ছো মেধা? আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি? তুমি বরাবর বাঁধন এড়াতেই চাও। অ্যাট লীস্ট দ্যাট ইজ মাই ইমপ্রেশন। য়ু আর আ ফ্রি বার্ড। কেন? কেনই বা ওর ভার নিতে যাবে?’
মেধা বললেন—‘অনেক দিন আগে তুমি একবার বলেছিলে তোমার মেয়ে আমার মতো, মনে আছে?’
রঘুনন্দন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।
—‘আমার আদলে যে গড়া সে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার মেয়ে।’
রঘুনন্দন চমকে উঠলেন। তারপর গাঢ়স্বরে বললেন—‘মেধা তোমার মধ্যে মাদার ইনস্টিংক্ট খুব কম। খুব উইক। তুমি কিন্তু বদলে যাচ্ছো। এর থেকে প্রমাণ হয়, যে মেয়ে যেমন করেই স্বাভাবিক নারীত্বকে অস্বীকার করুক না, শেষ পর্যন্ত তাকে প্রকৃতির কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে।’
মেধা মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন—‘কার কি ইনসটিংক্ট, সে সম্পর্কে তোমার রীতিমতো গবেষণা রয়েছে দেখছি। আদিবাসী ইনস্টিংক্ট, মাদার ইনস্টিংক্ট, রঘুদা তুমি যদি আমেরিকায় দশ বছর থাকতে দেখতে পেতে মাদার ইনস্টিংক্ট ফাদার ইনস্টিংক্ট এ সবই আমাদের সংস্কার। বহুযুগের সামাজিক শিক্ষার উত্তরাধিকার। বাঘিনী শাবককে ততদিনই বাঁচায় যতদিন তার দেহে ল্যাকটেশন হয়। পক্ষিমাতাও দেখো ছানা উড়তে শিখে গেলেই আর তাকে চেনে না। মানুষ এর থেকে বেশি যেটুকু হয়েছে সেটা হল তার পূর্বপুরুষেরা সমাজ টিকিয়ে রাখার জন্য যে-সব নীতি নিয়েছিলেন তারই বিবর্তিত চেহারা। যুগের পর যুগ, এই শিক্ষা মানুষের রক্তে মিশেছে—একেই বলব হিউম্যান ইনস্টিংক্ট। মানবিকতা। মানবিকতাকে যতই কোণঠাসা করা হচ্ছে, প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে দলীয় রাজনীতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ আর ভোগবাদকে ততই উবে যাচ্ছে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন, ভাই-বোনের সম্পর্ক। মানুষে মানুষে হার্দ্য সম্পর্কের কথা, সহনশীলতা, ক্ষমা এসব তো এ যুগ ভুলেই গেছে। তাছাড়া চিরকালই যেখানে নিজের স্বার্থের প্রশ্ন আছে মা-বাবা সন্তানের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করেছে। সন্তানের ওপর নির্যাতনের কথা উঠলেই তো আগে ভারতবর্ষের কন্যা-হত্যা, সতীদাহ, বিধবা-হত্যা ইত্যাদির উদাহরণ তুলে ধরা হয়। ইংলন্ডের ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা জানো? নিজের বারো তের বছরের মেয়েকে বৃদ্ধ ডিউকের সঙ্গে বিয়েতে রাজি করানোর জন্য তার বাবা-মা এমন অকথ্য অত্যাচার করে যে মেয়েটি মারা যায়। এর পেছনে কি? ডিউকের দেওয়া ভূ-সম্পত্তির লোভ। আমাদের দেশে শিশু কন্যা হত্যার পেছনে কি ছিল? —সমাজের চাপ। আবার দেখো, ধনী দেশগুলো এখন অনাথ-বাচ্চাদের দত্তক নিচ্ছে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মানুষ করে তুলছে এ-ও তো হচ্ছে। একই সঙ্গে সমাজে দেখবে কেউ মানবিক গুণের আকর, কেউ আবার স্বার্থপর দানব। মূল বিষয় থেকে বোধহয় অনেকটা সরে এলুম। রঘুদা আসল কথা আমাদের সব সময়েই কাজ হবে মানবিকতাকে সাহায্য করা, প্রোমোট করা।’
রঘুনন্দন উঠে পড়লেন। হাসছেন। এতক্ষণে একটু একটু, বললেন—‘একদিনের পক্ষে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে মিস ভাটনগর।’
—‘কি?’
—‘লেকচার। আরেক দিন এসে নিশ্চয় শুনবো। তুমি কি সত্যি মনে করো অরুণার কোনও বিপদ নেই।’
—‘আই ক্যান বেট।’
‘ও কে, তুমি কি সত্যিই মনে করো, মুন্নি পালাবে না!’
—‘সত্যি মনে করি।’
—‘তবে তুমি ওকে রাখো। আমি নিশ্চিন্তে কাজ করি। তবে আমি এখন চট করে দিল্লি ফিরছি না। অরুণার একটা খবর পাওয়া আমার বড্ড দরকার।’
‘লুকু অর্ধেক দিন কলেজ থেকে বেরিয়ে মেধার সঙ্গে চলে আসে। কখন মৈথিলী আসবে অপেক্ষা করে। ছাত্রসঙেঘর কাজ করে। এখন ওদের সদস্য-সংখ্যা অনেক বেড়েছে। মাসিক চাঁদার হার বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও। বড় বড় চ্যারিটি শো, সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে ওরা। টাকা উঠছে হু হু করে। সে সব বিনিয়োগ হচ্ছে। ওদের কাজ অনেক। লুকু ফার্ন প্লেসে এসেই একপট কফি তৈরি করে ফেলে। বলে—‘দিদি আজ চিঁড়ে ভাজব?’ মেধা বলেন, ‘ভাজ্। আমি আলু কুরে দিচ্ছি। আলুর কুটভাজা চিঁড়ের সঙ্গে ভালো লাগবে। একটু অপেক্ষা কর। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তো ভালো লাগবে না।’
লুকু বলে—‘জানেন দিদি, আমি আগে চিঁড়ে ভাজতে জানতুম না। মা করত ঠিক সাদা ধবধবে ফুলের মতো দেখতে হত। ঝড়ু ভাজতো সেগুলো কিরকম ভিজে-ভিজে কালো-কালো শুঁটকে-শুঁটকে হত। তারপর একদিন বাপী বলল আমাতে তোতে চেষ্টা করি ঠিক পেরে যাবো। চিঁড়ে বার করতে করতে তেলটা খুব পুড়ে উঠেছে, আমাদের ব্যাপার তো! বাপী তাড়াতাড়ি একমুঠো ছেড়ে দিয়ে গ্যাসটা কমিয়ে দিয়েছে। অমনি চিঁড়েগুলো ফুলে ঢোল। বাপী বলছে—“লুক লুক শীগগীর তোল, এইবারে হয়েছে। পারবো না মানে?” সেই থেকে আমি চিঁড়ে ভাজতে খুব ভালো পারি।’
কিছুক্ষণ পরই মৈথিলী আর দেব আসে। কোনও কোনও দিন উজান য়ুনিভার্সিটি থেকেই লুকুদের সঙ্গ নেয়। মোটামুটি চার পাঁচজন এসে গেলেই লুকু চিঁড়ে ভাজতে আরম্ভ করে, মেধা আলু কুরতে আরমভ করেন।
একটা বড় স্টীলের কানা-উঁচু থালায় ওরা চিঁড়ে ভাজাটা মাঝখানে রাখে, সবাইকার হাতে একটা করে কাগজের গ্লাসে কফি। মেধা বলেন—‘দেব তুই আর খোলস থেকে বেরোলি না, কি অতো ভাবিস বল তো? প্রেমে ট্রেমে পড়েছিস, না কি?’ এরকম হালকা ঠাট্টা মেধা সাধারণত করেন না। একমাত্র চিঁড়ে ভাজা খাওয়ার সময়েই তাঁর এই মেজাজটা আসে, এটা লুকু লক্ষ্য করেছে। তাই মাঝে মাঝেই সে চিঁড়ে ভাজার উদ্যোগটা নেয়। যথেষ্ট রাতে বাড়ি যায় সব। অর্থাৎ ছাত্রসংঘের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যরা। লুকু অর্ধেক দিন মৈথিলীর হাতটা জড়িয়ে ধরে বলে—মৈথিল, আমায় থাকতে বল্ না রে!’
মৈথিলী বলে—‘লুকু তুই থাক। প্লীজ।’
লুকু বলে—‘দিদি, মৈথিলী কিন্তু আমাকে আজকেও থাকতে বলছে।’
মেধা ডায়াল ঘোরান।
‘বিশ্বজিৎদা! হ্যাঁ আমি মেধা বলছি। লুকু থাকছে। আপনারা ঠিক থাকবেন তো!’ বিশ্বরজিৎ মজুমদার, লুকুর বাবা বলেন—‘থাকুক। কাল আসবে তো?’ গলায় যেন একটু হতাশা।
‘আচ্ছা, আমি ওকে ফোনটা দিচ্ছি।’
লুকু ফোন ধরে—‘বাপী, আজ মৈথিলীর মন খারাপ, থাকি?’
‘হ্যাঁ, তা…কিন্তু জয় একটু গোলমাল করছে।’
‘ভাইয়াকে দাও, ভাইয়া, কাল ভোরবেলা চলে যাবো, হ্যাঁ। ঘুম থেকে উঠেই দেখবি দিদি। বাবাকে দে। বাবা, আজকের দিনটাই শুধু, তুমি মন খারাপ করবে না তো?’
‘নাঃ।’ নাটা বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য শোনায় না। স্ত্রী মারা যাবারপর, লুকুর বাবা বিশ্বজিৎ মজুমদার ছেলেমেয়ের ওপর খুব নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। মানসিক নির্ভরতা যাকে বলে।
লুক্ একদিন থাকে। আবার দুদিন বাবার কাছে। তৃতীয় দিন সন্ধে উৎরে গেলে হয়ত বলবে—‘দিদি, মৈথিল আজ আমায় একটু থাকতে বলুক না?’
‘বলুক—’ মেধা হাসবেন। তাঁর চিবুকের ওপর টোলটা গভীর হয়।
সেইদিকে তাকিয়ে লুকুর কি যেন মনে হয়, ভেতর থেকে একটা আবেগ উথ্লে ওঠে। কোনমতে সামলে নিয়ে সে ফোনের দিকে ছোটে। —‘বাপী, আজকের দিনটা আমি দিদির কাছে থাকি।’
মেধার পাশের ঘরে, দু বন্ধু খাটে শোয়। লুকুর অভ্যেস গলা জড়িয়ে শোওয়া। মৈথিলী আবার ওভাবে শুতে পারে না। সারা রাত সে গলা থেকে লুকুর হাত নামাতে থাকে, তারপর এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে যায়। মাঝখানের দরজাটা খোলা থাকে। অনেক রাত অবধি শুয়ে শুয়ে স্ট্যান্ডিং ল্যাম্পের আলোয় পড়তে পড়তে এক সময়ে মেধা বই নামিয়ে রাখেন। ল্যাম্পের সুইচটা নিবিয়ে দিলে প্রথমটা সব ঘোর অন্ধকার হয়ে যায়, তারপরই পাশের ঘরে সাদা বিছানায় দুটি দুধ শাদা রাত জামার জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকার দৃশ্যটা দেখতে পান। ঘুমের বড়ি খাবার মতন নিশ্চিদ্র নিদ্রা আসে।
অধ্যায় : ১৪
সেবার নতুন বছরের শুরুতেই ছাত্রসংঘের প্রেসিডেন্ট মৈথিলী ত্রিপাঠী সংঘের সাধারণ সভায় ঘোষণা করল তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে। এই লক্ষ্য হচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ ছাত্রশক্তি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোট্ট অবহেলিত, অনুন্নত, নিরন্ন গ্রামকে সব দিক থেকে স্বয়ম্ভর করে তোলা। সেক্রেটারি উজান আফতাব তার সুলিখিত প্রতিবেদন পড়ে শোনায় সঙ্গে সঙ্গে তার তাৎক্ষণিক টীকা ভাষ্য। সে জানায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ওই কেওড়া গ্রাম এখন জেলার সবচেয়ে উন্নত মানের গ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানে প্রত্যেকটি গ্রামবাসী বাংলা ও ইংরেজিতে প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা করতে পারেন, দলিল-দস্তাবেজ ফর্ম ইত্যাদি পড়ে পূরণ করা এবং সই করবার বিদ্যা প্রত্যেকটি বয়স্ক মানুষের আয়ত্ত হয়েছে। অল্প বয়সীরা এখন নানারকম বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উৎসাহী। যথাসম্ভব কাছাকাছি তাদের প্রশিক্ষণের কাজ ছাত্রসংঘ আরম্ভ করে দিয়েছে। একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। গ্রামের চাষীরা আপাতত বলদ এবং লাঙল নিয়ে পুরনো পদ্ধতিতেই চাষ করছেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের জমি তেফসলি। ইঁদারা, পাতকুয়ো এবং নলকূপ যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় এবং শস্যক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অগভীর ডোবাগুলি ভালোভাবে খুঁড়ে বড় পুকুরে পরিণত হওয়ায় সেচের সমস্যা মিটেছে। তাঁদের প্রধান উৎপাদন নানারকম ফল ও সবজি তাঁরা নিজস্ব ভ্যান গাড়ি করে গঞ্জের বাজারে নিয়ে বিক্রি করে আসেন। প্রায় প্রতিদিন। পাইকারের হাত-ফেরতা হয়ে যায় না বলে লাভ অনেক বেশি থাকে। উদ্বৃত্ত ফল এবং কিছু কিছু আনাজ দিয়ে আচার-চাটনি তৈরি করার একটি মহিলাপ্রকল্প হয়েছে। এইসব বিশুদ্ধ ফলের আচার ছাত্রমেলায় বিক্রি হয়, ছাত্রসংঘের অফিসেও পাওয়া যায়, শহরের দোকানে সাপ্লাই দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। মহিলাদের দ্বিতীয় সমিতি সেলাইয়ের কাজ করে। জামা-কাপড় সেলাই ও বোনা, এর ফলে নিজেদের গ্রামে তো বটেই, আশপাশের গ্রামেও সস্তায় ভালো টিকসই জামা এবং গরম জামা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। গ্রামে রয়েছে একটি মাধ্যমিক স্কুল। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে এখনও গ্রামের মানুষ আরও উচ্চস্তরের পড়াশোনার জন্য আসছেন। গ্রামের রাজ এরং ছুতোর মিস্ত্রিরা মিলে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছেন, তাছাড়াও রয়েছে একটি ছোটখাটো আসবাব কারখানা। গ্রামান্তর থেকেও বহু ছাত্র এখানে শিক্ষা নিতে আসে। গ্রামগঞ্জে ব্যবহারের উপযোগী আসবাব তৈরি করে এবং মাদুর ও বেত বুনে এঁরা ভালোই উপার্জন করেন। সবচেয়ে মুশকিলে পড়া গিয়েছিল তেওড় পাড়া বা জেলে পাড়া নিয়ে। এঁদের অনেকটা পথ মাতলা বিদ্যাধরী দিয়ে গিয়ে হয় সুন্দরবনের বিপজ্জনক এলাকায় স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মাছ ধরতে হত, নয়ত ক্যানিঙের আড়ৎ থেকে মাছ কিনে ফেরি করতে হত। মাতলা নদীও গ্রাম থেকে যথেষ্ট দূরে। হাঁটা পথ, জলপথ দুবার অতিক্রম করে সামান্য উপার্জন নিয়ে এঁরা ঘরে ফিরতেন। এখন গ্রামের মধ্যে একটি চমৎকার পুকুর বড় করে কাটিয়ে দিঘি করার এবং গ্রামের প্রান্তিক খাল ও জলাগুলির সংস্কার করে আল দেওয়ায় মৎস্যচাষের সুবিধে হয়েছে। ইতিমধ্যেই কিছু সুফল পওয়া গেছে। এ ছাড়াও তেওড় পাড়ার বেকার মানুষদের গ্রামের যৌথ ডেয়ারি ও পোলট্রির ভার দেওয়া হয়েছে। মৌমাছির চাষও শুরু হয়েছে। ডেয়ারির উদ্বৃত্ত দুধে ছানা, দই, মাখন ও ঘি হচ্ছে, স্থানীয় বড় গঞ্জে এগুলোর দারুণ চাহিদা। গ্রামে আছে পাতাল ফোঁড় শিবের মন্দির ও ফকিরসাহেবের মাজার সংলগ্ন একটি মসজিদ। চৈত্র সংক্রান্তিতে এবার ফুলতলির মাঠে বিরাট মেলা বসানো হয়, মেলাটি সম্পূর্ণ ভাবেই বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির মেলা, মেলার পরিচালনাভার ছিল স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার মশাই নিরঞ্জন খাঁড়ার ওপরে। গ্রামে বেশ কিছু সঙ্গীত প্রতিভা আছে, একটি সঙ্গীত শিক্ষালয় খুলে ছাত্রসংঘ আপাতত এ গ্রামকে স্বয়ম্ভর, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যসচেতন, সংস্কৃতিবান একটি আদর্শ গ্রাম বলে ঘোষণা করছে।
এই দিনের অধিবেশনের পরে ছাত্রদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ওই একদিনে তিন হাজার নতুন ছাত্র সদস্য হবার জন্য আবেদনপত্র পেশ করে। স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা গান নাচ পাঠ কথকতা ইত্যাদির পর ছাত্রসংঘের আয়োজিত স্টল থেকে নানারকম মুখরোচক খাবার খেয়ে ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরে যায়।
বার্ষিক অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর মৈথিলী রাত নটায় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছে। মেধাদির ফোন পেল। মৈথিলী আজকাল বেশির ভাগ চ্যাপেল রোডেই থাকছে। সে মায়ের চিঠি পাচ্ছে মাসে একটা করে। তার ছোটমামা সত্যেন সোরেন ইতিমধ্যে তার সঙ্গে একবার দেখা করে গেছেন। কাজেই সে এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাবা যখনই কলকাতায় থাকছে সে-ও চ্যাপেল রোডের বাড়িতে এসে থাকছে। মেধাদি বললেন—‘বৈজুলালকে বলে আজ রাতটা এখানে চলে আয়। কিছু দরকারি কথা আছে।’
ছাত্রসঙ্ঘের এই অধিবেশনটা হয় মউমিতাদের বহুতল ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সের নিচের তলায়। শুধু ওদের কো-অপারেটিভের অনুমোদন ছাড়া আর কিচ্ছু লাগেনি। অধিবেশনের ছিল খানিকটা উৎসবের চেহারা। মুখে মুখে প্রচারিত এই ছাত্রমেলায় বহু ছাত্রছাত্রী সারাদিন ধরে এসেছে, গেছে। মৈথিলী আর উজানের গলায় রেকর্ড করা, ছাত্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য, তাদের কাজকর্ম এবং সাফল্যের খতিয়ান বারে বারেই টেপে বেজেছে। সঙ্গে পালান এবং সম্প্রদায়ের টেপ করা গান, আনোয়ারের মেয়ে ফতিমা ও ছেলে সুলেমনের গান। জায়গাটা ফার্ন-প্লেস থেকে বেশি দূরে নয়। মেধাদি আগে বললে মৈথিলী ওখানেই চলে যেত সোজা। কিন্তু এখন ন-টা তো বেজে গেছেই। আলিপুরের রাস্তা নির্জন। বড্ড ছিনতাই হচ্ছে আজকাল।
বৈজু বলল—‘আমি তোমাকে ছোট থেকে দু হাতে মানুষ করেছি মুন্নি, এই রাত্তিরে একা একা মুখের খাবার ফেলে যেতে চাও যাও, কিন্তু বৈজুর বুকে কষ্ট দিয়ে যাবে। চাকর-বাকর হতে পারি কিন্তু ভেবে দেখো আমি তোমার মায়ের কাজও করেছি, বাবার কাজও করেছি।’
মুন্নি আবার দিদিকে ফোন করল, বলল—‘রাত হয়ে গেছে, বৈজুদা যেতে দিচ্ছে না।’
মেধা বললেন, ‘ঠিক আছে তোর বৈজুদাকে বল, আমাকেও যেন খাওয়ায়।
আধঘণ্টার মধ্যে স্কুটারের আওয়াজ পাওয়া গেল। মেধাদি ঢুকতে ঢুকতে বললেন—‘বাঃ, এই বেশ ভালো হল। রোজ রোজ এক জায়গায় ঘুমোতে ভালো লাগে? কি বৈজু খুশি তো? কি খাওয়াবে?’
—‘আমি যা রাঁধি তা তো আপনার চলে না দিদি’—বৈজু গোমড়া মুখে বলল। অরুণা চলে যাবার পর দীর্ঘ দিন মুন্নি দিদির কাছে থেকেছে। তাকে মুন্নির ভার দেওয়া হয়নি, যদিও অরুণা দিল্লি গেলে বরাবর মুন্নি বৈজুর কাছে একলাই থেকেছে, সে এটা ভুলতে পারে না।
—‘কি রেঁধেছো বলোই না।’ মেধা হাসিমুখে বললেন।
—‘কিমাকারি আছে, আর গোল গোল পরোটা, ফিশ ফিংগার করেছিলুম কয়েকটা।’
—‘বাববাঃ এতো? তো ঠিক আছে, তোমার জন্য কি করেছো?’
বৈজু বলল—‘আলুচোখা আর চাটনি।’
—‘বাঃ তাই দিয়েই আমার হয়ে যাবে। আজ আমি বাড়ি তালা দিয়ে এসেছি।’
খাওয়া-দাওয়ার পর ধীরে সুস্থে গল্প-সল্প করলেন মেধা, মৈথিলীর সঙ্গে খানিকটা, বৈজুলালের সঙ্গে খানিকটা। তারপর বললেন—‘মৈথিলী, তোদের সভায় কোনও সাংবাদিক যায়নি?’
—‘কই না তো?’
—‘যায়নি? তাহলে যাবে। খবরটা ওদের কাছে খুব সম্ভব দেরিতে পৌঁছেছে। আমার কাছে এসেছিল।
—‘তাই নাকি? আপনি কি বললেন?’
—‘আমি বলেছি ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানের কথা ছাত্ররাই জানে। আমি বিশেষ কিছু জানি না।’
—‘এ কথা কেন বললেন, দিদি?’
—‘সে কথাটাই তোকে বোঝাতে এসেছি। ছাত্রসঙ্ঘ গড়েছিলি প্রধানত তুই উজান আর দেব। আমাদের কয়েকজনকে তোরা উপদেষ্টা হিসেবে চেয়েছিলি। বাইরে থেকে এইরকম কিছু পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আমরা আর কিছু করিনি।’
—‘কথাটা তো সত্যি নয়, দিদি!’
—‘শোন মৈথিলী, তোরা ঠিক কর তোরা প্রচার চাস কি না।’
মৈথিলী খানিকটা হকচকিয়ে গেছে। দিদি কি তাকে কোনও পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে চাইছেন! সে বলল—‘আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না দিদি।’
—‘যতক্ষণ তুই প্রাণপণ পরিশ্রম করছিস, একটা কিছু গড়বার সঙ্কল্প করে প্রাণপাত করছিস, ততক্ষণ দেখবি নানাজনে তোর সঙ্কল্প নিয়ে অনেক কথা বলবে। কেউ বলবে বোকামি, কেউ বলবে মতলব আছে, কেউ বলবে অবাস্তব ব্যাপার, কিন্তু যে মুহূর্তে সাফল্য পাবি অমনি এই লোকগুলোই তোকে ছেঁকে ধরবে। প্রচার এক হিসেবে খুব ভালো। কাগজে, টিভিতে, রেডিওতে। জনসাধারণ জানতে পারবে ছাত্ররা ভালো ভালো কাজ করছে। তোদের হয়ত সাহায্য করতে অনেক লোক এগিয়ে আসবে। কিন্তু এই প্রচারের একটা মারাত্মক বিপদের দিক আছে।’
—‘কি?’ মৈথিলী জিজ্ঞেস করল।
—‘জনসাধারণের সঙ্গে সব সময়ে মিশে থাকে কিছু বাজে লোক যারা স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কিচ্ছু বোঝে না। অনেক সময়ে এরা এমনকি কারণ বিনাই কুচক্রে লিপ্ত হয়। এই সব লোকেদের চোখে পড়ে গেলে তোর ছাত্রসঙ্ঘ ছত্রখান হয়ে যাবে। তোরা আর এগোতে পারবি না। দেখবি নানা দিক থেকে নানা বাধা আসছে। পাবলিসিটি অতি ভয়ানক জিনিস। আমার মনে হয় তোরা এই স্কুপ-নিউজ খুঁজতে আসা সাংবাদিকগুলোকে এড়িয়ে চল। প্রসারের জন্য প্রচার ভালো। কিন্তু প্রচারের জন্য প্রচার খুব বিপজ্জনক জিনিস। আরেকটা কথা, শীগগীরই তোরা অর্থাৎ তুই, লুকু, উজান, দেব তোদের গ্রুপটা আর ছাত্র থাকছিস না। তোকে দেবকে ইনটার্নি থাকতে হবে। প্রচণ্ড খাটুনি, উজানও যদি প্রথম পাস করার পরই কোনও ভালো জায়গায় চাকরি ধরতে না পারে ওর শিক্ষাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তোরা এখন থেকেই ঠিক করতে থাক, কে বা কারা তাদের জায়গা নেবে।’
মৈথিলী অবাক হয়ে বলল—‘কেন দিদি, না-ই বা ছাত্র থাকলাম।’
মেধা হেসে বললেন—‘তোর কি মায়া হচ্ছে? এই মায়া কিন্তু একেবারেই ভালো নয়। ব্যাপারটা কি জানিস দেশের কল্যাণের জন্যে চিরকালই মুষ্টিমেয় মানুষ পরিশ্রম করে গেছে, আত্মত্যাগ করে গেছে, তাতে তাদের তো ভালো হয়ই নি, দেশেরও হয়নি। একটা প্রতিষ্ঠানের হাতে বা গুটিকয় মানুষের হাতে সমস্ত ভুবনের ভার সঁপে দিয়ে স্বার্থপর আত্মসুখে কাল কাটাবার এই ভারতীয় অভ্যাসটা আমাদের ছাড়াতে হবে। তোরা এই ছাত্রসঙ্ঘের ব্যাপারটাকে চলিষ্ণু রাখ। এত বড় বিরাট দেশ, দেশের অভ্যন্তরে কত যুগের আশঙ্কা, কুসংস্কারে আবদ্ধ বিশাল জনতা—এদের উন্নয়ন একা তোরা আমরা কতটুকু করতে পারি, অথচ এটাই আসল কাজ। এবং এটা এক জেনারেশনের কাজও নয়। তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম যাতে খুব স্বাভাবিকভাবে এই কাজটা জীবনের আর কয়েকটা প্রয়োজনীয় কাজের মতো করে করে যায়, তবেই সত্যিকার কিছু কাজ হবে। কেওড়াখালি নিয়ে আমরা যেটা করলুম সেটা একটা এক্সপেরিমেন্ট। এক্সপেরিমেন্টটা সফল হয়েছে। এবার এটাকে আমরা পেটেন্ট নেবো। রূপরেখাটা আমাদের জানা হয়ে গেছে। এই প্রজেক্ট এখন একসঙ্গে অনেকগুলো শুরু কর। যে কটা পারিস। তোদের জনবল, অর্থবল বুঝে। এবং বিভিন্ন প্রজেক্টের ভার দিতে থাক দায়িত্বশীল, উৎসাহী, কর্মী ছাত্রদের। এইভাবে তোদের উত্তরাধিকারী তৈরি হবে। তোরা ছাত্রাবস্থা থেকে বেরিয়ে যাবি, যুক্ত থাকবি হয়ত অনেক দিন উপদেষ্টা হিসেবে, কিন্তু ক্রমশ নিজের নিজের পেশায় ব্যস্ত হয়ে পড়বি, গৃহস্থ হবি, সচেতন নাগরিক, দেশ-সচেতন, মূল্যবোধ-সচেতন গৃহস্থ। তোদের পরবর্তী বছরের ছাত্ররা আসবে, তারাও ঠিক এইভাবে কাজ করে যাবে, তৈরি করবে ভবিষ্যতের নেতাদের। এই চেনটা তৈরি করতে থাক, না হলে তোদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শেষ হয়ে যাবে। আর এক একটা গ্রাম বাছবি খুব সাবধানে। রাজনীতির আওতার বাইরে দরিদ্র, নিঃস্ব, ছোট্ট গ্রাম। শহরে, গঞ্জে, মফঃস্বলেও তোরা প্রজেক্ট কর, তবে সেগুলোর প্রকৃতি ন্যাচার্যালি আলাদা হবে। চিন্তা কর সে ক্ষেত্রে তোদের প্ল্যানে কোথায় কি অদলবদল হবে।’
মৈথিলী বলল—‘দিদি। আমরা কেউ কেউ যদি পুরো জীবনটাই এই কাজে থাকি তাতে ক্ষতি কি?’
মেধা হেসে বললেন—‘এসব কাজ এতো সময়সাপেক্ষ, এতো একঘেঁয়ে যে একটা সময় হতাশা আসবে, কল্পনাশক্তি ব্যবহার করতে পারবি না, নূতনত্বের স্বাদ না পেলে ক্লান্ত হয়ে পড়বি মৈথিলী। তাছাড়া আজ মনে হচ্ছে এই নিয়েই কাটাবি। সব সময়েই এইরকম মনোভাব থাকবেই তা বলা যায় না। না থাকাই স্বাভাবিক। মানুষের ফুল লাইফ চাই। পূর্ণ জীবন। সব চাই। স-ব। একটা ব্রতে নিজেকে সারাজীবনের জন্য বেঁধে ফেললে একদিন মুক্তির জন্য ছটফট করবি। কিম্বা অত্যধিক আসক্ত হয়ে, অটোক্র্যাট হয়ে যাবি, কাজটা মাঝখান থেকে মাটি হয়ে যাবে।’
কিন্তু এতো সাবধানতা সত্ত্বেও কলকাতার এক মাঝারি দৈনিকে ছবিসহ এক স্টোরি বেরিয়ে গেল। মেধা ভাটনগরের ছবি, মৈথিলীর ছবি, কেওড়াগ্রামের উন্নতিতে তাদের অবদানের কথা।
কার্য-নির্বাহক কমিটির মিটিং-এ উপস্থিত থেকে মেধা বললেন—‘সাংবাদিকদের কাছে আমিও মুখ খুলিনি, মৈথিলীও না। তোরা কে এ কাজ করেছিস স্বীকার কর। কাজটা হয়ত তোরা ভালো ভেবেই করেছিস, কিন্তু ঠিক করিসনি।’
উজান, দেবপ্রিয়, লুকু, গুঞ্জন কেউই স্বীকার করল না। মেধা বললেন—‘যাই হোক, তোদের জানা ছিল না, এখন জেনে রাখ প্রচার আমরা চাই না। প্রচার বিষ। আমরা নিঃশব্দে কাজ করে যাবো।’
অধ্যায় : ১৫
প্রমিত একটা সিগারেটের দোকান দেখিয়ে বলেছিল ‘দেব এইখানে অলওয়েজ পাবি। একটা কোড আছে।’ বলে সে কোডটা দেবপ্রিয়কে নিচু গলায় বলেছিল। তারপর থেকে দোকানটা থেকে রোজ এক প্যাকেট দুপ্যাকেট স্পেশ্যাল এবং দামী সিগারেট কিনতে হয় দেবপ্রিয়কে। এই নতুন খরচের জন্য তাকে দু-একটা টুইশান ধরতে হয়েছে। এখানেই সাকসেনা এবং প্রবীর রায় নামে দুজন যুবকের সঙ্গে তার আলাপ হয়, যারা তাকে আরও অনেক মজাদার নেশার সন্ধান দেয়। এখন দেবপ্রিয় বেশ কয়েকটা ঠেকে যাচ্ছে। মধ্য কলকাতায় একটা, হাওড়ার শালকেতে একটা আর দক্ষিণ কলকাতার উপান্তে একটা। এতে করে তার এতো সময় যাচ্ছে যে সে পড়াশোনার জন্য বিশেষ সময় দিতে পারছে না। মেডিসিনে গোল্ড মেডেলটা মৈথিলীই পাবে মনে হয়। সার্জারিতে এখনও দেবপ্রিয় সর্বাগ্রে আছে। কিন্তু ছাত্রসংঘের কাজকর্ম সে একেবারেই করছে না। ছাত্রসঙ্ঘ এখন একসঙ্গে তিনটে ফ্রন্টে কাজ করছে গ্রাম, মফঃস্বল ও শহরের মধ্যস্থিত বস্তি অঞ্চল। বহু ছেলে মেয়ে পালা করে করে এই প্রজেক্টে অংশ নিচ্ছে। মৈথিলী উজান সবারই ফাইন্যাল ইয়ার, তারা হিসেব রাখা প্রজেক্ট তৈরি করা, রিপোর্ট দেখা এগুলোই প্রধানত করে। নতুনদের মধ্যে অনেকেই কেন্দ্রীয় সমিতির মীটিং-এ এসে কাজকর্ম শিখছে, নিজেদের মতামত দিচ্ছে, মেধাদির সঙ্গে আলোচনা করছে।
সেদিন কাজ কর্মের শেষে বেশির ভাগই চলে গেছে। আছে খালি উজান আর মৈথিলী। উজান বলল ‘মৈথিল মেধাদিকে একটু ডাক। আমার দরকারি কথা আছে।’ মৈথিল বলল ‘চল না আমরাই ওপরে যাই।’
ওপরে উঠে ওরা দেখল দালান অন্ধকার। দিদির ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। মেধা তাঁর চেয়ারে সামান্য হেলান দিয়ে ভায়োলিন শুনছিলেন। চোখ বোজা। মৈথিলী দেখল দিদি একটা চাঁপা রঙের কালো পাড় টাঙ্গাইল শাড়ি পরেছেন। ঘরে মৃদু আলো। দিদিকে ভাস্বর দেখাচ্ছে। তাঁর মুখটা প্রশান্ত। প্রায় সদ্যমৃত মানুষের মতো। যেন পার্থিব কোন ব্যাপার আর তাঁকে স্পর্শ করছে না। মুখের রেখাগুলি যেন চিরতরে মিলিয়ে গেছে। ভায়োলিনে কোনও ভারতীয় সুর। সুরটা মৈথিলী জানে না। কিন্তু তার মধ্যে কান্না ভাবটা একেবারে নেই। মেধাদির ফার্ণ প্লেসের বাড়ির আধো-অন্ধকার দোতলার ঘরটা যেন শূন্যে ভাসমান একটা স্পুটনিক। আপাতত তিনি এ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাজনা শুনল। মৈথিলী উজানের পিঠে টোকা দিল, ইশারায় বলল বাইরে আসতে। বাইরের দালানে মৃদু আলো জ্বলছে। একদিকে গ্যাস উনুনের ওপর ছোট্ট একটা প্রেশারকুকার। ওর ভেতরে মেধাদির রাতের খাবার রান্না করা রয়েছে। হয়ত আজকে ভাত খাবেন, তাই সবকিছু প্রেশারে চাপিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছেন।
দুজনে পা টিপে টিপে নিচে নেমে এলো। মৈথিল নিচু গলায় বলল ‘উজান দিদিকে ডাকতে আমার মায়া হল।’
উজান বলল ‘ভায়োলিনটা অসাধারণ বাজছিল।’
মৈথিলী বলল ‘দিদিকে এতো নরম, স্নিগ্ধ দেখাতে আমি ইদানীং দেখিনি।
উজান দেখেছিলি যেন আপাদমস্তক কিরকম মোম দিয়ে গড়া। কবিত্ব করে বলতে ইচ্ছে করছে ভালোবাসার মোম।’
উজান বলল—‘য়ু আর রাইট। কিন্তু এই ভালোবাসা অন্যরকম। ঠিক আমাদের চেনা অনুভূতি বা আবেগগুলোর মতো নয়। ডিফরেন্ট ইন কাইন্ড।’
‘তা যদি বলিস’ মৈথিলী বলল ‘আবেগ জিনিসটাই যেন দিদির মধ্যে অনুপস্থিত। না তা-ও না। ইমোশনকে যদি ঘনীভূত সলিড স্টেটে রাখা যায় তো এই ধরনের একটা এফেক্ট আসতে পারে।
উজান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—‘মৈথিল তুই মেধা ভাটনগরের অতীত ইতিহাস জানিস।’
‘সামান্যই। বাবার কাছ থেকে শুনেছি ওঁর বাবা ডাঃ অশোক ভাটনগর ছিলেন রেডিও ফিজিক্সের একজন কর্ণধার লোক। ওঁর মা ডাঃ লীলা ভাটনগর বায়ো-কেমিস্ট্রির গবেষক। দুজনেই পড়াশোনা আর ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া আর কিছু জানতেন না। আমার বাবা ছিলেন ডাঃ ভাটনগরের ছাত্র। তবে বাবা সাইড-ট্র্যাক করে সরকারি আমলা হয়ে গেলেন। বাবার সঙ্গে একবার মেধাদির বিয়ের কথা হয়। আমার মায়ের সঙ্গে বাবার পরিচয়ের আগে। বাবা খুব কীন ছিলেন। দিদিই রাজি হননি।’
উজান বলল—‘এ পরিচয়টা তেমন কিছু নয়। আমি আমার দাদু আর বাবার কাছ থেকে শুনেছি মেধা ভাটনগর চূড়ান্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ষাট সত্তরের দশকে। দাদু অবশ্য কথাটা বলেছেন নিন্দাচ্ছলে ‘ওরে বলে ধিঙ্গি।’ এই আমার দাদুর ভাষা। বাবার কিন্তু ওঁর ওপর ভীষণ শ্রদ্ধা বাবা নিজেও তো কিছুদিন এসব করেছেন। দাদুর প্রচণ্ড ধমক-ধামকে আবার ভালোমানুষ গৃহস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন। আমার পিসিও এই রাজনীতি করত। হঠাৎ দাদুর বেছে দেওয়া বাংলাদেশি বড় ঘরের ছেলেকে বিয়ে করল, করে কয়েক মাসের মধ্যে আমেরিকা চলে গেল। যে আমেরিকার বিপরীত মেরুতে মার্কসিস্টদের অবস্থান। অথচ রোকেয়াপিসিই নাকি মেধাদিকে রাজনীতিতে নামিয়েছিল, ভাটনগর পরিবারের কেউ কস্মিনকালেও পলিটিক্স করেনি। সেইসময়ে মেধাদি নাকি একদিন উদ্ভ্রান্তের মতো আমার বাবার কাছে ছুটে আসেন বলেন—অঞ্জুদা দেখুন রোকেয়া কি লিখেছে, আমার তিনপাতার চিঠির উত্তরে একটা মাত্র লাইন—মেধা ড্রাইভিং শিখছি, এম এস করছি। আমার বিশেষ সময় নেই।’
‘বাবা বলে আমার মনের মধ্যে একটা খেদ রয়ে গেছে ভয়ে, সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে আমি আন্দোলন থেকে সরে এসেছি। কোট প্যান্ট পরা ভদ্দর লোক হয়ে জীবন কাটাচ্ছি। আরো একটা খেদ মেধার জীবনটা বোধহয় নষ্ট হয়ে গেল। আমি রোকেয়াকে বুঝি না, বোঝবার চেষ্টাও করি না আর, কিন্তু মেধাকে আমি একটু একটু বুঝি। তুই কি জানিস মৈথিল মেধাদি এখনও জানেন না, আমি রোকেয়া আমেদের ভাইপো। জানলে বোধহয় ছাত্রসঙ্ঘের কাজে কোনদিন আমাকে ডাকবেন না আর’
মৈথিলী এই সময়ে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারা দুজনেই দোতলা থেকে নেমে সিঁড়ির দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। মৈথিলী একটু পাশ ফিরতে দেখল মেধাদি সিঁড়িটার প্রায় সবটা নেমে এসেছেন। চোখ এখনও তেমনি আবিষ্ট। খালি পা। উজান দেখতে পায়নি।
মেধাদি বললেন—‘তোরা বাড়ি যাবি না? হিন্দি খবর শুরু হয়ে গেল যে।’
উজান একটু চমকে দিদির দিকে ফিরে দাঁড়াল। মেধা স্নিগ্ধ স্বরে বললেন ‘কে তোকে বলেছে যে আমি জানি না তুই অঞ্জুদার ছেলে রোকেয়া আমেদের ভাইপো। না জানা কি সম্ভব? তোর দাদু দীর্ঘদিন এম পি রয়েছেন এ আমার জানা থাকবে না?’
উজান কথা বলতে পারছে না। ছটফটে উজান। স্মার্ট উজান। কথার পিঠে কথা যার কখনও আটকায় না সে দেবপ্রিয় চৌধুরীর মতো চুপ করে গেছে। সে যেন তার পিসির, তার বাবার সমস্ত অপরাধ মাথায় নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়, নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে দিতে হলেও তার আপত্তি নেই।
মেধা আরও একটু এগিয়ে এলেন। তাঁর সমস্ত শরীর থেকে কি যেন একটা হালকা সুবাস উজানকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে আস্তে আস্তে। সে যেন একটা সুগন্ধময় আলোক বলয়ের মধ্যে অবস্থান করছে। মেধা ভাটনগর অতীত যুগের বর্তমান যুগের অনাগত দিনের এক চৌম্বক শক্তিধারী ব্যক্তিত্ব, যাঁর সম্পর্কে তার বাবা বলে থাকেন টোট্যাল ডিভোশন টু হার কজ, যিনি খানিকটা কাছাকাছি থাকেন বলেই সবসময়ে বোঝা যায় না, তিনি সত্যিই কী অসাধারণ এবং খুব কাছে এলে অনুভব করা যায় তাঁর শক্তি আর ভালোবাসা দিয়ে গড়া চৌম্বকক্ষেত্রের তীব্র আকর্ষণ এবং সে উজান যে তার এই অল্প বয়সেই খেলাধুলো, ধর্ম, রাজনীতি, পড়াশোনা ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তে ঘুরে ঘুরে বুঝেছে এইসব সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তার কোনদিন কিছুতেই পোষাবে না। তার অন্তরাত্মা চায় নিজেকে দুধারে ছড়িয়ে দিতে নিজেকে ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে যেতে। উজান এখন আর কাউকে, আর কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। চোখ ধাঁধাচ্ছে না এই দীপ্তি, শুধু আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে মৃদু উত্তেজনায়, এই উত্তেজনা মাদক কিনা সে বিচার করতে পারছে না, খালি বুঝতে পারছে এই সেই ঈপ্সিত মণ্ডল। এই অনুপ্রাণনাময় জ্যোর্তিময় কালিমাহীন শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে সে পৌঁছতে চায়।
মেধা মৃদু গলায় বললেন—‘উজান তুই কি জানিস আমাদের জেনারেশনের ভাঙা-গড়ার সেই অসহ যন্ত্রণার গোপন কথা! জানিস কি কীভাবে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? পারেনি, শেষ পর্যন্ত পারেনি। কেউই বোধহয় পারে না। দে ওয়্যার সো মেনি এঞ্জেলস উইথ ফীট অফ ক্লে। সোনার মাথা, মাটির পা। তোরা ভাবিস তোদেরই যত সমস্যা। তোদের পরীক্ষার অ্যাসেসমেন্ট ঠিক হচ্ছে না, তোদের অধ্যাপকরা ঠিকমতো পড়াচ্ছেন না। তোদের চাকরি নেই, দাঁড়াবার মাটি নেই। নেই সত্যি। কিন্তু ওদেরও বড় দুরূহ সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তোরা তার কিছুই জানিস না। মৈথিলী তোরা উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে। তোরা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছিস ক্রমশ। লাখ লাখ টাকা দিয়ে একেকজনের কেরিয়ার গড়া হচ্ছে, তারপরে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে। বলছে এদেশটা উচ্ছন্নে গেছে, আর থাকা যায় না। তোরা ব্যতিক্রম। সত্যি কথা বলতে কি, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এতো সাফার করেছে, এতো আত্মত্যাগ করেছে এবং এত পিষ্ট হয়েছে যে বর্তমানে তার আর শিরদাঁড়া নেই। উজান-মৈথিলী তোরা যারা অনেক পেয়েছিস, তারা ওদের জন্য কিছু কর। ওদের ভরসা দে যে ডলারের প্রলোভনে আর লোড-শেডিংহীন জীবনযাপনের হাতছানিতে তোরা ওদের এই পাঁকের মধ্যে ফেলে যাবি না। আমাদের সময়ে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের পোশাক আষাকে এতো ফারাক ছিল না। আমরা এতোটা স্টেটাস কনশাসও ছিলাম না। কলেজে কলেজে, স্কুলে স্কুলেও এমনি উচ্চবর্গীয় নিম্নবর্গীয় তফাত স্পষ্ট ছিল না। আমাদের সময়েরও অনেক দোষ ছিল, কিন্তু অল্প বয়স্কদের মধ্যে লোভ, উন্নাসিকতা, রুচির বিকার এইভাবে দেখিনি। যেসব জিনিস তোদের মূল্যবোধকে প্রতিদিন একটু একটু করে পঙ্গু করে দিচ্ছে তোরা সেগুলোকে চিনতে শেখ। ড্রাগ, মদ, বিকৃতরুচির ফিল্ম, রাজনীতি, ভারসাম্যহীন প্রতিযোগিতা, অসুস্থ উচ্চাকাঙ্খ। শুধু যন্ত্রের ওপর ভর দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর দিকে যেতে দিসনি দেশকে। ভর করতে হবে প্রকৃতিস্থ মূল্যবোধের ওপরে।
উজানের ভেতরটা অনেকক্ষণ এই চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে কিরকম কাঁপছে। খুব কাছে উনি দাঁড়িয়ে আছেন, মৃদু আলোয় হালকা হলুদ ফুরফুরে শাড়ি-মোড়া একটা উন্নত মূর্তি। তার ইচ্ছে করছে মেধাদিকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকে ঊরুতে তাঁর পায়ে সে মাথা ঘষে-ঘষে ঘষে তার নিজের সার কি সে যেন খুঁজে পেতে পারে। তাঁর দেহ-মন মস্তিষ্ক হৃদয়ের সারাৎসার কি, তাঁর সঙ্গে এই যাত্রার শেষ কোথায়, কোন অনির্বচন পরিণতিতে সে যেন তার সন্ধিৎসু জীবনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বুঝে নিতে চায়।
মেধাদি বললেন—‘তোরা যা। উজান, বাইরের গেটের ছিটকিনিটা আটকে দিয়ে যাবি। দুজনে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। কারুর মুখেই কথা নেই। ভেতরে লোহার খিল আটকানোর শব্দ হল। ফার্নপ্লেসের এই সুন্দর ছিমছাম পড়ুয়া দোতলা বাড়ির সদর দরজার ওপর অনেকখানি সানশেড। তার তলায় একটা গোল আলো থাকে। সেটা রোজ অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে। অন্তত যতক্ষণ ছাত্রসঙ্ঘের ছেলেমেয়েরা যাতায়াত করে। আজ সেটা জ্বলছে না। উজান সহসা মৈথিলীকে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরল। সে উন্মাদের মতো মৈথিলীর নতমুখের ভেতর ঠোঁট খুঁজছে।
—‘মৈথিলী বল, বল। কখনও কোনদিনও তুই আমায় ছেড়ে যাবি না। এমনিভাবে বরাবর আমার পাশে থাকবি। বল মৈথিল বল।’
মৈথিলী, যে খুব কাণ্ডজ্ঞানের কারবারী বলে খ্যাত, অতি সম্প্রতি তার মা রাধিকা সোরেনের কোনও এক অস্পষ্ট আন্দোলনের জন্য গৃহত্যাগের পটভূমিকায় যে সদ্য সদ্য মাত্রা-ছাড়া আবেগকে তার শরীরে মনে চিনতে শিখেছে, সে যে এমন সর্বাংশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, এমনি করে তার সর্বস্ব দিয়ে সাড়া দেবে সে একমুহূর্ত আগেও বুঝতে পারেনি। উজান তার কথা বলার রন্ধ্র রাখেনি তবু সে অস্ফুট গুঞ্জনের মতো বলতে লাগল —‘কখনও না, কখনও না, নেভ্ভার।’
মেধা দরজা বন্ধ করে নিচের দালানের আলোটা নেভালেন। ছাত্রসঙ্ঘের অফিস ঘরের দরজাটা তালা দিয়ে গেছে মৈথিলী, তিনি আরও একটা তালা লাগালেন। টেনে দেখলেন দুটোই। এখানে শুধু ফাইল ক্যাবিনেট ভর্তি, টেবিল-ভর্তি কাগজপত্র নেই, প্রাথমিক সংগ্রহের টাকাকড়িও ব্যাংকে যাবার আগে পর্যন্ত থাকে। পাতলা পাতলা সিঁড়ির ধাপ। ওঠানামায় শব্দ হয় না। কষ্টও নেই। খুব সহজে উঠে যাওয়া যায়। মেধা ওপরে উঠতে উঠতে ভায়োলিনের ছড়ের শেষ টানটুকু শুনতে পেলেন। টেপটা বন্ধ করে হাত ধুয়ে ফেললেন। প্রেশারকুকারের একটা বাটিতে ভাত। আরেকটাতে চিংড়িমাছের স্টু। ছোট্ট রেফ্রিজারেটরের ভেতর থেকে কাটা শশা, টোম্যাটো বার করে নিলেন। আজকে ভীষণ চিংড়িমাছ খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। মেধার বাবা ছিলেন নিরামিষাশী, মা প্রচণ্ড মৎস্য মাংসবিলাসী। মেধারা ভাইবোনেরা সবকিছুই খেতে শিখেছিলেন। কিন্তু মেধা লক্ষ্য করেছেন তাঁর জিভে কখনও বাবা, কখনও মা প্রবল হয়ে ওঠেন। তিনি আজ বছর পনের হল মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজকে যখন বাজারে চিংড়িমাছ দেখে হঠাৎ খেতে ইচ্ছে হল, তিনি নিজেকে না করলেন না। বাইরে থেকে চাপানো কোনও ত্যাগে বা ভোগে তিনি বিশ্বাস করেন না। মাংস সম্পর্কে তাঁর বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একটা বিতৃষ্ণা আছে। কিন্তু মাছ সম্পর্কেও যখন সেটা দেখা দিল, তিনি সেটাকে মেনে নিয়েছিলেন। আজ মনে হচ্ছে তাঁর খাদ্যরুচি আবার একটু পালটেছে। ছেলেমেয়েগুলো রোজ রোজ আসে, খাটে। ওদেরও শীগগীরই একদিন চিংড়িমাছের স্টু খাওয়াতে হবে। এই বিলাসিতা হয়ত বছরে একবার কি দুবার। একশ পঞ্চাশ টাকার চিংড়িমাছ তৃতীয়বার খাবার সাধ নেই তার। সাধ্য আছে। সাধ নেই।
আজকের দিনটা অদ্ভুত একটা দিব্য প্রশান্তির। আনন্দময়, স্বর্গীয়। শিশিরকণা ধরচৌধুরীর এই হংসধ্বনির টেপ এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের। মধুচ্ছন্দার কাছ থেকে পেয়েছেন। পশ্চিমের ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিখ্যাত কম্পাোজারদের সৃষ্টি স্বরলিপিতে ধরা থাকে। দেখে দেখে ওস্তাদ বাজিয়েরা বাজিয়ে যেতে পারবেন চিরদিন। কিন্তু এই প্রাচ্য শিল্পীরা প্রত্যেকেই সৃজন করছেন, প্রতিবারই। ঠিক এই হংসধ্বনি হয়ত ইনিও আর দ্বিতীয়বার বাজাবেন না। মহাকালের সময়সূত্রে প্রতিটি খণ্ড মুহূর্ত যেমন অনন্য এই সংগীতও তেমনি। সৃষ্টি এবং লয়। স্থিতি যদি কোথাও থাকে তবে দুচার জন শ্রোতার স্মৃতির মধ্যে আনন্দসার হয়ে থাকবে। বিশদ বৃত্তান্ত বা ডিটেল যাবে হারিয়ে, শুধু একটা অতুলনীয় উদ্বর্তনের আমেজ হয়ে থাকবে বহুকাল। চিরকাল কি?
মেধার একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে যা দিয়ে তিনি অনেক কিছু না বলা জিনিস চট করে বুঝে ফেলেন। সব সময়েই যে এ ক্ষমতাটা কাজ করে তা কিন্তু না। আজ করেছিল। বেহালা শুনতে শুনতে তাঁর মনে হল মৈথিলী আর উজান এসে দাঁড়িয়েছে। যেন হংসধ্বনির বাদী আর সম্বাদী। ওরা তাঁকে না ডেকে নিচে নেমে গেল। বেহালার ছড়ের হৃদয়মন্থন করা টানগুলো ভেদ করে নিজের অন্তরের মধ্যে কোথাও তিনি ওদের গুন গুন শুনতে পাচ্ছিলেন। বাড়ির নিচেটা একদম নির্জন, কেউ কোথাও নেই। শুধু মৈথিলী আর উজান। মেধার হঠাৎ মনে হল তিনি যেন কোনও তুঙ্গ মুহূর্তের সামনে দাঁড়িয়ে। এখুনি কিছু একটা ফেটে পড়বে। মেঘের বুকে আগুন বজ্রনির্ঘোষে এখুনি সব ফালাফালা করে দেবে। কিম্বা মেঘের অভ্যন্তরের শুদ্ধ জলের সঞ্চয় ভেঙে পড়বে প্রলয় বাদলে। তিনি ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেলেন। ওদের কোনও ক্ষতি না হয়। জীবনকে এইরকম তুঙ্গ মুহূর্তের কাছে সমর্পণ করার আনন্দ যত, বেদনা তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি। ইদ্রিস আমেদ না বলতে পারেন—‘আমার নাতিটারে ভুলাইছিস ধিঙ্গি।’ রঘুনন্দন ত্রিপাঠী না ব্যথিত বিস্ময়ে তাকান ‘মেধা আমি তোমার কাছে মেয়েটাকে রেখে নিশ্চিন্ত ছিলাম। তুমি তো কখনও সন্তান গর্ভে ধারণ করোনি তুমি কিইবা বুঝবে?’ তিনি দেখতে পাচ্ছেন উজান উদ্যত, মৈথিলী উন্মুখ। ওরা কি নীল শূন্যে সোনালি ঈগলের মতো পাখসাটে পাখসাটে ভালোবাসাবাসি করবে?
রোকেয়া! আহা রোকেয়া। সে নিজেও কি জানত অমিয় নাথ সান্যালকে সে কী তীব্রভাবে চেয়েছিল। বিপ্লবের সঙ্গিনী, সহধর্মিণী হতে তিনি তাকে ডেকেছিলেন। সেই নীরক্ত, অ-ব্যক্তিগত, পরার্থে উৎসর্গিত ডাক রাকেয়া ফিরিয়ে দিয়েছিল বিপুল অভিমানে। জীবনকে নিয়ে সে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল। অনেক কিছু দেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে যখন তৃপ্ত হয়, একমাত্র তখনই বোধহয় মানুষের বহুর জন্য প্রাণভরে জীবন উৎসর্গ করার ক্ষমতা আসে। শুধু আদর্শবাদের সাধ্য নেই রক্তমাংসে গড়া, ঈশ্বরের মতো নিয়ত-সৃজনশীল মানুষকে বরাবরের জন্য তৃপ্ত রাখে। কে জানে এও আবার সেই নিরর্থক সামান্যকরণ কিনা, যার থেকে পৃথিবীর একটার পর একটা অনমনীয় তত্ত্ব তৈরি হয়েছে। রোকেয়া বলেনি, কিন্তু ক্যালিফর্নিয়া সিটিতে তাকে দেখবার পর মেধা একেবারে পুরোপুরি নিশ্চিত যে রোকেয়া অভিমানে কঠিন, কঠোর, নিঠুর হয়ে গেছে। মেধার দিক থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, দেশ এবং দেশের জন্য সমস্ত ভাবনা-চিন্তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, শুদ্ধু অমিয়নাথ তাকে ঠিক সময়ে ঠিক সুরে ডাকলেন না বলে।
রোকেয়ার শহরতলির বাড়ির সামনে মস্ত ফুলের বাগান। লম্বা রাস্তা, দুপাশে ফুল, তার ওদিকে সবুজ লন। আমেরিকার সবুজ দেখে অনেক সময় সন্দেহ হয়, এতো সবুজ, এত সতেজ, এসব কৃত্রিম নয় তো!
রবিবারের সকাল। মেধা তার নতুন টয়োটা নিয়ে ঢুকছে। সে তার নিজের সমস্ত অভিমান জয় করেছে। খবর নিয়েছে রোকেয়া বাড়ি থাকবে। যদিও তাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি সে আসছে। লম্বা নীল স্কার্ট পরা একটি মহিলা লনের ওপর পাতা হালকা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। একটা কোল-কুকুর লুটোপুটি খেতে খেতে ছুটে আসছে। রোকেয়া অনেক মোটা হয়ে গেছে, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল। চকচকে শ্যাম রং ছিল ওর। তাতে এখন রক্তাভা। রক্তমুখী নীলা। চুল ছোট, সযত্নে সেট করা, কত অন্যরকম দেখাচ্ছে ওকে। মেধা নামছে। রোকেয়া এগিয়ে আসছে—‘হাই।’ সারা জীবনে বাবা মা ভাই বোন ছাড়া একমাত্র রোকেয়ার সঙ্গেই তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দুজনে পাশাপাশি জড়াজড়ি করে শুয়ে গল্প করা এ-ওর বুকে, মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ার সম্পর্ক। লুকু আর মুন্নির মতো।
মেধা তখন সবে ওদেশে গেছে। অত সহজে অনুনাসিক স্বরে ‘হা-ই’ বলতে পারল না।
—‘মেধা।’ এগিয়ে এসে হাত দুটো ধরেছে রোকেয়া ‘তুমি কবে এলে।’
—‘এসেছি বছর খানেক হয়ে গেল।’
রোকেয়ার স্বরে অভ্যর্থনা নেই। মুখের বিস্মিত হাসিটুকুও মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রোকেয়ার থেকে তার স্বামী রজ্জাক অনেক উৎসাহী, উচ্ছ্বসিত।
—‘ওহো। মেধা ভাটনগর! সেই কলকাতার মেধা! বৈঠকখানা রোডের ঠিকানায় কাঠ-দুপুরে সাদী মনে আছে মেধা? আপনার কনুই দিয়ে বিরিয়ানির ঘি নামছিল, গোস্তের সাইজ দেখে ভিরমি যাচ্ছিলেন। ইদ্রিসসায়েব সেই হুজ্জোতির সাদীতে বিরিয়ানি আর ফিরনি বাদে কিসসু করেন নাই। হা, হা, হা, খুব সংকট যায় সেদিন আপনার, খু-উ-ব। উঃ কত্তকাল পর। রোকেয়া ছিল না এমন একটা জীবন ছিল ভুলেই মেরে দিচ্ছি।’
রাতে ঘরে গুড-নাইট জানাতে এলো রোকেয়া। তার ফুলের মতো ছেলে মেয়ে দুটি আগেই গুডনাইট জানিয়ে গেছে।
রোকেয়া বলল—‘হ্যাভ আ গুড স্লীপ মেধা।’ তারপর একটু থেমে বলল—‘হাউ ডু য়ু ফাইন্ড হিম?’
—‘কাকে? রজ্জাককে? চমৎকার।’
—‘আ হানড্রেড টাইমস বেটার।’ রোকেয়া কঠিন মুখে বলল।
কার সঙ্গে তুলনাটা করছে মেধা বুঝতে পারছিস না। এক ঝলকেই বুঝতে পারল কার সঙ্গে তুলনা, কেন তুলনা। বুঝতে পারল সঙ্গে সঙ্গে রোকেয়াকেও। এতদিন পর।
কিন্তু রোকেয়াই কি অমিয় সান্যালকে ঠিকঠাক বুঝেছিল? মেধার সঙ্গে তাঁর যে বিয়েটা হয়েছিল সেটা তো নেহাতই কাগজের বিয়ে। আস্তে আস্তে তাই সেটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে চলে গেল। রোকেয়া বোধহয় ঠিক বোঝেনি। নৈর্ব্যক্তিক সমস্যাগুলো ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সঙ্গে যখন এমন পাকে পাকে জড়িয়ে যায় তখন কী জটিল হয়ে দাঁড়ায় জীবন। কী ভয়ঙ্কর দুর্বিপাক তখন। সান্যালদা যে চট করে আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলেন, গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন, সে কি খানিকটা ইচ্ছে করেই? মেধা যেন এতদিন পর সান্যালদার সেই ধারাল, তেজস্বী নৈর্ব্যক্তিক মুখখানার ভেতর তাঁর আসল মুখটা দেখতে পেল। মুখটা ভেঙে চুরে যাচ্ছে, মেধার স্মৃতিহর্ম্যের মণিকুট্টিমে ভাঙা আয়নার মুখের মতো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।
মেধার সব স্বপ্ন জাগা স্বপ্ন। ঘুমিয়ে তিনি সাধারণত স্বপ্ন দেখেন না। আজ কেন কে জানে ঘুমোতে যাবার আগে বারবার মনে হতে লাগল দেবপ্রিয় অনেক দিন আসেনি। আসে না কেন? তিনি সবসময়েই নিজেকে খানিকটা নির্লিপ্ত নিরাসক্ত রাখতে চান। ছাত্রসংঘের পরিকল্পনা তাঁর নয়। মৈথিলীর। কিন্তু সেটাকে আরও ব্যাপক আরও অর্থময় এবং সফল করতে যা যা করা দরকার সবই তিনি করেছেন। এখন বৃহত্তর কলকাতার হেন কলেজ বা য়ুনিভার্সিটি নেই যেখানে ছাত্রসঙ্ঘের সাধারণ সদস্য নেই। গঞ্জ ও গ্রামাঞ্চলের কলেজ থেকেও সদস্য নেওয়া শুরু হয়েছে। এ বছর সংখ্যাটা লাখ ছাড়িয়ে গেছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা এরা সব ঘুমন্ত সদস্য নয়। মৈথিলী আজকাল তিন চারটে শাখায় ভাগ করে দিয়েছে সঙ্ঘকে। প্রত্যেকটি শাখার আলাদা কর্মনির্বাহক সমিতি যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি এখনও পর্যন্ত খুবই সক্রিয় আছে। যাই হোক এক ফলে ছাত্রসঙঘ কাজ করছে খুব দ্রুত লয়ে। কিন্তু দেবপ্রিয় নীরবে এই ছাত্রসঙঘ থেকে সরে যাচ্ছে, এটা তাঁর ভালো লাগে না। অন্য কেউ ছেড়ে দিলে তিনি ততটা গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু দেবপ্রিয় ছেড়ে দিলে যেন ছাত্রসঙ্ঘকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয়। যে জিনিস সব প্রতিষ্ঠানকে ভাঙে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই তো এর ভেতরে? সেরকম কিছু হলে মৈথিলী অন্তত তাঁকে জানাত। এই ধরনের চিন্তা করতে করতে মেধা শুয়েছিলেন। একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন : তিনি যেন গর্ভবতী হয়েছেন। বিশাল গর্ভ, নড়তে চড়তে পারছেন না। তারপর হঠাৎ কি করে সেই গর্ভ হালকা হয়ে গেল, দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে একটি দশ বারো বছরের বালক। স্বপ্নে যার মুখ স্পষ্ট নয়। কারা যেন বলছে ‘বাপরে! এত বড় ছেলে হয়েছে? অস্ট্রেলিয়ায় দেখেছি চার পাঁচ বছরের পর্যন্ত হয়। কিন্তু একেবারে দশ-এগার?’ স্বপ্নের মধ্যে মেধার চেতনা আছে। ছেলেটা দেবপ্রিয়। যদিও আসল দেবপ্রিয়র সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র মিল নেই। তিনি যেন ছেলেটিকে ডাকছেন, সে খালি পালিয়ে যাচ্ছে, তাঁর বুক টনটন করছে, দুধ ঝরে পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে শরীর। এইরকম অবস্থায় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কখন বিদ্যুৎ চলে গেছে। ঘামে ভিজে গেছে সব। দুর্দান্ত গুমোট গেছে রাত্তিরে। বুকে এখনও ব্যথা করছে। হাতের মুঠিটা বুকের মধ্যে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন। আস্তে আস্তে হাতটাকে মুক্ত করলেন মেধা।
এখন আলো ফোটেনি। তবে এইবারে ফুটবে। দু একটা পাখির ডাক হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে, সেইসব বিরল চক্ষুষ্মান পাখি যারা অন্ধকারেও আলো দেখতে পায়। মহাজ্যোতিষ্ক সূর্য থেকে যখন পৃথিবীর সৃষ্টি তখন আলো ছিল না এমন দিন নিশ্চয়ই ছিল না। বাইবেল যতই বলুক ‘ডার্কনেস ওয়াজ আপন দা ফেস অফ দা ডীপ’। অন্ধকার আসে একটা নিয়মিত ছন্দে। প্রকৃতির জীবনে যেমনি মানুষের জীবনেও তেমনি। মানুষের জীবনে এই ছন্দটা অন্যরকম, এখনও কেউ বার করতে পারেনি এর সূক্ষ্ম হিসেব নিকেশ। জ্যোতিষশাস্ত্র খানিকটা চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। প্রকৃতি সচল হলেও নিয়মে বাঁধা। মানুষ এবং তার ঘাত-প্রতিঘাতে উৎপন্ন জীবন এতো জটিল যে সেই জীবনে আলো-অন্ধকারের যাওয়া আসার ছন্দ আবিষ্কার করা অতি দুঃসাধ্য কাজ।
ভোরের আলো-আঁধারির মধ্যে দিয়ে আকাশি-নীল রাতপোশাক পরে মেধা ছাতে উঠে গেলেন। হঠাৎ সূর্য-ওঠা দেখতে ইচ্ছে হল তাঁর একেবারে প্রথম আদি লগ্ন থেকে। কিছু বহুতল বাড়ির দৈর্ঘ্য দৃষ্টির গতি থামিয়ে দিচ্ছে, পূর্ব দিগন্তকে সোজাসুজি দেখা যায় না আর। কিন্তু সেই বহুতলের আশপাশ থেকে তিনি বিকীর্ণ হয়ে পড়তে দেখলেন সূর্যকে। স্বয়ং সূর্য হৰ্ম্য শিখরের আড়ালে। কিন্তু তার আলোর ছটা পূর্ব আকাশটাকে বিদীর্ণ করে দীপ্যমান। কাঞ্চনজঙ্ঘার পেছন থেকে যখন সূর্য ওঠে তখনও খানিকটা এইরকমই দেখায়। বরফে সেখানে রঙের খেলাটা জমে। এখানে বরফ নেই, শুধু ইঁট কাঠের প্রতিফলন ক্ষমতা নেই, তাই সূর্যকে তার ঐশ্বর্য সংবরণ করে নিতে হয়েছে।
ছাতে কয়েকটা গাছ। ছাতের ট্যাংকের কল থেকে জল ভরে সেগুলোকে স্নান করালেন মেধা। কাজটা করতে করতেই তাঁর শরীর মন টান টান হয়ে উঠল। কোথাও যেন ফোন বাজছে। কার বাড়িতে? এতো ভোরে? তাঁর বাড়িতে? হ্যাঁ, তাঁর বাড়িতেই। মেধা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলেন। ফোনটা একবার স্তব্ধ হয়ে গেল, আবার ঝনঝন করে বেজে উঠল একটু পরেই।
—‘মেধা ভাটনগর বলছি।’
—‘দিদি, আমি উজান। দেবপ্রিয়কে পুলিস অ্যারেস্ট করেছে।’
—‘সেকি? কেন? করে?’
—‘আমি আসছি। পাঁচ মিনিট।’
ফোনটা নামিয়ে রেখে মেধা শাড়ি পরে নিলেন। একেবারে প্রস্তুত। যে কোনও সময়ে যে কোনও জায়গায় আবার ডাক আসলে তিনি শতকরা শতভাগ প্রস্তুত। চুল আঁচড়ে নতুন করে বিনুনি বাঁধলেন। সদর দরজাটা খুলে নেমে গেলেন তাঁর ছোট্ট রুমালের মতো লনে। ছোট ছোট ফুলগাছগুলো উন্মুখ, তৃষিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। ওদের চাহিদা সামান্যই। আহা! তিনি জীবনের জটিল পদক্ষেপে বিচলিত বলে ওরা সেই সামান্যটুকু থেকে বঞ্চিত হবে কেন? মেধা জলের ঝারিটা নিয়ে এলেন।
উজান সাইকেল নিয়ে ঢুকছে। যোধপুর পার্ক থেকে ফার্ন প্লেস কতটুকুই বা! মেধা কিছু বলছেন না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শুধু।
অধ্যায় : ১৬
লুকুর দিনগুলো ভারহীন, হালকা কাটছে। পাখির মতো উড়ানে মত্ত, কিংবা মাছের মতো সাঁতারে সমর্পিত। এম এ পার্ট ওয়ানটা দেবার পরই সে গুঞ্জনের পরামর্শে একটা বিউটিশিয়ানস কোর্স নিয়ে নিয়েছিল। কিছু কিছু মডেলিং শুরু করেছে আবার। ভালো টাকা রোজগার করছে লুকু। ভাইয়ার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছে পার্কে গিয়ে। আরও কিছু কিছু পাড়ার বন্ধুরা আসে। তাদের অনেককেই অবশৎ সে পছন্দ করে না। কিন্তু খেলার মধ্যে দিয়ে সম্পর্কটা ভালোই থাকে।
বিশ্বজিৎ মজুমদারের সবচেয়ে স্বস্তির কারণ লুকু আজকাল আর ঝড়ুর ওপর নির্ভর করছে না। সংসারের যে জায়গায় তার মা ছিল, সেখানে সে ক্রমশই খাপে খাপে বসে যাচ্ছে। একটি গভীরভাবে জীবনাসক্ত মানুষ যেদিন দুমাসের মধ্যে জরায়ুর ক্যানসারে মারা গেল সেদিন নিজের কষ্টের চেয়েও তাঁর বিপদ হয়েছিল দুটি ছেলেমেয়ে, বিশেষ করে লুকুকে নিয়ে। তিনি বেসরকারী ফার্মের এগজিকিউটিভ। তাঁকে কিছু কিছু ওপরমহলের এবং ইউনিয়নের চাপ সামলে চলতে হয়। এই ব্যালান্স রাখার কাজটার জন্য তাঁর নিজের মানসিক ও পারিবারিক সুস্থিতি বজায় থাকাটা ভীষণ জরুরি। স্ত্রীর অসুখে প্রচুর ছুটি ঋণ ইত্যাদি হয়ে গেছে। অফিস থেকে অনেকটাই পান। তবু আরও নিতে হয়েছিল। এখন খুব খাটতে হচ্ছে। এদিকে বাড়িতে লুকু ওইরকম। তিনি বুঝতে পারছেন লুকু স্মোক করছে, ঝগড়াঝাঁটি করছে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, কেঁদে-কেটে আধা-অচেতন হয়ে যাচ্ছে সময়ে সময়ে। ভালো সাঁইকিয়ট্রিস্ট দেখালেন। সে ভদ্রলোক এতো ট্র্যাংকুইলাইজার দিলেন যে খেতে খেতে লুকুর প্রায় জীবন্মৃত অবস্থা। শেষ পর্যন্ত ওষুধগুলোকে নিজেই টান মেরে ফেলে দিল ও। ছাত্রসঙ্ঘের কাজ-কর্ম করে, মেধা ভাটনগরের বাড়িতে গিয়ে মেয়েটা ভালো আছে। তারপর একটি ছেলে আজকাল প্রায়ই আসছে। দুজনে একসঙ্গে কি পড়াশোনা করে ওরাই জানে। তবে লুকু যে অধীর আগ্রহে ছেলেটির জন্যে অপেক্ষা করে এটা তাঁর চোখ এড়ায়নি। ছেলেটি অমিশুক। তাঁর ছেলে জয়দীপের সঙ্গেও বিশেষ মেলামেশা করে না। তাঁর সঙ্গে একটা বিনীত দূরত্ব রাখে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এই ছেলেটি বড় উদাসীন, অন্যমনস্ক। কে জানে ও দায়িত্ব নিয়ে মেলামেশা করছে কিনা। লুকুর অন্যান্য বন্ধু উজান আফতাব, প্রমিত, বুল্টু এরা খুব স্মার্ট। এদের বেশি পছন্দ করেন বিশ্বজিৎ মজুমদার। এই ছেলেটিকে ঠিক মফঃস্বলী বলতে দ্বিধা হয়, চকচকে পালিশ না থাকলেও এর ভেতরে কোথাও একটা অনমনীয় সপ্রতিভতা আছে। সেটা তিনি দু একবার কথা বলে বুঝতে পেরেছেন। ডাক্তার হতে যাচ্ছে। সার্জারিতে নাকি অসামান্য হাত। মৈথিলী বলছিল। ভালো। ভালো হলেই ভালো। কোনও নিশ্চিন্ততা যেন ওপরঅলার চোখে না ঠেকে।
জীবনটা তো নিশ্চিন্ত, সুখী সুন্দরই ছিল। মঞ্জুশ্রী ছিল একটা তাজা চন্দ্রমল্লিকা ফুলের মতো। চটপট কাজ করে ফেলছে। এই বাজার-হাট করে এলো। তারপরেই বসবার ঘরের যাবতীয় সাজ-সজ্জা একটু এদিক-ওদিক করে পাল্টে ফেলল। পরক্ষণেই ফোন করে শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ির ডজনখানেক আত্মীয়স্বজনের খোঁজ নিয়ে ফেলল। লম্বা চুলগুলোকে একদিন ছেঁটে-ছুঁটে কুঁকড়ে ফিরে এলো—কি ব্যাপার? না, তোমায় অবাক করে দেবো।’
—‘আমায় না অন্য কাউকে?’
মঞ্জুর সে কী হাসি। বললে ‘সে তো আছেই। অন্যদের মুণ্ডু তো আকচার ঘোরাচ্ছিই। তুমি উনিশ বছর দেখে দেখে আজকাল একটু আসবাবপত্রের মতো দেখতে আরম্ভ করেছ আমাকে টের পাচ্ছি। তাই একটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম।
—‘তুমি কি সত্যি ভেবেছ নাকি চুল-টুল ছেঁটে নিজেকে আমার কাছে নতুন করবে? হোয়াট ননসেন্স?’
—‘তাহলে কি পুরো চরিত্রটাই পাল্টে ফেলতে হবে? এবার থেকে তাহলে ন্যাগিং ওয়াইফ হই?’
—‘ওরে বাবা, রক্ষা করো।’
এসব কথা বাড়তে দিতেন না কখনও বিশ্বজিৎ। গুরুত্ব দিতেন না। এখন অতীতের কথা মনে করলে বুঝতে পারেন মেয়েরা সবসময়ে প্রিয়জনের মনোযোগ চায়। বয়সটা কোনও ব্যাপার নয়। সব বয়সে, সব অবস্থায় তারা মনোযোগ চায়। দীর্ঘদিন দাম্পত্য-সুখের পর পুরুষদের আসে একটা নিশ্চিন্ততা, প্রশান্তি। কেজো জগতের দিকে মন ফিরে যায়। তার অর্থ এই নয় যে ভালোবাসার খাতে কিছু কম পড়ল। তার চেহারাটা একটু পাল্টে গেল শুধু। এটা মেয়েরা সইতে পারে না। অন্তত মঞ্জুশ্রী পারত না। প্রথম দিনের উচ্ছ্বাস, প্রথম যুগের মনোযোগ তাদের সারা জীবন চাই। তা নয়ত তারা ফুলের মতো ফুটে থাকবে না। তাদের কাজকর্মে আর ছন্দ আসবে না, জীবনযাপন থেকে লাবণ্য অন্তর্হিত হবে। যখন পেটে ব্যথা পেটে ব্যথা করে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, ডাক্তার দেখিয়ে ধরা পড়ল কুসুমে কীট প্রবেশ করেছে, তখন বিশ্বজিৎ দিশেহারা, ছুটি নিচ্ছেন, নার্সিং হোমে কাটাচ্ছেন প্রায় সব সময়ে, কি পেলে মঞ্জুশ্রী খুশী হয়, ফুল, চকোলেট, নিয়ে ছুটে ছুটে যাচ্ছেন, ব্যাকুল চোখ সবসময়ে তার মুখের ওপর স্থির—কী খুশি মঞ্জুশ্রী। লুকুকে রোগশয্যা থেকেই শেখাচ্ছে গাৰ্হস্থ্যের নানান খুঁটিনাটি। খেয়াল নেই সে একটা বালিকা, মায়ের অভাবনীয় অসুখে তার সুখের দুর্গ ভেঙে পড়েছে। মঞ্জুশ্রীর মতো প্রাণবন্ত, জীবনের প্রতি ভালোবাসায় নিবেদিত বিচিত্ররূপা রমণী যদি ভেতরে আসন্ন মৃত্যুর বীজ বহন করতে পারে তো প্রকৃতির দ্বারা সবই সম্ভব। বিশ্বজিৎ খুব সন্তর্পণে বাঁচেন। লুকুর মুখে হাসি ফুটেছে তিনি খুব খুশী। কিন্তু খুশীটা আদৌ প্রকাশ করেন না।
এ শনিবার দেব এলো না। গ্রীক সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে হয় লুকুদের। দেব বলেছিল বাছা বাছা কয়েকটা গ্রীক ট্রাজেডি পড়বে। ওরা সোফোক্লিসের ‘ইলেকট্রা’ পড়ে ফেলেছে। এখন শুরু করেছে ইউরিপিদিসের ‘মিডিয়া’। আজকে হয়ত সেটা শেষ হয়ে যেত। দেব কোথাও আটকে গেছে, আসতে পারল না। ও আজকাল ছাত্র পড়াচ্ছে। ছাত্রর পরীক্ষা-টরীক্ষা না কি? কিছু তো বলেনি। সন্ধেবেলা বাপী ফিরলে লুকু জলখাবার এনে দিল, বাপীর ঘরে।
বিশ্বজিৎ বললেন—‘কি রে, দেবপ্রিয় আসেনি?’
—‘না বাপী। আজকে কিন্তু তোমাকেই আমার সঙ্গে ‘মিডিয়া’ পড়তে হবে।’
—‘আমাকে? মিডিয়া? সেকি?’ বিশ্বজিৎ জীবনে কখনও মিডিয়া নাটকের নাম শোনেননি।
—‘কেন বাপী, নাটক হয়েছে তো মিডিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দেখোনি? খেয়াল করোনি?
—‘কই না তো।’
—‘তোমাকে আমার সঙ্গে ওটা পড়তেই হবে।’
বিশ্বজিৎ প্রচুর গাঁইগুঁই করেও সুবিধে করতে পারেন না। তাঁকে বসতে হয়। তবু রক্ষা যে লুকু আবার গোড়ার থেকে শুরু করেনি। সে অনেকটা অংশই গল্পটা বলে দিল। পড়া-টড়া শেষ করে বিশ্বজিৎ বললেন—‘এতো একেবারে বর্বর কাহিনী রে। গ্রীকরা এরকম বর্বর ছিল?’
লুকু হেসে কুটিপাটি। বলল—‘সবাই তো একদিন বর্বর ছিল। গ্রীকরা সভ্যশান্ত হবার অনেক আগেকার পুরাণ কথা এসব। আমাদের যেরকম শুনঃসেফের কাহিনীটা আছে! জমদগ্নি, রেণুকা পরশুরামের গল্প আছে! সেইরকম। শুনঃসেফের কাহিনীটাই কি বর্বর ধরো না। রাজপুত্র রোহিত নিজের বিকল্প হিসেবে গরিবের ছেলেকে বরুণ দেবতার কাছে বলি দিতে চাইলেন। বাবা বললে বড়টিকে দেবো না, মা বললে ছোটটিকে দেবো না। মেজোটাকে দিতে দুজনেই রাজি হয়ে গেল। রাজা নিশ্চয়ই অনেক ধনরত্ন দিলেন। শুনঃসেফ বরুণের স্তব করতে তিনি তাকে অব্যাহতি দিলেন। পরশুরামের গল্পটা তো আরও বীভৎস। রামের দ্বন্দ্ব তিনি বাবার কথা শুনবেন না মার প্রাণ রাখবেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ন্যায় অন্যায়ের ধারণা সাঙ্ঘাতিক রিজিড, প্রো-ফাদার, তাই তিনি মাকে হত্যা করলেন।’
—‘কিন্তু সেই মা আবার জমদাগ্নির বরে বেঁচে উঠলেন তো!’
—‘বেঁচে ওঠা কি সম্ভব বাপী? আর যে ভদ্রলোক অনায়াসে স্ত্রীকে মারবার হুকুম ছেলেকে দিতে পারেন, তাঁর কাছে আর কোনও প্রতিভা ঘেঁষতে পারে বলে মনে হয় না। এইসব বর্বর কাহিনীগুলোতে অলৌকিকের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। গ্রীক পুরাণের গল্পও তো আছে—ট্রয়যুদ্ধে জয়ের জন্য মানসিক করে আর্গস-এর রাজা আগামেমনন তাঁর মেয়ে ইফিজিনিয়াকে দেবী আর্তেমিসের কাছে বলি দিয়েছিলেন। সে মেয়ে নাকি আদৌ বলি হয়নি। আর্তেমিস মায়ার সৃষ্টি করে তাকে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। আচ্ছা বলো একি সত্যি হতে পারে? আসলে, দেবী নিজের প্রসন্নতার জন্য কারো রক্ত চাইছেন এই বিসদৃশ ব্যাপারটা পুরাণকারদের নিশ্চয়ই খারাপ লাগত, তাই তাঁরা কৌশলে ইফিজিনিয়াকে বাঁচিয়ে দিলেন। পেছনে আছে সেই নরবলি, কুমারীবলির বীভৎস রীতিনীতির দিনগুলো।’
বিশ্বজিৎ বললেন—‘বাইবেলের আব্রাহাম আইজাকের গল্পটাও তো সিমিলার রে। আব্রাহাম ছেলে আইজাককে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছেন ঈশ্বরের আদেশে, ঠিক শেষ মুহূর্তে ঝোপের মধ্যে ঈশ্বর আবির্ভূত হলেন। তিনি আব্রাহামকে নিরস্ত করলেন। শুনঃসেফ আব্রাহাম আইজাক আর তোর আগামেমননের গল্পের মধ্যে প্রচুর মিল।’
—বাইবেলের গল্পে আসল সত্যটা তাহলে কি বলো তো বাপী।’
—‘তোর মত অনুসরণ করলে বলতে হয় আব্রাহামের পিতৃহৃদয় জেগে উঠল, তিনি ছেলেকে শেষ পর্যন্ত বলি দিতে পারলেন না। তাঁর হৃদয়ই যেহোভার কণ্ঠ হয়ে তাঁকে বারুণ করল।’
—ওয়াণ্ডারফুল। বাপী ওয়াণ্ডারফুল! তুমি একদম দেবের মতো করে বললে।
বিশ্বজিতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। ছেলেমেয়ে এরা নতুন প্রজন্ম। এদের হাতে বাবা মারা বড়ই নাকাল হন। এরা হয় অনেক বেশি জানে। তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয় সব কিছু নয় তো বড্ড নির্ভর করে। নতুন প্রজন্মের কাছে বাহবা পেয়ে বালকের মতো খুশি হয়ে গেলেন তিনি। মঞ্জুশ্রীর মৃত্যুর পর থেকে তাঁকে বাহবা দেবার, সাহস দেবার কেউ নেই। তিনি কখন নিজের অজান্তেই ছেলে মেয়ের ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছেন। তিনি বললেন—‘দেবপ্রিয় এইসবই বলে নাকি?’
—‘হ্যাঁ বাপী আমি আগে কখনও ঠিক এইভাবে ভাবিনি। মেধাদি ক্লাসে কিছু কিছু বলতেন বটে, কিন্তু সপ্তাহে ওঁর মোটে একটা ক্লাস ছিল। শুনতাম, ভালো লাগত, তারপর আমার স্বভাব জানো তো। ভুলে যেতাম। দেব নিয়মিত আসে। আমার সঙ্গে পড়ে এইভাবে আলোচনা করে, আমার এতো ভালো লাগে যে কী বলব। তুমিও থাকো না কেন বাপী। তুমি মনে করো…আমরা বিরক্ত হবো, না?’ লুকু দুষ্টু হাসি হাসছে।
বিশ্বজিৎ বললেন—‘না, হ্যাঁ, তা…’
—‘আমতা আমতা করছো কেন? তোমার ধারণা কি আমি জানি।’ বলে লুকু ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, ‘আমি ঠিক করেছি এম এর পর মিথ নিয়ে রিসার্চ করবো। এইসব বর্বর যুগের মিথ। আমি দেখাবো বাপী আমাদের এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগেও আমরা কিরকম বর্বর রয়ে গেছি। কোনও কোনও সমাজে খোলাখুলি চলছে এইসব। কিন্তু সভ্য সমাজেও নরবলির ইনসটিংট, ভাগ্যকে যে কোনও মূল্যে খুশি করার ইনসটিংট এখনও কি প্রবলভাবে কাজ করে যাচ্ছে।’
বিশ্বজিৎ বললেন—‘তবে তো তুই তোর লাইন পেয়েই গেছিস। মনে আছে তোকে হিসট্রি পড়তে জোর করেছিল কে! তুই তো সায়েন্স পাবো না, সায়েন্স পাবোনা করে দাপাদাপি আরম্ভ করেছিলি।
…হ্যাঁরে লুকু’ বিশ্বজিৎ একটু নিচু গলায় ভিতু ভিতু স্বরে বললেন, ‘তুই স্মোক করিস?’
লুকুর মুখটা সাদা হয়ে গেল। মায়ের মৃত্যুর আগে বাপী ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাবা। গোটা সংসারটা চলত বাপীকে খুশি করবার জন্য। বাপীর ওয়ার্ডরোব, বাপীর স্যুট, জুতো সব ঠিকঠাক ঝকঝকে চকচকে থাকা চাই। বাপী যখন বাড়ি ফিরবে, কোনও গোলমাল চলবে না। যখন অফিস যাবে জয় যদি ‘দুঁধ খাঁবো না’ বলে নাকি কান্না ধরে সে প্রচণ্ড একটা ধমক খাবে। মা চলে যাবার পর বাপীর সমস্ত প্রকৃতি থেকে সেই প্রতাপের খোলস একটু একটু করে খসে পড়ছে। ভিতু ভিতু স্বরে বাপী বলছে ‘লুকু তুই স্মোক করিস?’ আগে হলে বাপী বলত ‘মঞ্জু ওকে ধরে আনো, ধরে আনো তো আমার সামনে। হাঁ কর দেখি, এত বড় স্পর্ধা…বিশ্বজিৎ মজুমদারের মেয়ে হয়ে তুমি….দাঁড়াও তোমার উপযুক্ত সাজা আমি বার করছি।’ এখন বাপী কুণ্ঠিত। যেন মাফ-চাওয়া স্বরে জানতে চাইছে ‘লুকু তুই স্মোক করিস?’ প্রশ্নটা নিশ্চয়ই বাপীর মনের মধ্যে অনেক দিন ধরে ঘোরাফেরা করছে। লুকুর মরিয়া ভাব, যখন তখন হিস্টিরিক হয়ে যাওয়া এসব কারণে বাপী প্রশ্নটা করেনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দুশ্চিন্তায় খুব কষ্ট পেয়েছে। খুব। লুকুর ভীষণ মায়া হল। সে টেবিলের ওপর কনুই রেখে বলল—‘বাপী তুমি কি করে বুঝলে?’
বিশ্বজিৎ বললেন, ‘আমাকে তোরা যতটা বোকা ভাবিস, ততটা বোকা আমি নই রে! আমি সিগারেট গুনে গেঁথে খাই, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যদি আমার প্যাকেট ফুরিয়ে যায়, আমি জানবো না? জয় আমার পাশে শোয়, ওর জামা কাপড়ে আমি গন্ধ পাই না। তোর ওয়ার্ডরোব খুললেই…ক্যাপস্টানের কড়া গন্ধ তুই লুকোবি কোথায়? লুকু প্লীজ, স্মোক করিস না।’
লুকু বলল—‘কেন বাবা, আজকাল ফ্যাশনেব্ল্ মেয়েরা তো অনেকেই স্মোক করে। তোমার বস মিঃ সুদের স্ত্রী সন্তোষ সুদের ছবি দেখেছি কতো সিগারেট ঠোঁটে। বিদেশে তো অনেকদিন চালু। এদেশেও নবাব-টবাবদের বেগমরা রীতিমতো স্মোক করত, জানো?’
বিশ্বজিৎ বললেন—‘যে যেখানে যাই করুক, অভ্যেসটা ভালো নয় এটা তো স্বীকার করবি? তোর মত বাচ্চা মেয়েকে একেবারেই মানায় না।’
লুকু বলল—‘বাপী, একটা কথা বলব, ভয় পাবে না। রাগ করবে না।’
ভেতরে ভেতরে খুব শঙ্কিত হয়ে বিশ্বজিৎ বললেন—‘কি কথা? ভয় পেতে হবে কেন?’
লুকু নিচু গলায় বলল—‘আমি ড্রাগ খেতে আরম্ভ করেছিলাম বাপী। অবশ্য না জেনে। কিন্তু আমি আস্তে আস্তে অ্যাডিক্ট হয়ে যাচ্ছিলাম। দেব আমাকে বাঁচালো, ছাড়ালো নেশাটা। কিন্তু এখনও মুখটা কিরকম সুড়সুড় করে তাই দেবকে লুকিয়ে তোমার থেকে একটা দুটো নিয়ে খাই। ধরা দিনে দুটো, কখনও তিনটে। বাপী প্লীজ। আস্তে আস্তে ছেড়ে দেবো।’
বিশ্বজিতের বুকের ধুকধুকি থেমে গিয়েছিল কয়েক সেকেন্ড। বললেন—‘ড্রাগ? কি ড্রাগ? কোথায় পেলি? না জেনে কি করে খেলি?’
‘—তুমি জানো না বাপী ড্রাগের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে! আমিও ভালো করে জানি না কোথা থেকে পেয়েছি। তুমি এসব নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। দ্যাট চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজড নাউ। ওনলি হ্যাভ পেশেন্স উইথ মাই স্মোকিং হ্যাবিট। ওটা আস্তে আস্তে যাবে।’
ঝড়ুকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে লুকু আজকে কি একটা পদ রান্না করিয়েছে। ছোট ছোট মুচমুচে পরোটা তার সঙ্গে। শিখেছে নাকি মৈথিলীদের রাঁধুনি বৈজুদার কাছ থেকে। আনন্দ-বিষাদে মেশা কী অদ্ভুত এই রাতের খাওয়ার স্বাদ। লুকু তুলে দিচ্ছে। যা হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে বলে বিশ্বাস হঠাৎ দেখা যায় না তা পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে তা হলে যে আনন্দ হয় সেই আনন্দ এখন লুকুর বাবার মনে।
—‘বাপী আমি বড্ড কম আইটেম করি, তোমার খেতে কষ্ট হয়, না? অনেস্টলি বলবে।’
—‘আরে না না, আবার কি?’
—‘মা অনেক রকম করত।’ মা চলে যাবার পর লুকু সহসা মায়ের কথা মুখে আনে না। বিশ্বজিতও না। সে আছে ফুলে-মালায় সাজানো ঘরের মধ্যের ছবিতে, আর আছে দুজনেরই মনের কোণে। বিশ্বজিৎ লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, বললেন—‘তোর মা বড় বাহুল্য ভালোবাসত। অত বাড়াবাড়ির দরকার কি? এই তো বেশ খাচ্ছি।’
জয়দীপ বলল—‘কেন বাপী, হোটেলে কেমন মেনু-কার্ড থাকে। তুমি এক রকম পছন্দ করলে, আমি আরেক রকম পছন্দ করলুম, হয় না? ধরো সেদিন পার্ক স্ট্রিটে তুমি খেলে চীনে, আমি খেলাম পিজা আর দিদি তুই শুধু আইসক্রিম। কটা খেলি রে দিদি? তিনটে। তিনটে আইসক্রিম খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেললি!’
—‘কেন, তুই খাসনি বুঝি?’ লুকু বলল।
—‘আমি তো পিজা খেয়েছি তার আগে। যাই বলো বাপী সেটাই ভালো। নানা রকম থাকবে, যে যার পছন্দসই জিনিস তুলে নেবে।’
—‘তুই তো সবগুলোই তুলবি!’ লুকু ঘাড় নেড়ে বলল।
—‘নট নেসেসারিলি। পায়েস তুলব না। চচ্চড়ি তুলব না। সুক্তো তুলব না। স্টু তুলব না।’
—‘হ্যাঁ তোর তো আবার সব গরগরে চাই। বাবা মনে আছে ও কি রকম মাকে বলত—মা মামার বাড়ির মতো দরদরে তারিয়া করতে পারো না?’
‘গরগরে কালিয়াটা মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না দরদরে তারিয়া।’ লুকু হাসছে।
জয়দীপ বলল—‘প্লেয়ার তো, সব হজম হয়ে যায়। যদি হালকা জিনিসই দিস তো স্টম্যাকটাকে কোনও কষ্টই করতে হয় না। শরীরের যন্ত্রপাতিকে অত রেস্টে রাখতে নেই। বুঝলি? কুঁড়ে হয়ে যায়।’
রবিবার সকাল আটটা নাগাদ মেধা ভাটনগরের ফোন পেলেন বিশ্বজিৎ মজুমদার।
—‘বিশ্বজিৎদা আমি লালবাজার থেকে বলছি। একবার আসতে পারবেন লুকুকে নিয়ে?’
—‘কেন? কি বলছেন?’
—‘দেবপ্রিয়কে এরা অ্যারেস্ট করেছে, ড্রাগ ট্রাফিকিং-এর দায়ে। লুকুকে খুব দরকার।’
—‘লুকু কি করবে?’—বিশ্বজিতের গলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।
—‘লুকু অনেক কিছু জানে।’
—‘আমি যেতে পারি। লুকুকে নিয়ে ওখানে যাবো না। শী ইজ ডেলিকেট।’
—‘না নিয়ে এলে ভুল করবেন। আপনি ওকে নিয়ে আসুন, কোনও ভয় নেই।’
অধ্যায় : ১৭
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের সঙ্গে সরাসরি দেখা করবার ব্যবস্থা করে রেখেছে উজান। দাদুকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে। মেধা বললেন ‘তোরা দাঁড়া। প্রথমে আমি কথা বলি।’
দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই মেধা অবাক হয়ে বললেন—‘রণজয়!’ পদস্থ লোকেদের অতিথি-অভ্যর্থনার রীতি এক। সামনে কিছু ফাইল-টাইল জাতীয় জিনিস নিয়ে তাঁরা পড়তে ব্যস্ত থাকেন। ইনিও তাই ছিলেন। ‘রণজয়’ নামটা কানে যেতে সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকালেন।
‘মেধা!’ চতুর্গুণ বিস্ময়ের সঙ্গে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ‘মেধা ভাটনগর, তুমি এখানে? কেমন আছো? কি করে এলে?’
মেধার ছাত্রজীবনের সহপাঠী রণজয় বিশ্বাস প্রথমেই পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থনে একেবারে উন্মন হয়ে গেলেন।
‘আঃ সেই সব দিনগুলো! কলেজ স্ট্রিটের ট্রাম-বাস-মোটরগাড়ির অবিরাম আবহসঙ্গীত। আশুতোষ বিল্ডিংয়ের মধ্যে সিনারিও আরম্ভ হল। এস. ডি. ঘরে ঢুকেই রোল কল করতে করতে ধুন্ধুমার বকতে আরম্ভ করলেন। কাট। পেছনের বেঞ্চ থেকে প্রদীপ হেঁড়ে গলায় বলল, ‘সার, মে আই শাট দা ডোরস অ্যান্ড দা উইনডোজ?’—‘কেন? হোয়াই?’ বকুনির স্রোতে বাধা পড়ায় এস. ডি. খানিকটা থমকে গেছেন। প্রদীপ বলল—‘বড্ড অপমান লাগছে সার। অন্যরাও তো সব শুনছে। তাছাড়া জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে কিছুটা এসকেপ করেও যাচ্ছে। টোটাল এফেক্টটা হচ্ছে না! কাট। এবার ক্যামেরা সরে যাবে মেয়েদের মুখের ওপর। ভয়ের চোটে হাসি চেপে আছে, মুখগুলো টকটকে।’
মেধা হাসতে লাগলেন, ‘হ্যাঁ প্রদীপ ছিল একের নম্বর বিচ্ছু…। তুমিও কিছু কম ছিলে না। আচ্ছা রণজয় আমার ছাত্র দেবপ্রিয় চৌধুরীকে ড্রাগ-চালানের দায়ে ধরেছ কেন? প্রিপসট্রাস!’
রণজয়ের চোখ সতর্ক হয়ে উঠল। বললেন, ‘ও! তা এই দেবপ্রিয় চৌধুরীটি তো মেডিক্যাল কলেজের ছেলে, তোমার ছাত্র হল কী সুবাদে?’
—‘আমি ইতিহাস পড়াই রণজয়। ইতিহাস সবার পাঠ্য।’
—‘জবাবটা মেধা ভাটনগরের মতোই হয়েছে’—রণজয় হেসে ফেললেন, তারপর বললেন
—‘সিরিয়াসলি বলো তো মেধা, ব্যাপার কি? ড্রাগ-অ্যাবিউজ ফাইট করবার জন্য আমাকে কলকাতায় ট্রান্সফার করা হয়েছে। এই ছেলেটিকে আমার লোক বেশ কিছুদিন চেজ করে করে ধরেছে। এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?’
মেধা বললেন—‘আমার সঙ্গে কিছু ইমপর্ট্যান্ট উইটনেস রয়েছে। তাদের সঙ্গে তুমি একটু কথা বলো।’
—‘ওর আত্মীয় স্বজন?’
—‘ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এখানে আমিই। আমার আরও কিছু ছাত্র-ছাত্রী আছে, ওরা সবাই একসঙ্গে নানা ধরনের সোশ্যাল ওয়ার্ক করে, ওদের সঙ্গে কথা বললেই জিনিসটা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে!’
রণজয় ওদের ডেকে পাঠালেন।
—‘তুমি এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলো’—মৈথিলীকে দেখিয়ে দিলেন মেধা।
মৈথিলী এগিয়ে এসে রণজয়কে নমস্কার করে বলল—‘দেবপ্রিয় চৌধুরী আমাদের বছরের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছাত্র। এইচ. এস-এ রেকর্ড মার্ক্স পেয়ে ফার্স্ট হয়। মেডিক্যাল কলেজেও ওর পার্ফম্যান্স খুব ভালো। ও গ্রামের ছেলে। এখানে কোনও পারিবারিক বন্ধুর বাড়ি থেকে পড়ে। আমাকে ও গত নভেম্বর মাসের সতেরই, সন্ধে সাতটা নাগাদ কথাচ্ছলে জানায় কে বা কারা ওকে ড্রাগ ধরাতে চাইছে ওর সিগারেটের প্যাকেট বদলে দিয়ে। ওর কথা শুনে মনে হয় এদের ধরতে ও বদ্ধপরিকর।
—‘প্রথমে হয়ত সদুদ্দেশ্যই ছিল। কিন্তু ড্রাগ এমনই জিনিস…’
—লক্ষ্মীশ্রী হঠাৎ বাকি দুজনকে সরিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে এলো। তার চোখ জ্বলছে। বলল—‘মিঃ ইন্সপেক্টর, আমাকেও কেউ ড্রাগ ধরাতে চেয়েছিল। দেবপ্রিয় চৌধুরী হ্যাজ প্রিভেনটেড ইট। আপনারা আসল নকল ধরতে পারেন না? দেবপ্রিয় এদের ধরবার জন্য আজ তিন বছর সাধনা করছে। আপনারা আসল বদমাশগুলোকে ধরতে পারবেন না। অনেস্ট প্রোবিং যে করছে, তাকে ধরছেন! ওয়ান্ডারফুল!’
উজান বলল—‘লুকু তুই চুপ কর।’
রণজয় অবাক হয়ে লক্ষ্মীশ্রীকে দেখছিলেন। বললেন—‘তোমাকে ড্রাগ ধরাতে চেয়েছিল কে? কিভাবে?’
—‘অতসব বলবার দায় আমার নেই। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি সামলাবো। আপনি দেবকে ডেকে পাঠান, পাঠিয়ে দেখুন ও ড্রাগ অ্যাডিক্টের মতো আচরণ করে কি না।’
রণজয়ের ইঙ্গিতে একটু পরেই দেবপ্রিয়কে আনা হল। দেখেই মেধা উঠলেন। এরা ওকে মারধোর করেছে। দেবপ্রিয়র চোখ লাল, চুল অবিন্যস্ত। যে দুজন কনস্টেবল ওকে ধরে এনেছিল তাদের একজন বলল—‘সার, জামাকাপড় থেকে পর্যন্ত উৎকট গন্ধ বেরোচ্ছে।’
—‘পকেট সার্চ করে কি কি পাওয়া গেছে দেখাও তো।’
কনস্টেবল দুটি তিন-চার রকম সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাইয়ের বাক্স, মানিব্যাগ, এবং গোটা দুই রুমাল এনে রাখল টেবিলের ওপর। মানিব্যাগটা উপুড় করে তার থেকে কিছু খুচরো টাকাপয়সা বার করল ওরা। সব মিলিয়ে টাকা তিরিশের মতো এবং কিছু রেজগী। তারপর বার করল একটা প্যাকেট, রণজয় বিশ্বাসের দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল—‘সার ব্রাউন সুগার।’
হঠাৎ দেবপ্রিয় কথা বলে উঠল। বলল ‘সিগারেটের প্যাকেট চারটে আছে দেখবেন। যে দুটো খালি হয়ে এসেছে, সেগুলো অর্ডিনারি চারমিনার। অন্য দুটোয় সিগারেটের মশলার সঙ্গে হেরোইন মিক্স করা আছে। দেখবেন দুটোই ভর্তি।’ প্রশান্ত স্বরে কথাগুলো বলে দেবপ্রিয় টলতে লাগল।
লুকুর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। সে ছুটে গিয়ে দেবপ্রিয়র পাশে দাঁড়াল—‘দেব, তোমাকে ওরা মেরেছে, না?’
দেবপ্রিয় বলল—‘লুকু উত্তেজিত হয়ো না।’ তারপর রণজয় বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল—‘মাফ করবেন, আমি আপনার নাম জানি না, পদ জানি না, শিক্ষক ছাড়া কাউকে ‘সার’ বলি না, আমি টলছি, ড্রাগের নেশায় নয়, কাল থেকে না খেয়ে, ঘুসুড়ির ঠেকে পুলিশের প্রতীক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মারিজুয়ানা আর হেরোইনের ধোঁয়ার মধ্যে বসে থেকে এবং তারপর যখন সত্যিই আপনারা এলেন তখন আপনাদের হাতে উত্তম-মধ্যম খেয়ে।’
রণজয় কনস্টেবল দুটিকে বললেন—‘ওকে ছেড়ে দাও, বসতে দাও, দুধ আনো খানিকটা।
কনস্টেবল দুটি চলে গেলে রণজয় বললেন—‘এক্সপ্লেন ইওরসেল্ফ।’
দেবপ্রিয় একটু ঝুঁকে বসেছিল— সে বলল—‘গত তিন বছর লুকোচুরি খেলার ধরন দেখে মনে হয়েছে বিশ্বাস করার মতো মানুষ এখানে খুব কম। আপনাকে কি বিশ্বাস করা যায়? এনিওয়ে আই ডোন্ট কেয়ার এনি মোর।’
মেধা বললেন—‘দেব কি বলছিস? ঠিক করে বল।’ তাঁর ইঙ্গিতে উজান কোথা থেকে দুটি ঠাণ্ডা দুধের বোতল যোগাড় করে এনেছিল। মেধা বললেন—‘রণজয়, এগুলো ওকে দিতে পারি?’
—‘দাও।’ একটা খেলো দেবপ্রিয়। তারপর ঝোঁকহীন ইংরেজিতে বলল— ‘আই ওয়ান্টেড দা পুলিশ টু ফলো মি। আই ডেলিবারেটলি স্টেইড ইন দা ডেন লং আফটার আদার্স ক্লীয়ার্ড আউট, প্রিটেন্ডিং দ্যাট আই ওয়াজ আউট। আই ডিড দিস টাইম অ্যান্ড এগেইন। বাট ইয়োর পীপল ইনভেরিয়েবলি অ্যারাইভ্ড্ হোয়েন দা কোস্ট ওয়াজ ক্লীয়ার। দে কলারড্ অ্যান্ড ম্যানহ্যাণ্ড্ল্ড্ মি। ইউ নো বেস্ট হোয়েদার অল দিস ইজ ডেলিবারেট অর নট।’
দেবপ্রিয়র কথা শেষ হতে না হতেই কলিংবেল টিপেছিলেন রণজয়। কনস্টেবলকে কি ইঙ্গিত করলেন, একজন পুলিশ অফিসার এসে ঢুকলেন। তিনি অন্যদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সোজা রণজয় বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে গেলেন এবং চুপিচুপি কি সব বলতে লাগলেন। শুনতে শুনতে রণজয়ের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠছিল। অফিসারটি চলে যাবার পর তিনি লক্ষ্মীশ্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার নাম কি?’
লক্ষ্মীশ্ৰী বেশ কড়া সুরে নিজের নাম বলল। রণজয় বললেন—‘ঠিক আছে তোমরা তিনজন তোমাদের বন্ধুকে নিয়ে যেতে পারো। ওর নামে কোনও চার্জের রেকর্ড নেই। ওকে আমরা ধরিনি। নাউ ইউ ক্যান অল গো। ও কে?’
লক্ষ্মীশ্রী দৃঢ়স্বরে বলল— ‘কিন্তু আপনারা ওকে শুধু শুধু মেরেছেন। এর জবাবদিহি আপনাদের করতে হবে। নইলে আমরা ছাড়ব না। অনেকদূর পর্যন্ত যাবো এর জন্য।’
—‘ঠিক আছে’, রণজয় হঠাৎ তাঁর টেবিলের ড্রয়ার খুললেন, একটা বড় প্যাকেট বার করে ছিঁড়ে ফেললেন। বার হল অনেকগুলো পাতলা পাতলা চকোলেট বার। তিনি সেগুলো চার বন্ধুর দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন—‘এগুলো সুইস চকোলেট। ভেতরে খুব সুন্দর নির্দোষ ওয়াইন আছে। এগুলো তোমরা খাও, উই আর ফ্রেন্ডস নাউ। আর তোমাদের বন্ধুকে খুব সাবধানে নিয়ে যেও। আমি তোমাদের দিদির সঙ্গে একটু কথা বলে নিচ্ছি। ওঁর কাছ থেকে পরবর্তী করণীয়গুলো তোমরা জেনে নেবে।’
চকোলেটগুলো কেউ ছুঁলো না। রণজয় নিজেই একটার মোড়ক ভেঙে দেবপ্রিয়র দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—‘তোমার নাম কি? দেব? শোনো, এগুলো খুব নারিশিং। মিলিটারিতে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়। তোমার ওপর খুব ধকল গেছে কাল থেকে। য়ু আর লিটর্যালি আ হাংরি ইয়ং ম্যান। টেক ইট, সে, ফ্রম অ্যান আঙ্কল।’
দেবপ্রিয় নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে চকোলেটটা নিল। কিন্তু মুখে পুরল না। সে উঠে দাঁড়াল। মেধা বললেন—‘বাইরে বিশ্বজিৎদা আছেন, তোরা সবাই লুকুর বাড়ি যা। আমি ওখানেই তোদের সঙ্গে দেখা করব।’
ওরা চলে গেলে রণজয় বিশ্বাস কয়েক মিনিট চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। তারপর যেন আপন মনেই বললেন— ‘ওরা তা হলে আমার সঙ্গে সন্ধি করল না!’
টেবিলের ওপর ছড়ানো চকোলেটগুলোর দিকে তাকিয়ে মেধা হেসে বললেন, ‘ওরা যে সুবিচার চেয়েছিল, তা তো তুমি ওদের দাওনি! কি করে সন্ধি করবে?’
রণজয় বললেন—‘মেধা, পুলিশ কিন্তু ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধু নয়। তার সঙ্গে টক্করে এলে দু-চার ঘা খেতে হতে পারে।’
—‘সেটা টক্করে এলে। যে সহযোগিতা করছে…’
হঠাৎ রণজয় ভেতরে ভেতরে কি যেন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, নিচু গলায় বললেন—‘মেধা, দ্যাট বয় ইজ ইন গ্রেট ডেঞ্জার।’
—‘মানে?’ মেধা সোজা হয়ে বসলেন।
—‘কিছুদিন আগে, ধরো বছরধানেকের সামান্য বেশি! এক বিখ্যাত কলেজের ছাত্রকে সার্কুলার রেলের কোনও একটা জায়গায় গলা-কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেনটা এসে গেলে, অ্যাকসিডেন্ট বলেই চলে যেত জিনিসটা। মনে আছে?’
মেধা মাথা নাড়লেন।
—তা হলে এ-ও নিশ্চয় মনে আছে তার এক সহপাঠীকে পুলিশ মার্ডার চার্জে ধরে। কেসটা দাঁড়ায়, এক সহপাঠিনীকে কেন্দ্র করে এদের মধ্যে লাভ-ট্র্যাঙ্গল ছিল, যার ফলে এই খুন। কনভিকশন শেষ পর্যন্ত হয়নি, অভিযুক্ত ছেলেটির বাবা খুব প্রভাবশালী মহলে ঘোরাফেরা করেন। কিন্তু আমার কাছে খবর আছে সংশ্লিষ্ট মেয়েটির কাছে কে বা কারা বার বার ফোন করে এই প্রেম-ত্রিভুজের কথা স্বীকার করে নিতে বলে। অভিযুক্ত ছেলেটি নাকি মরিয়া হয়ে উঠেছিল, মাঝে মাঝেই হত্যার ভয় দেখাত, এটাও তারা মেয়েটিকে স্বীকার করে নিতে বলে। মেয়েটি ছিল অনমনীয়। তাকে একবার একটা অ্যামবাসাডর গাড়ি আরেকবার একটি ট্রাক ধাক্কা মারে, সামান্য ক্ষতি হয় তাতে। সেই অবস্থায় আবার ওই ফোন আসে। যাই হোক, এই মেয়েটি তার সাক্ষ্যে অটল থাকে বলেই সহপাঠী ছেলেটি রক্ষা পেয়ে যায়।’ রণজয় চুপ করলেন।
মেধা অধৈর্য গলায় বললেন—‘সো হোয়াট? এই সব পুরনো স্ক্যান্ডাল আমাকে শোনাচ্ছো কেন?’
—‘শোনাচ্ছি এইজন্যে যে আসলে এই ছেলেটি ড্রাগ-ট্র্যাফিকারদের শিকার। খুব ট্যালেন্টেড ছেলে। তার রোখ চেপে গিয়েছিল যেমন করে হোক ছাত্রদের সর্বনাশ যারা করছে, তাদের ধরবে। ওই তার পরিণাম।’
—‘জানো যদি, তো আসল অপরাধীদের ধরলে না কেন?’
—‘কোনও প্রমাণ ছিল না। তা ছাড়াও ছেলেটির পেছনের পকেটে একটা “জেনুইন” সুইসাইড নোট পাওয়া যায়।’
—‘তাহলে নিশ্চিতই বা হচ্ছো কি করে যে এটা ড্রাগ-ব্যবসায়ীদের ব্যাপার?’
—‘সব কথা তোমাকে বলা সম্ভব নয় মেধা, দো য়ু আর মাই ওল্ড ফ্লেম,’ হাসতে হাসতে বললেন রণজয়;—‘এইটুকু শুধু জেনে রাখো এই ডেনগুলোর পেছনে প্রচুর পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আছে। বিরাট র্যাকেট একটা। পলিটিকস করতে গেলে আজকাল গুণ্ডাদের হাতে রাখতে হচ্ছে, গুণ্ডাদের চাই রেস্ত, অনে-ক অনে-ক, যা দিয়ে গোটা সমাজকে ভীত, কোণঠাসা করে রাখা যায়। সুতরাং ড্রাগ। সবটাই ভিশাস সার্কল। এ এক নতুন প্রেমচক্র। তোমার এ ছাত্রটি আগুনে হাত দিয়েছে। ওরই বিপদ বুঝে আমাদের ইন্স্পেক্টর রক্ষিত ওকে ধরে এনে, খানিকটা ধোলাই দিয়ে, ধরে রাখতে চেয়েছিল। সবটাই আই-ওয়াশ। আমাদের লোকেরা ইশারায় বুঝে যায় কে জেনুইন, কে জেনুইন নয়।’
—‘ইশারা-টিশারা নয়। তোমাদের লোকেরা সব কিছুই বোঝে।’
—‘জেনেশুনে ন্যাকা সাজে। সময়। সময়ের জন্য অপেক্ষা করে। বুঝলে কিছু?’
—‘তাহলে এখন উপায়?’ মেধা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।
—‘ওকে কিছুদিন কলকাতা থেকে সরিয়ে দাও।’
—‘রণজয়, তোমরা তাহলে এই ডেনগুলোকে, এই ড্রাগের ব্যবসাদারদের উচ্ছেদ করবে না?’
—‘লেটস সী’—নিচু গলায় বললেন রণজয়। তারপর হঠাৎই একটু চড়া সুরে বললেন ‘যাক এই উপলক্ষ্যে যে আবার এতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এটাই আমার ভাগ্য। তোমার ছাত্রটিকে কোনও নার্সিংহোমে রাখার ব্যবস্থা করো দরকার হলে। আর মেধা, কোনও অসুবিধেয় পড়লে অবশ্যই আমার কাছে আসবে। তোমাকে আমার প্রাইভেট নম্বর দিয়ে রাখছি, আমি যখন যেখানেই থাকি, এই নম্বরটা দিয়ে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি রীচ করতে পারবে।’
নম্বরটা নিয়ে মেধা চলে আসছিলেন। হঠাৎ কি মনে হল ফিরে গেলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিচু গলায় বললেন—‘রণজয়, তুমি এইজন্যই ট্রান্সফার হয়েছ বলছ, তোমার নিজেরও তো বেশ বিপদ মনে হচ্ছে!’
—‘বলছ?’ রণজয় দশ আঙুলের মাথা দিয়ে মন্দিরের চুড়ো করতে চেষ্টা করছেন। বললেন—‘ইন দ্যাট কেস, বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা/ বিপদে আমি না যেন করি ভয়।’
—‘প্রার্থনাটা কার কাছে করছ?’
—‘দ্যাট ডিপেন্ডস, কনফার্মড মার্কসিস্টদের কাছে বিশ্বাসের কথা প্রার্থনার কথা বলতে হলে ভাবতে হয়। আচ্ছা মেধা তুমি এইসব ছেলেদের নেত্রী? ওই ছেলেটি দেবব্রত না দেবপ্রিয়, ওকে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে যোগ দিতে বলো না! বুদ্ধিমান, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, হী ইজ স্পিরিটেড। ঠিক যতটা দুঃসাহস থাকা প্রয়োজন সেটুকুও ওর আছে। এরকমই দরকার, নইলে পুলিসি-ব্যবস্থা ক্রমেই ভেঙে পড়বে।
—‘কিন্তু ও তো শীগগীরই ডাক্তার হয়ে বেরোচ্ছে! তাছাড়া ওরা সরকারি কাজ করবে না। যেটুকু না করলেই নয়, সেটুকু ছাড়া সরকারি ব্যাপারের সঙ্গে ওরা সম্পর্ক রাখতে চায় না।’
—‘কেন?’
—মেধা চুপ করে রইলেন।
—‘বলবে না?’
—‘রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যেতে ওরা চায় না।’
—‘সরকারের বাইরেও তো রাজনীতি রয়েছে।’
—‘তাকেও ওরা এখনও পর্যন্ত বর্জন করে চলেছে।’
—‘ওদের পরিচালিকা তো একদা আকণ্ঠ নিমগ্ন ছিলেন রাজনীতিতে।’
কি যেন বলতে গিয়ে সামলে নিলেন মেধা। তারপর বললেন—‘লক্ষ্যে পৌঁছতে গিয়ে কেউ যদি একটা পথ ধরে এগিয়ে দেখে সামনে অতলস্পর্শ খাদ, তখন কি ভিন্ন পথ ধরবার স্বাধীনতা বা অধিকার তার নেই?’
—‘সেটাতেও যদি সামনে খাদ থাকে?’
—‘দ্বিতীয়বার সে নিশ্চয়ই খানিকটা সার্ভে করে নিয়ে এগোবে। হয়ত এ পথের খাদ তেমন চওড়া নয়।’
—‘ভালো!’ রণজয় বললেন, ‘রাজনৈতিক সচেতনতা বাদ দিয়ে চলবে? চলা সম্ভব নাকি?’
—মেধা অবাক হয়ে বললেন, ‘রাজনৈতিক সচেতনতা বাদ? কে বললে? এরা পুরোমাত্রায় সচেতন। কোথায় কি ঘটছে, কেন ঘটছে সব জানে, হিসেব রাখে, তাছাড়া আমি পরিচালক এটা তোমার ভুল ধারণা। এরা স্বাধীনভাবে নিজেদের গড়ছে। আমি একজন সাজানো উপদেষ্টা, তার বেশি কিছু নয়।’
—‘হ্যাঁ, তুমি সাজানো, আর ওরা আপনি গড়ে উঠছে! এসব মিথ্ আমায় বিশ্বাস করতে বলো না মেধা। ওই মেয়েটি, কি যেন নাম বললে? লক্ষ্মীশ্রী? শী ইজ এ ভেরি আনইউসুয়াল টাইপ। ওকে দেখে আমার ছাত্রজীবনের মেধা ভাটনগরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।’
মেধা মনে মনে অবাক হলেন। মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। যাবার সময়ে শুধু বললেন—‘এইসব ছেলেমেয়েদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করতে না পারলে ঠকবে, রণজয়। এরা সত্যিই স্বয়ম্ভর।’
বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলেন মেধা। ডালহৌসি গিয়ে মিনিবাস ধরবেন। তাঁকে প্রথমেই যেতে হবে বিশ্বজিৎ মজুমদারের বাড়ি রিচি রোড। সেখানে ওরা নিশ্চয়ই তাঁকে আশা করছে। রণজয় বলল লক্ষ্মীশ্রী তাঁর মতো, রঘুনন্দন বলেছিলেন মৈথিলী তাঁর মতো। মৈথিলী আর লক্ষ্মীশ্রী কতো আলাদা! যদিও দুজনের খুব বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব তো অনেক সময়েই বিপরীত মেরুর সঙ্গে হয়। হঠাৎ তাঁর মনে হল তিনি কি তা হলে বিশ্বময় ছড়িয়ে যাচ্ছেন? লক্ষ্মীশ্রী তাঁর মতো, মৈথিল তাঁর মতো, এর পরে কারো মনে হবে গুঞ্জন তাঁর মতো, ছাত্রসংঘের আরও সব কর্মী মেয়েরা—উজ্জ্বল, বুদ্ধিময় মুখচোখ, প্রত্যয়ে সংকল্পে স্থির, তারা সবাই কি মেধা ভাটনগরের আদলে গড়া? ভাবতে কি অসম্ভব ভালো লাগল। তাঁর শরীরটা যেন বিশাল হতে হতে ক্রমশই ঢেকে ফেলেছে কলকাতার রাজপথ, জনপথ। তারপর হঠাৎ সেই মহাকায় শরীর ভস্মে পরিণত হল, ভস্ম উড়ে যাচ্ছে এখানে, ওখানে, সেখানে। উঠে দাঁড়াচ্ছে শত শত মেধা ভাটনগর। এক রূপে নয়, শতরূপে। দেবপ্রিয় রূপে। উজান আফতাব রূপে, পূর্ণিমা, হাসিনা, সঙ্ঘমিত্রা, মীনাক্ষী, সন্দীপ, মৌমিতা, অজপা, শান্তনু, প্রমিত, শর্মিষ্ঠা, অনমিত্র, সঞ্জয়..অনেক..অনেক। সারা পথটা রোমাঞ্চিত হয়ে হাঁটতে লাগলেন মেধা। তিনি বিবাহিত, কিন্তু কুমারী। সন্তানধারণ করা কি জিনিস জানবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু কাল রাত থেকে তিনি যেন গর্ভভারে পীড়িত। কেউ কি তাঁকে শত পুত্রের জননী হও বলে আশীর্বাদ করেছিল? স্বামী অন্ধ বলে তিনি তো নিজের চোখ কখনও আবৃত করেননি! তাহলে তাঁর শত পুত্র-পুত্রী নিশ্চয় কুলক্ষয়ী হবে না। তাছাড়াও তাঁর এ গর্ভ তত আবিষ্ট গর্ভ, ইম্যাকুলেট কনসেপশন। ইতিহাস বলছে কুমারী জননীর সন্তানরা সব সময়ে সন্ত হয়।
অধ্যায় : ১৮
উজান বলল, ‘আই ও য়ু অ্যান অ্যাপলজি দেব, আমি তোকে ভয়ানক সন্দেহ করেছিলাম। ভেবেছিলাম তোকে ছাড়িয়ে এনে এক্ষুনি কোনও ডি-টকসিফিকেশন সেন্টারে দিতে হবে।’
দেবপ্রিয় চান করে চুল আঁচড়াচ্ছিল লক্ষ্মীশ্রীর বড় বড় দাড়ার চিরুনি দিয়ে। তার চুল থেকে জল ঝরে ঝরে লুকুর বাবার পাঞ্জাবির উপরিভাগ ভিজিয়ে দিচ্ছে।
এখন রোদ চড়ে গেছে। পাখাগুলো সব ঘুরছে। লক্ষ্মীশ্রী জানলার ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ডগুলো টেনে নামিয়ে দিল। সে আজ বাড়ি এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেবপ্রিয়র ফার্স্ট এইড। তার জামাকাপড়। আগে বাপীর পায়জামা পাঞ্জাবি দিয়ে সে দেবপ্রিয়কে বাথরুমে চান করতে পাঠিয়েছে। আজকে বন্ধুরা এবং মেধাদি সবাই এখানে খাবেন এই তার ইচ্ছে। সে মাঝে মাঝেই ঝড়ুকে নির্দেশ দিয়ে আসছে। তার বাপী ড্রয়িংরুমে বসে বসে জয়দীপের সঙ্গে দাবা খেলছেন। কিন্তু উৎসুক হয়ে মাঝে মাঝেই তাকিয়ে দেখছেন লুকু বারবার রান্নাঘরে যাচ্ছে, ঝড়ুকে একবার ধমক হলো, চটপট ড্রয়িংরুম থেকে কয়েকটা চেয়ার সে উঠিয়ে নিয়ে গেল। বন্ধুরা বসবে। হুকুমের সুরে বলল—‘এই আমার বিছানা হাঁটকাবি না। চেয়ার এনে দিয়েছি, বোস।’
উজান বলল—‘আমাকে বলতে পারতিস, আমি এনে দিতুম।’
লুকু বলল—‘বেশি বকবক না করে বোস, এখন দেবকে বেশি বিরক্ত করিস না, ব্রেকফাস্ট খেয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে নিক তারপর ওর কথা শুনিস। দেব, তুই ঘুমো।’
মৈথিলী হাসতে হাসতে বলল—‘বাপরে লুকু, মনে হচ্ছে দেব তোর একলার সম্পত্তি!’
—‘না তো কি? পাবলিকের হবে না কি?’ লুকুর মুখ গম্ভীর। কয়েক সেকেন্ড সবাই চুপ। তারপর সবাই হাসতে শুরু করল। দেবপ্রিয়র গলা শোনা গেল—‘এসব কি আবোল তাবোল বলছ লুকু?’
‘বলেছি, বলেছি’—লুকু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—‘ঝড়ু তুই ওমলেটটা পুড়িয়ে ফেললি নাকি? আঁচটা সিম করে দে। হ্যাঁ। টোম্যাটো আর চীজের কুচিগুলো দিয়ে দে। এইবার ভাঁজ কর। উজান তোরাও ওমলেট খাবি নাকি রে?’
বিশ্বজিৎ বললেন—‘জিজ্ঞেস করছিস কি রে? দে সবাইকে!’
লুকু বলল—‘ওরা হয়ত ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি এতো খাটবো কেন?’
মৈথিলী বলল, ‘না রে আমি অন্তত খাইনি। উজান তুই?’
‘আমিও না’, উজান বলল, ‘তবে দেব ব্রেকফাস্ট খেয়েছে। কি বল দেব, বেশ উত্তম-মধ্যম?’
দেবপ্রিয় হালকা গলায় বলল—‘ব্রেকফাস্ট তো নয়, লেট নাইট ডিনার। আমি হঠাৎ অহিংস সেজে গেলুম বুঝলি? ওরা দু-তিনটে চড়, ঘুষি, কিল ইত্যাদি মেরে টেরে যখন দেখল রেজিস্ট করছে না, তখন হঠাৎ থেমে গেল। না হলে আজ আর ওমলেট খেতে হত না।’
লক্ষ্মীশ্রী আড়চোখে তার দিকে তাকাল। দেবপ্রিয় ঠিক বলছে না। ওকে এর চেয়ে বেশি মার খেতে হয়েছে। পিঠে কালশিটে দাগ আছে। পেটে খিচখিচে ব্যথা।
দেবপ্রিয় বলল—‘আমারও কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার আছে উজান। আমি তোমাকেই প্রথম প্রথম সন্দেহ করেছিলুম।’
—‘কিসের সন্দেহ?’
—‘কেউ আমার পকেটের সিগারেট-প্যাকেট বদলে দিত। সেম প্যাকেট, খালি সাধারণ তামাকের বদলে হেরোইন পাইল করা তামাক।’
—‘বলিস কি? উজান বলল—‘আমাকে সন্দেহ করেছিলি কেন?’
—‘তুই-ই তো আমার সবচেয়ে কাছাকাছি থাকতিস। তবে আমি আমার সন্দেহের কথা কাউকে জানাইনি। কেওড়াখালিতে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল প্রমিতই ব্যাপারটা করে।
—‘প্রমিত?’ আশ্চর্য হয়ে মৈথিলী বলল।
—‘প্রমিত স্কুল ডেজ থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, তুই ভুল দেখিসনি?’ উজান বলল।
—‘নাঃ। ওই তো আমাকে কলেজ স্ট্রিটের লালের দোকানটা দেখিয়ে ছিল। তবে প্রমিত নিজে নেশা করলেও ওকে আমি এত দিনের মধ্যে কোনও ঠেকে দেখিনি। ও কোথায় নেশা করে ভগবান জানেন!’
মৈথিলী বলল— ‘দু সপ্তাহ কি তারও বেশি ওকে দেখছি না। আগে খেয়াল করিনি। দেব তুই আমাদের সাবধান করে দিসনি কেন?’
—‘সাবধান করেছি ঠিকই। ওর নামটা বলিনি। একেবারে নিশ্চিত না হয়ে বলাটা কি ঠিক হত!’
মৈথিলী উদ্বিগ্ন গলায় বলল—‘তোর আগে বলা উচিত ছিল দেব। প্রমিতটা ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে যাচ্ছে, তাকে আমরা বাঁচাব না?’
দেবপ্রিয় বলল, ‘আমার নানা সংশয় ছিল। ওর যোগাযোগগুলো কি ধরনের না জেনে ওর সম্পর্কে কোনরকম অ্যাকশন নেওয়ার বিপদ ছিল মৈথিলী। আফটার অল ও একজনকে তার অজান্তে, অনিচ্ছায় মাদকাসক্ত বানাবার চেষ্টা করেছিল। ও কোনও দলের এজেন্ট কি না সেটা জানারও চেষ্টা করছিলুম আমি। কাজটা সময়সাপেক্ষ।’
লক্ষ্মীশ্রী অভিভাবকসুলভ গলায় বলল—‘ওকে তোরা এবার ঘুমোতে দে। চল আমরা বাপীর কাছে গিয়ে বসি। এক্ষুনি বাপী ভাববে—লুকুটা বন্ধুদের মনোপলাইজ করে রেখেছে। না বাপী?’
বিশ্বজিৎ বললেন—‘তোর বন্ধুরা তো তোরই বন্ধু। আমার তো নয়।’
উজান মৈথিলী ছোট্ট থেকে দেখছে লুকুর বাবাকে। আগে খুব গম্ভীর, সুপুরুষ সাহেব মানুষ ছিলেন। উজানের বাবা যেমন তার বন্ধুর মতো, অনেক বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা যায়, তেমন নয়। মৈথিলীর বাবা যেমন কন্যা-অন্ত প্রাণ, রাশভারি অথচ স্নেহময়। তেমনও নয়। একটু যেন ফর্ম্যাল। একটু বুঝি উন্নাসিক। লুকুদের বাড়িতে মাঝে মধ্যেই পার্টি হতো। খুব শানদার কিছু ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা আসা-যাওয়া করতেন। দারুণ মড। অনেক দিন ওরা এসে দেখেছে লুকুর বাবা মা দারুণ সেজেগুজে পার্টিতে বেরোচ্ছেন। লুকু একটা লম্বা ড্রেস পরে মুখ চোখ ভারি করে বসে বাজে ইংরিজি নভেল পড়ছে। জয়দীপ একা একাই ব্যাডমিন্টন র্যাকেট আর কক নিয়ে ওদের বড় ড্রয়িংরুমটায় এদিক থেকে ওদিক মারছে, আবার কুড়িয়ে নিয়ে ওদিক থেকে এদিক মারছে।
এই বিশ্বজিৎকাকুকে তারা চেনে না। দুজনেই ড্রয়িংরুমে এসে দাবা বোর্ডটাকে ঘিরে বসল। লক্ষ্মীশ্রী বলল—‘দাঁড়া তোদের জন্যও ওমলেট বানাচ্ছি। টোম্যাটো চিজ দিয়ে ডবল ডিমের ওমলেট, খেয়ে দ্যাখ রেস্টুরেন্টের সঙ্গে তফাত করতে পারবি না।’
বিশ্বজিৎ বললেন—‘হ্যাঁ, এটা ঝড়ু ভালোই পারে।’
‘ঝ-ড়ু?’ লুকু ফিরে দাঁড়াল—‘বাপী ইয়ার্কি হচ্ছে, না? ঠিক আছে, তুমি পাবে না।’
—‘কিসের কথা বলছিস? ওমলেট? অ! আমি ভাবছি বুঝি চায়ের কথা বলছিস। চাটা ঝড়ুকে ভালোই শিখিয়েছিস!’
—‘খুব কথা ঘোরাতে শিখেছ’ লুকু হেসে ফেলছে। মৈথিলী, উজান, জয় সবাই হাসছে। ঝড়ুও একঝুড়ি মূলো বার করে ফেলেছে।
ঝড়ুকে দিয়ে, নিজেরটা প্লেটে নিয়ে লুকু গলদঘর্ম হয়ে ফিরে এলো।
মেধা যখন পৌঁছলেন তখন তিন বন্ধুই রান্নাঘরে। উজান বলছে ‘আমি বাবাকে মাংস রান্না করতে দেখেছি। পুরো প্রসেসটা দেখেছি বহুবার। থিয়োরিটা পুরোপুরি জানি। আজকে আমাকে মাংস রাঁধতে দিতেই হবে।’
লুকু বলল—‘দ্যাখ উজান, নিজের বাড়িতে রাঁধিস। আমার বাপীর খাওয়াটা নষ্ট করে দিস না প্লিজ। এই তো মৈথিলীও রয়েছে, ও তো জাস্ট সাহায্য করছে, উৎপাত করছে না তো তোর মতো?’
বিশ্বজিৎ বললেন, ‘দে না, ওকে দিয়েই দ্যাখ না।’
আসলে, বিশ্বজিৎ একে তো উজানকে ভীষণ পছন্দ করেন। দ্বিতীয়ত উজান মুসলিম। তাঁর ধারণা মুসলিম মাত্রেই মোগলাই রাঁধতে পারে। উজানের রান্নার প্রস্তাবে তিনি তাই খুব উৎসাহী। মেধাকে দেখে তিনি বললেন—‘বাঃ এই তো মিস ভাটনগর এসে গেছেন। ওঁর জন্য তোরা কি ডিশ রেখেছিস?’
মেধা দেখলেন সকলেই খুব হাসিখুশী। বললেন—কেন? ‘মেনু কি?’
লক্ষ্মীশ্রী বলল—‘দেখুন না দিদি, বাপী অত ভালো মাংসটা আনল, এখন উজান বায়না ধরেছে ও রাঁধবে। দিদি আপনার জন্য পোস্তর বড়া করে দেবো!’
মেধা সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললেন—‘তোরা যা যা রাঁধবি সব খাবো আজ। দেব কোথায়?’
—‘ঘুমিড়ে পড়েছে।’
—‘হ্যাঁরে মৈথিলী, তোদের ফাইন্যাল কবে?’
—‘মাস দুই দেরি আছে।’
—‘কাল আমি দেবকে নিয়ে ওদের দেশ দেখতে যাবো।’
—‘দিদি, হঠাৎ?’ লক্ষ্মীশ্রী বলল।
—‘ইচ্ছে হল। ওর মেজজেঠু তো সেখানে দারুণ কাজ করছেন, দেখতে যাবো না?’
—‘কেন, তুই যাবি?’
—‘ন্ না।’ লুকু একটু লজ্জা পেয়ে গেল, ‘এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।’
এবার গম্ভীর হয়ে মেধা বললেন, ‘তোদের জানা দরকার, দেবকে রণজয় বিশ্বাস ডি. আই. জি. কিছুদিন কলকাতা থেকে সরিয়ে দিতে বলছেন।
—‘কেন?’ লুকু জিজ্ঞেস করল, তার স্বরে উদ্বেগ।
মেধা বললেন—‘দেব উঠুক, একসঙ্গে সবাইকে বলব।’
অধ্যায় : ১৯
এখন এখানে পিচঢালা সড়ক হয়ে গেছে। বনবন করে রিকশা ছোটে, বাস ছোটে। বাসগুলো আপাদমস্তক যাত্রী-ঠাসা। এ সব অঞ্চলের বাসের সময়ের কোনও ঠিক নেই। সেইজন্য সব সময়েই বাক্স-পেঁটরা ঝুড়ি বালতি পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে লাইন দিয়ে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে থাকে। খানিকটা যাওয়ার পর মেধার তবু বসবার জায়গা হয়েছিল। দেবপ্রিয় সারাটা পথ ঠায় দাঁড়িয়ে। বাস থেকে নেমে রিকশা ধরল দেবপ্রিয়—‘গাঙ্গুলিবাগান।’
রিকশার হুড তুলে দেওয়া হয়েছে। হুডটা ঘোমটার মতো সামনে অনেকখানি আড়াল করে রয়েছে। মেধা মুখ বাড়িয়ে দুদিকে দেখছেন। বললেন—‘তোদের এদিকটা বেশ প্রসপারাস না রে দেব? হুগলি, বর্ধমান দুটোই বর্ধিষ্ণু জেলা।’
দেবপ্রিয় বলল—‘হুঁ।’
—‘তুই কি আমার ওপর রাগ করে আছিস নাকি?’
দেব বলল—‘না।’
—‘শোন। সাহস ভালো। দুঃসাহস ভালো না, এটা একটা কথার কথা নয়। একেবারে নির্জলা সত্যি কথা। যার যা কাজ, তাকেই সেটা করতে দেওয়া ভালো।’
দেবপ্রিয় বলল—‘আপনার ধারণা পুলিস কিছু করবে?’
—‘তোর নিজেরই তো তাই ধারণা! না হলে তুই পুলিসকে ওই ঘাঁটিগুলোতে লীড করার জন্য অত কষ্ট করলি কেন? তোকে তো সবই বলেছি। রণজয় বিশ্বাসের ওপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে। ইতিমধ্যে তুই মনে রাখিস তুই ডাক্তার। যে সব ডাক্তার মহামারিতে মাছি-মশার মতো থ্রাইভ করে তেমন না। তোর কাজ হবে প্রতিরোধ করতে শেখানো। তুই সামাজিক ব্যাধিরও ডাক্তার। ড্রাগের মতো এই সব এপিডেমিক সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে হলে শুধু পুলিসি সার্জারিতে কিছুই হয় না। ভেতর থেকে মূল নষ্ট করতে হবে। প্রলোভন কোন না কোন রূপে বরাবর থাকবেই। সর্বনাশা প্রলোভন। আমরা প্রলোভিত হবো না, নষ্ট হবো না, এমনিভাবে আমাদের নিজেদের গড়তে হবে। ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করে ড্রাগের প্রতি তাদের আকর্ষণ নষ্ট করতে হবে। একমাত্র তখনই শয়তানরা ফণা গুটোবে, নইলে নয়।’
—‘তাহলে আপনি কেওড়াখালির নিরঞ্জন মাস্টারমশাইকে টি ভি সেট দিতে এতো আপত্তি করছেন কেন?’
মেধা বললেন—‘তোর কাছে নিরঞ্জন বুঝি নালিশ করেছে?’
‘না। আমি মৈথিলীর কাছে ঘটনাটা শুনলুম।’
—‘শোন ওদের টি ভি সেট নিশ্চয়ই দেবো। তার আগে রুচিটা সামান্য গড়ে দেবার চেষ্টা করছি। প্রথমত একবার ভিশূয়াল দেখতে আরম্ভ করলে ওরা আর বই পড়তে চাইবে না। বইয়ের নেশাটা আগে ধরিয়ে দেওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, ওরা টি ভি পেলেই শনিবার-রবিবার এবং অন্যান্য হাজারোবার ওই সব অবাস্তব এবং ভালগার সিনেমাগুলো দেখবে। দেখে হাঁ করে থাকবে। অল্পবয়সী মেয়েগুলো হিরোর স্বপ্ন দেখবে আর ছেলেগুলো হিরোইনের স্বপ্ন দেখবে। আচ্ছা, তোরাও তো এই সব পোস্টার, কখনও সখনও এই সব সিনেমাও দেখিস, কিন্তু এসব কি তোদের বিভ্রান্ত করে? করে না। তার কারণ তোদের মনগুলো রুচির দিক থেকে সাবালক হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রামের এই সব বয়স্ক মানুষগুলো, যারা নিজেদের বংশগত কাজ এত ভালো জানে, এতো পাকা বিষয়ী, রুচির দিক থেকে তারাও কিন্তু নাবালক। অল্পবয়সীদের তো কথাই নেই। আগে ওরা বই ভালোবাসতে শিখুক। বই পড়ে কল্পনা শক্তির ব্যবহার করে, বুদ্ধির ব্যবহার করে মাথার মধ্যে অডিও ভিশূয়াল তৈরি করতে পারুক তারপর তুই ওদের যত খুশি টি ভি সেট দে, অসুবিধে নেই।’
দেবপ্রিয় চুপ করে রইল। মেধা বললেন—‘আমার কথা কি তুই মানতে পারছিস না?’
দেবপ্রিয় বলল—‘না, ভাবছি। একেকটা গ্রাম পুরো মার্জিত, পরিশীলিত হবে, তারপর তারা সভ্যজগতের যন্ত্রপাতির সংস্পর্শে আসবে। কী দীর্ঘ প্রতীক্ষা?’
হু-হু করে হাওয়া এসে ওদের চুল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মেধার শাড়ির সামনেটা হাওয়ায় ফুলে উঠছে, তিনি দু’হাতে তাকে ধরে আটকে রাখছেন।
মেধা হেসে বললেন—‘তুই কি ভেবেছিলি তোরই একার ওপর ভুবনের ভার? প্রাণহীন পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হতে কত সময় লেগেছে ভেবে দ্যাখ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে সভ্যজগৎ! আমরা আমাদের যৌবনের অধৈর্যে ভাবি সব সমস্যার সমাধান চট করে হয়ে যাবে, একবার একখানা বিপ্লব করে ফেলতে পারলেই। কিন্তু আসল কাজটা হল মানুষের মন পাল্টানোর কাজ। সেটাতে তেমনভাবে কেউ হাত দেয় না। ধর্মগুরু যাঁরা তাঁরা আধ্যাত্মিক দিকটার ওপর জোর দেন, আধ্যাত্মিকতা সবার ধাতে হয় না, মনীষীরা বুদ্ধির ব্যবহার করতে শেখান, মনকে মুক্ত রাখবার শিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁরাই আবার একটার পর একটা তত্ত্ব তৈরি করে বুদ্ধিরই পায়ে শেকল পরিয়ে দ্যান, নীতি শিক্ষা—তা-ও দেখি মানুষের ওপর জোর করে চাপানো। আমার নিজের মনে হয় ছোট থেকে মুক্ত হৃদয়ে এবং মুক্ত বুদ্ধিতে কর্ম, মানবিক সম্পর্ক এবং জ্ঞানের চর্চা করা দরকার। সেই সঙ্গে আমাদের শিল্পবোধ জাগ্রত করতে হবে। নীতিবোধ সৌন্দর্যবোধ সহৃদয়তা খোলা মন—কর্মে প্রীতি এবং জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ এই সমস্ত মিললে একটা যথার্থ মানুষ তৈরি হয়। এই টোট্যাল হিউম্যান বীয়িংকে তৈরি করার জন্যই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, আমাদের সামাজিক বিন্যাস। দেশের রাজনৈতিক গঠন এই মানুষকে রক্ষা করবে, বিন্যস্ত করবে, প্রোমোট করবে। দু-চার দিনের আবেগ দিয়ে কিছু হয়নি, হবে না। তাই তো তোদের বলি ছাত্রসংঘের চেইনটা তোরা চালু রাখ। ছাত্রশক্তি মানে যুবশক্তি, বড়রা এতদিন সব রকম আন্দোলনে এদের ধ্বংসাত্মক, আত্মঘাতী কাজে ব্যবহার করেছে। আমার ইচ্ছে, এবার এরা সত্যি যা তাই হোক, এরা দেশের সংরক্ষিত শক্তিকূট, যা করবে সমস্ত অন্তর দিয়ে করবে, ওদের হাতে সংগঠনের কাজ, সৃষ্টির কাজ তুলে দাও, ওরা জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে করে যাবে কাজটা। সেই ফলটা এক্ষুণি পাবার জন্যে ধড়ফড় করিসনি।’
দেবপ্রিয় একটু হেসে বলল ‘আমার সমস্যাটা কি জানেন দিদি, আমি প্রচুর কাজ করতে পারি। কথা বলতে পারি না। এটাই আমার স্বভাব। আমার পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে, সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করে ছাত্রদের ভেতরে ড্রাগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজটা শক্ত।’
মেধা বললেন—‘আমি জানি দেব। সব মানুষেরই যদি একরকম ক্ষমতা হত, তাহলে বিচিত্র কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আমরা কোথায় পেতাম? বাগ্মিতা তবু মেলে, কিন্তু নিঃশব্দে কাজ করার লোক পাওয়া যায় না দেব।
রিকশাওয়ালা বলল—‘গাঙ্গুলিবাগানের হাতায় এসে পড়েছি, এবার কোন দিকে যাবো দাদা?’
—‘জোড়বাংলার দিকে চলো’, দেবপ্রিয় বলল।
এই অঞ্চলের নাম পাল্টে দেবার অনেক চেষ্টা করেছেন পৃথ্বীন্দ্রনাথ। দায়পুর হাইস্কুল, দায়পুর পশু-পক্ষি-পালন প্রকল্প, তারপর সমস্ত জায়গাটার নাম রাখেন তিনি ‘বনশ্রী’। বড় বড় করে লেখাও আছে নামটা সাইনবোর্ডে। কিন্তু নানান নামের আসা-যাওয়ার মধ্যে দিয়ে গাঙ্গুলিবাগান নামটা ঠিক টিকে আছে। জোড়বাংলা পৃথ্বীন্দ্রনাথের নিজের থাকার জায়গা। দেবপ্রিয়র ইচ্ছে দিদিকে জোড়বাংলায় রেখে সে আপাতত বাড়ি চলে যায়।
‘বনশ্রী’র হাতায় ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে মেধার সমস্ত দেহ-মন কণ্টকিত হয়ে উঠল। বঙ্গভূমি সবুজেরই দেশ, প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের দেশ। কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, যথেষ্ট যত্ন ও সৌন্দর্য সচেতনতার অভাব যে কারণেই হোক, গ্রামাঞ্চলে গেলেও একটা এলোমেলো সবুজ, খয়েরি, হলুদ মেশানো ধ্যাবড়া ছবি ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। মনে হয় একটা ছবিকে বারবার ধোয়া হয়েছে, শিল্পীর পছন্দ না হওয়ায়। ইংলন্ড বা আমেরিকার গ্রামাঞ্চলে সেই সবুজকে খানিকটা আকার দেওয়ার চেষ্টা হয়। পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা হয়। বিজলিচালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহারের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। আজ এতদিন পর গাঙ্গুলিবাগান নামক এই জায়গাটাতে এসে তিনি পাশ্চাত্য গ্রামাঞ্চলের সেই প্রিয় সৌন্দর্য খুঁজে পেলেন। ছায়াবৃক্ষগুলোকে রেখে আশপাশের ছোট গাছগুলোকে কেটে ফেলা হয়েছে। দুটো তিনটে পরিষ্কার লাল রাস্তা ভেতরে চলে গেছে, দুধার সবুজে-সবুজ। তার মধ্যে দিয়েও ছড়িয়ে পড়েছে লাল পথের শাখা-প্রশাখা। শুকনো পাতা কাটি-কুটি ঝুড়িতে তুলতে তুলতে এগিয়ে চলেছে বেশ কয়েকটি ডুরে শাড়ি-পরা মেয়ে। ঘন সবুজের মধ্যে পা ডুবিয়ে এখানে ওখানে কয়েকটি লাল টালি ছাওয়া সাদা বাড়ি, সাইনবোর্ডে নামগুলো লেখা আছে। তাঁতঘর, আচারঘর, সেলাইঘর, বীজঘর। পাখি ডাকছে বিচিত্র সুরে এই বেলাতেও। একটা মাছরাঙা নীল আলোর ঝলক তুলে তীব্রগতিতে উড়ে গেল। চকচকে আয়নার মতো জল ডানদিকের বাঁধানো পুকুরে। তার ওধারে ঘন কালচে সবুজ গাঢ় গম্ভীর বনভূমি। দেবপ্রিয় বলল—ওইটাই বনশ্রীর প্রধান ফলবাগান। তরুণ শাল, সেগুন, দেবদারুর মধ্য দিয়ে জোড়বাংলার পথ। মাঝে মাঝেই খুঁটিতে পোঁতা পথ-নির্দেশক।
পৃথ্বীন্দ্রনাথ মাথায় বেতের টুপি পরে হনহন করে হাঁটছিলেন। তাঁর স্কুল, ডেয়ারি, পোলট্রি, সবজি ক্ষেত, ফলবাগান সব এতদিনে আপনা-আপনি চলতে আরম্ভ করেছে। তিনি শুধু ঘুরে ঘুরে দেখেন। দায়পুর গ্রামের বহু মানুষ তাঁর এই বনশ্রীতে নিযুক্ত। বাচ্চারা পড়তে আসে দুটো শিফ্টে, ছটা থেকে দশটা, দশটা থেকে চারটে, সন্ধে ছটা থেকে বায়োগ্যাসের আলোয় শুরু হয় বয়স্ক শিক্ষার স্কুল। এই সব স্কুলের শিক্ষকরা স্থানীয়। তিনি দুটো স্কুলেই কিছু কিছু ক্লাস নেন। এই স্কুল থেকে পাশ করে যারা কলেজে পড়তে চায় তারা সদরে কিংবা অন্য কোনও শহরে চলে যায়। কলেজ তৈরির আশা পৃথ্বীন্দ্রনাথ ছেড়ে দিয়েছেন। আজকাল আর প্রয়োজনও বোধ করেন না। কিন্তু একটা কৃষি বিদ্যালয় যেখানে পশু-পক্ষী পালন, মৌ চাষ, মাছ-আবাদ সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেটা তাঁকে শুরু করে দিয়ে যেতেই হবে।
একটা জিনিস তিনি এ ক বচ্ছরে পেরেছেন। তা হল দায়পুরের লোকেদের বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জন। প্রথম যখন আসেন তখন এরা সাঙ্ঘাতিক প্রতিরোধ করেছিল। তাঁর বাগানের ফল-ফুলুরি, গাছের কাঠ, ভাঙাচোরা ঘরবাড়ির ইঁট, দরজা-জানলা এসব বহুদিন ধরে এদের কাজে লেগে এসেছে। পঞ্চায়েতের সঙ্গে মিলে ভুয়ো দলিল দেখিয়ে তাঁর সমস্ত জমি এরা বর্গা করে নেবার চেষ্টা করেছিল। সেই সব পড়ো জমি, বাড়ি, বিশাল বিশাল বাগান তিনি একলা লড়ে উদ্ধার করেছেন। তিনি এদের রুজি দিয়েছেন, এই বিশাল বনশ্রী প্রকল্প গড়ে উঠেছে পুরোপুরি দায়পুরের লোকেদের হাতে। একজনও ‘বহিরাগত’ নেই। কৃষি ঋণের দরখাস্ত থেকে যে কোনও রকম বিষয়ে পরামর্শ তারা পৃথ্বীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য কারো কাছে নেয় না। বয়স্ক শিক্ষার প্রসার এখন এখানে এতদূর হয়েছে যে গ্রামের বয়স্ক লোকেরা তাঁর কাছে বিশ্বের ইতিহাস, ভূগোল এমন কি দর্শন পর্যন্ত পড়তে আসে। তাদের চাহিদাতেই বনশ্রীর লাইব্রেরি এতো সমৃদ্ধ। পঞ্চায়েতও গ্রামের লোকেদের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ আজকাল করতে সাহস করে না। সবচেয়ে আনন্দের কথা ‘বনশ্রী’ বাদেও দায়পুর গ্রামের বাকি অংশ যেন বনশ্রীর উদাহরণ অনুসরণ করেই ক্রমেই সুন্দর, সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, এবং উচ্চশিক্ষার তাগিদ ছাড়া অন্য কোনও কারণে গ্রামের কেউ শহরমুখো হতে চায় না। উপার্জনের কোনও না কোনও উপায় তাদের এখানেই হয়ে যায়। যারা মুশকিলে পড়ে তারা পৃথ্বীন্দ্রনাথের কাছে পরামর্শ নিতে আসে। এইভাবেই হয়েছে গ্রামের বহু ছেলের নিজস্ব রিকশা, দু-একজনের ট্যাকসি, ধানের কল, গম পেষাই কল, মিষ্টির দোকান, মনোহারি দোকান, ছোটখাটো সরাইখানা।
তিনি দেবপ্রিয়কে দেখতে পাননি। মুখ নিচু করে কৃষি বিদ্যালয়ের বিভাগ-বিন্যাসের কথা চিন্তা করতে করতে হাঁটছিলেন। ভারি সুন্দর একটি জামরঙের শাড়ি তাতে লম্বা লম্বা কালো কলকা পাড় চোখে পড়তে মুখ তুলে তাকালেন। পাশাপাশি দেবপ্রিয় ও মেধা ভাটনগরকে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।
দেবপ্রিয় বলল—‘মেজজেঠু, ইনি আমাদের মেধাদি, তোমার বনশ্রী দেখতে এসেছেন।’
পৃথ্বীন্দ্রনাথের মুখের ভাব দ্রুত বদলে বদলে যাচ্ছে। তিনি বললেন—‘আসুন, নিশ্চয়ই দেখবেন।’
তখন পৃথ্বীন্দ্রনাথের ‘বনশ্রী’র সংসার এতো বড় হয়ে গেছে এবং শুধু তদারকি ও লেখা-জোকার কাজেই তাঁকে এত সময় দিতে হয় যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য কিছুটা এ সংসারের লোকজনের ওপর তাঁকে নির্ভর করতেই হয়। ইদানীং তাঁর রান্নাবান্না চাষের কর্মীরাই পালা করে করে দেয়। তিনি সেদিনের ছেলেটিকে ডেকে কিছু নির্দেশ দিয়ে এলেন।
দেবপ্রিয় বলল—‘জেঠু, আমি কিন্তু এখন সোজা বাড়ি চলে যাবো।’
—‘তাই যা। বাড়িতে বলে এখানে চলে আয়। একসঙ্গে খাবো।’
—‘না জেঠু তা হয় না। মা খুব রাগারাগি করবে। আমি তো এখন দায়পুরে থাকছি।’ সে আর দাঁড়াতে চাইল না। বেশ বেলা হয়ে গেছে।
—‘তাহলে আমার সাইকেলটা নিয়ে যা’ পৃথ্বীন্দ্রনাথ বললেন। সাইকেলটা নিয়ে দেবপ্রিয় প্রায় তৎক্ষণাৎ রওনা দিল। মোরাম-ছাওয়া পথে সাইকেলখানা শাঁ শাঁ করে চলে গেল, দেবপ্রিয়র শার্টের পেছনটা বেলুনের মতো ফুলিয়ে দিয়ে। চলতে চলতে যেখানে বাঁক নিল সেখানে দেবপ্রিয় হাতটা উঁচু করে নাড়ল, পৃথ্বীন্দ্র তাঁর টুপিটা নাড়ছিলেন, মেধা তাঁর রুমাল শুদ্ধু হাত।
দুজনে পেছন ফিরলেন। একটু এগিয়েই জোড়বাংলায় ওঠবার নিচু নিচু মাটির ধাপ। মেধা বললেন, ‘আপনার এই বনশ্রী কন্যাটির কথা অল্পসল্প শুনেছি দেবের মুখে। ও তো কথা বলে না। কাজে যা করবার করে। আমার কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে। এতে সবুজ, এত সুস্থ নবীন এবং সবুজ। প্ল্যানিং রয়েছে অথচ প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়নি…আমার চোখ মন ভরে যাচ্ছে।’
—‘বিকেলবেলা আপনাকে সব ঘুরে ঘুরে দেখাবো’ সংক্ষেপে বললেন পৃথ্বীন্দ্রনাথ। সুন্দর ঠাণ্ডা কলঘরে চমৎকার ঠাণ্ডা জল ধরে রাখা। মেধা অনেকক্ষণ ধরে সেই ফুলের গন্ধমিশ্রিত জলে প্রাণভরে চান করলেন। চতুর্দিকে পাখি ডাকছে। ঘুঘু, কাক, কোকিল তো আছেই। আরও নানা রকম নাম-না-জানা মিষ্টি স্বরের পাখি থেকে থেকেই শিস দিয়ে উঠছে। চান সেরে একটা সাদা ধবধবে ভয়েল পরলেন মেধা, সাদা ব্লাউস। চুলগুলো তোয়ালে দিয়ে নিংড়ে নিয়ে তোয়ালেশুদ্ধুই মাথার ওপর বেঁধে রেখেছেন। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরটাতে এসে দেখলেন জানলায় খসখস টাঙানো। তাতে সদ্য জলের ছিটে দেওয়া হয়েছে। ভারি সুন্দর গন্ধ ঘরময়। খসখস একটু তুলতেই বহুদূর পর্যন্ত সবুজ ক্ষেত দেখা যায়। হু হু করে হাওয়া আসছে, খসখসের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ঘরে ঢুকছে। দেয়ালে গোল আয়না। বাঁশের কারুকার্যকরা ফ্রেমে আটকানো। ভালো করে চুল আঁচড়ে মেধা নিজের ব্যাগটা বিছানার পাশের টেবিলে রাখলেন, খালি পায়ে বাংলোর সামনের দিকে চলে এলেন যেখানে সুপরিসর, বাঁশের জাফরি-ঢাকা বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে পৃথ্বীন্দ্রনাথ অন্যমনে চুরুট খাচ্ছিলেন। পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে নিঃশব্দে বসলেন মেধা। দুজনের কারোই বেশি কথা বলবার মেজাজ নেই। তাঁতঘর সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন করলেন মেধা। পৃথ্বীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, কেওড়াখালিতে পরবর্তী প্রোগ্রাম কি? পৃথ্বীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন মেধা উত্তর দিলেন। দু-একটা করে কথা নির্জন গ্রীষ্ম দুপুরের আলোকিত প্রকৃতির নৈঃশব্দ্যে টুপটাপ চিলের মতো ডুবে যেতে লাগল। রমেশ নামে ছেলেটিকে এখানেই খাবার পরিবেশন করতে বললেন পৃথ্বীন্দ্রনাথ। যা কিছু আহাৰ্যবস্তু সব ‘বনশ্রী’র। ভাত এবং সুগন্ধে মাত করা মুগের ডাল, পটল ভাজা এবং আলুর দম। লাউ এবং পালং শাক। এখানকার ডেয়ারির মাখন এবং দই।
খাওয়া হয়ে গেলে পৃথ্বীন্দ্রনাথ মেধার কাছ থেকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বিদায় নিলেন। বেলা চারটে সাড়ে চারটে পর্যন্ত বেতের ঝুড়ি চেয়ারে সেখানে বসে বসেই কাটিয়ে দিলেন মেধা। বহুদিন পর এমনি গ্রামীণ দুপুর, গ্রামীণ বিকেল। শালপাতার মধ্যে দিয়ে হাওয়ার দাপাদাপি, রোদ্দুরের রং-বদল, আকাশের রং-বদল, পাখির ডাকে আস্তে আস্তে ক্লান্তির আভাস, দূরে দূরে কর্মীদের যাতায়াত, সাইকেল চালিয়ে বেশ কিছু অল্পবয়সী মেয়ে বনশ্রীর সীমানা পার হয়ে চলে গেল। স্কুলঘর থেকে ঘণ্টা বাজার শব্দ মৃদুতর হয়ে হাওয়ায় ভেসে আসছে। দলে দলে ছেলেমেয়েরা, তাদের পেছনে শিক্ষক, সব বেরিয়ে এলেন, একটা বড় পাখির দলের মতো ওরা ওদিকের পথ দিয়ে ডানা মেলে চলে যাচ্ছে। মেধা একটু উঁচু থেকে, অনেক দূর থেকে এই মনুষ্যশাবকের ঝাঁককে পাখি এবং অন্যান্য পশুর পালের সঙ্গে একই বিবর্তন রেখার উঁচুর দিকে অবস্থিত বলে চিনতে পারলেন অনায়াসে। দল বেঁধে যাচ্ছে সব, পায়রার ঝাঁকের মতো, একটু দূরে পেছনে একটি দুটি শিক্ষক। আকাশে একলা চিল। আপন মহিমায় ঘুরে বেড়ায়।
পৃথ্বীন্দ্রনাথ যখন এসে বসলেন তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে বেজে গেছে। যদিও বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে এই পাকাধানের রঙের সোনালি দিন ক্রমশই আয়ুষ্মান, আরও আয়ুষ্মান হয়ে উঠছে।
পৃথ্বীন্দ্রনাথ একটু হেসে বললেন—‘কিছু খাতা-পত্র দেখা ছিল। তারপর একটু দিবানিদ্ৰামতোও হয়ে গেল।’ আপনি কি এখানেই সারা দুপুর কাটালেন!
—‘খুব ভালো লাগছিল, এখান ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না।’ মেধা নড়ে চড়ে বসলেন।
—‘ঘরের মধ্যেও কিন্তু খুব ভালো লাগত।’
রমেশ ধোঁয়া-ওঠা কফির কাপ রেখে গেল। মেধা এক চুমুক খেয়ে বললেন—দেবপ্রিয়কে ওর ফাইন্যাল পরীক্ষা পর্যন্ত আপনার জিম্মা করে দিয়ে গেলাম। এ সময়টা ওর কলকাতায় যাবার দরকার নেই।’
পৃথ্বীন্দ্রনাথ বললেন—‘জরুরি কারণ আছে নাকি?’
মেধা বললেন— ‘কারণ আছে। কতটা জরুরি আমি নিজেও জানি না। যাঁর জানবার কথা এমন কারো নির্দেশ পালন করছি।’
পৃথ্বীন্দ্রনাথ অন্যদিকে চেয়ে বললেন—‘ওরা কি ভেতরে ভেতরে আবার কোনও বিপ্লবের আয়োজন করছে?’
মেধা বললেন—‘বিপ্লব? হয়ত। বিদ্রোহ নয়। আপনার কেন এ কথা মনে হল?’
—‘প্রথমত ওর আত্মগোপন করা দরকার হয়ে পড়েছে বলছেন, অথচ কারণটা খুলে বলছেন না…’
উনি চুপ করে আছেন দেখে মেধা বললেন—‘আর দ্বিতীয়ত?’
—‘দ্বিতীয়তঃ ষাটের দশকের শেষে, সত্তরের গোড়ায় যে মেধা ভাটনগরকে লেখা অমিয় সান্যালের চিঠি সেনশর করেছি তিনি এদের লিডারশিপ দিচ্ছেন।’
মেধা যেন আকস্মিক আঘাতে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলেন। একটু পরে অস্ফুট গলায় বললেন—‘আপনি?’
—‘ডি এস পি ছিলুম সে সময়টায়।’
—‘সেনশর করা চিঠিগুলো নিয়ে কী করতেন?’
—‘কোনোটা কোনোটা স্পেশ্যাল ফাইলে রাখা হত, নির্দোষ বিবেচিত হলে পাঠিয়ে দেওয়া হত।’
—‘সব পড়েছেন?’
—‘স-ব।’
—‘যে সব চিঠি আসত?’
—‘পোস্টে যা আসত, স-ব।’
—‘সেগুলো উনি পেতেন?’
—‘একই নিয়মে।’
মেধা খুব ধীর গলায় বললেন—‘চিঠির থেকে লেখকের গোটা চরিত্র বোঝা যায়?’
—‘বোঝাই আমাদের বিশেষ কাজ।’
—‘অমিয় সান্যালকে কি বুঝেছিলেন?’
—‘ক্লান্ত, হতাশ, আত্মনাশক।’
—‘মেধা ভাটনগরকে?’
—‘বৈপ্লবিক, আশাবাদী, চির-বিদ্রোহী।’
মেধা বললেন, ‘দেবপ্রিয় তার নিজস্ব উদ্যোগে, আমাদের কাউকেও ঘুণাক্ষরেও না জানিয়ে ড্রাগ-ব্যবসার পেছনে লেগেছিল, পুলিস তাকে তারই নিরাপত্তার জন্য ধরে, আমি খবর পেয়ে ছাড়াতে যাই। আমার প্রতি পুলিসের এই নির্দেশ।’
—‘কর্তাটি কে?’
—‘ডি আই জি রণজয় বিশ্বাস, আই. পি. এস, চেনেন?’
—‘রণজয় বিশ্বাস…রণজয়…’ পৃথ্বীন্দ্রনাথ বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে কপালে চাপ দিতে লাগলেন…‘মাস্ট বি সামবডি ফ্রম দা সেভেনটি এইট গ্রুপ’, না, মনে করতে পারছি না।
মেধা বললেন, ‘তাঁর একটা প্রাইভেট ফোন নাম্বার আমার কাছে আছে। ওই নাম্বারে সব সময়ে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। আপনি নাম্বারটা আপনার কাছে রাখুন।’
তিনি উঠে গিয়ে নিজের হাতব্যাগের মধ্যে থেকে নোট-বইটা নিয়ে এলেন। নম্বরটা পৃথ্বীন্দ্রনাথের ডায়েরিতে লিখে দিতে দিতে বললেন—‘ছাত্ররা নিজেদের সদবুদ্ধিতে যা করে করে, আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতা ও সংকল্পের সারটুকু তার সঙ্গে যোগ করে দিই। আবারও আপনাকে বলছি ছাত্রদের এই সব কার্যকলাপ বৈপ্লবিক, সমস্ত দেশের গণচেতনায় আস্তে আস্তে আমূল পরিবর্তন আনবে। হয়ত অনেক দিন লাগবে, তবু সে দিন যাতে নিশ্চিত আসে, তারই জন্য আমাদের যা কিছু উদ্যোগ। কিন্তু, আপনাকে আমি ঠিক মেলাতে পারছি না। সেভেনটির পুলিসের বড় কর্তা যিনি নিঃসন্দেহে নকশাল দমনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন…’
পৃথ্বীন্দ্রনাথ অস্বাভাবিক ভারি গলায় হাত দুটো মেলে বললেন ‘এই হাতে অনেক ভেঙেছি। ভাঙতে হয়েছে, মিস ভাটনগর। তাই অবসর নেবার পর ভাবলুম যদি কিছু গড়ে যেতে না পারি, ঈশ্বরের কাছে, আমার নিজের অন্তরাত্মার কাছে আমার আত্মপক্ষ বলে কিছু থাকছে না। কিছু আমি গড়বই।’ মেধা চুপ করে আছেন। পৃথ্বীন্দ্রনাথ ডান হাতের তেলোয় বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে যেন অদৃশ্য রক্তের দাগ মোছবার চেষ্টা করছেন, বললেন ‘বনশ্রী’ গড়েছি, ‘বনশ্রী’র প্রেরণায় গড়ে উঠেছে দায়পুর। দেবপ্রিয়ও আমার নিজের হাতের একসপেরিমেন্ট। মানস পুত্র যাকে বলে। হী ওয়াজ প্রাইমারিলি মেন্ট ফর দিস প্লেস, বাট হী ইজ ফাস্ট আউটগ্রোয়িং বনশ্রী অ্যান্ড দায়পুর। এটা আমি চাইনি। মিস ভাটনগর, আমাদের ব্যক্তিগত অ্যামবিশনকে আমরা যদি একটু কাট-ছাঁট না করি তাহলে এই পঁচাশি কোটির দেশ শেষ পর্যন্ত একটা নোংরা বস্তি অথবা একটা ভয়াবহ উন্মাদাগার হয়ে যাবে। এখন দেখছি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙক্ষাও না, দেবপ্রিয় দেশসেবার অন্য এক বিপজ্জনক পথ নিচ্ছে। নেওয়াই হয়ত স্বাভাবিক। অল্পবয়স, রক্ত গরম, ট্যালেন্টেড ছেলে। কিন্তু আমরা তো বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি মিস ভাটনগর। ডেটাগুলোকে, একসপেরিমেন্টের ফলগুলোকে তো আমরা আর অগ্রাহ্য করতে পারি না। আমাদের অভিজ্ঞতার ডেটা-ব্যাঙ্ক বলছে এভাবে হচ্ছে না। প্রত্যেকটা বিপ্লবই এক-একটা লং টার্ম ফেইলিওর। অল অফ দেম হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু অ্যান্ড বিগিন ফ্রম স্কোয়্যার এ। দেবপ্রিয়কে স্যাক্রিফাইস করতে হলে…আই ডোন্ট নো হোয়্যার আই এগজ্যাক্টলি স্ট্যান্ড…’ মাথাটা নাড়তে লাগলেন পৃথ্বীন্দ্রনাথ।
বিকেল গাঢ় হয়ে আসছে। চারদিকে কিরকম একটা ভিজে খড়ের মতো রঙের রোদ্দুর। হাওয়াটা আরও উত্তাল, উদ্দাম হয়ে উঠছে ক্রমশ। পাখির ডাক আরও যূথবদ্ধ। একটা দুটো একলা পাখির কূজন থেকে বহু পাখির কাকলি। বাংলোর পাশে একটা মহীরুহ জামগাছ। সেটার মাথা ক্রমশ টিয়াপাখিতে ভরে যেতে থাকে। মেধা বলেন—‘একটা “বনশ্রী” দেবপ্রিয়র ক্ষমতার পক্ষে একটু ছোট হয়ে যাবে পৃথ্বীন্দ্রদা। আরও অনেক এমন শ্রীভূমি পরিচালনা করবে ও। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙক্ষা তো নয়ই, ছোট মাপ, ছোট গণ্ডির কোনও সমাজ-ভাবনাও ওকে ধরে রাখতে পারবে না। নেতা নয়, ও অধ্যক্ষ হবে এই কর্মযজ্ঞের। বিপ্লব সম্পর্কে আপনি যা বললেন আমি তার সঙ্গে মোটামুটি একমত। খালি আমার মনে হয় এই সব অসফল বিপ্লবগুলোও নিশ্চয়ই ভাবী যুগ আরম্ভের অজানা পর্যায়গুলো কিছু-কিছু খুলে দিয়ে যায়। তা ছাড়া, নেতি নেতি করে এগোনোও তো অগ্রগতি!… আপনার আরও জানা দরকার রণজয় বিশ্বাস যিনি এখন পশ্চিমবঙ্গে ড্রাগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছেন তিনি একেবারে দেবপ্রিয়র আদলে বসানো। আমার সহপাঠী ছিলেন, আমি জানি। তিনি সাহস এবং সেই সঙ্গে সতর্কতা নিয়ে এগোচ্ছেন। তাঁকে অবিশ্বাস করা আমাদের ঠিক হবে না।’
পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখ তুলে বললেন—‘আপনি কি তাহলে অনেক বদলে গেছেন?’
—‘এ কথা কেন বলছেন?’
—‘পত্রালাপের ভাটনগরকে যদ্দূর মনে পড়ে খুব আবেগপ্রবণ, মরিয়া এবং সংশয়াকুল।’
মেধা বললেন, ‘সব মানুষই বদলায়। রাজনীতিকদের রং বদল নয়। অভিজ্ঞতার নিরিখে নিজেকে, নিজের ফর্মকে ক্রমাগত যাচাই করে করে বদলে যাওয়া। কিন্তু একদম মূলের দিক থেকে দেখতে গেলে মেধা তো বদলায়নি! আপনিই যে একটু আগে বললেন—সে আশাবাদী, বৈপ্লবিক, চির-বিদ্রোহী!’
—‘তাহলে একি ঋতুবদল?’
—‘তাই বা পুরোপুরি বলতে পারছি কই? বেসিক ঋতুটা তো বসন্তই দেখছি। গ্রীষ্মের খরা, বর্ষার প্লাবন, শীতের শুষ্কতা সবই সাময়িক! ঋতুরাজ আমাকে যেন পুরোপুরি অধিকার করে রেখেছেন। সৃজনের সম্ভাবনার বীজগুলোকে নিষিক্ত করতে করতেই তো আমার সময় চলে যায়। খরা-বন্যার কথা ভাবতে সময় পাই কই?’ মেধা মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন।
পৃথ্বীন্দ্রনাথের মাথার চুলগুলো সব সাদা। নিয়মিত ব্যায়াম আর স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনে কর্মঠ, উজ্জ্বল শরীর। চোখ ঝকঝক করছে। বললেন—‘বসন্ত যাকে জীবনের গোড়াতেই নিষ্ঠুরভাবে ঠকিয়েছে এমন মানুষকে এভাবে বসন্তের জয়গান করতে আমি এই প্রথম শুনলুম।’
মেধা বুঝলেন ইনি অনেক জানেন। তাঁর জীবনের লুকোনো ইতিহাসের পাতাগুলো ইনি ঘনিষ্ঠভাবে পড়ে নিয়েছেন। হয়ত মেধা নিজেও যা জানেন না, তারও অনেক এঁর জানা। মানুষটি স্বল্পবাক, কিন্তু ঋজু এবং গভীর। তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন—‘বিশ্বাস করুন দাদা, আমি ঠকিনি। আমার কিছুই হারায়নি। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে নিলেও দেখছি পূর্ণই বাকি থেকে যাচ্ছে।’
অধ্যায় : ২০
মেডিক্যাল কলেজের ইনটার্নী মৈথিলী ত্রিপাঠীর দিনগুলো খুব ব্যস্ত কাটছে। ভীষণ খাটতে হচ্ছে। এদিকে, সেদিকে। আবার এই দম-বন্ধ-করা কাজ আছে বলেই হয়ত বাঁচোয়া। বেশ কিছু দিন ধরে তার মনটা খুব বিষন্ন হয়ে আছে। বার বার সে এই মন খারাপটাকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে, পারছে না। মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে সে উত্তরমুখো হাঁটতে লাগল। এখন উত্তর-দক্ষিণ কোনও দিকেই চট করে ওঠার মতো বাস-ট্রাম পাওয়া যাবে না, তাকে যেতে হবে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। প্রমিতকে এখানেই একটা নার্সিংহোমে দেওয়া হয়েছে আজ বেশ কিছু দিন হয়ে গেল। ডাক্তার আপাতত সময় নিয়েছেন চার মাস। হয়ত তার চেয়েও বেশি লাগতে পারে। প্রমিতের যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না। প্রমিত, উজানের সঙ্গে ছোট থেকে এক স্কুলে পড়েছে সে। ওদের সঙ্গে সে খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রমিত যে এইভাবে তাদের চোখ এড়িয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়বে, এটা তার কাছে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে প্রমিতদের একটা ফ্ল্যাট বছর তিনেক আগে খালি হয়ে যায়। প্রমিত মায়ের কাছ থেকে সেই ফ্ল্যাটটা ছাত্রসংঘের নাম করে চেয়ে নেয়। সেখানেই আসত ওর নেশার সঙ্গীসাথীরা। ওখান থেকেই ওরা প্রমিতকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করে। সবচেয়ে ভয়ের কথা হচ্ছে, মাত্র এই তিন-চার বছরের মধ্যে প্রমিত হেরোইন তো নিয়েইছে, মিফকুয়ালোনের বড়ি খেয়েছে, হ্যালসিনোজেনস গ্রুপের ড্রাগ পর্যন্ত নিয়েছে। ডাক্তার বলছেন ওর অবস্থা খুবই খারাপ। জটিল। প্রমিতের ঘটনাটা জানবার পর এসব নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনা করেছে মৈথিলী। কিরকম ছেলেমেয়েরা সাধারণত ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয় তার মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ বেশ কয়েকটা পড়া হল। বিবাহ-বিচ্ছিন্ন বাবা-মার সন্তান, নানারকম সাংসারিক অশান্তি, বাবা-মার অমনোযোগ, উচ্চাকাঙক্ষার পূরণ না হওয়া, ক্রনিক অসুখ এইরকম নানা কারণ থাকে এর পেছনে। কিন্তু প্রমিতের সঙ্গে সে এসব মেলাতে পারছে না। প্রমিতের অবশ্য বাবা পাঁচ ছ বছর হল মারা গেছেন, কিন্তু মা ছেলেঅন্ত প্রাণ। তিনি অপেক্ষা করে বসে আছেন কবে ছেলে য়ুনিভার্সিটির পাট চুকিয়ে তার বাবার ব্যবসার হাল ধরবে। তিনি এখন বিশ্বস্ত কর্মচারীদের সাহায্যে কোনমতে চালিয়ে নিচ্ছেন। প্রমিতের স্বাস্থ্য ভালো। তার ফ্রাসট্রেশনের কোনও কারণই তো আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। ইদানীং সে নিজে মারুতি চালিয়ে সায়েন্স কলেজে যাচ্ছিল। তার বাবার মৃত্যুর কারণে যদি নিরাপত্তাবোধের অভাব কারো ঘটে, তো সেটা রঞ্জুমাসীর ঘটবে। ধনী গৃহবধূ। তিনি কোনদিন বাইরের কাজে অভ্যস্ত ছিলেন না। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর ব্যবসা গুটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কর্মচারীরা এসে কান্নাকাটি করতে লাগল। তাদের রুজি বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সেই অনভিজ্ঞ, অনভ্যস্ত হাতে হাল ধরলেন তো! এ সব প্রমিতের কাছেই ওরা শুনেছে বেশি। মাকে নিয়ে প্রমিতের যথেষ্ট গর্ব। গর্ব করার কারণ আছে। সেই প্রমিত এইভাবে ড্রাগের শিকার হয়ে গেল? ড্রাগ ধরার কথা তো তার! বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো যার মা স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছেন আজ দু বছর হয়ে গেল!
আকাশটা আজ কালচে হয়ে আছে। মনে হয় বৃষ্টি হবে, হোক। তার আগে প্রমিতের খবরটা নেওয়া দরকার। এখনও ওরা দেখা করতে দিচ্ছে না কাউকে। মাসী হয়তো এসে বসে থাকবেন, মৈথিলীরা গেলে তাঁর ভালো লাগবে। কাকুর মৃত্যুতেও উনি এতোটা ভেঙে পড়েননি! আকাশের দিকে তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি পা চালাল।
মন খারাপের কারণ আরো একটা আছে। গুঞ্জন। গুঞ্জনের বাবা এয়ারফোর্সে আছেন। বরাবরই বদলির চাকরি। গুঞ্জন বোর্ডিঙে, হোস্টেলে মানুষ। ছোট থেকে মৈথিলী, লুকু, প্রমিত, উজানের সঙ্গে ওর মেলামেশা। খুব স্মার্ট, করিৎকর্মা মেয়ে। গ্র্যাজুয়েশনের পর ও ইনটিরিয়র ডেকারেশনের একটা ট্রেনিং নিয়েছিল। ওর রীতিমতো প্রতিভা আছে এ বিষয়ে। ভালো টাকা রোজগার করছিল ও। আর ক’মাস পর ভিসার ব্যবস্থা হয়ে গেলেই ও আমেরিকা চলে যাচ্ছে। প্রধানত এগজিকিউটিভ হবার ইচ্ছে ওর। এখানকার কোনও প্রতিষ্ঠানে এম. বি. এ করার সুযোগ পেল না। পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে জেরবার হয়ে গেছে। বলছিল—‘রোজগার করছি ভালোই। কিন্তু জানিস মৈথিল, আমাকে ওরা চেক পেমেন্ট করে না। সব ক্যাশ। অর্থাৎ দু নম্বরী টাকা। আমাদের মতো যত জন আছে সবাইকেই। যখন একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকে কিভাবে খাটিয়ে নেয়, ধারণা করতে পারবি না, শনি-রবিবার বলে কিছু নেই, দিন রাত বলে কিছু নেই। প্রাণ দিয়ে কাজ করি। কয়েকটা নোট ঠেকিয়ে দেয়। টাকাটা ভালোই। কিন্তু কোনও নিয়মিত চাকরি নয়, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার মুশকিল। যে কোনওদিন চাকরি চলে যেতে পারে, প্রভিডেন্ট ফান্ড, এটা-ওটা অ্যালাওয়্যান্স ইত্যাদি যেসব সুবিধে যে কোনও নিয়মিত চাকরির থাকে, তার কিছুই আমার নেই। একেবারে শূন্যে ভাসমান।’ ওর মামা আছেন ওয়াশিংটনে। তাঁর সাহায্যেই ও চলে যাচ্ছে, দুটো তিনটে জায়গায় এম. বি. এতে সুযোগ পেয়েছে। ফিরে আসবে কি না ভবিষ্যতই জানে! ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে এই রকম মূল্যবান দুজন কর্মীকে হারিয়ে তার মনটা বিষন্ন হয়ে আছে। শুধু কর্মীই নয়, বন্ধুও তো!
মেধাদি জানেন সবই। প্রমিতের নার্সিংহোমে তিনি নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন। গুঞ্জনের ব্যাপারটা শুনেও তিনি একই রকম শান্ত, অবিচলিত। বলছেন—‘আমি তো তোকে অনেক আগেই বলেছি মৈথিলী, নিজেদের ওপর খুব বেশি নির্ভর করিসনি। তোদের পরে, তার পরে, তার পরেও যদি তোদের বয়সী ছেলেমেয়েরা নিয়ম করে কাজটা করে যায় তবেই তোদের কাজ সত্যি সত্যি সার্থক হবে। গুঞ্জন তো তিন চার বছর যথেষ্ট খাটাখাটনি করেছে, তার চেয়ে বেশি সময় দিতে পারত ভালো। না পারে, তাতেও ইতরবিশেষ হওয়া উচিত নয়।’ গুঞ্জনের ভিসা যে কোনওদিন বেরোতে পারে, তাই ওর ফেয়ার ওয়েল উপলক্ষ্যে গতকাল মেধাদির বাড়িতে তাদের কয়েকজনের নিমন্ত্রণ ছিল। দিদি করেছিলেন খুব চমৎকার চিংড়িমাছের স্টু। ছোট ছোট রুটি বা ফুলকা তৈরি করল গুঞ্জন নিজে। উজান ওর বাবার রান্না মাংস এনেছিল। লুকু নিজে হাতে মালপো করেছিল। মৈথিলীর বৈজুদা করে দিল রাশিয়ান স্যালাড। দেবপ্রিয়ই একমাত্র যে বাসন-ধোয়া ছাড়া বিশেষ কিছু করল না। বুল্টুটা পর্যন্ত মনে করে ওর মায়ের ভাঁড়ার ঘর থেকে এক বোতল আমের আচার হাতিয়ে এনেছিল। দিদি বললেন—‘গুঞ্জন তুই তোর পছন্দমতো শিক্ষার জন্য চলে যাচ্ছিস আপাতত, তোর ভবিষ্যতের প্ল্যান কি?’
গুঞ্জন বলল—‘অনেস্টলি আমি জানি না মিস। আমার মামা বলছেন ইন্ডিয়ায় এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আমেরিকায় সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে থাকাও অনেক ভালো। আমাকে সেখানে গিয়ে দেখতে হবে তাঁর কথা সত্যি কিনা। সত্যি হলেও ওভাবে বাঁচতে হয়ত আমার সম্মানে বাধবে। তাছাড়াও বাবার রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে এলো, বাবার ইচ্ছে কলকাতাতেই কোথাও কাজ নেন। বরাবরের মতো বাবা-মাকে ছেড়ে থাকার আমার ইচ্ছে নেই। এতদিন তো হোস্টেলে হোস্টেলেই কেটে গেল। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব মিস?’
দিদি বললেন—‘কর, করে ফেল। অনুমতি চাইছিস যখন, খুব গোলমেলে কিছু জিজ্ঞেস করবি মনে হচ্ছে।’
—‘আপনি তো অনেক বছর ছিলেন, আপনি কী ফীল করতেন? কেন ফিরে এলেন?’
দিদি বললেন—‘আমি যখন ফিরেছি, তখন আমার বাবা-মা কেউই আর বেঁচে ছিলেন না, আমার বোনের সঙ্গে বরং ওখানে থাকতেই বেশি দেখা হত। ছাত্রছাত্রীরা খুব পছন্দ করত, পড়াশোনার ব্যবস্থা এত ভালো যে, পড়াটা ওখানে একটা আলাদারকম আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।’ দিদি চুপ করলেন।
কিছুক্ষণ পর গুঞ্জন বলল—‘তো?’
দিদি একটু লাজুক হেসে বললেন—‘জানিস, আমার প্রতিদিন মনে হত বড় লজ্জাকর ভাবে হেরে যাচ্ছি। আমেরিকা দেশটা তো ইমিগ্রান্ট্স্দেরই দেশ। এই বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বিশাল ব্যাপ্তি। তবু তো শান্তি, শৃঙ্খলা, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, সেই উন্নতিকে সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া সবই সম্ভব হচ্ছে। আমাদের দেশে ভাষা ধর্ম জাতির ভিন্নতা নিয়েই তো চিরকালের বসবাস। যাতে এই সব ভিন্নতা সত্ত্বেও সবাই মানুষের মতো বাঁচতে পারি সেই ফর্মূলাটা আমরা কেন কিছুতেই বার করতে পারছি না? কেনই বা পারবো না! এই ভাবনাটা আমায় সবসময়ে কামড়াত।’
লুকু বলল ‘কিন্তু দিদি, ইতিহাস তো বলছে ভারতবর্ষ বরাবরই বিচ্ছিন্ন। একমাত্র মুঘল শাসন এবং ইংরেজ শাসনের আওতায় এসে তবে ভারত এক হয়েছে। তার আগে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ তো চলতই!’
দিদি বললেন—‘তুই অশোককে ভুলে যাচ্ছিস। অশোকের সময়ে তো এ সমস্যা ছিল না!’
—‘সে সময়ে সেতুবন্ধনের মূল সূত্রটা কি ছিল? বৌদ্ধ ধর্ম?’
—‘বোধহয় না। ধর্ম না। অশোক তো বৌদ্ধধর্ম কারো ওপর চাপিয়ে দেননি!’ গুজ্ঞন এই সময়ে বলল— ‘দিদি, ধর্ম না হলেও, বোধহয় ধর্মের এসেন্স।’
দিদি বললেন—‘ঠিক। ধর্মের সার। টলারেন্সের শিক্ষা। বৃদ্ধ পিতা-মাতা, প্রতিবেশী, পশুপাখি, ভিন্ন জাতি ধর্ম সবই এই টলারেন্সের আওতায় পড়ে। ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে আমরা এইটুকু পাই। কিন্তু পুরনো ইতিহাসের ছাঁচে কি আর নতুন করে সমাজকে গড়া যায়? অশোকের অনুশাসন এখন মাস-মিডিয়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার ফল কি পুরোপুরি ফলছে? সমাজ এখন অনেক জটিল, সমস্যাও অনেক বেশি। মূল দুর্বলতাটা কোথায় জানিস? কুশিক্ষা। অশিক্ষা। অশিক্ষা তবু এক রকম, কিন্তু কুশিক্ষা অতি ভয়ানক।’
দেবপ্রিয় বলল—‘এই কুশিক্ষাকে ইচ্ছে করে জিইয়ে রাখা হচ্ছে চতুর্দিকে। রাজনীতির ভোটের স্বার্থে, ব্যবসাদারের মুনাফার স্বার্থে, মোল্লার ক্ষমতার স্বার্থে। শুধু একটা নাম সই করবার ক্ষমতা আবার শিক্ষা নাকি? ডিসক্রিমিনেশন চাই। বিচার-বুদ্ধি চাই।’
দিদি উজ্জ্বল মুখে বললেন—‘একমাত্র এই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষাই আমাদের পঁচাশি কোটিকে মানুষের মতো বাঁচবার সামর্থ্য দেবে। চতুর্দিকে খালি শুনি জনগণ এখন নাকি পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করেছে, ছাত্ররাও। কথাটা ঠিক বলা হয় না। জনগণ কেউ এ দলের কেউ ও দলের কথা শুনে চলে অন্ধের মত, আর ছাত্ররা রাজনীতি করে আজকাল কেরিয়ার হিসেবে : চাকরি, মান, সম্মান ইত্যাদির আশায়। আসলে আমরা যদি নিজেদের ভালো-মন্দটা না বুঝি সরকার কতদূর করবে? সরকার কখনই আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত গলদগুলো সরাতে পারবে না। যেমন পারেনি মুসলিম নারীস্বার্থ রক্ষা করতে, যেমন পারেনি পণপ্রথা রুখতে। যেটুকু হয়েছে সমাজের ভেতর থেকে হয়েছে। সু-শিক্ষার দরুন। দ্যাখ গুঞ্জন, এই সুশিক্ষা কি? ইংরেজি শিখে দিবারাত্র মিলস অ্যান্ড বুন্স্ পড়তে পারার শিক্ষা নয়, বা টি ভি আর কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ঘর সাজাবার জন্য উন্মত্তের মতো কালো টাকা রোজগার করার ধান্দা করতে পারার শিক্ষাও নয়। এই শিক্ষার পুরো চেহারাটা কি তাই নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমি দেশে ফিরেছি। যদি ওদেশে থাকতাম পুরো অ্যাকাডেমিক হয়ে যেতাম। তাতেও খুব সুখী হতাম। কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই আমার একটা কথা মনে হত…কনসেপচ্যুয়ালাইজেশন অর্থাৎ তত্ত্ব তৈরি করার অভ্যাসটা একদিক থেকে বড় বিপজ্জনক। তত্ত্ব তৈরি হয় বহু তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে, তবেই। অথচ কি পরিহাস দ্যাখ, যে মুহূর্তে তত্ত্ব তৈরি হয়ে গেল, তাকে আমরা অভ্রান্ত সত্য বলে ব্যবহার করতে আরম্ভ করি। আর তার ছাঁচে ফেলতে থাকি চলিষ্ণু এই মানব সমাজকে। দেশ-কাল-পাত্রের কথা ভাবি না। প্রত্যেকটি ধর্মগুরুর শিক্ষা নিয়ে আমরা এই করেছি। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য সব। প্রত্যেকটি সেকুলার তাত্ত্বিকের শিক্ষা নিয়েও নিয়ত এই করে চলেছি, সবচেয়ে বড় উদাহরণ মার্কস। জাগ্রত বুদ্ধি অর্থাৎ দেব যাকে বলছে ডিসক্রিমিনেশন তা-ও বটে, আবার কনশেন্স যাকে বলে তা-ও। দুটোই যে সমাজে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে একমাত্র সেই সমাজেরই অধিকার আছে তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করার। সুশিক্ষার সিলেবাসটা কি হবে ভাবতে ভাবতেই আমার দেশে ফিরে আসা। আর, নিজের দেশ ছাড়া কোথায়ই বা এর গবেষণা করব? দেশকে ত্যাগই বা করতে যাবো কেন? সামান্য ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য?’
গুঞ্জন বলল—‘মিস, আপনি তো সাধারণ মানুষ নন!’
—‘সেইজন্যে মুষ্টিমেয় তথাকথিত অসাধারণ মানুষের হাতে যাবতীয় দায় তুলে দিয়ে তোরা আত্মসুখ তৃপ্তির উদ্দেশ্যে চলে যাবি গুঞ্জন? সবাই ভাববি, ওরা তো আছে, ওরা করবে! অথচ এতদিনে তোরা নিশ্চয়ই বুঝেছিস সংঘবদ্ধ কর্মের যা ক্ষমতা কোনও ব্যক্তিমানুষের দ্বারা তা হবার নয়।’
দিদির কথায় ক্রোধ ছিল না, হতাশা ছিল না, খুব সূক্ষ্ম একটা আর্তি কি ছিল? কি যে ছিল মৈথিলী বলতে পারবে না। সে নড়ে চড়ে বসেছিল। উজান হঠাৎ বলেছিল—‘গুঞ্জন যেখানে যায় যাক দিদি আমরা যাচ্ছি না। আমরা মানে আমরা এই কজন নয় শুধু, ছাত্রসংঘের দেড় লাখ সদস্য। এই দেড় লাখ অঙ্কটা ক্রমশ বাড়তে থাকবে, তবে কিছু যোগ, কিছু বিয়োগের পর এই দেড় লাখ সংখ্যাটা সবসময়ে থাকবে। সেই ব্যবস্থা করাই এখন আমার, দেবের, লুকুর আর মৈথিলের এবং বুল্টুর প্রধান কাজ। আর সব তো এখন রুটিন কাজ হয়ে গেছে। স্বয়ম্ভর হয়ে গেল আজিগ্রাম, কেতুপুর, ফুলতলা। উত্তর চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুরশিদাবাদ এলাকায় কাজ করছে ছাত্রসঙ্ঘ। রাজাবাজার আর নন্দীর বাগানের বস্তিতে কাজ এগিয়ে চলেছে। এগুলোর একটাও হাতে কলমে আমরা করছি না। ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ারের ছাত্ররা করছে। এখন হায়ার সেকেন্ডারি থেকেও আসতে চাইছে প্রচুর। তাদের আমরা প্রধানত সংস্কৃতি মেলার কাজগুলো দিই। এই ব্যাপারগুলোর আসলে গুঞ্জন এতদিন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছিল। মধুচ্ছন্দাদির কাছ থেকেও ও অনেক শিখেছে। কিন্তু আরও অনেক সদস্য আছে। তাদের মধ্যে থেকে অনেকেই ওর জায়গা নিতে পারবে। দিদি, আপনার ছাত্ৰশৃঙ্খল তৈরি হয়ে গেছে।’
বুল্টু এই সময়ে গোঁজ মুখে বলেছিল—‘গুঞ্জন অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ানের থেকে অনেক ভালো অবস্থায় আছে। দু আড়াই হাজার টাকা মাসে রোজগার করছে। ওর বাবা এয়ার-ফোর্সের লোক। এবার নিশ্চয়ই সিভিল এভিয়েশনে এসে বসবেন। ওর জীবনে ইন্ডিয়ার স্বাভাবিক নিয়মেই শীগগীরই অনেক সুযোগ আসবে। তাছাড়া যতই যাই বলুক, বিয়ে করলে ওর কেরিয়ারের ওইরকম ভাইট্যাল প্রয়োজনীয়তা থাকছে কি? ওর চিরদিনের জন্য দেশ ছাড়ার কোনও যুক্তি নেই। সোজাসুজি বল না বাবা গরিব দেশে আর পোষাচ্ছে না, তোরা তো ভারতবর্ষের সাধারণ ছেলে মেয়ের মতো মানুষ হসনি। এয়ারকুলার, ক্যাডিল্যাক, তাজ-বেঙ্গলের আবহাওয়ায় মানুষ, ইন্ডিয়া ইজ ন্যাস্টি, ম্যারিকাই তোদের আসল লক্ষ্য। কেমন সুন্দর বুশ গভমেন্ট সব করে কম্মে দিচ্ছে। সারাদিন খেটে-খুটে সন্ধেবেলায় সেন্ট্রালি হিটেড রুমে বসে একটু মদ্যপান এবং একটু সোপ দেখা! মাঝে মাঝেই গাড়ির ব্র্যান্ড পাল্টানো। বন্ধু-বান্ধবরা মিলিত হলেই, কত ডলার থেকে কত ডলারে জাম্প করলি আলোচনা করবি। লাস ভেগাসে যাবি, জুয়ো খেলবি, রেস খেলবি…।
গুঞ্জন এই সময়ে বলল—‘স্টপ ইট বুল্টু, স্টপ ইট প্লীজ।’
বুল্টু বলল— ‘মনে কিছু করিস নি। আমি বি এস সিটা পাশ করার পরে একটা সুযোগ পেয়েছিলুম, মায়ের আর মেধাদির মুখ মনে করে যেতে পারলুম না। আচ্ছা দিদি, আমাকে ছাত্রসঙেঘর অ্যাকটিভ মেমবার করে কিছু অ্যালাউয়েন্স-টেন্স দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন না? বাবার রিটায়ার করার সময় হয়ে এলো। দিদির বিয়ে ইমিনেন্ট। দিদিটা ভালো রোজগারপাতি করছিল তো হেন্স্ ফোর্থ সেটা দিদির বরের পকেটে যাবে!’
দিদি বললেন : ‘বুল্টু তুই ইকনমিক্স নিয়ে পাস করলি। কম্প্যুটর শিখেছিস। চাকরি চট করে জুটে যাবে। যদি নাও যায় তোকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ছাত্রসঙ্ঘ সুদ ছাড়া টাকা ধার দেবে। ঘাবড়ে যাবি না একদম। ছাত্রসঙ্ঘ শুধু অন্যলোকের জন্য নয়, তোদেরও জন্য। কাউকে কষ্ট পেতে আমরা দেবো না। আর তোর দিদির সঙ্গে আমি কথা বলব। দিদির উপার্জন জামাইবাবুর পকেটে যাবে মানে? তোর দিদি যেমন ভালো বুঝবে খরচ করবে। ছেলে আর মেয়েকে আজকাল মধ্যবিত্ত বাবা মা সমান যত্ন ও খরচ করে তৈরি করে। মেয়েদের দায় নেই?’
গুঞ্জন এই সময়ে সংক্ষিপ্ত কয়েকটা কথা বলে— ‘মিস, আমি কোর্সটা শেষ করে হয়ত কিছুদিন চাকরি করবো। তারপর ফিরে আসব।’
—‘যদি ওখানেই বিয়ে করিস। করতেই পারিস।’
—‘না, পারি না।’ গুঞ্জন গোঁয়ারের মতো বলে, ‘আমি এখানে এসে বিয়ে করব।’
নার্সিং হোমে পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি নামল। মৈথিলী ছাতা ব্যবহার করে না। বাড়িগুলোর গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন শেষ অবধি পৌঁছল তখন নাসিং হোমের অফিস বন্ধ করে দিচ্ছে। রঞ্জুমাসীর গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে। মৈথিলী ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধরল। —‘মাসি! মাসি!’ ‘ঘ্যাঁচ্’ করে থেমে গেল মারুতি।
প্রমিতের মা দরজা খুলে বললেন—‘উঠে আয়।’ মৈথিলীর গায়ে হাত দিয়ে বললেন— ‘ইস ভিজে গেছিস যে রে!’
—‘হ্যাঁ মাসি। জিন্স্টা ভারি লাগছে।’
—‘চল তোকে তোর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই।’
—‘সেই ভালো। বেশ বৃষ্টি পড়ছে। প্রমিত কেমন আছে মাসি? কিছু খবর পেলেন?’
—‘ওরা তো বলছে আগের থেকে ভালো। হ্যাঁরে মৈথিলী লুকু কি আজ কালের মধ্যে এসেছিল?’
—‘আজ যদি এসে থাকে বলতে পারব না। আমিই তো দেরি করে ফেললাম। গতকাল আসেনি জানি। তার আগের দিন আপনি চলে যাবার পর এসেছিল। কেন?’
একটু চুপ করে থেকে মাসি বললেন— ‘ডাঃ সিনহা জিজ্ঞেস করছেন লুকু নামে কি ওর কোনও বান্ধবী আছে! প্রমি নাকি বারবার ওর নামই করে। ওঁরা প্রথম প্রথম নামটা ধরতে পারতেন না। ইংরেজি লুক বলে মনে করতেন। যন্ত্রণার মধ্যে খালি লুক লুক করে চেঁচায়।’
মৈথিলী চুপ। হাসি-খুশি রহস্য-পটু প্রমিত যে এতো চাপা স্বভাবের ছেলে এতদিন মিশেও তারা কোনদিন বুঝতে পারেনি। বরং দেবকে ওদের বরাবর রহস্যময়, চাপা বলে মনে হয়েছে।
একটু পরে মাসি চুপি চুপি কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন— ‘মৈথিলী তোরা ছোট্ট থেকে এক স্কুলে পড়ছিস। মেলামেশা করছিস। ভাইবোন সম্পর্কটা হওয়াই বেশি স্বাভাবিক ছিল না?’
মৈথিলী চট করে কিছু বলতে পারল না। মাসির তত্ত্বটা যে তাদের জীবনে একেবারেই খাটছে না। উজানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী অদ্ভুত! ভাইও বটে। বন্ধুও বটে, আবার…আর লুকু তো ঘোষণাই করে দিয়েছে দেব যদি তাকে বিয়ে না করে তো সে আবার ড্রাগ ধরবে। দেব মৃদু মৃদু হেসে বলছে— ‘মৈথিল। লুকু কিন্তু আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে।’ মৈথিলী বলে—‘তো তুই ব্ল্যাকমেইল্ড্ হস না।’
—‘একটা বন্ধুলোক এভাবে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে যাবে, চোখে দেখা যায়?’
মৈথিলী মাসির হাতটা ধরে রাখল কোলের ওপর। একটু পরে বলল—‘মাসি, তাই-ই তো! আমরা সবাই আছি, ওর ভাই-বোন বন্ধু যা বলেন। প্রমিতকে আমরা স্বাভাবিক করে তুলবই। আপনি ভয় পাবেন না।’
—‘তুই এমন করে কথা বলিস মনে সত্যিই বল আসে।’ মাসি বললেন, ‘কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হবে কি করে? লুকু তো…। তাছাড়া কারুর ভালোবাসার ওপর তো জোর চলে না!’
—‘মাসি বেসিক্যালি সব ভালেবাসা তো ভালোবাসাই। আন্তরিক টান আর শুভেচ্ছা। এই জায়গায় যদি কোনও গণ্ডগোল না থাকে, তাহলে ভালোবাসার চেহারাটা বোধহয় পাল্টে দেওয়া যায়। এখন আমাদের চারদিকে পটভূমি অনেক বড় হয়ে গেছে। সেই প্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়ে দেখতে হবে আমাদের সো-কল্ড্ ভালোবাসার কতটা পজেসিভ ইনফ্যাচুয়েশন, আর কতটা এই আদি অকৃত্রিম শুভকামনা। আপনি আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন। আমাদের বলতে প্রমিতের কথাও বলছি কিন্তু।’
বাকি পথটা দুজনে চুপচাপ এলেন। মৈথিলীর বাড়ির দরজায় তাকে নামিয়ে দিতে দিতে মাসি বললেন— ‘আমি আশা হারাইনি। চট করে হারাই না। তোরা পাশে থাকলে আরও সাহস পাই। কতদিন যে একলা-একলা পথ হাঁটছি।’ তিনি মৈথিলীর হাতটা জড়িয়ে বুকের মধ্যে রাখলেন কিছুক্ষণ। বললেন—‘তোকে বহুদিন ধরে দেখছি, বড্ড ভালো লাগে তোকে আমার, প্রমিতটা লুক লুক করে না চেঁচিয়ে যদি মৈথিলী মৈথিলী করে চেঁচাত আমি বেশি খুশি হতাম।’
দুজনেই হেসে ফেললেন।
দরজা খুলে দিল বৈজুদা। একমুখ হাসি। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। বলল— ‘আবার ভিজেছ তো? বেশ করেছে, রোদে, জলে ভিজে, এতো করে বলি ছাতা নাও, কি ওয়াটারপ্রুফ নাও। যাও তাড়াতাড়ি এই ঝোলাগুলো পালটাও। আমি কফির জল বসিয়ে দিচ্ছি।’
মৈথিলী নিজের ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখল অন্ধকার ঘরে পাখা চলছে। তার বিছানায় কে যেন শুয়ে। সাদা ধবধবে খাদির শাড়ি আর গাঢ় রঙের ব্লাউজ। তার বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এমন ঘন ঘোর বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকার সন্ধ্যায় যখন মৈথিলী মাতৃবিরহ সইতে শিখে গেছে, মা যখন আর তার অবলম্বন মাত্র নয়, বিশুদ্ধ আনন্দে পরিণত হয়ে গেছে, তখন সেই শুভক্ষণে মৈথিলীর মা ফিরে এসেছে।
মৈথিলী মায়ের পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে অরুণা মুন্নিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, অস্ফুটে বললেন— ‘ওরা আমাকে ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার ক্যানডিডেট হিসেবে চাইছে মুন্নি। আমি এবার না করেছি। অনেক কাজ করে দিয়েছি মুন্নি। অনেক। টোলায় টোলায় ঘুরে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত…আমার আর মনে কোনও গ্লানি নেই।’
স্বামীর নিরাপত্তার জন্য না মেয়ের চরিত্র গঠনের জন্য না নিজের কর্মৈষণা পূর্ণ করতে না পিতৃ ভূমির ঋণ শোধ করতে…কিসের জন্য যে অরুণা রাধিকা সারেনের এই নিবার্সন, এই অজ্ঞাতবাস প্রয়োজন ছিল তা একমাত্র জনগণমন অধিনায়ক কোনও ভাগ্যবিধাতাই জানেন!
অধ্যায় : ২১
আজ রাত্তিরে মেধার চোখে ঘুম আসছে না। সারা সন্ধে বৃষ্টি হয়েছে। জল জমে গেছে রাস্তায় রাস্তায়। মরশুম শেষ হয়ে আসছে তবু এরকম ভারি বৃষ্টি। এলোমেলো ছাট দিচ্ছিল অনেকক্ষণ। জানলা বন্ধ করে রাখতে হয়েছিল। এখন অনেক রাত, বৃষ্টি থেমেছে। ভেজা-ভেজা দমকা হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে। শিয়রের জানলাটা খুলে দিয়েছেন এবার। কালচে নীল আকাশ, চোখ চেয়ে কটাক্ষে আকাশ দেখতে না পেলে তাঁর ঘুম আসে না। চাঁদ উঠেছে মেঘের আড়ালে। চাঁদের ওপর দিয়ে বড় বড় মেঘের চাঙড় ভেসে যাচ্ছে। অন্ধকার, আবার আলো, আবার অন্ধকার। মেধা উঠে ছাতের দরজা খুললেন। ছাতে উঠে গেলেন। এ বাড়ির এই একটা ত্রুটি। বারান্দা নেই। ছাতটাকেই বারান্দার মতো শৌখিন করে তৈরি করেছিলেন বাবা। খোলামেলায় যাবার ইচ্ছে হলে ছাতে উঠে আসতে হয়। মেধা পায়চারি করছেন। অশান্ত পদক্ষেপ। আজ কদিন ধরেই তাঁর খুব অস্থির লাগছে। গুঞ্জন চলে যাচ্ছে। গুঞ্জন চলে যাচ্ছে। শুধু চলে গেলে এতো চিন্তা ছিল না। কত আসবে। কত যাবে। সে হিসেবে তো সেরকম কিছু বিয়োগ হয়ইনি। কিন্তু গুঞ্জন বুকে কষ্ট নিয়ে যাচ্ছে।
গুঞ্জনকে ওরা ফেয়ারওয়েল দিল। গুঞ্জন তাঁর কাছে থাকতে চাইল। আগে বাড়িতে লুকুকে, মৈথিলীকে কত রেখেছেন তিনি। ওরা দু বন্ধু তো যখন তখন আসত, এসে আর যেতে চাইত না। দুজনেই মাতৃহীন। মেধা সন্তান গর্ভে ধরেননি। মাতৃস্নেহ কি জিনিস জানা নেই। কিন্তু দুটি মাতৃহীন মেয়েকে তাদের প্রয়োজনের সময়ে আশ্রয় দিতে পেরেছিলেন। আবেগকে তিনি প্রকাশ্য জীবনে যথাসাধ্য পরিহার করে চলতে চেষ্টা করেন। আবেগ তাঁর নির্জন সময়ের একলার উপভোগের বস্তু। আবেগ সৃজনী-প্রতিভার সহচর ও স্নায়ুতন্ত্র এবং এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি মন্থন করা অমৃত এবং গরল, ঊর্বশী এবং লক্ষ্মী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা এবং কৌস্তুভ। তাকে প্রয়োজনমতো বক্ষে ধারণ করো তাকে তোমার বাহন বানাও, তীব্র বৃংহণে, গম্ভীর পদক্ষেপে, কিম্বা উচ্চ হ্রেষায় শূন্য প্রকম্পিত করে সে তোমায় লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। সে উত্তেজক আবার শান্তশ্রীমণ্ডিত সৌন্দর্যসার। সে আবার ধন্বন্তরিও। কতবার সে নিভৃতে নিরাময় রূপে এসেছে। মেধা এই আবেগের নীলকৃষ্ণ গরলটুকু তাঁর কণ্ঠে ধারণ করে থাকেন। হৃদয়ে পৌঁছতে দেন না। মস্তিষ্কে উঠতে দেন না।
গুঞ্জন বলল—‘মিস, আজ আমি আপনার কাছে থাকি।’
—‘থাক। হোস্টেলে ফোন করে দে। না হলে অনর্থক কথা শুনবি।’
অনেক চেষ্টা করেও ফোন পাওয়া গেল না। উজান বলল—‘আমি খবর দিয়ে যাবো এখন।’
ঘরের ভেতর সেদিন খুব গুমোট। মেধা বললেন—‘গুঞ্জন আমি ছাতে যাচ্ছি। তুই আসবি?’
তিনি বুঝতে পারছিলেন গুঞ্জনের কিছু বলার আছে। গুঞ্জনকে নিজের একটা শাদা বিদেশী নাইট-ড্রেস পরতে দিয়েছেন। লেসে ভর্তি পোশাকটা। গুঞ্জন প্রায় মেধার কাছাকাছি লম্বা। ওর কুচকুচে কালো চুল কাঁধ পর্যন্ত থাকে থাকে কাটা। খুব জৌলুস-অলা চেহারা। অনেকের মধ্যে চোখে পড়ার মতো। মাধুর্য একটু কম। কিন্তু খুব জমকালো।
মেধা বললেন—‘তোর রুটিগুলো দারুণ সুন্দর হয়েছিল।’
—‘পাঞ্জাবি রুটি। আমার দাদিমার কাছ থেকে শিখেছি।’
—‘এক পিঠ সেঁকিস, না?’
—‘হ্যাঁ খুব পাতলা তো! গুজরাটি রুটি খেয়েছেন? আরও পাতলা, ভীষণ ভালো খেতে। ওরা সেগুলো তাওয়ার ওপর সেঁকে সেঁকে একেবারে ক্রিস্প্ করে নিয়ে কৌটোর মধ্যে রেখে দেয়। মাখন বা জ্যাম লাগিয়ে খায়। খাকরা বলে।’
মেধা হেসে বললেন—‘ভারতবর্ষে বোধহয় যতরকম জাতি ততরকম রুটি। রুটির আমি রুটির তুমি তাই দিয়ে যায় চেনা। কি রিচ দেশটা, ভাবলে অবাক লাগে।’
—‘ভারতবর্ষকে আপনি খুব ভালোবাসেন, না মিস?’
—‘বোধহয়।’ গুঞ্জন স্কুলগার্লের মতো মিস বলাটা কোনদিন ছাড়ল না। ওর এই স্বাতন্ত্রটাও মেধার ভালো লাগে।
ও বলল—‘দেশের মাটিটাকে, না দেশের আইডিয়াটাকে, না মানুষগুলোকে?’
—মেধা বললেন—‘দ্যাখ গুঞ্জন, আমার বাবার শেষ উপলব্ধি ছিল দেশের মাটিটাই আসল দেশ। মানুষগুলো চেঞ্জিং, চেঞ্জফুল্, মাটিটা কনস্ট্যান্ট। এর মধ্যে যুক্তির অংশটা আমি মেনে নিতে পারি না। কিন্তু অনুভূতির দিক থেকে এই ভূখণ্ডের ওপর বোধহয় ভালোবাসা আমার বেশি।’
—‘মিস, তাহলে আপনি পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলে দূষণমুক্ত করতে চাইতেন জল, বাতাস। বন কাটা বন্ধ করতে চাইতেন। তাতো করেন না! আপনি তো মানুষ নিয়েই কাজ করেন। মানুষ নিয়ে কাজ করেন অথচ তাদের ভালোবাসেন না তা-ও কি হয়?’
গুঞ্জন আজ তাঁকে এরকম ছিন্নভিন্ন করার মেজাজে কেন আছে মেধা বুঝতে পারছিলেন না। বললেন,—‘বাসি। নিশ্চয়ই বাসি। কিন্তু তারা এই ভূমির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আমার কাছে। আমিও এক রকমের এনভায়রনমেন্টালিস্ট। জল, বাতাস, বন শুদ্ধ করবার মন নিয়েই আমি ভারতের মানুষ, ভারতের সমাজকে গড়বার চেষ্টা করি বোধহয়।
—‘তার মানে মিস খুঁটিয়ে দেখতে গেলে আপনি আইডিয়াটাকেই ভালোবাসেন।’
—‘তোর তাই মনে হয়?’
—‘তবে কি বলুন! এইসব গ্রামের মানুষ যাদের জন্য এত করেন, তাদের আপনি ব্যক্তি হিসেবে দেখেন?
—‘ব্যক্তি হিসেবে দেখি, কিন্তু ইমোশন্যাল ইনভল্ভ্মেন্ট চাই না। তবে গুঞ্জন, তোদের কথা আলাদা। তোরা কিন্তু আমার কাছে ব্যক্তি। প্রত্যেকে আলাদা। তোদের সুখদুঃখের কথা আমাকে ভাবায়।’
—‘তবে কেন উজান বলল গুঞ্জন চলে গেলে আরেকজন তার স্থান নেবে! কোনও অসুবিধে নেই।’
—‘গুঞ্জনের কাজটা আরেকজন করবে। কাজের দিক থেকে কোনও ফাঁক পড়বে না। উজান নিজেও চিরকাল থাকবে এ আমি আশা করি না। কাজের চেইনে যদি ফাঁক থাকে তাহলে তোদের সঙ্ঘ চলবে কি করে? তার মানে এই নয় যে তুই গুঞ্জন মানুষটা আমাদের মধ্যে কোনও ভ্যাকুয়াম রেখে যাবি না!’
—‘যাবো? আমার এমন কি গুণ আছে, এমনকি শক্তি আছে মিস, যাতে আপনাদের মনে শূন্যতা রেখে যেতে পারি! মিস, আমার কাজটুকু ছাত্রসংঘ নেয়। আমাকে নেয় না।’
মেধা অনেকক্ষণ কিছু বললেন না। গুঞ্জন এতো অভিমানী তাঁর জানা ছিল না। দুজনে দুটো বেতের মোড়ায় বসলেন। খানিকটা পর তিনি বললেন—‘গুঞ্জন এ অভিমান কি তোর সাধারণভাবে ছাত্রসঙ্ঘের প্রতি, না আমার প্রতি, না অন্য কোনও বিশেষ ব্যক্তি আছে এর মধ্যে?’
চাঁদের আলোয় মেধা দেখলেন গুঞ্জনের চোখ ভারি হয়ে এসেছে। টুপ করে একফোঁটা নামল তার সাদা গালে, আরেক ফোঁটা, আরেক ফোঁটা। ফোঁটাগুলো পরস্পরকে অনুসরণ করতে করতে চিবুকের খাঁজে এসে মিলিত হচ্ছে, তারপর শূন্যে ঝাঁপ দিচ্ছে।
মেধা বললেন— ‘আমার কথা যদি বলিস, আমি তোদের মধ্যে যার যার সঙ্গে খানিকটা মিশেছি প্রত্যেককে গভীরভাবে ভালোবেসেছি, যেন তোরা আমার চোখ, কান, হাত, পা। তোদের কল্যাণ, তোদের সম্পূর্ণতা আমার ততটাই কাম্য যতটা এই বিশাল দেশের। তোরা ঠিক পথে চললে, তোরা কষ্ট পেলে আমি এতো কষ্ট পাই যা আমার কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু নিজের মত যাতে তোদের ওপর চাপিয়ে না দিই, যাতে তোদের চয়েস তোদেরই থাকে, সে বিষয়ে আমি সতর্ক থাকি। আমার কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দেওয়া হলে সেটা তো আমায় মেনে নিতেই হবে। মানিয়ে নিতেই হবে। তোদের চলে যাওয়াটাও সেইরকম। ভেবেছিলাম তোদের ভেতরে ঢুকব না, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। ইমোশন্যাল ইনভলভ্মেন্ট আমাকে কি ভীষণ কষ্ট দেয় তার একাধিক অভিজ্ঞতা আমার আছে। সে রকম হলে আমি পঙ্গু হয়ে যাবো; কাজ করতে পারব না। কিন্তু, তোদের ব্যাপারে আমি এই নীতি বজায় রাখতে পারছি না গুঞ্জন। প্রমিতটা ছাত্রসঙ্ঘের এই সৌহার্দ্য, সৎ-সংকল্পের আবহাওয়াতে থেকেও নষ্ট হয়ে গেল, এ যেন শূলবেদনার মতো আমাকে বিঁধছে।’
গুঞ্জন হঠাৎ মেধার কোলের ওপর মুখ নামিয়ে দিল, তারপর ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ‘মিস আপনি প্রমিতকে বাঁচান। প্রমিত নষ্ট হয়ে যায়নি। আপনি লুকুকে একটু বুঝিয়ে বলুন। লুকু যদি প্রমিতকে অ্যাকসেপট করে ওর জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। মিস, প্লিজ ওকে বাঁচান। দেবের সম্পর্কে লুকুর ব্যাপারটা আসলে হিরো ওয়ারশিপ। দেব আপনার মতো নির্বিকার, মহান, বড় বড় কাজ করার জন্যই ওর জন্ম। ওর লুকুকে না হলেও চলবে, প্রমিতের চলবে না…’
চোখের জলে মাখামাখি গুঞ্জনের মুখটা অনেক কষ্টে তুলে ধরলেন মেধা। ভারি গলায় বললেন—‘এইজন্যে তুই চলে যাচ্ছিস?’
গুঞ্জন কোনও উত্তর দিল না। মেধার কোলটা গরম চোখের জলে ভিজে উঠতে থাকল। তিনি কোলের ওপর কালো কঠিন কোমল ক্লান্ত করুণ মাথাটায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর মনের মধ্যেকার সক্রিয় ভালোবাসা যদি আরোগ্য হয়ে আঙুলগুলো দিয়ে নামে তো নামুক। বুকের ভেতরে একটা শেল বিঁধেছিল, তীব্র গতিতে আরেকটা শেল এসে বিঁধে গেল। তাঁর বিশাল ভারতকল্যাণযন্ত্রের নাট, বল্ট, পিস্টন, রোলার, সব দীর্ঘশ্বাস ফেলে গা মোড়ামুড়ি দিচ্ছে।
এতগুলো তরুণ হৃদয় নিয়ে কারবার। এটা তাঁর ভাবা উচিত ছিল। তাঁর অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা এতো অবাধ হয়নি। তাই হৃদয় নিয়ে গণ্ডগোল প্রায়ই হত। মেধার নিজের বাড়িতে কত খোলামেলা আবহাওয়া ছিল সে সময়ের তুলনায়, বাবা-মার ছাত্ররা যখন তখন আসতেন, দাদাদের বন্ধু-বান্ধব, বাবা-মার ছাত্র-ছাত্রী সবাইকে নিয়েই যেন ছিল তাঁদের বৃহৎ যৌথ পরিবার। তবু তো মেধা অমিয়নাথের প্রচণ্ড আকর্ষণ কাটাতে পারেননি। সে আকর্ষণটা পরে মিথ্যা, গুঞ্জন যাকে হিরো-ওয়ারশিপ বলছে তা-ই-ই প্রমাণিত হয়ে যায়। অমিয়নাথের ঘটনাটা প্রতিষেধক টিকার মতো কাজ করেছে তাঁর জীবনে। বিয়ের কথা মনে হয়েছে, সম্ভাবনাও হয়েছে অনেকবার, কিন্তু আর কখনো অমন গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েননি, পড়তে চায়নি তাঁর অন্তরাত্মা। তাঁর আনুগত্য, তাঁর প্রতিজ্ঞা সবই নিয়ে নিয়েছে এই জীবনব্যাপী গবেষণা।
এ যুগের ছেলে-মেয়েরা কত ছেলেবেলা থেকে মেলামেশা করছে। ওদের সম্পর্ক কত সহজ! গুঞ্জন কী শক্ত মেয়ে। অথচ ভেতরে ভেতরে এইরকম অভিমানী! এই ঝুঁকির কথা ভেবেই বা তিনি কী করতেন! তিনি কি এদের আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন? ওরে তুই ওদিকে যাসনি, এদিকে আয়, এভাবে হৃদয়-নিয়ন্ত্রণ করার ট্রাফিক পুলিস কি পাওয়া যায়! সে পুলিস অনেক দুঃখে নিজেকেই হতে হয়। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার পথ দিয়ে যাবে, যে পথ দিয়ে একজন গিয়ে ঠকেছে, সে পথ দিয়েই আরেকজনকে যেতে হবে। পূর্ববর্তীর অভিজ্ঞতা থেকে—সে প্রায় কিছুই শিখবে না। জীবনের পর্বতারোহণ এমনি এক অদ্ভুত জিনিস!
প্রমিতের ব্যক্তিত্বটা আজ এই বর্ষণক্ষান্ত রাত্রে তাঁর স্মরণে আসছে বারবার। খুব শৌখিন ছেলে। এতো পরিষ্কার, কড়া ইস্ত্রির পোশাক পরে থাকতো এবং আগাগোড়াই তাকে টিকিয়ে রাখতে পারতো যে ওর বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলত, প্রমিত পোশাক পরেনি ওর পোশাক প্রমিতকে পরেছে। ছেলেটা উদার স্বভাব। অনেক টাকা ছাত্রসংঘকে দিয়েছে ডোনেশন হিসেবে। কর্মী হিসেবে উজান বা মৈথিলীর মতো, এমন কি লুকু বা গুঞ্জনের মতোও নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু সীরিয়াস কাজকর্ম করতে করতে মাঝে মাঝে একটা মুক্তির দরকার হয়। সেই হাসিখুশি, ফাজলামি, রসের স্রোত অব্যাহত রাখার কাজটা প্রমিতকে দিয়ে খুব ভালো হত। প্রমিতের চরিত্রের সীরিয়াস দিকটা তখনই প্রকাশ পেত, যখন ও চুপিচুপি ওঁর মার নাম করে ডোনেশন দিয়ে যেত, বলত—‘ম্যাডাম, আমার নিজের বিজনেস চলবে যতদূর সম্ভব স্ট্রেট লাইনে, আমাদের জীবনধারণের জন্য যতটা দরকার রেখে, বাকি সবটাই ছাত্রসঙ্ঘের কাজে যাবে।’
মেধা বলতেন—‘কেন? অত দরকার কি? “আমার ভাণ্ডার আছে ভরে তোমা সবাকার ঘরে ঘরে” এই নীতিই তো ছাত্রসঙঘ নিয়েছে।’
প্রমিত বিজ্ঞের মতো হাসত—‘কত টাকা লাগবে, আপনার কোনও ধারণা আছে ম্যাডাম! আপনি তো বলেইছেন এদেশে ধনের বণ্টনে চূড়ান্ত বৈষম্য। সিসটেমের বিরুদ্ধে যাবার শক্তি তো আমাদের নেই। এভাবেই সেই বৈষম্য দূর করা যাক।’
মেধা বলতেন— ‘ঠিক আছে। যখন সত্যি-সত্যি আন্তরিকভাবে পারবি, করবি, কিন্তু কমিট করার দরকার নেই। আমি মুষ্টিমেয়ের আত্মত্যাগের থিয়োরিতে বিশ্বাস করি না। করা উচিত বলেও মনে করি না।’
একথা প্রমিতকে কি কোথাও আঘাত করেছিল? তার মধ্যে কি কোথাও দানের অহঙ্কার কাজ করছিল? তাঁর কথা সেখানে আঘাত করে থাকলে তিনি নিরুপায়। সমস্ত দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করবে মুষ্টিমেয়র দান, সুবুদ্ধি তার ত্যাগের ওপর, পৃথিবী জোড়া এই ব্যবস্থাটাকে পাল্টানো তাঁর খুব জরুরি মনে হয়। উন্নয়ন হবে কেওড়াখালির। কেওড়াবাসীরা সেই উন্নয়নের যাবতীয় উপকরণ কোনও গৌরী সেনের কাছ থেকে লাগাতার নিয়ে যাবে এ হয় না। সেইজন্যেই এবার যখন ওদের ট্র্যাক্টর দেবার কথা হল, ছাত্রসঙ্ঘ পুরো টাকাটা দিতে চাইলেও তিনি বাধা দিয়েছেন। ওরা এখন যথেষ্ট উপার্জন করছে। ওরা অর্ধেক দিক, বাকিটা ছাত্রসঙ্ঘের কাছ থেকে সুদ ছাড়া ঋণ। কলের লাঙল আসছে। ওদের জমি কয়েক ঘণ্টায় চাষ হয়ে যাবে, তারপরে ওরা সরাল আর ফলসা গ্রামে ভাড়া খাটাবে কলের লাঙল। সেই টাকায় বছর খানেকের মধ্যে শোধ হয়ে যাবে ছাত্রসঙ্ঘের ঋণ। নিজেদের টাকায়, নিজেদের ঋণ করে কেনা টাকায়, নিজেদের কলের লাঙল। তার আনন্দই আলাদা।
অধ্যায় : ২২
উজান আর বুল্টুর কাছ থেকে রিপোর্ট পেলেন মেধা ওরা তেল-সিঁদুর দিয়ে পান দিয়ে জোড়া শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে বরণ করেছে কলের লাঙল। খুব উৎসাহ গ্রামে। যেদিন প্রথম লাঙল পড়বে সেদিন পর্যন্ত উৎসব। হেলে গরু আর লাঙল বেশির ভাগই ভালো দামে বিক্রি হয়ে গেছে। কিছু কিছু এখনও রেখে দিয়েছে ওরা। বলছে—‘উজানদাদা, বুল্টুদাদা কলেরও তো সর্দি কাশি, জ্বর, পেটের ব্যামো আছে। ওকেও তো রেস্টো দিতে হবে? না কি বলো!’
ছাত্রসঙঘ থেকে মাত্র দুজন গেছে, দিদিরা কেউ যাননি বলে ওদের ভারি দুঃখ। উজান কি করে বলে—ওদের মিলিদিদির এখন মা এসেছে সে থেকে থেকেই সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে নিচ্ছে, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ায় হবে এবার তাদের নতুন প্রজেক্ট। কি করেই বা বলে লুকু দেবপ্রিয় নতুন বিয়ের পর পাহাড়ে বেড়াতে গেছে। এও সে বলতে পারছে না প্রমিত নার্সিং হোমে, যদিও এখন আগের থেকে অনেক অনেক ভালো, কিম্বা মেধাদি এখন গুঞ্জনের বিদেশ যাবার পোশাক-আশাক কেনা, তার পাসপোর্টভিসার জন্য ছোটাছুটি করতে ব্যস্ত। উজানের ক্যামপাস ইনটারভিউয়ে অনেকগুলো চাকরির অফার এসেছে, সে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, বুল্টু মফঃস্বলের কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছে, মুখ ভীষণ ভার।
উজান বলেছিল ‘তুই আচ্ছা ছেলে তো! গ্রামের জন্য কাজ করছিস আর মফঃস্বলের কলেজে কাজ করতে চাস না?’
বুল্টু উবাচ—‘গ্রামের জন্য কাজ করছি ঠিকই। কিন্তু ফাউগুলো বড় ভালো ছিল রে! আড্ডাগুলো কি জমত বল্!’
‘আমরা আড্ডা জমাতুম!’ উজানের র্ভৎসনা তীব্র হয়ে ওঠে।
বুল্টু বলে— ‘না না, কাজ করতিস, কাজ। তাতে কোনও সন্দেহ আছে? ওই কাজটাই বেশ আড্ডার সঙ্গে মিলে মিশে সাড়ে বত্রিশ ভাজা হয়ে যেত না?’
—‘এর পরে তো মেদিনীপুরেই কাজ হবে, তুই ওখানে সঙ্ঘের কর্ণধার হবি।’
—‘দ্যাখ উজান, কান-টান আমি করো ধরতে-টরতে পারি না। আমার কান যদি বন্ধুলোক কেউ ধরে তো ক্ষ্যামাঘেন্না করে অনেক সময় ছেড়ে দিই। ব্যাস। কানের সঙ্গে আমার এইটুকু সম্পর্ক।’
বুল্টুর দিদি বলে— ‘ওরে তোরা ওকে প্রথমে ওটা নিয়ে নিতে বল। পরে না হয় শহরের দিকে চেঞ্জ করে নেবে।’
বুল্টু বলে— ‘পাঁচ বছরের মুচলেকা দিতে হয়, তা জানো? জয়েন করো বললেই হলো, না? উজান ভেবে দ্যাখ তোরা কিন্তু বুল্টু দাসের মতো একজন উৎসাহী অভিজ্ঞ, মূল্যবান, শক্তিমান কর্মীকে হারাতে যাচ্ছিস!’
—‘গ্ল্যাডলি, মোস্ট গ্ল্যাডলি’—উজান বলে।
বুল্টু বোধহয় চাকরিটা নিয়ে নিয়েছে। কিছুদিন দেরি আছে চাকরিতে যোগ দিতে। ইতিমধ্যে ও মুখ শুকিয়ে মেধাদির বাড়ি আসা-যাওয়া করছে। গুঞ্জনের কেনাকাটার সঙ্গী হচ্ছে। অনেক সময়ে দিদিকে বলে— ‘দেখুন দিদি, এই এতো মার্কেটিং বওয়া কি আপনাদের কাজ? ভার বইবার জন্যে একজন পুং ভীষণ দরকার আপনারা বুঝতে পারছেন না।’ মেধা বলেন— ‘খুব বুঝতে পারছি। আমাদের এবার স্বাবলম্বী হবার সময় এসেছে। শুধু তোর জন্য হতে পারছি না।’
কেওড়াখালির সর্বশেষ রিপোর্টটা শুনে থেকে মেধার ভেতরে কি যেন একটা অনুভূতি ফুলে ফুলে উঠছে। এ কি গর্ব! নির্লিপ্ত ভাবটা প্রাণপণে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন তিনি। আনন্দের প্লাবনে সেটা ভেসে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ক্লাস নেন, তাঁর গলায় যেন একটা শাঁখের মতো আওয়াজ বাজে, চলনে একটা নতুন ছন্দ, করিডর দিয়ে চলে গেলে মনে হয় একটা মশাল হেঁটে গেল। সংস্কৃত বিভাগের নন্দিতা একদিন ঘরে এসেই বলেই গেল ‘মেধাদি, তোমার নামে এবার নতুন গুজব ছড়াচ্ছে কিন্তু। কি জানো তো? সবাই বলছে মেধা ভাটনগর প্রেমে পড়েছে। সত্যি নাকি?’
মেধা মিটিমিটি হাসেন, বলেন—‘আমি যে প্রেমে পড়েই আছি, কতদিন কত যুগ থেকে, সে খবর ওরা জানে না?’
দুজনে মিলে খুব হাসেন।
নতুন ফসল উঠবে অঘ্রাণ মাসে। কলের লাঙলে চষা জমির প্রথম ফসল। কেওড়াখালি এখন সবুজ হলুদের গালচে। পাকা হয়ে গেছে স্কুলঘর, মহিলা সমিতি, গ্রন্থাগার। মাটির খড়ো ঘরগুলি ঠিক তেলরঙে আঁকা ছবির মতো। জলার চারপাশে ইঁটের বাঁধ। হরেকরকম ছোট মাছ আর চিংড়িতে ভর্তি। দিঘি কুয়ো সব পরিচ্ছন্ন বাঁধানো। জঙ্গল বাঁশঝাড় বাগান যেখানে যা আছে সব নিয়মিত সাফ হয়। কলের লাঙল এসে চাষীদের হাতে এখন কাজ অনেক কমে গেছে। তারা সব সাফ-সুরত রাখে। সোনালি গোলাগুলো দেখলে মনে হবে এসব পত্রিকার পাতা থেকে কেউ কেটে রেখেছে। পংক্তিবদ্ধ শিশু ও বালক-বালিকার দল উজ্জ্বল, সরল, নীলকান্তমণি চোখ মুখ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে-আসছে, অঙ্গে বাড়ির মেয়েদের তৈরি শাদা শার্ট, খাঁকি প্যান্ট, শাদা ফ্রক, ঘাসে-ছাওয়া জমির ওপর শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে গোলাপি বাঁট-অলা, দোহারা নধর-চেহারার ভোলেভালা গাইগুলো। আশেপাশে গ্রামের প্রবীণরা রোদ পোহায়, বসে বসে সারাই, ঝালাইয়ের কাজ করে। লাল-হলুদ ডুরে শাড়ি পরে পদ্ম তার জায়ের কোলের মেয়েটিকে দুধ খাওয়াতে বসেছে। মকবুল মিঞা গ্রামের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, পাশ দেয়নি কিন্তু হাতযশ খুব। সে যেতে যেতে বলে গেল, ‘অমন হাত-পা চেপে ঢকাস ঢকাস খাইও না চাচী। ওতে লিভার খারাপ হয়। যতটুকু খাবার ও আপনি খাবে।’ ডিম বোঝাই হচ্ছে খড় বিছানো ঝোড়াতে। ভ্যানগাড়ি করে চলে যাবে গঞ্জের বাজারে, ক্যানিং-এর হোটেলগুলো বড় খদ্দের। বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ। নির্জন সকালের বুক চিরে কাঠ চেরাইয়ের আওয়াজ ওঠে ঘসঘস। শীতের শুরুতেই আনোয়ার তার ছুটকি বিবির তৈরি নস্যি রঙের সোয়েটারটা পরে ফেলেছে। কানঢাকা টুপি। যেন ঠাণ্ডা না লাগে। ভালো মন্দ খেয়ে খেয়ে, ওষুধ আর বিশ্রামের জোরে তার চেহারাখানা হয়েছে বেশ চুকচুকে একটা খাসীর মতো। সে নিজেই কথাটা বলে আর হাসে। তাকত এসেছে শরীরে, কিন্তু সাবধানে থাকতে হচ্ছে। বিবি দুটিও তার ধারে-কাছে ঘেঁষছে না আজকাল। খুব যত্ন করে মালিশ করে দিচ্ছে অবশ্য। আনোয়ার বলে ‘পালিশ চড়াইছে।’ মেয়েরা ভাত বেড়ে দেয়, পাখা করে। বিবি দুটি ফুকফাক পালিয়ে যায়। আনোয়ার ভোটকম্বল চাপা দিয়ে গরগর করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কানে আসে তার বড়কি বিবির কন্যা ফতিমা গান ধরেছে, বেহুলো বিবির গান।
ওরে আমার সোনার নখীন্দর রে
কুন ডাঙাত্থে কুন ডাঙায় আইলাম জেবন মান্দাসে ভর।
চান সদাগর শ্বশুর পাইলাম, সন্কা বিবি মা
নোয়ার বাসর সোনার বাসর
(ওরে) সোনার বাসর হীরার বাসর কপালে সইল না।
(আমার) কপালে সইল না।
(এখন) অকূল পাথারে ভাসাইলাম জৈবন
মনসায় করি গড়
মনসা মায়েরে করি গড় রে……।
কেওড়াখালির সবার ইচ্ছে ছাত্রসঙ্ঘ হা-ই একবার যেমন অনেকে মিলে এসেছিল, তেমনি আসুক আবার। গাঁ জুড়ে মেলা বসে যাক। খাওয়া-দাওয়া আহার আপ্যায়ন কিছুর জন্য ভাবতে হবে না। নিরঞ্জন খাঁড়া হেড মাস্টারমশাই বড় বড় মোচ্ছব আর মেলা পরিচালনা করে করে এখন এক্সপার্ট হয়ে গেছেন। এসব নাকি এখন তাঁর কাছে কিছুই না। সেক্রেটারি উজান আফতাব তাই ছাত্রসঙেঘর সাধারণ সভায় ঘোষণা করে দিয়েছে অভিযানের দিন। যে যে যেতে চায় সবাই যেতে পারে। যাওয়ার দায়িত্ব নিজেদের। খাওয়া-দাওয়াও তাই। কারণ সংখ্যা কত দাঁড়াবে কোনও হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। অনিশ্চিত সংখ্যার দায়িত্ব নিরঞ্জনদার হাতে তুলে দেবার ইচ্ছে তার নেই। যতই তাঁর অভিজ্ঞতা থাক। কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। সারাদিন ধরেই এই যাওয়া আসা চলবে। প্রথম সারির কর্মী যারা অর্থাৎ বরুণ হালুই, অনমিত্র সরকার, সায়ন্তনী সেনগুপ্ত, অচিরা পল্লে, সুচিত্রা সাত্তার, অজয় চোংদার এরা তো আসছেই। সেইসঙ্গে আসবে অজস্র সাধারণ সদস্য। দেবপ্রিয়র খুব ইচ্ছে মেজজেঠু আসেন, মেধার ইচ্ছে রণজয় আসেন, উজান তার দাদুকে আনতে চাইছে। পলিটিক্যাল পার্সনদের আসায় মৈথিলীর আপত্তি ছিল, যেমন তার মা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা কর্মী খুব সম্ভব পরবর্তী নির্বাচনে একজন প্রার্থী। মাকে সে বাদ দিয়ে রেখেছে তাই। কিন্তু উজান বারবার আশ্বাস দিয়েছে তার দাদু পলিটিক্যাল পার্সন হিসেবে আসছেন না। তিনি তাঁর মামার বাড়ি বরিশাল জেলার কীর্তনখোলা গ্রামের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না।
—‘এ গুলা কি গ্রাম নাকি? গাঁ দেখতি হয় ও বাংলায় যা।’ এই হল তাঁর মুখের বুলি। দাদুকে স্বভূমি হারানো একজন বিরহী মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়া গ্রামের চাঁদমুখ দেখিয়ে ভোলাতে চায় উজান। তা ভোলাক। মেধা বা মৈথিলী আর আপত্তি করেননি।
সকাল থেকেই অগ্রবাহিনী আসছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্রসঙ্ঘের ছেলে মেয়ে। উত্তর কলকাতা, পূর্ব কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, হাওড়া…আসছে তো আসছেই। আকাশ গাঢ় নীল। এখনও বেশি শীত পড়েনি। বিদ্যেধরী মাতলার দিক থেকে একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া গরম হত হতে আবার গাঁয়ের পুবে জলাভূমিতে কাক-চান করে মিঠে মিঠে ঠাণ্ডা হয়ে কেওড়াখালির ওপর দিয়ে বয়ে যায়। আকাশে শাদা শাদা তুলো মেঘের পাশাপাশি বহু বিচিত্র পাখি। হায়ার সেকেন্ডারির চৈতালি বলল—‘ছাগলছানাগুলোকে কি জুতোর পালিশ দিয়ে পালিশ করেছে নাকি রে?’
—‘যা বলেছিস।’ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সারং বলল।
এঞ্জিনিয়ারিং ফাইন্যাল ইয়ারের উদিত সুইটজারল্যান্ড ঘুরে এসেছে। বলল— ‘এই লেকটা অবিকল সুইস লেকের মতো নীল। এতে নীল যেন মনে হয় আর্টিফিশিয়াল।’
সুমিতা বলল—‘আসলে লেকটা এ তো পরিষ্কার যে আকাশটা পুরোপুরি রিফ্লেকটেড হয়েছে, তীরের গাছগুলোর ছায়া পড়েছে কী ওয়াণ্ডারফুল দ্যাখ্।’
—‘ওই দ্যাখ্, মাছ খেলা করছে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তলায় জলজ বন। হ্যারে, এখানে মুক্তোর চাষ করা যায় না?’
অমৃক ভরদ্বাজ বলল—‘দিস ইজ নিপা পাম, আই হ্যাভ রেড অ্যাবাউট দীজ ইন কনর্যাড।
‘সুমিতা হোয়াট ইজ ইট্স্ লোক্যাল নেম?’
সুমিতা অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল— ‘সরি, জানি না রে, লোক্যাল পীপলরা বলতে পারবে, এই খোকা; তোমার নাম কি?’
—‘এরসাদ।’
‘এই গাছগুলোকে তোমরা কি বলো ভাই?’
‘হেঁতাল।’
—‘এই হেঁতাল? এখানে বাঘ লুকিয়ে থাকে না?’
এরসাদ ফিক করে হেসে ফেলল। বলল—‘আমরা নুকুই।’
—‘চকলেট খাবে?’
—‘তুমি বাদাম খাবে?’ হাতের মুঠো ফাঁক করে দেখাল এরসাদ। রাস্তায় ঘাটে, শিশু বালক বৃদ্ধ সবার সঙ্গেই কিশোর-কিশোরীদের ভাব হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলে। বাঁশবনে। পুকুর ধারে, উজ্জ্বল রোদ্দুরের মধ্যে তাদের সাদা শাড়ি, ফ্রক, পাজামা-পাঞ্জাবি জিনস, সালোয়ার-কুর্তা ঝলমল করছে। মৈথিলীদির নির্দেশ আছে সবাই যেন যথা সম্ভব শুভ্র বেশ পরে। শুভ্রতার মধ্যে ধনী দরিদ্র, শহর-গ্রাম, উন্নত-উন্নয়নশীল সব একাকার হয়ে যাক। এতোজন ছেলে মেয়ে যদি আজকালকার বাজার-মাত করা বহুবর্ণ বিচিত্র ছাঁটের পোশাক পরে আসতে থাকে তো—গ্রামের সদ্য জাগ্রত শিশু-বালক-কিশোর মনগুলি উদ্ভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। মেধাদি সেবার এদের পুরনো কাপড় দেওয়ায় খুব আপত্তি করেছিলেন। এখন ওদের মা মাসি পিসি জেঠি কাকীদের হাত দিবারাত্র চলছে। হাটে কেনা কাপড়, সমিতিতে সেলাই-করা পরিচ্ছদ পরে যে যার নিজস্ব পরিচ্ছন্ন চেহারায় আছে। শহরের ছেলেমেয়েদের বাতিল পোশাকের ময়ূরপুচ্ছ পরেনি। রণজয় বিশ্বাস এবং উজানের বাবা তার দাদুকে নিয়ে পৌঁছে গেছেন। মেধাই কেন্দ্রীয় কমিটির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পৌঁছতে দেরি করে ফেললেন। খালি দেবপ্রিয় এখনও আসেনি। সে মেজজেঠুকে নিয়ে আসছে। লুকু এসেছে তার বাবা ও ভাইকে নিয়ে। এরকম পেল্লাই সাইজের পিকনিক কেউ আশা করেনি। সবাই অবাক হয়ে গেছে। অঞ্জুমন বললেন— ‘এ যে দেখি মহতী জনসভা। মেধা, এরকম তো চিন্তা করিনি।’ মেধা স্মিত মুখে বললেন—‘ ছেলেকে শুধান।’ লুকুর মাথায় সিঁদুর দেখে পদ্ম, বিজলি, কমলা, সুবচনী, রেহানা বিবি, শরিফা বিবি, সব ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ‘লুকুদিদি, বিয়ে করেচো, খাবার দাও নাই? নুকিয়ে, নুকিয়ে, অ্যাঁ? লুকু লাজুক মুখে বলে— ‘এতজন বরযাত্রী গেলে আমার বাবা হার্ট ফেল করত কাকী।’ ‘হা-ই দ্যাকো, বরযাত্তর কেন, তুমি আমাদের কন্যা নয়? আমরা কনের ঘর তো?’ লুকু লজ্জায় বরের পরিচয় দিতে পারছে না। ইদানীং স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঢেলে সাজাবার জন্য, গ্রামের ছেলেদের ট্রেনিং দেবার জন্য দেবপ্রিয় গ্রামে ঘন ঘন আসছে। দেবুদাদা বলতে এরা অজ্ঞান! সে বাচ্চাদের পিপারমিন্ট দেবার ছল করে উৎসুক নারীজনতার ভিড় থেকে কোনক্রমে নিজেকে সরায়। দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে ওরা লুকুদিদির কোনও তফাৎ খুঁজে পাচ্ছে না, কেউ কেউ অবশ্য লক্ষ্মী কিম্বা সরস্বতীর নামও করছে। কিন্তু বেশির ভাগই একমত যে এ সাক্ষাৎ অসুরদলনী মা দুর্গা। উজান তার বাবাকে বলল— ‘সভা নয় বাবা মেলা, আমরা সংখ্যায় কতো তোমরা দেখো, তোমাদের দেখা দরকার।’
ইদ্রিস আমেদ স্কুল বাড়ির বাইরের দাওয়ায় জমিয়ে বসেছেন, মেধা তাঁর দলবল নিয়ে পৌঁছতে তাঁর মামার বাড়ির ভাষায় বললেন, ‘আমায় চিনতে পারস? ধিঙ্গি, কদমবুসী কর, অনেক বড় হইছস, বুড়া তো হস নাই আমার মতো!’ মেধা হেঁট হতেই বৃদ্ধ তাকে ধরে ফেললেন। আশির অনেক ওপারে বয়স চলে গিয়েছে। মুখময় পাকাদাড়ি। অর্ধেক দাঁত নেই। মেধার গালে তিনি সশব্দে চকাস করে একটা চুমু খেলেন—‘বিয়া করস নাই? খালি নাচ? নেচে নেচে বেড়াইছস? ভারি মজা!’ তাঁর কাণ্ড দেখে মৈথিলী উজান হাসছে। রণজয় বিশ্বাসের পরিচয় নিয়ে পাশে বসতে বলছেন—‘তুমি শুনি পুলিসের লোক, ধিঙ্গির সাথে জুটছ ক্যান? আমারে সরকারি বান্দর কয়, তা জানো? তোমারে কি কইসে?’ লাঠির বাঁকানো ডগা বাড়িয়ে বৃদ্ধ উজানকে ধরেন—‘এই দ্যাখো, আজকালের পোলাপান সব আমারে খেদায়, আমি নিষ্কম্মা, আমি ঢেঁকি…।’
বাড়িতে বাড়িতে আলাদা আলাদা করে খবর নিতে নিতে এগোচ্ছেন মেধা। ‘সিধু ভাই, সর্ষে হবে? পাটের দর কত যায়?’ ‘সর্ষে হবে, পাটের দর ভালোই।’ ‘ময়না, তোমার ছোটটা হামা দিচ্ছে? ‘ধরে ধরে দাঁড়ায়’, ‘বলো কি? তবে তো আনোয়ার সায়েবের আর একটি বংশধরের আসবার সময় হয়ে গেল!’ ময়না হাসে। হাত মুখের ভঙ্গি করে জানিয়ে দেয় সেটি আর হতে হচ্ছে না। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নীলমণি বসে। বলছে ‘গাঁ থেকে একটা ডাক্তার বার করতেই হবে দিদি, বাইরে যাবে না, এখানেই বসবে, এই কড়ারে।’ মেধা আশ্বাস দিচ্ছেন—‘কড়ার করতে হবে না, এ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ক্রমে বিরাট হাসপাতাল হয়ে উঠবে। দেবদাদা সেই চেষ্টা করছে। লাইব্রেরিতে রয়েছে নিতাই। তার অভিজ্ঞতা ছেলেরা বড় বৈজ্ঞানিক রূপকথা পড়ছে। এতোটা কি ভালো? এতো সত্যি বিজ্ঞান নয় কো দিদি।’ মেধা বললেন— ‘তোমার বার্ষিক বই কেনার লিস্টিটা মৈথিলিদিদির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কিনো। পড়ুক না ছেলেরা সায়েন্স ফিকশন। সেই সঙ্গে ওরা ছড়ার বই, কবিতার বইও পড়ছে তো? সহজ জ্ঞান-বিঞ্জানের যে সব সিরিজ কেনা হয়েছে। বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া সেগুলোও নিচ্ছে তো?’
—‘নিচ্ছে, তবে গল্পের দিকে ঝোঁক বেশি।’
গরু-মহিষগুলি দেখে রণজয় মুগ্ধ। বললেন—‘তোমরা এ দুধ শহরে পাঠাতে পারো না?’
অনিল বাইরি, বাথানের ভারপ্রাপ্ত ছেলেটি বলল— ‘টাটকা দুধ অল্প লাভে ছাড়া হয় দাদা খুব তাড়াতাড়ি উঠে যায়, ছানা, তা-ও বড় শহর পর্যন্ত পৌঁছতে পায় না। আজকাল তালদী, ধপধপি, ক্যানিং সব জায়গায় ভালো ভালো মিষ্টির দোকান ফেঁপে উঠছে। কেওড়াখালির দুধ খেতে হলে, আপনাকে আজ্ঞে এখানে এসে কদিন থাকতে হয়! আসুন না!’
মেধা হেসে বললেন—‘আসলে রণজয় ব্যবসার নীতি নিয়ে এগুলো এরা করেনি। নিজেরা পরিপূর্ণ খেয়ে যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে সেটা বিক্রি করে খরচ উশুল হয়। নিজেরা খাবো না, সব চালান যাবে, দেশের লোক চেয়ে চেয়ে আঙুল চুষবে এ এদের একেবারে ইচ্ছে নয়। এদের জলায় ভালো চিংড়ি হচ্ছে। কলকাতায় দেড়শ টাকা কিলো। এরা গ্রামেই বেচে, আসে পাশে অনেক খদ্দের আছে। শহর থেকেও লোক এসে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। অনিল বাইরি বলল— ‘কিন্তু পাইকারকে আমরা দিই না দাদা। এক কেজি দু কেজি নিজেদের ব্যবহারের জন্য নিতে চাইলে ঠিক আছে।’
ঘুরতে ঘুরতে গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে মেধা বললেন—‘এটা কি নিরঞ্জন? এ স্ট্রাকচারটা কিসের?’
দাওয়ায় নামানো নতুন ঝকঝকে সাইনবোর্ড। সেটা উল্টে দেখিয়ে নিরঞ্জন বলল— ‘আজ্ঞে চা-ঘর দেখুন!’
—‘কে করল এত বড় চায়ের দোকান? তুমি?
—‘আজ্ঞে না।’ নিরঞ্জন জিভ কাটে, ‘আমার সময় কই দিদি? আমি তো ঝালে ঝোলে অম্বলে সবেতে রয়েছি। পঞ্চ থেকে লাইসেন্স বার করে দিয়েছে গঞ্জ থেকে লোক এসে করেছে।’
—‘বুঝলাম না।’ মেধার মুখে বিস্ময়। এ গ্রামে কোথায় কি হচ্ছে তার ব্লু-প্রিন্ট সব সময়ে ছাত্রসঙ্ঘের কাছে থাকে।
মৈথিলী বলল— ‘আপনারা তো এটার কথা আমাদের জানাননি নিরঞ্জন দা!’
নিরঞ্জন বলল— ‘আজ্ঞে পঞ্চ থেকেই করল একরকম। ভোট আসছে, বলছে ভিডিও বসাবে। গ্রামের লোক দেশ-বিদেশের খপর পাবে। ওরাই কাকে লাইসেন্স্ দিয়েছেন, আমি আর কি বলবো! তাছাড়া এই তো কদিনও হয়নি। স্ট্রাকচার সবে শেষ হয়েছে। ধরুন গত পরশু।’
—‘এ বিষয়ে কথা-বার্তা নিশ্চয়ই হচ্ছে অনেকদিন থেকে, জানাতেও তো পারতেন,’ উজানের কণ্ঠ তীক্ষ হয়ে উঠছে।
সায়ন্তনী এতোক্ষণ কাছ থেকে মেধাদিকে দেখবার আনন্দে বিভোর হয়েছিল, সে বরুণকে ইশারা করল, আরও ছেলেমেয়েদের এখানে ডাকতে।
মেধা বললেন—‘ভিডিও পার্লার বানাচ্ছে উজান বুঝেছিস? চা-ঘরের সাইনবোর্ড সামনে। কেন? মৈথিল বুঝলি কিছু?’ তিনি নিরঞ্জনের দিকে চকিতে ফিরে বললেন—‘নিরঞ্জন তোমার কটা চোঙা আছে স্কুল ঘরে?
—‘আজ্ঞে পাঁচ ছটা তো হবেই।’
—‘একটা আমাকে দাও। আর কয়েকটা নিয়ে ছেলেমেয়েদের দাও। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ওরা লোক জড়ো করুক, এখানেই ডাকো সবাইকে। ফাঁকা আছে অনেক লোক ধরবে। আমি এখানেই সবাইকে বুঝিয়ে বলব। যাও নিরঞ্জন, কুইক।’
কিছুক্ষণের মধ্যেই চা-ঘরের সামনেটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। চোঙা হাতে মেধা সদ্য-নির্মিত ঘরের উঁচু দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালেন।
‘কেওড়াখালির ভাইবোনেরা। আমরা এতদিন শহর গ্রাম, ছাত্র গৃহস্থ, ছেলেমানুষ-বুড়োমানুষ সবাই মিলে একমন একপ্রাণ হয়ে নিজেদের সুখে, আনন্দে থাকবার মতো একটা পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছি। আমাদের আনন্দের সীমা নেই এই ভেবে যে এইখানে পরিচ্ছন্ন, শিক্ষিত, সাবলম্বী, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসায় মমতার একতাবদ্ধ একটি পরিবারের মতো এই গ্রাম গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর যে কোনও জায়গা থেকে যে-কেউ এসে এখানে থেকে যেতে পারে, সকলেই বিনা দ্বিধায় বলবে এ গ্রাম আদর্শ গ্রাম। কিন্তু সম্প্রতি চা-ঘর বলে যে দোকানটা এখানে বসানো হয়েছে এটা আপনাদের সর্বনাশ করবে। সামনে চা-ঘর সাইনবোর্ড টাঙিয়ে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে এরা ভেতরে ভিডিও-যন্ত্র বসাবে। যদি জঘন্য, নোংরা ছবি দেখাবার ইচ্ছে ওদের না থাকত, এই কারচুপিটা ওরা করত না। এই সব ফিল্ম দেখতে আসবে আপনাদের ঘরের ছেলে-মেয়ে-বউরা, পরে লুকিয়ে-চুরিয়ে আসবে অল্পবয়সীরাও। যে-সব পাপের কথা, অন্যায়ের কথা, নোংরামির কথা ওরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না সেগুলো এখানে দেখানো হবে সামান্য পয়সার বিনিময়ে। আমোদ-প্রমোদের বস্তু বলে, হাসতে হাসতে দেখানো হবে। আপনাদের কষ্ট করে জমানো পয়সা পাপ ব্যবসায়ীর থলিতে চলে যাবে। সেই সঙ্গে যাবে আপনাদের ছেলেমেয়েদের চরিত্র। আপনাদের ফুলের মতো ছেলেমেয়েরা, এমনকি নিষ্পাপ ভাই-বোন-স্বামী-স্ত্রীরা সেই সব পাপ বয়ে আনবে আপনাদের পবিত্র সংসারের ভেতর, সমাজের ভেতর’—উজান তার ব্যাটারি-সেটে টেপ করে নিচ্ছিল এই ভাষণ, বার বার পুনরাবৃত্তি করবার দরকার হতে পারে এ ভাষণ। এখানে, অন্যত্র। এ তাদের এক নতুন অভিজ্ঞতা। নতুন বাধা।
মেধা বলতে লাগলেন—‘আপনারা এখানে সুখের, আনন্দের স্বর্গ গড়েছেন, আমরা আপনাদের দেখে প্রেরণা পেতে আসি। আদমের ইডেন উদ্যানে সর্বনাশের পরামর্শ নিয়ে এসেছিল খল শয়তান, জানেন তো সামান্য অপবিত্রতার কারণে নলরাজার কী দুর্গতি হয়েছিল কলির হাতে? এই কলি, এই শয়তান আপনাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনারা এই চা-ঘর চালু করতে দেবেন না। আপনারা সবাই আছেন, আমি দরখাস্ত লিখে দেবো, পঞ্চায়েতের কাছে এর লাইসেন্স বাতিল করার দাবি করুন। ছাত্ৰসঙ্ঘ আপনাদের টিভি সেটের ব্যবস্থা শীগগীর করবে, আপনারা এই ভিডিও-পার্লার বন্ধ করুন, বয়কট করুন, জ্বলন্ত আগুনের হাত থেকে, উদ্যত সাপের ছোবল থেকে, বাঘের থাবা থেকে যেমন বাচ্চাদের রক্ষা করেন, ঠিক সেই ভাবে রক্ষা করুন ওদের এই সর্বনেশে চা-ঘরের হাত থেকে।’
জনতার মধ্যে থেকে শোরগোল উঠল, মহিলা কণ্ঠে। পুরুষ গলায়। অনেকে চিৎকার করে উঠল—‘লিখে দ্যান দিদি, সই করে দিচ্ছি।’
‘আমরা আজকেই পঞ্চে ছুটব, ঠকাচ্ছে, আবার আমাদের ঠকাচ্ছে।’
‘শয়তানের পো রক্তবীজের ঝাড়। একদিকে কোপ মারি তো আরেক দিকে বাড়ে।’
মেধা বললেন—‘নিরঞ্জন কাগজ-কলম নিয়ে এসো।’ জনতার মধ্যে থেকে প্রধান প্রধান লোকেরা সামনে এগিয়ে আসছে, মেধা চা-ঘরের দাওয়া থেকে নামছেন, হঠাৎ কোথা থেকে দমকা হাওয়ার মতো কয়েকটা লোক ছুটে এলো উজান মৈথিলী দেখল নিমেষের মধ্যে মেধাদি উধাও।’
নিরঞ্জন খাঁড়া ভীষণ চিৎকার করে উঠল—‘ওই দিদিকে নিয়ে যায়, উজান ভাই। গুণ্ডা, গুণ্ডা। চোট্টা,’ নিরঞ্জন বাঘের মতো লাফ মেরে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিরাট জনতা মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। জনতার মধ্যে থেকে কান্নার রব উঠেছে ‘বাঁচাও।’ ‘মেরে ফেললে।’ ‘পালা’। ‘পালা’। ‘দিদিমণিকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল গো?’ ‘রণজয়দা…মেধাদি কোথায়’ দেব আর্তস্বরে চেঁচাচ্ছে, ‘দক্ষিণের মাঠের দিকে চলো, ‘বাবা, বাবা, বুল্টু! গুঞ্জন!’ মৈথিলীকে দেখছি না কেন’ ‘প্রমিত ফলসাগাঁয়ের দিকে চল।’ পদ্ম কেঁদে বলল—‘ও দিদি গো, ওরা বোধহয় ফুলতলির দিকে গেল, আমার ছোট ছেলেটার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে গেছে।’
পদ্মর কথাই ঠিক। ওরা বোধহয় দলে অনেক ছিল। ভিড়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। জনতাকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে কেউ কেউ ফলসা গ্রামের দিকে ছুটে গিয়েছিল। মেধাকে শেষ পর্যন্ত ফুলতলির মাঠে যাবার পথের জঙ্গলটায় পাওয়া গেল। অভিজ্ঞ পুলিসের চোখ, রণজয় বিশ্বাসই প্রথম তাঁকে পেলেন। তিনি একটা প্রকাণ্ড শিশু গাছের তলায় উপুড় হয়ে পড়ে আছেন যেন কেওড়াখালির এই বনস্থলীকে প্রণাম করছেন, কিম্বা চুমো খাচ্ছেন। আশেপাশে বন্য ঝোপ। পরনের পাটকিলে রঙের কলাক্ষেত্র শাড়ি বিস্রস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু তাঁর কুমারী জননীদেহের সমস্ত লজ্জাস্থান আবৃত করে রয়েছে এখনও। তিনি বলতেন শাড়িগুলো খুব টাফ।
পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের বাহুবলের যুদ্ধ এমনিতেই অসম যুদ্ধ। কিন্তু সমাজ যখন সামগ্রিকভাবে সর্ব অর্থে গৃধ্নু হয়ে ওঠে, তার সমস্ত মূল্যমান যখন ভোট আর টাকা, টাকা আর ক্ষমতার মাপকাঠিতে নিরূপিত হতে থাকে তখন সে সমাজে পুরুষ আর পুরুষ থাকে না, কিম্পুরুষ হয়ে যায়। নারীর সঙ্গে লড়াইয়ে নামলে সম্মুখসমরে তাকে প্রাণে মারবার আগে এই কিম্পুরুষরা আগে তাকে তার করুণতম স্থানে আঘাত করে। নারী যেন এ সময়ের এক নিরপরাধ দুর্যোধন, অন্যায় যুদ্ধে যার উরু ভঙ্গ করছে ওরা। মেধা প্রাণপণ শক্তিতে ওদের ঠেকিয়েছেন। ঠেকিয়েছেন জীবনের শেষতম সংগ্রামে। হয়ত শেষ পর্যন্ত পারতেন না, কিন্তু রণজয়রা আসছেন টের পেয়ে ওরা বোমা ফাটাতে ফাটাতে চলে গেছে। দেবপ্রিয় ভাঙা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ‘স্ট্রেচার।’ পদ্ম, সিধু, নিতাই, নীলমণি নিমেষের মধ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্ট্রেচার এনে দিয়েছে। দেহটা উল্টেই দেবপ্রিয় আর মৈথিলী স্থির হয়ে গেল। দলা দলা রক্ত। রক্তে ভাসছে চারদিক। কেওড়া এবং ফলসা, সুযযিপুর, সরাল এবং আরও কিছু কিছু নিকটবর্তী গাঁয়ের জনতা ততক্ষণে আঘাতে আঘাতে ধরাশায়ী করে ফেলেছে চা-ঘর। তার ভেতর থেকে রঙিন টিভি, ভিসিপি, ক্যাসেটের প্রাথমিক আয়োজন সব টুকরো টুকরো হয়ে চতুর্দিকে ছিটকে যাচ্ছে। দলে দলে ছাত্র ছুটে আসছে উত্তর কলকাতা, মধ্য কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, বৃহত্তর কলকাতা, হাওড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুরের কলেজ, য়ুনিভাসিটি, এঞ্জিনিয়ারিং মেডিক্যাল কলেজ থেকে। গ্যারিসনের পর গ্যারিসন অস্ত্রধারী সৈনিকের মতো। তাদের ছুটন্ত পায়ের তলার মেদিনী কম্পমান। তারা শুভ্র, স্নাত, নিষ্কলঙ্ক। মেধাদি, মেধা ভাটনগরকে অজ্ঞাত আততায়ী মেরেছে। তাই তারা ছুটেছে, সকলে এক দিকে, এক লক্ষ্যে। আজ বহুদিন হল মেধা ভাটনগর জীবন্ত কিংবদন্তী হয়ে গেছেন। কেউ সেভাবে বলেনি তবু তিনি তাদের মধ্যে প্রচারিত, প্রসারিত হয়ে গেছেন। তিনি তাদের সমস্ত আশা সমস্ত স্বপ্নের কাণ্ডারী। তাদের শেষ নির্ভর।
দেবপ্রিয়, উজান, প্রমিত, নিতাই স্ট্রেচার নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে, পথ করে দাও, মৈথিলী লুকু গুঞ্জন ছুটেছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দিকে। নীলমণি আর মকবুলের সঙ্গে যদি প্রাথমিক কিছু ব্যবস্থা করা যায়। বৃদ্ধ আমেদ সায়েব ঘোলাটে চোখ আকাশের দিকে তুলে বলছেন ‘অত মন্দ কিসু কয় নাই, হায় আল্লা তোরা রুকুরে মারস ক্যান?’ নিরঞ্জন খাঁড়া আর সিধু দুটো বিরাট পাহাড়ের মতো জনতা সামলাচ্ছে। পৃথ্বীন্দ্রকে নিয়ে রণজয়ের জিপ সগর্জনে ছুটে আসছে, মেধাকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাবে সোজা। এখুনি। রণজয়ের মুখের রেখা ক্রমশ কঠিন টান টান হয়ে যাচ্ছে। এখুনি বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।
দেবপ্রিয় জানে, মৈথিলী জানে, উজান লুকু গুঞ্জন যারা ডাক্তার নয় তারাও জেনে গেছে নিয়ে যাওয়া বৃথা। হয়ত যেতে যেতেই সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই হাজারে হাজারে ছাত্রদল তা জানে না, মানেও না। তারা এখনও ছুটে চলেছে তাদের চোখ সংকল্পে জ্বলছে, নিষ্পাপ হাত প্রতিবাদে ওপরে তোলা, পদভরে মেদিনী প্রকম্পিত, তারা ছুটছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, গ্রামান্তর থেকে গঞ্জে, গঞ্জ থেকে শহরে, বস্তিতে বস্তিতে, বাস্তুতে বাস্তুতে, সেই সঙ্গে ছুটছে কেওড়া, আজিগ্রাম, মখতবপুর, ভাঁটরো, কেতুপাড়া, ফলসা, সরাল, মনসাপাড়া, নবগ্রাম, হর্তুকি, শিমুলডিহি…। তারা বিশ্বাস করে মেধা ভাটনগর বেঁচে উঠবেন, বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন। শুধু এই আশ্বাসটুকু নিয়েই তারা পরবর্তী শতাব্দীর দিকে অনির্বাণ মশাল হাতে দৌড়য়।