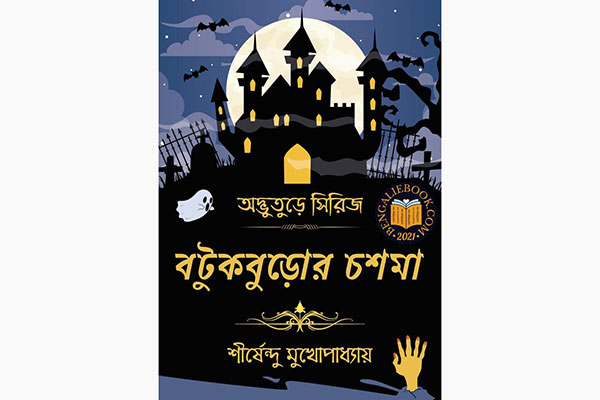১. কর্তাবাবু, একটা কথা ছিল
“কর্তাবাবু, একটা কথা ছিল।”
“কী কথা?”
“বলছিলাম কী, এই লম্বা লোকেরা মানুষ কেমন হয়?”
“এ আবার কেমন ধারা কথা, লম্বা লোকেরা আবার আলাদা করে ভাল বা খারাপ হতে যাবে কেন?”
“একটা ধাঁধায় পড়েই জানতে চাইছি আর কী!”
“তা লম্বা লোক নিয়ে তোর সমস্যা হচ্ছে কেন? এই তো আমিই তো একজন লম্বা লোক। আমার তিন ছেলে লম্বা, পুরুতমশাই ব্রজ ভটচাজ লম্বা, সাত্যকি বাঁড়ুজ্যে লম্বা, দারোগা পরেশ ঘোষ লম্বা, নব মিত্তির লম্বা, তা আমরা কি খারাপ লোক?”
বটু ওরফে বটকেষ্ট গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, “আপনারা তার কাছে নস্যি। আপনাদের মাথা তার কোমরের কাছ বরাবর হবে বড়জোর। তার বেশি নয়।”
“বটে! তা এ তল্লাটে তেমন লম্বা কে আছে? হরিপুরে বৃন্দাবন পাল অবশ্য বেজায় লম্বা, আর নবগঞ্জের বিষ্ণু পাঠকও বটে বিশাল ঢ্যাঙা…!”
“আজ্ঞে, তাঁরাও তার বুক পর্যন্ত হবেন কি না সন্দেহ।”
“অ, কিন্তু লম্বা লোক তুই পেলি কোথায়? আর তাকে নিয়ে তোর সমস্যাই বা হচ্ছে কেন?”
বটু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “সে কাছেপিঠেই আছে। বাড়ির পিছনের ফটকে একটু আগেই দাঁড়িয়ে ছিল কিনা!”
“দাঁড়িয়ে ছিল মানে? ফটকে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? হয় ভিতরে আসবে, না হয় বিদেয় হবে। লোকটা কে, কী চায় জিজ্ঞেস করেছিস?”
“আজ্ঞে, ঠিক সাহস হয়নি।”
“কেন, লোকটা কিষণ্ডাগুন্ডা গোছের?”
“বলা মুশকিল।”
“পোশাক আশাক কেমন?”
“আজ্ঞে, পোশাক তেমন খারাপ কিছুও নয়। পরনে বোধহয় একটা পাতলুনের মতো দেখলুম, গায়ে একটা জামাও মনে হয় ছিল, গলায় একটা মাফলার জড়ানো ছিল কি না ঠিক মনে পড়ছে না, গায়ে একটা কোট থাকলেও থাকতে পারে।”
“বুঝলাম। এখন দয়া করে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো লোকটা কী চায়, কোথা থেকে এসেছে, এ বাড়ির আত্মীয়-কুটুম কি না, আর যদি ভিখিরি হয় তো সোজা বলে দিয়ো, কানাখোঁড়া ছাড়া আমরা কাউকে ভিক্ষে দিই না।”
“আজ্ঞে, আমারও সেই সব জানতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু লোকটা এমন ভেকুড়ি কাটল যে, ঠিক সাহস হল না।”
“ভেচকুড়ি! সেটা আবার কী?”
“আজ্ঞে, ভেচকুড়ি খুব ভয়ের জিনিস। বড় বড় চোখ করে মুখটা ভেংচি কেটে এমন একখানা ভাব করা যাতে লোকে ভড়কে যায়।”
“তুই তো ভড়কেই আছিস। পাগল দেখলে ভড়কাস, মাতাল দেখলে ভড়কাস, পুলিশ দেখলে ভড়কাস। তোর হল রজ্জুতে সর্পভ্রম!”
“আজ্ঞে কর্তাবাবু, ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে হয়তো। তবু বলি, ভয়ভীতি থাকা কিন্তু ভাল। ধরুন সর্পে রঞ্জুম হওয়াই কি তা হলে ঠিক হত?”
“দ্যাখ, দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। তা তুই যদি এতই ভেড়ুয়া যে একটা লোক খানিকটা লম্বা বলে তার কাছেই ঘেঁষতে পারলি না, তখন না হয় নব, হরেন আর কানুকে জুটিয়ে দলবেঁধে গিয়ে লোকটার উপর চড়াও হতিস।”
“আজ্ঞে, নবর কথা আর কবেন না। সে সেই সাতসকালে গিন্নিমার কাছ থেকে বাজারের পয়সা নিয়ে বেরিয়েছে। এখন দেখুন গে, বাজার ফেলে কালীস্যাকরার সঙ্গে দাবা খেলায় মশগুল হয়ে আছে। রোজ সকালে এক পাট্টি দাবা না খেললেই তার নয়।”
“বলিস কী, নব আবার দাবাড়ুও নাকি? তাজ্জব ব্যাপার তো!”
“তবে আর বলছি কী? আর হরেন? তার কথা আর কী বলব কর্তাবাবু। যত কম বলা যায় ততই ভাল। বুড়োকর্তার জন্য রোজ ডাব পাড়তে নারকোল গাছে উঠে কী করে জানেন? নারকোল গাছের সঙ্গে কোমরের গামছাখানা কষে বেঁধে নিয়ে আরামসে ঘুম লাগায়।”
“ওরে বাবা! নারকোল গাছের উপর উঠে ঘুমোয়? কী সব্বোনেশে কথা!”
“গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালে তার নাকের ডাকও শুনতে পাবেন।”
“বটে! একদিন পড়ে মরবে যে!”
“আর কানুর কথা শুনতে চান? না শুনলেই ভাল হত।”
“কেন রে? সে আবার কী করল? দিব্যি তো ভালমানুষের মতো চেহারা, চোখ তুলে কথা কয় না।”
“কর্তাবাবু, আপনার মেলা গুণ আছে বটে, আর সেকথা আমরা বলাবলিও করি। এই যেমন আপনার দয়ার শরীর, আপনার বেজায় বুকের পাটা, সুজনবাবুর ছেলের বিয়েতে আপনি বাহান্নটা রসগোল্লা খেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি মানুষ চেনেন, একথা আপনার বন্ধু কেন, শ্যুরেও বলবে না।”
“এ তো বড় চিন্তায় ফেলে দিলি! কানু করেছেটা কী?”
“গত কদিন ধরে সকালের দিকে অঘোরখুড়ো যে তাঁর চশমাটা খুঁজে পাচ্ছেন না, সেকথা কি আপনি জানেন? না, জানার কথাও নয়। রোজই সকালে চশমা হারানো নিয়ে খুডোমশাই চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করেন। কিন্তু একটু বেলার দিকে চশমাজোড়া ঠিকই আবার খুড়োমশাইয়ের টেবিলেই পাওয়া যায়। ঠিক কিনা কর্তাবাবু, বলুন?”
“হু। ঠিকই বলছিস বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু চশমার সঙ্গে কানুর কী সম্পর্ক?”
“গভীর সম্পর্ক কর্তাবাবু, গভীর সম্পর্ক। আর শুধু খুড়োমশাইয়ের চশমাজোড়াই তো নয়, ব্ৰজবিহারী ঠাকুরমশাইয়ের নামাবলিখানা আর বিজয়বাবুর ল্যাবরেটরির আতশ কাঁচখানাও সেই সঙ্গে গায়েব হয়ে যায়, একটু বেলার দিকে অবশ্য ফিরেও আসে।”
“দ্যাখ বটু, তোর কথা বুঝবার চেয়ে চিনেম্যানের কথা বোঝা বরং সহজ।”
“কথায় একটু মারপ্যাঁচ না থাকলে ঠিক জুত হয় না কিনা। তবে আসল কথাটা হল, কানু সকালে এ বাড়ির চারটে দুধেল গাইকে নিয়ে গোচারণের মাঠে চরাতে যায়, জানেন তো?”
“তা জানব না কেন? কানু তো আমাদেরই রাখাল।”
“আজ্ঞে, তাই বলছি। মাঠে গোরুগুলোকে খোঁটায় বেঁধে দেওয়ার পর কিন্তু সে আর রাখাল থাকে না। গায়ে নামাবলি জড়িয়ে চোখে চশমা এঁটে হাতে আতশ কাঁচ নিয়ে সে তখন কানাইপণ্ডিত জ্যোতিষার্ণব।”
“বলিস কী?”
“আজ্ঞে, আপনি যদি এখনই বটতলায় গিয়ে হাজির হতে পারেন, তা হলে কানাইপণ্ডিতের চেহারা দেখে তাকে কানু বলে চিনতেও পারবেন না। টিকিতে কল্কে ফুল বেঁধে কম্বলের আসনে বসে লোকের কুষ্টি আর হস্তরেখা বিচার করে গড়গড় করে নিদান আউড়ে যাচ্ছে। তার সামনে অন্তত বিশ-পঁচিশজন লোকের লাইন।”
“বাপ রে! আমাদের বাড়িতে একটা আস্ত জ্যোতিষী ঘাপটি মেরে বসে আছে, কখনও টেরটিও পেলাম না তো! ভাল কথা, আমার বাহান্ন বছর বয়সে নাকি একটা ফাঁড়া আছে। কানু ফিরলে একটু বলিস তো, আমার হাতটা যেন একটু দেখে দেয়।”
“যে আজ্ঞে। সে না হয় হল, কিন্তু ওই লম্বা লোকটার কী করা যায় তা একটু ভেবে দেখবেন কি কর্তা?”
“ও হ্যাঁ, তাই তো! তোর গল্পের চোটে তো ঢ্যাঙা লোকটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তা নব, হরেন আর কানু নেই বলে কি এ বাড়িতে লোকের অভাব? আমার তিন-তিনটে সোমত্ম ছেলে রয়েছে, তা ছাড়া অঘোরখুড়ো, বিরাজজ্যাঠা, একচন্দ্রদাদা, ব্রজঠাকুর, বিজয়মামা…!”
“আর কবেন না কর্তা। আপনার তিন ছেলের মধ্যে বড়জন নীলকান্তদাদাবাবু এ সময়ে লেখাপড়া নিয়ে গম্ভীর মুখে বইপত্তরে ডুবে থাকেন। মেজদাদাবাবু অয়স্কান্ত হাপুস-হুঁপুস করে ব্যায়াম করে যাচ্ছেন, এ সময়ে কথা কন না। আর ছোটদাদাবাবু কৃষ্ণকান্ত তানপুরা সাপটে গলা সাধছেন। কাউকে ডেকে সাড়া পাওয়ার উপায় নেই। অঘোরখুড়ো এ সময় তাঁর কবিরাজি গাছগাছড়ার খোঁজে বেরিয়ে যান। বিরাজজ্যাঠার কথা তো সবাই জানে। গতবার হালদারদের পুকুরের সেই অতিকায় কাতলা মাছটা জ্যাঠাকে লেজে খেলিয়ে তাঁর ছিপ সমেত পালিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে মাছটাকে ধরার জন্য রোজই ছিপ নিয়ে সাতসকালে হালদারপুকুরে হানা দেন। একচন্দ্ৰদাদা রোজ সকালে নিয়ম করে গঞ্জের মোট তিনশো তেইশজনকে কুশল প্রশ্ন করতে বেরিয়ে যান, এতক্ষণে বোধহয় একশো বাইশজন পর্যন্ত হয়েছে। ফিরতে তাঁর বেলা হবে। ব্রজঠাকুরের পাঁচবাড়ির নিত্যপূজা আছে। আর বিজয়মামা তাঁর জাদুইঘরে বসে নুনের সঙ্গে চুন মেশালে কী হয় তাই হাঁ করে ভাবছেন।”
“নুনের সঙ্গে চুন! তা মেশালে কী হয় বল তো?”
“আজ্ঞে, ওটা কথার কথা। জাদুইঘরে বসে তিনি যে নানা সাইজের কাঁচের পাত্রে কোন বিটকেল জিনিসের সঙ্গে কোন বিঘুঁটে জিনিস মেশান, তা কে জানে বাবা! তবে এমন সব কিম্ভুত
গন্ধ বেরোয় যে, নাকে চাপা দিয়ে পালানোর পথ পাই না।”
“বুঝলাম। তা হলে লম্বা লোকটাকে তাড়ালি কী করে?”
“তাড়ালাম? তাড়ালাম আর কোথায়? সে দিব্যি এখনও পিছনের ফটকের কাছে ঝুপড়ি আমগাছটার তলায় গ্যাট হয়ে বসে আছে।”
“এখনও বসে আছে? আগে বলবি তো! চল তো গিয়ে দেখি।”
“তা হলে বরং বন্দুকটা নিয়ে নিন সঙ্গে। দিনকাল ভাল নয়, বলা তো যায় না।”
“দুর পাগল! এই সকালে তো আর চোর-ডাকাত আসবে না।”
“অন্তত মোটা লাঠিগাছটা হাতে থাকলে ভাল হয়।”
“দুর-দুর। ওসবের দরকার নেই।”
“আপনার কর্তা, বড্ড সাহস।” বীরেন রায় ডাকাবুকো মানুষ, লম্বা-চওড়া চেহারা। ইজিচেয়ার থেকে উঠে বীরদর্পে পিছনের ফটকের দিকে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর পিছনে একটু তফাতে বটু ওরফে বটকৃষ্ণ।
পিছনের ফটকের বাইরে ঝুপসি আমগাছটার তলায় সত্যিই একটা লোক বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। পরনে আধময়লা হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা সুতির মোটা জামা, গলায় একটা গামছা জড়ানো, মাথা ন্যাড়া এবং টিকি আছে। পাড়ায় নেড়িকুকুরগুলো অচেনা লোক দেখে একটু দুরে দলবেঁধে দাঁড়িয়ে খুব ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে।
বীরেনবাবু তাকে দেখেই একটা বাঘা গর্জন ছাড়লেন, “অ্যাই! ওঠো তো, উঠে দাঁড়াও। তুমি নাকি বেজায় লম্বা! দেখি তো তোমার হাইটটা!”
লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে হাতজোড় করে বলল, “আজ্ঞে না কর্তা, আমি তেমন কিছু লম্বা নই। গরিবের কি আস্পদ্দা সাজে? লম্বা হতেও তো মুরোদ চাই কর্তা!”
বীরেনবাবু এই বিনয়বচনে একটু নরম হয়ে বললেন, “আহা, লম্বা হওয়ার সঙ্গে গরিব-বড়লোকের কথা উঠছে কেন? গরিবেরা কি আর লম্বা হয় না? একটু উঠে দাঁড়াও দেখি বাপু, হাইটটা একটু দেখে নিই।”
লোকটি ভারী অনিচ্ছের সঙ্গে দাঁড়াল। দেখা গেল, বটু যতটা বলেছিল ততটা না হলেও লোকটা বেশ লম্বাই!
ভ্রূ কুঁচকে খুব মন দিয়ে লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জরিপ করে নিয়ে বীরেনবাবু বটুকে উদ্দেশ করে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, “তোর সব তাইতেই বাড়াবাড়ি। এমনভাবে বললি যে মনে হল, লোকটা বুঝি দু’পেয়ে তালগাছ। তা ছাড়া পরনে পাতলুন নেই, কোট নেই, মাফলারের জায়গায় গামছা। এবার হরডাক্তারকে দেখিয়ে চোখে চশমা নে।”
বটু মাথা চুলকে লজ্জিত হয়ে বলল, “মাপজোকে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে বটে।”
বীরেনবাবু লোকটাকে বললেন, “ওহে বাপু, ভেকুড়ি কাটতে পারো?”
লোকটা ভয় খেয়ে বলল, “আজ্ঞে, না বাবু।”
“এই বটু যে বলছিল তুমি নাকি এমন ভেচকুড়ি কাটতে পারো যে, দেখে লোকে ভড়কে যায়!”
“কক্ষনও নয়। আমি জীবনে কখনও ভেকুড়ি কাটিনি। কাকে ভেচকুড়ি বলে তাই জানি না।”
“আহা, সে তো আমিও জানি না। ওরে বটু, ভেচকুড়ি ব্যাপারটা যেন কী?”
“ভেচকুড়ি খুব ভয়ের জিনিস কর্তাবাবু। চোখ দুটো বড় বড় গোল্লা গোল্লা করে তাকিয়ে মুখটায় বিকট রকমের ভেংচি কেটে… উরে বাপ রে, সে বলা যায় না।”
লোকটার দিকে চেয়ে বীরেনবাবু বললেন, “কিছু বুঝলে?”
লোকটা সবেগে মাথা নেড়ে বলল, “আজ্ঞে, না বাবু। ভেচকুড়ি কথাটাই জন্মে শুনিনি। আর অন্যকে ভয় দেখাব কী, নিজেই আমি সর্বদা ভয়ে মরছি।”
“কেন বাপু, তোমার ভয়টা কাকে?”
“আজ্ঞে, কাকে ভয় না পেলে চলে বলুন? চোর, ঠ্যাঙাড়ে, ডাকাত, পুলিশ, গুন্ডা, বদমাশ, ফাজিল ছেলেছোঁকরা, ভূত-প্রেত, সবাইকেই সমঝে চলতে হয় আজ্ঞে। সবাইকেই ভয়।”
“আহা, সেসব তো আমরাও ভয় পাই।”
লোকটা ঘাড় চুলকে লজ্জা পেয়ে বলল, “কী যে বলেন বাবু, কোথায় আপনারা আর কোথায় আমি? এই যে দেখুন না, ঈশেন দাস মাত্র তিনটি হাজার টাকার জন্য আমাকে ভিটেমাটি ছাড়া করে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করল, ভেচকুড়ি টেচকুড়ি জানা থাকলে কি আর পারত ওরকম?”
বীরেনবাবু বললেন, “কিন্তু বাপু, বটু যে স্বচক্ষে তোমাকে ভেচকুড়ি কাটতে দেখেছে সেটাও তো মিথ্যে নয়। আর ভেচকুড়ি দেখে ভয় খেয়েই না সে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল।”
“কী যে বলেন কর্তা! ও ভেচকুড়ি টেচকুড়ি নয়, তখন বোধহয় একটা হাই তুলেছিলুম, তাই দেখেই উনি ভয় পেয়েছিলেন।”
“হাই আর ভেচকুড়ি কি এক হল বাপু? কী বলিস রে বটু?”
“আজ্ঞে, না কর্তা। হাই এক জিনিস আর ভেকুড়ি অন্য জিনিস। ভেচকুড়ি হল ভেচকুড়ি, আর হাই হল হাই। জলের মতো সহজ ব্যাপার।”
বীরেনবাবু লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, “বুঝলে তো! ভেচকুড়ি হল ভেকুড়ি, আর হাই হল হাই। তা তুমি যখন ভেচকুড়িটা পেরে উঠলে না, তখন বরং একটা হাই তুলেই দেখাও।”
লোকটা ভারী দুঃখের সঙ্গে বলল, “কর্তা, হাই কি আমার বাপের চাকর যে, ডাকলেই এসে হাজির হবে? নাঃ, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন বগলা হাইতের মুখ দেখেছিলুম, তখনই বুঝেছিলুম দিনটা আজ খারাপই যাবে।”
বীরেনবাবু অবাক হয়ে বললেন, “বগলা হাইত! সে আবার কে?”
“তাকে আর চিনে আপনার দরকার নেই বাবুমশাই। শুধু খেয়াল রাখবেন, প্রাতঃকালে ঘুম ভেঙে যেন বগলা হাইতের মুখ আপনাকে দেখতে না হয়। দিনমানে দেখুন, ঠিক আছে, রাতবিরেতে দেখুন, তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রাতঃকালে দেখেছেন কী হয়ে গেল।”
বীরেনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, “ওরে বাপু, অত সাঁটে বললে কি কিছু বোঝা যায়? কে বগলা হাইত, কী তার বৃত্তান্ত, প্রাতঃকালে তার মুখ দেখলে কী হয়, সব খোলসা করে বলবে তো?”
“প্রাতঃকালে তার মুখ দেখলে কী হয় তা এই আমাকে দেখেই কি অনুমান হচ্ছে না কর্তা? কাল সন্ধেবেলা মদন প্রামাণিকের বাড়িতে সত্যনারায়ণের কাটা ফলের পেসাদ আর একটি সিন্নি খেয়েছিলুম। তারপর চার পো রাত গিয়েছে, এত বেলা অবধি দানাপানি জোটেনি মশাই। এর পরও কি প্রাতঃকালে বগলা হাইতের মুখ দেখলে কী হয় তা বলার দরকার আছে?”
বীরেনবাবু তেরিয়া হয়ে বলেন, “তা এ বাড়িতে কি খ্যাটনের আশায় এসে জুটেছ নাকি?”
“না মশাই, না। আপনার মতো হাড়কেনের বাড়িতে যে এক ঘটি জলও জোটার আশা নেই, তা সবাই জানে। খালি পেটে গাছতলায় বসে একটু জিরেন নিচ্ছিলাম, অমনি এসে আপনি নানা বায়নাক্কা শুরু করলেন। ভেকুড়ি দেখাও, হাই তুলে দেখাও, বগলা হাইতের খতেন দাখিল করো। তা মশাই, খালি পেটে কি ওসব হয়?”
বীরেনবাবু একটু মিইয়ে গিয়ে বললেন, “আমি কেন একথা তোমাকে কে বলল বলো তো বাপু? খগেন তপাদার নয় তো? ওর কথা মোটেই বিশ্বাস কোরো না বাপু। ব্যাপারটা হয়েছিল কী, আমার ছোট মেয়ের বিয়ের সময় খগেন লুচি-মাংস, পোলাও কালিয়া ঠেসে খাওয়ার পর দশ হাত পায়েস সাঁটায়। তারপর আরও পায়েস চাইছিল বলে আমি ওর ভালর জন্যই বলি, খগেন, আর পায়েস খেয়ো না, পেটে সইবে না। এই তো ক’দিন হল রক্ত আমাশায় ভুগে উঠলে! এই কথাতেই খগেন রেগেমেগে উঠে গেল, আর চারদিকে রটাতে লাগল আমি নাকি হাড়কেপ্পন।”
লোকটা মাথা চুলকে বলল, “কর্তাবাবু, ভুল শুনছি কি না জানি। আপনি তো বললেন হাতা, কিন্তু খগেন তপাদারদাদা তো বলে বেড়াচ্ছেন সেটা নাকি একটা চায়ের চামচ ছিল।”
“আরে না, না। হাতাটা একটু ছোট ছিল ঠিকই। তা বলে অত ছোট নয়। তা বাপু, তোমার মুখোনা তো দেখছি শুকিয়ে গিয়েছে! ওরে বটু, আহাম্মকের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? লোকটাকে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণের দাওয়ায় বসিয়ে একটু জলটল দে। একধামা মুড়ি বাতাসা, কয়েকটা শশা, যা যা শিগগির। অতিথি হল নারায়ণ!”
বীরেনবাবু শশব্যস্তে ভিতরবাড়িতে চলে যাওয়ার পর লোকটা নাক কুঁচকে বলল, “মুড়ি, বাতাসা আর শশা! ছ্যাঃ, কোনও ভদ্দরলোকে খেতে পারে ওসব? একধামা মুড়ি শেষ করতে তো বেলা গড়িয়ে যাবে।”
বটু বলল, “হু, তবু তো বাপু তোমার বরাত ভাল যে, অন্তত মুড়ি-শশার হুকুম হয়েছে। আর ধামা নিয়ে ভেবো না, এ বাড়ির ধামার সাইজ হল নারকোলের মালার মতো।”
“তা হলে তোমরা সব বেঁচেবর্তে আছ কী করে? চেহারাও বেশ নধরই মনে হচ্ছে।”
“ওরে বাপু, বীরেনবাবু পাষণ্ড বলে তো আর গিন্নিমাও পাষণ্ড নন। তার একটু মায়াদয়া আছে। আর বলতে নেই, আমরাও তো আর লক্ষ্মীছেলে নই রে বাপু, হাতযশে কিছু কম যাই না। কাটা মুলোটা, নাড়ুটা-মোয়াটা, দুধটা-ক্ষীরটা সবই নিয়ম করে হাপিস করি, নইলে উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে কি শরীর টিকত? ওই যে দক্ষিণের দাওয়া, গিয়ে চুপ করে বসে থাকো, তোমার মুড়ি শশার ব্যবস্থা দেখছি।”
২. আশ্বিন মাসে পুজোর পর
আশ্বিন মাসে পুজোর পর থেকেই নিমাদের মনে হতে লেগেছে যে, সে বুড়ো হচ্ছে। বয়সের হিসেব সে জানে না। কিন্তু বুড়ো যে হচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা বলে কি নিমচাঁদ এক প্যাকেট তাস একসঙ্গে ধরে দু’হাতে এক টানে ছিঁড়ে ফেলতে পারে না? পারে। দু’মন লোহার বারবেল কি এক ঝটকায় মাথার উপর তুলে ফেলতে পারে না? পারে। হাতের কানা দিয়ে এখনও কি সে নারকোল ফাটাতে পারে না? খুব পারে। মোটা নাইলনের দড়ি দু’হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে কি তার খুব কষ্ট হচ্ছে আজকাল? হচ্ছে বোধহয়, তবে ছিঁড়েও ফেলছে। আর রাজবাড়ির বড় কামানটা যে সেদিন বাগানের উত্তর দিক থেকে তুলে নিয়ে দক্ষিণ দিকে বসাতে হল, তাতে কি গা ঘামাতে হল তাকে? তেমন কিছু নয়।
তবু নিমাদের ক’দিন হল মনে হচ্ছে, বুড়ো হতে আর বিশেষ বাকি নেই। তার বুড়ো বয়স এসে দরজায় কড়া নাড়ল বলে!
সকালে কথাটা তার ছেলে ভীমচাঁদকেও বলল। ভীমচাঁদের বয়স মোটে বারো।
“বুঝলি রে ভেমো, আমি বোধহয় শেষ অবধি বুড়োই হয়ে গেলুম।”
ভীমচাঁদ জানলার কাছে বসেইসকুলের পড়া করছিল। ভারী অবাক হয়ে বলল, “তাই নাকি বাবা? তা হলে তো বড় মুশকিল হল?”
“কেন রে? মুশকিলটা কীসের? বয়স হলে মানুষ তো বুড়োই হয়।”
“কিন্তু নোয়াপাড়ার ছেলেরা যে তা হলে দলবেঁধে আমাকে পেটাবে?”
“তোকে পেটাবে! কেন, তুই কী করেছিস?”
“ওদের ক্লাবের সেক্রেটারি গোবিন্দ নতুন সাইকেল কিনে খুব কায়দা করে চালাচ্ছিল দেখে আমি হিংসের চোটে ঢিল মেরে গোবিন্দর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলুম যে! তখনই ওরা শাসিয়ে রেখেছে, তোর বাবার গায়ে তো আর চিরকাল জোর থাকবে না। যখন বুড়ো হবে, তখন দলবেঁধে তোকে পেটাব। দেখব, তোর বাবা কী করতে পারে?”
নিমচাঁদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তাহলে হাটুরে মার খাওয়ার জন্য তৈরি হ’ রে ভেমো। আমি সত্যিই বুড়ো হতে চললুম।”
“তোমার গায়ে কি আর একটুও জোর নেই বাবা?”
দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে নিমচাঁদ বলল, “না রে বাবা, জোর বল খুবই কমে যাচ্ছে। পরশু দিন শিবাইচণ্ডীতলা দিয়ে আসছিলুম, দেখলুম, আমাদের দাগি ষাঁড় ভোলা বটতলায় শুয়ে আছে। শিং ধরে কতবার ভোলার ঘাড় মুচড়ে দিয়েছি। তা ভাবলুম, আজও একটু মুচড়ে দিই। ঠেলাঠেলি করে তাকে তোলার পর ভোলা রেগেমেগে তেড়ে এল বটে, আর আমিও তার ঘাড় মুচড়ে দিলুম ঠিকই। কিন্তু নাঃ, ঠিক আগের মতো হল না। ভোলাও যেন সেটা টের পেয়ে মিচিক মিচিক হাসছিল।”
ভীমচঁদ খুব চিন্তিতভাবে বলল, “তা হলে তো বড় মুশকিল হল বাবা। ইসকুলের নগেনমাস্টারমশাই পড়া না করলে সবাইকেই খুব বেত মারেন, শুধু আমাকে ছাড়া। তুমি বুড়ো হয়েছ জানলে যে নগেনস্যার আমাকে মেরে পাট পাট করবেন।”
“তা হলে বরং লেখাপড়াতেই মন দে রে ভেমো। আর আমার ভরসায় বসে থাকিস না।”
ভীমচাঁদ কাদো কাঁদো হয়ে বলল, “কিন্তু বাবা, তা হলে যে এখন থেকে লবঙ্গলতা স্টোর্সের বিশে আর বিনা পয়সায় লজেন্স বা চকোলেট দেবে না! গদাইয়ের দোকান থেকে খাতা-পেনসিল বিনা পয়সায় তুলে আনাও চলবে না। ইসকুলে বন্ধুরা পালা করে টিফিনের ভাগ দেবে না।”
নিমাদ দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “হাতি কাদায় পড়লে কী হয় জানিস তো? না না, এখন থেকে তোরা সব ন্যায্য পয়সা দিয়েই জিনিসপত্তর কিনিস বাপ! আর গাজোয়ারি করে তুলে আনিস না।”
“ইস, তুমি আর কটা দিন পরে বুড়ো হলে আমি ততদিনে ক্লাস পরীক্ষাটাও পাশ করে যেতাম!”
“উঁহু, আর ওসব নয়। তিন-চার বিষয়ে ফেল মেরেও নতুন ক্লাসে ওঠা আর চলবে না। এখন থেকে সব বিষয়ে পাশ নম্বর পেতে হবে।”
নিমাদের বউ খবর পেয়ে হুলস্থূল হয়ে এসে ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়ল, “ওগো, এ কী সব্বোনেশে কথা শুনছি! তুমি নাকি বুড়ো হয়েছ?”
“আহা, তাতে চেঁচামেচির কী আছে? বয়স হলে বয়সের নিয়মেই বার্ধক্য আসে। হুঁ হুঁ বাবা, এ হল অঙ্কের হিসেব।”
“কিন্তু আমার কী দুর্দশা হবে ভেবে দেখেছ? পাশের হাজরাবাড়ির কুঁদুলি বউটা পাড়ার সকলের সঙ্গে নেচে নেচে ঝগড়া করে বটে, কিন্তু আমি কিছু বললে বা দু’কথা শোনালে চুপ করে থাকে, রা-টি কাড়ে না। এখন তো সে আমারও বিষ ঝেড়ে দেবে রোজ। গলার হার ভেঙে এই যে বালা গড়িয়েছি, স্যাকরা কথাটি কয়নি। কিন্তু এখন সে কি মজুরি আদায় না করে ছাড়বে? আমি পাড়ায় বেরোলে লোকে কত খাতির করে রাস্তা ছেড়ে দেয়, রিকশাওয়ালা বিনা ভাড়ায় খেপ দিয়ে দেয়। আর কি ওসব হবে? এখন যে দুধওয়ালাও দুধের দাম চাইবে গো।”
নিমাদ গম্ভীর হয়ে বলল, “ওসব ভুলে যাও গিন্নি। এখন থেকে লোকের সঙ্গে ভাবসাব রেখে চলো। মনে রেখো, গয়না গড়ালে মজুরি দিতে হবে, রিকশায় উঠলে ভাড়া মেটাতে হবে, দুধ খেলে দাম দিতে হবে। আর এটাও যেন খেয়াল থাকে, সেইদিন আর নাই রে নাতি, থাবা থাবা চিনি খাতি।”
না, সেই দিন আর নেই-ই বটে। নিমচাঁদ যে বুড়ো হল! খুব চিন্তিত মুখে পাড়ায় বেরিয়ে খুব ধীরে ধীরে টুকটুক করে হাঁটছিল নিমচাঁদ। বয়স হয়েছে, এখন হুড়দৌড় করে হাঁটাচলা ঠিক হবে না। বুড়ো বয়সের নিয়মকানুন সব মেনে চলতে হবে। অধিক উত্তেজনা বারণ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ, হাঁকডাক করা নিষেধ।
সে রাস্তায় বেরোলে চারদিকটা ভারী শুনশান হয়ে যায়, লোকজন সিঁটিয়ে থাকে, বাচ্চারাও কাঁদে না, লোকের কথাবার্তা, চায়ের দোকানে আড্ডা সবই যেন থেমে থাকে। আজও সেরকম হচ্ছে।
তবে এ আর ক’দিন? এরপর একদিন রাস্তায় বেরোলে তাকে দেখে আশপাশের লোকেরা টিটকিরি দেবে, বক দেখাবে, ছেলেপুলেরা পিছনে লাগবে, কেউ আর ফিসফিস করে একে অন্যকে বলবে না, “ওই দ্যাখ, নিমেপালোয়ান যাচ্ছে।’
রাস্তার ধারে একটা নধর ঝুপসি সজনেগাছ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল নিমচাঁদ। নিজের গায়ের জোর-বল নিয়ে আজকাল প্রায়ই তার খুব সংশয় হচ্ছে। তার ঘোর সন্দেহ, আগের মতো ক্ষমতা তার আর নেই। দোনোমনো করে সে গুটি গুটি সজনেগাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে তার দু’খানা মজবুত হাতে গাছটাকে সাপটে ধরে ‘হেঁইও’ বলে একটা হ্যাঁচকা চাড় দিতেই গাছটা কেঁপে উঠে যেন মানুষের গলাতেই চাপা স্বরে বলে উঠল, “বাপ রে! তবে গাছটা ওপড়াল না। নিমাদ আর-একবার দম নিয়ে ফের গাছটাকে সাপটে ধরে চাড় দিতেই গাছটা যেন একটা মর্মর ধ্বনি তুলে বলে উঠল, “হচ্ছেটা কী?’ নিমাদ আর-একবার গভীরভাবে শ্বাস টেনে গাছটাকে শক্ত করে ধরে চাড় মারতেই ঝুম্বুস করে শেকড়বাকড় আর মাটির চাঙড় সমেত গাছটা বিঘতখানেক উপরে উঠে পড়ল। নিমচাঁদ একটা স্বস্তির খাস ছেড়ে গাছটাকে আবার জায়গামতো বসাতেই উপর থেকে হুড়মুড় করে ডালপালা সমেত একটা লোক, “ভূমিকম্প হচ্ছে! ভূমিকম্প হচ্ছে।” বলে চেঁচাতে চেঁচাতে মাটিতে চিতপাত হয়ে পড়ে গেল।
নিমাদ ভারী অপ্রস্তুত! তাড়াতাড়ি লোকটাকে তুলে দাঁড় করিয়ে ধুলোটুলো ঝেড়ে বলল, “অঘোরখুড়ো যে!”
অঘোরখুড়ো কঁকালের ব্যথায় মুখ বিকৃত করে বললেন, “ভূমিকম্প হচ্ছে যে! টের পাসনি?”
নিমাদ আমতা আমতা করে বলল, “ভূমিকম্প হচ্ছিল নাকি?”
“তোর কি ভীমরতি হল যে, এত বড় ভূমিকম্পটা টের পেলি না! একটা ব্লাডপ্রেশারের ওষুধ তৈরি করব বলে সজনে ফুলের সন্ধানে গাছে উঠেছি কী, অমনি সে কী কাঁপুনি আর দুলুনি রে বাবা! ওঃ, মাজাটা বুঝি ভেঙেই গিয়েছে রে, ডান হাতের কনুইটাও যেন অসাড়। বুড়ো বয়সে হাড় ভাঙলে কি আর জোড়া লাগবে রে বাপ!”
নিমাদের ভারী মনস্তাপ হল। গাছের গোড়ায় ছেড়ে রাখা হাওয়াই চটিজোড়া সে দেখেও তেমন খেয়াল করেনি। বুড়ো বয়সের চিন্তায় ভারী মনমরা হয়েছিল তো! লজ্জিত মুখে সে বলল, “চলুন, আমি বরং কাঁধে করে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।”
“দিবি? তাই দে বাবা! হাঁটাচলা ক’দিনের জন্য বন্ধ হল কে জানে?”
অঘোরখুড়োকে কাঁধে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিমচাঁদ জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা খুড়োমশাই, আপনি তো মস্ত কোবরেজ! মানুষের বুড়ো বয়সটা ঠিক কবে থেকে শুরু হয় বলুন তো?”
“ও বাবা, সে বলা খুব শক্ত। কেউ কুড়িতেই বুড়োটে মেরে যেতে থাকে, আবার কেউ নব্বইতেও বুড়ো হতে চায় না। ওর কোনও নিয়ম নেই যে! কেন রে, তোর হঠাৎ বুড়ো বয়সের চিন্তা কেন?”
“না, এই জেনে রাখা ভাল কিনা! তা বুড়ো হওয়ার কি কোনও নিয়ম নেই খুড়ো?”
“তা আছে বই কী, তবে সে বড় জটিল জিনিস, তুই বুঝবি না। এই যে আমি, এই আমাকেই দ্যাখ দেখি, চুরাশি বছর বয়সেও আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, গাছগাছালিতে উঠে পড়ছি, দাঁতে চিবিয়ে মাংসের হাড় গুঁড়ো করে ফেলছি।”
“তা বটে। তবে বুড়ো হওয়ার একটা নিয়মও তো আছে। ধরুন, বুড়ো বয়সেও কেউ যদি বুড়ো হতে না চায়, তা হলে কি সেটা ভাল দেখায় খুড়ো? লোকে নিন্দেমন্দও তো করতে পারে? বুড়োদের মধ্যে একটু বুড়োমি না থাকলে কি মানায়?”
“দুর আহাম্মক! তোর মাথায় বুড়ো বয়সের পোকা ঢুকেছে দেখছি। বলি, সত্যিই কি তোর ভীমরতি হল?”
“তা না হবে কেন বলুন? মা ষষ্ঠীর কৃপায় বয়স তো কম হল না! বেশ বুড়োই তো হয়েছি।”
“বটে! তা বুড়ো যে হলি টের পেলি কীসে?”
“আজ্ঞে, গায়ের জোর-বল কমে যাচ্ছে, সেই আগের মতো চটপটে হাত-পা নেই। তারপর ধরুন ক্ষুধামান্দ্যও হতে লেগেছে। দিনমানে এককাঠা চালের ভাত পথ্য ছিল, জামবাটি ভরতি ডাল, তিনপো মাছ, রাতে আশিখানা রুটি, সঙ্গে সেরটাক মাংস। তা এখনও খোরাক কমাইনি বটে, কিন্তু খেয়ে যেন আইঢাই হচ্ছে। তারপর ধরুন, চোখেও কি আর আগের মতো নজর আছে? ওই যে দুরে নারকেল গাছের ডগায় গাছের সঙ্গে গামছা দিয়ে কোমর জড়িয়ে লোকটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ও যে হরেন তা কি আর সত্যিই ঠাহর করতে পারছি? অনুমান করছি ওটা হরেনই হবে। তারপর ধরুন, আপনাদের দক্ষিণের দাওয়ায় যে একটা ন্যাড়ামাথাওলা লম্বাপানা লোক বসে মুড়ি আর শশা খাচ্ছে, তাও কি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! আন্দাজে বলা! তারপর ধরুন, ওই যে গোচারণ মাঠের ওধারে বটতলায় নামাবলি গায়ে, চোখে চশমা এঁটে একটা লোক হাটুরেদের হস্তরেখা আর কুষ্ঠি বিচার করছে। ও যে আসলে কানু সেটা জানি বলেই বলতে পারছি।”
অঘোরখুড়ো আঁতকে উঠে বললেন, “কানু! কানু চশমা পেল কোথায়? অ্যাঁ! এ নিশ্চয়ই আমার চশমা! ওরে আমাকে নামা! নামা! এক্ষুনি ছুটে গিয়ে পাজিটাকে বমাল ধরতে হবে।”
“উত্তেজিত হবেন না খুড়ো! এই বয়সে উত্তেজনা ভাল নয়। কত চশমা যাবে, কত চশমা ফের আসবেও। কিন্তু উত্তেজনার বশে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে তাকে কি আর হাতে-পায়ে ধরেও ফেরাতে পারবেন?”
অঘোরখুড়ো খিঁচিয়ে উঠে বললেন, “আমার প্রাণবায়ু নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। প্রাণবায়ু তো বিনি পয়সার জিনিস, কিন্তু চশমার যে অনেক দাম!”
“কানুও তাই বলছিল বটে!”
“কী বলছিল?”
“চশমাটা পরলে নাকি ও ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে পায়।”
“বলিস কী সব্বোনেশে কথা? ওই চশমা পরে আমি বুড়ো হলুম, কখনও তো ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে পাইনি।”
“কিন্তু কানু পায়। নইলে এত লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ গড়গড় করে বলে দিচ্ছে কী করে? আর সব ঠিকঠাক মিলেও তো যাচ্ছে।”
“কীরকম?”
“এই তো দিন সাতেক আগে নগেন বৈরাগীকে বলল, “মনে হচ্ছে তোমার কোমরে দড়ি পড়বে হে।’ শুনে ইস্তক নগেন তো গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে মরে। শেষে দারোগাবাবুর কাছে গিয়ে কান্নাকাটিও করে এল। দারোগাবাবু অভয় দিলেন, “ভয় নেই, তোকে গ্রেফতার করলেও কোমরে দড়ি পরাব না। তারপর কী হল জানেন? নগেন বৈরাগী জল তুলতে গিয়ে পা হড়কে কুয়োয় পড়ে গেল। তারপর সেই কোমরে দড়ি বেঁধেই কুয়ো থেকে তুলতে হল তাকে। তারপর মহেশ প্রামাণিকের কথাই ধরুন। ক’দিন আগে মহেশ প্রামাণিককে বলল, “যার নাম ‘ন’ দিয়ে শুরু তেমন জিনিস থেকে সাবধান। কী মুশকিল বলুন তো! মহেশের বাপের নাম নবীন, মা নগেন্দ্ৰবালা, বউ নলিনী, ভাই নরেশ, ছেলে নবকুমার, মেয়ে নীপবালা। মহেশ এখন যায় কোথায়? ভয় খেয়ে সে তার বড় শ্যালকের বাড়িতে গিয়ে ক’দিনের জন্য ঘাপটি মেরে রইল। তা একদিন বারান্দায় বসে পাকা কাঁঠালের ফলার সারছে, হঠাৎ বাড়ির কেলে গোরুটা ধেয়ে এসে মহেশকে গুঁতিয়ে সাত হাত দূরে ছিটকে ফেলে কাঁঠাল খেয়ে গেল। মাজা ভেঙে মহেশ সাতদিন শয্যাশায়ী। পরে জানা গেল সেই গোরুর নাম নাকি ‘নিশিপদ্ম। বুঝুন কাণ্ড!”
“তাই তো রে! তুই যে ভাবিয়ে তুললি! আমার চশমার যে এত গুণ তা তো আমিই এতকাল টের পাইনি!”
“আজ্ঞে, স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাত্রবিশেষে ফল। সকলের কি সব কিছু সয় খুড়ো? নীলার আংটি যেমন, কারও হাতে গেলে পৌষমাস, কারও হাতে সর্বনাশ।”
অঘোরখুড়ো খুব চিন্তিত গলায় বললেন, “কথাটা বোধহয় খুব একটা মন্দ বলিসনি। চশমাটার মধ্যে কিছু অশৈলী ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে। ওটা চোখে দিলে মাঝে মাঝে কিম্ভুত সব জিনিস দেখা যায় বটে।”
“কীরকম খুড়ো?”
“আগে ভাবতুম বয়সের দোষে ভুলভাল দেখছি। কিন্তু এখন তলিয়ে ভেবে দেখলুম, সেটা চশমার গুণেও হতে পারে।”
“তা কী দেখতে পান খুড়ো? ভূতটুত নাকি?”
“ভূতও হতে পারে। তবে মাঝে মাঝে চশমাটা খুব আবছা হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ আবছায়া কেটে গিয়ে হয়তো দেখলুম, ঘরের মধ্যে একটা খুব ঢ্যাঙা লোক উবু হয়ে কী যেন খুঁজছে। সাড়া দিতেই ফুস করে কোথায় যেন সটকে পড়ল। তারপর ধর, আমার জানলার ওধারে কদমতলার মাঠ। জ্যোৎস্না রাতে মাঝে মাঝে দেখতে পাই কয়েকটা খুব ঢ্যাঙা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের গায়ের রং যেন কেমন সবজে সবজে।”
“তা হলে ও চশমা আপনি কানুকেই দান করে দিন খুড়ো। ও আপনার সইবে না।”
“দান করে দেব কী রে? ও যে খাঁটি সোনার চশমা! বটুকবুডোর বাতব্যাধির চিকিৎসা করেছিলুম। বটুক খুশি হয়ে মরার আগে চশমাজোড়া আমাকে দিয়ে যায়। আমার চোখেও দিব্যি ফিট হয়ে গেল। দিনের বেলা দিব্যি সব স্পষ্ট দেখা যায়। রাতের দিকেই যা একটু গন্ডগোল হয়।”
“চশমা ছাড়াই যখন আপনি সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, তখন ওই অলক্ষুনে চশমা চোখে দেওয়ার দরকার কী আপনার?”
“তা বটে, তবে কী জানিস, চশমা পরলে একটা ভারিক্কি ভাব আসে। লোকে একটু মান্যিগন্যি করে। চশমা একটা কেতার জিনিস তো! চোখে দিলে বাহারও হয় খুব!”
“যদি অভয় দেন তো একটা কথা কব?”
“কী কথা?”
“বলছিলুম কী, এখন কি আর আমাদের সেই বয়স আছে? এই জাগতিক তুচ্ছ জিনিসপত্রের উপর লোভ করা কি আমাদের শোভা পায়? আমাদের এই বুড়ো বয়সে তো জাগতিক বস্তু ছেড়ে পরমার্থেরই খোঁজ করা উচিত? কী বলেন?”
অঘোরখুড়ো খিঁচিয়ে উঠে বললেন, “তুই বুড়ো হচ্ছিস তো যত খুশি হ। কিন্তু তোর দলে আমাকে ভেড়াচ্ছিস কেন? আমি মোটেও বুড়ো হইনি।”
নিমচাঁদ ভারী অবাক হয়ে বলল, “হননি? কিন্তু বয়সকালে বুড়ো হলে যে বড় সমস্যা হবে খুড়োমশাই!”
কথায় কথায় বাজারের কাছেপিঠে এসে পড়ায় লোকজন হাঁ করে দেখছিল তাঁদের। খগেন তপাদার বাজার সেরে ফিরছিল, দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, “বলি ও অঘোরখুড়ো, ভোটে জিতলেন, না ডবল সেঞ্চুরি করলেন?”
অঘোরখুড়ো খ্যাক করে উঠে বললেন, “তার মানে?”
“আজকাল তো দেখি ভোটে জিতলে, আর ডবল সেঞ্চুরি করলেই লোকে কাঁধে নিয়ে নাচানাচি করে। তা আপনার কোনটা?”
অঘোরখুড়ো ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “দ্যাখ খগেন, সব সময় রঙ্গ-রসিকতা ভাল নয়। কত বড় ভূমিকম্পটা হয়ে গেল দেখলি না? তার ধাক্কায় গাছ থেকে পড়ে মাজাটা ভেঙে দ’ হয়ে গেলুম, আর তুই রসিকতা করছিস?”
“তা ভূমিকম্প তো হয়েছিল এক বছর আগে, আপনার পড়তে এত সময় লাগল কেন বলুন তো? কত উঁচু গাছ যে, পড়তে এক বছর সময় লাগে?”
অঘোরখুড়ো খেপে গিয়ে বললেন, “তোরা কি নেশা করেছিস নাকি যে, এত বড় ভূমিকম্পটা টের পেলি না! মাত্র দশ মিনিট আগেই তো উপর্যুপরি ঝাঁকুনির চোটে আমি গাছ থেকে পড়লুম।”
বাজারের লোকজন মুখ তাকাতাকি করে বলতে লাগল, “না মশাই, ভূমিকম্প তো মোটেও হয়নি!”
খগেন তপাদার বলল, “ও ভূমিকম্প নয় খুড়ো, ও হল আপনার হৃৎকম্প।”
বিপদ বুঝে নিমচাঁদ ডবল গতিতে হাঁটা দিয়ে বলল, “সবার কথায় কান দেওয়ার দরকার কী আপনার বলুন তো খুড়োমশাই?”
অঘোরখুড়ো কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, “হারে, তুই না বুড়ো হয়েছিস? তোর নাকি হাতে-পায়ে আর আগের মতো জোর নেই! তা হলে এখন এই টাটুঘোড়ার মতো ছুটছিস কী করে?”
“ছুটছি নাকি?”
“আলবাত ছুটছিস!”
“ওইটেই বুড়ো বয়সের দোষ খুড়োমশাই, বয়সটা সব সময় খেয়াল থাকে না কিনা! ভীমরতিই হচ্ছে বোধহয়।”
“তোকে যে ভীমরতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছে তা এখন আমি দিব্যি বুঝতে পারছি। ভেবে দেখলুম, যখন সবাই একই কথা বলছে, তখন একটু আগে যেটা হয়ে গেল সেটা মোটেও ভূমিকম্প নয়।”
নিমচাঁদ ভারী অবাক হয়ে বলল, “নয়! তা হলে কী হল বলুন তো?”
“কেউ গাছটা ঝাঁকিয়ে আমাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল।”
“এ তো ভারী অন্যায়।”
“তা তো বটেই। তা ভাবছি, অত বড় মজবুত একটা গাছকে ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ানো তো যার-তার কম্মো নয়। মস্ত পালোয়ানের পক্ষেই সম্ভব। কী বলিস?”
কাঁচুমাচু হয়ে নিমচাঁদ বলল, “আজ্ঞে, ঠিক ইচ্ছে ছিল না খুড়োমশাই। কী করে যেন হয়ে গেল! বুড়ো বয়সের দোষ বলেই ধরে নিন।”
“বুড়ো বয়সের দোষ হবে কেন রে? এ সব নষ্টামি-দুষ্টামি কি বুড়ো মানুষের কাজ? এ তো করে বাচ্চা বখাটে ছেলেরা! তোর বয়স মোটেও বাড়ছে না, বরং কমছে। তুই আসলে ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছিস।”
চিন্তিত হয়ে নিমচাঁদ বলল, “এ তো বড় ধন্দে ফেলে দিলেন খুড়ো! বয়স বাড়ছে না কমছে, সেটাই যে এখন ঠিক ঠাহর পাচ্ছি না।
৩. যারা রটিয়ে বেড়ায়
যারা রটিয়ে বেড়ায় যে, হরেন রোজ নারকোল গাছে উঠে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়, তারা মোটেও সত্যি কথা বলে না। তবে হ্যাঁ, এ কথাও ঠিক যে, নারকোল গাছের মাথাটা ভারী ভাল জায়গা। সেখানে উঠলে গায়ে মিঠে মোলায়েম হাওয়া এসে লাগে! মিষ্টি রোদ আর নারকোল পাতার ঝিরিঝিরি ছায়া, আর সেইসঙ্গে গাছের মৃদুমন্দ দোলে যদি ঘুম এসেই যায়, তা হলে কাউকে দোষও দেওয়া যায় না। আর তাই হরেন গাছের সঙ্গে কোমরটা গামছা দিয়ে কষে বেঁধে নিয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নেয় বটে। তবে আসলে সে গাছের ডগায় বসে এই গঞ্জশহরের চারদিকটা নজরে রাখে বই তো নয়! নজরদারি করার মতো কিছু ঘটনাও আজকাল ঘটতে লেগেছে। আর সেইসব ঘটনা গাছের ডগা থেকে যতটা দেখা যায় মাটিতে দাঁড়িয়ে তার সিকিভাগও দেখার উপায় নেই।
আজও ঘুম ভাঙার পর গোটা কয়েক হাই তুলে আর আড়মোড়া ভেঙে চারদিকটা দেখছিল হরেন। ওই তো চিমসে চেহারার মিতব্যয়ী নিশাপতিবাবু দেড়শো গ্রাম চাল, দুটি আলু, একচিমটি ডাল আর দুটি পুঁটিমাছ কিনতে বাজারে চলেছেন। থানার হোঁতকা সেপাই লাটু হাজারি চৌপথির বটতলায় ইটের উপর বসে উপেন নাপিতের কাছে বিনা পয়সায় আরামসে খেউরি হচ্ছে। নধরকান্তি চিন্তামণি সমাদ্দারের মিষ্টি খাওয়া বারণ বলে, ওই যে বলরাম ঘোষের মিঠাইয়ের দোকানের পিছনে দাঁড়িয়ে শালপাতায় মুখ আড়াল করে টপাটপ জিলিপি খাচ্ছে। এসব রোজকার চেনা দৃশ্য। না, নতুন কিছু দেখা যাচ্ছে না।
কোমর থেকে গামছাটা খুলে মুখের ঘাম মুছে গাছ থেকে নামবার তোড়জোড় করছিল হরেন। এমন সময় তার নজর গিয়ে পড়ল দেওয়াল-ঘেঁষা জায়গাটায়। ওখানটায় মেলা গাছপালা আর ঝোঁপঝাড়ের জঙ্গল। কামিনী ঝোঁপের লাগোয়া একখানা ফাঁদালো গন্ধরাজ লেবুর ছড়ানো গাছ। নীচেটায় ভারী অন্ধকার। সেইখানে ঝোঁপঝাড়ের আড়াল থেকে কার যেন দু’খানা ঠ্যাং একটুখানি বেরিয়ে আছে। পায়ের পাতা দুটো উপর দিকে ওলটানো, তার মানে লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে।
দৃশ্যটা দেখে হাত-পা একটু ঝিমঝিম করে উঠল হরেনের, সর্বনাশ! কার আবার কী হল রে বাবা! তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে গাছের ঘষটানিতে বুকের নুনছাল উঠে গেল হরেনের। নেমেই হাঁফাতে হাঁফাতে সে লেবুতলায় হাজির হয়ে যাকে দেখতে পেল, সে মোটেও চেনা মানুষ নয়। মাথা ন্যাড়া, তাতে আবার টিকিও রয়েছে, পরনে হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা জামা। কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপারটা হল, জামাটা উলটে আছে বলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, লোকটার কোমরের কষিতে একটা ঝকঝকে পিস্তল।
হরেনের চেঁচামেচিতে লহমায় লোক জড়ো হয়ে গেল।
বীরেনবাবু কাহিল গলায় বললেন, “কী সব্বোনেশে লোক! পিস্তল নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে! দেখে তো মনে হয়েছিল ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না!”
বটু গম্ভীর হয়ে বলল, “আমি তখনই বলেছিলাম কিনা কর্তাবাবু, ভেচকুড়ি-কাটা লোককে মোটেও বিশ্বাস নেই।”
বীরেনবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, “কিন্তু কাজটা কি তুই ভাল করলি বটু?”
“কোন কাজটা?”
“এই যে লোকটাকে খুন করে ফেললি? খুনটুন নিজের হাতে করা কি ভাল রে? বরং পুলিশকে জানালেই তো হত!”
বটু আকাশ থেকে পড়ে কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, “কী বলছেন কর্তাবাবু? জীবনে মশা-মাছিটা অবধি মারিনি, আর আমি অমন দশাশই লোককে খুন করতে যাব? দক্ষিণের দাওয়ায় বসিয়ে শশা আর মুড়ি খেতে দিয়ে আমি তো ঘানি থেকে সরষের তেল আনতে গিয়েছিলুম। ফিরেই চেঁচামেচি শুনে এসে দেখি এই কাণ্ড!”
বীরেনবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, “তা হলে একে মারল কে?”
একচন্দ্র নিবিষ্ট মনে হাঁটু গেড়ে বসে লোকটার নাড়ি দেখছিল। মাথা নেড়ে বলল, “না হে, মরেনি। তবে মাথায় আর ঘাড়ে চোট হয়েছে দেখছি। চোখে-মুখে জলের ঝাঁপটা দিলে জ্ঞান ফিরতে পারে।”
বিজয়বাবু বললেন, “দাঁড়াও বাপু, জ্ঞান ফেরার আগেই ওর অস্ত্রটা সরিয়ে নেওয়া দরকার। জ্ঞান ফেরার পর কোন মূর্তি ধরে তার ঠিক কী?” এই বলে তিনি গিয়ে লোকটার কোমর থেকে সাবধানে পিস্তলটা খুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললেন, “এ তো বেলজিয়ামে তৈরি অত্যাধুনিক জিনিস। এরকম একটা পেঁয়ো টিকিধারী লোক এটা পেল কোথায়?”
বীরেনবাবু বললেন, “হয়তো কুড়িয়ে টুড়িয়ে পেয়েছে।”
বিজয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, “এ জিনিস রাস্তায়-ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া শক্ত। লোকটা হয় ডাকাত, না হয় ছদ্মবেশী পুলিশ।”
ব্রজবিহারী সভয়ে বললেন, “ও বাবা! তা হলে জ্ঞান ফেরার আগেই ওর হাত-পা বেঁধে ফেলা হোক। সাবধানের মার নেই!”
বিজয়বাবু মৃদু হেসে বললেন, “তার দরকার নেই। মূর্ছা ভাঙলেও লোক চট করে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠার অবস্থায় থাকে না। তার উপর এর মাথায় আর ঘাড়ে চোট রয়েছে। বটু বরং গিয়ে বনবিহারী ডাক্তারকে ডেকে আনুক।”
চোখে-মুখে বেশ কিছুক্ষণ জলের ছিটে দেওয়ার পর লোকটা চোখ চাইল বটে। কিন্তু চোখের চাউনি ভ্যাবলা আর ফ্যালফ্যালে। যেন কিছুই বুঝতে বা চিনতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষণ টালুমালু করে চারদিকটা দেখার চেষ্টা করে হঠাৎ ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, “লোকটা কোথায় গেল? অ্যাঁ! লোকটা?”
সবাই মুখ তাকালাকি করে অবশেষে বিজয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কে হে, কার কথা জিজ্ঞেস করছ?”
“ওই যে সবুজ রঙের লোকটা!” সবুজ রঙের লোক শুনে একচন্দ্র মাথা নেড়ে বলল, “মাথায় চোট হলে অনেক সময় লোকে ভুলভাল বলে। সবুজ লোক কোথা থেকে আসবে? ওহে বাবু, সবুজ পোশাক পরা কাউকে দেখেছ নাকি?”
লোকটা জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে বলল, “একটু জল দেবেন? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।”
জল খেয়ে লোকটা যেন একটু ধাতস্থ হল। হাতে ভর দিয়ে উঠে বসবারও চেষ্টা করতে লাগল।
বীরেনবাবু বীরের গলাতেই বলে উঠলেন, “উঁহু, পালানোর চেষ্টাও কোরো না, পুলিশে খবর দিতে লোক গিয়েছে। এই এল বলে। পিস্তল নিয়ে দিনেদুপুরে লোকের বাড়িতে ডাকাতি করতে ঢোকা বের করছি তোমার।”
বটু আর হরেন গিয়ে ঘরে লোকটাকে বসানোর পর লোকটা মাথা নেড়ে বলল, “ডাকাত নই মশাই!”
“তবে তুমি কে?”
“বলা বারণ আছে।”
“ওসব চালাকি করে পার পাবে না হে। শক্ত পাল্লায় পড়েছ।” লোকটা জবাব দিল না। মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দুর্বল গলায় বলল, “আমার পিস্তলটা কি ফেরত দেবেন?”
বীরেনবাবু আঁতকে উঠে বললেন, “পিস্তল! পিস্তল ফেরত চাও? তুমি তো বিপজ্জনক লোক হে! পিস্তল নিয়ে নিজের মূর্তি ধরবে বুঝি?”
লোকটা ক্লান্ত গলায় বলল, “আমি খুব ভাল লোক নই বটে। কিন্তু আপনাদের কোনও ক্ষতি করতে আসিনি।”
বিজয়বাবু ঠান্ডা মাথার মানুষ। নরম গলায় বললেন, “তুমি কে তা না হয় না বললে। কিন্তু ঘটনাটা কীভাবে ঘটল, কে তোমাকে মারধর করল, সেটা তো বলতে পারো?”
“একজন সবুজ মানুষ।” হরেন বলে উঠল, “ও তো…।”
কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারল না, বিজয়বাবু একটা ধমক দিয়ে বললেন, “বেশি কথা না বলে দৌড়ে গিয়ে এক কাপ গরম দুধ নিয়ে আয় তো৷”
হরেন মিইয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।
বীরেনবাবু সখেদে বললেন, “চোর-ডাকাতকে গরম দুধ খাওয়ানোটা কি ঠিক হচ্ছে বিজয়দাদা? এরকম আপ্যায়ন হলে যে ঘনঘন তারা এসে এ বাড়িতে চড়াও হবে? ওদের সঙ্গে কুটুম্বিতা কি ভাল?”
বিজয়বাবু উত্তেজিত না হয়ে মৃদু হেসে বললেন, “দ্যাখো বীরেন, লোকটা চোর-জোচ্চোর কি না তা এখনও জানা যায়নি। লোকটা উন্ডেড, অসুস্থ। শুশ্রূষা দরকার। চোর-ডাকাত বলে মনে হচ্ছে না আমার।”
এ বাড়িতে বিজয়বাবুকে সবাই একটু খাতির করে। একসময় বড় কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। বিয়েটিয়ে করেননি। এখন এই বাড়িতে নিজের মতো একটা ল্যাবরেটরি করে গবেষণা নিয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা আর কাণ্ডজ্ঞান অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। ব্যক্তিত্বও সাংঘাতিক। চাপা স্বভাবের মানুষ বলে কেউ তাঁকে বড় একটা ঘটায় না।”
গরম দুধটুকু লোকটা এক চুমুকে শেষ করে বলল, “এবার আমাকে ছেড়ে দিন।”
বীরেনবাবু বললেন, “ছেড়ে দেব মানে? তুমি কে, কোন মতলবে এখানে উদয় হয়েছ, নামধাম, ইতিবৃত্তান্ত কী, এসব
জেনেই ছেড়ে দেব নাকি? পুলিশ আসুক, তারপর যা ব্যবস্থা হওয়ার হবে।”
বিজয়বাবু নরম গলাতেই বললেন, “উঠে দাঁড়াতে পারবে?”
“পারব।”
“তা হলে এই ভেজা মাটিতে বসে না থেকে ওই দাওয়ায় গিয়ে বসবে চলো।”
“আমি চোর-ডাকাত নই, আবার ভিখিরি-কাঙালও নই। এখানে একটা জরুরি কাজে এসেছিলাম।”
“কাজটা কী?”
“সবুজ মানুষ।”
“সবুজ মানুষ বলে কিছু নেই। ওটা আষাঢ়ে গল্প।”
“আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি ওই বারান্দাটায় বসে মুড়ি খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, এই ঝোঁপঝাড়ের ভিতর অন্ধকার থেকে একটা লম্বা, ঘন সবুজ রঙের মানুষ উঁকি দিচ্ছে। যা শুনেছিলুম, হুবহু সেইরকম।”
হঠাৎ বিজয়বাবুর চোখ দুটো যেন ধক করে জ্বলে উঠল। চাপা হিংস্র গলায় বললেন, “কী শুনেছিলে?”
“এখানে সবুজ রঙের মানুষ আছে।”
“এরকম অবাস্তব গল্প কে তোমাকে বলেছে? সবুজ মানুষ থাকলে আমরা দেখতুম না? আর তুমি কোমরে পিস্তল নিয়ে সবুজ মানুষ খুঁজতে এসে ভয়ংকর অন্যায় করেছ। যদি ভুল দেখে গুলি চালিয়ে দিতে তবে একজন নিরীহ মানুষ মারা পড়তে পারত?”
“গুলি চালানোর হুকুম নেই। আমি চালাইওনি গুলি।”
“তবে পিস্তল নিয়ে এসেছিলে কেন?”
“আত্মরক্ষার জন্য।”
“আত্মরক্ষার নামে দুনিয়ায় অনেক খুনখারাপি হয়ে থাকে। ওই অজুহাতটা আমি বিশ্বাস করছি না। ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে আমি মেনে নিচ্ছি যে, তুমি একটা সবুজ রঙের মানুষ দেখেছ। কিন্তু সে কি তোমার কোনও ক্ষতি করেছে?” ৪০
“ক্ষতি করেছে কি না সেটা তো নিজের চোখেই দেখছেন। আমার মৃত্যুও হতে পারত।”
“বিনা কারণেই কি লোকটা তোমাকে অ্যাটাক করেছিল?” লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “আমি সবুজমানুষ দেখে মুড়ির বাটি ফেলে ছুটে আসছিলাম। লোকটার কাছে পৌঁছোনোর আগেই একটা লম্বা হাত এসে আমার মাথায় হাতুড়ির মতো একটা ঘুসি মারল। আমি অজ্ঞান হওয়ার আগে দেখতে পেলাম, সবুজ লোকটা দৌড়ে গিয়ে এক লাফে ওই প্রায় দশ ফুট উঁচু দেওয়ালটা পার হয়ে গেল।”
একচন্দ্র বলল, “ওরে, হাইজাম্পের বিশ্বরেকর্ড যেন কত ফুট, একটু খোঁজ নিয়ে দ্যাখ তো!”
বিজয়বাবু অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, “তোমার মাথার ঠিক নেই। তুমি ভুল দেখেছ এবং ভুল খবর পেয়ে এসেছ। এখন যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও।”
“বলুন?”
“এই পিস্তলের লাইসেন্স কি তোমার আছে?”
“আছে।”
“না থাকলে কিন্তু বিপদে পড়বে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, তুমি কি ছদ্মবেশ পরে এসেছ? তোমার পোশাকের সঙ্গে কথাবার্তা মিলছে না।”
“হ্যাঁ, ছদ্মবেশ।”
“ছদ্মবেশ ধরার কারণ কী?”
“হুকুম হয়েছিল গাঁয়ের মানুষ সেজে আসতে।”
“কারা তোমাকে পাঠিয়েছে সেটা তুমি বলতে চাও না?”
“না।”
“আমাদের কাছে বলতে না চাইলেও পুলিশ কিন্তু তোমার কাছ থেকে কথা বের করবে।”
“আমি আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেটলি কথা বলতে চাই।”
বীরেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠে বললেন, “খবরদার না। ওসব প্রাইভেট কথা বলার নাম করে নির্জন, নিরিবিলিতে গিয়ে একটা হামলা করে পালানোর মতলব তো? সে হবে না।”
বিজয়বাবু শান্তভাবেই বললেন, “না রে, হামলা করার মতো অবস্থা এর এখনও নয়। তা ছাড়া আমার কাছে ওর পিস্তলটা তো আছেই। তোরা বরং আমার ঘরের বাইরে পাহারায় থাকিস। এসো হে, তোমার প্রাইভেট কথাই শোনা যাক।”
বিজয়বাবু লোকটাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাড়ির লোকেরা বাইরে পাহারায় রইল।
দরজা বন্ধ করে লোকটাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে বিজয়বাবু মুখোমুখি বসে বললেন, “এবার বলো কী বলতে চাও?”
লোকটা বলল, “আমাকে দয়া করে পুলিশে দেবেন না। আমি তেমন কোনও অপরাধ করিনি।”
“ট্রেসপাসিং এবং ছদ্মবেশে ঘোরা কি অপরাধ নয়?”
“প্রথম কথা আমি ট্রেসপাস করিনি। বাড়ির কর্তা বীরেনবাবুই আমাকে ভিতরে ঢুকতে দিয়েছেন। আর ছদ্মবেশ অপরাধ হলে বহুরূপীদের ধরে ধরে জেলে পোরা হত।”
“বুঝলাম। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য কী? খুলে বলো!”
“সবটা বলার উপায় নেই। তবে আমার নাম অগ্নি। এই অঞ্চলে যে মাঝে মাঝে অদ্ভুত ধরনের সবুজ রঙের মানুষ দেখা যাচ্ছে, এই খবরটা পেয়েই আমার আসা। গত সাতদিন ধরে আমি এখানকার মাঠ, ঘাট, জঙ্গল চষে বেড়িয়েছি। কোনও সবুজ মানুষের দেখা পাইনি। বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলেও দেখেছি। কেউই সবুজ মানুষ দেখেছে বলে স্বীকার করেনি। আমার ক্রমে বিশ্বাস হচ্ছিল যে, এটা একটা গুজব ছাড়া কিছুই নয়। আমি ফিরে গিয়ে সেই কথাই কর্তৃপক্ষকে জানাব বলে ঠিক করেছিলাম। আর আজই আমার ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু আজকেই ভাগ্যক্রমে আমি এই বাড়িতে
একজন সবুজ মানুষের দেখা পেয়ে গিয়েছি।”
“তুমি ভুল দেখেছ।”
লোকটা মাথা নেড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, “না মশাই, আমি একটুও ভুল দেখিনি। লোকটা বেজায় লম্বা, অন্তত সাড়ে সাত ফুট তো হবেই। রোগাটে কিন্তু জোরালো চেহারা, গায়ে আঁট করে পরা কালচে রঙের পোশাক। অনেকটা ডুবুরিদের পোশাকের মতো।”
“ডুবুরিদের সর্বাঙ্গ পোশাকে ঢাকা থাকে, গায়ের রং বোঝার উপায় নেই।”
“এ লোকটার মুখ, দুটো হাত আর হাঁটুর নীচের অংশ খোলা ছিল।”
বিজয়বাবু হাসলেন, বললেন, “তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সাড়ে সাত ফুট লম্বা সবুজ রঙের কোনও লোক যদি এখানে থাকত, তা হলে গ্রামদেশে একটা হইচই পড়ে যেত। এরকম অদ্ভুতদর্শন কোনও লোককে এখানে কারও কখনও চোখে পড়েনি। পড়লে অবশ্যই আমাদের কানে সে খবর আসত।”
“আপনার কি মনে হচ্ছে আমি মিথ্যে কথা বলছি?”
“না। তাও মনে হচ্ছে না। কারণ, মিথ্যে করে এ গল্প বলে তোমার কোনও লাভ নেই। কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাইছি যে, তুমি যা দেখেছ তা একটা ইলিউশন মাত্র। গাছের ছায়ায় কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে থাকলেও থাকতে পারে। ওই ঝোঁপঝাড়ের অন্ধকারে কারও গায়ের রং বোঝা সম্ভব নয়। তা ছাড়া তুমি একজন সবুজ রঙের লোককে খুঁজছিলে বলে তোমার ভিতরে একটা অটো সাজেশন তৈরি হয়েছিল। তাই বলছি, ওটা চোখের বিভ্রম ছাড়া কিছু নয়।”
লোকটা যেন একটু ধন্দে পড়ে গেল। চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে একটু ভেবে তারপর মুখ তুলে বলল, “আপনি বিচক্ষণ মানুষ, তাই আপনাকে একটা ঘটনার কথা বলতে চাই।”
“বলো।”
“দিনতিনেক আগে রাজবংশীদের পোডড়া বাড়ির মাঠে একজন দেহাতি বুড়ি খুঁটে দিচ্ছিল। অনেক খুঁটে।”
“হ্যাঁ জানি। ও হল দুধওলা রামভরোসার মা গিরিজাবুড়ি।”
“অত খুঁটে দেওয়া দেখে আমি একটু অবাক হয়েছিলুম। কারণ, আজকাল কয়লা বা গুলের উনুনে রান্না করা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের লোকও এখন গ্যাস বা কেরোসিনে রান্না করে। আমি তাই সেই বুড়িকে গিয়ে বললাম, এত খুঁটে কার জন্য দিচ্ছ গো মাসি? কে নেবে? তখন বুড়িটা একটুফুঁসে উঠে বলল, তোরা লা লিবি তো লা লিবি। হমার ঘুটিয়া হারা আদমিরা লিবে।”
“তার মানে?”
“হারা আদমি মানে সবুজ মানুষ। তখন আমি বুড়িকে ধরে পড়লাম। কিন্তু আমার আর একটি কথারও জবাব দিল না। গম্ভীর মুখে ঘুঁটে দিয়ে যেতে লাগল। তার মানে কি এই নয় যে, ওই গিরিজাবুড়ির সঙ্গে সবুজ মানুষদের একটা যোগাযোগ আছে?”
বিজয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “তুমি কি জানো যে, গিরিজাবুড়ি রোজ ভূত দেখতে পায়, রাজবংশীদের বাড়িতে পরিদের আনাগোনা টের পায় এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জলার ওধারকার জঙ্গলে একটা রাক্ষসও বসবাস করে?”
“বুড়োবুড়িদের কথায় নানা অসংগতি থাকে একথা ঠিক। কিন্তু সবুজ মানুষের কথা বলেছিল বলে আমার একটু বিশ্বাস হয়েছিল।”
“গিরিজাবুড়ি রোজ আমাদের বাড়িতে শাক তুলতে আসে। সারাক্ষণ বকবক করে যায়, যার কোনও মাথামুণ্ডু নেই।”
অগ্নি নামের লোকটা কিছুক্ষণ নিজের করতলের দিকে চেয়ে থেকে বলল, “তা হলে আপনি বলছেন যে, এখানে সবুজ মানুষের অস্তিত্ব নেই?”
“না, নেই।”
“আপনি কি একজন বৈজ্ঞানিক?”
“দুর পাগল! বৈজ্ঞানিক বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তবে কলেজে বিজ্ঞান পড়াতাম। আমার গবেষণার খুব শখ ছিল বলে একটা ছোট ল্যাবরেটরি করেছি। সেটা আমার খেলাঘর বলতে পারো। কাজের কাজ কিছুই হয় না।”
“আমি কি এখন যেতে পারি?”
“অবশ্যই। পুলিশে সত্যিই খবর দেওয়া হয়েছে কি না তা অবশ্য আমি জানি না। তুমি বরং আর বেশি দেরি না করে রওনা হয়ে পড়ো। এই নাও তোমার পিস্তল।”
“ধন্যবাদ।”
“পিস্তলটা দেখে মনে হচ্ছে খুব দামি।”
“হ্যাঁ। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা পিস্তলগুলোর একটা।”
“তুমি কি খুব বিপজ্জনক জীবনযাপন করো?”
“আমার কাজ কিছুটা হ্যাঁজার্ডাস। তা হলে আমি…!”
“এসো গিয়ে।” বিজয়বাবু অগ্নিকে সঙ্গে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। উদ্বিগ্ন মুখে সবাই বাইরে অপেক্ষা করছে দেখে বললেন, “একে তোমরা ছেড়ে দাও। এ কোনও বদ মতলবে এ বাড়িতে আসেনি।”
অগ্নিকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন বিজয়বাবু। অগ্নি চলে যাওয়ার পর তাঁর কপালে জাকুটি দেখা দিল।
বীরেনবাবু বললেন, “লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে ভাল কাজ করলে না দাদা।”
“ছেড়ে দিয়েছি কে বলল?”
“এই যে গটগট করে হেঁটে চলে গেল?”
“ও আবার আসবে। এবার অন্য মূর্তি ধরে। ওর সন্দেহ যায়নি।”
“কিন্তু পুলিশে তো দেওয়া যেত!”
“কোন আইনে? অপরাধ তো কিছু করেনি। তুই ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিস, সুতরাং ট্রেসপাসার নয়, চুরি-ডাকাতি করেনি, কারও উপর হামলাও করেনি। বরং নিজেই মারধর খেয়েছে।”
“কিন্তু বেআইনি পিস্তলটা?”
“আমার যতদূর ধারণা, পিস্তলের লাইসেন্স ওর আছে। তা তুই-ই বা ওকে রাস্তা থেকে ডেকে ঘরে আনতে গেলি কেন?”
বীরেনবাবু বললেন, “সব দোষ ওই বটুর। ও এসে বলল, লোকটা নাকি ওকে ভেকুড়ি দেখিয়েছে।”
বিজয়বাবু ভ্রু কুঁচকে বললেন, “ভেচকুড়ি! সেটা আবার কী?” বীরেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, “আমি জানি না, বটু জানে।”
বটু তাড়াতাড়ি বলল, “ওঃ, ভেকুড়ি বড্ড ভয়ের জিনিস মশাই। চোখ দুটো তাড়াং তাড়াং হয়ে যায়, মুখোনা যেন দুনো ফুলে যায়, আর হাঁ-এর ভিতর দিয়ে যেন আলজিভ অবধি দেখা যায়…! না, সে বলা যায় না।” বিজয়বাবু বললেন, “বাচ্চারা তো ওরকম করেই এ-ওকে ভ্যাঙায়। তাতে ভয় পাওয়ার কী আছে?”
৪. সকালের দিকটায়
সকালের দিকটায় কালীবাড়ির চাতালের একধারে থামের আড়াল দেখে যে লোকটা মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোয়, সে হল তারক দুলে। সারা রাত্তির তার বিস্তর মেহনত যায়। রক্তজল করা মেহনতের পরও তারকের তেমন সুবিধে হয়ে উঠছে না। না হল নামডাক,
হল পয়সা। এসব গুহ্য কথা আর কেউ না জানুক ঠাকুরমশাই ব্রজবিহারী ভটচাজ খুব জানেন।
পাঁচবাড়ি নিত্যপূজা সেরে ব্রজবিহারী এসে কালীবাড়ির চাতালে একটু বসলেন। এ সময় চাতালের গায়ে মস্ত বটগাছটার ঝুপসি ছাওয়ায় চাতালটা ভারী ঠান্ডা থাকে। একটু ঝিরঝিরে হাওয়া পুকুরের জল ছুঁয়ে এসে গা জুড়িয়ে দেয়। চারদিকটা ভারী নিরিবিলি আর নির্জন বলে মনটা জুড়োতে পারে। আর এই সময়টায় নানা ভাবনাচিন্তাও এসে পড়ে।
“বুঝলি রে তারক, অনেক ভেবে দেখলুম, ভগবান বোধহয় কানে ভাল শুনতে পান না।”
তারক টক করে উঠে বসে একটানমোঠুকে বলল, “প্রাতঃপেন্নাম হই ঠাকুরমশাই। তা কী যেন বলছিলেন?”
“অবিচারটা দ্যাখ। সেই ছেলেবেলা থেকে বাবার কানমলা আর পণ্ডিতমশাইয়ের বেত খেয়ে খেয়ে শব্দরূপ-ধাতুরূপ, সমাস বিভক্তি মুখস্থ করে করে বড়টি হলুম। কিন্তু শাস্ত্রটাস্ত্র শিখে কোন লবডঙ্কাটা হল বল তো? এই যে রোজ মন্দিরে বল, বাড়ি বাড়ি ঘুরে বল, ঠাকুর-দেবতার এত পুজো-অর্চনা করছি, তাতে কোন হাত পা গজিয়েছে রে বাপু? আজ বাপ বা পণ্ডিতমশাই বেঁচে থাকলে তাঁদের কাছেই জবাবদিহি চাইতুম। এত যে মেরে-বকে সংস্কৃত আর শাস্ত্র শেখালেন, তাতে হল কোন কচুপোড়া? এই যে রোজ সংস্কৃত মন্তর পড়ে ভগবানদের তোষামোদ করে যাচ্ছি, তা তারা কি আর তাতে কান দিচ্ছেন? বদ্ধ কালা না হলে মন কি একটু ভিজত না রে?”
তারক গম্ভীর হয়ে বলল, “আজ্ঞে, শুধু কালা কেন, ভগবানগণ চোখেও ভারী কম দেখেন। এই যে রাতবিরেতে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে মেহনত করে বেড়াই, খাটুনি তো কম নয় মশাই। খাটুনিটার কি কোনও দাম নেই? চোখ থাকলে কি আর-একটু দয়ামায়া হত না! কলিকাল বলেই চারদিকে যেন অবিচারের মচ্ছব চলছে ঠাকুরমশাই?”
“অবিচারের কথাই যখন বললি বাপ, তখন দুঃখের কথা তোকে খুলেই বলি। ওই যে দুধওলা রামভরোসার মা গিরিজাবুড়ি, শতচ্ছিন্ন একখানা কাপড় পরে ঘুঁটে দিয়ে মরত, হঠাৎ ভগবান যেন তেড়েফুঁড়ে তার ভাল করতে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছেন।”
“বটে ঠাকুরমশাই?”
“তবে আর বলছি কী? গোয়ালপাড়ায় পাঁচকাঠা জমি কিনবে বলে বায়না করেছে, ইটভাটায় গিয়ে দশ হাজার ইটের বরাত দিয়ে এসেছে। পাকাবাড়ি উঠল বলে! আজও দেখলুম, বুড়ি সকালে নতুন শাড়ি পরে বসে জিলিপি দিয়ে নাস্তা করছে।”
“লটারি মেরেছে নাকি ঠাকুরমশাই?”
“আরে না। তার খুঁটে নাকি কে বা কারা ভাল দামে কিনে নিচ্ছে। যার কপাল খোলে তার খুঁটের মধ্যেও ভগবান মোহর গুঁজে দেন কিনা!”
“তা যা বলেছেন ঠাকুরমশাই। এই পতিতপাবনকেই দেখুন না, ভুসিমাল বেচে কেমন খুশিয়াল হাবভাব! তা ঠাকুরমশাই, ঘুঁটে কি আজকাল বিলেত-আমেরিকায় চালান যাচ্ছে নাকি?”
“তা না যাবে কেন? গিরিজাবুড়ির কপাল ফেরাতে হয়তো সাহেবরাও আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছে।”
“এ কিন্তু খুব অন্যায় ঠাকুরমশাই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কত কৌশল করে থানা-পুলিশ থেকে গা বাঁচিয়ে সারারাত জেগে, মাথা খাঁটিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কী রোজগার হয় বলুন? ওই তো দেখুন না, কাল রাতে তিন বাড়িতে হানা দিয়ে জুটেছে মাত্র বিয়াল্লিশটা টাকা আর একটা রুপোর নথ। না, জীবনের উপর ঘেন্না ধরে গেল।”
“তা তো হবেই রে!”
“তা ঠাকুরমশাই, এই চুরিটুরি ছেড়ে কি ঘুঁটের ব্যাবসাতেই নেমে পড়ব নাকি?”
“দুর পাগল! স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরো ধর্ম ভয়াবহ! কুলধর্ম কি ছাড়তে আছে? তোরা হলি তিন পুরুষের চোর, অন্য কাজে তোর আর্ষই নেই। যার কর্ম তারে সাজে, অন্যের হাতে লাঠি বাজে। এই আমাকে দেখছিস না, সকাল থেকে মন্তর পড়ে পড়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, জুটেছে কয়েকটা মজা কলা, একধামা মোটা আতপচাল, কয়েকটা অখাদ্য কাটা ফল, দশটি টাকা। তা কী আর করা যায়? বাপ-দাদা এই কর্মেই জুতে দিয়ে গিয়েছেন, দিনগত পাপক্ষয় করে যাচ্ছি।”
তারক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে খুব গভীর চিন্তায় ডুবে রইল। তারপর বলল, “আচ্ছা ঠাকুরমশাই, খোলও কি আজকাল বিলেত আমেরিকায় চালান যাচ্ছে?”
“কেন রে, হঠাৎ খোলের কথা উঠছে কেন?”
“এই মহিন্দির ঘানিওলার কথাই বলছিলাম। আগে তো তার তেল কেনার তেমন খদ্দেরই ছিল না। ইদানীং শুনছি, সে তেলের বদলে খোল বেচে দেদার রোজগার করছে।”
“বলিস কী?”
“একেবারে নির্যস খবর ঠাকুরমশাই। সামনের শনিবার পরানগঞ্জে গোহাটা থেকে গোরু কিনবে বলে মহিন্দির কোমর বেঁধেছে।”
ঠাকুরমশাই চোখ কপালে তুলে বললেন, “মহিন্দির গোর কিনছে! ও বাবা, তা হলে তো তার ভাসাভাসি অবস্থা।”
“আরও একটা খবর আছে ঠাকুরমশাই।”
“বলে ফেল।”
“পরেশ তোপদারের একখানা সবজির খেত আছে, জানেন তো?”
“তা জানব না কেন? মদনপুর জঙ্গলের দক্ষিণে তার সবজির চাষ।”
“হ্যাঁ, ভারী নিরিবিলি জায়গা, কাছেপিঠে লোকালয় নেই। পরেশ সেখানে একখানা কুঁড়ে বেঁধে চৌপর দিন খেত পাহারা দেয়।”
“ফলায়ও ভাল। ভারী বড় সাইজের মিঠে বেগুন হয় তার খেতে।”
“বেগুন, বেগুনের কথা আর কবেন না। আপনার তো সত্তরের উপর বয়স হল, তাই না? এই সত্তর বছরে কত বড় সাইজের বেগুন দেখেছেন?”
“তা দেখেছি বই কী। ছোটখাটো লাউয়ের সাইজের কাশীর বেগুন খেয়েছি, এখনও মুখে লেগে আছে।”
“পরেশের খেতে যে বেগুন ফলেছে তা দেখলে আপনি মূর্ছা। যাবেন। চার-পাঁচ হাত উঁচু গাছে পাঁচ-সাত সের ওজনের শ’য়ে শ’য়ে বেগুন ঝুলছে দেখে আসুন গে!”
“দুর পাগল! ও নিশ্চয়ই বেগুন নয়!”
“আমারও প্রত্যয় হয়নি ঠাকুরমশাই। আর শুধু বেগুনই বা কেন, এই অসময়েও পরেশের বাগানে গেলে দেখতে পাবেন, রাক্ষুসে ফুলকপি আর দৈত্যের মতো বাঁধাকপি ফলে আছে। দুটো কপিতে একটা ভোজবাড়ির রান্না হয়ে যায়। তা ভাবলুম, রাতবিরেতে পরেশদাদা ঘুমোলে এক-আধটা জিনিস তুলে এনে বউ-বাচ্চাদের দেখাতাম। তা বলব কী মশাই, বাগানের ফটকটাই ডিঙোতে পারলাম না।”
“কেন রে? ফটকটা খুব উঁচু নাকি?”
“দুর দুর, চার ফুটও নয়। কিন্তু যতবার ভিতরে ঢুকতে যাই, কীসে যেন বাধক হয়। দেখলে মনে হয় ফাঁকা, কিন্তু ঢুকতে গেলেই যেন একটা শক্ত জিনিসে ঠেকে যেতে হয়। একবার মনে হয়েছিল পরেশদাদা বুঝি কাঁচ দিয়ে বাগান ঘিরেছে। কিন্তু দেখলুম, সেটা কাঁচও নয়। তাতে হাত দিলে হাত চিনচিন করে।”
“হ্যাঁরে, নেশাভাঙ করিসনি তো?”
“মা কালীর দিব্যি ঠাকুরমশাই, চোর হতে পারি, নেশাখোর নই। তবে পরেশদাদাকে গিয়ে পরদিন বেলাবেলি ধরেছিলুম। জিজ্ঞেস করলুম, “দাদা, এরকম সরেস জিনিস ফলালে কেমন করে? তা পরেশদাদা মিচিক মিচিক হেসে কথাটা পাশ কাটিয়ে গেলেন। শুধু বললেন, “যত্নআত্তি করলে সব জিনিসেরই বোলবোলাও হয়। তারপর রাতের ব্যাপারটাও কবুল করে ফেলে জিজ্ঞেস করলুম, “দাদা, বাগানের চারদিকে কাঁচের দেওয়াল তুললেন নাকি?” পরেশদাদা মৃদু হেসে বললেন, “কাঁচটাচ নয় রে, বাগান মন্তর দিয়ে ঘেরা থাকে। চোর তো দূরের কথা, একটা মাছি অবধি ঢুকতে পারে না।”
“বলিস কী! পরেশের মন্তরের এত জোর? আর আমি যে সারাটা জীবন মুখের ফেকো তুলে বিশুদ্ধ দেবভাষায় এত মন্তর পড়লুম, তাতে তো কোনও কাজই হল না! পরেশ কি আমার চেয়ে বেশি মন্তর জানে?”
“কুপিত হবেন না ঠাকুরমশাই। ব্রাহ্মণের রাগ বড় সাংঘাতিক। প্রলয় হয়ে যাবে।”
“দুর দুর! তোর কথা শুনে তো সন্দেহ হচ্ছে, ব্রহ্মতেজ বলে কি কিছু আছে নাকি? মন্তর ঘেঁটে বুড়ো হয়ে গেলুম, আজ অবধি মন্তরে একটা মশা-মাছিও মারতে পারিনি!”
এমন সময় চাতালের পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, “কে বলে যে আপনার মন্তরের জোর নেই? বললেই হল? আর পরেশের সবজির খেতে যেসব কাণ্ডমাণ্ড হচ্ছে তা মোটেই মন্তরের জোরে নয়। ও হচ্ছে ভুতুড়ে কারবার।”
ব্রজবিহারী নবকুমার দিকপতিকে দেখে ভারী খুশি হয়ে বললেন, “আয় নব, বোস এসে। তা ভুতুড়ে কারবার যে সেটাই বা কী করে বুঝলি?”
“পরেশের চোদ্দো পুরুষের কেউ মন্তর-তন্তরের কারবার করেনি। মন্তরের মহিমা ও কী করে বুঝবে? আর আপনার মন্তরের কথা কী বলব ব্রজখুড়ো, আপনি হয়তো মন্তরের জোর টের পান না, কিন্তু আমরা তো দিব্যি পাই। এই যে সেদিন কেষ্ট হাজরার বাড়িতে শেতলা পুজো করছিলেন, ঘরের ভিতর বসে আপনি মন্তর পাঠ করছেন, আর বাইরে সেই মন্তর যেন চারদিকে ঠং ঠং করে হাতুড়ির ঘা দিয়ে বেড়াচ্ছে! মধুদের বাগানে গাছ থেকে দুটো ডাঁশা পেয়ারা খসে পড়ল, হাবুদের কাবলি বিড়ালটা একটা মেঠো ইঁদুরকে তাড়া করতে গিয়েও করল না। পরে দেখলুম, জটা ওদের দাওয়ায় বসে ফাঁস ফাঁস করে কাঁদছে, আর সুদখোর মহাপাপী খগেন সাঁতরা মন্তরের শব্দ শুনে দু’কানে হাতচাপা দিয়ে বাবা রে, মা রে’ করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। স্বচক্ষে দেখা।”
ব্রজবিহারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “এই গাঁয়েগঞ্জে কে আর ওসবের মর্ম বোঝে রে, দামই বা দেয় কে?”
“কেন ব্রজখুড়ো, এই তো সেদিন কেষ্ট হাজরাই বলছিল, শেতলা পুজোর পর থেকেই নাকি তার নব্বই বছরের শয্যাশায়ী বুড়ি ঠাকুরমা তেড়েফুঁড়ে উঠে চেঁকি কুটতে লেগেছেন। জ্যাঠামশাইয়ে বাঁ হাঁটুতে বাত ছিল, এখন সেই বাত জ্যাঠার হাঁটু তো ছেড়েছেই, এই গঞ্জ ছেড়েও উধাও হয়েছে। কেষ্টর ছেলে সেভেন থেকে এইটে ওঠার জন্য গত তিন বছর ধরে মেহনত করে যাচ্ছিল। এবার দেখুন, মাত্র তিন বিষয়ে ফেল মেরেছে বলে মাস্টারমশাইরা তার কত প্রশংসা করে সেভেনে তুলে দিলেন। কেষ্টর মেয়ে ফুলির হাতে একজিমা ছিল বলে বিয়ে হচ্ছিল না। শেতলা পুজোর পর সেই একজিমা তাড়াতাড়ি পায়ে নেমে গিয়েছে। ফুলির বিয়েও ঠিক হল বলে।”
তারক এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল। এবার বিরক্ত হয়ে বলল, “আহা, ভূতের বৃত্তান্তটা যে চাপা পড়ে যাচ্ছে মশাই।”
নব দিকপতি বগল থেকে দাবার বোর্ড আর খুঁটির কৌটো নামিয়ে আসনসিঁড়ি হয়ে বসে বলল, “ও, সেকথা আর বলিস না। পরেশের চাষবাড়িতে শুধু তরকারির চাষই হয় না রে, রীতিমতো ভূতেরও চাষ হয়, এ কথা তল্লাটের সবাই এখন জেনে গিয়েছে। আর হবে না-ই বা কেন? পরেশের ওই চাষবাড়িতেই তো একসময় খেরেস্তানদের কবরখানা ছিল। তো তারাই এখন কবর ছেড়ে তেড়েফুঁড়ে উঠে আস্তিন গুটিয়ে ওইসব অশৈলী কাণ্ড করছে।”
তারক সন্দিহান হয়ে বলল, “নিজের চোখে দেখেছ নবদাদা?”
“তা আর দেখিনি? জানিস তো, রোজই আমি সকালে বাজারে গিয়ে কালীস্যাকরার সঙ্গে এক পাট্টি দাবা খেলে আসি।”
“তা আর জানি না!”
“তা সেদিন গিয়ে দেখি, কালী ম্যালেরিয়া জ্বরে কোঁ কোঁ করছে। তা মনটা খারাপ হয়ে গেল। দাবার নেশা বড় সব্বোনেশে নেশা। তাই ভাবলুম, এ গাঁয়ে তো আর পাতে দেওয়ার মতো দাবাড়ু নেই। তা যাই, গিয়ে পরেশের সঙ্গেই এক পাট্টি দাবা খেলে আসি। দিনে এক পাট্টি দাবা না খেলতে পারলে আমার খিদে হতে চায় না, পেটে বায়ু হয়, মাথা ঝিমঝিম করে। কিন্তু পরেশের ওখানে গিয়ে বাইরে থেকে অনেক ডাকাডাকি করেও তার সাড়া না পেয়ে চলে আসব ভাবছি, ঠিক এমন সময় বেগুনখেতের আড়াল থেকে একটা সবুজ রঙের লম্বা লিকলিকে ভূত বেরিয়ে এসে আমার দিকে কটমট করে চেয়ে রইল। দেখে তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছেড়ে উড়ে যায় আর কী!”
তারক অবাক হয়ে বলল, “দিনেদুপুরে?”
“তবে আর বলছি কী? আজকাল ভূতেদের যা আস্পদ্দা হয়েছে, বলার নয়। আর শুধু কি কটমট করে চাউনি? একটা লম্বা আঙুল তুলে আমার বগলের দাবার বোর্ডটা দেখিয়ে কী যেন বলল।”
“কী বলল গো নবদা?”
“সে ভাষা বুঝবার কি সাধ্যি আছে আমাদের? ভাষাও নয়, অনেকটা ঝিঝিপোকার ডাকের মতো একটা শব্দ। আমি তো অবাক। ভূত কি দাবাও খেলতে চায় নাকি রে বাবা! আমার তো ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু হাতে-পায়ে এমন খিল ধরে গিয়েছে যে, পালানোরও উপায় নেই।”
ব্রজবিহারী বললেন, “ভূতের গা থেকে বোটকা গন্ধ পাসনি?”
“তা আর পাইনি! খড়বিচালি আর শুকনো ঘাসপাতা থেকে যেমন গন্ধ আসে, অনেকটা তেমনি।”
তারক বলল, “তা কী করলে নবদা?”
একটা বেগুনগাছের ছায়ায় অগত্যা দাবার ছক বিছিয়ে বসতেই হল। নইলে কে জানে বাবা, ভূতের অসাধ্যি তো কিছু নেই! গলাটলা টিপে ধরে যদি? কিন্তু দাবা খেলতে বসলে আমার আবার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ভয়ডরও উধাও হল। আশ্চয্যির ব্যাপার হল কী জানিস? ভূতটা আমাকে গো হারান হারিয়ে দিল।”
“বলো কী?”
ব্রজবিহারী বললেন, “হবে না? ও হল সাহেবভূত। সাহেবদের সঙ্গে কি আমরা এঁটে উঠতে পারি?”
তারক মাথা নেড়ে বলল, “না না, সাহেব হতে যাবে কেন? শুনছেন না গায়ের রং সবুজ। এ নিশ্চয়ই কাফ্রির ভূত।”
নব বলল, “তো হতে পারে। সাহেবদের তো মেলা কাফ্রি কাজের লোক ছিল বলে শুনেছি। তবে যাই বলিস, দাবা যেন গুলে খেয়েছে। দেড় ঘণ্টার মধ্যে তিন পাট্টি খেলা শেষ। প্রতিবার বারো চোদ্দো চালের পরই বুঝতে পারছিলাম, হারা ছাড়া উপায় নেই।”
“তারপর কী হল?”
“কী আর হবে? তিন পাট্টির পর ভূতটা উঠে বেগুনখেতের মধ্যে ঢুকে গায়েব হয়ে গেল।”
ব্ৰজবিহারী বললেন, “খুব বেঁচে গিয়েছিস। ঘাড় যে মটকে দেয়নি সেই ঢের!”
নবকুমার গম্ভীর হয়ে বলল, “বাঁচলুম আর কোথায় ব্ৰজখুড়ো! সেই থেকে যে নেশা ধরে গেল? ফের পরদিন গেলুম। ফের তিন পাট্টি খেলা। ফের গোহারান হার। তারপর থেকে রোজই যাচ্ছি।”
“বলিস কী?”
“এই তো সেখান থেকেই আসছি, আজ্ঞে! আজও হেরেছি বটে, তবে ক’দিন হল ভূতটার চালগুলো লক্ষ করে খানিক খানিক শিখেও নিয়েছি কিনা! তাই আগের মতো সহজে হারছি না। আজ তো ওর মন্ত্রীও খেয়ে নিয়েছিলুম। তবে এমন চালাক যে, দুটো নৌকো দিয়ে অ্যাইসান চেপে খেলল যে, পথই পেলুম না।”
ব্রজবিহারী গম্ভীর হয়ে বললেন, “ভূতের সঙ্গে দাবা খেলছিস, একটা প্ৰাশ্চিত্তির করে নিস বাবা। সংহিতা দেখে আমি বিধান বলে দেবখন।”
“আহা, সে না হয় পরে হবে। আগে জুত করে কয়েকদিন ভূতটার সঙ্গে একটু খেলে নিই ব্রজখুড়ো। ভূতটা যে মাপের দাবাড়ু তাতে বিশ্বনাথন আনন্দ, দিব্যেন্দু বড়ুয়া, টোপালভ, ক্রামনিক সবাইকেই বলে বলে হারিয়ে দেবে।”
ভ্রূ কুঁচকে ব্রজবিহারী বললেন, “এরা সব কারা রে?”
“দুনিয়ার নামজাদা সব দাবাড়ু ব্ৰজখুড়ো!”
“বলিস কী? দাবা খেলেও নাম হয় নাকি? ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি তাস-দাবা-পাশা, এ তিন কর্মনাশা।”
“সেসব দিন আর নেই খুড়ো। এখন দাবা খেলে নাম হয়, লাখো লাখো টাকা হয়।”
“দ্যাখো কাণ্ড! আগে জানলে তো পুরুতগিরি না করে দাবা নিয়েই লড়ে যেতুম রে। বাবা যে কখনও ওসব ছুঁতেও দেননি! না,
জীবনে কত সুযোগ যে ফসকে গেল!”
তারকও বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল, “যা বলেছেন ঠাকুরমশাই, বসে বসে দাবা-বোড়ে টিপে যদি আয়-পয় হত, তা হলে রাত জেগে মেহনত করতে যেত কে? তা নবদাদা, ভূতবাবাজির সঙ্গে তো তা হলে এখন তোমার খুব ভাবসাব!”
“তা একরকম বলতে পারিস। তবে কথাটথা তো আর হয় না। কেবল ঝিঝিপোকার মতো একটা শব্দ করে যায়। তা থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই কিনা!”
“তা হলে পরেশদাদার বাগানে যা হচ্ছে তা ভূতুড়ে কাণ্ডই বলছ তো?”
“তা ছাড়া আর কী! পরেশ অবশ্য স্বীকার করতে চায় না। কেবল মিচকি মিচকি হাসে আর পাশ কাটিয়ে যায়।”
ব্রজবিহারী একটা নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলে বললেন, “খবরটা দিয়ে বাঁচালি বাপ৷ পরেশ মন্তরের জোরে অশৈলী কাণ্ড ঘটাচ্ছে শুনে নিজের উপর ঘেন্না এসে গিয়েছিল। পরেশের মন্তরের যদি ওরকম জোর হয়, তবে কোন ঘোড়ার ঘাস কাটলুম?”
“আরে রামো, মন্তরতন্তর নয় খুড়ো, ভূত!”
৫. তা রোজগারপাতি আজও কিছু
তা রোজগারপাতি আজও কিছু কম হল না নবর।
গুনেগেঁথে দেখল, সকাল থেকে মাত্র ঘণ্টা তিনেকের মেহনতে তিনশো বাহান্ন টাকা। এই রেটে চলতে থাকলে বছরটাকের মধ্যে নন্দকিশোরের আট বিঘে ধানিজমি, সতু হাজরার আটা চাক্কি, যদু ঘোষের বসতবাড়ি আর অন্তত একটা দুধেল গাই কিনে ফেলতে পারবে।
নামাবলিখানা ভাঁজ করে, পুঁথিপত্র গুছিয়ে চশমাজোড়া খুলতে যাবে, এমন সময় একজন মোটাসোটা লোক, “বেঁধে ঠাকুরমশাই, বেঁধে! ও কাজ করবেন না, তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে! প্রলয় ঘটে যাবে!” বলে চেঁচাতে চেঁচাতে, হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। নব ঘাবড়ে গিয়ে থপ করে বসে পড়ল।
লোকটা সামনে এসে বসে পড়ে বলল, “করছিলেন কী ঠাকুরমশাই! সেই গেড়েপোতা থেকে আপনার শ্রীচরণ দর্শনে কত কষ্ট করে আসছি, আর আপনি পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলছিলেন?”
নব আমতা আমতা করে বলল, “না, এই বেলা হয়েছে তো! মানুষের স্নানাহার বলেও তো একটা ব্যাপার আছে!”
পকেট থেকে ফস করে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে হাতে গুঁজে দিয়ে হেঁঃ হেঁঃ করে বলল, “আজ্ঞে, গ্রহ-তারকা, রাহু কেতু চিবিয়ে ছাতু করে ফেলছেন, আপনার আবার স্নানাহার! ও হবেখন। তা ঠাকুরমশাই, শরীরগতিক সব ভাল তো?”
“যে আজ্ঞে।”
“আজ্ঞে, সেই যে জষ্টি মাসে বলেছিলেন, সাইকেল থেকেই আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করবে! মনে নেই আপনার?”
নব মাথা চুলকে বলল, “আজ্ঞে, কতজনাকেই তো রোজ কত কিছু বলতে হয়, সব কি আর স্মরণে থাকে?”
“তা তো বটেই, তা তো বটেই! চুনো-পুঁটিদের মনে রাখাটাও কাজের কথা নয় কিনা। আর আপনারা হলেন গিয়ে বাকসিদ্ধাই, মুখের কথাটি খসল কী সেটাই বোমা হয়ে ফাটল। ওঃ, কী কাণ্ড মশাই!”
নব আঁতকে উঠে বলল, “বোমা ফেটেছে নাকি? ও বাবা!”
“আহা, সেই বোমা নয়! এ হল বাক্যের বোমা, একেবারে অব্যর্থ। তা মশাই, একদিন সত্যিই ওই সাইকেলে চেপেই আমার ভবিতব্য ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে এসে হাজির।”
নব ভারী খুশি হয়ে বলল, “তাই নাকি?”
“তবে আর বলছি কী! দুপুরবেলা সবে খেতে বসেছি, পঞ্চদেবতাকে নিবেদন করে সবে উচ্ছেসেদ্ধ দিয়ে এক গরাস মুখে তুলেছি কি তুলিনি, অমনি বাইরে সাইকেলের পিরিং পিরিং ঘণ্টি। ছোট মেয়ে পটলি ছুটে এসে বলল, ও বাবা, তোমার টেলিগ্রাম এসেছে। কী মুশকিল বলুন, ভাত ছেড়ে উঠলে পাত ত্যাগ হয়ে যাবে। সারা দিনমানে আর অন্নজল মুখে ভোলার উপায় নেই। আর আমার বাড়ির লোকগুলোও সব ক অক্ষর গোমাংস। তখন পিয়ন নীলমণি হাঁক দিয়ে বলল, “ও বিদ্যেধর, আজকের মতো ভাত খাওয়া এমনিতেই ঘুচেছে। টেলিগ্রামে খবর এসেছে যে, তোমার খুড়োমশাই গত হয়েছেন।”
“আহা, কিন্তু এ তো বড় দুঃখের খবর মশাই।”
“কে বলল দুঃখের খবর?”
নব অবাক হয়ে বলল, “নয়? কিন্তু আমি যেন শুনেছিলুম খুড়ো জ্যাঠা গত হওয়া দুঃখেরই ব্যাপার!”
“আহা, তা তো বটেই। তবে কিনা কোনও কোনও খুড়ো গত হলে কারও কারও একটু সুবিধেও হয় আর কী। এই আমার স্বর্গত খুড়োমশাইয়ের কথাই ধরুন। বছরটা আগে বড্ড আতান্তরে পড়ে তিনশোটি টাকা ধার চাইতে গিয়েছিলুম। তা খুড়োমশাই ফস করে একটা হিসেবের খাতা বের করে গড়গড় করে খতিয়ান দিয়ে বললেন, “আমি নাকি গত বাইশ বছরে তাঁর কাছ থেকে মোট এগারো হাজার তিনশো বারো টাকা হাওলাত নিয়ে এক পয়সাও শোধ দিইনি। বুঝুন কাণ্ড! যার অত বড় ফলাও অবস্থা, ত্রিশ বিঘে ধানিজমি, আম-নারকোলের বাগান, মাছের পুকুর আর তেজারতির ব্যাবসা, তার কাছে ওটা একটা টাকা হল? তা বুক ঠুকে সেদিন বলেই ফেললুম, “খুড়ো, আপনি পটল তুললে আপনারটা খাবে কে? এই শৰ্মাই তো আপনার একমাত্র ওয়ারিশান। তারপর মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধশান্তি সেসবও আমি ছাড়া করার লোক নেই!’ এ কথায় খাপ্পা হয়ে খুড়ো আমাকে খড়ম-পেটা করে তাড়ালেন। বুড়ো বয়সে কী অপমান বলুন? খুড়িমা বেঁচে থাকতে এত অনাদর ছিল না। বছর দুই আগে তিনি মরে গিয়ে ইস্তক খুড়োমশাই যেন আরও কঞ্জুস, আরও তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিলেন। তার ফলটা কী হল দেখুন।”
“কী হল বলুন?”
“অপঘাত মশাই, অপঘাত! একপাল শেয়াল ক’দিন ধরে বাগানের ফলপাকুড় খেয়ে বেজায় ক্ষতি করে যাচ্ছিল। তাই সেদিন সন্ধের মুখে বন্দুক নিয়ে খুড়োমশাই শেয়াল মারতে বেরিয়েছিলেন। তখনই ভূত দেখে হার্টফেল হয়। গত জষ্টি মাসে আপনি চেতাবনি দিয়েছিলেন, সাইকেলে চেপে আমার ভাগ্য আসবে। একেবারে চার মাসের মাথায় কাঁটায় কাঁটায় ফলে গেল। তা সব দখলটখল নিয়ে এখন জেঁকে বসেছি আর কী। তাই ভাবলুম আপনাকে আর একবার হাতটা দেখিয়ে যাই। তা দেখুন তো ঠাকুরমশাই, সামনে আর কী কী ভাল জিনিস আসছে?”
নব একটু অবাক হয়ে বলল, “আপনার খুডোমশাই ভূত দেখে হার্টফেল হয়েছিলেন বুঝি?”
বিদ্যেধর সতর্ক চোখে চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, “লোকে নানারকম কথা রটাচ্ছে মশাই! কেউ কেউ বলছে সম্পত্তির লোভে আমিই নাকি খুড়োকে মেরেছি! ও কথায় মোটেই কান দেবেন না মশাই। সন্ধেবেলা শেয়াল মারতে বেরিয়ে খুড়োমশাই যে ভূতটাকে ভুষনোর মাঠে জঙ্গলের ধারে দেখেছিলেন, সেটা তালগাছের মতো লম্বা, আর তার গায়ের রং সবুজ। নির্যস সত্যি কথা। আর আপনার কাছে লুকিয়ে তো লাভ নেই। ত্রিকালদশী মানুষ আপনি, আপনার কাছে মিছে কথা বলে কি পার পাওয়ার জো আছে…? ভুষনোর মাঠের সেই ভূতকে রাতবিরেতে অনেকেই দেখেছে। আমার ছেলে বলাইয়ের বয়স এই সাত বছর, সেও নাকি দেখেছে সবুজ রঙের ঢ্যাঙা ভূতটা সন্ধের পর আনাচে-কানাচে ঘুরে কেঁচো আর গুবরেপোকা তুলে নিয়ে খায়। কী নিঘিন্নে জীব বলুন!”
নব আতশ কাঁচটা বের করে বলল, “শেয়াল মারতে যাওয়াটা আপনার খুড়োর উচিত কাজ হয়নি।”
বিদ্যেধর গলা নামিয়ে বলল, “আমরাও তো তাই বলাবলি করি। তা শেয়ালে দুটো ফলপাকুড় খাচ্ছিল তো খেত। কিন্তু খুড়োমশাইয়ের তো ওইটেই মস্ত দোষ ছিল কিনা। পুরনো জুতোজোড়া অবধি প্রাণে ধরে কাউকে দেননি কখনও। কেউ কুটোগাছটি সরালেও খেপে উঠে লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করতেন। আর তাই তো বেঘোরে প্রাণটা দিতে হল।”
“আপনার খুড়োমশাইয়ের খুব ভূতের ভয় ছিল নাকি?”
“খুব, খুব। দিনমানে পর্যন্ত কাছে লোকজন রাখতেন। সন্ধের পর বড় একটা ঘরের বাইরে বের হতেন না। সেদিন যে কোন নিশির ডাক শুনে হুড়োহুড়ি করে বেরোতে গেলেন কে জানে? আর ভূতেরাও কেন ভুষনোর মাঠে ঘুরঘুর করছে কে জানে!”
“আপনাদের গেজেঁপোতায় কি খুব ভূতের উপদ্রব নাকি?”
“আমি অবিশ্যি দেখিনি, তবে শুনি, ইদানীং তেনাদের আনাগোনা বড্ড বেড়েছে। অনেকেই দেখতে পাচ্ছে তাঁদের। ক’দিন হল দেখছি, দু-তিনজন উটকো লোকও এসে ভুষনোর মাঠের ঝোঁপঝাড়ে ওত পেতে বসে থাকে। তারা ওঝা-বদ্যিই হবে কিংবা ফকির-দরবেশ। আমাদের নিয়ামত ফকিরবাবা তো ভূত ধরে শিশিতে মশলা-তেলে ভিজিয়ে রেখে দিতেন। এদেরও মনে হয় সেই মতলব। তা ভূতের বাজারদর এখন কেমন যাচ্ছে ঠাকুরমশাই?”
নব তার জিনিসপত্র গুটিয়ে উঠে পড়ল। বলল, “আমার স্নান খাওয়ার দেরি হয়ে যাচ্ছে মশাই। আমি চললুম।”
.
হালদারপুকুর হল ভারী একটেরে নিরিবিলি জায়গা। ওপারে ফলসার ঘন বন, চারদিকে জমাট বাঁধা ঝোঁপঝাড়। এ পাশটায় জনমনিষ্যির বড় একটা যাতায়াত নেই। চারদিকে গাছে মেলা পাখিপক্ষী আছে, জঙ্গলে কাঠবিড়ালি, গিরগিটি, সাপ, বেজি, তক্ষক, বাঁদর আর মেঠোহঁদুরের অভাব নেই। পুরনো ভাঙা ঘাটলায় বসে সকাল থেকে ছিপের ফাতনার দিকে নজর রাখছেন বিরাজমোহন। ওই একটা কাতলা মাছ এক বছর ধরে তাঁকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। সত্যিকারের ধরা পড়েছিল একবারই। গত বছর। কিন্তু ধূর্ত মাছটা বঁড়শি গিলেও এমন চুপ করে রইল, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। বিরাজমোহন সেদিন লুচি আর মোহনভোগের পেল্লায় জলখাবার খেয়ে এসেছিলেন। সকালের মনোরম আবহাওয়ায় বয়সের দোষে একটু ঘুম এসে গিয়ে থাকবে। সেই ফাঁকে শয়তান মাছটা ছিপ টেনে নিয়ে পালাল। সেই ছিপ পরে উদ্ধার হয় বটে, কিন্তু সুতোটা কাটা ছিল। সেই থেকে এই পর্যন্ত মাছটা বিরাজমোহনের আরও তিনটে দামি হুইল বঁড়শি ছিনতাই করেছে। তার মধ্যে দুটি আর পাওয়া যায়নি। বিরাজমোহন আজকাল স্বপ্ন দেখেন, বিরাট কালো মাছটা বিরাজমোহনের আহাম্মকির কথা ভেবে মাঝরাতে জলের মধ্যে অট্টহাস্য করে।
আজও সকাল থেকে বসে গিয়েছেন বিরাজমোহন। কাতলার সঙ্গে তাঁর লড়াই কবে শেষ হবে কে জানে? কিন্তু ধৈর্য হারানোর পাত্র তিনি নন। একটি ইতর প্রাণীর কাছে এরকম লজ্জাজনকভাবে হেরে যাওয়াকে তিনি খুবই অপমানজনক বলেই মনে করেন। নিত্য নতুন চারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আজও একটি আনকোরা নতুন চার লাগিয়েছেন তিনি। অতি মজবুত সুতো এবং খুবই দামি হুইল ছিপ।
ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর বিরাজমোহন হঠাৎ খুব জোরালো ঝিঝির ডাক শুনতে পেলেন। ঝিঝির শব্দই, তবে একটু যেন অন্যরকম। কেমন যেন তালে-লয়ে ঝিঝি ডাকছে। সেই সঙ্গে দেখতে পেলেন ফাতনা একটু একটু নড়তে লেগেছে। বিরাজমোহন ছিপটা শক্ত করে ধরে রইলেন।
হঠাৎ জলে একটা বিপুল ঘাই মেরে মাছটা একবার ভেসে উঠে বিরাজমোহনকে যেন জিভ ভেঙিয়ে আবার জলে ডুব দিল।
তারপরই ছিপে প্রচণ্ড টান। আচমকা টানে ছিপটা আজও চলে যাচ্ছিল প্রায়। একেবারে শেষ মুহূর্তে সামাল দিয়ে বিরাজমোহন সুতো ছাড়তে লাগলেন। মাছটা অনেক দূর চলে গেল। আবার বিরাজমোহন সুতো গুটিয়ে টেনে আনলেন মাছটাকে। আবার মাছটা সুতো নিয়ে পালাতে লাগল। খেলাটা ভারী জমে উঠতে লাগল। এতদিনে ব্যাটা ঠিকমতো বঁড়শি গিলেছে বলে টের পাচ্ছেন বিরাজমোহন। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি মাছটাকে খেলাতে লাগলেন।
আজ যে তার ভাগ্য সদয় তা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বুঝতে পারলেন বিরাজমোহন। কারণ, মাছটা যে হেদিয়ে পড়ছে তা তিনি সুতোর টান দেখেই অনুমান করতে পারছেন। আর-একটু খেলিয়ে নিয়েই এবারে তুলে ফেলতে পারবেন।
ঠিক এই সময় মাঝপুকুরে ভুস করে একটা মাথা জলের উপর জেগে উঠল। সেই সঙ্গে তীব্র ঝিঝির শব্দ। বিরাজমোহন অবাক হয়ে দেখলেন, মাথাটা একজন মানুষের, তবে আকারে বড় এবং রং গাঢ় সবুজ। লোকটা তার দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল যে, বিরাজমোহনের গা দিয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে লোকটা মাঝপুকুরে উঠে দাঁড়াল। বিরাজমোহন দেখলেন, হালদার পুকুরের মতো গভীর জলেও লোকটার মাত্র কোমর অবধি ডুবে আছে। আর তার বাঁ হাতে সাপটে ধরা একটা বিশাল কাতলা মাছ লেজ ঝাঁপটাচ্ছে, মুখে বঁড়শিটা গেঁথে আছে এখনও।
সবুজ লোকটা খুব যত্ন করে মাছের মুখ থেকে বঁড়শিটা খুলে নিয়ে মাছটাকে আবার জলে ছেড়ে দিয়ে বিরাজমোহনের দিকে আঙুল তুলে যেন কিছু বলল। ভাষাটা বুঝতে পারলেন না বিরাজমোহন। শুধু ঝিঝির ডাক তো কোনও ভাষা হতে পারে না। কিন্তু বিরাজমোহন ওই ঝিনঝিন শব্দের মধ্যেই যেন লুকিয়ে থাকা বাক্যটা বুঝতে পারলেন।
লোকটা যেন বলল, “এখান থেকে চলে যাও। আর কখনও এ কাজ কোরো না।”
বিরাজমোহন কাঁপতে কাঁপতে বললেন, “ভুল হয়ে গিয়েছে বাবা, আর কখনও হবে না।”
ছিপটিপ ফেলে বিরাজমোহন সিঁড়ি বেয়ে উঠে একরকম দৌড়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তারপর বুড়ো বয়সে দৌড়ের ধকলে এমন হাঁফিয়ে পড়লেন যে, কিছুক্ষণ কথাই কইতে পারলেন না।
বীরেনবাবু তাকে দেখে শশব্যস্তে উঠে ধরে এনে বসালেন। “কী হয়েছে বিরাজজ্যাঠা?”
“ভূতে বিশ্বাস করিস?”
“ফুঃ! ভূতটুত কেউ বিশ্বাস করে নাকি? আজগুবি ব্যাপার।”
“আমি এইমাত্র হালদারপুকুরে ভূত দেখে এলাম। শুধু দেখাই নয়, কাতলা মাছটাকে এক বছরের চেষ্টায় আজ বাগে এনে প্রায় তুলেও ফেলেছিলাম। ঠিক সেই সময় জলের ভিতর থেকে একটা সুড়ঙ্গে লম্বা মূর্তি বেরিয়ে এসে মাছটা কেড়ে নিয়ে জলে ছেড়ে দিল। তারপর সে কী তড়পানি! সোজা আঙুল তুলে জানিয়ে দিল, হালদারপুকুরে ফের গেলে দেখে নেবে।”
বীরেনবাবু খুবই চটে গিয়ে বললেন, “হালদারপুকুর তো আমরা বছর চারেক আগেই কিনে নিয়েছি। ও আমাদের খাসপুকুর। কার এত সাহস যে, হালদারপুকুর থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেয়? এক্ষুনি লোজন পাঠাচ্ছি। জবর দখল করা বের করছি আজই। দরকার হলে রক্তারক্তি করে ছাড়ব।”
“মাথা গরম করিসনি। সে মনিষ্যি হলেও না হয় কথা ছিল।”
“মানুষ না তো কী?”
বিরাজমোহন মাথা নেড়ে বললেন, “মানুষ কি আট-দশ হাত লম্বা হয় নাকি তার গায়ের রং সবুজ হয়?”
বীরেনবাবু হা হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, “সবুজ মানুষ! মানুষের ন্যাবাট্যাবা হলে রং হলদেটে মেরে যায়। জানি, রোদে পুড়লে কালচেও মেরে যায়। কিন্তু সবুজ হচ্ছে কোন সুবাদে? এই তো সেদিনও ভেচকুড়ি-কাটা লোকটা সবুজ মানুষের কথা বলছিল। এ তো বড় সমস্যা হল দেখছি! পুলিশে একটা খবর দেওয়া দরকার।”
বিজয়বাবু সব শুনে বললেন, “এটা নিয়ে বেশি হইচই করার দরকার নেই। আপাতত বিরাজদাও আর হালদারপুকুরে না গেলেই ভাল। কারণ, সবুজ মানুষেরা মাছটাছ ধরা পছন্দ করে না।”
বীরেনবাবু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “কিন্তু এটা তো আমাদের পক্ষে অপমান! আমাদের পুকুরে আমরা মাছ ধরব তাতে অন্যে বাগড়া দিতে আসবে কেন? এত আস্পদ্ধা কার?”
বিজয়বাবু মৃদু স্বরে বললেন, “আস্পদ্ধা কাঁদের হয় জানিস? যারা শক্তিমান। আমার ধারণা তুই লোকজন, লেঠেল পাঠিয়েও তাদের কিছুই করতে পারবি না।”
“ওরা কারা বিজয়জ্যাঠা?”
“সেটা আমিও ভাল জানি না, তবে জানবার চেষ্টা করছি। সবুজ মানুষরা আমাদের কিছু বলতে চাইছে। সেটা হয়তো খুব খারাপ কথাও নয়।”
বীরেনবাবু বললেন, “কথা কইতে চায় তো ভাল কথা, বাড়িতে এসে চা খেতে খেতে বলুক না। অসুবিধে কোথায়?”
বিজয়বাবু বললেন, “অসুবিধে আছে। তুই বুঝবি না।”
৬. বুড়ো বয়সের একটা লক্ষণ
বুড়ো বয়সের একটা লক্ষণ হল, ইন্দ্রিয়াদি একে একে বিকল হতে থাকে। চোখ যায়, কান যায়, নাক যায়, বোধবুদ্ধি গুলিয়ে যেতে থাকে। এখন যেন সেই রকমই হতে লেগেছে নিমচাঁদের। একচন্দ্রদাদার যখন কানের দোষ হল তখন একদিন তাকে বলেছিল, “বুঝলি নিমে, যখন কানে..সব সময়, দিনমানে কি রাতদুপুরে কেবল ঝিঝিপোকার ডাক শুনবি তখনই জানবি যে, তোর কানের দোষ হয়েছে। ওই শব্দের ঠেলায় অন্য সব আওয়াজ আর কানে ঢুকবার পথই পায় না।‘
কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। বুড়ো বয়স এসে অন্য সব ইন্দ্রিয় ছেড়ে তার কানটাকেই যেন আগে পাকড়াও করেছে। সেই রকমই শুনেওছে নিমচাঁদ। বার্ধক্য এসে আগে কানের উপরেই চড়াও হয়। তারপর সেখানে থানা গেড়ে বসে অন্যসব যন্ত্রপাতি বিকল করার কাজে লেগে পড়ে।
জলার ধারের জঙ্গলের পাশ দিয়ে বুড়োমানুষদের মতোই টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কানে ঝিঝির ডাকটা শুরু হল। ভারী জ্বালাতনের ব্যাপার। প্রথমটায় ভেবেছিল, সত্যি ঝিঝিই ডাকছে বুঝি। তা বনে-জঙ্গলে ঝিঝিরা ডেকেও থাকে। কিন্তু নিমাদ খেয়াল করে দেখল, এই ঝিঝি যেন ঠিক সেই ঝিঝি নয়। শব্দটা অনেক বেশি জোরালো, আর তাতে বেশ একটা ওঠা-পড়া আছে। গান বাজনা সে জানে না, সুরজ্ঞানও নেই। কিন্তু তার যেন মনে হল, এই ঝিঝির ডাকের মধ্যে যেন একটু সুরেলা মারপ্যাঁচও আছে। কানের দোষ হলে বোধহয় এরকমই সব হয়।
বাঁ ধারে জলা, ডান ধারে জঙ্গল। মাঝখানে নিরিবিলি পথ ধরে খুব আনমনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল নিমাদকে। জলা থেকে তিড়িং করে লাফ দিয়ে ডাঙায় উঠে একটা ভেজা, লম্বাপানা, সবুজ রঙের বিটকেল লোক যেন শাঁ করে রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল।
নাঃ, কানের সঙ্গে সঙ্গে কি চোখটাও গেল? বিশুজ্যাঠা যেন বলছিলেন, চোখে চালসে ধরলে বা ছানি পড়লে লোকে ভুলভাল দেখে। মানুষের রং তো সবুজ হওয়ার কথাই নয়। তবে কি হোলি ছিল আজ? তাই বা কেমন করে হয়? আশ্বিন গিয়ে সবে কার্তিক পড়েছে, এ সময় তো হোলিখেলা হওয়ার কথা নয়!
বুড়ো বয়সে মাথারই গন্ডগোল হচ্ছে নাকি? দোনোমনো করে একটু পঁড়িয়ে পড়ল নিমচাঁদ। তারপর বুক ঠুকে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। জঙ্গল তার হাতের তালুর মতো চেনা। ছেলেবেলা থেকে যাতায়াত। বনকরমচা, বুনো কুল, মাদার ফল কত কী ফলত। ভিতরে একটা ভাঙা মনসা মন্দির আছে, একটা ভুতুড়ে নিলকুঠিও।
ভিতরবাগে ঢুকে জঙ্গলের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার জায়গায় একটু দাঁড়াল নিমাদ। অন্ধকারটা চোখে-সওয়া হয়ে এলে ধীরেসুস্থে এদিক-ওদিক সাবধানে এগোতে থাকল। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর একখানা জব্বর মোটা শিশুগাছের গুঁড়ির আড়ালে লোকটাকে দেখতে পেল নিমাদ। খুব জোরালো ঝিঝির শব্দ হচ্ছে নিমচাঁদের কানে। সে এমন শব্দ যে কান ঝালাপালা হয়ে যাওয়ার জোগাড়! নিমচাঁদ ভুল দেখছে কি না তা বুঝতে পারছে না, তবে তার ঠাহর হচ্ছে, লোকটার গায়ের রং শ্যাওলার মতোই গাঢ় সবুজ। আর লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর লোকটার হাতখানেক দূরে একটা প্রকাণ্ড দুধগোখরো ফণা তুলে হিসহিস করে দুলছে। ছোবল মারল বলে। কিন্তু লোকটা নড়ছেও না, চড়ছেও না।
নিমাদ এক পলকও সময় নষ্ট না করে ছুটে গিয়ে লোকটার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু খুবই অবাক হয়ে দেখল, লোকটাকে এক চুলও নড়াতে পারেনি সে। বরং লোকটাকে ধরতেই তার সর্বাঙ্গে কেমন যেন একটা শিরশিরে ভাব হচ্ছিল। আর দুধগোখরোটাও এই ফাঁকে একটা চাবুকের মতো ছোবল বসিয়ে দিল লোকটার ঊরুতে।
সাপটা যে তাকে কামড়েছে এটা যেন লোকটা টেরই পেল না। মুখ ঘুরিয়ে নিমচাঁদকে একটু দেখে নিয়ে তাকে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে পিছনে ঠেলে দিল। সেই ধাক্কায় প্রায় তিন হাত ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল নিমচাঁদ। এবং পড়ে গিয়েও দেখতে পেল, সবুজ লোকটা ভারী যত্ন করে নিচু হয়ে প্রকাণ্ড ভয়ংকর সাপটাকে তুলে নিয়ে কোমরে একটা জালদড়ির মতো জিনিসের থলিতে ভরে নিল।
নিমচাঁদ অতি কষ্টে উঠে বসে ভারী অভিমানের গলায় বলল, “বাপু হে, মানছি যে, আমার গায়ে আর আগের মতো জোর-বল নেই, বুড়োও হচ্ছি। কিন্তু সাপটা যে কামড়াল তার একটা ব্যবস্থা করো। এক্ষুনি দড়ির বাঁধন না দিলে মরবে যে!”
লোকটা তার দিকে আবার তাকাল মাত্র। কথার জবাব দিল না। “ওটা যে দুধগোখরো হে, ওর সাংঘাতিক বিষ!” লোকটা কথাটাকে গ্রাহ্যই করল না। অবশ্য অবাক কাণ্ড হল, লোকটার মধ্যে বিষক্রিয়ারও কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।
দুধগোখরো কামড়ালে এতক্ষণে তো ওর ঢলে পড়ার কথা! লোকটার বাঁ হাঁটুর মালাইচাকির উপরে ক্ষতস্থানটা এই আবছায়াতেও দেখতে পাচ্ছে নিমচাঁদ। সাপের ছোবল নিমচাঁদ ভালই চেনে। পাকা গোখরোটা পুরো বিষ ঢেলেছে লোকটার শরীরে। লোকটার শরীরে বিষটা হয়তো একটু দেরিতে কাজ করবে। কিন্তু রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।
নিমষ্টাদ একটা হাঁক ছেড়ে বলল, “কথাটা কানে যাচ্ছে না নাকি হে! বাঁধন না দিলে কী দুর্দশা হবে তোমার জানো?” বলে দাঁত কড়মড় করে নিমচঁদ উঠে লোকটাকে শক্ত করে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, “পাগল নাকি তুমি?”
লোকটাকে ছুঁতেই আবার কেমন একটা শিরশিরে ভাব টের পেল নিমাদ। এসব কী হচ্ছে বুঝতেই পারছে না সে।
লোকটা হঠাৎ নিমাদের মতো দশাসই একটা মানুষকে তার দুটো লিকলিকে হাতে তুলে মাথার উপর এক পাক ঘুরিয়ে গদাম করে ছুঁড়ে মারল। কোথায় লাগল কে জানে, নিমাদ মূর্ছা না গেলেও ঝিম ধরে খানিকক্ষণ পড়ে রইল। ওরকম লিকলিকে রোগা একটা লোকের গায়ে এত জোর হয় কী করে? তার উপর সদ্য সদ্য একটা বিষগোখরোর কামড় খেয়েছে!
একটু পরে যখন নিমষ্টাদ একটু ধাতস্থ হয়ে পিটপিট করে চাইল, তখন লোকটা মুখোমুখি একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। একটা পা সামনে ছড়ানো, আর-একখানা পা ভাঁজ করে বুকের কাছে ভোলা। হাবভাব তেমন মারমুখো নয়, বরং তার দিকে একটু করুণার চোখেই চেয়ে আছে।
নিমাদও উঠে বসল। কানে এখনও সেই প্রচণ্ড ঝিঝির শব্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু নিমাদের এখন আর শব্দটা তো অসহ্য মনে হচ্ছে না। দম নেওয়ার জন্য নিমচাঁদও মুখোমুখি গাছের গুঁড়িটায় ঠেস ৭২
দিয়ে বসল। লোকটা যে কেন এখনও বিষক্রিয়ায় ছটফট করছে না, মুখ দিয়ে গাজলা উঠছে না তা ভেবে পেল না নিমচাঁদ। লোকটা কি সাপের বিষের ওষুধ জানে?
ঝিঝির ডাকটার ভিতরে হঠাৎ নিমচাঁদ যেন একটা কিছু বুঝতে পারতে লাগল। ঠিক শোনা গেল না বটে, কিন্তু বোঝা গেল। যেন বলা হল, “সাপের বিষে আমাদের কোনও ক্ষতি হয় না।
নিমাদ সোজা হয়ে বসে বলল, “কথাটা তুমিই বললে নাকি বাপু? কিন্তু কীভাবে বললে? কোনও কথা তো শুনতে পেলুম না!”
“তুমি যে ঝিঝির ডাক শুনতে পাচ্ছ সেটা ঝিঝির ডাক নয়। ওটাই আমাদের কথা।”
“ও বাবা, কিন্তু ঝিঝির ডাকের কথা আমি বুঝলুম কী করে?”
“কথা নয়, তুমি ভাবটা বুঝতে পারছ।”
“ও বাবা! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! তা ওরকম একটা গোখরোর বিষ তুমি হজম করলে কী করে?”
“আমাদের শরীরে এমন জিনিস আছে যাতে এসব বিষ কাজ করে না।”
“তুমি লোকটা তা হলে কে বাপু? কোথা থেকে আসছ?”
“আমি অনেক দুরের লোক।”
“তোমার গায়ের রং ওরকম সবুজ কেন?”
“তোমার গায়ের রং কেন বাদামি?”
“আহা, মানুষের গায়ের রং তো এমনধারাই হয়।”
“আমাদের রংও আমাদের মতোই।”
“আমাকে তো বাপু তুমি গায়ের জোরে হারিয়েই দিলে। অবশ্য আমিও বুড়ো হয়েছি।”
“তুমি মোটেই বুড়ো হওনি।”
“হইনি! বলো কী? কানে শুনছি না, চোখে দেখছি না, পায়ে জোর-বল কমে গিয়েছে।”
“তোমার বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ। তোমার চোখ, কান, গায়ের জোর সবই ঠিক আছে। তবে আমাদের শরীরে যে শক্তি আছে তার একশো ভাগের এক ভাগও তোমাদের নেই।”
নিমাদ খানিকটা ভরসা পেয়ে বলল, “আমার বয়স তুমি কী করে জানলে?”
“যে-কোনও মানুষ, জীবজন্তু বা গাছপালা দেখে আমরা তাদের নির্ভুল বয়স বলে দিতে পারি। এই ক্ষমতা তোমাদের নেই। তোমরা মানুষের প্রজাতি হিসেবে অনেক ব্যাপারে পেছিয়ে আছ।”
নিমাদের কেমন যেন গা শিরশির করছিল। কথাগুলো ভারী আজগুবি ঠেকছে তার কাছে, কিন্তু অবিশ্বাসও করা যাচ্ছে না। ভুতুড়ে কাণ্ড কি না তাই-বা কে জানে?
কথাটা ভাবামাত্রই জবাব এল, “না, ভুতুড়ে কাণ্ড নয়।”
“কিন্তু আমি যে বড় ঘেবড়ে যাচ্ছি বাপু, তুমি ভাল লোক না খারাপ লোক সেটাই তো বুঝতে পারছি না। তোমার মতলবখানা
কী?”
“সেটা বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। তবে আমরা খারাপ লোক নই। তোমাদের কিছু উপকারও করতে চাই।”
“কীসের উপকার?”
“সেটা খুব জটিল বিষয়। তুমি একজন সরল সাধারণ মানুষ, তো জ্ঞানী নও। তোমার পক্ষে সব কিছু বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তবে আমি তোমার কাছে একটু সাহায্য চাই।”
“কী সাহায্য?”
“আগে এই জিনিসগুলো নাও।”
বলে লোকটা নিমাদের দিকে দু’খানা চ্যাপটা মতো ধাতুর চাকতি ছুঁড়ে দিল।
নিমাদ কুড়িয়ে নিয়ে দেখল, দুটো তেকোনা সোনালি রঙের জিনিস। বেশ ভারী। সোনাদানা সে বিশেষ চেনে না, তাই সোনা কি না বুঝে উঠতে পারল না। বলল, “এ কি সোনাটোনা নাকি রে বাবা?”
“হ্যাঁ, সোনা।”
“এর যে অনেক দাম!”
“হ্যাঁ। আর এটা তোমার পারিশ্রমিক।”
“তা কী করতে হবে বাপু?”
“কিছু লোক আমাদের সম্পর্কে জানতে চায় বলে খোঁজখবর নিতে আসছে। তারা আমাদের ক্ষতিও করতে পারে। তুমি একজন শক্তিশালী এবং সাহসী লোক। তুমি আজ রাতটা এই জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে পাহারা দেবে। পারবে না?”
“পারব। তারা এলে কী করতে হবে?”
লোকটা ছোট্ট একটা চার আঙুল লম্বা নলের মতো জিনিস তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, “এটা একটা বাঁশি। ফুঁ দিলে কোনও শব্দ হবে না। কিন্তু আমরা সংকেত পেয়ে যাব।”
“তা তোমরা কোথায় থাকো বাপু?”
“এই জঙ্গলের মধ্যেই, আরও গভীরে এবং মাটির নীচে।”
“তা শুধু বাঁশি বাজিয়েই খালাস! একটা লাঠিটাঠি হলে আমি একাই দশটা লোকের মহড়া নিতে পারি।”
“তার দরকার নেই। আমরা হিংস্র মানুষ নই, মারপিট পছন্দ করি না।”
“তা বললে হবে কেন বাপু! এই যে একটু আগে আমাকে তুলে রাম আছাড় মারলে?”
“সেটা তোমাকে মারার জন্য নয়। তুমি সত্যিই একজন শক্তপোক্ত লোক কি না সেটা পরীক্ষা করার জন্যই আছাড় মেরেছিলাম।”
নিমষ্টাদ একটু নাক কুঁচকে বলল, “শুধু পাহারা দেওয়া সার, বাঁশি বাজানোটা তেমন গা-গরম করা কাজ নয়। একটু লড়ালড়ি হলে বড় ভাল হত।”
“না, ওদের কাছে বন্দুক-পিস্তল আছে। হয়তো শিকারি কুকুরও থাকবে।”
“ঠিক আছে বাপু, সন্ধের পর-পরই আমি না হয় খেয়েদেয়ে চলে আসব। তা বাপু, এই সামান্য কাজের জন্য এত সোনাদানার কী দরকার ছিল?”
“সোনাকে তোমরা খুব মূল্যবান মনে করো তা আমরা জানি। কিন্তু তোমাদের এই পৃথিবীর মানুষরা নির্বোধ। তারা কখনও ভেবেই দেখেনি যে, সোদানার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান হল কাদামাটি, কেঁচো, পোকামাকড়, গাছপালা এবং অনেক বর্জ্য পদার্থ, আর জল। মানুষ যেদিন সেটা বুঝবে, সেদিনই সে সত্যিকারের সভ্য হবে।”
“তুমি বাপু কেবল গোলমেলে কথা বলো। যেগুলোর কথা বললে সেগুলো কি দামি জিনিস নাকি?”
“ওসব বুঝতে তোমাদের অনেক সময় লাগবে। কোন জিনিসের কী দাম সেটা বুঝতে পারাটাই বিচক্ষণতা।”
লোকটা টক করে উঠে দাঁড়াল। নিমচাঁদ দেখল, ঢ্যাঙা লোকটার মাথা এত উঁচুতে যে, সে পঁড়িয়ে হাত বাড়িয়েও নাগাল পাবে না।
স্তম্ভিত এবং বাক্যহারা নিমচাঁদ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে আর বুড়োদের মতো হাঁটা ধরল না। বরং কমবয়সি চনমনে একটা মানুষের মতো বড় বড় লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তার বুড়ো বয়সটা তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। আর সহজে এদিকপানে আসবে বলে মনে হয় না।
৭. কোনও বালব জ্বলছে না
কোনও বালব জ্বলছে না, টিউবলাইট জ্বলছে না, আলোর কোনও উৎসই নেই, অথচ ঘরটা স্নিগ্ধ একটা আলোয় ভরে আছে। সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু চোখে আলো লাগছে না। মাটির নীচে এ গুহার মতো বড় ঘরখানা আসলে একটা বেসমেন্ট। কিন্তু যেন প্রাগৈতিহাসিক। নীচে মাটি, দেওয়াল মাটির, কোনও আসবাবপত্র নেই। লম্বা, সবুজ অদ্ভুত চেহারার মানুষরা দেওয়ালের গায়ে পিঠ রেখে আসনসিঁড়ি হয়ে ধ্যান করার ভঙ্গিতে বসে আছে। তাদের মেরুদণ্ড সোজা। তারা এতটাই লম্বা যে, বসা অবস্থাতেও তাদের মাথা পাঁচ-ছ’ ফুট উপরে উঠে আছে। ঝিঝির শব্দে চারদিকে বাতাসে একটা ঢেউ খেলে যাচ্ছে।
বিজয়বাবু চারদিকটা খুব ভাল করে লক্ষ করলেন। গুনে দেখলেন সবুজ মানুষরা সংখ্যায় এগারোজন। হয়তো আরও আছে। এগারোজনই তাকে স্থির চোখে লক্ষ করছে। তাতে অবশ্য বিজয়বাবুর ভয় হচ্ছে না।
ঝিঝির ডাকের ভিতর একটা পরিবর্তন ঘটল। টানা আওয়াজটা নানা টুকরো টুকরো স্কেলে ভেঙে গেল, চড়া হল আবার খাদে নামল। বিজয়বাবু হঠাৎ সেই শব্দের ভিতর থেকে কথা বা বার্তা টের পেতে শুরু করলেন। তাকে প্রশ্ন করা হল, “তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে?”
“হ্যাঁ। আমি আপনাদের সম্পর্কে জানতে চাই।”
“তোমাদের পক্ষে আমাদের অনুধাবন করা অসম্ভব। তোমাদের মস্তিষ্কের অত ক্ষমতা নেই। তোমরা শুধু এটুকু জানলেই চলবে যে, আমরা অনেক দূর গ্রহের লোক।”
“কত দুর?”
“জেনে লাভ নেই। তোমাদের ধারণার বাইরে।”
“আপনারা আমাদের গ্রহে কেন এসেছেন তা কি জানতে পারি?”
“পারো। আমরা তোমাকেই আমাদের মধ্যস্থ হিসেবে ঠিক করে রেখেছিলাম। তুমি একটু বিজ্ঞান জানো। তুমি একজন সদাশয় এবং ভাল লোক।”
“আমি সদাশয় এবং ভাল লোক সেটা কী করে বুঝলেন? আমাকে তো আপনারা চেনেন না?”
“চিনি। আমরা আমাদের চারদিকে গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু এবং মানুষেরও সব কিছু জানতে পারি। প্রত্যেকটা মানুষ, গাছপালা, এমনকী, কীটপতঙ্গেরও কিছু ভাষা আছে। তোমরা বুঝতে পারো না, আমরা পারি।”
“আপনারা কি খুব জ্ঞানী মানুষ?”
“তোমাদের তুলনায় হাজার গুণ।”
“আমি কি আপনাদের কোনও ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি?”
“পারো। তোমার সাহায্যের উপরেই আমরা নির্ভর করছি। আমরা দস্যু বা লুটেরা নই। কিন্তু আমাদের একটু স্বার্থ আছে। তোমাদের কাছে আমরা কিছু চাই।”
“কী চান আপনারা?”
“খানিকটা জল, কয়েকটা কীটপতঙ্গ, কিছু গাছপালা আর কিছুটা বর্জ্য পদার্থ।”
“এসব কি আপনাদের নেই?”
“আছে। কিন্তু আমাদের গ্রহ তোমাদের গ্রহের চেয়ে পাঁচ গুণ বড়। আমাদের যথেষ্ট জল নেই, তোমাদের মতো এত প্রজাতির পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ নেই। জীববৈচিত্র্য অনেক কম এবং প্রাকৃতিক বর্জ্য পদার্থ যৎসামান্য। আমাদের গ্রহ খুব সুন্দর, আমাদের সভ্যতা অনেক বেশি প্রাগ্রসর, কিন্তু তোমাদের মতো এত প্রাকৃতিক সম্পদ, যার মূল্য তোমরা আজও বুঝে উঠতে পারোনি, তা আমাদের নেই। তাই বন্ধুভাবে আমরা তোমাদের কাছে এসব জিনিস চাইছি। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের সেটা বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব
আমরা তোমাকে দিতে চাই।”
“কতটা জল আপনাদের চাই?”
“পৃথিবীর সমুদ্রে যত জল আছে তার দশ ভাগের এক ভাগ।”
“সে তো অনেক জল! এত জল পৃথিবী থেকে সরে গেলে যে আমাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে! ঋতুচক্রের গোলমাল হবে, বৃষ্টিপাত হয়ে পড়বে অনিয়মিত। আর প্রায় গোটা একটা সমুদ্রই যদি লোপাট হয়ে যায়, তা হলে পৃথিবীর ওজন কমে যাবে, হয়তো বা আহ্নিক গতিও বদলে যেতে পারে।”
“তুমি খারাপ দিকটার কথা আগেই ভাবছ কেন? ভাল দিকটার কথাও ভাবো। পৃথিবী ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে, ধীরে ধীরে জলস্তর উপরে উঠছে। আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যেই নিচু এলাকাগুলো সমুদ্রের গ্রাসে চলে যেতে থাকবে। এই শতাব্দীর শেষে স্থলভূমির অনেকটাই নিমজ্জিত হয়ে যাবে, বহু দেশ মুছে যাবে মানচিত্র থেকে। সমুদ্রের মধ্যে এবং ধারে যেসব আগ্নেয়গিরি আছে, সমুদ্রের জল যদি তার মুখ পর্যন্ত উঠে যায়, তা হলে আগ্নেয়গিরির মধ্যে জল ঢুকে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটবে এবং সুনামির সৃষ্টি হবে তা এতই ভয়ংকর যে, উপকূলের বড় বড় সব শহর শুধু ভেসেই যাবে না, মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। আমরা যদি তোমাদের একটা সমুদ্র নিয়ে যাই তা হলে অন্তত সেই ভয়টা থাকবে না। তার উপর তোমরা পেয়ে যাবে অনেকটা নতুন স্থলভূমি, পেয়ে যাবে একটা আস্ত মহাদেশও।”
“পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা আপনাদের প্রস্তাব মানবেন না।”
“তাদের বুঝিয়ে বলল, আমরা অকৃতজ্ঞ নই। যে জিনিস আমরা নিয়ে যাব তাতে তোমাদের সামান্য ক্ষতি হবে বটে, কিন্তু আমরা প্রতিদানও দিতে জানি। বিনিময়ে আমরা তোমাদের বাতাসের দূষণের মাত্রা কমিয়ে দেব। ওজোন স্তরের ছিদ্র মেরামত করে দেব, আরও সবুজ করে দিয়ে যাব পৃথিবীকে।”
“এক সমুদ্র জল আপনারা কীভাবে নেবেন?”
“খুব সোজা। বঙ্গোপসাগরে নীচে আমাদের মহাকাশ ভেলা অপেক্ষা করছে, আর আকাশে এক লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে আমাদের বড় মহাকাশযান। সমুদ্রের জল আমাদের নিজস্ব পাম্পে খানিকটা শূন্যে তুলে নিলেই তা বরফের চাঙড়ে পরিণত হবে। খুব সূক্ষ্ম একটা জ্যাকেটে মুড়ে তা আমাদের মহাকাশযানের সঙ্গে সুতো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হবে। এরকম অজস্র চাঙড় করে জল নিয়ে যাওয়া কঠিন ব্যাপার কিছু নয়।”
দুশ্চিন্তায় বিজয়বাবুর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, উত্তেজনায় ঘাম হচ্ছে, বললেন, “আমি চেষ্টা করে দেখব।”
“কোনও প্রশ্ন আছে?”
“অনেক প্রশ্ন। আপনারা কোন ভাষায় কথা বলছেন? ভাষাটা আমি জানি না, কিন্তু সব বুঝতে পারছি কী করে?”
“আমরা ভাষা দিয়ে কথা বলি না। আমাদের কথা ধ্বনি-সংকেত। তোমার মস্তিষ্ক সেটা অনুবাদ করে নিচ্ছে।”
“পৃথিবীর চারদিকে অনেক উপগ্রহ ঘুরছে, সারাক্ষণ নানা জায়গা থেকে দূরবীক্ষণ আর রাডার দিয়ে আকাশের সর্বত্র নজর রাখা হচ্ছে। কোনও মহাকাশযানের পক্ষে এত সব নজরদারি এড়িয়ে পৃথিবীতে আসা সম্ভব নয়। আপনারা এলেন কী করে?”
“তোমাদের প্রযুক্তিকে ফঁকি দেওয়া কঠিন নয়। নামবার সময় আমরা কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের সন্ধানী যন্ত্রগুলোকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছিলাম, তবে তা মাত্র এক সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ের জন্য। তাই সেটা নিয়ে খুব একটা হইচই হয়নি। আর নেমে পড়ার জন্য আমাদের ওটুকু সময়ই যথেষ্ট।”
“সমুদ্রের তলায় আপনাদের যে যানটি লুকনো আছে সেটা কি আমাদের সাবমেরিনগুলো খুঁজে পাবে না?”
“না। আমাদের যানটি থেকে কোনও বিকীরণ ঘটে না। সেটা অবিকল একটা তিমি মাছের মতো ঘুরে বেড়াতে পারে।”
“আমি শুনেছি আপনারা জীবজন্তু এবং পোকামাকড় খুবই ভালবাসেন। এমনকী, একজন লোক বন্দুক দিয়ে শেয়াল মারতে গিয়েছিল বলে আপনারা তাকে মেরে ফেলেছেন।”
“কথাটা সত্যি নয়। লোকটা ভয় পেয়ে মারা যায়। তবে আমরা তাকে ফের বাঁচাতে পারতাম। সেটা করিনি। কারণ, পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা সব জীবজন্তুর চেয়ে বেশি। একটা মানুষের চেয়ে একটা শেয়ালের প্রাণের দাম বেশি।”
“আপনারা পশুপ্রেমিক, তার মানে কি আপনারা মাছ-মাংস খান না?”
“মাছ-মাংসকে আমরা খাদ্যবস্তু বলেই মনে করি না।”
“আমাদের বৈজ্ঞানিক এবং রাষ্ট্রপ্রধানরা যদি আপনাদের প্রস্তাবে রাজি না হন, তা হলে কী করবেন?”
“সেক্ষেত্রে আমরা জোর করেই তোমাদের সমুদ্র চুরি করব এবং কোনও প্রতিদানও পাবে না।”
“আপনারা কি এতটাই নিষ্ঠুর যে, আমাদের গ্রহটিকে বিপাকের মধ্যে ঠেলে দিয়ে চলে যাবেন?”
“তোমরা আমাদের চেয়েও অনেক নিষ্ঠুর, স্বার্থপর এবং বোকা।”
“একথা কেন বলছেন?”
“তোমাদের সৌরলোকে এই একটিই প্রাণবান গ্রহ। ঠিক তো?”
“হ্যাঁ, ঠিক।”
“প্রাণীদের তিনটি আশ্রয়। জল, মাটি, অন্তরীক্ষ। তাই না?”
“হ্যাঁ।”
“সমানুপাত বোঝো?”
“একটু-আধটু।”
“এই তিনটি আশ্রয়ে যেসব প্রাণীকুল থাকে এবং সবকিছুকে পাহারা দেয় যে উদ্ভিদ, তাদের সমানুপাত না থাকলে গ্রহের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। জানো?”
“জানি।”
“তবে মানো না কেন? পৃথিবীকে খনন করে করে জ্বালিয়ে দিলে তেল-কয়লা, সমুদ্রে-নদীতে ঢেলে দিলে বিষ, বাতাসে ছড়ালে তেজস্ক্রিয় কণা, এ তোমাদের গ্রহ নয়? এ কি নয় তোমাদের বাড়িঘর? কত প্রাণীর প্রজাতিকে অবলুপ্ত করে দিলে, মেরে ফেললে কত পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ। মাটি ঢেকে দিয়ে কেবল বাঁধানো শহরে ভরে দিলে পৃথিবী। ভোগের বস্তুর জন্য কত কলকারখানায় কণ্টকিত করে দিলে চারদিক!”
“আমরা আপনাদের তুলনায় নির্বোধ, স্বীকার করছি। এই গ্রহের মানুষ জ্ঞানী হয়ে জন্মায় না। তারা ঠেকে এবং অভিজ্ঞতা থেকে আজ নিজেদের সর্বনাশ বুঝতে পারছে। বিপরীত প্রক্রিয়ায় সেই সর্বনাশ রোখার জন্যও আমরা চেষ্টা করছি। আপনারা যদি আমাদের সমুদ্র এবং কীটপতঙ্গ সব নিয়ে যান, তা হলে আমাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবে।”
“আমাদের উপায় নেই।”
“আপনারা আমাদের হিতৈষীর মতো কথা বলছেন। কিন্তু যা করতে চাইছেন তাতে পৃথিবীর মঙ্গল হওয়ার কথা নয়। প্রকৃত শক্তিমানরা দুর্বলের শক্তিহীনতার সুযোগ নেয় না।”
“প্রকৃতির নিয়মের বাইরে কেউ নয়। দুর্বলের অধিকার প্রকৃতির নিয়মেই সীমাবদ্ধ। বাঘ হরিণকে খাবে, এটাই নিয়ম।”
“বাঘ ও হরিণ ইতর প্রাণী। বুদ্ধিমান নয়। তারা পৃথিবী ও প্রকৃতি বা পরিস্থিতির নিয়ামক হতে পারে না। বাঘ একসময় মানুষকেও খেত। কিন্তু মানুষ যখন অস্ত্র আবিষ্কার করল, তখন বাঘ হয়ে পড়ল বিপন্ন। বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষকে শক্তিমান করেছিল, সে প্রকৃতির সব নিয়ম মেনে নেয়নি।”
“বাঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে কী লাভ হয়েছে তোমাদের বলো! আর কটা বাঘ অবশিষ্ট আছে পৃথিবীতে? শুধু অস্ত্রধারণ করলেই হয় না। নিয়ন্ত্রণও অধিগত করতে হয়। আত্মভুক কাকে বলে জানো? যে নিজেকে খেয়ে ফেলে। সমষ্টিগতভাবে তোমরাও আত্মভুক। নিজেদের প্রজাতিকে মারো, পশুপাখি মারো, গাছপালা মারো? ওরাও যে তোমাদেরই অস্তিত্বের বিস্তার তা জানো না।”
মাথা নিচু করে বিজয়বাবু বললেন, “মানছি।”
মানুষটা হঠাৎ তার দিকে একটা থান ইটের মতো ভারী জিনিস ছুঁড়ে দিয়ে বলল, “এই নাও।”
নিখুঁত লক্ষ্যে জিনিসটা বিজয়বাবুর কোলের কাছে এসে পড়ল। কিন্তু গায়ে লাগল না। তিনি জিনিসটা তুলতে গিয়ে দেখলেন, সোনার রঙের একখানা অত্যন্ত ভারী ইট। কয়েক কেজি ওজন। সবিস্ময়ে তিনি বললেন, “কী এটা?”
“সোনা! এটা বিক্রি করলে তুমি অনেক টাকা পাবে। তাই দিয়ে তুমি তোমার ল্যাবরেটরির জন্য অনেক আধুনিক সরঞ্জাম এবং রাসায়নিক কিনতে পারবে।”
“এই সোনা আপনি কোথায় পেলেন?”
“সোনা আমরা সঙ্গে করে আনিনি। তোমাদের গ্রহেরই নানা ধাতুর পরমাণুর গঠন বদলে দিয়েছি মাত্র।”
“এটা কি ঘুষ?”
“ঘুষ কাকে বলে জানি না। তবে এটা আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন।”
“আমি শুনেছি আপনারা কাউকে কাউকে অনেক সোনা দিয়েছেন।”
“হ্যাঁ। আমরা মানুষের বন্ধুত্বই চাই। ইচ্ছে করলে আমরা পৃথিবীর সব মানুষকেই রাশি রাশি সোনা উপহার দিয়ে যেতে পারি।”
“তাতে সোনার দাম শুন্যে নেমে যাবে এবং পৃথিবীর অর্থনীতিতে দেখা দেবে বিরাট বিপর্যয়।
“সেটা হয়তো একটা ভারী মজার ব্যাপারই হবে। লোভী মানুষ বুঝতে পারবে সোনা একটা সাধারণ ধাতু ছাড়া কিছুই নয়।”
“আমি আপনাদের দান প্রত্যাখ্যান করছি। সোনা আমি নেব না।”
“বেশ তো। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান কোরো না। তা হলে তোমাদের ভাল হবে না।”
“বন্ধুত্ব সমানে সমানে হয়। আমরা আপনাদের পণবন্দি মাত্র। তবু আপনারা যে সৌজন্য প্রকাশ করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি এটাও বুঝতে পারছি, আপনারা যা চাইবেন তাই হবে। আমাদের কিছুই করার নেই।”
“এই সত্যটা তাড়াতাড়ি বুঝেছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ। এখন তুমি যেতে পারো। তোমাদের রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং বিজ্ঞানীদের প্রতিনিধিরা উপরে অপেক্ষা করছেন। তোমার পিছন দিকে যে গুহামুখ দেখছ, ওইটেই বেরোনোর পথ। যাও।”
বিজয়বাবু উঠলেন। গুহামুখে পৌঁছে ফিরে একবার চেয়ে দেখলেন, দু’জন সবুজ মানুষের পাহারায় পাঁচজন লোক গুহায় এসে ঢুকল। লতাপাতা দিয়ে তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। বিধ্বস্ত চেহারা। দেখে বোঝা যাচ্ছে তাদের উপর কিছু অত্যাচার হয়েছে। এদের মধ্যে অগ্নিকেও দেখতে পেলেন বিজয়বাবু। বোধহয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছিল। তাই মারধর খেতে হয়েছে। বিজয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে ঢালু বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। মানুষকে হয়তো এভাবেই তার দীর্ঘদিনের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। একটা সমুদ্র লোপাট হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে হয়তো নিয়ে যাওয়া হবে কীটপতঙ্গের বিরাট ঝক। আর কী কী নিয়ে যাবেন ওঁরা, জানেন না তিনি। তবে পৃথিবীর সামনে যে বিরাট দুঃসময় আসছে তাতে সন্দেহ নেই।
গভীর রাত। বিজয়বাবুর ল্যাবরেটরিতে গভীর দুশ্চিন্তা মুখে নিয়ে অঘোরখুড়ো, বীরেনবাবু, বিরাজজ্যাঠা, নীলকান্ত, অয়স্কান্ত, কৃষ্ণকান্ত, কানু, বটু, নব, হরেন সবাই হাজির। বিজয়বাবু বিপদের কথাটা তাঁদের বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলছিলেন। কথা শেষ হয়েছে। এখন সবাই গুম হয়ে বসা। কারও কথাটথা আসছে না।
ঠিক এই সময় উত্তরের বন্ধ জানলায় খুট খুট করে একটা শব্দ হল।
বিজয়বাবু নিচু গলায় বললেন, “কে?”
“আজ্ঞে, জানলাটা খুলুন। কথা আছে।”
বিজয়বাবু উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দেখতে পেলেন, গামছায় মুখ ঢাকা একটা বেঁটেমতো লোক দাঁড়ানো।
“কে হে তুমি?”
“আমি বঙ্কাচোর।”
“চোর! অ্যাঁ! কী সর্বনাশ! চোর আজকাল সাড়া দিয়ে আসা ধরেছে?”
“আহা, অত উঁচু গলায় কথা কইবেন না। বাতাসেরও কান আছে। তারা আবার সবই শুনতে পান কিনা।”
“কী চাও বাপু?”
“আজ্ঞে, গুরুতর কিছু কথা নিবেদন করেই চলে যাব।”
“অ। তা ভিতরে এসো বাপু। ভয় নেই।”
“আজ্ঞে, ভয়ডর থাকলে কি আমাদের চলে? তা হলে বরং দরজাটা খুলে দিন। গুহ্য কথা কিনা, খোলা জায়গায় বলাটা ঠিক হবে না।”
বিজয়বাবু দরজা খুলে দিলেন। বঙ্কা ভারী সংকোচের সঙ্গে ভিতরে ঢুকে হাতজোড় করে বলল, “পেন্নাম হই মশাইরা।”
বিজয়বাবু বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে। এবার কথাটা হোক।”
বঙ্কা মাথাটাথা চুলকে বলল, “আজ্ঞে, অপরাধ নেবেন না। পেটের দায়ে আমাকে চুরিটুরি করতে হয়। তা চুরি করি বলেই কিছু সুলুকসন্ধান জানা আছে। ইদানীং দেখছিলাম গাঁয়ের কিছু লোকের বেশ উন্নতি হতে লেগেছে। রামভরোসা নতুন দুটো মোষ কিনল, তার মা গিরিজাবুড়ি রুপোর বদলে সোনার বালা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দু’বেলা পোনা মাছের কালিয়া রান্না হচ্ছে বাড়িতে। তাই দেখেই একদিন সিঁধ দিলাম। কিন্তু কপাল খারাপ। বুড়ি সারাদিন গোবর কুড়োয়, ঘঁটে দেয়, রাতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোনোর কথা। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখি, বুড়ি উদুখলের ডান্ডাটা নিয়ে বসে আমার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। ঘা-কতক খেয়ে আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে প্রাণটা হাতে করে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলুম, এই যা। ৮৮
তবে তক্কে তক্কে কয়েকদিন নজর রাখার পর লক্ষ করলাম, বুড়ি রোজই দুপুরের দিকে ঝুড়িভরতি খুঁটে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে। জঙ্গলে ঘুঁটের খদ্দের থাকার কথা নয়। পিছু পিছু গিয়ে যা দেখলাম তাতে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়!”
বিজয়বাবু ম্লান হেসে বললেন, “সবুজ মানুষ তো!”
“যে আজ্ঞে, যাদের ডেরায় আজ আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।”
“তারপর কী হল?”
“বুঝলুম, সোনাদানা ওই ডেরাতেই আছে। বুড়ি একঝুড়ি খুঁটে বেচে এক মোহর করে পায়। তাও সে ইয়া বড় মোহর, অন্তত ভরি পাঁচেক ছাচা সোনা! মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে দিব্যি ডেরা বানিয়েছে। তা আজ মাঝরাতে ঢুকে পড়লাম মা কালীকে একটা প্রণাম ঠুকে।”
বীরেনবাবু বলে উঠলেন, “জব্বর সাহস তো তোমার?”
“আজ্ঞে না, সাহসের বালাই নেই। পেটের দায়ে প্রাণ বাজি রেখে ওসব করতে হয় আর কী। তবে কিনা একেবারে নির্যস প্রাণটাই যাওয়ার কথা। সুড়ঙ্গের অন্ধিসন্ধি তো জানা নেই। পড়বি তো পড় একেবারে দু-দুটো ঢ্যাঙা মানুষের সামনে। কিন্তু কী বলব মশাই, দু’জন যেন আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠে কুঁকড়ে লটকে পড়ে গেল।”
“বলো কী?”
“আজ্ঞে, এক বর্ণ বানিয়ে বলা নয়। মা কালীর দিব্যি।”
“তোমাকে দেখে ভয় পাওয়ার কী হল?”
“আজ্ঞে, সেই কথাই বলতে আসা।”
“বলে ফেলো বাপু।”
“ইদানীং চোখে একটু কম দেখছি বলে রাতবিরেতে কাজের খুব অসুবিধে হচ্ছে। তাই ভেবেছিলুম, একজোড়া চশমা হলে বড় ভাল হয়। তা দেখলাম, আমাদের কানু রোজ অঘোরখুডোর চশমা চোখে দিয়ে বটতলায় বসে লোকের ভূতভবিষ্যৎ দেখতে পায়। তা ভাবলুম ওরকম জোরালো চশমা হলে কাজের খুব সুবিধে। তা পরশু রাতে…!”
অঘোরখুড়ো হুংকার দিয়ে বললেন, “তাই চশমাজোড়া পাচ্ছি না বটে! এ তা হলে তোমার কাজ?”
বিজয়বাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, “আস্তে খুড়ো, আস্তে।”
বঙ্কা বিগলিত মুখে হাত কচলে বলল, “যে আজ্ঞে, আপনার চশমার গুণ আছে বটে খুড়ো। অন্ধকারেও সব দিব্যি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। কী বলব মশাই, মোট বারোখানা মোহর সরিয়েছি, দিব্যি গটগট করে বেরিয়েও এসেছি। তাই বলছিলাম, ওই বিটকেল লোকগুলোর সঙ্গে এমনিতে পেরে ওঠার জো নেই বটে, তবে…!”
বিজয়বাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, “চশমাজোড়া কোথায়?”
বঙ্কা চশমাজোড়া খাপসুদ্ধ বের করে বিজয়বাবুর হাতে দিয়ে বলল, “আজ্ঞে, কাজ হয়ে গেলে যদি চশমাজোড়া বখশিশ দেন তবে কাজকর্মের বড় সুবিধে হয়। বড় অনটন চলছে।”
“ওই লোক দুটোর কী হল দেখলে?”
“আজ্ঞে, দেখেছি। ফেরার সময় দেখলাম তখনও লটকে পড়ে আছে। তবে সাইজে যেন একটু ছোট লাগল।”
“ছোট! কিন্তু এসব হয় কী করে? তারা সাপের কামড়ে মরে না, দুনিয়ার কোনও কিছুকে ভয় পায় না!”
অঘোরখুড়ো বললেন, “ও একটা ব্যাপার আছে।”
“কী ব্যাপার খুড়ো?”
“বটুকবুড়ো আমাকে বলেছিল, চশমার অনেক রকম গুণ আছে।
সব গুণের কথা বটুকবুড়োর জানা ছিল না। মন্ত্রটন্ত্রের ব্যাপার আর কী।”
বিজয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, “তা হতে পারে না। একটা কোনও বিজ্ঞানসম্মত কারণ থাকতেই হবে। ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দে তো নব। দেখি, সত্যিই অন্ধকারে দেখা যায় কিনা!”
নব বাতিটা নিভিয়ে দেওয়ার পর চশমার ভিতর দিয়ে বিজয়বাবু দেখলেন, তিনি ঘরের সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। এমনকী, আলোর চেয়েও অনেক স্পষ্ট।”
বিজয়বাবু চিন্তিতভাবে বললেন, “বঙ্কা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, তা হলে হয়তো একটা উপায় আছে। আমি আজই ওই গুহায় আবার যেতে চাই।”
সবাই ‘না না করে আপত্তি জানাতে লাগলেন। বিজয়বাবু বললেন, “আমাদের ঘোর বিপদ, ওই গুহায় ওদের বারোজন আছে। আরও হয়তো আছে, আমরা জানি না। কিন্তু বারোজনের একজন হচ্ছে ওদের লিডার। নাঃ, আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। বঙ্কা, তুমি চলো আমার সঙ্গে। একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকতে হবে বাপু। তুমি পথ দেখাবে।”
“যে আজ্ঞে। অন্ধিসন্ধি সব আমার জানা।”
নিশুত রাতে জঙ্গলে ঢোকার মুখেই একটা বাধা পড়ল। বিভীষণ চেহারার একটা লোক লাঠি হাতে পথ আগলে দাঁড়িয়ে। একটা হাঁক দিল, “কে রে?”
বিজয়বাবু বললেন, “নিমচাঁদ, আমি হে, বিজয়বাবু।”
নিমচাঁদ হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, “বিজয়কর্তা, এই নিশুত রাতে এই জঙ্গলে কী মনে করে? এখানে যে সব বিটকেল কিম্ভুত জীবের আস্তানা। তারা যে সব কাঁচাখেগো দেবতা। এইবেলা পালিয়ে যান কর্তা।”
“সেই উপায় নেই নিমচাঁদ। পালিয়ে গেলে দুনিয়া ছারখার হয়ে যাবে।”
“কিন্তু কী করতে চান আপনি? হাতে বন্দুক-পিস্তল নেই। লাঠিসোঁটা নেই। তারা যে অসুরের চেয়েও বড় পালোয়ান! আমাকে এক ঝটকায় সাত হাত দূরে ছিটকে ফেলেছিল।”
“সেসব জানি। কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো হবে না। একটা চেষ্টা তো করতেই হবে।”
“তবে চলুন আমিও সঙ্গে যাই, আপনার সঙ্গে উটি কে?”
“এ হল বঙ্কা। পথ চেনাতে এসেছে।”
“খুব চিনি। পাকা চোর।”
বঙ্কা ভারী খুশি হয়ে বলল, “যে আজ্ঞে। বঙ্কার নাম পাঁচ গাঁয়ের লোক জানে।”
বঙ্কা জঙ্গলে ঢুকে আগে হাঁটতে হাঁটতে বলল, “গুহার অনেক মুখ। সব মুখ দিয়েই ঢোকা যায় বটে, তবে বিপদও আছে। ওই খালধারের মুখটাই ভাল।”
অন্ধকারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে চশমা-পরা বিজয়বাবু সবকিছু স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল, চশমা থেকে কোনও একটা বিচ্ছুরণ হয়। নইলে এমনটা সম্ভব ছিল না।
বিজয়বাবু ভারী অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ভাবতে ভাবতে। এই চশমা কোথা থেকে পেয়েছিলেন বটুকবুড়ো? কোন প্রযুক্তি বা অভিনব বস্তু দিয়ে এটা তৈরি তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। তবে চশমাটি অভিনব তাতে সন্দেহ নেই। দুনিয়াতে কত বিস্ময়ই যে এখনও আছে।
অন্যমনস্কতার দরুন বার দুই হোঁচট খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন। নিমচাঁদ ধরে ফেলল। নিচু স্বরে বলল, “এঁরা মানুষ তেমন খারাপ নয় বিজয়কর্তা। একটু কেমনধারা এই যা।”
“সেটা আমিও জানি। তবু পৃথিবীর পক্ষে এঁরা বিপজ্জনক। যদি এঁরা কোনও কারণে বিগড়ে যান তা হলে এক লহমায় বোধহয় দুনিয়া লয় করে দিতে পারেন।”
নিমচাঁদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তা পারেন কর্তা। এঁদের অসাধ্য কিছু নেই।”
খালধারের একটা ঢিবির সামনে এসে দাঁড়াল বঙ্কা। একটা শেয়ালের গর্তের মতো গর্ত দেখিয়ে বলল, “এইটে।”
বিজয়বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, “এটা দিয়ে ঢুকব কী করে?”
“মাথা গলিয়ে দিয়ে দেখুন, ভিতরে অনেক জায়গা।”
বিজয়বাবুও দেখলেন, তাই। মসৃণ পথ নেমে গিয়েছে ঢালু হয়ে। অন্ধকার। বিজয়বাবু অবশ্য সবই দেখতে পাচ্ছেন।
হঠাৎ বঙ্কা হাত চেপে ধরে বিজয়বাবুকে থামাল, “ঝিঝির ডাক শুনতে পাচ্ছেন কর্তা?”
“হ্যাঁ।”
“এসে গিয়েছি। ধীরে পা টিপে টিপে চলুন।”
সামনেই গুহার রাস্তাটা একটা বাঁক নিয়েছে। তারপরই আশ্চর্য আলোকোজ্জ্বল ঘর। আলোর কোনও উৎস নেই, তবু ঘর আলোয় আলোময়। এসব স্বপ্নের প্রযুক্তি ওদের হাতে। ওরা শত্রু না বন্ধু তা এখনও বুঝতেই পারছেন না বিজয়বাবু। কিন্তু তাঁর হাতে কোনও বিকল্পও নেই।
একটু উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল, দশ-বারোজন সবুজ মানুষ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে কিছু একটা দেখছে, তাদের প্রায় বাহ্যচৈতন্য নেই।
দু’দিকে বঙ্কা আর নিমচাঁদ, মাঝখানে বিজয়বাবু ঘরের ভিতরে নেমে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তীব্র ঝিঝির আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু এবার ঝিঝির আওয়াজে কোনও কথা
বুঝতে পারছেন না বিজয়বাবু। চুপচাপ লোকগুলোর দিকে চেয়ে বিজয়বাবু মনে মনে শুধু বললেন, “আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাদের ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিল না আমার। কিন্তু আমরা আমাদের মতো বেঁচে থাকতে চাই, যতদিন পারি।
হঠাৎ যেন তাঁদের উপস্থিতি এতক্ষণে টের পেয়ে সবুজ মানুষরা ফিরে তাকাল তাঁদের দিকে। তারপরই যেন স্তম্ভিত হয়ে কুঁকড়ে গেল। আর একের পর-এক ঢলে পড়ে গেল মাটির উপর।
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বিজয়বাবু মাটিতে পড়ে থাকা লম্বা আর সবুজ মানুষগুলোকে অপলক চোখে দেখছিলেন। শরীরে কোনও স্পন্দন নেই, ছটফটানি নেই। কেমন যেন কুঁকড়ে দলা পাকিয়ে শুয়ে আছে।
চশমাটা খুলে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি। সামনে পড়ে থাকা লোকটার কবজি ধরে নাড়ি দেখার চেষ্টা করলেন। নাড়ির স্পন্দনের মতো নয়, কিন্তু সেতারের মতো দ্রুত একটা ঝিনঝিন শব্দ হচ্ছে যেন।
একটু সময় লাগল। তারপর দেখতে পেলেন কুঁকড়ে-যাওয়া শরীর যেন আরও কুঁকড়ে ভিতরকার কোনও কেন্দ্রাভিগ টানে দলা পাকিয়ে আস্তে আস্তে গোল গোল হয়ে আসছে, অনেকটা বলের মতো।
বিজয়বাবুর কবজির ঘড়িতে যখন সকাল ছ’টা বাজে তখন দেখতে পেলেন, মেঝের উপর মানুষগুলোর আকার আস্তে আস্তে ছোট্ট পোকার মতো হয়ে যাচ্ছে। মানুষের পোকা হয়ে যাওয়ার একটা কাল্পনিক গল্প ফ্রাঞ্জ কাকা লিখেছিলেন বটে, কিন্তু এটা তো গল্প নয়। কী করে এই রূপান্তর ঘটল, কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, কিছুই বুঝতে পারলেন না বিজয়বাবু।
তবে একটা জিনিস দেখে এই দুঃখের ঘটনাতেও তিনি একটু খুশি হলেন। পোকাগুলো মৃত নয়। ছোট ছোট সবুজ গুবরেপোকার মতো আকারের সবুজ পোকারা একটু-আধটু নড়াচড়া করছে।
তিনি উঠে গুহাটা দেখলেন ভাল করে। এরা কি আসলে কোনওকালে পোকাই ছিল?মাটির নীচে থাকত? তারপর বিবর্তনের কোনও এক ধাক্কায় হয়ে গিয়েছিল লম্বা লম্বা মানুষ? এই চশমার কোনও রহস্যময় বিচ্ছুরণ কি আবার ওই বিবর্তনকে উলটো পথে চালিত করেছে? প্রশ্নগুলো জরুরি। কিন্তু জবাব কে দেবে?
নিমচাঁদ একটা থাবড়া তুলেছিল, “দেব নাকি নিকেশ করে?”
“না নিমচাঁদ। পৃথিবীতে নতুন প্রজাতির একটা পতঙ্গ হল। বেঁচে থাকতে দাও। পোকামাকড়কে যত বাঁচিয়ে রাখবে তো নিজেদের বাঁচার পথ প্রশস্ত হবে।”
বঙ্কা কাজের লোক, পোকামাকড় নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। ভিতরের কোনও উপগুহা থেকে দু’বস্তা সোনার চাকতি এনে বলল, “এই যে, দু’বস্তা। মেলা মোহর। কী করা যায় বলুন তো?”
“কিছু তুমি নাও, কিছু গাঁয়ের গরিব-দুঃখীকে দিয়ে। আর কিছু গাঁয়ের সংস্কারে কাজে লাগিয়ো৷”
ভিতরে আর-একটি প্রকোষ্ঠ থেকে পাঁচজন সংজ্ঞাহীন লোককে উদ্ধার করা হল, তাদের মধ্যে অগ্নিও। চোখে-মুখে জলের ঝাঁপটা দেওয়ার পর জ্ঞান ফিরতেই তাদের প্রশ্ন, “ওরা কোথায়?”
বিজয়বাবু শুধু বললেন, “চলে গিয়েছে।”
“আমাদের সমুদ্র?”
“আছে। চিন্তা নেই। ওরা আর আসবে না।”
বিজয়বাবু দেখতে পাচ্ছিলেন, পোকাগুলো মহানন্দে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেড়াক, ওরা এই নতুন জীবনও উপভোগ করুক।
(সমাপ্ত)